- বুলবুলভাজা ধারাবাহিক স্মৃতিকথা শনিবারবেলা

-
কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন
ইমানুল হক
ধারাবাহিক | স্মৃতিকথা | ০৫ জুলাই ২০২৫ | ৯২০ বার পঠিত | রেটিং ৪.৭ (৩ জন) - কথা - ১ | কথা - ২ | কথা - ৩ | কথা - ৪ | কথা - ৫ | কথা - ৬ | কথা - ৭ | কথা ৮ | কথা - ৯ | কথা - ১০ | কথা - ১১ | কথা - ১২ | কথা - ১৩ | কথা - ১৪ | কথা - ১৫ | কথা - ১৬ | কথা - ১৭ | কথা - ১৮ | কথা - ১৯ | কথা - ২০ | কথা - ২১ | কথা - ২২ | কথা - ২৩ | কথা - ২৪ | কথা - ২৫ | কথা - ২৬ | কথা - ২৭ | কথা - ২৮ | কথা - ২৯ | কথা - ৩০ | কথা - ৩১ | কথা - ৩২ | কথা - ৩৩ | কথা - ৩৪ | কথা - ৩৫ | কথা - ৩৬ | কথা - ৩৭ | কথা - ৩৮ | কথা ৩৯ | কথা ৪০ | কথা ৪১ | কথা ৪২ | কথা ৪৩ | কথা ৪৪ | কথা ৪৫ | কথা ৪৬ | কথা ৪৭ | কথা ৪৮ | কথা ৪৯ | কথা ৫০ | কথা ৫১ | কথা ৫২ | কথা ৫৩ | কথা ৫৪ | কথা ৫৫ | কথা ৫৬ | কথা ৫৭ | কথা ৫৮ | কথা ৫৯ | কথা ৬০ | কথা ৬১ | কথা ৬২ | কথা ৬৩ | কথা ৬৪ | কথা ৬৫ | কথা ৬৬ | কথা ৬৭ | কথা ৬৮ | কথা ৬৯ | কথা ৭০ | কথা ৭১ | কথা ৭২ | কথা ৭৩ | কথা ৭৪ | কথা ৭৫ | কথা ৭৬, ৭৭, ৭৮ | কথা ৭৯ | কথা ৮০ | কথা ৮১ | কথা ৮২, ৮৩, ৮৪ | কথা ৮৫, ৮৬, ৮৭
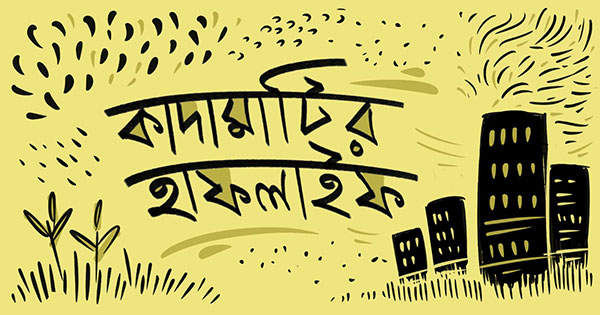
ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায় কথা - ৬৪
বর্ধমান শহরে এসে যাত্রার প্রতি আগ্রহ কমল। কারণ, শহরে যাত্রাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে দেখা হয়। এখানে নাটক হচ্ছে সংস্কৃতি, যাত্রা ঠিক অপসংস্কৃতি নয়, তবে উচ্চকিত ব্যাপার। যাত্রা নিয়ে উদাসীনতা শুধু নয়, গোপন ও প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভূত ক্ষতি করেছে। কারও গোপন নির্দেশ ছিল কি না জানি না, যাত্রার অনুমতি দিতে খুব বেগড়বাঁই করতো প্রশাসন। করের ঝামেলা বাড়ল। একটা কারণ হতে পারে, যাত্রার আয়োজকদের বড় অংশ ছিলেন কংগ্রেসের লোক। কিন্তু তাঁরা তো রক্তে রোয়া ধান, পদধ্বনি, মা মাটি মানুষ, হোচিমিন--এর মতো অজস্র প্রগতিশীল যাত্রা মঞ্চস্থ করিয়েছেন। হয়েছে, বামপন্থীদের পরোক্ষ উদ্যোগে, হিটলার, কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুঙ, রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা র মতো তরুণ অপেরার অসাধারণ সব যাত্রাপালা। হরেকৃষ্ণ কোঙার বলতেন, আমাদের একটা জনসভায় বক্তব্যের চেয়ে এইসব যাত্রা অনেক কাজের।
উৎপল দত্ত যে সব পালা লিখেছেন, রাইফেল, বৈশাখী মেঘ, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, কুঠার, নীল রক্ত, সাদা পোষাক, তুরুপের তাস-- রাজনৈতিক চেতনা গড়তে বিপুল ভূমিকা নেয়।
সিপিএমের লোকদের হাতে আশির দশকের শুরুতেও তেমন পয়সা ছিল না। তাঁরা খুব বেশি পেশাদার যাত্রার আয়োজন করতে পারতেন না। তবে অপেশাদার বা অ্যামেচার যাত্রায় বামপন্থীরা সচেতনভাবে যোগ দিতেন।
অভিনয় নৈপুণ্য দিয়ে জনমন জয় করে দলের ক্যাডার ও সমর্থক বাড়াতে। ফুটবল দাবা এইসব খেলাও খুব কাজে আসতো। আশির দশকের শেষ দিক থেকে দলে মুখে মারিতং জগৎ ও গ্রুপবাজদের খুব প্রাধান্য বেড়ে গেল।
এরা জনগণের নেতা নয় দলের একটা গোষ্ঠীর জোরে নেতা হতে লাগলেন।
তার বিষফল ফলল।
আগে নেতা হতো নৈপুণ্যের জোরে। জনগণের পছন্দ। এখন হল ইয়েসম্যান তৈরির নেতা প্রকল্প।
সিপিএমকে আশির দশকের মাঝ পর্যন্ত মিল মালিকরাও খুব একটা চাঁদা দিতে চাইতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল, এই সরকার ইন্দিরা গান্ধী বেশিদিন চলতে দেবেন না। আমেরিকাও চায় না, ইন্দিরাও চান না। অতএব সরকার ভেঙে দেওয়া হবে। সিপিএমের লোকেরাও অনেকেই তাই ভাবতেন। ইন্দিরা গান্ধীর অকাল মৃত্যু সব হিসেব, জল্পনা বদলে দিল। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু মহিলাদের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আমাদের পিসি, ময়না ফুফু, ভোটের দিন মার পর্যন্ত খেয়েছেন, ভাইয়ের পার্টি কাস্তে হাতুড়িতে ভোট দেন বলে। লুকিয়ে দিতে পারতেন, তা স্বভাবে নেই। যা করবেন, বলেই করবেন। ভাইয়ের মতো। সেই ময়না ফুফু টিভিতে ইন্দিরা গান্ধীর শেষ যাত্রা দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। এবং ভোটের পর ভাইকে খবর পাঠালেন, এবার ইন্দিরা গান্ধীর পার্টিকেই ভোট দিয়েছি। মেয়েটাকে এমন করে মেরে দিলে গো!
ইন্দিরা গান্ধী জীবিত থাকতে আমার ফুফু কোনওদিন কংগ্রেসকে ভোট দেননি। অমানবিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দিলেন। এটা শুনে আমার আব্বা বললেন, এবার আর রক্ষা নেই। ময়না পর্যন্ত কংগ্রেসের হাত চিহ্নে ছাপ দিলে। তখন ব্যালট পেপারে ভোট হতো। স্ট্যাম্প মারতে হতো পছন্দের প্রার্থীর নামের পর চিহ্নের পাশে। ইভিএম তখন কল্পনাতেও আসেনি। সেবার ৪২টার মধ্যে কংগ্রেস ১৬ টা আসন পেল পশ্চিমবঙ্গে। আর জ্যোতি বসু বললেন, জীবিত ইন্দিরার চেয়ে মৃত ইন্দিরার শক্তি বেশি।
একথাও বললেন, জনগণও মাঝে মাঝে ভুল করেন। আবেগের বশে।
এই শক্তি বৃদ্ধির কারণেই কিনা জানি না, আর ভুল পরামর্শদাতাদের প্ররোচনায় বামফ্রন্ট সরকারের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন রাজীব। সেই পরামর্শদাতাদের অধিকাংশই এখন বিজেপির সঙ্গে। সংসদে শাউটিং ব্রিগেড নামে রাজীবের বন্ধু বান্ধবের একটা দল ছিল।
আলুওয়ালিয়া, টাইটলাররা ছিলেন সেই ব্রিগেডের সদস্য। কাছের মানুষ ছিলেন অরুণ নেহরু, আরিফ মহম্মদ খান ( এখন কেরালার রাজ্যপাল। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি রাজভবনে সঙ্ঘের পতাকা তুলে বিতর্কিত)।
কলকাতাকে সম্ভবত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, মিছিল নগরী। (এখন আর নেই!)। নাতি রাজীব গান্ধী আস্ফালন করে বললেন, মুমূর্ষু নগরী। আরও বললেন, জ্যোতি বসু রিটায়ার করুন। জ্যোতি বসু কম কথা বলতেন, বললেন, আগে ওঁকে রিটায়ার করাই তারপর ভাবব। রিটায়ার করিয়েই ছাড়লেন। তবে এই বাদ প্রতিবাদ ভারতের ইতিহাসের জন্য ভালো হয়নি। সঙ্ঘ পরিবারের পোয়া বারো হলো। শাহবানু মামলা, তার জেরে মুসলিম মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করতে মুসলিম মহিলা বিল, এবং এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করতে রাম মন্দিরের তালা খোলা, রাজীবের মাচান বাবার আশির্বাদ নিতে যাওয়া-- সব মিলিয়ে দলে ভাঙ্গন ধরলো। সাংবাদিক অরুণ শৌরির তখন দেশজুড়ে খ্যাতি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা ঝড় তুলল, বোফর্স কেলেঙ্কারি হয়েছে। অরুণ শৌরি পরে বিজেপির শিল্প বেচা দপ্তরের মন্ত্রী হন। জলের দরে হোটেল বা অন্য শিল্প বেচেন। সঙ্ঘ পরিবারের ইন্ধনে বামপন্থীদের গোপন সমর্থনে রাজীব গান্ধীর সরকারের অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং অর্থমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন দুর্নীতির অভিযোগ করে।
১৯৮৭তে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জ্যোতি বসু, ভিপি সিং, বাজপেয়ী মিলে বিশাল সমাবেশ। রাজীবকে উৎখাত করার ডাক দেওয়া হল।
কদিন আগে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আলী খান রনো ভাইয়ের আত্মজীবনী পড়ছিলাম। শতাব্দী পেরিয়ে।
ঢাকায় যখন যাই, তিনি নিজে উপহার দিয়েছিলেন। পড়া হয়নি। এইবার পড়লাম। অশোক মিত্রের আত্মজীবনী 'আপিলা চাপিলা', অমর্ত্য সেনের 'জগৎকুটির' ফিরে পড়লাম।
হায়দার আকবর খান রনোকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতা রণদিভে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন।
রনো ভাই সিপিএমের নেতাদের বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি কমিউনিস্টদের জন্য ভালো।
রনদিভে তার জবাবে বলেন, মুশকিল কী জানেন, গোটা পৃথিবী জুড়েই এই অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি যখনই খুব ভালো, তখনই কমিউনিস্টরা মারাত্মক ভুল করে বসেন।
আমার ব্যক্তিগত বিচারে ১৯৭৫-এ সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে জোট, ১৯৮৭ &তে আবার পরোক্ষ জোট এবং লাগাতার কংগ্রেস বিরোধিতা ও সঙ্ঘ পরিবারের বিপদ সম্পর্কে ভুল ধারণা-- ভারতের বর্তমান অবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী।
মুখে বলা হয়েছে, কংগ্রেস বিজেপি দুটোই সমান বিপদ। কাজে, কংগ্রেস বিরোধিতা মূল।
যাই হোক, আবার ফিরে যাই যাত্রার কথায়। একথা সত্য, কংগ্রেসের নেতারা অনেক অত্যাচার করেছেন সত্তর দশকে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের কোনও বড় নেতা জেলে যাননি জরুরি অবস্থার সময়।
যাত্রা গ্রাম বাংলার ও মফস্বল শহরের বিবেকের কাজ করতো। যে কাজ করতো একসময় গ্রিক নাটকগুলো। করতো সমাজ শোধন ও বিপ্লবী চিন্তা প্রসারের কাজ। নাটকের প্রভাব আছে। তবে তা সীমিত। নির্দিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ঘোরাফেরা।
যাত্রার দর্শক প্রকৃত অর্থে আমজনতা।
গ্রামের নিঃস্ব হতদরিদ্র মহিলাকেও যাত্রার আসরে খুঁজে পাওয়া যেত। সেটাই তাঁর বিনোদন ও লোকশিক্ষা আসর।
নাটকে দর্শক আসে। যাত্রা দর্শকের কাছে যেত।
যাত্রা দলের বাসের পিছনে হাজার হাজার লোক ছুটতো। যে পথে বাস যেতো ভিড় জমে যেতো রাস্তার দুপাশে।
যাত্রার নায়ক নায়িকাদের মতো জনপ্রিয়তা জ্যোতি বসু মমতা ছাড়া আর কেউ পাননি পশ্চিমবঙ্গে। তবে রাজনৈতিক নেতারাও এতটা পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। আইনজীবী একরামুল বারি যাত্রার বাসের পেছনে ছোটার গল্প করছিলেন সেদিন।
শহরে এসে রথের দিন আলাদা করে কাগজ কেনা রইল। তবে এবার সেটা দেওয়াল লেখার টাইপ নকল করার জন্য।
গ্রামে খবরের কাগজ সকালে নয়, পৌঁছাতো নটা দশটার সময়। এটা বর্ধমানের গ্রাম। বাঁকুড়ার গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা তিনটা চারটা হয়ে যেত। বলছিলেন কবি ভজন দত্ত। আর বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের ছেলে প্রদীপ কেজরিওয়ালও তাই জানাল। প্রদীপ কেজরিওয়াল মাড়োয়ারি পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা বাংলা মাধ্যমে পড়েছেন। যুগান্তর কাগজের গ্রাহক ছিলেন। প্রদীপ কেজরিওয়াল নিজেও বাংলা মাধ্যমে পড়েছে। আমাদের সঙ্গে। এখন বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু ছেলেমেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ায়নি। বাংলা মাধ্যমেই পড়িয়েছে। প্রদীপ কথায় কথায় এত বাংলা প্রবাদ বলে, চমকে যেতে হয়।
গ্রামে সকাল সকাল বাংলা কাগজ ঢোকানোর মূল কৃতিত্ব 'ওভারল্যান্ড' নামে এক চিটফান্ডের। কাগজের সম্পাদক ছিলেন অজিত ভাওয়াল। ওভারল্যান্ড কাগজ প্রথম গ্রাম বাংলার খবরকে গুরুত্ব দেয়। আগে কলকাতার কাগজ মানে সেখানে গ্রাম বাংলার খবর মানে খুন খারাপির কথা।
ওভারল্যান্ড বাধ্য করেছে বাংলা কাগজকে গ্রাম বাংলাকে গুরুত্ব দিতে । বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম জেলায় গ্রামে সকাল সকাল কাগজ পৌঁছানোর কৃতিত্ব 'সংবাদ' পত্রিকার। নয়ের দশকে।
এক টাকা দামের কাগজ। এত জনপ্রিয় হয় যে আনন্দবাজার পত্রিকাকেও দাম কমাতে হয়। বাকিদেরও।
(ক্রমশঃ)
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।কথা - ১ | কথা - ২ | কথা - ৩ | কথা - ৪ | কথা - ৫ | কথা - ৬ | কথা - ৭ | কথা ৮ | কথা - ৯ | কথা - ১০ | কথা - ১১ | কথা - ১২ | কথা - ১৩ | কথা - ১৪ | কথা - ১৫ | কথা - ১৬ | কথা - ১৭ | কথা - ১৮ | কথা - ১৯ | কথা - ২০ | কথা - ২১ | কথা - ২২ | কথা - ২৩ | কথা - ২৪ | কথা - ২৫ | কথা - ২৬ | কথা - ২৭ | কথা - ২৮ | কথা - ২৯ | কথা - ৩০ | কথা - ৩১ | কথা - ৩২ | কথা - ৩৩ | কথা - ৩৪ | কথা - ৩৫ | কথা - ৩৬ | কথা - ৩৭ | কথা - ৩৮ | কথা ৩৯ | কথা ৪০ | কথা ৪১ | কথা ৪২ | কথা ৪৩ | কথা ৪৪ | কথা ৪৫ | কথা ৪৬ | কথা ৪৭ | কথা ৪৮ | কথা ৪৯ | কথা ৫০ | কথা ৫১ | কথা ৫২ | কথা ৫৩ | কথা ৫৪ | কথা ৫৫ | কথা ৫৬ | কথা ৫৭ | কথা ৫৮ | কথা ৫৯ | কথা ৬০ | কথা ৬১ | কথা ৬২ | কথা ৬৩ | কথা ৬৪ | কথা ৬৫ | কথা ৬৬ | কথা ৬৭ | কথা ৬৮ | কথা ৬৯ | কথা ৭০ | কথা ৭১ | কথা ৭২ | কথা ৭৩ | কথা ৭৪ | কথা ৭৫ | কথা ৭৬, ৭৭, ৭৮ | কথা ৭৯ | কথা ৮০ | কথা ৮১ | কথা ৮২, ৮৩, ৮৪ | কথা ৮৫, ৮৬, ৮৭
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 দীপ | 2402:3a80:198f:101d:878:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১২:১৭732302
দীপ | 2402:3a80:198f:101d:878:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১২:১৭732302- বাংলাদেশের পরিস্থিতি সারা পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে। তবে নির্লজ্জরা দেখতে পায়না!
 দীপ | 2402:3a80:198d:c6a3:778:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১২:৫৭732303
দীপ | 2402:3a80:198d:c6a3:778:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১২:৫৭732303- মহাবিপ্লবীর কথা খুব স্পষ্ট! কংগ্রেসের ল্যাজ ধরতে হবে! মহাবিপ্লবী যেমন মাকু ছেড়ে চটিতে গেছেন!
 কৌতূহলী | 103.249.***.*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৩:২৯732304
কৌতূহলী | 103.249.***.*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৩:২৯732304- ওভারল্যান্ড চিটফান্ডের কাগজ ছিল , কিন্তু কাগজটার কোয়ালিটি নাকি খুবই ভাল ছিল। বাবার কাছে শুনেছি
 কৌতূহলী | 103.249.***.*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৩:৩৩732305
কৌতূহলী | 103.249.***.*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৩:৩৩732305- পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের কোনও বড় নেতা জেলে যাননি জরুরি অবস্থার সময়।
এটা ঠিক কি? আমি তো পড়েছিলাম ৭৭ সালের নির্বাচনের সময় সিপিএমের সব বড় নেতাই জেলে ছিলেন
 দীপ | 2402:3a80:198b:7bb:678:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৭:২০732308
দীপ | 2402:3a80:198b:7bb:678:5634:1232:***:*** | ০৫ জুলাই ২০২৫ ১৭:২০732308- পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত কোনো নেতা জেলে যাননি। জ্যোতির্ময় বসুকে দিল্লিতে গ্রেফতার করা হয়েছিলো! সেই সময়ের ইতিহাস যেটুকু পড়েছি, সেখান থেকেই বলছি।
 কৃশানু ভট্টাচার্য্য | 115.187.***.*** | ০৬ জুলাই ২০২৫ ১৫:৫২732319
কৃশানু ভট্টাচার্য্য | 115.187.***.*** | ০৬ জুলাই ২০২৫ ১৫:৫২732319- ৭৫ এবং ৮৪ নিয়ে মন্তব্য টি অনেকটাই ঠিক।আর ওভারল্যান্ড কাগজটায় একসময় লিখেছি। বেকবাগান এলাকায় বাংলাদেশ ভিসা অফিসের পাশে ওদের অফিস ছিল। জেলা র খবরের জন্য দুটো পাতা থাকত। স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটা পাতা থাকত।
-
Eman Bhasha | ০৬ জুলাই ২০২৫ ১৮:২৮732322
- . ধন্যবাদ কৃশাণু
-
Eman Bhasha | ০৬ জুলাই ২০২৫ ২০:৩১732325
- ধন্যবাদ কৃশানু
 স্বপ্নময় চক্রবর্তী | 2409:4060:eca:a133::284a:***:*** | ০৭ জুলাই ২০২৫ ১৫:১০732333
স্বপ্নময় চক্রবর্তী | 2409:4060:eca:a133::284a:***:*** | ০৭ জুলাই ২০২৫ ১৫:১০732333- খুব ভালো হচ্ছে। এসব আমার স্মৃতি তে খোঁচা দেয়। আমার অনেক কথাই যেন ফিরে পাই।
-
Eman Bhasha | ০৭ জুলাই ২০২৫ ২১:৫৬732335
- ধন্যবাদ স্বপ্নময়দা। আপনি পড়ছেন জেনে খুব ভালো লাগছে
 তৌহিদ হোসেন | 42.108.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৫:০২733817
তৌহিদ হোসেন | 42.108.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৫:০২733817- যাত্রার নায়ক নয়িকারা সত্যিই এত জনপ্রিয় ছিলেন। আশির দশকের শুরুর দিকে আমিও গ্রামে দেখেছি। নব্বই দশক থেকেই সব বদলে যেতে লাগল। কারণ টিভি। অনবদ্য স্যার❤
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












