- বুলবুলভাজা ধারাবাহিক স্মৃতিকথা শনিবারবেলা

-
কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন
ইমানুল হক
ধারাবাহিক | স্মৃতিকথা | ১২ জুলাই ২০২৫ | ৭৬৪ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - কথা - ১ | কথা - ২ | কথা - ৩ | কথা - ৪ | কথা - ৫ | কথা - ৬ | কথা - ৭ | কথা ৮ | কথা - ৯ | কথা - ১০ | কথা - ১১ | কথা - ১২ | কথা - ১৩ | কথা - ১৪ | কথা - ১৫ | কথা - ১৬ | কথা - ১৭ | কথা - ১৮ | কথা - ১৯ | কথা - ২০ | কথা - ২১ | কথা - ২২ | কথা - ২৩ | কথা - ২৪ | কথা - ২৫ | কথা - ২৬ | কথা - ২৭ | কথা - ২৮ | কথা - ২৯ | কথা - ৩০ | কথা - ৩১ | কথা - ৩২ | কথা - ৩৩ | কথা - ৩৪ | কথা - ৩৫ | কথা - ৩৬ | কথা - ৩৭ | কথা - ৩৮ | কথা ৩৯ | কথা ৪০ | কথা ৪১ | কথা ৪২ | কথা ৪৩ | কথা ৪৪ | কথা ৪৫ | কথা ৪৬ | কথা ৪৭ | কথা ৪৮ | কথা ৪৯ | কথা ৫০ | কথা ৫১ | কথা ৫২ | কথা ৫৩ | কথা ৫৪ | কথা ৫৫ | কথা ৫৬ | কথা ৫৭ | কথা ৫৮ | কথা ৫৯ | কথা ৬০ | কথা ৬১ | কথা ৬২ | কথা ৬৩ | কথা ৬৪ | কথা ৬৫ | কথা ৬৬ | কথা ৬৭ | কথা ৬৮ | কথা ৬৯ | কথা ৭০ | কথা ৭১ | কথা ৭২ | কথা ৭৩ | কথা ৭৪ | কথা ৭৫ | কথা ৭৬, ৭৭, ৭৮ | কথা ৭৯ | কথা ৮০ | কথা ৮১
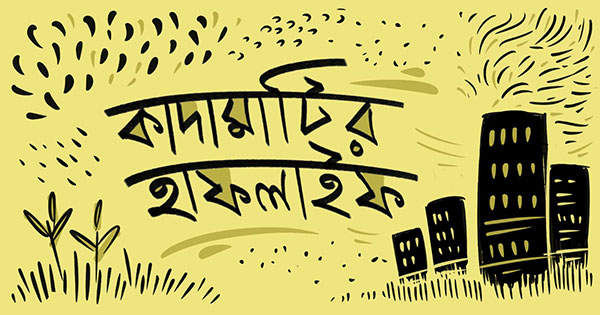
ছবি: রমিত চট্টোপাধ্যায় কথা - ৬৫
গ্রাম বাংলা ও মফস্বল শহরে অজস্র ছোট পত্রিকা ছিল। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক। কিছু জেলা শহরে দৈনিকও ছিল। আসানসোল থেকে বের হতো দৈনিক লিপি, কাঁথি থেকে দৈনিক তীরভূমি, বর্ধমান থেকে সদানন্দ সরকারের পত্রিকা ( নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না), পুরুষোত্তম সামন্ত সম্পাদিত দৈনিক মুক্তবাংলা। সত্যজিৎ রায় 'গণশত্রু' ছবি বানাবেন বলে দৈনিক মুক্তবাংলার প্রেস ছাপার পদ্ধতি ইত্যাদি দেখেছিলেন। এগুলো আশির দশকে অফসেট নয় লেটার প্রেসে টাইপ করে ছাপা হতো। কলকাতার দৈনিকগুলোর মানসিকতায় এই পত্রিকাগুলো ঘা দিতে সক্ষম হয়নি। হল, ওভারল্যান্ড। আটের দশকে চিটফান্ডের খুব রমরমা বাড়ে। একটা কথা চালু ছিল, এমন কোনও গ্রাম নেই, যেখানে সিপিএম আর পিয়ারলেস নাই। পিয়ারলেস, ফেভারিট, ওভারল্যান্ড, ভেরোনা ইত্যাদি নানা সঞ্চয় সংস্থা বেড়ে ওঠে। সঞ্চয়িতা কলকাতায় যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, গ্রাম বাংলায় ততটা যায়নি। কিন্তু বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র চিটফান্ড বন্ধের চেষ্টা করায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সঞ্চয়িতা বন্ধ হয়ে যায়। এর অন্যতম কর্ণধার শম্ভু সেন বহুতল ছাদ থেকে পড়ে মারা যান। অনেকের মত, ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। ভেরোনা, ফেভারিট, পিয়ারলেস বন্ধের বিরুদ্ধে আবার সিটুর নেতৃত্বে আন্দোলন হয়। ছাত্রনেতা হিসেবে আমিও বহু সভায় বক্তব্য পেশ করেছি। বহু লোকের কাজ চলে যায়। অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যায়।
আরও অনেক পরে সারদা ইত্যাদি গড়ে উঠবে। ২০০০ এর পর। গ্রামে বা ছোট শহর বাজারে ব্যাঙ্ক না থাকা, থাকলেও অ্যাকাউন্ট খোলা একটা বিরাট সমস্যা ছিল। তারচেয়েও বড় কথা, এই সঞ্চয় সংস্থার এজেন্টরা বাড়ি বাড়ি এসে টাকা নিয়ে যেত। দিয়েও যেত প্রথম দিকে। ঋণ পাওয়া যেত সহজে। এর সঙ্গে ছিল চড়া সুদের প্রলোভন। আজও ব্যাঙ্কগুলো দৈনিক ১০/২০/৩০ টাকা করে সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমার ব্যবস্থা করতে পারল না। মানুষকে যেতে হচ্ছে। মানুষের কাছে ব্যাঙ্ক পৌঁছে যাচ্ছে না। ইদানীং অবশ্য কিছু কিছু এলাকায় এজেন্ট নিয়োগ হয়েছে। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা যায়। আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে। তবে দৈনিক ১০/২০/৩০ টাকা জমার ব্যবস্থা হয়নি। হয়নি বলেই আবার কোনও চিট ফান্ড গড়ে উঠবে। উঠবেই।
ওভারল্যান্ড কলকাতার বড় দৈনিকগুলোকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল।
তিনভাবে।
এক, লরি করে কাগজ পৌঁছে এজেন্ট মারফত সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বাড়িতে কাগজ।
দুই, গ্রাম বাংলার খবর দুটো পাতা জুড়ে।
তিন, ছেলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পাতা। বিশেষ করে ইংরেজি ও অঙ্ক। গ্রাম বাংলায় অঙ্ক ও ইংরেজির ভালো টিউটর পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। আমার অভিজ্ঞতা আগে লিখেছি, একটা অঙ্ক বা ইংরেজি আটকালে তিন থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে ছুটতে হতো। অপেক্ষা করতে হতো। ওভারল্যান্ড এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করে দিল। ফলে গ্রামে কাগজ বিক্রি বেড়ে গেল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বিনা বেতনে প্রথমে মাধ্যমিক পরে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করায় ছাত্রছাত্রী বাড়ে। ১৯৮০ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৈনিক পাঁউরুটি দেওয়া শুরু হয়। গরম পাঁউরুটির একটা আলাদা আবেদন আছে। যদিও দু একজন সরবরাহকারী পচা পাঁউরুটি দিয়েছে । ঝামেলাও হয়েছে।
এর পাশাপাশি তপশিলি ছাত্র ছাত্রীরা বছরে ২৪০ টাকা করে পেতে থাকে। এছাড়াও কিছু মেয়ে স্কুল গেলে সাদা জামা ও সবুজ স্কার্ট পায়। মনে রাখবেন, লাল নয়, সবুজ। তখন পোশাকের রঙ দিয়ে রাজনৈতিক মতামত বিচাররীতি অনুপ্রবেশ করেনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।
টকটকে লাল ব্লাউজ সিপিএম কংগ্রেস সব বাড়িতেই চলতো্। তবে লাল বা সবুজ শার্ট দেখিনি।
ওভারল্যান্ড পত্রিকার দেখাদেখি বড় পত্রিকা কেউ কেউ পড়ার পাতা চালু করে। জেলার খবর একটু হলেও বাড়ে।
ওই সময় আরেকটি সাপ্তাহিক খুব সাড়া ফেলে। পরিবর্তন।
পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক। কী মার মার কাট কাট উত্তেজনা। ক্রাইম রিপোর্টারদের খুব কদর ছিল। পিনাকী মজুমদার দারুণ সব খবর করতেন। পরে নয়ের দশকে পিনাকী মজুমদারের সঙ্গে আজকাল দৈনিকে কাজ করেছি।
আর মনে আছে, দুই ক্রীড়া সাংবাদিকের নাম। রূপক সাহা ও নির্মলকুমার সাহা। ক্রীড়া আনন্দে রূপক সাহা ও নির্মলদার প্রতিবেদন পড়ে খুব কাঁদতাম। নির্মলদার সঙ্গে আজকাল কাগজে কাজ করার সময় সেকথা বলেছি। নির্মলদা খুব চুপচাপ মানুষ ছিলেন। রূপক সাহা পরে আনন্দবাজার গিয়ে খুব বিখ্যাত হন।
রূপক সাহা ও নির্মলদা অভাবী ক্রীড়াবিদদের কথা লিখতেন। তাঁদের কাছে যাতে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা পৌঁছায় তার চেষ্টা করতেন। তখন ক্রীড়া আনন্দ ও খেলার আসর এই দুটো পত্রিকাই ছিল জনপ্রিয়। পরে আজকাল এসে দৈনিক পত্রিকায় খেলার খবরের গুরুত্ব খুব বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে ক্রিকেটের খবর। দেবাশিস দত্ত খুব পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। দেবাশিস দত্তের লেখা আর সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ছবির যুগলবন্দি খুব জনপ্রিয়।
আজকাল পত্রিকার আরও তিনজনের লেখা খুব পড়তাম আশির দশকে। হামদি বে, জিষ্ণু উপাধ্যায় এবং উর্দু দুনিয়ার খবর দেওয়া বাহারউদ্দিন।
জিষ্ণু উপাধ্যায় ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। প্রাথমিকে ইংরেজি বিরোধী আন্দোলন, পরমাণু বোমা বিরোধী আন্দোলন, কার্গিল যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে ১৯৯৮ থেকে ভাষা ও চেতনা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন ডাক্তার বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। জিষ্ণু উপাধ্যায়ের এটাই ছিল আসল নাম।
কফি হাউসে চমৎকার আড্ডা দিতেন। বাহারউদ্দিনের সঙ্গে আজকাল পত্রিকায় পরে কাজ করেছি। নয়ের দশকের শুরুতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভায় খুব জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন বাহারদা।
দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সুদর্শন (পদবী মনে পড়ছে না) আলোকচিত্রী হিসেবে খুব বিখ্যাত হয়ে যান। ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় গ্যাস লিক করে শত শত মানুষের মৃত্যু ও চির অসুস্থ হওয়ার ঘটনার ছবি তুলে। রাজ্যের বহু জায়গায় এই আলোকচিত্রের প্রদর্শন হয়। আমিও দৈনিক বসুমতী দপ্তর থেকে নিয়ে যাই বর্ধমান শহরে প্রদর্শন করার জন্য।
এই ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় দুর্ঘটনার ঘটনায় রাজীব গান্ধীর খুব নিন্দা হয়। সংস্থার অন্যতম কর্তাকে নিরাপদে গোপনে ভারত ছাড়তে দেওয়ায়।
দৈনিক বসুমতী পত্রিকা পরে বামফ্রন্টের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তুলে দেন। ১৯৮৯-এ এই পত্রিকা এক টাকায় পাওয়া যেত। বহু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার রাখতে পারতেন। প্রশান্ত সরকারের সম্পাদনায় পত্রিকাটি একটি অনন্য স্থান অধিকার করেছিল। এই পত্রিকা তুলে দেওয়া চরম হঠকারিতা। সরকারের কাজ নাকি পত্রিকা প্রকাশ নয়! এই ছিল বক্তব্য। কোন যুক্তিতে তিনি রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক সংগঠন লোকরঞ্জন তুলে দিয়েছিলেন জানা নেই। এটাও তাঁর কিছু অবিমৃষ্যকারী কাজের একটি। ময়মনসিংহ গীতিকাকে জনপ্রিয় করেন সাধারণ মানুষের মাঝে লোকরঞ্জন শাখা। তাঁদের মহুয়া ও মলুয়া পালা আজও চোখে লেগে আছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো। শুধু মাত্র খাওয়া খরচ দিলেই তাঁরা অনুষ্ঠান করে আসতেন। বাংলায় লোকসংস্কৃতি প্রসারে লোকরঞ্জন শাখার ভূমিকা অপরিসীম। আরেকজন মানুষ, সুধী প্রধান, লোকসংস্কৃতি প্রসারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বহু লোকসংস্কৃতি গবেষণক গ্রাম বাংলায় বিকশিত হন তাঁর প্রভাবে।
আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব হতো সরকারের অর্থে। দেখার মতো আয়োজন। জেলা ও মহকুমা শহরে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলচ্চিত্র উৎসব হতো। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হতো। সেগুলো বন্ধ করে কী লাভ হয়েছে কে জানে!
পরে কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসব হল, নাট্যমেলা হলো। সব কলকাতাকেন্দ্রিক।
জেলা মহকুমা ব্রাত্য।
জেলাতেও লোকসংস্কৃতি উৎসবের চেয়ে অন্য ধরনের পাঁচ মেশালি মেলার আয়োজন হতে লাগল। বইমেলাও হল একাধিক। কিন্তু খেটেখাওয়া মানুষের অংশগ্রহণ খুবই কম তাতে।
(ক্রমশঃ)
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।কথা - ১ | কথা - ২ | কথা - ৩ | কথা - ৪ | কথা - ৫ | কথা - ৬ | কথা - ৭ | কথা ৮ | কথা - ৯ | কথা - ১০ | কথা - ১১ | কথা - ১২ | কথা - ১৩ | কথা - ১৪ | কথা - ১৫ | কথা - ১৬ | কথা - ১৭ | কথা - ১৮ | কথা - ১৯ | কথা - ২০ | কথা - ২১ | কথা - ২২ | কথা - ২৩ | কথা - ২৪ | কথা - ২৫ | কথা - ২৬ | কথা - ২৭ | কথা - ২৮ | কথা - ২৯ | কথা - ৩০ | কথা - ৩১ | কথা - ৩২ | কথা - ৩৩ | কথা - ৩৪ | কথা - ৩৫ | কথা - ৩৬ | কথা - ৩৭ | কথা - ৩৮ | কথা ৩৯ | কথা ৪০ | কথা ৪১ | কথা ৪২ | কথা ৪৩ | কথা ৪৪ | কথা ৪৫ | কথা ৪৬ | কথা ৪৭ | কথা ৪৮ | কথা ৪৯ | কথা ৫০ | কথা ৫১ | কথা ৫২ | কথা ৫৩ | কথা ৫৪ | কথা ৫৫ | কথা ৫৬ | কথা ৫৭ | কথা ৫৮ | কথা ৫৯ | কথা ৬০ | কথা ৬১ | কথা ৬২ | কথা ৬৩ | কথা ৬৪ | কথা ৬৫ | কথা ৬৬ | কথা ৬৭ | কথা ৬৮ | কথা ৬৯ | কথা ৭০ | কথা ৭১ | কথা ৭২ | কথা ৭৩ | কথা ৭৪ | কথা ৭৫ | কথা ৭৬, ৭৭, ৭৮ | কথা ৭৯ | কথা ৮০ | কথা ৮১ - আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনপ্রথম রেখা - albert banerjeeআরও পড়ুনঅনন্ত জীবন - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনসেই দিন সেই মন - রঞ্জন রায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 তৌহিদ হোসেন | 42.108.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৪:৫৪733815
তৌহিদ হোসেন | 42.108.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৪:৫৪733815- মনে পড়ল ওভারল্যাণ্ড। সত্যিই, গ্রাম এখনও ব্রাত্য। গ্রামের সংস্কৃতিই উঠে যাচ্ছে। স্যার❤
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)
(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)
(লিখছেন... b, lcm, Bratin Das)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... গুগুস, aranya, রঞ্জন)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।















