- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে - পাঠ প্রতিক্রিয়া
হীরেন সিংহরায়
পড়াবই | প্রথম পাঠ | ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ৮৭৩ বার পঠিত 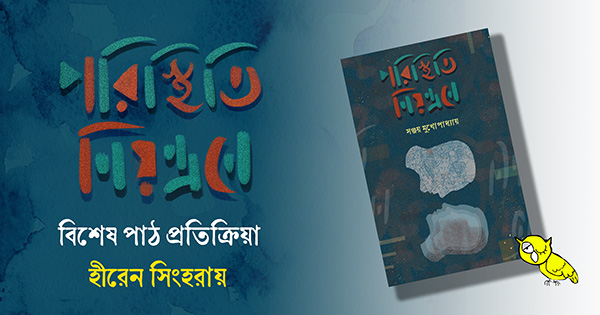
ছবি: রমিত
সাড়ে চার দশক আগে দেশ ছেড়েছি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সিনেমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মায়ের মৃত্যুর পর তিরিশ বছর একটিও বাংলা শব্দ লিখিনি। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।
প্রতিদিনের পথের ধূলায় বিবর্ণ কাজের দিন ফুরোলে সময় পেয়েছি; ফিরে দেখার দিন। যা হারিয়েছি তাকে ফেরানো যায় না, কিন্তু ধরা ছোঁয়া কি যায়?
ইউটিউব নামক অষ্টম আশ্চর্যের আবিষ্কারের ফলে দূর দেশ থেকেও সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি, শুনেছি, পড়েছি তাঁর লেখা।
সারের ছোট গ্রামের নিরালায় বসে তাঁর কল্যাণে জেনেছি অনেক কিছু। কোনোদিন ভাবিনি তাঁর পাশে বসার সুযোগ হতে পারে। শ্রীমান রমিত যখন আমাকে তার নবতম উপহার 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে' বইটি আমার হাতে দিয়ে বলল, "অন্য কেউ পড়ার আগে আপনার এই সুযোগ, বইটির মোড়ক উন্মোচন করবেন আপনি, সঙ্গে দু-চার কথা!"
তাহলে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল—সঞ্জয়ের বই এবং তাঁর পাশে বসার সুযোগ! জানি, ঋদ্ধিযুক্ত মানুষ প্রশংসার প্রস্তাবনা শুনতে পছন্দ করেন না। তাঁর সদ্গুণের বিষয়ে তিনি সম্যক অবহিত আছেন। তিনি জানেন তিনি কোন আকাশে বিরাজমান। তাই মার্ক অ্যান্টনির কথা ধার করে বলতে চাই, আই কাম টু টেল হোয়াট সঞ্জয় মিনস টু মি, নট টু প্রেজ হিম।
বইটির নাম 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে'।
আখ্যানের ঘুরপথ থেকে পাণ্ডুলিপি বনাম আইটেম সং-এর মধ্যে সংবদ্ধ আছে ৩৬টি রচনা। আমার কাছে এই প্রবন্ধ সংকলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার সংক্ষিপ্ততা।
সম্ভবত মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, "আমার চিঠির দৈর্ঘ্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। হাতে সময় বেশি থাকলে ছোট করে লিখতাম।"
সঞ্জয় অনেক সময় নিয়ে একেকটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন, কোনটি হয়তো দেড় হাজার শব্দ অতিক্রম করেনি।
আমি কী খুঁজে পেলাম?
তাঁর প্রখর মেধা, অসামান্য ভাষা শৈলী, সহজ হওয়ার কঠিন ক্ষমতা দিয়ে তিনি আমাকে আচ্ছন্ন করেননি, তিনি আমাকে সচেতন করেছেন।
কেন এই সচেতনতা আমার কাছে মূল্যবান?
দীর্ঘ জীবনে অনেক দেশ-মহাদেশ, দীনদুনিয়া দেখেছি, কিন্তু আজ, আশির কাছাকাছি এসে বুঝেছি ছুঁয়ে গেছি অনেক কিছুই, ঠিকমতো করে দেখিনি। আমার নিত্যদিনের সব ভাবনার সঙ্গী ছোট মেয়েকে বলি, "এখান দিয়ে গেছি কতবার, এটা তো লক্ষ্য করিনি!" সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "তখন তুমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলে। কাম্পালা থেকে পাওয়ার প্রজেক্ট দেখতে গেছ, পথে নীল নদীর সোর্স দেখোনি।"
কন্যা নিজেও জানে, এটা নিছক সান্ত্বনা।
এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক উত্থান-পতন দেখলাম। জুন ১৯৮৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৯০—এই ন'টি মাসের ভেতরে পৃথিবীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দেয় তিনটি ঘটনা। এখন নিজেকেই প্রশ্ন করি, বৃহস্পতিবার ৯ই নভেম্বর আমি কী করছিলাম? বিবিসির লেট নাইট খবরে জানা গেছে বার্লিন ওয়াল উন্মুক্ত। তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে যুবকটি যখন একটি গোলাপ ফুল এগিয়ে দিয়েছে ট্যাঙ্ক চালকের হাতে, সেটা কি ফিল্মের স্ক্রিপ্ট ছিল? আমি কী ভাবছিলাম তখন?
উর্দুতে বলে, 'হাম সব কুছ শিখি চিনি জানি ইস দুনিয়া কে পাঠশালায়।' তা যদি হয়, তাহলে আমার মতো মানুষের আকাট অজ্ঞানতার ব্যাখ্যা কী?
'কুছ লোগ জো আঁখে বন্দ করকে ভি চলতে হ্যাঁয়।'
দেখার জন্য চোখ লাগে অথবা কারো চোখ ধার করতে হয়। ইহুদি পিতা পুত্রকে বলেন, "বৎস, লেখাপড়া জানাটা খুব জরুরি। হয় নিজে শেখো নয় এমন কাউকে কাজে রাখো যে লেখাপড়াটা করেছে।"
সঞ্জয়ের কাছে চোখ ধার করতে হয়।
তাঁর দেখার চোখ বিধিদত্ত। সে কেবল অর্জুনের পাখির চোখ দেখা নয়। একটা বিশাল পটচিত্রের মধ্যে প্রত্যেককে চিনে নেওয়ার চোখ।
এই সোমবার আমার অনুজপ্রতিম সতীর্থ ঋত্বিক মিত্রের পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো ব্রিস্টলের আর্ট মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামে ঢুকতেই দেখলাম প্রকাণ্ড হলের ওপরে টাঙানো আছে 'দোজ ম্যাগনিফিসেন্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিনস'-এর সাত নম্বর প্লেনটির রেপ্লিকা, চালকসহ। কারো কারো মনে থাকতে পারে, ১৯৬৫ সালের এই ছবিটি—লন্ডন থেকে প্যারিস উড়ে যাওয়ার জন্য চোদ্দটি প্রাচীন কালের (১৯১০) এক কম্পিটিশন। প্লেনটি দেখতেই মনে পড়ল আরেক কথা। সত্যজিৎ রায় এক রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ভিড়ের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ অত্যন্ত শক্ত কাজ। ভিড়ের কোনো মুখ থাকে না। যারা সেই কর্মটি সুসম্পন্ন করেন, তাঁদের সাধুবাদ দিয়ে 'দোজ ম্যাগনিফিসেন্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিনস' ছবিটির বিশেষ উল্লেখ করেন।
সেই সমস্যা কি শুধু চলচ্চিত্রে?
রেমব্রান্টের রাতের পাহারা (নাইট ওয়াচ) ছবিতে অজস্র মুখ—কিন্তু সেখানে প্রতিটি মুখকে রেমব্রান্ট দিয়েছেন স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি।
এইটাই সঞ্জয়ের অসাধারণ গুণ—তিনি একটা ছবির অজস্র এক্সট্রার ভিড়ে, লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনের মাঝে, তিন ভলিউমের কেতাবে হাজার চরিত্রের পদধ্বনির মধ্যে প্রতিটি মুখ স্পষ্ট দেখেন, দেখান।
ছবি তো আমরা সকলেই দেখি। ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময়ে সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার চাঁদা দেওয়া সদস্য ছিলাম। অ্যাকাডেমির দোতলায় বসে 'ব্যাটলশিপ পোতেমকিন', 'মিরাকল ইন মিলান', 'সাইলেন্স' দেখার পরে দু'নম্বর চৌরঙ্গীতে ক্লাবের অফিসে চায়ের সঙ্গে কত আলোচনা হতো। এক বিজ্ঞ জন বলেছিলেন, "কিছুই বোঝোনি। জানো আন্তোনিওনির ছবি বুঝতে গেলে ব্যাকগ্রাউন্ড, ফোরগ্রাউন্ড, মিউজিক, ডায়ালগ—এই চারটে জিনিসকে বুঝতে হবে।"
সঞ্জয় বলেন না, "ফেলিনি দেখেছেন, কী বুঝেছেন?"
তিনি বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখে বলেন, "দেখলেন, নীতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিকের ক্যামেরা পাহাড়-বন ছেড়ে কেমন যেন উঠে গেল আকাশ পানে?"
প্রকৃতি নীতার সঙ্গে সহমরণে গেল।
এই লাইনটি পড়েছি হয়তো 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখার চার দশক বাদে, কিন্তু এটি আমৃত্যু আমার সঙ্গে থাকবে।
ঋত্বিক সম্বন্ধে শেষ কথা সঞ্জয় বলেছেন:
"সময়ের নৈকট্য তাঁকে বোঝার অন্তরায়।"
আবার তপন সিংহ সময়ের নিকটে গেলেন না। বললেন, "এ গল্প হলেও সত্যি।"
'নির্জন সৈকত'-এর শেষ দৃশ্যে সাগরবেলা ধুয়ে দেওয়া ঢেউ তপন সিংহর নির্মলতার প্রতীক।
দেবেশ রায়ের পাশের বাড়িতে কিছুদিন থেকেছি জলপাইগুড়িতে, সাক্ষাতে কথা হয়নি। তাঁর লেখা পড়ার আগেই তিস্তার পারে ঘোরাঘুরি করেছি, কিছুই দেখিনি, পুরনো বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলেছি।
সঞ্জয় দেবেশ রায়কে চেনালেন— "ইনি ইতিহাস থেকে ব্যক্তিকে তুলে এনে আবার ইতিহাসের মধ্যেই নিয়ে যেতে চেয়েছেন।" দেবেশ রায়কে পড়ার চোখ তিনি খুলে দিয়েছেন।
'দুর্গেশনন্দিনী'-র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নিশ্চয় সমরেশ বসু 'বিবর' লেখেননি। 'সূর্যমুখীর বিহনে প্রাসাদের বিবরণ' রাজকুলবধূর অন্তর্ধানে যেন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ, কিন্তু 'বাসনার এমন দগ্ধাবশেষ বিবর এ কোথাও নেই'। সেটি ঘটনা, আমাদের কৈশোরকালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 'বিবর'। সন্তোষ ঘোষ (এককালের আনন্দবাজার সম্পাদক) বলেছিলেন, "চিৎ হয়ে এ বই পড়া যায় না।"
আহা, আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম!
সঞ্জয় লক্ষ্য করেন, পদ্মা নদী নিয়ে মানিক ততটা চিন্তিত নন যতটা মানব চরিত্র নিয়ে। আর অন্য বিশাল নদীর পটভূমিতে লেখা 'গঙ্গা'-য় যতটা ঘটনার কুচকাওয়াজ, সত্যের বিস্তার ততটা নয়।
গত শতকের দ্বিতীয় অর্ধে আমরা তেমনই পেয়েছি শংকর, তেমনই অবধূত, তেমনই যাযাবর। সঞ্জয় আক্ষেপ করেছেন, মতি নন্দীর তারক চ্যাটার্জির গলিতে নায়ক রোজ আসতে পারেন না, কমল কুমার মজুমদার রোজ শ্মশান আলো করে বসতে পারেন না। আজকের টেলি সিরিয়ালের গতিক দেখে সঞ্জয় বলেছেন: "অন্ধকারকে আজ অন্ধকার বলে চিনিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।"
হলিউড-টেলিউডের আস্বাদে আনন্দিত আমেরিকান কিশোরকে বাবা নিয়ে এসেছেন ইউরোপে। রোমান আর্চ, গ্রিক কলাম দেখানো শেষে বাবা তাকে নিয়ে গেছেন ডেনমার্কের ক্রোনবর্গ (হ্যামলেটের এলসিনোর) ক্যাসেলের মুক্তাঙ্গনে হ্যামলেট দেখাতে। নাটক দেখে ছেলেটি বলে, "আই ডোন্ট নো হু রোট ইট বাট বয় ইট ওয়াজ ফুল অফ প্রোভার্বস।"
"অন্ধকারকে আজ অন্ধকার বলে চিনিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।"
তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মাত্রায় তিনি ভারতীয় ফিল্মের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন, সেটি আমার মতন পল্লবগ্রাহী মানুষের কাছে একটি স্বর্ণখনি!
আমি নিজে ট্রিভিয়া সংকলন ও যেখানে সেখানে সেগুলি বিলিয়ে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করে থাকি, শ্রোতার মুখ দেখি না, আমি বলেই খালাস। সঞ্জয়ের ট্রিভিয়া অন্য মাত্রার।
সাদা-কালো সিনেমায় অজয় কর শাড়ির লাল পাড়টুকু প্রদীপের শিখায় পুড়িয়ে তার ছাপ দিয়ে বানালেন সিঁদুরের টিপ। সেটি কেবল একটি কালো বিন্দু নয়। এটি তথ্য, কিন্তু ট্রিভিয়া নয়, কেননা সঞ্জয় দ্রুত যোগ করেন, "মাধবী অলৌকিক শ্রদ্ধায় বলেছেন, সেই পরিচালকেরা কোথায় গেলেন?"
সঞ্জয় মনে করিয়ে দেন, 'পথের পাঁচালী' এবং 'শাপমোচন' একই বছরের ছবি, সমান সমাদৃত। 'কালেক্টিভ অ্যাপ্রিসিয়েশন' বলে কোনো কথা নেই।
প্রথমবার রোমে গিয়ে ফোয়ারা দেখেছি। এখন ফন্তানা দেই ত্রেভিতে সিলভিয়াকে নেমে যেতে দেখি। গত বছর মিলান ক্যাথেড্রালের সামনে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম কতজন একটা ঝাঁটায় বসে উড়ে যাচ্ছেন। 'আমারকর্ড'-এর রিমিনিতে কোনো টানা গল্প নেই—কেননা তিত্তি নামক বালকটির জীবনে সেই বছরে এলোমেলো যা সব ঘটে তাই তো গল্প।
চিড়িয়াখানায় বাঘের নদী ও বনানী শাসনের অধিকার থাকে না।
এই প্রবন্ধমালায় সঞ্জয় আমাকে ভাবিয়েছেন, সচেতন করেছেন।
আমার গুরু, আমার মৌলা, মরহুম সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের নির্লজ্জ অনুকরণ করেই এ যাবৎ দু'লাইন লেখার বাহবা কুড়োনোর অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আজও তাঁর কথা ধার করে বলি—"সঞ্জয়, আপনার হিরের ম্যাকবুক হোক।"
পুনশ্চ: রমিতের প্রচ্ছদটি অসাধারণ
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
প্রকাশক - গুরুচণ্ডা৯
প্রচ্ছদ - রমিত চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ২০২৫
( ৯ই আগস্ট ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাভবনে পঠিত )
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
Ranjan Roy | ১৪ আগস্ট ২০২৫ ০১:১০733302
- "সঞ্জয় লক্ষ্য করেন, পদ্মা নদী নিয়ে মানিক ততটা চিন্তিত নন যতটা মানব চরিত্র নিয়ে। আর অন্য বিশাল নদীর পটভূমিতে লেখা 'গঙ্গা'-য় যতটা ঘটনার কুচকাওয়াজ, সত্যের বিস্তার ততটা নয়"।---একশ ভাগ সত্যি।পদ্মা নদীর মাঝির গল্প অন্য যে কোন নদী নিয়ে হতে পারত, শুধু সে গল্পে ময়নাদ্বীপ হতে পারত না।তবে গঙ্গার মালোদের জীবন আর তিতাসের মালোপাড়ায় যোজন তফাত।আবার গঙ্গার ব্যাপারে সঞ্জয় যেন একটু বেশিই নির্মম।হীরেনদার প্রিয় ইকনমিক্সের শব্দাবলী ধার করে বলিঃপদ্মানদীতে মাইক্রো অ্যানালিসিস।গঙ্গায় লেখকের ইতিহাসবোধ, এবং ভাঙনের চাপা আওয়াজ মিলে এক ম্যাক্রো পটচিত্র।আর একটা মাইক্রোচিত্র কাহিনীর শেষে।নায়কের মন পেতে ব্যর্থ সহনায়িকা মেয়েটি (নাম ভুলে গেছি) মেলার মধ্যে ইচ্ছে করে আকণ্ঠ মদ গিলে এর ওর তার গায়ে ঢলে পড়তে লাগল।এই ছবির কল্পনায় বুকে রক্তক্ষরণ হয়।তবু বলব কোলকাতায় ফিরে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহটি বগলদাবা করতেই হবে।
-
দ | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২১:৪২733347
- হীরেনদা সত্যিই দুহাতে লেখেন, যেমন ইমানুল বললেন। কি তাড়াতাড়ি লিখে ফেলেছেন! ভাল লাগল।
-
রমিত চট্টোপাধ্যায় | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২১:৪৫733350
- পাঠ-প্রতিক্রিয়াটা খুবই ভালো লাগল। এত ব্যাস্ততার মধ্যে থেকেও লেখার প্রতি এমন ডেডিকেটেড মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আপনার ম্যাকবুকটাও স্বর্ণখচিত।
 kk | 2607:fb91:17ad:4ed7:c97a:9a72:5bcc:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২২:২৫733353
kk | 2607:fb91:17ad:4ed7:c97a:9a72:5bcc:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২২:২৫733353- ভালো লাগলো রিভিউটা খুবই।
আজকাল 'পাঠপ্রতিক্রিয়া' দেখলেই ভেতরে কেমন যেন "হাঁ হাঁ বেয়াই, সেটাকাটালেখাটা বাকি আছে বটে" ধরণের অপরাধবোধ হয়। কিন্তু ... দেখি... :-(
 ৡ | 103.27.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২৩:০৬733355
ৡ | 103.27.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২৫ ২৩:০৬733355- সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখি নিয়ে একটা টই ছিল। রমিত বা অন্য কেউ যিনি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে ওঁর এখন অবধি প্রকাশিত বইয়ের তালিকাটা প্রকাশকের নাম সহ কমপ্লিট করে দেবেন ওখানে ? সম্ভব হলে বইগুলোর সূচিপত্র আর প্রচ্ছদ সহ। সে ছবি সঞ্জয়বাবুর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয় ছাত্র ছাত্রী বা সরাসরি ওঁর ফোনে তোলা ছবির মাধ্যমে।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












