- বুলবুলভাজা আলোচনা অর্থনীতি

-
উদ্ভাবন, ধ্বংসাত্মক সৃজন এবং উন্নয়নঃ অর্থনীতির নোবেল ২০২৫
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়
আলোচনা | অর্থনীতি | ১৮ নভেম্বর ২০২৫ | ৫৪৩ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 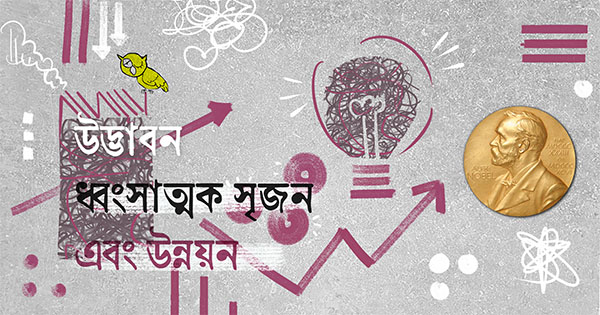
অলংকরণ: রমিত
উন্নয়নের মূল প্রশ্ন
উন্নয়ন অর্থনীতির মূল প্রশ্নটিকে একটু সরলীকৃত ভাবে উপস্থাপন করলে তা দাঁড়ায় অনেকটা এরকম – কেন কেউ গরিব থেকে যায় আর কেউ বড়লোক হয়। এখানে বলে রাখা ভালো গরিব-বড়লোক আমরা হিসেব করি আয় দিয়ে। কিন্তু আয় বেশি হলেই যে কারো পুষ্টি, শিক্ষা বা অন্য উন্নয়নের সূচক ভালো হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই নিয়েও অনেক গবেষণা আছে। তা সত্ত্বেও আয়ের সঙ্গে যে অন্য উন্নয়ন সূচক সমানুপাতিক তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তাই আয় বাড়ানোর তত্ত্ব অনুসন্ধান উন্নয়ন অর্থনীতির কেন্দ্রে থাকা একটি গবেষণা প্রকল্প।
গরিব কেন গরিব থাকে, উন্নয়ন অর্থনীতি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে দুভাবে – ব্যক্তি (মাইক্রো) এবং সমষ্টির (ম্যাক্রো) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একটু সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও বলি, মাইক্রো দৃষ্টিকোণ দেখার চেষ্টা করে গরিব মানুষ কেন বড়লোক হতে পারে না, অন্যদিকে ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণ দেখতে চায় একটি দরিদ্র দেশ কেন বড়লোক হতে পারে না। এই দুটি দৃষ্টিকোণ যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি ধারণা তা নয়, কারণ একটি দেশের নাগরিকদের বড়লোক করতে পারলে সেই দেশটিও তো বড়লোক দেশ বলেই গণ্য হবে। বিশ্লেষণের প্রকরণের দিক থেকেও ম্যাক্রো-মাইক্রো খুব আলাদা কিছু না। ম্যাক্রো-অর্থনীতি বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা আসলে মাইক্রো ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মূল যেখানে পার্থক্য সেটা হল দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। মাইক্রো দৃষ্টিকোণ যেখানে বোঝার চেষ্টা করে গরিব মানুষ কেন ঋণ নিয়ে, বিনিয়োগ করে বড়লোক হতে পারে না, ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণ সেখানে দেখে কী ধরণের নীতি একটা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বাড়াতে পারে। এবারে, অর্থাৎ ২০২৫ এ যাঁরা নোবেল পেলেন (অ্যাঘিয়ন, হাউইট এবং মোকির), তাঁরা উন্নয়নের ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্যাটা দেখেছেন এবং দুধরণের প্রকরণের মাধ্যমে সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করেছেন।
উদ্ভাবন, ধ্বংসাত্মক সৃজন এবং উন্নয়ন
ধ্বংসাত্মক সৃজন (Creative Destruction) শব্দবন্ধটি এসেছে জোসেফ শুম্পিটারের (১৮৮৩-১৯৫০) লেখা থেকে। এই ধারণাটির মূল অর্থ হল, নতুন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, পুরোন প্রযুক্তিকে বাতিল করে দেয়। নতুন সৃজনের এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতাই কোন দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি। অ্যাঘিয়ন-হাউইট (এরপর থেকে আমরা যাঁদের আ-হা বলে অভিহিত করব) এই ধারণাটির একটি গাণিতিক রূপ দেন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে নতুন ভাবে বুঝতে সাহায্য করেন। লেখাটি আর এগোবার আগে গাণিতিক মডেলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। অর্থনীতির আধুনিক পাঠ গণিত নির্ভর অর্থাৎ, অর্থনীতির আধুনিক তত্ত্ব গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি অর্থনীতির এই গণিত নির্ভরতা দু’ধরণের ভুল মানসিকতার জন্ম দেয়। একদিকে কিছু লোক ভাবতে থাকেন অর্থনীতি মানেই গণিতের কারিকুরি এবং গাণিতিক মডেল লেখাই একজন অর্থনীতিবিদের আশু কর্তব্য। তা থেকে সমাজকে বোঝা গেল বা গেল না, তাতে কিছু যায় আসে না। এই ধরণের মতামতের প্রতিক্রিয়ায় অন্য যে মতামত উঠে আসে তা হল গাণিতিক মডেলের সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই দুটি মতই অতি-একপেশে মতামত যা অর্থনীতিতে গাণিতিক মডেলের গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম। অর্থনীতির তত্ত্ব একটি যুক্তিকাঠামো মেনে এগোয়। সেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করি কোন একটি প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে। আমরা যখন কোন বিষয় নিয়ে ভাষায় আলোচনা করি তার মধ্যে অনেক রকম বিষয় জড়িয়ে থাকে – আমরা সেইসব সূতোর জট ছাড়িয়ে কার্যকারণের পদ্ধতিটির মূলে পৌঁছতে পারি না। যদি পারতাম তাহলে সত্যি গাণিতিক মডেলের প্রয়োজন হত না। গাণিতিক মডেল আসলে এক ধরণের বৌদ্ধিক ব্যায়াম, যেখানে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে, প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারি। মডেল আমাদের সুশৃঙ্খল ভাবে ভাবনাকে চালিত করার একটি উপকরণ – তার কমও নয়, বেশিও নয়। এই বিষয় নিয়ে একটা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। আগ্রহী পাঠক ড্যানি রডরিকের ইকোনমিক রুলস পড়েও দেখতে পারেন। কিন্তু নোবেলের প্রসঙ্গে এই কথা বলার কারণ ইতি উতি কিছু মন্তব্য দেখলাম সমাজ মাধ্যমে যে যেহেতু ধ্বংসাত্মক সৃজনের মূল ধারণাটি শুম্পিটারের তাই আ-হা’র কাজ নোবেলের যোগ্য নয়। এই প্রেক্ষিতে আসলে আ-হা’র মডেলের মূল বক্তব্যটি বুঝে দেখা দরকার। এটাও বোঝা দরকার যে আধুনিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তত্ত্বের ইতিহাসে আ-হা’র তত্ত্ব অতিরিক্ত কী জানিয়েছে আমাদের।
আধুনিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তত্ত্বের সূত্রপাত রবার্ট সোলোর মডেলের মাধ্যমে। এই মডেলে সোলো দেখান কীভাবে পুঁজি বিনিয়োগ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটায় এবং কখন গিয়ে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি থেমে যায়। এই মডেল দেখায় শুধু পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এক সময়ে থেমে যাবে। এই থেমে যাওয়ার মূল কারণ পুঁজির ফেরত হা্রের (যা তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দিয়ে মাপা হয়) ক্রমহাসমানতা। তাহলে বৃদ্ধির ঘড়ি জারি রাখার উপায় খুঁজতে এর পরবর্তী প্রজন্মের বৃদ্ধি মডেলগুলির সূত্রপাত। সোলো মডেল থেকেই এই সূত্র পাওয়া গেছিল যে ক্রমাগত উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে বজায় রাখা যেতে পারে। কিন্তু উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার উপায় কী? গবেষক বললে সাধারণত আমাদের গ্যালিলিও, আইনস্টাইন বা জগদীশচন্দ্র বোসের কথা মনে হয়, যাঁদের জ্ঞানাণ্বেষণের মূল চালিকা শক্তিটি আবিষ্কারের আনন্দ, অর্থ নয়। কিন্তু প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অর্থই মূল চালিকা শক্তি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজে যাঁরা নিয়োজিত থাকেন, তাঁদের আবিষ্কারের মূল প্রণোদনাটি আসে অর্থ থেকে যা তাঁরা পেয়ে থাকেন আবিষ্কারটি পেটেন্ট করার মাধ্যমে। প্রশ্ন হল তাহলে উদ্ভাবনের চাকা সব দেশে গড়গড় করে চলে না কেন? এর একটা সহজ উত্তর হল, বিভিন্ন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবনের হার বিভিন্ন হয়। যেমন, কোথাও পেটেন্ট সংক্রান্ত নিয়ম যদি এমন হয় যে কোন উদ্ভাবনের নকল বের করা সহজ তাহলে আবিষ্কারকরা নতুন উদ্ভাবনের উৎসাহ হারাবেন। মোকির ঐতিহাসিক ভাবে এই প্রশ্নেরই অনুসন্ধান করেছেন -- উদ্ভাবনে কেন শেষ দুশো বছরে পশ্চিম ইউরোপ বাকিদের পেছনে ফেলে দিল – এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে আমরা এই প্রশ্নটির তাত্ত্বিক দিকটি দেখে নেব যা আ-হা’র গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।
আগেই বলেছি তত্ত্বের মূল কথা হল, উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াটির অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতিকে বোঝা। ধরে নিন, আমরা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে তুলনা করছি না। বরং একটি সমাজে উদ্ভাবনের পদ্ধতিকে বোঝার চেষ্টা করছি। সেই সমাজের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে যা উদ্ভাবককে পুরষ্কৃত করে তাকে পেটেন্ট দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু পেটেন্ট আসলে কী? পেটেন্ট হল কোন একটি দ্রব্য বিক্রির ওপর একচেটিয়া কারবারের অধিকার দেওয়া। যেমন ধরুন উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র মাইক্রোসফটের। কিন্তু একচেটিয়া অধিকারটি উদ্ভাবককে চিরকালীন মুনাফা দিতে পারে না। কারণ, কাল অন্য একজন নতুন এবং আরো ভালো কিছু আবিষ্কার করলে সবাই সেটিই ব্যবহার করবেন এবং তার ফলে পুরনো উদ্ভাবকের কাছে পুরোন দ্রব্য উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার থাকলেও তা থেকে আর মুনাফা আসবে না। এই প্রক্রিয়াই ধ্বংসাত্মক সৃজনের প্রক্রিয়া। যেমন ধরুন, এন্ড্রয়েড এবং স্মার্টফোন এসে উইন্ডোজের ব্যবহার অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে, টাচস্ক্রীন এসে ব্ল্যাকবেরিকে বাজার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কী কী ভাবে এই প্রক্রিয়া তরান্বিত হতে পারে, তার তত্ত্বই আ-হা’র কাজের মূল জায়গা। আমার আলোচ্য হল তাঁদের ১৯৯২ সালের গবেষণাপত্রটি (Aghion and Howitt, 1992)। এই মডেলে অর্থনীতিতে ভোগদ্রব্য (যেমন কম্পিউটার) উৎপাদিত হয় অন্তর্বর্তী দ্রব্যের সাহায্যে (যেমন, মাদারবোর্ড)। অন্তর্বর্তী দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানি কর্মী নিয়োগ করেন নতুন উদ্ভাবনের জন্য। উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সাফল্য অনিশ্চিত যা পয়শঁর প্রোবালিটি নিয়ম মেনে চলে। উদ্ভাবন কোম্পানিকে মুনাফা দেয় কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়। প্রথমতঃ অন্য কোন নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হলে, পুরোন দ্রব্যটি বাজার থেকে বিতাড়িত হয়।
দ্বিতীয়তঃ, অনেক কোম্পানি উদ্ভাবনের কাজে এলে গবেষণাকর্মীদের ধরে রাখতে গেলে বেশি মজুরি দিতে হয়। ফলে মুনাফা কমে যায়। এই মডেলের মূল টানাপোড়েনটি মজার। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবন দরকার। কিন্তু উদ্ভাবন যদি খুব দ্রুত হারে হয়, তাহলে উদ্ভাবনকারী কোম্পানি জানবে আজকের আবিষ্কার কালই বাতিল হয়ে যাবে। তাহলে সে আর উদ্ভাবনের পেছনে বিনিয়োগ করতে চাইবে না। দীর্ঘমেয়াদী ইকুইলিব্রিয়ামে এই টানাপোড়েন কী ভাবে কাটানো যায় এবং তখন বিনিয়োগের হার কী হয়, বৃদ্ধির হার কী হয় সেইসবই এই মডেলের আলোচ্য। (আমি বিষয়টা একটু সরল করে বললাম। বৃদ্ধি-তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা মার্জনা করবেন।) আ-হা’র গবেষণা ধ্বংসাত্মক সৃজন ধারণাটির একটি কাঠামো নির্মাণ করে যা এই বিষয়ে গবেষণাকে নতুন জন্ম দেয়। একটি পরিসংখ্যান দিলে ব্যাপারটি খানিকটা বোঝা যাবে। এই গবেষণাপত্রটি ১৭৩৮২ বার অন্য গবেষণায় উল্লিখিত বা সাইটেড হয়েছে! বিষয়টি আরো চমকপ্রদ কারণ অর্থনীতির যত গবেষণাপত্র লেখা হয় তার গড় (মিডিয়ান) সাইটেশন শূন্যের কাছাকাছি (Aigner et al., 2025)। যদি ১৯৯২-১৯৯৬ এর মধ্যে শীর্ষ স্থানাধিকারী ৫ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র ধরা হয় তাহলেও ২০ বছরের মিডিয়ান সাইটেশন ২১৭ (Anauati et al., 2019)। সুতরাং, যাঁরা “ধংসাত্মক সৃজন শুম্পিটারের ধারণা” বলে আ-হা’র অবদানকে নস্যাৎ করছেন তাঁদের আরেকটু ভেবেচিন্তে মন্তব্য করা উচিত। এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অংশে আসি অর্থাৎ জোয়েল মোকিরের অবদানে।
ইতিহাসের চোখে ধ্বংসাত্মক সৃজন এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন
মানব সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। কিন্তু সমসাময়িক সভ্যতা যে সব প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার সিংহভাগ এসেছে শেষ আড়াইশ বছরে, শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে। প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে পণ্য উৎপাদনের এক অভূতপূর্ব স্ফীতি যা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলার পাশাপাশি আমাদের জীবতকালকে বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণ এবং অসহনীয় চাপ তৈরি করছে পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর। কিন্তু সে অন্য আলোচনা। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে আছে দুটি প্রশ্নঃ কেন পশ্চিম ইউরোপেই (বা আরো ঠিক ভাবে বললে ইংল্যান্ডে) হল এই উদ্ভাবনের বিপ্লব? আর সেটা অষ্টাদশ শতকেই হল কেন? আগে বা পরে নয় কেন? জোয়েল মোকিরের দীর্ঘ গবেষণা এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের সাহায্য করে। মূল প্রশ্নের আসার আগে আরেকটি বিষয়কেও একটু ছুঁয়ে যাওয়া দরকার – সেটা হল প্রযুক্তির উন্নয়নের পরিমাণগত পরিমাপ। ব্যাপারটা সহজ নয়। যেমন ধরুন, কম্পিউটার। কুড়ি বছর আগে যে কম্পিউটার ছিল, তার তুলনায় বর্তমান কম্পিউটার নিঃসন্দেহে প্রযুক্তিগত ভাবে বেশি উন্নত। কিন্তু পরিমাণগত ভাবে এটা বোঝার উপায় কী? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটি অর্থনীতিতে লাখ লাখ জিনিস তৈরি হয়। একটি সার্বিক পরিমাপ পদ্ধতি না থাকলে আমরা কীভাবেই বা বুঝব যে দেশটি প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে আছে? অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত পরিমাপের একটি মাপ হল “সোলো রেসিডুয়াল (Solow Residual)”। খুব সহজভাবে বললে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যে অংশটি পূঁজি বা শ্রমের বৃদ্ধি দিয়ে মাপা যায় না সেই বাকি (অর্থাৎ, রেসিডুয়াল) বৃদ্ধি প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, সোলো রেসিডুয়ালকে প্রযুক্তির একটা গোদা মাপ হিসেবে ধরা হয়।
সমস্যা হল সোলো রেসিডুয়াল একটি ব্ল্যাক বক্স! এর ভেতরে প্রযুক্তি ছাড়াও প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি এরকম অনেক কিছু মিশে থাকতে পারে। তার থেকেও বড় কথা আধুনিক গবেষকরা শিল্পবিপ্লবের সময় উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে খুব বড় পরিবর্তন সেই সময় হয় নি, যা হয়েছে তা ধীরগতির (Crafts, 2021, 2004)। অথচ, আমরা গুণগত ভাবে বুঝি যে শিল্পবিপ্লবের সময় যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয়ান অর্থনীতি গেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসকেই পালটে দিয়েছে। মোকির তাঁর Lever of Riches (1990) বইতে প্রযুক্তিগত উন্নতির ধারণাকে সোলো রেসিডুয়ালের কালো বাক্স থেকে মুক্তি দিয়ে প্রযুক্তি পরিবর্তনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করে দেখালেন প্রযুক্তি বিপ্লবের মূল সুর সবসময় পরিমানগত পরিবর্তনের চোখে ধরা পড়ে না। এই আলোচনা করতে গিয়ে মোকির উদ্ভাবনকে দু’ভাবে ভাগ করলেন – ম্যাক্রো এবং মাইক্রো। ম্যাক্রো উদ্ভাবন হল বড় মাপের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন যা পুরোন প্যারাডাইমের অবসান ঘটিয়ে, নতুন প্যারাডাইমের জন্ম দেয়। কিন্তু অনেক সময় বড় মাপের পরিবর্তন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না যতক্ষন ছোট, ছোট কিছু পরিবর্তন বা মাইক্রো উদ্ভাবন তার চলার পথকে সুগম করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জেমস ওয়াটের সেপারেট কন্ডেন্সারের কথা যা স্টীম ইঞ্জিনকে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকর করে তোলে। মাইক্রো এবং ম্যাক্রো উদ্ভাবন পরপস্পরের পরিপূরক। মোকির বলেন শিল্পবিপ্লবের সময় এই দুধরণের উদ্ভাবনের এক আশ্চর্য সমণ্বয় দেখা যায় যা শিল্পবিপ্লবকে সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য করে তোলে।
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, অষ্টাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপেই কেন? তার আগেও ইউরোপে রোমান সভ্যতা ছিল, পৃথিবীতে ছিল চিন, ভারত, ইরাক, ইরান, মিশরের সভ্যতা। সেখানে নয় কেন? এই আলোচনা করতে গিয়ে মোকির তাঁর The Gifts of Athena (2002) বইতে জ্ঞানচর্চার দুটি বিভাজন করেন – প্রস্তাবমূলক জ্ঞান (Proposional Knowledge) এবং নির্দেশমূলক জ্ঞান (Prescriptive Knowledge)। এর মধ্যে প্রথমটি আমাদের চারপাশের ঘটে চলা ঘটনা কেন ঘটে তার অনুসন্ধান করে এবং দ্বিতীয়টি কীভাবে সেইসব ঘটনা ঘটে তা বোঝার চেষ্টা চালায়। প্রস্তাবমূলক জ্ঞান মূলত তত্ত্ব নির্ভর। অন্যদিকে নির্দেশমূলক জ্ঞান আসে হাতেকলমে কাজ করতে করতে যাকে আমরা ইংরিজিতে ট্রায়াল এবং এরর বলি তার মাধ্যমে। মোকির বললেন অন্য সব সভ্যতায় এই দুধরণের জ্ঞান চর্চাকারীদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব থেকেছে যে দূরত্ব আমরা এখনও দেখি পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার এবং হাতেকলমে কাজ করা মিস্ত্রীদের মধ্যে। মোকির দেখাচ্ছেন শিল্পবিপ্লবের ইউরোপে এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একধরণের আদানপ্রদানের পথ তৈরি হয় যেখানে ব্যবহারিক এবনফ তাত্ত্বিকরা একে অপরের থেকে শিখতে শুরু করেন। এই আদান প্রদানই, মোকিরের মতে শিল্পবিপ্লবকে এক অভাবনীয় সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।
কিন্তু কেন ইংল্যান্ড? মোকিরের মতে অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক এবং জ্ঞানের সংস্কৃতি এক ধরণের মুক্ত আদান প্রদানের পরিসর তৈরি করে যা এর আগে কখনো দেখা যায় নি। এর সঙ্গে ছাপাখানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের এক ধরণের নেটওয়ার্ক তৈরি হয় যা এই জ্ঞান সংস্কৃতির প্রসার এবং আদান-প্রদানের পথটি সুগম করে।
পুনশ্চঃ
লেখাটা শেষ করব জোয়েল মোকিরের সঙ্গে একটি একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে। মোকিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একবারই, ২০০৮ বা ২০০৯ সাল নাগাদ। নিউ হ্যাভেনে সেবার বসেছিল ইকোনমিক হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন। ওনার সঙ্গে আমার দেখা লিফটে। আমার সুপারভাইসরের পরিচয় পেয়ে উনি বললেন, “ইউ আর মাই একাডেমিক গ্র্যান্ডচাইল্ড”। তার কারণ আমার সুপারভাইসর মরিশিও ড্রেলিচম্যান, মোকিরের কাছে পিএইচডি করেছিল। অধিবেশনে আরও অনেক পিএইচডি ছাত্রের মত আমারও পোস্টার প্রেসেন্টেশন ছিল। মোকির দুটি সেশনের মাঝে ঘুরে ঘুরে পোস্টার দেখছিলেন। দেখতে দেখতে আমার পোস্টারের কাছে এলেন। এসে, দেখে খুশি হয়ে বললেন, “তুমি যেটা করেছো সেটা ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটা ধাঁধাঁ। খুব একটা কাজ নেই এটা নিয়ে। তুমি করেছো দেখে খুব ভাল লাগল।“ তারপর আমার পেপারটা ওনাকে পাঠাতে বললেন।
এইখানে বলে নিই আমি কী নিয়ে কাজটা করেছিলাম। তাহলে মোকির কেন বিষয়টি নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন বোঝা যাবে। ইংল্যান্ডে ১৫০০ থেকে ১৭০০ এর মধ্যে কোর্টে আনা মামলার এক অভূতপূর্ব উত্থান এবং তারপরে পতন হয়। অর্থাৎ, যদি সময়ের সঙ্গে মামলার সংখ্যা প্লট করা হয় তবে তা দেখতে লাগে উল্টানো U এর মত। এই প্যাটার্ণ যেমন লন্ডনের কেন্দ্রীয় কোর্ট কমন’স প্লী এবং কিংস বেঞ্চে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই এক্সেটার, কিংস লিনের মত শহরের বরো কোর্টেও দেখতে পাওয়া যায়। সব কোর্টেই মামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি এবং তারপর তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় কোর্টগুলিতে ইংল্যান্ডের পরিবার পিছু প্রায় দুই থেকে তিনটি মামলা জমা হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান থেকে ঘটনাটির অস্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন। আমার গবেষণায় আমি দেখিয়েছিলাম যে এই পর্যায়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ড অর্থনৈতিক বিবাদ মীমাংসার গোষ্ঠী ভিত্তিক, ইনফরমাল ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রে ভিত্তিক, ফর্মাল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। মামলার সংখ্যার এই বৃদ্ধি আসলে দুটি ইকুইলিব্রিয়ামের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।
অধিবেশন শেষ করে ফিরে আমি মোকিরকে আমার গবেষণাপত্রটি পাঠাই। এই পর্যন্ত গল্পটি স্বাভাবিক। মোকির ছাড়াও আরো দু-এক জনকে পাঠিয়েছিলাম যাঁরা আমার গবেষণার বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এটা একাডেমিক অধিবেশনে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তারপরে যেটা ঘটল সেটার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। অধিবেশনের দু-এক সপ্তাহ পরে জোয়েল মোকির আমাকে একটি দীর্ঘ ইমেইল করে আমার পেপারের ভাল এবং মন্দ দুদিক নিয়েই একটি অত্যন্ত গভীর মতামত লিখে পাঠান। এই ঘটনার পরে ১৬-১৭ বছর কেটে গেছে। মোকিরের সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয় নি। দেশে ফিরে এই ধরণের বিষয়ে কাজ চালানো কঠিন। আমিও অন্য ধরণের কাজ করতে শুরু করি। পেপারটি আমার থিসিসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও জার্নালে পাঠানো হয় নি আর। তবুও এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর একটা দাগ কেটে গেছিল।
আজ এই গল্পটি বলার কারণ জ্ঞানান্বেষণের প্রতি মোকিরের গভীরের ভালবাসা এবং ছাত্রদের প্রতি তাঁর গভীর যত্নের কথা সবাইকে জানানো। তখনও নোবেল না পেলেও, ২০০৮ এও কিন্তু মোকির অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক প্রতিষ্ঠান, আর আমি নেহাতই সামান্য একজন পিএইচডি ছাত্র যে নাকি অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করছে। তারপরেও তাঁর বহুমূল্য সময় ব্যয় করে মোকির ওই গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ ইমেইলটি করেন শুধুমাত্র একজন ছাত্রকে সাহায্যের অভিপ্রায়ে। এই লেখাটি লেখার আগে আমি সেই পুরোন ইমেইল খুঁজে বের করলাম একবার দেখার জন্য। মেলটি কপি পেস্ট করে ওয়ার্ড ফাইলে ফেলে দেখলাম তার দৈর্ঘ প্রায় চারপাতা! আমার মনে হয় জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা এই ধরণের ঔদার্যের জন্ম দিতে পারে এবং জ্ঞানচর্চায় প্রকৃত অর্থে নিয়োজিত একজন মানুষ নিজের লাভ ক্ষতির ক্ষুদ্র হিসেবের বাইরে গিয়ে জ্ঞানচর্চার বৃহত্তর আনন্দের পথে যেতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত ভাবনায়, মোকিরের নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তি, জ্ঞানচর্চার সেই বৃহত্তর আনন্দ সন্ধানের একটা উদযাপনও বটে।
পাঠসূত্র
Aghion, P., Howitt, P., 1992. A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica 60, 323–351. https://doi.org/10.2307/2951599
Aigner, E., Greenspon, J., Rodrik, D., 2025. Global Distribution of Authorship in Economics.
Anauati, M.V., Galiani, S., Gálvez, R.H., 2019. Differences in citation patterns across journal tiers: The case of economics.
Crafts, N., 2021. Understanding productivity growth in the industrial revolution. Econ. Hist. Rev. 74, 309–338. https://doi.org/10.1111/ehr.13051
Crafts, N., 2004. Productivity Growth in the Industrial Revolution: A New Growth Accounting Perspective. J. Econ. Hist. 64, 521–535. https://doi.org/10.1017/S0022050704002785
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 মতামত | 165.225.***.*** | ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ০২:৩৯735912
মতামত | 165.225.***.*** | ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ০২:৩৯735912- ধন্যবাদ, বিষয়টি বোঝাবার জন্যে।
-
Debanjan Banerjee | ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ১৮:২৯735938
- অনেক ধন্যবাদ জটিল একটা বিষয়কে বোঝাবার জন্যে l
-
Ranjan Roy | ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ২৩:১৯735949
- ভাল লাগল।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc, kk, দ)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












