- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-
ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিং -এর কর্ম ও জীবন
রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়
পড়াবই | প্রথম পাঠ | ২৭ জুলাই ২০২৫ | ৮৩৯ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন) 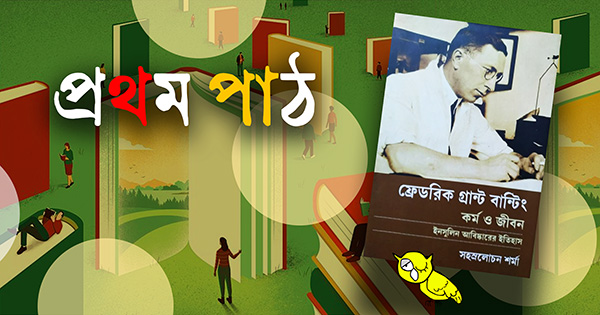
ছবি: রমিত
১৯২১ সালের জুলাই মাস। স্থানঃ টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি গবেষণাগার। সময়ঃ সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। একটি কুকুরের পাশে উদবিগ্ন মুখে বসে আছেন দুটি যুবক, ফ্রেডরিক বান্টিং আর চার্লস বেস্ট। তাঁদের বয়স যথাক্রমে তিরিশ বছর আর একুশ বছর। কয়েকদিন আগে তাঁরা একটি বিশেষ নির্যাস আবিস্কার করেছেন; কুকুরটিকে ইতিমধ্যে একবার সেই নির্যাসের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়ছে, নির্দিষ্ট সময় পরে তার রক্ত পরীক্ষা করে দ্বিতীয়বার ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে। তাই বার বার ঘড়ি দেখা।
এই নির্যাসটি হল ইনসুলিন। বিশ্বজোড়া ডায়াবেটিস রোগীদের প্রাণদায়ী ওষুধ। ইস্কুলের জীবনবিজ্ঞান ক্লাসে সবাই পড়েছি যে অগ্ন্যাশয়ের (প্যাংক্রিয়াস) আইলেট্স অফ ল্যাঙ্গারহান্স কোষস্তূপ থেকে নিঃসৃত এই হরমোন শর্করা বিপাকে সাহায্য করে। আসল কথাটা হল ইনসুলিন রক্তে উপস্থিত অতিরিক্ত শর্করাকে শোষণ করার জন্য যকৃৎকে (পাকস্থলীকে নয়) নির্দেশ দেয়। কোনোভাবে ইনসুলিনের অভাব ঘটলে যকৃত সেই নির্দেশ পায় না আর রক্তে শর্করার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলে যে রোগের নামই হল ডায়াবেটিস। তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন প্রয়োগ করে সেই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হয়। কিন্তু ইনসুলিন তো একটি জৈব পদার্থ, তাকে কি ভাবে পাওয়া যায় ? মানে, কিভাবে নিস্কাশন করা হয় ইনসুলিন ? জীবনবিজ্ঞানের বইতে পড়ার সময় এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসেনি। কিন্তু আসলে সে এক দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। সেই পদ্ধতি প্রথম সম্পন্ন করেছিলেন ওই দুই যুবক আর সেই নিষ্কাশিত যৌগের প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল ওই কুকুরের ওপরে; আংশিক সফল হয়েছিল সেই পরীক্ষা। তারপর কতরকম ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে বান্টিং-বেস্ট জুটি তাঁদের নিষ্কাশন পদ্ধতিকে উন্নত করে তুলেছিলেন, কিভাবেই বা সেই নির্যাসকে ডায়াবেটিসের ওষুধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন সে আর এক কাহিনী।
বিজ্ঞানের এক একটা আবিস্কারের পেছনে এই রকম কত কাহিনীই থাকে। শুধু আবিস্কারটুকুর কাহিনী তবু গবেষণাপত্র থেকে কিছুটা জানা যায়, বিজ্ঞানীরা নিজেরাও লেখেন অনেক জায়গায়। কিন্তু একটা আবিস্কারের ভাবনা থেকে শুরু করে তার আবিস্কার, পুরস্কার প্রাপ্তি, সংশ্লিষ্ট যাবতীয় টানাপড়েনের কথা জানতে পারা সহজ নয়। তার জন্য শুধু গবেষণাপত্র পড়লে হয় না, আরো অজস্র নথি পত্র থেকে তথ্য যোগাড় করার গুরুদায়িত্বও পালন করতে হয়।
সেই কাজই করেছেন সহস্রলোচন শর্মা, ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিং এর কর্ম ও জীবনের ওপর লেখা তাঁর বইতে। শ্রীশর্মার লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন বিজ্ঞানের জগতের ঘটনাবলী কি টনটানভাবে উপস্থাপনা করতে পারেন তিনি। কিন্তু ইনসুলিনের নিস্কাশনের পিছনে দৌড়ে বেড়ানো তো শুধুই বিজ্ঞানের জগতের বিষয় নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানীটির জীবনের আপাতঃ তুচ্ছ নানা ঘটনাও। সেই সব কিছুকে কালানুসারে গ্রন্থিত করে টানটান গল্পের মত করে পরিবেশন করা সহজ কাজ নয়। সেই কাজটিই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন শ্রীশর্মা এই বইয়ে। এককথায় বলতে গেলে ফ্রেডরিক বান্টিং-এর গোটা জীবন এবং ইনসুলিনের জন্য তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র ঘটনাবহুল অধ্যয়টুকু নিখুঁত ভাবে আঁকা হয়েছে এই বইয়ে। বিজ্ঞানী বান্টিং এর পাশপাশি মানুষ বান্টিং কেও লেখক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, এই যত্নের ছাপ বইয়ের সর্বত্র পাওয়া যায়। অর্থাৎ বান্টিং-এর জীবনপঞ্জিই লেখা হয়েছে যার কেন্দ্রে রয়েছে ইনসুলিন; ঘটনা বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে এই কেন্দ্রের কাছাকাছি কিন্তু তাকে পুনরাবৃত্তি মনে হয়নি কখনোই।
এই বই থেকে যে বান্টিং কে পাওয়া যায় তিনি তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এক তরুণ, একই সঙ্গে তীব্র আবেগপ্রবণ আবার চূড়ান্ত উদাসীন। একটা কাজের জন্য সদ্য জমে ওঠা ডাক্তারীর পশার ছেড়ে অনিশ্চিতের সন্ধানে পাড়ি দিতে পারেন, অথচ কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেলে অনায়াসে সরে যেতে পারেন সম্পূর্ণ অন্য কাজে। ব্যক্তিগত জীবনেও এমনকি সম্পর্কের প্রতিও তিনি একই রকম উদাসীন; বাড়ি কেনার কয়েকমাসের মধ্যে সেই বাড়ি বেচে দেন, সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারেন দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে, আর তার একমাসের মধ্যেই নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বিয়েও সেরে ফেলতে পারেন। সেই সম্পর্ককেও যত্ন করলেন না, টিকল না সেই বিয়ে। কাজের প্রয়োজনে অজস্র কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছেন, তাদের অগ্ন্যাশয়ের নালী বেঁধে তাদের স্বাভাবিক বিপাকীয় ক্রিয়া নষ্ট করে মৃত্যু ঘটিয়েছেন, আজকের বিচারে যাকে নিষ্ঠুরতাই বলা যায়। আবার কুকুর ৩৩ কে ভালোবেসে নাম রেখেছেন মার্জরী। কিন্তু মাথাগরম এই মানুষটির শত্রুতার প্রতি দায়বদ্ধতা অসাধারণ; একবার যাকে শত্রু হিসেবে চিনে নেবেন, তার প্রতি মনোভাব ধরে রাখবেন সারাজীবন। যেমন, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক ম্যাক্লাউড; সারা বই জুড়ে ছোট ছোট ঘটনায় এঁর সঙ্গে বান্টিং বিরোধের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নানারকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিরপেক্ষভাবে এই মানুষটির ভালো-মন্দয় মেশানো পরিস্কার ছবি এঁকেছন লেখক।
দু-বছর কতটুকু সময় ! একটা গবেষণার প্রাথমিক কাজটুকু করে উঠতেই দুবছর লেগে যায়। অথচ যে ঘটনার কথা দিয়ে এই লেখা শুরু হয়েছিল, সেই দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে, কখনো সাফল্যে, কখনো ব্যর্থতায়, কখনো হতাশায়, কখনো অভিনন্দনের বন্যায়, বচসায় ও সম্মিলিত কাজের অভিজ্ঞতায় মাত্র দু বছরের মাথায় বান্টিং-এর জীবনের পরম পুরস্কার নিয়ে এল ইনসুলিন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পুরস্কার পেলেন বান্টিং (তাঁর তরফ থেকে) চিরশত্রু ম্যাক্লাউডের সঙ্গে যৌথভাবে। বান্টিং-এর জীবনে গোলাপের মধ্যে কাঁটাটা রয়েই গেল। কিন্তু প্রশ্নটা পাঠকের মনেও রয়ে গেল, ম্যাক্লাউড ঠিক কি কারণে নোবেল পুরস্কারটা পেলেন ? তিনি তো হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি কোনোদিনই। শুধুমাত্র ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন, মতামত দিয়েছেন, কখনো জনসভায় নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন বান্টিং-বেস্ট-এর করা পরীক্ষার ফলাফল। শুধু তার জন্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায় ! আর বেস্ট, যিনি গোটা পরীক্ষায় সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন, হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবেই তাঁর অবদানের কথা উহ্যই থাকল ! এখানে এসে হয়তো পাঠকের মনে পড়ে যাবে মহাকাশবিজ্ঞানী জসলিন বেল বার্নাল আর পদার্থবিজ্ঞানী লিজ মাইটনারের কথা, যাঁদের হাতে-কলমে আর খাতায়-কলমে কাজের কৃতিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেছিল নোবেল কর্তৃপক্ষ। তবে বান্টিং-ম্যাক্লাউড কেউই অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তাই পুরস্কারের সম্মান না হোক অর্থের আধাআধি ভাগ দিয়েছিলেন নিজের নিজের সহকর্মী বেস্ট আর কলিপকে। সেও এক বিরল ঘটনা বটে। এই সব ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার যথাযথ উল্লেখ ও তার তথ্যসূত্রের সংযোজন বইটিকে অমূল্য করে তুলেছে।
বিখ্যাত মানুষদের জীবনী মনোগ্রাহী গল্পের আকারে লিখতে গেলে অনেক লেখকই নিজের কল্পনা মিশিয়ে কিছু ছবি আর সংলাপ যুক্ত করেন। অনেক সময়ই তা বাস্তবের বাইরে চলে যায়, সচেতন পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, এই সংলাপ কে শুনেছে! এই বইতে লেখক সেই প্রবণতা সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। সংলাপ প্রায় নেইই, ব্যক্তিগত আলাপচারিতার কথা যেখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটির তথ্যসূত্র (প্রায় জার্নালে যেভাবে রেফারেন্স দেওয়া হয়, সেইভাবে) দেওয়া আছে। গোটা বই জুড়ে অজস্র পাদটিকার মাধ্যমে নানারকম সহযোগী তথ্য সরবরাহ করেছেন লেখক। সেসব পাদটিকা জুড়ে জুড়ে হয়তো বইয়ের অর্ধেকের কাছাকাছি হয়ে যাবে। মূল আখ্যানের গতিকে ব্যহত না করে এই সব সহায়ক তথ্যের সংযোজন বইটির সম্পদ। সত্যি বলতে কি এইভাবে পাদটিকার মাধ্যমে তথ্যসূত্র সংযোজনের পদ্ধতি থেকে বিজ্ঞান লেখকরাও কিছু শিক্ষা নিতে পারেন। বইটির পাতা ও ছাপা খুবই ভালো, কিন্তু অলঙ্করণে আর একটু যত্নশীল হওয়া উচিৎ ছিল। সামান্য ছাপার ভুল রয়ে গেছে, আর ছবিগুলো বাঙলা হরফে এবং একটু বড় পাঠযোগ্য হরফে পাওয়া গেলে বইটি ত্রুটিহীন হত।
ইনসুলিনের নিষ্কাশনের বর্ণনা, ধাপে ধাপে তাকে ওষুধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার প্রচেষ্টা, ম্যাক্লাউডের সঙ্গে আপাতঃ শত্রুতার কারণ ? সেসব কিছু এখানে ফাঁস করব না। জানতে গেলে বইটা পড়তে হবে।
বই: ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টিং - কর্ম ও জীবন
লেখক: সহস্রলোচন শর্মা
প্রকাশক: বাঙলার মুখ
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনপ্রথম স্পন্দন - albert banerjeeআরও পড়ুনঅনন্ত জীবন - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনসেই দিন সেই মন - রঞ্জন রায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)
(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)
(লিখছেন... lcm, Bratin Das, সেই এক)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... গুগুস, aranya, রঞ্জন)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।















