- বুলবুলভাজা পড়াবই বই কথা কও

-
দাদামশায়ের থলে থেকে প্রশাসনের পাঠ
দিলীপ ঘোষ
পড়াবই | বই কথা কও | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ | ১০৩৪ বার পঠিত 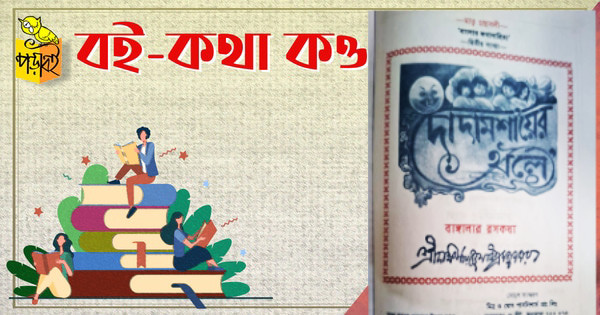
বছর ছয়েক বয়স তখন। জন্মদিনে একসঙ্গে তিনখানা কাপড়ে বাঁধানো বই উপহার পেয়েছিলাম। একই লেখকের লেখা দুটো ‘ঝুলি’ আর একটা ‘থলে’। যথাক্রমে ‘ঠাকুরমার’, ‘ঠাকুরদার’ এবং ‘দাদামশায়ের’।
ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষস খোক্কস, লালকমল নীলকমল অবশ্যই টেনেছিল একটা বয়স পর্যন্ত। ঠাকুরদার ঝুলি শেষ করতে পারিনি বেশ কয়েকটা চেষ্টার পরেও, সেখানে অনেক ক’জন মেয়ের গল্প, আর তাদের কারোর সঙ্গেই আমার তখনো পর্যন্ত বাস্তবে দেখা মেয়েদের কারুরই কোনো মিল পাইনি। আমার সবচেয়ে ভাল লাগতো ‘দাদামশায়ের থলে’ পড়তে। সেখানে দৈত্য, দানব রাক্ষস, খোক্কস, পরী, কেউ নেই, আছে শুধু নানা রকমের মানুষ; বোকা, চালাক, সৎ অসৎ সবরকম আর খুব ছোট্ট পরিসরে কয়েকটা ভূত, তাও এক আধটা গল্পে, একটু সময়ের জন্য।
বেশী ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই সম্ভবত, দাদামশায়ের থলেটাই সবচেয়ে আগে হারিয়ে গেল। পরে কিনব বলে অনেক খুঁজেছি, কোথাও পাইনি। ঠাকুরমার ঝুলি অবশ্য সবসময়েই পাওয়া যেত।
কলেজের পালা শেষ করার অল্প কিছু পরেই রাজ্যের প্রশাসনে যোগ দিয়েছিলাম। অগ্রজ প্রশাসকরা আমাদের মতো আনাড়িদের সতর্ক করার সময়ে দুটো প্রবচন প্রায়ই ব্যবহার করতেন। প্রথমটা “এখানে মুড়ি মিছরি এক দর” আর দ্বিতীয়টা হলো, “চাইলে ঢেউ গুনেও পয়সা করা যায়”। প্রথমটা সাধারণত অতি উৎসাহ দেখালে উচ্চারিত হতো, দ্বিতীয়টি আসতো দুর্নীতি তথা ঘুষের অনুষঙ্গে। দুটো প্রবচনই আমার খুব চেনা, এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ‘দাদামশায়ের থলে’ - র সৌজন্যে।
তাঁর সংগৃহীত বাংলার রূপকথা সিরিজে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের প্রথম বই ছিল ঠাকুরমার ঝুলি। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছিলেন মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকার শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া, তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত। আমি হইলে ত এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্বে কোন কোন গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি-কিন্তু হৌক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।
কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।
এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু- শয়ন- রাজ্যে পুনর্বার তাঁহাদের নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।”
দক্ষিণারঞ্জন যথেষ্ট সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ।
১৯০৭ সালে প্রথম প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই বইটির (ঠাকুরমার ঝুলি) তিন হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। একে একে প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর বাকি বইগুলি - ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯০৯ সাল), ঠানদিদির থলে (১৯০৯), দাদামাশয়ের থলে (১০১৩ সাল), চারু ও হারু (১৯১২), ফার্স্ট বয় (১৯২৭), লাস্ট বয়, বাংলার ব্রতকথা, আমার দেশ, সরল চন্ডী (১৯১৭), পুবার কথা (১৯১৮), উৎপল ও রবি (১৯২৮), কিশোরদের মন (১৯৩৩), কর্মের মূর্তি (১৯৩৩), বাংলার সোনার ছেলে (১৯৩৫), সবুজ লেখা (১৯৩৮), চিরদিনের রূপকথা (১৯৪৭), আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী (১৯৪৮)।
ঠাকুরমার, ঠাকুরদার এবং সম্ভবত ঠানদিদির (‘সম্ভবত’ কারণ ঠানদিদির থলে আমার পড়ার সুযোগ হয়নি) কাল্পনিক জগত থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণারঞ্জনের দাদামশায় হেঁটেছেন কৌতুকে মোড়ানো প্রশাসনিক বাস্তবের কঠিন মাটিতে। এই বইতে একটি গল্পের ছোট্ট একটি অংশে কয়েকটা ভূত ছাড়া সব চরিত্রই রক্ত মাংসের মানুষ, যদিও তাঁদের কারুর কারুর বুদ্ধি কিম্বা বুদ্ধিহীনতা দুটোই চরম পর্যায়ের।
দাদামশায়ের থলে - র প্রথম গল্প ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’। দুটি নামই খুব জনপ্রিয় এবং নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়। নামের সঙ্গে মিল রেখেই রাজা ও মন্ত্রীর বুদ্ধির বহর। গল্পের গোড়ার দিক থেকেই একটা নমুনা রাখা যেতে পারে।
“অনেক দূর হইতে কয়েকজন বিদেশী লোক আসিয়াছে। তাহারা রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে দেখিল, পরিষ্কার ঠাঁই। দেখিয়া, সেইখানে তাহারা পাকসাক করিয়া খাইবে ঠিক করিল। একজন কাঠ কুড়াইতে লাগিল, একজন উনন খুঁড়িতে বসিল, আর সকলে আর আর সব আয়োজন করিতে লাগিল।
হাওয়া-কুঠরি হইতে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন,-“মন্ত্রী! পুকুরপাড়ে ও কী? অত লোক কেন দেখ তো!”
মন্ত্রী এ জানালা, ও দরজা, ও জানালা, সে দরজা দিয়া ঝুঁকি দিয়া, গলা বাড়াইয়া, কাৎ হইয়া, বেশ করিয়া দেখিয়া টেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,-"মহারাজ! ভয়ানক সর্বনাশ!-রাজ্য গেল! কোথা থেকে কতগুলি লোক আসিয়া পুকুর তো চুরি করিয়া নিল! ঐ দেখুন সিঁদ কাটিতেছে!"
রাজাও দেখেন, তাই তো!
লোকেরা উনুন খুঁড়িতেছিল কি না? রাজা মন্ত্রী ভাবিলেন, সিঁদ কাটিয়া পুকুর চুরি করিতেছে!
অমনি-"ধর! ধর"-
রাজদুয়ারে ডঙ্কায় কাটি পড়িল। ঢাল তরোয়াল নিয়া যত সিপাই ছুটিল। লোকগুলাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ধরিয়া আনিল।
তখনি শূলে!
রাজ্য গিয়াছিল আর কি! “
এ হেন রাজা মন্ত্রীর রাজত্বে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী আর তাঁর শিষ্য।
দুপুর রৌদ্র। পুকুর-পাড়ে সুন্দর বটগাছ দেখিয়া, সন্ন্যাসী বলিলেন, "শিষ্য, এস এখানে একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করি।"
শিষ্য ভারি খুশী। বিশ্রাম তো হইবেই, আবার টিশ্রামও।
সন্ন্যাসী, খুঁজিয়া টুজিয়া দেখেন, সঙ্গে, শুধু দুটি পয়সা। শিষ্যকে কিছু খাওয়াইতে হইবে, নিজেও স্নান করিয়া কিছু জল টল খাইবেন, পয়সা দুটি শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন,-"বাছা, তোমার জন্য এক পয়সার মুড়ি আর আমার জন্য এক পয়সার মিশ্রি নিয়া এস।"
শিষ্যের খুব রাগ হইল। শিষ্য মনে মনে বলিতে লাগিল,-"ভাবিলাম, ভাল করিয়া বিশ্রাম টিশ্রাম হইবে। তা শেষে এই?-এতে আমার কি হইবে? দু-দুদিন পর, শুধু কিনা এক পয়সার টিশ্রাম!"
কি করিবে, বিড় বিড় করিতে করিতে শিষ্য গেল।
সন্ন্যাসী, স্নান ধ্যান করিয়া, বাঘছালখানা গাছতলে পাতিয়া বসিলেন। কতক্ষণ পর, এক মস্ত ভাঁড় হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্য ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত।
- "ঠাকুর, ঠাকুর, আমরা কি স্বর্গে এলাম?"
"সে কি!" - সন্ন্যাসী অবাক। বলিলেন, "সে কি বাছা শিষ্য; ও তোমার ভাঁড়ে কি?"
আর শিষ্য! শিষ্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল, - "আর কি! মুড়ি মিশ্রি কে খায়? এখানে এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি, রসগোল্লাও এক পয়সায় পাঁচ সের! পেট পুরিয়া রসগোল্লা খাইলাম। আপনি বলিলেন মিশ্রি, তাই আপনার জন্য এক পয়সার মিশ্রি আনিয়াছি - পাঁচ সের। এখানে মুড়ি মিশ্রি ক্ষীর ছানা সন্দেশ' রসগোল্লা সব সমান। ঠাকুর, নিশ্চয় স্বর্গ। ঠাকুর, আজ এতদিনে আমরা স্বর্গে আসিয়াছি!!"
সন্ন্যাসী বলিলেন, - "শিষ্য, বাছা, ও ভাঁড় ঐখানেই রাখ। শীঘ্র চল, শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পলাও। মুড়ি মিশ্রির সমান দর। এ নিশ্চয় কোন মূর্খের দেশ; এদেশে আর এক মুহূর্তও থাকিতে নাই।"
বলিয়া, সন্ন্যাসী তখনই উঠিয়া পড়িলেন।
আর শিষ্য। শিষ্য তল্পির কাছে বসিয়া পড়িয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, - "ঠাকুর গো! ক্ষীর ছানা সন্দেশে প্রাণটা যে আমার জুড়াইবে গো। এমন স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো!"
সন্ন্যাসী কত বুঝাইতে লাগিলেন। পেটুক শিষ্য কিছুতেই বুঝিল না। শিষ্য, স্বর্গের মাটি ধরিয়া শুইয়া পড়িল। একবার স্বর্গ পাইয়াছে, সে কি আর স্বর্গ ছাড়ে?
কি করিবেন সন্ন্যাসী? বলিলেন, - “বাছা, আমার কথা শুনিলে না, ভাল করিলে না। এদেশে থাকিলে একদিন না একদিন বিপদে পড়িবেই। যা' হউক, তখন আমায় স্মরণ করিও!"
দীর্ঘ গল্পটির শেষে বিনা দোষে যখন শুলে চড়তে বসেছিল শিষ্য তখন সন্ন্যাসী তা জানতে পেরে শিষ্যকে উদ্ধার করতে আবার সেই শহরে উপস্থিত হয়ে তাকে বাঁচান। ক্লাইম্যাক্সটি চমকপ্রদ এবং ঘুরেফিরে ঠিক কতোবার যে পড়েছিলাম ছোটবেলায় তার ঠিক নেই। ‘মুড়ি মিছরি একদর’ -এর উৎসও এই লোককথাটি।
একদম বিপরীত একটি চরিত্রকে পাওয়া যায় ‘সরকারের ছেলে’ গল্পে, যেখানে ঢেউ গোণার প্রসঙ্গটি আছে। গ্রামের সবচেয়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষের ছেলে রামধন সরকার বাবা মারা যাওয়ার পর গ্রামে আর তেমন কোনো কাজ জোগাড় করে উঠতে পারল না। গ্রামের লোকজন বলতে শুরু করল রামধন ‘বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে’। কাজ খুঁজতে রাজবাড়িতে ঢুকে রামধন রাজাকে বলল সে যে কোন কাজ করতে রাজী। রাজা বললেন কাজ দেবেন কিন্তু মাইনে দেবেন না। রামধন রাজি হয়ে গেল। প্রথম কাজ ছিল রাজবাড়ির সিংহদরজায় ঘন্টা বাজানোর হুকুম দেওয়ার কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে রামধন একটা চোর ধরে ফেলল। এরপর কাজ ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠল। মূল গল্প থেকেই পড়া যাক,
“অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী বলিলেন,-"রামধন সরকার! এবার তোমায় একটা নূতন কাজ দেওয়া গেল! কাজ এই, এই শহরে মোট কতগুলি রাস্তা আছে, কোন্ রাস্তা কতটা লম্বা, কতটা চওড়া, কোন্ রাস্তার উপর কটা বাড়ি আছে, কোন বাড়ীটি কত বড়, এই সব মাপিয়া আসিয়া তোমায় বলিতে হইবে। এ থেকে তুমি যা' উপায় করিতে পার!"
চমৎকার কাজ। রামধনের দিকে চাহিয়া সকল লোক, তখন, হাসিতে লাগিল।
রামধন বলিল,- "আজ্ঞা, তা আচ্ছা।"
রাজা বলিলেন,-"রামধন! কেমন এইবারের কাজটা কর দেখি! কাজটা ভাল নয়?"
রামধন বলিল,- "যো হুকুম মহারাজ।"
বলিয়া, রামধন, তখনই রাজার দপ্তরখানা হইতে পরওয়ানা, আর, লোক জন, দড়াদড়ি, মাপিবার জিনিষপত্র সব লইয়া, শহর মাপিতে বাহির হইয়া পড়িল।
বাহির হইয়াই রামধন, শহরের যে দিকে প্রকাণ্ড বাজার আর অনেক বাড়ি ঘর, সেইদিক হইতে, উত্তর দিকে প্রথম মাপ আরম্ভ করিল।
রাস্তার উপর দিয়া, বাড়ি ঘরের উপর দিয়া, দোকানের উপর দিয়া, লম্বালম্বি, পাশাপাশি, যে দিক দিয়া সোজা আর খুব সহজ হয়, রামধন সেইরূপে মাপিবার দড়ি ফেলিতে লাগিল। এখানটায় কতকগুলি ইট ফিট রহিয়াছে, কি ভাঙ্গা দেওয়াল রহিয়াছে, কিংবা দোকানদারের পসরা রহিয়াছে, বাড়ী ঘরের বারান্দায় জিনিসপত্র রহিয়াছে, লোকজন দিয়া সেগুলি সরাইয়া, ফেলিয়া- যতদূর সোজা আর সহজে মাপা যায়, রামধন তাহাই করিতে লাগিল। সারা শহরটাই মাপিতে হইবে তো। বাড়ি ঘর, রাস্তা, ঘাট, সব সুদ্ধ। সহজে না করিলে চলিবে কেন?
ছোট বড় যত দোকানদার, মহাজন, সকলে আসিয়া উপস্থিত, "ব্যাপার কি?"-
ওদিক হইতে, যাঁহাদের বাড়ি ঘর মাপের মধ্যে পড়িল, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত,- "কথা কি?"-
রামধন সকল বলিল।
শুনিয়া সকলে দেখিল, সর্বনাশ।-
- এরূপ করিয়া মাপ চলিলে তাহাদের বাড়ি ঘর জিনিস পত্রের দুর্দশা,- বেচা কেনা, কাজ কর্ম, খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ। সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল।
সকলে রামধনকে বলিল,- "দেখুন, রাজার যখন হুকুম, তখন মাপের জায়গা করিয়া দিতেই হইবে! কিন্তু এভাবে মাপিলে আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়, আপনি যদি দয়া করিয়া বাড়ীগুলির পিছন দিয়া ঘুরিয়া মাপিয়া যান, তাহা হইলে আমাদের কাজও বন্ধ হয় না, মাপাও হয়। এজন্য আপনাকে অবশ্য অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, তা আমরা সকলে আপনাকে সেজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিব,- আপনি দয়া করিয়া এইটুকু করুন।"
রামধন দেখিল, কথা ঠিক। নইলে লোকগুলির কাজের বড়ই ক্ষতি হয়। অথচ তাহাকে সমস্ত শহর মাপিতেই হইবে। ভাবিল- "আচ্ছা, ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মাপা যাক। তাহাতে সময় অবশ্য অনেক বেশিই লাগিবে। তবে পারিশ্রমিক যখন পাওয়া গেল, না হয় সারা রাত্রি খাটিয়াও শেষ করিব। তা ছাড়া আর উপায় কি?"
রামধন আর কি করিবে, কাজেই তাহাই স্বীকার করিল। লোকেরাও খুব সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে তার যা' অতিরিক্ত পারিশ্রমিক, সকলেই তা' দিতে লাগিল।
রামধন, সেদিন, সারা রাত্রি খাটিয়া, পরদিন প্রভাতে- পনের হাজার টাকা নিয়া রাজভাণ্ডারে জমা দিল। আর মাপের হিসাবপত্র নিয়া রাজসভায় বুঝাইয়া চুকাইয়া দিল।
রাজা বলিলেন, "শহরের সামনের এই নদীতে দিবারাত্র কত ঢেউ উঠে, ইহাই তুমি গণিবে। একটি ঢেউও যেন গণিতে ভুল হয় না; সঙ্গে পাহারা যাইতেছে; যাও!"
"যে আজ্ঞা!"-
রামধন একটু ভাবিলও না। বলিল,- "তা নদীর কতটা দূর পর্যন্ত ঢেউ আমায় গণিতে হইবে?"
মন্ত্রী বলিলেন,- "যত দূ-র দৃষ্টি যায় শহরের এ দিক থেকে ওদিক, স-বটা নদীর ঢেউ তোমায় গণিতে হইবে।"
- "আচ্ছা। তাহা হইলে মহারাজ, কয়েকজন লোক আমার লাগিবে।”
রাজা বলিলেন,- "তা বরং লইয়া যাইতে পার।"
তখন রাজসভা হইতে বিদায় লইয়া রামধন, খাতাপত্র, দোয়াত কলম, আর কয়েকজন লোক লইয়া ঢেউ গণিতে চলিল।
শহরের শেষ সীমানায় গিয়া রামধন নদীর এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিয়া, বলিল,- "এই পর্যন্ত তো আমার ঢেউ গণিতে হইবে?- আচ্ছা?"
লোকজনদিগকে বলিল,- "এই যে এখানে রাজ-নৌকার কাছিটি রহিয়াছে, এই কাছি এপার ওপার ধরিয়া আমার সীমানা এইখানে ঠিক করিয়া লও তো-"
হুকুম মত লোকজনেরা তাহাই করিল।
তখন রামধন ঢেউ গণিতে আরম্ভ করিল,-
-"দশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ শত ষাট্! ... পাঁচ লক্ষ দশ হাজার তিন শত সাত। ...সাত লক্ষ তিন হাজার আট শত তিন।..." রামধন হু হু করিয়া গণিয়া যাইতেছে, ঘরে একজন লোক রহিয়াছে সে হুকুম মত সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতেছে। গণা একটুকুও ফাঁক যাইতেছে না; লেখা একটুকুও বাদ যাইতেছে না।
এইরূপে ঢেউ গণা চলিতেছে। কোটি কোটি ঢেউ গণা হইয়া গেল। এদিকে বিস্তর নৌকা, সেই সীমানার কাছির কাছে আসিয়া আটক হইয়া গিয়াছে। রামধন পাহারাওয়ালা সিপাইদিগকে গর্জিয়া বলিল,- "পাহারাওয়ালা-সিপাই সব! তোমরা কি রকম পাহারা দিতেছ? শোন! সাবধান!-একটি নৌকাও যেন এদিকে আসে না,-"
আর গণিতে লাগিল,- "তের লক্ষ পনর হাজার পাঁচ শত পঁচিশ ...একটি আমার ঢেউ ভাঙ্গিবে কি, দশ হাজার টাকা জরিমানা।–
-বত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাত শত চৌরাশী...."
রামধন ঢেউ গণিয়া যাইতে লাগিল।
পাহারাওয়ালা-সিপাইরাও দেখিল, কথা ঠিক। তাহারা হাঁকিয়া বলিল,- "হুঁশিয়ার! নৌকা যেন আর একটুকুও বাড়াইও না!"
সব নৌকা সেইখানে আটক!
নৌকাগুলি প্রায়ই ছিল সব বড় বড় মহাজনদের। তাহারা দেখিল, সর্বনাশ। এরূপে নৌকা আটক থাকিলে, বন্দরে আজ গিয়া পৌঁছিতে না পারিলে তাহাদের যে, লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া যাইবে। উপায়?-
এদিকে তাহারা শুনিল যে, ঢেউগণা রাজার হুকুম!
শুনিয়া সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।
বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কি করিবে, অনুপায় দেখিয়া সকলে শেষে, রামধনের কাছে গেল। বলিল, “হুঁজুর, আপনি একটা গতি করুন। আপনি যদি আমাদিগকে এক ধার দিয়া একটু জায়গা না করিয়া দেন, তাহা হইলে আর উপায় নাই। দেখুন- আমরা একেবারে মারা যাই। হুজুর, আপনাকে আমরা টাকা দিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমাদের এইটুকু করুন-"
তখনি সকলে তোড়ায় তোড়ায় টাকা আনিয়া হাজির করিতে লাগিল। টাকার তোড়ায় স্তূপ হইয়া গেল।
রামধন বলিল,- "এ কি! টাকা কেন? সাবধান! তোমরা ও সব করিও না।" মহাজনেরা রামধনকে একেবারে ধরিয়া পড়িল, বলিল,- "হুঁজুর, তবে আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন; আমাদিগকে রক্ষা করুন!"
রামধন ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল, "ইহাদিগকে কোনরূপে একটু জায়গা করিয়া না দিলে বাস্তবিকই ইহাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। অথচ তাহাতে বিস্তর ঢেউ ভাঙ্গা যাইবে। কি করি?” ভাবিল,- "বেচারারা এত করিয়া ধরিয়া পড়িয়াছে, আর বাস্তবিকই বেচারাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। আচ্ছা, ঢেউ যাহা ভাঙ্গিবে, যত কষ্টে হউক কোন প্রকারে গণিয়া লইব। ইহারা যাক্।” বলিল- "আচ্ছা ভাই, যাও। সাবধান, ঢেউ যেন বেশি ভাঙ্গে না- তবে, যাহা ভাঙ্গিবে, আমি গণিয়া লইতেছি। কিন্তু এ সব টাকা তোমরা লইয়া যাও।"
ঢেউ যেমন গণিতেছিল, রামধন, তেমনই গণিতে লাগিল।
এ উপকারে মহাজনদের তখন আনন্দ আর ধরে না। তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তাহারা পরামর্শ করিল,- "ভাই দেখ, ইনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিলেন। আমাদিগকে অনেক টাকার ক্ষতি হইতে বাঁচাইলেন। যে টাকা আমরা * দিতে আনিয়াছি, এ টাকা আমরা উহাকে দিয়া যাইব।” পরামর্শে তাহাই ঠিক হইল। সকলে বলিল, "হুজুর, এ টাকা আপনার লইতেই হইবে। বহু টাকার উপকার আপনি আমাদের করিয়াছেন, এ টাকা না লইলে চলিবে না। আমরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এ টাকা দিয়া গেলাম।”
রামধন বলিল,- "না। শোন, তাহা হইবে না।"
মহাজনেরা কিছুতেই শুনিবে না।- "না হুজুর, টাকা লইতেই হইবে।" কিছুতেই রামধনকে মহাজনেরা ছাড়িল না। অনেক কথা কাটাকাটির পর শেষে, রামধন, কি করিবে, অগত্যা টাকাটা খাতায় জমা করিয়া লইল।
যেমন ঢেউ গণিতেছিল তেমনি গণিতে লাগিল।
ও-ই দূর দিয়া খুব সাবধানে মহাজনেরা নৌকা লইয়া যাইতে যে সব ঢেউ ভাঙ্গা গেল, রামধন নিজ কথামত সেগুলি খুব পরিষ্কার হিসাব করিয়া নিখুঁতভাবে লিখিয়া লইল। একটিও তাহার ভুল গেল না।
সারা দিনরাত এইরূপে ঢেউ গণিয়া, পর দিন ভোরে রামধন বিশ হাজার টাকার বিশ তোড়া নিয়া রাজভাণ্ডারে জমা দিল। আর ঢেউয়ের হিসাব নিয়া রাজসভায় বুঝাইয়া দিল।
রাজা মন্ত্রী বলিলেন, "তাই তো!" জিজ্ঞাসা করিলেন,- "তুমি কি করিয়া ২০,০০০ টাকা উপায় করিলে?"
রামধন মাথা নোয়াইয়া সব কথা বলিল।
রাজা মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুঁ? আচ্ছা, নৌকা যাইতে যেসব ঢেউ ভাঙ্গিয়া ছিল তাহার হিসাব তুমি কি করিয়া পাইলে?"
রামধন বলিল- "মহারাজ, কেন ৮ টুক্রাতে ১; ৪ টুক্রাতে ১; ২ টুকরাতে ১; এইরূপে, এই দেখুন, মোট ভাঙ্গা ঢেউ হইয়াছে, নিরানব্বুই নিখর্ব্ব নিরানব্বুই বৃন্দ নিরানব্বুই কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই হাজার নয়শত নিরানব্বুই।"
- ঢেউ গণার সমস্ত খাতা রাজসভায় ছড়াইয়া, রামধন, ভাঙ্গা ঢেউয়ের অঙ্কগুলি পরিষ্কার দেখাইয়া দিল।
রাজা মন্ত্রী বলিলেন,- “বেশ্। কিন্তু তোমার যে ভুল হয় নাই তার ঠিক কি?"
রামধন, জোড়হাত করিয়া বলিল,- "মহারাজ, যে কাহাকেও দিয়া আবার গণাইয়া দেখুন। যদি একটিও ভুল হইয়া থাকে, আমি অবশ্যই শাস্তি পাইব।”
রামধনের চরিত্রের সবচেয়ে অনন্য দিক হলো সে বুদ্ধিমান, কিন্তু সৎ। নানা উপায়ে সে যে অর্থ সংগ্রহ করছে তা রাজকোষে জমা দিচ্ছে, আত্নসাৎ করছে না। গল্পের শেষে রামধন রাজার দেওয়া বিশাল অর্থভাণ্ডার নিয়ে গ্রামেই ফিরে আসে এবং টাকাটা জনকল্যাণে নিয়োগ করে।
এই ঢেউ গোনার গল্পে মনে হয় সমকালীন একটা ঘটনার ছায়া পড়েছিল। রাণী রাসমণি ঘুসুড়ি এবং মেটিয়াব্রুজের মাঝে একটি আন্তর্জাতিক অংশ লিজ নিয়ে বড় বড় লোহার চেন দিয়ে নদীর এ পাড় ও পাড় আটকে ব্রিটিশ নৌকা গঙ্গা নদীতে চলাচল বন্ধ করেছিলেন ১৮৪০- এর দশকে, বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাছ ধরা নিয়ে জেলেদের ওপর যে কর আরোপ করেছিল তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে। নৌকা চলাচল স্থগিত করে তিনি এই কর বাতিল করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা একান্তই আমার মনে হওয়া, কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই।
এরকমই আরেকটা প্রশাসনিক গল্প ‘রাজপুত্র’। এক বুড়ো রাজা মারা যাওয়ার সময়ে তাঁর পুত্রকে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন,
“প্রতিদিন, প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও।
টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও।
আর, তিন ঠেঙ্গে, তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও।
- এই কথামত, তুমি কাজ করিও।”
রাজপুত্র এই সব উপদেশ আক্ষরিক অর্থে পালন করতে গিয়ে রাজ্য একেবারে রসাতলে পাঠিয়ে দিলেন। শেষে এক বৃদ্ধ রাজাকে এই উপদেশগুলো্র মর্মার্থ বোঝালেন।
“রাজপুত্র, তিনি যা বলিয়াছিলেন, তা এই,- ………… -রাজার যে রাজভাণ্ডার, তা প্রজার জন্য। রাজা, নিজে কখনও লোভী হইবেন না। প্রজার আর সৎকারের জন্য সব রাখিয়া, রাজা নিজের জন্য খুব অল্পই রাখিবেন। তাহাতেই রাজা বড় হন। আপনি যদি, ছোট ছোট মাছ খাইতেন, তবে প্রতিদিন, প্রতি গ্রাসেই মুড়া খাওয়াও হইত, আর, কখনও অসুখও করিত না। অথচ রাজপুত্র, কত অল্পেই আপনার চলিয়া যাইত। রাজভাণ্ডারের ধন সব দরিদ্রের জন্যই থাকিত। তা ছাড়া, রাজা খুব বেশী ব্যয়ীও হইবেন না। রাজা খুব বেশি ব্যয়ী হইলে, রাজার রাজভাণ্ডারও তো ফুরাইয়া যায়!
- রাজা যদি অল্পে তুষ্ট হন, প্রজারাও অল্পে তুষ্ট হয়। ঘরে ঘরে সঞ্চয় হয়; রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা হোক, দরিদ্র হোক, এই ভাবে চলিলে, তাঁদের ঘরেই লক্ষ্মী অচলা হন।"
বলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন, আর কি বলিয়াছেন?- “ধার দিয়া টাকা লইও না-”
- হাঁ, ও কথার অর্থ এই যে,- ধার অনেক সময় দিতে হয়। ধার দিবেন। কিন্তু ধার, আর দান তো, এক কথা নয়। ধার যদি দিতেই হয়, এমন ভাবে দিবেন, যেন আপনার টাকা আপনার কাছেই থাকে। নষ্ট না হয়।
কি করিয়া তা' হয়?-
যাহাকে টাকা ধার দিবেন, তার কাছ থেকে এমন কোন জিনিস রাখিয়া ধার দিবেন, যে, টাকা যদি ফিরিয়া না পান, তবু যেন আপনার ক্ষতি না হয়। মনে রাখুন, রাজপুত্র! পাইব না ভাবিয়াই কোন জিনিস রাখিয়া টাকা ধার দিতে হয়! তা' হইলে, টাকা না পান, টাকার বদলে সেই জিনিসটিই থাকে! এই রকমে ধার দিলে, টাকা নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। বরং ধন বৃদ্ধি হয়।”
রাজার যেন, চক্ষু খুলিল। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, বৃদ্ধের কথা প্রাণ দিয়া শুনিতে লাগিলেন।
বৃদ্ধ বলিলেন,-"তার পর রাজপুত্র!-শাসন”
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিবে, এর অর্থ?
রাজপুত্র! যিনি রাজা, তাঁর রাজ্য যাতে ঠিকমত খুব ভাল শাসন হয়, তা তিনি করিবেন। যা'তে প্রজা সুখে থাকে, শান্তি পায়, গরীব না হয়, মূর্খ না হয়, তাদের উপর কেউ না অন্যায় করে, তারাও কেউ অন্যায় না করে,- এইসব দেখিবেন। তাদের মধ্যে কেউ গুণী থাকিলে রাজা তাঁর আদর করিবেন, সম্মান করিবেন, তাঁকে পুরস্কার দিবেন, এইভাবে সব প্রজাকে সুখী করিবেন। তাহা হইলে বাজপুত্র, প্রজারা প্রাণ খুলিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করে। ইহারই নাম শাসন। এমনি কবিয়া রাজা যদি সজাগ হইয়া শাসন করেন, তবে সে রাজ্য সোনার রাজ্য হয়, সে রাজ্যে রাজা প্রজা- পরমানন্দে কাল কাটায়।–
- বুঝিলেন রাজপুত্র?"
নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন, "বুঝিলাম!"
রাজা মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।
তাহার পর, বৃদ্ধ বলিলেন-"রাজপুত্র, এখন তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথার কথা। তা, রাজপুত্র, আপনি যা করিয়াছিলেন, সে সব তো- তামাশা!
কিন্তু তা না রাজপুত্র, তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথার অর্থ হ'ল- বুড়ো মানুষ।
এই দেখুন আমি বুড়ো হইয়াছি; এখন আমার ঠ্যাং হইয়াছে তিনটি; লাঠিটি ধরুন আমার একটি ঠ্যাং! ইহার উপর ভর না দিলে আর আমি দু'পায়ে চলিতে পারি না। তিনটি পায়ে আমায় চলিতে হয়। দেখুন আরও, হাঁটু দুটি উঁচু হওয়াতে, আমার আর দুটি মাথার মত হইয়াছে। কাজেই, আমি এখন তিন-ঠেঙ্গেও হইয়াছি, তে-মাথাও হইয়াছি।
-রাজপুত্র! এইরকম তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা বুড়োরা অনেক কিছু দেখিয়াছে, শুনিয়াছে। কাজেই তাঁহারা অনেক কথা বলিতে পারেন। আপনার পিতার কথার অর্থ এই যে, অনেক সময় শুধুই নিজের বুদ্ধিতে, কি যারা বেশি কিছু দেখে শুনে নাই, তাদের কথামত কাজ করিতে নাই। তাতে অনেক দোষও হয়, বিপদও হয়। আর রাজপুত্র! বিপদকালে শেষে বুড়োর বুদ্ধি নিতেই হয়!- রাজপুত্র! বৃদ্ধের কাছে উপদেশ নিয়া, তবে সব কাজ করিবেন।"
বলিয়া, বৃদ্ধ শেষে বলিলেন,-
- “এইবার, রাজপুত্র! যে সব উপদেশ আমি দিলাম, এখন গিয়া সেই মত কাজ করুন, দেখিবেন আপনার পিতার কথা সত্য হইবে। আপনার রাজ রাজ আবার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিবে।”
ছয় থেকে আট বছর বয়সে পড়া মোট আটটা গল্পের সেই বইটা- তখন বুঝিনি, কিন্তু অজান্তেই মনের ভেতর এক ধরনের প্রশাসনিক মূল্যবোধ গেঁথে দিয়েছিল। চৌদ্দ-পনের বছর পরে, যখন সত্যিকারের প্রশাসনের ভেতরের জটিল কলকবজা চিনতে শুরু করলাম, তখন হঠাৎ হঠাৎ সেই পুরোনো গল্পগুলো মনে পড়ত। তারা ভিতর থেকে ফিসফিসিয়ে বলত- “সেই গল্পটাই এখন তোমার চারপাশে ঘটছে।”
ধীরে ধীরে একটা ধারণা তৈরি হতে থাকে- দুর্নীতি আর অদক্ষতা আসলে আলাদা কিছু নয়; তারা একই অসুস্থ প্রশাসনিক শরীরের দুই দিক। একে অপরকে খায়, আবার একে অপরকে বড় করে তোলে। যেখানে দক্ষতা, তথ্যপ্রবাহ ও জবাবদিহির অভাব, সেখানে কাজের মান পড়ে যায়, নিয়ম-কানুন ঝাপসা হয়ে যায়, আর সেই ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে দুর্নীতি। অদক্ষ কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠান নিজের দুর্বলতা আড়াল করতে ঘুষ, পক্ষপাত কিংবা রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ার ভরসা নেয়।
অন্যদিকে, একবার দুর্নীতি ঢুকে পড়লে যোগ্যতা ও সততার দাম কমে যায়। পদোন্নতি, নিয়োগ বা সিদ্ধান্ত তখন আর কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে না- নির্ভর করে কার সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে তার ওপর। এতে যারা সত্যিই কাজ জানে, তাদের উৎসাহ হারায়; প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এভাবেই গড়ে ওঠে এক দুষ্টচক্র- অদক্ষতা জন্ম দেয় দুর্নীতিকে, আর দুর্নীতি আরও অদক্ষ করে তোলে প্রশাসনকে। তখন নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব বাড়ে, জনস্বার্থের জায়গা দখল করে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ।
তবে “অদক্ষতা” মানে শুধু মেধা বা বুদ্ধির অভাব নয়। আসল অদক্ষতা জন্ম নেয় নৈতিক বুদ্ধিহীনতা থেকে- যে বুদ্ধি জানে কী সঠিক, কিন্তু তবু স্বার্থের পথে হাঁটে। আমি নিজের চোখে দেখেছি- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফল করা, অ্যাকাডেমিকভাবে উজ্জ্বল অনেক আধিকারিকের ভেতরেও এই নৈতিক বুদ্ধিহীনতার ছাপ। এঁরা যেন দক্ষিণারঞ্জনের রামধন সরকারের উল্টো প্রতিরূপ বুদ্ধিমান, কিন্তু অসৎ।
আমার এই ধারণাগুলো নিয়ে সহকর্মীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কেউ একমত হন, কেউ তর্ক করেন; কিন্তু আমি যতই দেখেছি, ততই মনে হয়েছে- প্রশাসনের আসল সংকট কোথাও না কোথাও এই নৈতিক অদক্ষতাতেই লুকিয়ে আছে।
এ বছর পুজোর সময়ে ব্যাঙ্গালোরের এক পুজো মণ্ডপের বইয়ের স্টলে হঠাৎ পেয়ে গেলাম ‘দাদামশায়ের থলে’, নতুন করে ছেপেছেন মিত্র ও ঘোষ। ৬৪/ ৬৫ বছর পরেও একই রকম ভাল লাগল পড়তে।
প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সিলেবাসে দাদামশায়ের থলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন কর্তৃপক্ষ।
------------------
বই: দাদামশায়ের থলে
প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
মূল্য: ২৯৯ টাকা
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনকী আসে যায় নামে? - দিলীপ ঘোষআরও পড়ুনছেঁড়া তার - Rajat Dasআরও পড়ুনপ্রথম স্পন্দন - albert banerjeeআরও পড়ুনভূত-ই ভবিষ্যৎ - Rajat Dasআরও পড়ুনস্থলপদ্ম - Manali Moulikআরও পড়ুনসেই দিন সেই মন - রঞ্জন রায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 kk | 2607:fb91:4c21:664d:b539:75bb:5e2:***:*** | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:১৫735286
kk | 2607:fb91:4c21:664d:b539:75bb:5e2:***:*** | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:১৫735286- খুবই ভালো লাগলো এই লেখাটা। আমি 'দাদামশায়ের থলে' বইটা পড়িনি। 'ঠানদিদির থলে'টা পড়েছিলাম। ওতেও খুব ভালো ভালো গল্প ছিলো -- তূলা রাশি রাজকন্যা, নয়নমণি, ছেলে কার, এইসব।
 Shyamal Chakrabarti | 2401:4900:882b:cdbd:2005:13df:4010:***:*** | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ১৮:২৭735296
Shyamal Chakrabarti | 2401:4900:882b:cdbd:2005:13df:4010:***:*** | ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ১৮:২৭735296- বেশ ভালো লাগলো নিবন্ধটি। রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জনহিতের সূত্রগুলো অবশ্যই ব্যতিক্রমী।"দাদামশায়ের থলে" সংগ্রহ করে অবশ্যই পড়ব।
 সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। | 2409:40e1:11b9:823:ca95:93ad:66ac:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ০০:০৯735302
সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। | 2409:40e1:11b9:823:ca95:93ad:66ac:***:*** | ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ০০:০৯735302- ভীষণ ভাল লাগল। খারাপ লাগল এই অমূল্য বই পড়িনি বলে। আপনার কাছে কত কি শিখি। বইটি জোগাড় করে পড়ব।
 গৌতম কুমার পাল | 2402:3a80:198d:5aa2:2c0c:146f:83e9:***:*** | ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ০৯:১৪735338
গৌতম কুমার পাল | 2402:3a80:198d:5aa2:2c0c:146f:83e9:***:*** | ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ০৯:১৪735338- খুব ভালো লাগলো স্যার। গল্প আর তার মর্মার্থ। দুইই। অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন আর আমাদের সমৃদ্ধ করতে এমন লেখা দিতে থাকবেন, স্যার।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)
(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)
(লিখছেন... lcm, Bratin Das, সেই এক)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... গুগুস, aranya, রঞ্জন)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।















