- বুলবুলভাজা পড়াবই বই পছন্দসই

-
আবহমান কল্পনার উন্মুক্ত পরিসর
উপল মুখোপাধ্যায়
পড়াবই | বই পছন্দসই | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৬২১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 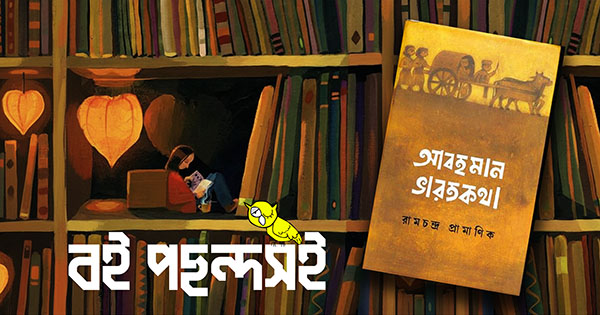
ছবি: রমিত
জহরলাল নেহেরু এক যুগ সন্ধিক্ষণে ভারত আবিষ্কার কল্পে তাঁর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া মহাগ্রন্থ রচনা করলেন। ভারত, যা কিনা ইন্ডিয়াও বটে তার কি আবিষ্কার সম্ভব? না তা এক বহমানতা, এমন এক বহমানতা যা কালাতীত ও মান্য, কারণ কন্টিনুয়াস, ওয়াজেদ আলির সেই ‘ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে’? যা ‘সমানে চলে’ তাতে কি আবিষ্কারের যুক্তিবাদী প্রকল্প চাপানো যায়? বরিষ্ঠ কথাকার রামচন্দ্র প্রামাণিকের ‘ভারত -আত্মার বিকাশ বিবর্তন এবং অমোঘ দুর্বলতাকে ধরার’ চেষ্টায় ব্যপ্ত গল্প সংকলন অনুস্টুপ প্রকাশনীর আবহমান ভারতকথা প্রসঙ্গে এই কটি কথা উল্লেখ্য বলে বোধ হয়। যে প্রয়াস তার ঘোষিত অবস্থানেই এক বৃহৎ প্রকল্পের অমোঘ দুর্বলতা ধরতে ধাবিত হয় তা অবশ্যই রিভিশনিস্ট বা সংশোধকামী হবে, যেমন নেহরুজির প্রয়াস, কিন্তু তা বিশিষ্ট হবে কিনা তার ওপর নির্ভর করছে তা ডিসকভারি- আবিষ্কার করবে কিনা, আবিষ্কারক হবে কিনা। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ কি তেমনি কোন পুনরাবিষ্কারে ধাবিত হওয়া এক বিশিষ্ট প্রয়াস?
ভারত, যা কিনা ইন্ডিয়া, তার অতীত কথা তথ্য নির্ভর হিস্ট্রি নয়। সে হিস্ট্রি হতেও চায় না। অতীত কথা তবে কী হতে চেয়েছিল না- হিস্ট্রি হয়ে? লোকগাথায় সে ছিল অবাধ কল্পনার আকর আর সংস্কৃতে সে বলত ইতিহাসের কথা। ইতিহাস মানে না-হিস্ট্রি। দু-ধরণের ইতিহাস। এক নায়কের গাথা (একনায়ক নয়!) আর বহু নায়কের গাথা। প্রথমটার উদাহরণ রামায়ণে পেলে দ্বিতীয়টা মেলে মহাভারতে। রামায়ণের কাব্য প্রসিদ্ধি, কাব্য গুণ তাকে সাহিত্যের দিকেও ঠেলেছে অনবরত। যতটা সাহিত্যের দিকে যায় ততটাই জয়গাথা থেকে চরিত মানসের আদর্শ পুরষোত্তমে শ্রীরামের উত্তরণ। মর্যাদা পুরুষোত্তমে, আদর্শ পুরুষে উপনীত হয়ে রামায়ণ নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি রচয়িতার কাব্য, সন্ত তুলসীর কাব্য হয়ে ওঠে না? অর্থাৎ না- হিস্ট্রি থেকে রামায়ণের যাত্রা ভাষা নদীর কূল বেয়ে, সংস্কৃত থেকে স্থানীয় ভাষায় রচিত কবিবরের কাব্য হওয়ায় যাত্রা নয় কি? কিন্তু অনেক সর্গে জটিল মহাভারতের গহীন অরণ্যে ভারতের যে রোদন তা নিছক কাব্যগুণের গুণী কোন স্রষ্টার কল্পসৃষ্টি তেমন হয়ে ওঠে না রামায়ণের মতো। এত জটিল এক বহুনায়কের বিষাদাচ্ছণ্ণ জয়গাথা মহাভারত, সে কারই বা একার চরিত মানস হবে? সে জন্য মহাভারত হল, হয়ে উঠল নানা সর্গের সমাহার, এক সর্গবন্ধ। এক ছকভাঙ্গা টেক্সট। ভাঙ্গা সময়ের সমাহার যার প্রতি সর্গের পরিণতি আছে। এক পরিণতি অন্যটায় আবহমান সময়রেখার নিরবিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ। আবহমান ভারতকথা বইটাও এই সর্গবন্ধ রূপে উনিশটি কাহিনীর জোড়কলম, যা খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো আশি থেকে একেবারে সাম্প্রতিক দু’হাজার দশ পর্যন্ত আগুয়ান সময়রেখা অনুসারে গ্রথিত। সে গ্রন্থনায় কত খানি বিশিষ্ট আমাদের লেখক রামচন্দ্র প্রামাণিক, সে বুঝতে আর আশপাশে না ঘুরে জয় মা বলে আলোচ্য টেক্সটে কামড় বসানো যাক তবে।
প্রথম গল্প সেই প্রাচীনকালে তথাগত প্রত্যাশী উপক নামের এক অরণ্যবাসী শ্রমণের আধ্যাত্মিক অধিযাত্রার গল্প যা শেষ পর্যন্ত দুই বৌদ্ধ আর্যসত্যের পূর্বানুমানে ফিরে আসে– এক, জীবন দুঃখময়, দুই, দুঃখের মুলে রয়েছে তৃষ্ণা। কিন্তু কালপুরুষ শ্রমণকেও যুবক করেছে আর সে যুবকের শরীর স্পর্শ করে ক্ষেমা নামের এক নারী। এখানে অপর পক্ষ নারী। কিন্তু সত্যের ঝংকারে, আর্যসত্যের পূর্বানুমান চাপে ক্ষেমার মনের জরিপ হয়েও হয় না। তার প্রকৃতিবৎ বর্তুল স্তন, তৃষ্ণার অবশেষ হয়েই থেকে যায়। টেক্সটের আর্যসত্যের নিপুণ বয়ান যেন গল্পকে বেশি রকম নিশ্ছিদ্র করেছে, একটু ধ্যাবড়ানো তুলির আঁচড়ের প্রত্যাশা কি থাকতে নেই?
যে আক্ষেপ প্রথম গল্পে ছিল তা বেশ দূর হল দ্বিতীয় গল্পে। এই গল্পটার নাম সুলক্ষণা, সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব দুশো চল্লিশ অর্থাৎ প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বের শেষভাগে। এই আখ্যানের কেন্দ্রে নারী আর তার অতৃপ্তি। ঘরের ভেতর আর বাহিরের সংযোগ ঘটায় দুই বিপরীত পদ্ধতি। কানাকানির নানা কামার্ত মুখরোচক কেচ্ছা আর ভিক্ষুণীর উপদেশ। একই সঙ্গে দুই বিপরীত পদ্ধতির গ্রহীতা এক শ্রেষ্ঠী জায়া সুলক্ষণা। সে বোঝে তার স্থানাঙ্ক, যা শুধু মানতেই বাধ্য সে। এমনকি ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী তথাগতও নারীর জন্য, ভিক্ষুণী সংঘের জন্য আঁটোসাঁটো নিষেধই প্রণয়ন করেন। কানাকানির পদ্ধতি এক ট্র্যাজেডির গল্প শোনায়- অশোকপত্নী মহিষী তিষ্যরক্ষিতা আত্মহত্যা করেন রাজকুমার কুণালের প্রতি অবৈধ প্রেম- প্রতিহিংসার জালে জড়িয়ে, কুমারকে অন্ধ করার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে প্রাণদণ্ডের শাস্তি এড়াতে। একই সঙ্গে বৌদ্ধ ভুক্ষুণী সংঘের নারী অবরোধী স্বরূপ সুলক্ষণাকে মুক্তিপথ বিমুখ করে আর যখনি সে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বয়স্ক লোলচর্ম স্বামীর বদলে সপুত্রকে কামনা করে তার পরিণতিও হয় আত্মহত্যায়। এ গল্পে রামচন্দ্র প্রামাণিক বৌদ্ধ ধর্মের নারী বিরোধিতার স্বরূপ অনেক মোটা দাগের কর্কশ এক তুলিতে এঁকে তত্বায়নের সব সম্ভাবনাকে কথার আরো বড় সম্ভবনার অধীনে রেখেছেন। গল্পটা হয়ত এ জন্যই বিশিষ্ট।
তৃতীয় গল্প খিলভূমির (অকর্ষিত জমি) প্রেক্ষাপট অনেকটা এগিয়ে চারশো পঁচাশি খ্রিষ্টাব্দ। সময় টা গুপ্তযুগ আর ব্রাহ্মণরা ফিরেছে পূর্ণ মহিমায়। তাদের দাপটে সমাজ দেহ বর্ণাশ্রম ভিত্তিক নানা নিদানের ভারে ঝুঁকে আছে। মানবিকতা প্রেম, নারীর মনের আকাঙ্খা চারদিক দিয়ে বেড় দিয়ে বাঁধা। কর্ম নিপুণ পিতৃ পরিচয়হীন শেখর আর বিধবা শ্রেষ্ঠী কন্যা বিদূষী শুভংসুকার অব্যাখ্যাত প্রেমে অকস্মাৎ ছেদ ঘটে যখন জানা গেল শেখরের অন্ত্যজ পরিচয়। লেখক এই শেখর ছেলেটিকে একাধারে বুদ্ধিবৃত্তি আর প্রকৃতিলগ্ন কর্ষকের মিলিত রূপে গড়েছেন যার বর্ণ পরিচয় আছে কর্ম পরিচয়ে। ব্রাহ্মণের তৈরি বর্ণবাদের বিধানে কোটিবর্ষ নগরী-দিনাজপুরের বাণ গড়, থেকে বাস্তুচ্যুত হলেও নগর পরিখার ওপারে সংলগ্ন অকর্ষিত খিলভূমি বা কর্ষিত ক্ষেত্রভূমি আহবান জানায় শেখরকে। রাতে আকাশের তলায় সে নিঃসঙ্কোচে খোলে ভালোবাসার মানুষ শুভা দিদির প্রেমের পুঁটুলি, বেরিয়ে আসে একটার পর একটা উপহার। আপাত পরিণতিহীনতা অন্য মাত্রা পায় গল্পে।
ভদ্রা নামের চতুর্থ গল্পটার সময়কাল আরও দুশো বছর পর, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি। স্থান গান্ধার দেশ– আফগানিস্তান-উত্তর পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চল। আখ চাষের সমৃদ্ধ অঞ্চল। রামায়ণের পবিত্র ইক্ষ্বাকু রাজবংশের আর মহাভারতের গান্ধারীর স্মৃতিধন্য তথাগতের বিচরণভূমি, পাণিনির জন্মভূমি। অশোক আর কণিষ্কের ক্ষমতা বৃত্তে থাকা ঐতিহ্যশালী অঞ্চল। কনিষ্ক পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ প্রভাব কমেছে, মন্দিরে পুজো-আচ্চা বেড়েছে। শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে পাশেই কুষাণ আমলে বানানো এখন শ্রীহীন স্তুপ আর তথাগতের ধুলোমলিন মূর্তিতেও পেন্নাম ঠুকছে মানুষ। ব্রাহ্মণ আচার্যরা এই সর্বগ্রাহী পরিমণ্ডলে সহনশীল। এখন গান্ধার কাশ্মীরের রাজার শাসনে। এটা আন্তর্জাতিক বানিজ্যপথের অঙ্গ। পশ্চিমে তুরান-ইরান–তুরস্ক–আরব ভুমি আর পূর্বে থানেশ্বর–কনৌজ-মগধ। পশ্চিমে তুরান-ইরান-আরব থেকে থেকে ঘোড়া আর অন্য সামগ্রীর সঙ্গে একেশ্বরবাদের– ইসলামের আর তার দ্বিগবিজয়ের আবছায়া খবর আসে। যে পথে ঘোড়া আর অন্য সামগ্রীর লেনদেন হয় পূর্বের থানেশ্বর -কনৌজ -মগধের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে। লেখক বর্ণনা করেছেন ‘ অবিশ্বাস্য কিছু সন্দেশের কথা ’ (পৃষ্ঠা ৫৮) আর তা হল একেশ্বরবাদী ইসলামী দিগ্বিজয় নাকি সবাইকে সমান মনে করে, জাত ধর্ম মানে না আর তার ধর্মরথের চাকায় পৌত্তলিকতা আর পুরোনো ক্ষমতা প্রভাবকেন্দ্রের প্রতীক মন্দির-মঠ-বিহার-স্তুপ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, কচুকাটা হয় ব্রাহ্মণ-শ্রমণ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তিনি ‘সন্দেশ’ বললেন কেন? আক্রমণকারীর ক্ষমতার ভঙ্গিমা কি কারো সুসংবাদ-সন্দেশ হতে পারে? হয়ত রামচন্দ্র প্রামাণিক বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর প্রান্তবাসীদের দৃষ্টিতে দেখতে চাইছেন। সেসময়ের এই বর্গটাকে যে জুঙ্গিত-অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হতো এ আমরা জানতে পারছি এ গল্পে যার মধ্যে পড়ে চণ্ডাল, মেথর, ব্যাধ, মৎসজীবী, ঘাতক ও নর্তকরা। ‘এরা বাস করে গ্রামের বাইরে’ বলছেন লেখক। তাই তাঁর বর্ণনায় ইসলামের আক্রমণকারী বিভঙ্গ কি এই অংশের মানুষের কাছে সন্দেশ? ঠিক এর পরেই লেখক এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ কুলপতিদের ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়া ও অর্বাচীন জ্ঞানে তা খণ্ডন প্রক্রিয়া বর্ণনা করছেন। ব্রাহ্মণরা বলে: ইসলামের মানব সমতার ধারণা প্রকৃতিবিরুদ্ধ আর বিধবা বিবাহ পাপকর্ম। অর্থাৎ অনাগত ইসলামের প্রশ্নে লেখক তর্ক শাস্ত্রসম্মত পূর্বপক্ষ ও অপরপক্ষ বিচারে লিপ্ত এমনটা ধরা যেতে পারে। যেখানে প্রান্তবাসী অপর। কিন্তু লেখক কি এই আইডিয়ার প্রতর্কে পূর্বানুমান মুক্ত হতে পারেন? নতুন ধর্মের কথা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রেষ্ঠী জায়া ভদ্রা, তার জায়ের ছেলে বিম্বর মুখ থেকে শোনে তখন ‘তার (ভদ্রার) মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।’ অর্থাৎ ভদ্রার মনেও আগমনের ঔৎসুক্য থেকে আক্রমণের ভয় বেশি। এই গল্প যত এগোয় এই আক্রমণের বীভৎসার পূর্বানুমান আরবদেশের ধর্মের প্রতি ঔৎসুক্যে রূপান্তরিত হচ্ছে কারণ নারীর পুনর্বিবাহে ইসলামের সম্মতি, স্বামী বদলে নেবার অধিকারের বার্তা ভাবাচ্ছে একসময়ের স্বেচ্ছাচারী ভোগী এখন অক্ষম, স্বামীর কারণে সন্তানহীনতার দুঃখে কাতর ভদ্রাকে। সে বিম্বর সঙ্গে মিলিতও হতে চাইছে। আর অবশেষে হয়ত কোন এক কাম তাড়িত শ্রমণে উপগত হয়ে ভদ্রা হচ্ছে সন্তানসম্ভবা। কিন্তু কার সেই সন্তান কেউ জানতে পারছে না। এ গল্পটা সঙ্কলনের অন্যতম সেরা এক খোলামুখ টেক্সট। ঠিক ইসলাম পূর্ব এক ব্রাহ্মণ প্রভাবিত অথচ ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ প্রতিবেশের অনন্য চিত্রণ নারী মানস কেন্দ্রিক এ গল্প।
পঞ্চম গল্প ‘পূর্বাভাস’ একশো বছরের ব্যবধানের সময়কে ধরেছে। বৌদ্ধ রাজাকে সরিয়ে সিন্ধু প্রদেশে ক্ষমতা দখল করেছে ব্রাহ্মণ রাজা। সে কথায় কথায় বিধিবিধান ভাঙার অপরাধে বা আশংকায় কমজোরিদের শুলে চড়ায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রঙ্ক নিম্নবর্ণের মানুষ, তার অধিকার নেই বেদে। পশ্চিম দিক থেকে ইসলামের পদধ্বনির কানাকানি শোনা। দেশের ব্রাহ্মণ রাজা আপন ক্ষমতা আর ব্রাহ্মণ্যবাদি গুমরে বিভোর। রাজার এঁটো রঙ্ক ভাবছে পশ্চিমের সেই ধর্মকথা যে ধর্মে না আছে ব্রাহ্মণ না শূদ্র।
চতুর্থ ও পঞ্চম গল্প ইসলামের আগমনের বার্তাবহ প্রথমটা নারীর চোখে দ্বিতীয় টা শূদ্রের দৃষ্টিতে দেখা সময়ের কথা।
ষষ্ঠ গল্প ‘পতিত মিনারে’ সমান্তরাল দুটি বয়ান আছে একটা প্রথম পুরুষে জইফ নামের গজনীর সুলতান মামুদের এক অশ্বারোহীর। সে ছিল চণ্ডাল বালক টিয়োক, তারপর বিক্রি হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যোদ্ধা হয়ে এখন বিয়ে করেছে ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মেয়ে জমিলাকে। অন্যটা বয়ানটা সুলতান মামুদের নিজের যদিও তৃতীয় পুরুষে। শাহী বংশের রাজা জয়পালের পতন হয় মামুদের হাতে। সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এক প্রাচীন মন্দিরের আপনিই ভেঙে পড়ার রূপকের এক অতুলনীয় ব্যবহার করেছেন লেখক যা মন্দির ভাঙায় মুসলিম শাসকের প্রতিহিংসার মিথকেও ভাঙে। গল্প দেখায়, বিধর্মীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নয়, সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি লুটের লোভই সুলতান মামুদকে দেবস্থান আক্রমণে প্রলুব্ধ করছে যা তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনায় ছিল না আর সে কাজে তাঁর সলাহকার হয়ে যাচ্ছেন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত, জইফের শ্বশুর, রহমতুল্লা। এটা এক বহুস্তরীয় অনন্য মিথ ভাঙার গল্প যা মুসলমান আক্রমণের আশিরনখপদ বিশ্লেষণে বিশিষ্ট।
সপ্তম গল্প ‘উলট–পুরাণ’ আরো দুশো বছর পর এগারোশো বিরানব্বই। প্রথমেই ধাক্কা খেতে হয় মুহম্মদ ঘোরীর বিজয় পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনায় এই কটি বাক্যে: ‘রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এবার হেরে ভূত। রাজার ভাই দিল্লীর অধীশ্বর গোবিন্দরাজকে খতম করেছেন জামুঁ রাজকুমার নরসিংহদেব স্বয়ং। তাই মুসলিম-হিন্দু দু-তরফই খুশির জোয়ারে ভাসছে।’ দিল্লী সুলতান শাহী প্রতিষ্ঠায় জামুঁ রাজা যে ঘোরীর সহযোগী ছিলেন তা ইতিহাসের মিথ শেখায় না। এসব নিয়ে সাধারণের জীবনের দুঃখ হাসির মিশেলে এ কাহিনী।
অষ্টম, নবম আর দশম গল্পে সময় বিশেষ এগোয় না; বারশো তিন থেকে চুরাশি। ‘খোজা’ গল্পটা ঘোরী সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির কেল্লা ভেবে, উদন্তপুর বিহার আক্রমণের গল্প। ইতিহাসের মিথ এখানেও ভাঙা হয় কারণ লোকমান্য ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে বখতিয়ার নালন্দা বিহার আক্রমণ করেন সেটা যে উদন্তপুর এটা জানানোর জন্যই এ গল্প নয়। আসলে মুসলিম শাসনে ক্ষমতা কাঠামোয় অপর লিঙ্গের বা খোজাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। গল্পের এই খোজা মকবুল কিন্তু জয়ী পক্ষে থেকেও সবসেরা লুটের মাল- অবমানিত নারীদের মনের খোঁজে থাকে। জান্নাতের দরওয়াজা গল্পটা চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে বোখারা থেকে তাড়া খাওয়া মানুষের গল্প। এই গল্প সিন্ধু নদী পার হলেই যে মঙ্গোলদের থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, অসহায় মানুষের সেই হিন্দুস্থানে আসার গল্প। বিপদ সংকুল পথে এরশাদ আর নাদিরা দুই ক্রীতদাস স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে, নিকাহর স্বপ্ন। অবশেষে তারা পৌঁছয় সিন্ধুর অপর পারে, হিন্দুস্থানের সুলতান একসময়ের গোলাম শামসুদ্দিন ইলতুৎমিসের এলাকায় আসতে পারে না মঙ্গোলরাও।আব্দুল্লাহ গল্পটাও সুলতান বলবানের সময় মঙ্গোল আক্রমণ কালে এক সীমান্ত বর্তী কেল্লার ক্রীতদাসের স্বাধীন এক মানুষ হয়ে ওঠার গল্প, প্রেমের বাদশা হয়ে ওঠারও বটে।
একাদশতম গল্পের সময় চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে, নাম ‘কুমকুম’– জাফরান যা একমাত্র কাশ্মীরেই পাওয়া যায় আর রাজা রাজড়াদের ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট। শূদ্র দিবির সেই মহার্ঘ জাফরানের বাহক হতে পারে কিন্তু গ্রাহক হওয়া নেই তার কপালে। কাশ্মীর রাজ দাসী রমন্যার সঙ্গে প্রেম তার কিন্তু ব্রাহ্মণদের বিধানে বিয়ের পথে কাঁটা তার শূদ্র পরিচয়। সে জাফরানের কৌটো নিয়ে যায় রানী কোটার আরেক বিয়েতে যা হবে শাহ মীরের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় না। রানী আত্মহত্যা করেন নানা পালাবদলের আসর শ্রীনগর রাজপ্রাসাদ যাচ্ছে শাহ মীরের- সুলতান সামসুদ্দিনের কব্জায়। যারা মুসলমান হবে তারা থাকবে সেখানে। প্রেমিকা দিবিরকে বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে, তাহলে শূদ্র ও দাসীর মেয়ের বিয়ের পথের কাঁটাও দূর হবে। কে যেন জাফরানের কৌটোটাও ফিরিয়ে দিয়েছিল দিবিরের হাতে। সে কি জাফরানের গ্রাহক হবে?
দ্বাদশ গল্পের নাম ‘উম্মি’, সময় দু’শো বছর পর। বাবর তখন হিন্দুস্থানের বাদশা। তাঁরই এক সেপাই আফতাব। সে হিন্দুস্থান জেতার যুদ্ধে লুটের বখরা পেয়ে খুশিতে কিনে ফেলে এক বাঁদিকে নাম তার উর্মিলা। বাঁদি হলেও মেয়েটার সংস্কৃতে জ্ঞান আছে। ফার্সি জানা আফতাব তার প্রেমে পড়ে, সে হয় তার আদরের উম্মি। এই সাধারণ সেপাই আর তার বাঁদির প্রেম নিয়ে এ গল্পের ছলে লেখক এক পরিশীলিত যৌথ যাপনের কথা বলেন যার মুলে আছে সংস্কৃত আর ফার্সির আদানপ্রদান। সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণন, মোঘল রণকৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব, রাজপুতের একবগ্গা বীরত্ব আর জওহর ব্রতের নিঠুর সংকল্পের বিপ্রতীপে প্রেমের -জীবনের বোধ। গঙ্গা যামুনি তেহজিবের - হিন্দুস্থানের মিশ্র সংস্কৃতির সার্থক ভাষ্য এ গল্প।
ত্রয়োদশ গল্পটার নাম ‘পোস্তপানি’। সময় ষোলোশো উনসত্তর। ঔরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনকালের প্রথম দিক। প্রেক্ষাপট মথুরা সংলগ্ন জাট অঞ্চল। লেখকের মতে ঔরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনকাল মুসলিম ঘেঁষা (হিন্দু বিরোধী) শাহী নীতির জন্য কুখ্যাত।এ প্রশ্নে লেখক ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ায় নেহরুর অবস্থান পুনরাবৃত করেছেন মাত্র, যার মুলে আছে আকবর ভালো আর ঔরঙ্গজেব খারাপ এমন এক অবস্থান। নেহরুর এই চরম অবস্থান কলোনি প্রভু ইংরেজদের ইতিহাস সলাহকারদের মতের সঙ্গে কতটা প্রতর্কে লিপ্ত হয়েছে সেও প্রশ্নের উর্ধে কি? পোস্তপানি হল মোঘল শাসনকালে দুর্গে ব্যবহৃত রাজবন্দীদের ধীরে ধীরে মারার মৃদু বিষ। সেই রূপকের আধারে জাট যুবকের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের প্রেম-বিয়ে আর সেসময়ের জাট ভূস্বামীদের নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় সামরিক শক্তি মোঘল ফৌজদারের সঙ্গে স্থানীয় বাহিনীর সংঘর্ষ আর তাতে লিপ্ত উভয়পক্ষের মানুষকে লেখক পোস্তপানির মৃদুবিষ মাদকে আসক্ত মৃতপ্রায় কারাবন্দীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাক আধুনিকতায় এই তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কতটা অস্তিত্ব ছিল? ঔরঙ্গজেব আলমগীর কি সত্যিই মোঘল রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সুল-ই-কুল বা সবার জন্য শান্তি -সুস্থিতির চরম বিরোধিতা করে দীর্ঘকাল শাসন করলেন? গল্পে বিধৃত বাস্তব, প্রকৃত বাস্তবের কতটা কাছাকাছি এ জানার আক্ষেপ নিয়ে যেন লেখাটা শেষ হয়।
চতুর্দশ গল্পটার নাম ‘ব্যাধি’, সময় সতেরোশো পঁয়ষট্টি, নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর বছর। মোঘল শাহী কেন্দ্র দুর্বল, সমৃদ্ধ সুবে বাংলা স্বাধীন মতে চলে, লাম্পট্যে অভিযুক্ত শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পতন, বর্গী হানা, ফিরিঙ্গীর লুট অব্যাহত, যে লুটের ফল হবে মন্বন্তর, কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত পুতুল নবাব মীরজাফর, তাঁর ছেলে অত্যাচারী মীরণ মারা গেছে। শেষশয্যায় নবাব মা কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত খেতে চেয়েছেন। সেই চরণামৃত নিয়ে যাচ্ছে দুর্গাদাস যার প্রথম পক্ষের বউ দয়াময়ীকে ধর্ষণ করেছিল বর্গীরা তার পর সে প্রথমে ত্যাজ্য ও পরে নিরুদ্দেশ হয়। দুর্গাদাস দীর্ঘ যাত্রার পর নবাবকে চরণামৃত নিজের হাতে খাইয়ে আসার সময় আবার ফিরে পায় হারিয়ে যাওয়া দয়াময়ীকে। সে তখন হয়েছে মুর্শিদাবাদের নবাবের জেনানার বাঁদি। সেই দুর্গাকে বলে নবাবের কুষ্ঠ ব্যাধির কথা, যে ব্যাধিতে যেন গোটা সুবে বাংলাই আক্রান্ত, নেই কোন মুক্তি তার। এক অদ্ভুত বিষাদাচ্ছন্ন টেক্সট। ধর্মাধর্ম সব মূল্যবোধ যেন কলোনির যূপকাষ্ঠে, ফিরিঙ্গী লুটের যজ্ঞে সমর্পিত হয়েছিল বড় বেশি মানবিক হননের মূল্যে।
পরের তিনটে গল্প চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাকাপোক্ত বনেদে গাঁথা ফিরিঙ্গী ইংরেজের অধীন বাংলার কথা। ‘আগুন খাকি’ গল্পে ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপাদাপি নির্ভর কৌলীন্য, বালিকা বিবাহ, সহমরণের কুপ্রথার যুগে নারীর আর্তনাদ শুনিয়েছেন লেখক। ‘দাস–দাসী সংবাদ’ গল্পে দেখা যাচ্ছে কলকাতার কড়চা। কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্তে কিছু লোক টাকা কামাচ্ছে, ইংরিজি বুলির ফুট ফুটানিও শোনা যাচ্ছে, কিছু লোক সাহেবের কুঠির কাজে লেগেছে আবার এরই সঙ্গে চলতে থাকে দাস ব্যবসা, সেই দাসেদের ওপর যৌন শোষণ। ‘সাগরে’ গল্পটা প্রথম পুরুষে লেখা। কথক মহিলা, লেখক কি আধুনিকতার আবাহন করলেন যেখানে সেলফ-ব্যক্তির উন্মোচন, সেখানেই কি আধুনিকতার শুরু নয়? গল্পটা নৌকাডুবির, এক বিধবার শূন্যতার অথবা এক পরার্থবাদী প্রেমিকের গল্প? নারী স্বর এ গল্পে স্পষ্ট, তার বাঁচার আর্তি নিয়ে তীব্রতম। হয়ত সাগর নামকরণের মধ্যে আধুনিক মননের, প্রেমিক মননের, পরার্থবাদী মননের, সব হারানোর নৌকাডুবির পরও এক অনাগত জাতীয়তাবাদের নতুন দ্বীপে উত্তরণের বার্তাই দিয়েছেন লেখক দিনের শেষে, যে সময়ের মহাসাগরের মুখোমুখি দাঁড়াবে।
অষ্টাদশ গল্পটার পর রামচন্দ্র প্রামাণিক লিখলেন “ ‘স্বাধীনতা’ শীর্ষক স্বর্গারোহণকথা সমাপ্ত।” এখানে স্বাধীনতা উদ্ধৃতি কণ্টকিত, পরম জাতীয়তাবাদে আক্রান্ত মনন কি এই উদ্ধৃতি দিত? তার মানে কি দাঁড়াল যে লেখক শেষ করছেন প্রশ্ন চিহ্নে? কিন্তু কেন? শেষ গল্পটা শুরু হয়- এটা যে গল্প নয় এই আভাসে। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, লেখক তাঁর স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে এক নিম্নবর্গের মানুষের কথোপকথনের হুবহু অনুলিপি তুলে দেন সেখানে স্বাধীনতা মানে রেডিওবাহী এক বার্তা। গোটা বইটায় ক্লাসিক্যাল মহাভারতের অঙ্গে ইতিহাস ছেঁচা চূড়ান্ত পরিশ্রমী এক ডিস্কভারির-আবিষ্কারের বিশিষ্ট প্রয়াসে গিয়ে এই বেপথু চলনকে কী রূপে দেখব সেটা ভাবতে গিয়ে নজর করলাম, এখানেই শেষ কথা নয় স্বর্গারোহণকথার মহাভারতসুলভ অভ্যাসের পরও অতিরিক্ত একটা সর্গ যুক্ত করেছেন আমাদের লেখক, তার নাম খিল কথা। যা শুরুও হয় এই উক্তি দিয়ে ‘এই জগতে আমি গরুর তুল্য কোন ধন দেখিতে পাই না।’ বলাই বাহুল্য উক্তিটা মহাভারতের আর গল্পের, খিল কথার, নাম গোধন। পড়তে শুরু করে দেখি, আরে এযে এক্কেরে লালি আর কালি দুই গরুর গল্প, গোবরের গন্ধ মাখা গোয়ালে ধীরেন আসে সাঁজাল দিতে, ধুনো লাগাতে যাতে মশার উৎপাতে গরুগুলো বিরক্ত না হয়। বাকি শুধু নেই কথা। কিছুই অবশিষ্ট নেই চাষীর; জমি নেই, পরিবেশ নেই, প্রতিবেশ নেই, নেই অর্থ বল আর তাই গোয়ালের গোধন বিক্রি করে সেই পয়সায় মাংস খাওয়া চলে। সেকি ওই গরুরই মাংস? নানা আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার অন্তে এই কল্পনায় অর্গলমুক্ত অনন্য মহাকাব্যপম সর্গবন্ধ রচনা করেও যে এক আত্মধ্বংসী বস্তু জগতের, এক অভাগা দেশের করুণ পরিণতির পানে তাকিয়ে থাকাটার থেকে মুক্তি স্বর্গারোহণেও নেই হয়ত সে কথাটাই রামচন্দ্র প্রামাণিকের খিল কথা।
বই: আবহমান ভারতকথা
লেখক: রামচন্দ্র প্রামাণিক
প্রকাশক: অনুষ্টুপ
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 পাঠক | 165.225.***.*** | ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ২০:০৭737404
পাঠক | 165.225.***.*** | ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ২০:০৭737404- পড়ার ইচ্ছে রইল, তার সাথে অন্য পাঠকদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)
(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)
(লিখছেন... lcm, Bratin Das, সেই এক)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... গুগুস, aranya, রঞ্জন)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।















