- বুলবুলভাজা ইস্পেশাল উৎসব ইস্পেশাল

-
নবান্ন, গাজা থেকে বাংলার দুর্ভিক্ষ কীভাবে মিলে মিশে গেছে
সুমন সেনগুপ্ত
ইস্পেশাল | উৎসব | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৮৯১ বার পঠিত - অবিস্মরণীয় নজরুল | বাঙালি বিদ্বেষ ও পরিচিতি নির্মাণের রাজনীতি | সোনম ওয়াংচুক: গণতন্ত্র কি শুধুই কাগজে-কলমে? | নবান্ন, গাজা থেকে বাংলার দুর্ভিক্ষ | দুই ঘর | সমসাময়িক | ফ্লোটিলা | ঢাকের দিনে ঢুকুঢুকু | দু-প্যান্ডেলের মাঝখানটায় | সুন্দরী কমলা নাচে রে | কাশী বোস লেনের পুজো : লড়াইয়ের হাতিয়ার | অস্তিত্ত্ব | শালপাহাড়ের গান | পুজোর দিনগুলি | অপেক্ষা-দিন | ভোলুরামের হাঁচি ও মত্তের উৎসব | এ অবধি আঠারো | মিনিবাসে গদার | জালিকাটু | তিনটি কবিতা | সাত সেতুর সাতকাহন | ফ্রান্স - একটি অবতরণিকা | শারদীয়া | বালিকা ও ইস্ত্রিওয়ালা | তিনটি কবিতা | গগন | যে জীবন গেঁড়ির, গুগলির | লা পাতা | দু’টি কবিতা | ধাতব পাখিটি একা | নিষিদ্ধ গন্ধ ছড়িয়েছে হাসনুহানা বলে | তিন ঋতুর কবিতা | গ্যেরনিকা | "এই জল প্রকৃত শ্মশানবন্ধু, এই জল রামপ্রসাদ সেন।" | ছায়া দুপুর | আমাদের ছোট নদী (২) | শারদ অর্পণ ২০২৫ | আমি হিটলারের বাবা | হিমাংশু ও যতীনবাবুদের খবরাখবর | যে চোখে ধুলো দেয় তার কথা | লক্ষ্মীর ঝাঁপি | ত্রিপুরায় পিরামিড রহস্য | এবং আরো শিউলিরা | উৎসব সংখ্যা ১৪৩২
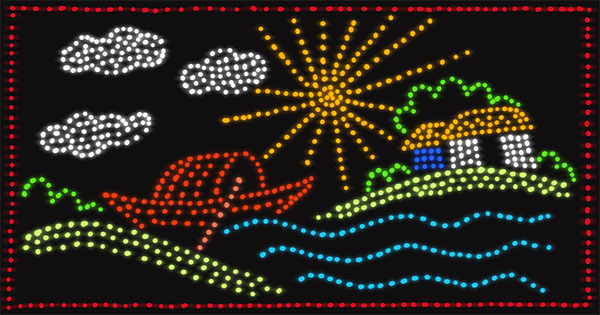
অলংকরণ: রমিত
কলকাতার পুজো এখন আর শুধু পুজো নয়, কলকাতার পুজো এখন একটি শিল্পকর্মের নিদর্শন ও বটে। কলকাতা এখন এই পুজোর সময়ে একটা চলমান আর্ট গ্যালারি হয়ে উঠেছে। কোনও প্রবেশমূল্য ছাড়াই সমস্ত ধরনের মানুষ এই পুজোর শিল্প উপভোগ করছেন। বেশ কিছু পুজো সংস্থা এবার পুজো আক্ষরিক অর্থে শুরুর আগেই একটি বিশেষ প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করেছে যাতে মানুষজন শিল্পীদের কাজ দেখতে পারেন। সেই পুজোগুলোর অন্যতম একটি বেহালা ফ্রেন্ডসের পুজো, যা দেখতে গিয়ে চমকে উঠবেন অনেকেই। পুজোর ভাবনা – ‘নবান্ন’- যুদ্ধ, ক্ষত আর ক্ষুধা। মূল শিল্পী প্রদীপ দাস। কলকাতার বেহালা অঞ্চলের শিল্পী সংগঠন ‘চাঁদের হাট’ কালেক্টিভের অন্যতম সদস্য প্রদীপ কলকাতার নানা প্যান্ডেলে ইতিমধ্যেই দেশভাগ ও তার যন্ত্রণা নিয়ে একাধিক কাজ করেছেন। দক্ষিণ শহরতলির বেহালা ফ্রেন্ডস এবার যে চমক দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে মানুষের মননে ভাবনার সঞ্চার করবে।

যুদ্ধে কে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাঁরা যুদ্ধ করে তাঁদের গায়ে কি এতটুকুও আঁচ লাগে? যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হয়, খাবারের সঙ্কট দেখা দেয় যখন মাথা গোঁজার একটা ছোট্ট ঠাঁই নিজের চোখের সামনে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যায়, তখন হয়তো কিছু মানুষ তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে টিভি বা মোবাইলের পর্দায় উপভোগ করেন, কিন্তু ঐ মানুষদের মনে এবং শরীরের ওপর কী প্রভাব পড়ে, তার আন্দাজ কি আমাদের আছে? নিমা হাসান নামে এক কবি তাঁর সাত সন্তান নিয়ে মাথার ওপরের ছাদ কিংবা একটু খাবার না পেয়ে প্যালেস্টাইন থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়ে কবিতায় প্রকাশ করেন আর প্যালেস্টাইনেরই থিয়েটার কর্মী রিয়াদার গলায় যখন অ্যারাবিক ভাষায় শোনা যায়, ‘প্রতিদিনকার রুটি বানানোর কাজ আর এই দেশে নেই’ তার সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যায় আমাদের দেশের এই বাংলার ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ছবিটি। একজন মা তাঁর সন্তানকে কোলে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরছেন একটু খাবারের সন্ধানে, জীর্ণ, ক্লান্ত দেহে আর ভেসে আসছে ‘ফ্যান দাও... ফ্যান দাও...’। কোথায় যেন ২০২৫ সালের গাজা আর ১৯৪৩ সালের বাংলা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।
বেহালা ফ্রেন্ডসের নবান্ন ভাবনা সেইখান থেকেই শুরু। মণ্ডপে প্রবেশের একদিকে লেখা ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ অনেক মানুষের বাঁচার আর্তি নিয়ে ঐ লেখাও বহু মানুষের লেখার সমাহার আর উল্টোদিকে ‘কোকোকোলা’র ফন্ট দিয়ে লেখা Genocide বা গণহত্যা। এই ফন্ট ব্যবহারেরও একটা কারণ আছে। এই বহুজাতিকরাই তো এই গণহত্যাগুলোকে পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এরপরে মণ্ডপের দ্বিতীয় অংশ। বুলেটের ক্ষত স্পষ্ট হয়ে আছে দেওয়ালে তাও আতস কাঁচ রাখা আছে, ইন্সটলেশনের অঙ্গ হিসেবে যাতে আরও বড় করে বোঝা যায় ক্ষত কত গভীরে। তার পিছনেই একটা ছোট্ট ছিদ্রের পিছনে দেখা যায় একটি পিয়ানো যেন জার্মানির গণহত্যার সময়ের প্ররিপ্রেক্ষিতে লেখা লুকোনো আছে ছোট আনা ফ্রাঙ্কের পিয়ানো। শিল্পী প্রদীপ দাসের ভাবনায় এই পিয়ানোটি যেন ২০০২ সালের পোলিশ চলচ্চিত্রকার রোমান পোলান্সকি’র ‘দি পিয়ানিস্ট’ ছবির লুকিয়ে রাখা পিয়ানো। সব কেড়ে নিলেও সব হারিয়ে গেলেও কীভাবে তা যেন থেকে যায়, বেঁচে ওঠে ধ্বংসস্তুপ থেকে।

এরপরেই আসে পঙ্গপাল আর তার সঙ্গেই আসে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা। বাংলার মাটি এতো উর্বর এতো শষ্যশ্যামলা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসক এবং কিছু মুনাফাখোর কতিপয় মানুষ এবং অবহেলার কারণে বাংলার মানুষের এত দুর্দশা হয়েছিল, সেটাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে মন্ডপের তৃতীয় অংশে। সেই স্মৃতিকে ধরে রেখেছিলেন ঐ সময়ের শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকারেরা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা, বিজন ভট্টাচার্যের নাটক, সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ এবং জয়নুল আবেদিনের ছবিতে উঠে এসেছে ঐ সময়ের ছবি। সেই ছবি, কবিতা এবং নাটকের অংশই খন্ড খন্ড ভাবে আবার নতুন করে উঠে এসেছে শিল্পী প্রদীপ দাস এবং অন্যান্য সহযোগী শিল্পীদের তুলিতে। গত তিনমাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়কার মানুষের হাহাকারের ছবি মিলে গেছে আজকের গাজার বেঁচে থাকা কিছু মানুষের আর্তির সঙ্গে।
সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিক বিজয় প্রসাদ ২০২৫ সালের একটি লেখায় লিখেছেন কিছুদিন আগে অর্থাৎ ২০২৪ সালে যত মানুষ গাজায় বেঁচেছিলেন, তাঁদের যে ক্ষুধা আজ সেই সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ যে খাদ্য গাজায় তৈরী হতো, তা কিন্তু গাজার সমস্ত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার মানুষ না খেতে পেয়ে শুতে যান রোজ। সেই সময়ের বাংলার মানুষের অবস্থাও অনেকটা আজকের গাজার সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যায়। ১৯৯৫ সালে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন লিখেছিলেন বাংলার দুর্ভিক্ষ কিন্তু খাবারের অপ্রতুলতার জন্য হয়নি, হয়েছে খাবারের অসম বন্টন এবং কিছু মানুষের লোভের কারণে। কিছু মানুষের আয়ের সঙ্গে বেশীরভাগ সাধারণ মানুষের আয়ের এতটাই বৈষম্য ছিল যে একদিকে মজুতদারেরা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল আর অন্যদিকে জীর্ণ শীর্ণ সন্তান কোলে মায়েরা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন একটু খাবারের খোঁজে।
হতে পারে গাজার সঙ্গে বাংলার ভৌগলিক দূরত্ব হয়তো ৫০০০ কিলোমিটার সময়ের ফারাক হয়তো ৮০ বছরেরও বেশী, কিন্তু কোথায় যেন দুই দেশের সাধারণ মানুষের আর্তি মিলে মিশে গেছে আর এই মেলানোর কাজটাই করেছেন শিল্পী প্রদীপ দাস। জর্জ ওরওয়েল একসময়ে লিখেছিলেন, যাঁরা যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার চালান, যাঁরা যুদ্ধ চায়, তাঁরা কি যুদ্ধে যায়? তাহলে কার জন্য এই ধ্বংসলীলা রচনা করা হয়? ১৯৯৫ সালে মহাশ্বতা দেবী লিখেছিলেন, ইতিহাস শুধু রাজা রাজড়ার শৌর্য, বীর্যের কাহিনী নয়, ইতিহাস মানুষের ঘাম, রক্তের ও শ্রমেরও ইতিহাস। মানুষের প্রতিদিনকার বাঁচার কথাও বলে ইতিহাস। সেই জন্যেই বিজন ভট্টাচার্য তাঁর ‘নবান্ন’ নাটকে ঐ মানুষদের কথাই তুলে এনেছিলেন, বলেছিলেন ‘আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাই নি, আমরা মৃতদেহের ওপর আমাদের ঘর তৈরী করেছি’’।
বেহালার এই মণ্ডপ আমাদের ঐ স্মৃতিকে শুধু উস্কে দেয় না, আমাদের ভাবনার খোরাক ও দেয়। সেই জন্যেই দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়ালে খুঁজে পাওয়া যায় ঐ সময়ের প্রতিচ্ছবি। তবে তার মধ্যেও আশার কথা থাকে, তার মধ্যেও বাঁচার কথা থাকে। শুভ- অশুভের দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে উঠে আসে আর এক মাতৃমূর্তি। কোথায় যেন মিলে যান গাজার নিমা হাসান এবং বাংলার ঐ সময়ের মায়েরা। দূরত্ব বা সময়ের ফারাক থাকে না। এই মণ্ডপকে কেউ যদি শুধু গাজা বা প্যালেস্টাইনের আদপে তৈরী কাজ বলেন, সেটাও যেমন ভুল হবে আবার শুধু ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়কে ধরা হয়েছে বলেন, সেটাও ভুল হবে। স্থান, কাল পাত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে বাঙময় হয়ে ওঠেন এক নারী শিল্পী প্রদীপ দাসের কৃতিত্বে। ছবি, কবিতা, গানের সংমিশ্রণে কলকাতা দেখতে পায় ৫০০০ কিলোমিটার দূরের প্রতিবেশীকে। একাত্ম বোধ করে ৮০ বছর আগের এক মায়ের সঙ্গে। নবান্ন মানে তো বেঁচে থাকার উৎসব, নবান্ন মানে তো খাদ্যের উদযাপন।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।অবিস্মরণীয় নজরুল | বাঙালি বিদ্বেষ ও পরিচিতি নির্মাণের রাজনীতি | সোনম ওয়াংচুক: গণতন্ত্র কি শুধুই কাগজে-কলমে? | নবান্ন, গাজা থেকে বাংলার দুর্ভিক্ষ | দুই ঘর | সমসাময়িক | ফ্লোটিলা | ঢাকের দিনে ঢুকুঢুকু | দু-প্যান্ডেলের মাঝখানটায় | সুন্দরী কমলা নাচে রে | কাশী বোস লেনের পুজো : লড়াইয়ের হাতিয়ার | অস্তিত্ত্ব | শালপাহাড়ের গান | পুজোর দিনগুলি | অপেক্ষা-দিন | ভোলুরামের হাঁচি ও মত্তের উৎসব | এ অবধি আঠারো | মিনিবাসে গদার | জালিকাটু | তিনটি কবিতা | সাত সেতুর সাতকাহন | ফ্রান্স - একটি অবতরণিকা | শারদীয়া | বালিকা ও ইস্ত্রিওয়ালা | তিনটি কবিতা | গগন | যে জীবন গেঁড়ির, গুগলির | লা পাতা | দু’টি কবিতা | ধাতব পাখিটি একা | নিষিদ্ধ গন্ধ ছড়িয়েছে হাসনুহানা বলে | তিন ঋতুর কবিতা | গ্যেরনিকা | "এই জল প্রকৃত শ্মশানবন্ধু, এই জল রামপ্রসাদ সেন।" | ছায়া দুপুর | আমাদের ছোট নদী (২) | শারদ অর্পণ ২০২৫ | আমি হিটলারের বাবা | হিমাংশু ও যতীনবাবুদের খবরাখবর | যে চোখে ধুলো দেয় তার কথা | লক্ষ্মীর ঝাঁপি | ত্রিপুরায় পিরামিড রহস্য | এবং আরো শিউলিরা | উৎসব সংখ্যা ১৪৩২ - আরও পড়ুনউৎসব সংখ্যা ১৪৩২ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনএবং আরো শিউলিরা - অনুরাধা কুন্ডাআরও পড়ুনলক্ষ্মীর ঝাঁপি - দময়ন্তীআরও পড়ুনযে চোখে ধুলো দেয় তার কথা - কেকেআরও পড়ুনআমি হিটলারের বাবা - রঞ্জন রায়আরও পড়ুনছায়া দুপুর - শ্রাবণীআরও পড়ুনফেয়ারওয়েল - Manali Moulikআরও পড়ুনগ্যেরনিকা - অমর মিত্রআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 kk | 2607:fb91:4c1f:77b8:491d:9681:1543:***:*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৩:০৯734504
kk | 2607:fb91:4c1f:77b8:491d:9681:1543:***:*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৩:০৯734504- খুবই ভালো লাগলো। ডেকোর গুলো অসাধারণ!
-
শ্রীমল্লার বলছি | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৩:৩৯734506
- দারুণ!

 aranya | 2600:1001:b003:5cc8:690c:475a:9d54:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ০৬:২৪734514
aranya | 2600:1001:b003:5cc8:690c:475a:9d54:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ০৬:২৪734514- ভাল ও জরুরী লেখা
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।














