- বুলবুলভাজা আলোচনা রাজনীতি সিরিয়াস৯

-
স্লোগানেই আত্মসমর্পণের জন্মদাগ
সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোচনা | রাজনীতি | ১৪ আগস্ট ২০২০ | ৭৭৫৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 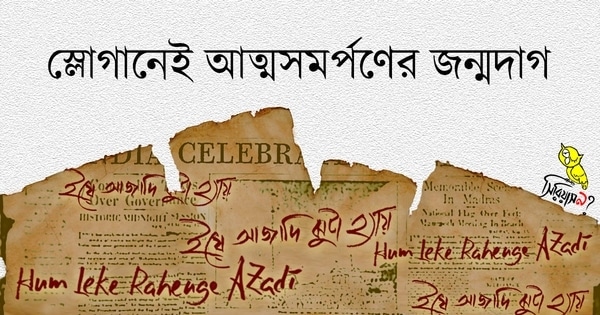
ব্রিটিশ পরবর্তী ভারতে আজ পর্যন্ত যতগুলি ‘আজাদি’র স্লোগান উঠেছে, তার প্রতিটিরই জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গী হল আয়রনি। এর মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়" তো প্রবাদপ্রতিম। স্লোগানটি গোটা ভারতে এতটিই জনপ্রিয় (ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুই অর্থেই) হয় যে, সত্তর বছর পরেও মানুষ সেটিকে মনে রেখেছেন। এবং এখানে অব্যর্থ আয়রনিটি এই, যে, হিন্দি ভাষায় উচ্চারিত এই স্লোগানটির জন্মই হয়েছিল হয়েছিল এককেন্দ্রিক ভারত রাষ্ট্র তথা হিন্দির আধিপত্যের বিরুদ্ধতা করে।
সমস্ত ‘আজাদি’র জননী এই স্লোগানের প্রেক্ষিত, ১৯৪৮ সালের। দেশভাগের পর কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস বসে কলকাতায়। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিনফর্ম তখনও বেঁচে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিনফর্ম সে সময় ভারতবর্ষকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবেই দেখত। প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করা হত। ১৯৪৬ সালের উত্তাল সময়েই পার্টির সম্পাদক পিসি যোশি "জাতীয় বিধান সভাগুলির সম্পূর্ণ এবং সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব"-এর কথা বলেছিলেন। বলাবাহুল্য ‘জাতীয়’ শব্দের অর্থ ছিল রাজ্যের বিধানসভাগুলি। গোটা দেশের সংবিধানসভা উল্লেখ করতে গিয়ে যোশি ‘সর্বভারতীয়’ শব্দটি ব্যবহার করেন। গোটা ভারতকে বাম-বুলিতে তখনও একটি ‘জাতি’ ভাবা হতনা (শব্দের অর্থ কীভাবে কালানুক্রমিক ভাবে পিছলে যায়, এর থেকে তার যথোপযুক্ত উদাহরণ বোধহয় আর হয়না)।
১৯৪৮ সালে যোশিকে সরিয়ে শুরু হয় রণদিভে জমানা। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও "সমস্ত জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং বিচ্ছিন্নতার অধিকার"-এর সজোর ঘোষণা করে। ভারতে বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষের প্রথম পর্ব শুরু হয়। তেলেঙ্গনায় রাজাকার এবং নিজামের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয় সিপিআই। পরে ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করলে তাদের বিরুদ্ধেও শুরু হয় গেরিলা যুদ্ধ। গোটা ভারত জুড়ে নেওয়া হয় 'সক্রিয় প্রতিরোধ' কর্মসূচি। “ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়” -- এই অগ্নিগর্ভ সময়ের স্লোগান।
ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়ে গেলেও, এই স্লোগান কিন্তু কার্যত দু-বছরের বেশি টেকেনি। অভ্যুত্থানপন্থী বনাম সংবিধানপন্থী (পড়ুন চিনপন্থী বনাম কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতাপন্থী) দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে পার্টি প্রায় দুটুকরো হবার উপক্রম হলে ১৯৫০ সালে স্বয়ং স্তালিন মস্কোয় দুই গোষ্ঠীর নেতাদের ডেকে পাঠান। বাম দিক থেকে রাজেশ্বর রাও এবং ডানদিক থেকে ডাঙ্গে মস্কো যান। সঙ্গে ছিলেন বাসবপুন্নাইয়া এবং অজয় ঘোষ। স্তালিন তেলেঙ্গানার যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেন। এবং রণদিভের জমানা শেষ হয়ে যায়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের লাইনকে ‘হঠকারী অতিবাম’ আখ্যা দেওয়া হয়। যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে এই স্লোগানের আয়ুষ্কালও শেষ হয়। রণদিভেকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও বাদ যান তিনি। আবার ফেরত আসার জন্য তাঁকে দীর্ঘ ৬ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৫১ সালে রাজেশ্বর রাওয়ের বদলে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন ডাঙ্গে।
উল্লেখ্য, যুদ্ধের লাইন পরিত্যক্ত হলেও, ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে পার্টির মত কিন্তু বদলায়নি। মোহিত সেনের লেখায় পাওয়া যায়, স্তালিন ভারতবর্ষকে বহুজাতিক যুক্তরাষ্ট্র হিসেবেই ভাবতেন। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে নয়। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু হয়ে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হয়নি। কমিনফর্ম তখনও টিকে। সোভিয়েতের ভারত-বিশেষজ্ঞ দিয়াকভের "জাতীয়তার প্রশ্ন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ" নামক রচনাটিই ১৯৫৩ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিনফর্মের দৃষ্টিভঙ্গির দলিল। ১৯৪৮ সালের ওই লেখায় দিয়াকভ লেখেন, যে, "ভারতের কোনও সাধারণ ভাষা বা সাধারণ জাতীয় চরিত্র নেই", যে কারণে গোটা ভারতকে একটি জাতি হিসেবে ধরা যায় না। নানা জাতির মধ্যে সাধারণ যে মিলগুলি আছে, সেগুলি ইউরোপের বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলের থেকে বেশি কিছু নয়।
একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, কথাগুলি উপর-উপর বলে দেওয়া। ভারত সংক্রান্ত বিশ্লেষণে দিয়াকভ বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন। ভারতের পূর্ণাঙ্গ জাতিগুলির একটি তালিকা বানান তিনি। তালিকাটি এইরকম: পূর্ব ভারতে বাঙালি, অসমিয়া, ওড়িয়া; পশ্চিম ভারতে গুজরাতি, মারাঠি; দক্ষিণে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লম। যাদের পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠবার পথে, তারা হল হিন্দুস্তানি এবং পাঞ্জাবি। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা জাতিগুলি, দিয়াকভ লেখেন, অন্যান্যদের চাপে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে। বাংলাকে নিয়ে দিয়াকভের বিশেষ আগ্রহ ছিল, দুই বাংলার মিলনের জন্য উন্মুখ ছিলেন। ভারত এবং পাকিস্তান, দুই পক্ষেরই বাংলাকে নিয়ে সমস্যা হবে, দেশভাগলগ্নে লেখেন দিয়াকভ। এবং ১৯৫২ সালে ভারত এবং পাকিস্তান, দুই সরকারকেই তিনি দায়ী করেন, সংকীর্ণ স্বার্থে উভয় বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জিইয়ে রাখার জন্য। দিয়াকভের স্পষ্ট মত ছিল, এরা বাংলার ‘জাতীয়’ আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকারের পথ ধরেই রক্তে ডুবিয়ে দিতে চায় (পরবর্তীতে ৬৯ এবং ৭১-এ উভয় বাংলাই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা প্রমাণ করে)। বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে ওই ৫২ সালেই দিয়াকভ লিখেছিলেন, যে, উনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল দিয়ে চলেন। কারণ? এখন অবিশ্বাস্য মনে হলেও এগুলি দিয়াকভের নিজের লাইন: কারণ তিনি "মারওয়াড়িদের হাতের পুতুল"(stooge of the Marwaris)।
এখন অবিশ্বাস্য লাগলেও এতে আশ্চর্য হবার আসলে কিছু নেই। কারণ তৎকালীন পার্টির বক্তব্যও অন্যরকম কিছু ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি চালু করার। ছাত্র ফেডারেশন তখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। ‘ইয়ং গার্ড’-এ তখন সোচ্চারে লেখা হচ্ছে, আন্দোলনের বর্শামুখ দুই শত্রুর দিকে: হিন্দি ভাষা এবং মারওয়াড়ি পুঁজিপতি। ‘দ্য কমিউনিস্ট’-এ লেখা হচ্ছে "রাষ্ট্রভাষার দাবি আসলে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ"। দিয়াকভ নিজেও রীতিমত নাম করে লিখছেন, কেন্দ্রের হাতে বিপুল ক্ষমতা এলে বিড়লা-ডালমিয়াদের উপকারে লাগার জন্য। সমস্ত ভাষাকে সমানাধিকার না দিয়ে হিন্দি-ইংরিজিকে রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে গুজরাতি-মারওয়াড়ি শিল্পপতিদের আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে, দুয়ের লক্ষ্য একই দিকে ধাবিত। এর রাজনৈতিক লাইনটি খুবই স্পষ্ট। ভারতবর্ষে বৃহৎ পুঁজির রাজত্বের জন্য স্থানীয় বৈচিত্র্যগুলিকে মুছে দেওয়া দরকার। সে জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে হিন্দি-ইংরিজির স্টিমরোলার। বৃহৎ পুঁজি অর্থে গুজরাতি ও মারওয়াড়ি পুঁজি। তারা নিজেদের বাকি সবার মতো নিজের সংস্কৃতি এবং ভাষাকে বিসর্জন দিতে রাজি আছে, মুনাফা এবং আধিপত্যের স্বার্থে। বৃহৎ পুঁজি এবং বৃহৎ ভাষা উভয়ের আধিপত্য তাই হাতে হাত ধরে চলেছে।
মোটামুটি এই লাইন চলে ১৯৪৮ (বা আরও আগে থেকে) ১৯৫৩ পর্যন্ত। জাতি বলতে তখন বাঙালি বা তামিলকে বোঝানো হত। বিচ্ছিন্নতাবাদ কিছু নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। হিন্দি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ছাত্র ফেডারেশন আন্দোলন করত। এবং গুজরাতি ও মারওয়াড়ি পুঁজিকে স্বনামে ডাকতে রাজনৈতিক সঠিকত্বের কোনো সমস্যা ছিলনা। যুগটা অন্য ছিল। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের সেই শেষ কয়েক বছর। সবে বিপ্লব সমাধা করেছেন মাও, চিন এবং সোভিয়েতে খুব সামান্য মতবিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুত্ব অটুট। কমিনফর্ম টিকে। এবং স্তালিন বেঁচে। বস্তুত ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্টদেরও সেটাই স্বর্ণযুগ। তেলেঙ্গনার সশস্ত্র লড়াই শেষ হয়ে যায় ৫০-৫১ সালেই। কিন্তু কমিউনিস্ট প্রভাব ঐ এলাকায় কমেনি। ১৯৫১ সালের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে ওই এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি আসনে জেতে সিপিআই। লোকসভার নবনির্বাচিত কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালন নির্বাচনের ঠিক পরেই ঘোষণা করেন, ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনই সেই মুহূর্তে পার্টির লক্ষ্য। এবং সেটিই নবগঠিত রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা।
নেহরু এবং কংগ্রেস, বলাবাহুল্য এই নীতির ঠিক উল্টোদিকে ছিলেন। নেহরু স্বয়ং তখন বোম্বের সিনেমাকে ঐক্যবদ্ধ ভারতের মুখ হিসেবে দেশে-বিদেশে ঘুরে-ঘুরে প্রচার করছেন। কংগ্রেসের মডেল ছিল, কেন্দ্র হবে সর্বশক্তিমান এবং প্রদেশগুলি ভাষা বা জাতিভিত্তিক স্বায়ত্ত্বশাসিত এলাকা নয়, বরং সীমিত ক্ষমতার অধিকারী প্রশাসনিক একক হবে মাত্র। কিন্তু নেহরু শেষ পর্যন্ত এই ধারণায় অবিচল থাকতে পারেননি। ভাষাভিত্তিক রাজ্যের জন্য, রাষ্ট্রের এই ঊষালগ্নেই নানারকম আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এর প্রতিটিতেই কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকা বা মদত ছিল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যোগদানের জন্য মানভূমের আন্দোলনটি সুপরিচিত, কালক্রমে যা থেকে জন্ম হবে পুরুলিয়া জেলার। কিন্তু সবচেয়ে বড় আন্দোলনটি হয় আজকের অন্ধ্রে, যা কোনও কারণে এখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। মাদ্রাজ প্রদেশের বদলে তেলুগু জনতার নিজস্ব অন্ধ্র রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বড় এই আন্দোলনটি হয় ১৯৫২ সালে। কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্থানীয় গান্ধিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রীরামালু অনশন শুরু করেন ১৯৫২ সালে। কেন্দ্রীয় সরকার মৌখিক কিছু আশ্বাস দেয়, কিন্তু ওই অবধিই। কিছুই না এগোনোয় কিছুদিন অপেক্ষা করে শ্রীরামালু আমরণ অনশন শুরু করেন। এবং যতীন দাসের পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন। এর পর আন্দোলনের ঝড় ওঠে ওই এলাকায়। পুরোভাগে, যথারীতি কমিউনিস্টরা। নেহরু পিছু হঠেন এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্যের জমানার সেই শুরু। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কংগ্রেসের সেই প্রথম পরাজয়। এবং কমিউনিস্টদের যুক্তরাষ্ট্রীয় লাইনের প্রথম জয়।
আয়রনি এই, যে, এই জয়ের সূচনা দিয়ে আসলে ইতিহাসের কিছুই বোঝা যায়না। ইতিহাস ওরকম সরলরৈখিক নয়, বরং আয়রনি ময়। স্বর্ণযুগের মধ্যেই সম্ভবত পতনের বীজ নিহিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যেমন। ১৯৫৩ সালে দুম করে মারা যান স্তালিন। মৃত্যু না হত্যা, এ নিয়ে বিতর্ক তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু যা নিয়ে বিতর্ক নেই, তা হল, এরপরই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য শেষ হয়ে যায়। ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। সোভিয়েত তার লাইন বদলে ফেলে। যদিও নামে জোট-নিরপেক্ষ, কিন্তু আদতে দ্বিমেরু পৃথিবীতে ভারতীয় রাষ্ট্র সোভিয়েত-শিবিরে যোগ দেয়। ক্রুশ্চেভের সোভিয়েতের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং দুম করে বদলে যায় কমিউনিস্ট পার্টির লাইনও। ১৯৫৩ সালে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে অজয় ঘোষ লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করেন, যে, পার্টি এতদিন ভারতবর্ষের ঐক্যের উপর জোর না দিয়ে বিচ্ছিন্নতাকে গৌরবান্বিত করেছে। খুব স্পষ্ট করেই জানানো হয়, এবার থেকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে হিন্দিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। যেখানে হিন্দি বলা হয়না, সেখানেও 'জাতীয়' ভাষার পূর্ণ অধিকার রক্ষা করেই পার্টি হিন্দিকে উৎসাহ দেবে এবং জনপ্রিয় করার চেষ্টা করবে। এখানে 'জাতীয়' শব্দটি লক্ষ্যণীয়। তখনও সর্বভারতীয় শব্দভাণ্ডারে 'আঞ্চলিক' শব্দটি এসে পৌঁছয়নি। স্থানীয় ভাষাকে তখনও বলা হচ্ছে 'জাতীয়', যদিও ঠোঙার ভিতর সম্পূর্ণ বদলে গেছে বাদামভাজা।
কয়েক বছরের মধ্যেই শব্দবিধিও বদলাতে শুরু করে। তেলেঙ্গানায় যে পার্টি কংগ্রেসকে “মারওয়াড়ি পুঁজির দালাল” আখ্যা দিয়েছিল, তাদের দলিল ক্রমশ ভব্য হয়ে ওঠে। ‘মারওয়াড়ি পুঁজি’র বদলে ‘একচেটিয়া পুঁজি’, বা ‘টাকার কারবারি বণিকগণ’ ইত্যাদি ‘সঠিক’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রাভদা নেহরুর উচ্চকিত প্রশংসা করে একটি সম্পাদকীয় ছাপে। সংসদে হিন্দির ব্যবহারেরও প্রশংসা করা হয়। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।
একথা ভাবার অবশ্য কোনও কারণ নেই, যে, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিলনা। কিন্তু সেসবও থেমে আসে নানা কারণে। সোভিয়েতকে অনুসরণ করা নিয়ে বিতর্কের অনেকগুলি মুখের মধ্যে একটি ছিল জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আরও নানা বিষয় ছিল, এবং পার্টি প্রথমবার ভাঙে ১৯৬৪ সালে। দ্বিতীয়বার ভাঙে ১৯৬৯ সালে। জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই চলে যান নকশালপন্থী অংশে, যে অংশটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও পক্ষে। ১৯৭১-এর মধ্যে প্রথম পর্বের নকশাল আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতির মূলধারা থেকে মুছে যায়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতিসত্তার আন্দোলনও মূল ধারায় বৈধতা হারিয়ে ফেলে। রাজ্য এবং প্রদেশের পার্থক্য আলোচ্যসূচি থেকে বাদ পড়ে যায়। আগে যাকে সর্বভারতীয় বলা হত, তা হয়ে যায় জাতীয়, আর আগেকার জাতি হয়ে যায় আঞ্চলিক। বৈচিত্র থেকে নজর সরে যায় ঐক্যে।
৭০ বছর পরে ফিরে দেখলে মনে হয়, বাইরের প্রভাবে নয়, এ আসলে প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ব্যাপারই। স্লোগান হিসেবে "ইয়ে আজাদি"র দুটি অভিমুখ ছিল। এক, সমস্ত জাতিসত্তার সমানাধিকার। দুই, একটি সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা। এই দুইয়ের মধ্যে টানাপোড়েনে সর্বভারতীয় হবার আকাঙ্ক্ষাটি বেশি এগিয়ে থাকে, অধিকতর শ্রোতার কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যে স্লোগানটির ভাষা হয়ে যায় হিন্দি। এবং আয়রনি এই, যে, যে মুহূর্তে হিন্দি আধিপত্যের বিরুদ্ধে, জাতিসত্তার সমানাধিকারের পক্ষে একটি স্লোগানের জন্ম দিতে হয় হিন্দিতে, স্রেফ ‘সর্বভারতীয়’ হবার বাসনায়, সেই মুহূর্তেই তার পরিণতিও লেখা হয়ে যায় দেয়ালে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতিসত্ত্বাদের উত্থান যদি রাষ্ট্রের ভাষাতেই করতে হয়, তা আসলে "যোগাযোগের মাধ্যম" হিসেবে হিন্দিকে ব্যবহার করার রাষ্ট্রীয় আখ্যানের পক্ষেই দাঁড়িয়ে যায়। যার অনিবার্য পরিণতিতে কোনও এক সময়ে রাষ্ট্রের আখ্যানকে সরাসরি মেনেও নিতে হয়। এই আয়রনি, "ইয়ে আজাদি" স্লোগানের রক্তের অন্তর্গত। বাইরে থেকে আসেনি।
এবং এই একই জন্মদাগকে আমরা চিনে নিতে পারি পরবর্তীর যেকোনো আজাদির স্লোগানেও। যেকোনো অঞ্চলের সমানাধিকারের স্লোগান, আজাদির স্লোগান এখন সমস্বরে উচ্চারিত হয় হিন্দিতে। অথচ ভারতর্ষের হিন্দিবলয় কখনও ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে আজাদি চায়নি। তেলেঙ্গানা থেকে কাশ্মীর চেয়েছে। এন-আর-সি থেকে মুক্তি চেয়েছে বাংলা, আসাম। অথচ তার স্বঘোষিত অগ্রণী অংশ স্লোগান দেয় হিন্দিতে। কারণ, এ স্লোগানের ভিতরে ঢুকে আছে "সর্বভারতীয়" হবার আকাঙ্ক্ষা। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দাবি বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্নতাকে স্বীকার করে তবেই সম্ভব। সমস্ত দাবির ভাষাকে পিটিয়ে সমতল করে দিয়ে কোনওমতে সর্বভারতীয় শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই যদি প্রাধান্য পায়, তবে সে স্লোগান আঞ্চলিক জাতিগোষ্ঠীর স্বাধিকারের স্লোগান নয়। অথচ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মূলধারার সমস্ত আজাদির স্লোগানই দেওয়া হয়েছে হিন্দিতে। এই আয়রনিই এদের প্রতিটিরই জন্মদাগ। ১৯৪৮ সালের প্রথমটি থেকে যার শুরু।
থাম্বনেল গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনইমরান খান - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়আরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 অনির্বাণ | 86.2.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২১:৩৪96247
অনির্বাণ | 86.2.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২১:৩৪96247"অথচ তার স্বঘোষিত অগ্রণী অংশ স্লোগান দেয় হিন্দিতে।" - অনেক সংগঠনের নামও হয় হিন্দিতে।ক্রান্তিকারী, ক্রান্তি, কিষান, মজদুর এইসব থাকে নামের মধ্যে।
 S | 2405:8100:8000:5ca1::fe:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৭96248
S | 2405:8100:8000:5ca1::fe:***:*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৭96248- ‘আজাদি’ ফার্সি শব্দ।
-
রৌহিন | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২৩:১২96249
"সর্বভারতীয়" হওয়াটাই ভারতীয়ত্বের প্রকৃত পরিচয়, এই ধারণা গেঁড়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা জাতীয়তাবাদ বা তামিল জাতীয়তাবাদ বা কাশ্মীরি স্বায়ত্তশাসন এর দাবী সবই "বিচ্ছিন্নতাবাদ" বলে দেগে দেওয়া হয়। কারণটাও এই নিবন্ধেই আছে। বৈচিত্র্য না রাষ্ট্রের প্রিয়, না পুঁজির। এতরকম কাস্টমার সেট হলে কোন প্রোডাকশনই মাস স্কেলে করা যায় না। তাই "জাতীয়" ভাবধারায় দেশকে উদবুদ্ধ করা প্রয়োজন
 এলেবেলে | 202.142.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২৩:৪১96252
এলেবেলে | 202.142.***.*** | ১৪ আগস্ট ২০২০ ২৩:৪১96252সাধারণত গুরুতে সৈকত নতুন কিছু লিখলে আগ্রহ নিয়ে পড়ে থাকি। তবে আগের লেখাটিতে সৈকত কোনও প্রত্যুুত্তর দেওয়ার পরিশ্রম করেননি। সেটি বুবুভা-তে প্রকাশিত হওয়ার কারণে কি না, তা অবশ্য জানি না। এখানে তিনি যদি উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখেন, তবে দু-কথা লেখার ইচ্ছে রইল।
-
 Ishan | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:১৭96258
Ishan | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:১৭96258 আরে আপনি লিখুন না। সম্পাদিত লেখার সমালোচনা হয় তো। সাধারণভাবে সেটাকে ডিফেন্ড করতে নামা ভাল দেখায়না বলে নামিনা। কিন্তু পড়ি তো বটেই। সব কিছুর সঙ্গে একমত হইনা, কিছু পড়ে ঋদ্ধ হই। সবরকমই হয়।
 hu | 2607:fcc8:ec45:b800:f5ab:bfe7:a225:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:৩২96259
hu | 2607:fcc8:ec45:b800:f5ab:bfe7:a225:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:৩২96259- এটা ভেবে অবাক লাগে যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের বৈচিত্ররক্ষার জন্য লড়াই করেছিল যেখানে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈচিত্রের চেয়ে ঐক্যকেই প্রাধান্য দিয়েছে বেশি। কমিউনিস্ট পার্টি এই অনুপ্রেরণা পেল কোথায়?
 :|: | 174.255.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:৫১96260
:|: | 174.255.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৪:৫১96260- ঠিক যে কারণে বাঙালীর আর তামিলের জাতীয়তাবাদ এক নয়, ঠিক তেমনই সোভিয়েতের আর বাংলার কম্যুনিজমও এক নয়।
মনে হয়।
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৯:৪৮96262
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৯:৪৮96262- বাঙালির শেষ আশা কমব্যাটান্ট তরুণ প্রাবন্ধিক, সে যদি মাইরি সোশাল মেডিয়ার চক্করে 'ঋদ্ধ' হতে শুরু করে, এ পথের শেষ কোথায়? এর পরে হয়তো দেখা যাবে যখন তখন আমরা রেগুলার ইশানের মন ছুঁয়ে ফেলছি অথবা আমাদের হাতটা ধরে নিয়মিত ইশান চুপ করে বসে থাকছে। বা তাপোষ দাষ সৈকত চট্টো সোমনাথ দাশগুপ্ত রা পরিবেশবান্ধব ভাবে হিমালয় কি করে যাওয়া এই ভেবে তিস্তায় বেলা অর্ডার দিচ্ছে, আর্বান বিকল্প আর্ট ফ্রন্টে র দফারফা। এই দেওয়া নেওয়া য় মাইরি অমিত শা ছাড়া কারো উপকার হবেনা, এলে তুমি মাইরি যা ল্যাখার ল্যাখো না, প্যানোর প্যানোর করো ক্যান। আমার তো এই লেখাটা পড়ে এত কিছু বলতে ইচ্ছে করছে যে সেটা আরেকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে যায় , কিন্তু সেটা আমার অন্য যে কোন নাতিদীর্ঘ র মত সম্পূর্ণ ইউজলেস বকোয়াজ হবার চান্স আছে তাই চেপে আছি। পরাজয়ের নানা বেদনা ময় মুহূর্তে র কথা আমরা আজকে র দুটো প্রবন্ধে জানতে পেরেছি, হ্যাঁ আমার বলতে দ্বিধা নেই এই ডিসকাউন্টের ভীড়ে চোখের জল ও মুছে ছি, কালরাতে ই কলম দুটির কারসাজি তে, কিন্তু সৈকতে র লেখাটা সম্পর্কে যেটা বলতে হচ্ছে, আর্ট মুভমেন্ট বা রাজনৈতিক বা অন্য দর্শনচর্চার ঘরানা থেকে এসে ম্যানিফেস্টো লেখার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা সৈকতের আছে, আমার গুরু চন্ডালির নেশার এইটেই মূল ডোপ, কিন্তু ইতিহাস বিষয়ে আলোচনার সময়ে সেটা এতদিন আ্যভয়েড করেছে, এবার এ সেটা হয়নি। বেদনাময় কতগুলি ঘটনা যে কার্যকারণ দিয়ে জোড়া গেছে সেটি আসলে খানিকটা আরোপন হয়ে গেছে। যাই হোক তবু ধন্যবাদ একটা সজীব , ভাষার সত্তার নিপীড়নে যন্ত্রনাবিদ্ধ কলম, এই সব প্লাস্টিক সেলিব্রিটি প্রতিযোগিতা আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর যুগে এসব তো দেখা যায় না।
 বোধিসত্ত্ব | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৯:৪৯96263
বোধিসত্ত্ব | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ০৯:৪৯96263- ***
 বোদাগু | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১০:০৭96267
বোদাগু | 2402:3a80:a6e:c274:f3ec:cabb:2d16:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১০:০৭96267- ***ভ্যালা
 এলেবেলে | 202.142.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১১:০৫96268
এলেবেলে | 202.142.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১১:০৫96268খ, ঠিকই প্যানর প্যানর করা উচিত হয়নি। তবুও সৈকত যেহেতু সংবেদনশীল লেখক এবং তাঁর অনেক লেখাতেই আমি এই বিষয়টা লক্ষ করেছি, তাই মনে হয়েছিল এখানে মনোভাবের আদানপ্রদানটা জরুরি। সৈকতকে উপনিবেশবিরোধী বলেই জানি, এ-ও জানি যে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হিন্দির জন্ম নিয়ে একটি লেখা লিখেছিলেন (যদিও তা খুঁজে পাইনি, কেউ তুলে দিলে পড়তে পারতাম)।
কিন্তু ১৮০২ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্তানির অধ্যাপক গিলক্রিস্ট যে ভাষাকে 'embryonic stage' -এ আছে বলেছিলেন, কিছু দিন যেতে না যেতেই কোন অদৃশ্য ভোজবাজিতে তার সেই দশা ঘুচল এবং হিন্দুস্তানি ভেঙে গেল হিন্দি ও উর্দুতে - আমার মনে হয় তখন থেকেই এই জন্মদাগের শুরু। খেয়াল করলে দেখা যাবে, তখন থেকেই কলেজের ছোকরা সাহেবদের ভাষা হিসেবে প্রথম পছন্দ ফারসি এবং দ্বিতীয় হিন্দুস্তানি যা কালক্রমে হিন্দি হয়ে উঠছে। এবং প্রথমাবধি বাংলা হচ্ছে কলেজের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ।
ভারতবর্ষের এই বিবিধ বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে তাকে এক জাতি-এক ভাষার দেশ গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ঔপনিবেশিক 'প্রভু'রা নিয়েছিল তাদের শাসনস্বার্থে, তারই পুনরাবৃত্তি করেছে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে বিজেপি। ফাউ হিসেবে কংগ্রেস মুখে এক ধর্মের কথা না বললেও আড়ালে-আবডালে তা বুঝিয়ে দিতে বাকি রাখেনি। বিজেপির সে বালাই প্রথম দিন থেকেই নেই।
কাজেই জন্মদাগের বয়স আসলে কিন্তু অনেক আগের। এটাই বলার ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, সৈকত এগুলোর সবটাই জানেন এবং কোনও ভাবেই তাঁর এই আলোচনার 'ঋদ্ধ' হওয়ার চান্স নেই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন!!
 S | 2405:8100:8000:5ca1::59b:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১২:১২96272
S | 2405:8100:8000:5ca1::59b:***:*** | ১৫ আগস্ট ২০২০ ১২:১২96272- এক্দম একমত। ভারতের ভাগ হওয়ার পর হিন্দুস্থানীকেও জোড় করে ভাগ করে দেওয়া হয়। হিন্দিকে হিন্দুস্থানের ভাষা হিসাবেই স্বাধীনতার পর থেকে প্রোমোট করা হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান উর্দুকে নিজেদের ভাষা হিসাবে নিয়ে বলা নেই কওয়া নেই উর্দুর মতন একটা সেকুলার ভাষাকে ইসলামী পোষাক পড়িয়েছে। পাকিস্তান যদি মুসলিমদের দেশ হয়, তাহলে হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ - এইটাই মোটামুটি হিসাব। আর হিন্দুদের দেশ হিন্দুস্থানের ভাষা হবে হিন্দি, ন্যাচারালি। মোটামুটি এই যুক্তিকেই প্রথম থেকে জল দিয়ে বড় করা হয়েছে। ফলে হিন্দুস্থানীর যে ইনহেরেন্ট ডাইভার্সিটি ছিল, সেখানে লোকাল ডায়ালেক্টের প্রাধাণ্য ছিল, প্রচুর অ্যাকসেন্টের ছড়াছড়ি ছিল সেসব ক্রমশ বন্ধ হয়েছে। সেটি করার জন্য বলিউডের আরেকটি ধন্যবাদ প্রাপ্য। ফলে মারাঠি, গুজরাতি, পান্জাবী, পাহাড়ি, হরিয়ানি, কোন্কানি, মৈথিলী, ভোজপুরি থেকে বেলগাওঁএর লোক সবাই হিন্দি বলছে গড়গড় করে। এখন চোখ পড়েছে পূর্বে।
-
Tapas Das | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০১:৩৭96319
গুরুতে প্রেক্ষিতা ঘোষ দেখে পাগলা হয়ে যেতে হত যে বোধি। আর আজ ছ্যাঁকা লাগলে হবে?
ইতি তাপস দাশ (সঠিক বানান হিমালয়ে পাঠাবেন না)
-
বিপ্লব রহমান | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০৮:১৩96341
"ইয়ে আজাদী" শ্লোগানের আয়রনি ও আদ্যোপান্ত জেনে ভাল লাগল।
এপারে নয়ের দশকে স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ সরকার বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিজেও শ্লোগান লিড করেছি, দু-একটি শ্লোগান বানিয়েওছিলাম, যেগুলো এখনো সাবেক সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের মিছিলে উচ্চারিত হয়।
এটি বিস্ময়কর, কীভাবে যেন কবিতা এসে শ্লোগানে মিশে যায় :
"আমাদের ধমনীতে শহীদের রক্ত/ এই রক্ত কোনোদিন পরাভব না!"
আবার ১৯৭১ এর শ্লোগান ২০১৩ তে এসে শাহবাগ বিস্ফোরণে ফের উচ্চারিত হয় :
"পদ্মা মেঘনা যমুনা/ তোমার আমার ঠিকানা!"
অথবা :
"জয় বাংলা!"
-
বিপ্লব রহমান | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০৮:১৮96342
* কিভাবে
-
 Ishan | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০৮:৫২96345
Ishan | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০৮:৫২96345 - আরে ঋদ্ধ কথাটা একেবারেই ব্যঙ্গ না। রসিকতাও না। লোকে শব্দটাকে বহুব্যবহারে জীর্ণ, দুচ্ছাই করে দিয়েছে, তো আমি কী করব। :-( কত কিছু জিনিস নতুন জানি। এই তো গতকালই একজন একটা ১৯১২ সালের ১০ টাকার নোটের ছবি দেখাল। তাতে দেখলাম, নাগরী লিপি নেই, অন্যান্য ভারতীয় লিপি আছে। এইটা জানা ছিলনা। সত্যিই ঋদ্ধ হলাম। এখনও অবশ্য বিশদটা জানিনা। কেউ ভারতীয় নোটের ইতিহাস জানালে সত্যিই হব।
পুঃ ১। এলেবেলের সঙ্গে এক্ষেত্রে একেবারেই দ্বিমত নেই। সত্যিই ফোর্ট উইলিয়াম নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। এবং সত্যিই আমিও সেটা খুঁজে পাচ্ছিনা।
পুঃ ২। হুচিকে। সোভ্যেত ইউনিয়ন আসলে ৭০ বছরে বারবার রঙ পাল্টেছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েতকে ভাবা হয়েছিল পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে, বিচ্ছিন্নতার অধিকার সহ। তারপর এল গৃহযুদ্ধ। ওয়ার-্কমিউনিকম। জরুরি অবস্থার বাবা। ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রইল। সেসব মিটতে যুক্তর্ষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হল। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকেও তুলে নেওয়া হবে কিনা ভাবা হচ্ছিল। তখন কিছুদিন সোভিয়েতে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় হাওয়া।
এরপর লেনিন দুম করে মারা গেলেন। ত্রৎস্কির আর সাধারণ সম্পাদক হওয়া হলনা। স্তালিন নানা যুদ্ধ করতে লাগলেন নানা গোষ্ঠীর সঙ্গে। কিন্তু তখনও গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষত।
ত্রৎস্কিকে তাড়ানো হবার পর অবস্থা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। সে হল প্যারানইয়ার বজ্রমুষ্টি। বাধ্যতামূলক সমবায়ীকরণ শুরু হল। খেতখামারের। ওই জোরাজুরিতে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কোনো কাঠামোই অক্ষত রাখা সম্ভব না। শুধু তাই না, ওই সময়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে। ইউক্রেন আর কাজাকস্তানে দুর্ভিক্ষ হয়। মানে মন্তন্তর স্তরের দুর্ভিক্ষ। কিন্তু স্তালিন কোনো স্তরে কোনো বিরোধিতা শোনেননি।
মস্কো ট্রায়ালের পর ৩৭ নাগাদ দেখা যায়, পুরোনো পার্টির অর্ধেকই স্তালিন ভোগে পাঠিয়ে দিতে পেরেছেন। তখন উনি একটু ঠান্ডা হন। কিন্তু এই করতে করতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন কীসের যুক্তরাষ্ট্র, কার কী।
বিশ্বযুদ্ধ মেটার পর, এবং সবাই হাতে-হাত মিলিয়ে লড়ার পর, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাব-্ভালোবাসা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। স্তালিন অবশেষে ১৭ সালের লেনিন প্রস্তাবিত মডেলে ফেরার কথা ভাবতে শুরু করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে সার্বভৌমত্ব দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেকের বিদেশ মন্ত্রক সহ। এবং লেনিনের মডেল অনুযায়ী এশিয়ার মডেল যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েতকে ভাবা শুরু হয়। কমিনফর্মকেও সেই মর্মেই অবহিত করা হয়।
এই দশাটা হল সেই সময়, যখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল। এইটাই সেই সময়, যখন চিন এবং ভারত স্বাধীন হচ্ছিল। ৪৫ থেকে ৫৩।
৫৩ তে স্তালিন মারা যান। ক্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়ন আর রাশিয়া মোটের উপর সমার্থক করে ফেলার দিকে এগোন। শক্তিশালী কেন্দ্র না হলে ঠান্ডা যুদ্ধ জিতবেন কীকরে। তারপর থেকে গর্বাচভ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে নীতি আর বিশেষ বদলায়নি। পুরোটাই রুশ আধিপত্য। এই হল গল্প।
পুঃ ৩। এতটা লিখে ফেললাম, দু লাইন লিখব ভেবে। এই জন্য নিজের লেখার নিচে কমেন্ট করতে নেই।
-
রৌহিন | ১৬ আগস্ট ২০২০ ১০:৩৬96350
"দু লাইন" লিখে কী মজা পাও?
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:a10b:cd95:a6e7:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ১২:৫৬96354
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:a10b:cd95:a6e7:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ১২:৫৬96354- এটা যে লিখেছে ইশান ভালো লিখেছে, নইলে মনে হচ্ছিল স্তালিন ভীষণ ফেডেরালিস্ট ছিলেন:---))))), তবে ওদের স্ট্রাকচারাল আর মডার্নাইজেশনের প্রশ্নে অন্য কতগুলো বিষয় ছিল, যেটাকে পুরোটাই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলা কঠিন। বিভিন্ন ফর্মার সোভিয়েত এর অন্তর্ভুক্ত দেশ গুলির নানা লেখা পড়ে , আর এখনকার রিসারচার দের বক্তৃতা ইত্যাদি শুনে আমি মোটামুটি তিন চারটে সিদ্ধান্তে উপনীত , বলাবাহুল্য সেগুলি ও অন্তর্বর্তী কালীন::--))
 কৃষ্ণেন্দু দে | 113.2.***.*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ১৭:১৮96360
কৃষ্ণেন্দু দে | 113.2.***.*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ১৭:১৮963601950 সালে স্তালিনের মধ্যস্থতার reference পাওয়া যাবে?
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৩২96365
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৩২96365- তো সোভিয়েট ফেডেরালিজম সংক্রান্ত তিন চারটে অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত আপাতত আমার মনে যা রয়েছে, সেটা হলঃ
১) ইউরোপের দেশ গুলির, ইউক্রেন, বেলারুস এর অভিজ্ঞতা র সংগে ইস্টার্ন ব্লকের দেশ গুলির অভিজ্ঞতার মিল। অর্থাৎ তাদের রাজনীতিতে সোভিয়েত আমলের ছায়া থেকে বেরোনোর প্রচেষ্টা প্রবল। তারা সিকিউরিটি বাফার হতে হতে ক্লান্তো হয়েছিল। এভিডেন্স স্বেতলানা আলেকসেইভিচ।
এবং যতদূর মনে হয় আর্বান ইন্টেলেকচুয়াল দের একটা ইউরোপীয় ঐতিহ্য ছিল, তাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতার সংগে হাংগেরি বা চেক ইনটেলেকচুয়াল দের সমতুল্য। ৫৬ ও ৬৮ সালে র আপরাইসিং গুলির কথা এবং অবশেষে ৮৬ র ওয়ারশ র আপরাইজিং গুলির কথা আমার ধারণা ইউক্রেন এবং বেলারুস এ অন্তত একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেই রয়েছে।
২) কিন্তু এই দেশ গুলিতেই, বাল্টিক স্টেট গুলিতেও রাশিয়ান এথ্নিক জনতা প্রচুর আছেন, এবং সামাজিইক ফল্টলাইন প্রখর।
৩) জাতীয়তাবাদ বিচিত্র জিনিস , তাই ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বা আমেরিকা পন্থী পলিটিশিয়ান রাও এসব দেশে জাতীয়তাবাদী, সোভিয়েত অতীত কে লজ্জাজনক মনে করার প্রেক্ষিতে, আবার হাংগারি তে ও কনজারভেটিভ জাতীয়তাবাদী রা রয়েছেন, যাঁদের অ্যান্টি সেমিটিজম, এবং পুতিন ঘরানা র শাসন্যন্ত্র চুড়ান্ত।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সদস্যপদ একটা সময় অব্দি গাজর হিসেবে কাজ করেছে বটে, কিন্তু ২০০৮ এর ক্রেডিট ক্রাইসি, ২০১১-২০১২ এর ডেট ক্রাইসিস, গ্রীসের অভিজ্ঞতা, এবং এখনকার রাইট উইং ওয়েভ, সিরিয়ান রিফিউজি ক্রাসিস মিলিয়ে, সে গাজরে আর জোর তেমন নাই। অতএব কে কতটা দক্ষিন পন্থী হতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা চলে অনেক সময়ে।
৪) বসনিয়া, হর্জেগোভিনা, সার্বিয়া, কসোভো , আলবেনিয়া এখানে বলকান যুদ্ধের ভয়ানক স্মৃতি যা, কিছু কবে নর্মালাইজ করবে বলা মুশকিল, তবে বসনিয়া এবং কসোভো, তে ওয়েস্টার্ন স্টাইল ডেমোক্রাসি র ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি হয়েছে। তাতে সোভিয়েত সিকিউরিটি বাফার হিসেবে অবদমিত জাতীয় গৌরব আর রক্তাক্ত এথনিক সআধীনতা র মাঝে কোথাও ন্যাশনাল কনশাইন্স ঝুলে আছে, এই দেশগুলো র কথা না বললে অঞ্চলের পলিটিক্স বলা অসম্ভব, বিশেষ করে ভাষা ও জাতি প্রসংগে।
৫) এশিয়ান সোভিয়েত ইউনিয়ন এর অনেকের ই অভিজ্ঞতা হল, সোভিয়েত আমল তাদের দেশের ইউরোপীয় শিল্পায়ন, উন্নয়ন, আর্বানিটি, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদির আমল, তাদের সআধীনতার পরে জিও পোলিটিকাল বোড়ে হওয়া ছাড়া অনেকের ই আর বিশেষ ভূমিকা নেই। এবং প্রি সোভিয়েত নেশনহুড সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক সূত্র ঐতিহ্য গুলির সংগে যোগাযোগ ও কিন্তু সোভিয়েত আমলে গড়ে ওঠা আকাডেমিক বা প্রকাশনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে আর ইরাণ ও চীনের সংগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা সূত্র আছে, তার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ আছে, কিতু গবেষণার পয়সা বিশেশ সর্বদা নেই। এগুলি কিছু একেবারে সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা থেকে শোনা।
৬) সোভিয়েত আর্কাইভ্স খোলার পরে রাশিয়া নিয়ে , তার পলিটিক্স নিয়ে যত কাজ হয়েছে, সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া নিয়ে কাজ কর্ম অপেক্ষাকৃত অল্পো, সেইটে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু গবেষক প্রাণপাত করছেন, প্র্যাকটিকালি নিজেদের উদ্যোগে। এখানে সোভিয়েত আমল শুধুই স্থানীয় জাতীয়বাদের দম্বন্ধ হবার ইতিহাস না। ইত্যাদি।
অতএব জাতি প্রশ্নে স্ভিয়েত পলিসি ইভ্যালুয়েশন এ অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা একটা রয়েছে। বোধিসত্ত্ব
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৫96367
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৫96367- যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁর নন্দিনী ভট্টাচার্য্য র লেখা পড়তে পারেন ... এই সেন্ট্রাল এশিয়া সোভিয়েত পাস্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত অথরিটি।
https://books.google.co.in/books/about/Dueling_Isms.html?id=PoRGPgAACAAJ&redir_esc=y
সদ্য প্রয়াত প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক হরি বাসুদেবন স্যার এর রুশ পর্যটক আফানাসি নিকিতিন সংক্রান্ত বইটি পড়তে পারেন। "ইউরেশিয়া" র বিভিন্ন রুট রিট্রেস করেছিলেন একটা টিম নিয়ে।
In the footsteps of Afanasii Nikitin, travels through Eurasia and India in the Twenty First Century, ভদ্রলোকের বিভিন্ন অবিচুয়ারি তে এই কাজটির উল্লেখ পাবেন, এবং , অঞ্চলটির মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে , শুধুই সমর্খন্দ আর বুখারার ছবি না দেখে বইটি পড়তে পারেন। রাশিয়া সম্পর্কে ইউরোপ এর আগ্রহ পিটার দ্য গ্রেট এর আমল থেকে, সেই একধরণের ওরিয়েন্টালিজম আর স্লাভিক কনশাসনেস এর নানা আজগুবি থেকে, আমাদের চেনা সময়এর তুর্গেনেভ , দস্তয়েভস্কি দের আমলের নিহিলিজম এর আমএর মস্কো, কিয়েভ, পিটার্সবার্গ এর নাগরিক সংস্কৃতি, ইত্যাদি এবং তার পরে বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়া সংক্রান্ত স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ বা ১৯৭০ এর পরে নিউ লেফ্ট পরবর্তী দের করা রাশিয়ান সোশাল হিস্টরি এবং তার পরের রাশিয়ান ন্যাশনালিজম এর উত্থান, এই সব ফরেন পলিসি র ছায়া বা নতুন লিবেরাল কনশাইন্স এর চক্করে রাশিয়ান মধ্যযুগ , নিয়ে বেশি চর্চা হয় নি, বা একেবারে স্পেশালিস্ট মহলে হয়েছে। কি পরিমান সঅচ্ছন্দ ছিলেন এই সব সোর্সে, হরি বাসুদেবন, এসব কল্পনার অতীত, দেখতে পারেন। লেখাটা যদিও একটু পুরোনো স্টাইলের, তাঁর সম্পর্কে যে বইঠকি আড্ডার লেজেন্ডের কথা শোনা যায়, তার চিহ্ন একটু খুঁজে নিতে হয়।
তো সোভিয়েত পলিসির মধ্যে জাতি ইত্যাদি খুঁজলেই এই অঞ্চল বিশেষের ভিন্নতার কথাটা একটু মাথায় রাখতে হবে, এর মানে অবশ্য এই না, গোটা সেন্ট্রাল এশিয়া চাইছে, জার, লেনিন, স্তালিন, এক ই ক্রমে ফিরে আসুন। শুধু বলছি, ট্রানস্জিশন এর নানা যন্ত্রনা, নানা নষ্টলজিয়া উথলে দেয় , এই আর কি। বোধিসত্ত্ব, বলা বাউহ্ল্য এই পোস্টে যা লিখলাম, তার অনেকটাই প্রাথমিক ভাবে ইভস ড্রপিং তার পরে আমাজন বিলিং ও অবশেশে পরের বাড়ির মেয়ের রচনায় স্পেল চেকিং এর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। ঃ-))))
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৮96368
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২১:৫৮96368- অধ্যাপিকা নন্দিনী ভট্টচার্য্যর বইটি আমি পড়িনি, শুধু প্রচুর প্রশংসা শুনেছি।
হরি বাসুদেবন এর বইটি এখন পড়ছি, সময় লাগছে। বোধিসত্ত্ব
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২২:০২96369
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8802:c7b5:9d74:1fb8:30a9:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ২২:০২96369- বাসুদেবন এর অবিচুয়ারি, শোভোনলাল দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের লেখা, আমার পড়া বেস্ট অভিচুয়ারি র গুলির মধ্যে থাকবে ....
https://www.mainstreamweekly.net/article9386.html
বোধিসত্ত্ব
 সুশান্ত কর | 117.2.***.*** | ১৭ আগস্ট ২০২০ ২১:০২96398
সুশান্ত কর | 117.2.***.*** | ১৭ আগস্ট ২০২০ ২১:০২96398সিদ্ধান্তটি কী? অতিকেন্দ্রীক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা ঠিক ছিল কি বেঠিক? কিন্তু ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় বলবার এটাই কারণ ছিল না। একটি উপনিবেশ আধা উনপনিবেশে পরিণত ছিল, ব্রিটিশ সরাসরি শাসন থেকে যাচ্ছিল কিন্তু তাঁর পুঁজির স্বার্থ অক্ষত রেখে যাচ্ছিল--- এবং তা ভারতীয় তাবেদারদের হাতে--সেটিও ছিল বড় কারণ...এই স্লোগানের। দেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু হিন্দিটা (না হয় তাকে হিন্দুস্তানী বা উর্দুই বলুন) বোঝে, সেজন্যেও হিন্দিতে স্লোগান দেওয়া হয়। হিন্দি বিদ্বেষের তো কোনো কারণ নেই।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)
(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
















