- বুলবুলভাজা আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শনিবারবেলা

-
বিষের ইতিহাস, ইতিহাসের বিষ
যদুবাবু
আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ | ২১৩৯ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৪ জন) - প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি | তৃতীয় কিস্তি | চতুর্থ কিস্তি | পঞ্চম কিস্তি | ষষ্ঠ কিস্তি | সপ্তম কিস্তি | অষ্টম কিস্তি | সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি | ভক্স পপুলি | দুই লেজান্ড্রর গল্প | বিষের ইতিহাস, ইতিহাসের বিষ
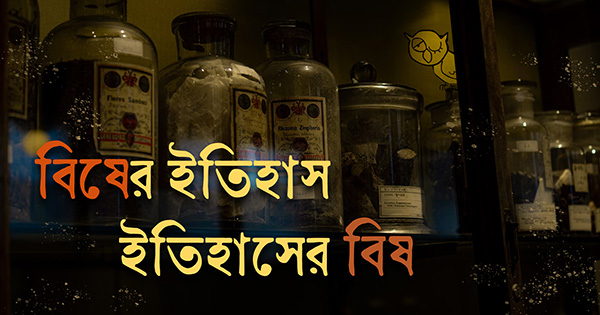 সতর্কীকরণ: এই লেখাটিতে বিষ, বিষক্রিয়া, প্রাণঘাতী মাত্রা, আত্মহত্যা, ওষুধ ও রাসায়নিক বিষয়ে আলোচনা আছে।
সতর্কীকরণ: এই লেখাটিতে বিষ, বিষক্রিয়া, প্রাণঘাতী মাত্রা, আত্মহত্যা, ওষুধ ও রাসায়নিক বিষয়ে আলোচনা আছে।
("Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.")
"What is there that is not poison? All things are poison and nothing is without poison. Only the dose makes a thing not a poison”(প্যারাসেলসাস, ১৪৯৩-১৫৪১)
বিষ এবং বিষক্রিয়া নিয়ে মানুষের কৌতূহল ঠিক কবে থেকে শুরু তার কোনো ঠিক নেই। প্রাগিতিহাস থেকে এই গতকালের খবরের কাগজ অব্দি প্রায় নিঃশব্দে তার পদচারণা। কিন্তু সেই ইতিহাস রহস্যময়, আকর্ষণীয়, অন্তহীন এবং কিঞ্চিৎ জটিল। “জটিল”, কারণ, বিষ ঠিক কাকে বলে, সেই কড়া সংজ্ঞা দেওয়াই একটু মুশকিল। টক্সিকোলজি, অর্থাৎ বিষবিজ্ঞানের বইয়ের শুরুয়াতেই লেখা, “Toxicology is often regarded as the science of poisons or poisoning, but developing a strict definition for poison is problematic”। শুধু তাই-ই নয়, যে উপাদান খুব সামান্য পরিমাণে দিলে হয়তো জীবনদায়ী ওষুধ হতে পারে, সেই এক-ই বস্তু মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী বিষ।
আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডের কথাই ধরুন, সামান্য বেশি মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়ায় গা গোলাবে, বমি হবে, তারপর দাস্ত, ক্রমে অর্গ্যান ফেইলিওর, শেষে মৃত্যু। স্বয়ং নেপোলিয়ঁর মৃত্যুর (নাকি হত্যার?) কারণ খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন সংরক্ষিত চুলের নমুনায় আর্সেনিকের ঘনত্ব সেই সময়ের একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রায় ৪০-গুণ বেশি। আবার এই আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইডের সাথে অন্য ওষুধের (ট্রিটিওনিন) মিশেলেই তৈরি হয় একটি বিরল ক্যান্সারের (অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিম্ফোমা) ওষুধ। আর্সেনিক ছাড়ুন, আপনি রোজ-ই খাচ্ছেন, এই ধরুন জল, কফি, ভাগ্যবান হলে চিনি, সেই সব-ই মাত্রা ছাড়িয়ে খেলে একসময় বিষক্রিয়া হবেই। এই ক্যাফেইন-ই ধরুন, এক কাপ এসপ্রেসোয় ক্যাফেইন থাকে কমবেশি ৬৪ মিলিগ্রাম, আর ক্যাফেইনের ফেটাল ডোজ, অর্থাৎ প্রাণঘাতী মাত্রা ৫০০০ মিলিগ্রামের কাছাকাছি, অর্থাৎ, শুধু কফি খেয়েই পটল তুলতে গেলে আপনাকে খেতে হবে প্রায় ৭৮ কাপ! কিন্তু ঐ সকালে এক কাপ গরম কালো কাপ্পা – ওতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।
অথবা, যে সব ফলমূল কি শাকসব্জি আমরা প্রায়-ই বাজার থেকে থলে ভরে আনি, তাদের কথাই ভাবুন না কেনে? আপেলের বীজে থাকে অ্যামিগডালিন (০.৬ গ্রাম/কেজি), পেয়ার অর্থাৎ ন্যাসপাতিতে থাকে ফর্ম্যালডিহাইড (~০.০৬ গ্রাম/কেজি), আলু – বিশেষত সবুজ আলুতে থাকে সোলানিন (~০.২ গ্রাম/কেজি), কুর্গেট, যাকে আম্রিকায় বলে যুকিনি (আর বাংলায় ঝিঙের ট্যাঁশভাই) – তাতেও থাকে কিউকারবিটাসিন ই। এই সবকটিই মানুষের দেহের জন্য বিষাক্ত অর্থাৎ “টক্সিক”, কিন্তু তবুও তো দিব্যি আলু[1], আপেল, ঝিঙে খেয়েও বেঁচে থাকে মানুষ, কারণ এই সবকটিই ফলমূল-শাকসব্জিতে এতো কম পরিমাণে থাকে যে তাতে কারুর কোনো ক্ষতিবিশেষ হয় না। অর্থাৎ, কোনো একটি রাসায়নিক যৌগ কোনো খাবারে থাকলেই যে সেটা ক্ষতিকারক পরিমাণে আছে এমন না। এই সারসত্যটিই হয়তো সমস্ত টক্সিকোলজিক্যাল অনুসন্ধানের মূলকথা, যা সেই সুদূর রেনেসাঁর সময় অনুধাবন করেছিলে সুইস চিকিৎসক/বিজ্ঞানী প্যারাসেলসাস। যাঁর পুরো নাম, অরিওলাস থিওফ্রাস্টাস বোম্বাস্টাস ফন হোহেনহাইম, আর ছদ্মনাম “প্যারাসেলসাস”, সম্ভবত প্রাচীন রোমের চিকিৎসক সেলসাসের সঙ্গে মিলিয়ে। প্যারাসেলসাস বলেছিলেন, “Only the dose makes a thing not a poison”, অর্থাৎ শুধু মাত্রার তফাত-ই ঠিক করে দেয়, কোনটা বিষ, আর কোনটা বিষ নয়। আজকের দিনে এই কথাটার তাৎপর্য বোঝা বোধহয় আরও একটু বেশিই দরকারি হয়ে পড়েছে আমাদের সবার জন্যেই, কারণ বিজ্ঞাপন কিংবা মিডিয়া থেকে শুরু করে খবরের বিভিন্ন সূত্রে প্রায়-ই শোনা যায় ভয়-ধরানো সব বিশেষণ, “সাঙ্ঘাতিক বিষ”, “দ্য মোস্ট টক্সিক সাবস্ট্যান্স” ইত্যাদি প্রভৃতি। যা থেকে আমাদের মনে হয় যেন আসলে প্রকৃতিতে একটা দুর্দান্ত বাইনারি ব্যবস্থা আছে - কিছু পদার্থ বিষাক্ত আর বাকি সব নির্বিষ। কিন্তু আরেকটু তলিয়ে দেখলে বোধহয় প্যারাসেলসাসের মতই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুব কঠিন না। আরও সহজ করে বললে, যত বিষাক্ত পদার্থই হোক না কেন, যদি তার একটিমাত্র অণু, একটি মলিকিউল প্রবেশ করে কারুর শরীরে, বাজি রেখে বলা যায় তার কিস্যু হবে না, আবার অন্য দিকে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, এমন কী জল-ও প্রাণহানির কারণ হতে পারে। আর তাই, আজকের আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা দূষকের মাত্রা পার্টস পার বিলিয়ন অর্থাৎ পিপিবি এককে মাপতে পারছি যখন, আবার-ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন ‘বিষবিজ্ঞানের জনক’ প্যারাসেলসাস।
মাত্রা তবে মাপবো কী করে? কাকে বলে বায়ো-অ্যাসে, অথবা ডোজ-রেস্পন্স কার্ভ? কাকেই বা বলে LD-50? সেই সব গল্পে আসতে গেলে আমাদের রেনেসাঁ পেরিয়ে এসে অপেক্ষা করতে হবে সেই ১৯৩৫ অব্দি। ওহায়োর স্প্রিংফিল্ডের একজন সাধারণ কিন্তু অসামান্য মানুষ চেস্টার ব্লিসের গল্প বলবো। ব্লিসের গল্পে আসবেন ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট, আসবে গ্রেট ডিপ্রেশন, রোনাল্ড ফিশার এবং স্তালিন-জমানার লেনিনগ্রাদের গল্প। এবং একটু অঙ্ক, আর নির্বিষ অঙ্কের সাথে একটু বিষাক্ত ইতিহাস। যদিও অঙ্কের মত, ইতিহাস আদৌ আমার বিষয় নয়, তাই আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ইতিহাসবিদ পাঠকদের কাছে।কতটুকু চাই?
যে কোনো রাসায়নিকের তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া মাপার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা মূলত যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করেন, সেটির নাম ডোজ়/রেস্পন্স স্টাডি – ডোজ় = মাত্রা অর্থাৎ মুখ, অথবা ফুসফুস অথবা ত্বক দিয়ে মোট যেটুকু পদার্থ শরীরে প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ যেটুকু পদার্থে একজন মানুষ “এক্সপোজ়ড” হচ্ছেন। সে খাবারের মাধ্যমে হতে পারে, অথবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে, অথবা আপনার স্নানের জলে বা সাবান/শ্যাম্পুতে। আর রেস্পন্স = প্রতিক্রিয়া, মাত্রা যত বাড়বে, প্রতিক্রিয়াও বাড়বে তার সাথে পাল্লা দিয়ে। আর সেটাই মাপার জন্য পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকরা যে পরীক্ষাটি করেন, তার পোষাকি নাম বায়ো-অ্যাসে। সাধারণত, ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীদের উপরেই এই বায়ো-অ্যাসে হয়, অনেকগুলি হতভাগ্য ইঁদুর একত্র করে, কয়েকজনের উপর এক্কেবারে সবথেকে কম মাত্রা, আর বাকিদের উপর মাঝারি বিভিন্ন স্তর, আর কয়েকজনের উপর সর্বোচ্চ। আর এর পাশে থাকে আরেকটি ‘কন্ট্রোল’ গ্রুপ যাদের বাকি সব এক, শুধু তাদের এই রাসায়নিক এক্সপোজারটি হয়নি, অর্থাৎ তাদের সবার ডোজ় শূন্য। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মাপা উদ্দেশ্য হলেও সাধারণত ১৪ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয় বেচারি ইঁদুরদের, যাতে কিছুটা সময় পাওয়া যায়। ১৪ দিন পেরিয়ে গেলে গোনাগুনতি হয়, কোন ডোজ়ের গ্রুপে কতগুলো হতাহত? এবং, এখান থেকেই প্রশ্ন আসে, যে মাত্রা বাড়াতে থাকলে ঠিক কী ভাবে প্রতিক্রিয়াটি বাড়ে বা কমে? কোন সূত্র ধরে?
এই ধাঁধাটাই সমাধান করেন আমাদের গল্পের দ্বিতীয় প্রোটাগনিস্ট চেস্টার ব্লিস। ব্লিস এন্টমোলজ়ি নিয়ে পড়াশুনো শেষ করে ১৯২০-র দশকে যোগ দেন ইউ-এস-ডি-এ, অর্থাৎ আমেরিকান সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারে। ওঁর কাজের অন্যতম একটি বিষয় ছিলো আঙুর পাতার পোকার জন্য উন্নত কীটনাশক তৈরি করা, কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর ব্লিস অচিরেই বুঝতে পারেন যে বাইরের উন্মুক্ত পরিবেশে কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা না করে, ল্যাবোরেটরির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করাই শ্রেয়। এবং, সেই পরীক্ষাগুলি করতে করতে ব্লিস দুটো জিনিষ খেয়াল করেন। প্রথমত, যত বেশি ডোজ়েই কীটনাশক দেওয়া হোক না কেন, দু-একটা পোকা কেমন করে যেন বেঁচে যাচ্ছে, আবার উলটো দিকে যত কম ডোজ়-ই দেওয়া যাক, দু-একটা ঠিক তাতেও পটকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, সব পোকার সহ্যক্ষমতা এক-ই নয়, কেউ অল্পেই কুপোকাৎ, কেউ নাছোড়বান্দা। রাশিবিজ্ঞানের ভাষায় একে আমরা বলবো ইনডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েবিলিটি। আর ব্লিস এ-ও খেয়াল করেন, যে একটা কাগজে যদি একটি রেখচিত্র এঁকে তার অনুভূমিক অক্ষে (এক্স-অ্যাক্সিস) ডোজ় বা মাত্রা, আর উল্লম্ব অক্ষে (ওয়াই-অ্যাক্সিস) শতকরা মৃত্যুর হার প্লট করি, তাহলে তার আকৃতি হবে অনেকটা লম্বাটে S অক্ষরের মতন, যাকে আমরা বলি সিগময়েড কার্ভ। তাই, মাত্রা বাড়লে মৃত্যুর হার বাড়ে, কিন্তু সরলরৈখিক ভাবে নয়, বরং কিছুটা এই এস-আকৃতির রেখায়, শুরুতে খুব আস্তে, মাঝে চড়-চড় করে, আবার একটা মাত্রা পেরিয়ে গেলে আবার আস্তে। ১৯৩৪ সালে ব্লিস বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে একটি গবেষণাপত্রে এই ধরণের তথ্য-উপাত্ত মডেল করার একটা নতুন মডেল প্রস্তাব করেন, আর সেই মডেলের নাম দেন প্রবিট – প্রোবাবিলিটি ইউনিটের সংক্ষেপিত রূপ। বলাই বাহুল্য, এই গ্রাফের উল্লম্ব অক্ষে যে চলরাশিটি সেটি প্রোবাবিলিটি – মৃত্যুর সম্ভাব্যতা। ব্লিসের প্রবিট পদ্ধতিতে ঐ প্রোবাবিলিটি-র সংখ্যাটিকে মডেল করা হয় নর্ম্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের সাহায্যে। এখানে বলে রাখা উচিত, যে ব্লিসের আবিষ্কার অন্তত সেই প্রাক-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক বিশাল লাফ। এই রকমের তথ্যে অন্যান্য যে সব মডেল দেখতে আমরা অভ্যস্ত – সেসবের আসতে তখন-ও ঢের বাকি। আর এটাও বলা উচিত যে ব্লিসের সেইসময়কার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন স্বয়ং রোনাল্ড ফিশার। প্রবিট মডেল ফিট করার একটি সহজ উপায় বাতলে দেন ফিশার – এবং, ১৯৩৫ সালের অ্যানালস অফ অ্যাপ্লায়েড বায়োলজ়ি-তে প্রকাশিত ব্লিসের পেপারে একটি অ্যাপেনডিক্স লেখেন ফিশার।
এইরকম সিগময়েড কার্ভ ফিট করানোর অন্যতম লাভ যে এর ফলে ডোজ়-রেস্পন্স স্টাডি থেকে জানা যায়, যে ঠিক কতটা মাত্রায় একটি পদার্থ একটা অর্গ্যানিজ়মের জন্য কতটা মারাত্মক। এর-ই একটি বিশেষ মাত্রা - এল-ডি-৫০, LD50 - মিডিয়ান লিথাল ডোজ়, যার ব্যবহারিক অর্থ: যদি অনেকগুলি প্রাণীর উপরে ঐ পদার্থ ‘প্রয়োগ’ করা হয়, তাহলে ঠিক ঐ LD50 মাত্রার পদার্থ শরীরে প্রবেশ করলে ঐ দলের ৫০% বা অর্ধেক বেঁচে থাকবে। নিচের ছবিটি দেখলে LD50 ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমরা Y = 50% থেকে একটা সোজা লাইন টেনে ঐ লম্বা S-পানা বক্ররেখাটিকে ফুটো করে ঠিক সোজা নিচে নেমে X-অক্ষের যেখানে পা রাখবো, সেটাই LD50। এই ছবিতে যেমন সায়ানাইডের জন্য এই মাত্রা ~১.৫ মিগ্রা/কেজি। বলাই বাহুল্য, যে পদার্থে LD50 যত কম, সে তত-ই বিষাক্ত।
এই যেমন, বটুলিন – ঠিক করে ক্যান না করা খাবারে অথবা পচা মাছ-মাংসে ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামে একটি ব্যাক্টেরিয়া এই টক্সিনটি তৈরি করে – ফল বটুলিজ়ম। বটুলিনের ক্রিয়ায় মাংসপেশীতে স্নায়বিক সংকেত যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়, ফল প্যারালাইসিস, আর চরম পরিণতি শ্বাসরোধ, এবং মৃত্যু। ইঁদুরের উপর করা পরীক্ষায় বটুলিনের LD50 0.00001 মিগ্রা/কেজি, আর একজন ৭০ কেজি পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য ০.৩৫ গ্রামের কিছু কম (আন্দাজ)। বটুলিনকে তাই ক্লাসিফাই করা হয় “সুপার টক্সিক” হিসেবে। আবার ধরুন অ্যাস্পিরিনের মূল উপাদান অ্যাসিটাইলস্যালিসাইলিক অ্যাসিড, তার LD50 ৫০০-৫০০০ মিগ্রা/কেজি, অর্থাৎ, একজন ঐ সত্তর কেজির মানুষের জন্য ৩৫-৩৫০ গ্রাম, আর একটা বড়ির ওজন? মাত্র ৩২৫ মিলিগ্রাম। তাই, টক্সিনের ক্যাটেগরিতে বটুলিনের দলের নাম “সুপার টক্সিক”, আর অ্যাস্পিরিন নেহাত-ই “মডারেটলি টক্সিক”। আবার চিনির জন্য ঐ LD50 ১৫০০০ মিগ্রা/কেজির-ও কিছু বেশি। ঐটি তাই “প্র্যাকটিক্যালি নন-টক্সিক”, কার্যত নির্বিষ। এইরকম বেশ কিছু যৌগের নাম আর মাত্রা দেওয়া রইল পুনশ্চ-র একটি সারণিতে।
এখানে দুটো মন্তব্য বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক, এক-ই পদার্থ কোনো প্রাণীর জন্য খুব-ই ক্ষতিকর কিন্তু অন্য প্রাণীর জন্য একেবারেই নয় এমন আকছার ঘটে। কারণ এক-এক প্রাণীর বিপাক অর্থাৎ মেটাবলিজ়ম এক-এক রকমের। মানুষের জন্য চকোলেটের LD50 অনেক বেশি, কুকুরের থেকে। ফলে, শুধু চকোলেট খেয়ে একজন মানুষের আত্মহত্যা করা বেশ কঠিন, কিন্তু বেচারি কুকুর কয়েকটা চকোলেট বার খেয়ে ফেললেই আর রক্ষে নেই। চকোলেটের থিওব্রোমিন যৌগের LD50 কুকুরদের জন্য ২০-১০০ এমজি/কেজি আর মানুষের আন্দাজ প্রায় ১০০০। আবার ডাইওক্সিনের জন্য – হ্যামস্টারের LD50 গিনিপিগের থেকে ৫০০০ গুণ বেশি! কোনো মানে হয়? (ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত কুখ্যাত এজেন্ট অরেঞ্জের অন্যতম একটি উপাদান এই ডাইওক্সিন।)
আর দুই, মানুষ বা এমনকি কুকুর আজেবাজে কিছু খেয়ে ফেললে বমি করে উগরে দিতে পারে, রোডেন্ট-জাতীয় কোনো প্রাণীর সেই ক্ষমতা নেই। বেচারিদের ডায়াফ্রাম কমজোরি, এবং পেটটিও নাদাবিশেষ। ভাবলে খুব-ই কষ্ট লাগে, অস্বীকার করবো না। কে জানে হয়তো এই পাপেই আমরাও বাধ্য হচ্ছি বিভিন্ন রকমের বিষ ক্রমাগত গিলে যেতে, যা ওগরানোর আর কোনো জায়গা নেই। আর হ্যাঁ, শুধুমাত্র নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখলেও এর একটা বাজে দিক এই যে কোনো কোনো ওষুধ পরীক্ষাগারে সফল হলেও মানুষের আর কাজে লাগে না। রোলিপ্র্যাম নামে একটি অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট এই দলে – ইঁদুর মস্তিষ্কে দিব্য কাজ করলেও, মানুষ সে জিনিষ খেলেই অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে চলে আসে।
মোদ্দা কথা, ইঁদুর বা অন্য অ্যানিম্যাল স্টাডি থেকে পরীক্ষালব্ধ LD50 থেকে বিভিন্ন রাসায়নিকের ক্ষমতার একটা আন্দাজ পাওয়া গেলেও, ইঁদুরের থেকে মানুষে লাফ দিয়ে পৌঁছনোর কাজটা সহজ নয়। বাস্তবে, এইসব পরীক্ষাগার ছাড়াও আমরা বিভিন্ন সার্ভে, হাসপাতালের এমার্জেন্সি বা করোনার’স অফিস থেকে পাওয়া রিপোর্ট, বা ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি। বলাই বাহুল্য, সেই সব বিকল্প পদ্ধতির-ও প্রচুর সীমাবদ্ধতা আছে, বিশেষ করে যদি একাধিক দ্রব্য এক-ই সাথে প্রবেশ করে শরীরে, তবে সে আলোচনা অন্য একদিন।
তবুও, এটা বলে রাখা উচিত যে এই LD50 অর্থাৎ মিডিয়ান লেথাল ডোজ় শুধুই সমষ্টির কথা বলে, ব্যক্তির নয়, তার একটা অন্যতম কারণ যে এক-এক মানুষের (বা প্রাণীর) বিপাক-ক্রিয়া এক-এক রকম। যে মাত্রার ‘বিষ’ একটি ইঁদুরের জন্য প্রাণঘাতী, সেই এক-ই বিষে অন্য একটি হয়তো শুধুই ঝিমোবে। এই ‘ভুল’ কি মানুষের-ও হয় না? দলের একজন প্রভূত নেশা করেও দণ্ডায়মান মানেই আমিও যে ঐ এক-ই নেশা করে এমার্জেন্সিতে পৌঁছে যাব না চৌদোলায়, এর কোনো গ্যারান্টি-ই নেই। এই যেমন ধরা যাক ইথাইল অ্যালকোহলের মিডিয়ান লিথাল ডোজ় প্রায় ৩৩০ গ্রাম, আর এফেক্টিভ ডোজ় তার দশভাগের এক ভাগ প্রায় ৩৩ গ্রাম। মানে দুই শট ভদকা বা দু-ক্যান বিয়ার খেলে হাল্কা ঝিল আসতেই পারে (যাকে বলে ‘রিল্যাক্সড অ্যাফেবিলিটি’), কিন্তু, খালি পেটে মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যেই কেউ তার দশগুণ খেয়ে ফেললে?
এই যে ‘লিথাল’ আর ‘এফেক্টিভ’ ডোজ়ের অনুপাত, রিক্রিয়েশনাল ড্রাগসের বেলায় এইটিও ব্যবহার করা হয় বিপদের মাত্রা বুঝতে। এই যেমন হেরোইন – বেশ বিপজ্জনক, লিথাল আর এফেক্টিভের অনুপাত ১০-এরও কম। কোকেইন বা এমডিএমএ ইত্যাদি একটা বেশ বড়সড় গ্রুপের জন্য এই অনুপাত ১০ থেকে ২০-র মধ্যে। এদের পরের গ্রুপে রোহিপনল, যার ডাকনাম রুফি, ঐ ২০ থেকে ৮০, আর সবথেকে কম বিপজ্জনক রিক্রিয়েশনালের দলে সাইলোসিবিন মাশরুম আর আমাদের ভোলেবাবা, এদের রেঞ্জ ১০০ থেকে ১০০০! সত্যি বলতে, ফুঁকে খাওয়া গাঁজার সত্যিকারের লিথাল ডোজ় কত, সেটা এই প্রবন্ধ লেখার সময় আমার জানা নেই, তবে ১০০০-এর বেশি এমন আন্দাজ করা হয়। বিভিন্ন নেশাদ্রব্যের লিথাল/এফেক্টিভ অনুপাত নিচের ছবিতে দেওয়া হ’ল।
ব্লিসে বিষক্ষয়
বলাই বাহুল্য, এই ডোজ় রেসপন্স কার্ভ ফিট করার যে কলটি চেস্টার ব্লিসের অক্লান্ত চেষ্টার ফসল– অর্থাৎ প্রবিট রিগ্রেশন - সেটি টক্সিকোলজ়ির এবং রাশিবিজ্ঞান – দুইটি শাখার জন্যই যথেষ্ট যুগান্তকারী আবিষ্কার। ব্লিসের সময় যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত-র বিশ্লেষণ করা হত, তাতে এমন প্রায় একটিও অস্ত্র ছিলো না যাতে সহজে বিষের মাত্রা মাপা যায় পরীক্ষামূলকভাবে।
কিন্তু কেমন ছিল ব্লিস-সায়েবের জীবন? সে গল্প কিছুটা ভয়ের, তবে অনেকটাই আমাদের চেনা, অন্তত, এই ২০২৫-এর এপ্রিলে দাঁড়িয়ে। ১৯৩২ সালে অর্থাৎ প্রায় একশো বছর আগে, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজ়ভেল্ট প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থী হলেন। সাধারণ মানুষের তখন ব্যুরোক্রেসি, অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের উপর প্রবল অনাস্থা। রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কমাবেন (আরেকভাবে বলতে গেলে, গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি বাড়াবেন, এখন মাস্ক যা করছেন)। সে প্রতিশ্রুতি রাখতেই ঐ ইউ-এস-ডি-এ’র কোনো এক কেষ্টুবিষ্টু, অর্থাৎ, সহকারীর-সহকারীর-সহকারী কর্তা সিদ্ধান্ত নিলেন - যেহেতু কীটনাশক মাঠে ব্যবহার হওয়ার কথা, তাই এগুলোর ওপর ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে ১৯৩৩ সালে চাকরি হারান চেস্টার ইটনার ব্লিস। ঠিক সেই সময়ে আমেরিকায় চলছে প্রবল মন্দা - গ্রেট ডিপ্রেশন—বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দার সময়। ১৯২৯ সালের শেয়ারবাজার ধস দিয়ে যার শুরু, ১৯৩০-এর দশকজুড়ে দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব আর অর্থনৈতিক অস্থিরতা যার পরিণাম। এই সময়ে আমেরিকায় নতুন চাকরি পাওয়া কার্যত অসম্ভব - চাকরিচ্যুত ব্লিস চলে গেলেন ইংল্যান্ডে, রোনাল্ড ফিশারের (১৮৯০–১৯৬২) পরিবারের সাথে থাকতে। ফিশার নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্লিসের জন্য ল্যাবরেটরির ফেসিলিটির ব্যবস্থা করতে পারলেও চাকরি-বাকরি জোটাতে পারেননি সঙ্গে-সঙ্গে, তবুও ব্লিস লণ্ডনে থেকে প্রবিট মেথডের উপরেই ফিশারের সাথে আরও কিছুদিন কাজ করেন, কিছু ফাঁক-ফোঁকর ভরাট করেন কয়েক মাসে।
এর কিছুদিনের মধ্যেই ফিশার ব্লিসের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন—লেনিনগ্রাদে (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ)। অতএব, ১৯৩৫ সালে ইন্সটিটিউট অফ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন - তিন বছরের চুক্তিতে কাজে যোগ দেন ব্লিস। গোটা ইউরোপ ট্রেনে অতিক্রম করে, একটিমাত্র স্যুটকেসে কয়েকটি জামাকাপড় নিয়ে লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছলেন তিনি। সারাজীবনে ইংরেজি ছাড়া একটিও ভাষা না শেখা, চূড়ান্ত অরাজনৈতিক, একেবারেই আমেরিকান মিড-ওয়েস্টার্ন মানুষ ব্লিস এসে পৌঁছলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রে, যেখানে ধীরে ধীরে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দীদের একে একে সরিয়ে ক্ষমতায় আসছিলেন যোসেফ স্তালিন। ইন্সটিটিউটের কাছেই যে বাড়িতে ভাড়া উঠলেন ব্লিস, সেই বাড়ির মালকিন জানেন না ইংরেজি, ব্লিস জানেন না রুশী ভাষা। ভাগ্যক্রমে আলাপ হয়ে গেলো এক স্বেচ্ছাসেবী আমেরিকান তরুণীর সাথে, আদর্শের প্রেরণায় (বা তাড়নায়) সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই বৃহৎ যৌথ খামারের দুনিয়ায়।
কিন্তু, মারে হরি, রাখে কে? চাকরিতে যোগ দেওয়ার অল্পদিনের মাথায়, লেনিনগ্রাদে ব্লিসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মস্কো ডেকে পাঠানো হয় সামান্য প্রশ্নোত্তরের জন্য। সে বস ঘরে ফেরে নাই। তারও কিছুদিন পর, যে ভদ্রলোক ব্লিস-কে চাকুরি দিয়েছিলেন, তাকেও ডেকে পাঠানো হয় মস্কো। ফেরার পথে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে আত্মহত্যা করেন তিনিও। ব্লিস-ও সন্দেহাতীত ছিলেন না – কমিউনিস্ট পার্টির অচিরেই ধারণা হয় ঐ আপাত-নিরীহ বৈজ্ঞানিকের বেশে ব্লিস আসলে একজন আমেরিকান গুপ্তচর। মস্কোয় সেই কুখ্যাত ইন্টারোগেশন অর্থাৎ "জবাবদিহির ট্রায়াল"-এর মুখোমুখি হতে হয় ব্লিসকে। ডেভিড স্যালসবার্গের বইতে এই অংশের মজাদার বর্ণনা আছে, এবং সেটি স্বয়ং ব্লিসের জবানিতে শোনা গল্প। সেই গল্প অনুযায়ী, জিজ্ঞাসাবাদ-কক্ষে কারা থাকবেন, ব্লিস তা আগে থেকেই জানতেন বান্ধবীর সূত্রে, কারণ সে বান্ধবী পার্টির সদস্যা। কিন্তু শত সাবধানবাণী সত্ত্বেও, ব্লিস ঢুকেই একজন অধ্যাপককে চিনতে পারেন, এবং তাকে সপাটে বলে বসেন, যে ঐ ভদ্দরলোকের সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রটি তাঁর পড়া, তো সেই পত্রে যে ডিজাইনটি অধ্যাপক প্রস্তাবনা করেছেন, সেটিই কী সন্ত লেনিন ও সন্ত মার্ক্সের মহান বাণীর অনুসারী? আগেই বলেছি, ব্লিস ছিলেন মোনোলিঙ্গুয়াল, দোভাষী ভয়ে প্রশ্নের অনুবাদ করতে পারছেন না সেখানে। ব্লিস আবার-ও বলেন, ঐ ডিজাইন-ই কি তাহলে ‘অফিশিয়াল পার্টি লাইন?’ ঐভাবেই[2] এগ্রিকালচারাল ডিজাইন করতে হবে এমন কথা কী লেখা আছে পার্টির কেতাবে? যদি থাকে, তাহলে ব্লিস স্বীকার করেন নিচ্ছেন যে উনি ঐ মহান কমিউনিস্ট ধর্মের অবমাননার দায়ে দোষী, এবং সেই অর্থে তিনি একজন প্রকৃত নাস্তিক। শেষমেশ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, ব্লিস শুধু একজন নিরীহ, অজ্ঞ আমেরিকান বৈ কিছু নন – এরকম লোককে গবেষণা করতে দেওয়া যেতেই পারে, শুধু শর্ত এই —কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে হবে। এই সদস্যপদ থাকার দোষে, অনেক পরে ১৯৫০-এর দশকে আমেরিকান সরকার ব্লিস-কে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করবে, তবে সে গল্প অন্য। ব্লিস লেনিনগ্রাদে ফিরে প্রবিট মডেলের উপরেই গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন, পেপার লেখেন এক-এক করে, যতক্ষণ না রাশিয়ায় বিজ্ঞানীদের পক্ষে টিকে থাকাই বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। একদিন সেই আমেরিকান বান্ধবী আচমকা উপস্থিত হন ব্লিসের সেই ল্যাবটিতে, প্রায় জোর করে ঐ সুটকেস বগলদাবা করেই সেইদিন-ই লেনিনগ্রাদ থেকে পালিয়ে আসেন ব্লিস - রিগা, লাটাভিয়াতে।
১৯৩৮ সালে শেষমেশ আমেরিকায় ফেরেন ব্লিস। প্রথমে যোগ দেন কানেক্টিকাট এগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেন্ট স্টেশনে। তারপর ১৯৪২-১৯৬৭, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে। এর-ই মধ্যে ১৯৪৭ সালে ব্লিস আরও কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তৈরি করে ফেলেন ইন্টারন্যাশনাল বায়োমেট্রিক সোসাইটি – আই-বি-এস। কারণ? সেই বছরের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের (আই-এস-আই, কিন্তু এ বড় আই-এস-আই) কনফারেন্সে গিয়ে ব্লিস দেখেন যে কনফারেন্সে বায়োমেট্রিক কাজের প্রায় কিছুই নেই। “It seemed to me outrageous that the field which led all others should have been treated so shabbily."। আনন্দের কথা এই যে, বায়োমেট্রি, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, বায়োইনফরম্যাটিক্সের সে দুর্দিন বহুদিন হল ঘুচেছে। এখন সেই আই-বি-এস বৃহৎ একটি সংস্থা, প্রায় পাঁচ-ছ’হাজার সদস্য নিয়ে উত্তর আমেরিকার অন্যতম রাশিবিজ্ঞানের কনফারেন্স ইনারের আয়োজক। স্যালসবার্গ জানিয়েছেন, এই সব ঘটনার অনেক-অনেক পরে, ১৯৬০-এর দশকে রাশিয়াতে ব্লিস ফেরৎ যান। ততোদিনে ব্লিস আই-এস-আইয়ের ফেলো, স্বনামধন্য মানুষ। লেনিনগ্রাদ গিয়ে দেখেন সেই সময়কার চেনা কেউ-ই আর বেঁচে নেই, কেউ মারা গেছে স্তালিনিস্ত পার্জ-এ, কেউ বিশ্বযুদ্ধের আগুনে। শুধু সেই রাশান বাড়িউলি তখনও বেঁচে, আবার বছর কুড়ি পরে সেই সেই এক-ই ভাবে দেখা হয় তাদের।
শুরু করেছিলাম প্যারাসেলসাসের গল্পে। শেষ করবো আবার তাঁর-ই গল্পে। তিনিও এক বিচিত্র বর্ণময় চরিত্র। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত - কিন্তু ভয়ানক কুঁদুলেও। প্রায় কখনই এক জায়গায় থিতু হতে না পেরে নানা দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারাজীবন, কিন্তু সেই ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেই লিখে গেছেন একের পর এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। যদিও স্বভাবদোষে প্রকাশ করতে দেরি হয়েছে অনেক। বিষ যে শুধু মাত্রা-নির্ভর, সেই বিখ্যাত উক্তিটি যে বইতে সেটিই লেখা হয় ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে-এ আর প্রকাশিত হয় ১৫৬৪। প্যারাসেলসাসের দর্শন তবুও ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়ায়। শুধু পশ্চিম গোলার্ধের গজদন্তমিনার নয়, প্যারাসেলসাসের উল্লেখ পাই স্বয়ং বঙ্কিমের লেখায়, বঙ্গদর্শনে।
“প্যারাসেলসাস আজ বুঝিয়াছেন, “সময় বহিয়া যায়” এ কথার অর্থ কি ? জীবন সম্বন্ধে প্যারাসেল্সাস কি লিখিয়াছেন ? পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা গেল, লেখা রহিয়াছে -- “সময় বহিয়া যায়, যৌবন চলিয়া যায়, জীবন স্বপ্নমাত্ৰ—কালের এই অবিরাম ধ্বনি। যত লোক জন্মিয়াছে, সবাই এ কথা শুনিয়াছে এবং বলিয়াছে । তবু, ঋতুর পর ঋতু আসে-যায়, মানুষ হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটায়—হঠাৎ একটা মুহূৰ্ত্ত আসে, যখন চকিতে কথাটার অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়— এবং সেই মুহূৰ্ত্ত হইতে চিরকাল তাহার কুঞ্চিত ললাট, তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষু বলিয়া দিতে থাকে যে, ঐ প্রবাদবাক্যটির অর্থ সত্যসত্যই সে বুঝিয়াছে।”—এইরূপে প্যারাসেলসাস তাহার সাধনা ও সিদ্ধির মোট শিক্ষাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।“
সময় সত্যিই বহিয়া যায়, লেখাও দীর্ঘতর হতে থাকে, তবু গল্পের কী শেষ আছে? তাই এই প্রবন্ধ এইখানে শেষ। বিষের ইতিহাস অথবা ইতিহাসের বিষ - কিছুই ঠিক করে লেখা হ'লো না। আশা করি সে-ও আরেকদিন হবে।
যাওয়ার আগে, মনে করিয়ে দিয়ে যাই, প্যারাসেলসাসের মোটো, প্রতিকৃতির উপরেও যেটি উৎকীর্ণ। এই বিষাক্ত সময়ে, এই গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে যে কথাটা ভুলে গিয়েছি সক্কলেই!
"Alterius not sit, qui suus esse potest." অর্থাৎ, “Who can be himself, shall not belong to someone else."
সূত্রঃ
- Chester Bliss: An Anniversary Portrait – https://jhanley.biostat.mcgill.ca/anniversaries/ByTopic/Chester-Bliss.pdf
- Greenberg on Bliss (McGill) –
http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/hanley/anniversaries/ByTopic/ChesterBlissByBGreenberg.pdf
- Stats History – Chester Bliss (including USSR episode) – https://www.usu.edu/math/schneit/StatsHistory/ModernStatisticians/Bliss
- International Biometric Society – Our History – https://www.biometricsociety.org/about/our-history
- Bliss, C.I. (1934). The method of probits. Science, 79, 38–39.
- Bliss, C.I. (1935). The calculation of the dosage-mortality curve. Annals of Applied Biology, 22, 134–167.
- Paracelsus and Toxicology – ScienceDirect – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750018305808
- University of Zurich – Paracelsus Exhibition – https://www.paracelsus.uzh.ch/paracelsus.html
- PMC Article on Paracelsus – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4942381/
- Chemical Safety Facts – “The Dose Makes the Poison” – https://www.chemicalsafetyfacts.org/health-and-safety/the-dose-makes-the-poison/
- Chemical Safety – Chapter 1 – https://www.chemicalsafetyfacts.org/wp-content/uploads/ATR_Chapter1_X.pdf
- The Atlantic – Lab Mice Can’t Vomit (and Why That Matters) – https://www.theatlantic.com/science/archive/2023/04/lab-mice-rat-rodents-vomit-drug-testing-side-effects/673714/
- Salsburg, D. – Statistics for Toxicologists (Google Books) –
https://www.google.com/books/edition/Statistics_for_Toxicologists/hvb2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=toxicology+salsburg&pg=PR5&printsec=frontcover
- The Toxicity of Recreational Drugs By Robert S. Gable, https://www.americanscientist.org/article/the-toxicity-of-recreational-drugs
পরিশিষ্ট:
[1] আলু খেলে যে ঘিলু ভেস্তিয়ে যায়, আর বুদ্ধি গজায় না, এ কথা বলেছেন সুকুমার রায়, আশা করি সোলানিন তার কারণ নয়।[2] ব্লিসের এই সময়ের গল্প দুর্দান্ত বর্ণনা আছে ডেভিড স্যালসবার্গের লেখায়। স্যালসবার্গের গল্পে, ব্লিসের দেখা সেই পেপারটিতে চাষের জমির সমস্ত প্লটেই এক-ই ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ, এক-ই সার/কীটনাশক/অন্যান্য জিনিষ, প্রয়োগ করা উচিত বলে দাবী করা হয়েছিল, সাম্যবাদের সূত্র মেনে, আর ব্লিস ফিশারের স্কুলে দীক্ষিত – উনি জানতেন যে ঐভাবে এক্সপেরিমেন্ট ডিজ়াইন করে না, এক-একটা প্লটে এক-এক রকমের ট্রিটমেন্ট না দিলে বোঝার উপায় নেই কোনটা কেমন ফসল দেবে। তবে, এই গল্পটা আমার কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। অগত্যা, পাদটীকা।
বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিডিয়ান লিথাল ডোজ় তালিকা
LD₅₀ (মিডিয়ান লেথাল ডোজ) বলতে বোঝায় এমন মাত্রা—যা একটি নির্দিষ্ট প্রাণীদলের অর্ধেককে (৫০%) একক ডোজে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এটি সাধারণত মিগ্রা/কেজি (মিলিগ্রাম প্রতি কেজি শরীরের ওজন) এককে প্রকাশ করা হয়। টেবিলের LD₅₀ মানগুলি ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে প্রাপ্ত। এই মানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে নির্ধারিত হয় এবং মানুষের ক্ষেত্রে আনুমানিক হিসেব দেওয়া হয়। মূলসূত্রঃ https://www.chemicalsafetyfacts.org/wp-content/uploads/ATR_Chapter1_X.pdfপদার্থ (Substance)
মন্তব্য (Comments)
LD₅₀* (মিগ্রা/কেজি)
বটুলিন (Botulin) অত্যন্ত বিষাক্ত একটি যৌগ। ঠিক করে ক্যান না করা খাবারে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়; খাদ্য বিষক্রিয়ার মারাত্মক রূপ ‘বোটুলিজম’-এর কারণ। 0.00001 আফ্লাটক্সিন (Aflatoxin) শস্য ও বাদামে mold থেকে তৈরি ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক, কিছু পিনাট বাটার ও অন্যান্য বাদামজাত দ্রব্যে পাওয়া যায়। 0.003 সায়ানাইড (Cyanide) অতিবিষাক্ত পদার্থ, যা এপ্রিকট ও চেরির বীজে পাওয়া যায় এবং প্লাস্টিক, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ও রাসায়নিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় 10 ভিটামিন ডি (Vitamin D) মানবদেহের খাদ্যতালিকায় অপরিহার্য, তবে স্বাভাবিক খাদ্যমাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে বিষক্রিয়া ঘটায় 10 নিকোটিন (Nicotine) প্রাকৃতিকভাবে তামাকে পাওয়া যায়। সিগারেটে আসক্তি বাড়াতে যোগ করা হয়। 50 ক্যাফেইন (Caffeine) কোকো ও কফি বীজে পাওয়া যায়; একটি সাধারণ খাদ্য উপাদান 200 অ্যাসিটাইলসালিসাইলিক অ্যাসিড (Acetylsalicylic acid) অ্যাসপিরিনের সক্রিয় উপাদান 1,000 সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium chloride) সাধারণ লবণ 3,000 ইথানল (Ethanol) বিয়ার, ওয়াইন ও অন্যান্য মদ্যপ পানীয়ের অ্যালকোহল 7,000 ট্রাইক্লোরোইথিলিন (Trichloroethylene) একটি দ্রাবক এবং ভূগর্ভস্থ ও পৃষ্ঠজলের সাধারণ দূষক 7,200 সিট্রিক অ্যাসিড (Citric acid) কমলা, জাম্বুরা, লেবু ইত্যাদি সাইট্রাস ফলে পাওয়া যায় 12,000 সুক্রোজ (Sucrose) চিনি; আখ বা চিনি বিট থেকে পরিশোধিত 30,000
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি | তৃতীয় কিস্তি | চতুর্থ কিস্তি | পঞ্চম কিস্তি | ষষ্ঠ কিস্তি | সপ্তম কিস্তি | অষ্টম কিস্তি | সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি | ভক্স পপুলি | দুই লেজান্ড্রর গল্প | বিষের ইতিহাস, ইতিহাসের বিষ - Chester Bliss: An Anniversary Portrait – https://jhanley.biostat.mcgill.ca/anniversaries/ByTopic/Chester-Bliss.pdf
- আরও পড়ুনফলিবেই ফলিবে (২০২৬) - যদুবাবুআরও পড়ুনরাধিকা ও আর্শোলা - যদুবাবুআরও পড়ুনতাই যেন হয় - যদুবাবুআরও পড়ুনআলো ঘন হয়ে আসছে - যদুবাবুআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুননীলাক্ষী - Srimallar
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 b | 117.238.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২০:৪৭542679
b | 117.238.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২০:৪৭542679- দিব্বি হয়েছে। তবে প্যারাসেলসাস একটা পুরো প্রবন্ধের বিষয় .
-
যদুবাবু | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২১:২১542680
- ঠিক ঠিক ঠিক। এই লেখাটা লিখেই আমি ঠিক করেছি শুধু প্যারাসেলসাস-কে নিয়েই আরও পড়াশুনো করতে হবে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে ওঁর অন্যান্য দার্শনিক কাজকর্ম নিয়ে কিছু লিখলাম না, কিন্তু সেগুলোও পড়তে হবে। আপনার কিছু রেকো থাকলে প্লিজ বলুন।
বিষের ইতিহাস নিয়েও, কত রোমহর্ষক গপ্পো সেসব - অ্যাক রাশিয়াতেই কতো, তারপর বোর্জিয়াস! কিন্তু আমার এই বিষয়ে পড়া ননফিক বইগুলোর বেশিরভাগ-ই পশ্চিম-দুনিয়া-কেন্দ্রিক। আমাদের দেশের ইতিহাসে বিষ, বিষের প্রয়োগ (বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাস), এসবের উপর বই খুঁজছি।
 b | 117.238.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২১:৪৪542681
b | 117.238.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২১:৪৪542681- পূর্বের বিষ বলতে ঐ লাস্ট মুঘল বইতে পড়লাম। বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত হেকিম , স্যর টমাস মেটকাফকে থ্রেট দিয়েছিলেন, "বলুন স্যার , কদ্দিনে মরতে চান ? এক দিন, এক সপ্তা , এক পক্ষ , এক মাস না কি ছয় মাস? অর্ডার অনুযায়ী মাল সাপ্লাই করব । "
 কৌতূহলী | 115.187.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২১:৪৪542682
কৌতূহলী | 115.187.***.*** | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২১:৪৪542682- দারুণ লাগল ,আর সোভিয়েতের গল্পটা বেশ মজাদার লাগল , যদিও এটা মজার ঘটনা নয়। খিদে বেড়ে গেল বিষপান করার। এটা নিয়ে একটু ধারাবাহিক লিখুন না প্লিজ। সম্ভব হলে প্রোবাবিলিটি প্যারাডক্স এঁর মত এঁর ওপরও বই বের করতে পারেন ,দারুণ হবে।
-
হীরেন সিংহরায় | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২২:০৪542683
- খানিকটা বুঝলাম মনে হল বলে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে!
-
যদুবাবু | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২২:১৬542684
- @b ওঃ, লাস্ট মুঘল দুর্দান্ত। আমি ড্যালরিম্পলবাবুর বিশাল পাখা। ঐ সেই কবে সিটি অফ জ়িনস পড়েছিলাম। এখন নিয়মিত এম্পায়ার পডকাস্ট শুনি। তবে গোল্ডেন রোড পড়া হয়নি এখনো। আশা করি হতাশ করবেন না।
@কৌতূহলীঃ আরে অনেক ধন্যবাদ! হ্যাঁ, আর একটা অন্তত পর্ব লিখবোই। ইচ্ছে আছে বিষের ব্যবহার কীভাবে পাল্টালো, কোন দেশে কীরকম বিষ ব্যবহৃত হত, তার সাথে অন্যান্য শাখার সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে লেখার।
এই যেমন, ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এবারস প্যাপাইরাসের স্ক্রলে বিশদে বর্ণনা আছে আফিম (ওপিয়াম), আর্সেনিক ট্রাইক্সাইড, অ্যাকোনিটিন, ফাইসোস্টিগমাইন ইত্যাদি ‘বিষের’। এই শেষোক্ত বিষটি পাওয়া যায় ক্যালাবার বীন থেকে নিষ্কাশন করে - সেই ক্যালাবার বীন, অর্থাৎ এসেরিন, যার ব্যবহার হত প্রাচীন আফ্রিকায় দোষীদের শাস্তিবিধানে। হামানদিস্তেয় এই ক্যালাবার বীন বা এসেরিন থেঁতো করে যে দুগ্ধনিভ তরলটি পাওয়া যেত, উইচক্রাফটে অভিযুক্তদের পান করতে হত সেটি। মৃত্যু হলে ধরে নেওয়া হত, আসলেই সে দোষী, আর বমি করে বা অন্য কোনো ভাবে বেঁচে ফিরলে বেকসুর খালাস। পড়েই তো আমার আক্কেল গুড়ুম! ইকিরে ভাই, এ ক্যামন বিচার? বলাই বাহুল্য, সেই আদিম আদালতে আমরা কেউ-ই পৌঁছতে চাই না। এ মানে আমাদের মহামান্য সুপ্রিমের থেকেও খাজা কোর্ট।
বইয়ের কথা জানি না। তবে, ইচ্ছে আছে টিউশনির একটা দ্বিতীয় খণ্ড লেখার। দেখা যাক।
-
যদুবাবু | ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ২২:৩২542685
- @ হীরেনদা, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজ়ভেল্ট গ্রেট ডিপ্রেসনের সময়ে, এবং আগে বা পরে কী কী করেছিলেন পড়ছিলাম। মহামন্দার উপর বার্নানকের বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত কাজের কথা মনে পড়ল, এবং আপনার অর্থনীতি ও নোবেল বইটিও।
FDR যে এখনকার DOGE-এর মতই একটা জিনিষ করতে চাইছিলেন সেটা পড়ে বেশ আশ্চর্য হলাম। একটা ইন্টারেস্টিং পিস পেলাম, এখানে রেখে যাই।
Why FDR might have supported DOGE,
Roosevelt expanded government to help the nation climb out of the Great Depression. But he also recognized that too much bureaucracy was a big problem.
By Janie Nitze
https://archive.is/sdcYB
-
হীরেন সিংহরায় | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ০০:১০542687
- খোলা যাচ্ছে না!
-
যদুবাবু | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ০১:৩১542689
- আচ্ছা, আসলে অজ্জিনাল-টা বস্টন গ্লোবের, তাই পে-ওয়ালের পেছনে। এইবার দেখুন তো। এটা আমার ড্রাইভে তোলা পিডিএফ ফাইল। আশা করি খুলবে।
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ০৬:৩৬542690
- জ্জিও! ব্যাপক! আরও আসুক, আসতে থাকুক। কোন এক লেখায় বিষে-বিষক্ষয় নিয়েও?
 kk | 172.58.***.*** | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ০৭:১২542691
kk | 172.58.***.*** | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ০৭:১২542691- খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। আর যদুবাবুর হাতের তার! খুব ভালো লাগলো এই লেখাটা।
-
হীরেন সিংহরায় | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ১৩:১৫542696
- যদুবাবুধন্যবাদ , পড়া গেল! আমলাতন্ত্রের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি তাকে সীমিত রাখার চেষ্টা চিরকাল চলে আসছে । এফিশিয়েন্সির বিষয়টা দ্রুত তলিয়ে যায়, অফসরদের পোয়া বারো হয়। যেমন প্রনম্য সি নর্থকোট পারকিন্সন দেখিয়েছেন ব্রিটিশ নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কিন্তু আমলার সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে , আমলারা কে কোথায় বসেন তার খেলা আরেক রকম হুরে ফিরে ব্যাংকিঙের কথাই ভাবি – আমেরিকায় ফেডারেল রিজার্ভ ( যা ব্যাঙ্ক নয়, সরকারি নয়, যার শেয়ার কেনা বেচা যায় না ) এর বারোটি ডিসট্রিক্ট । সেটা যুক্তিযুক্ত কারণ দেশটা যে বিশাল কিন্তু এই শাখা গুলির অবস্থিতি লক্ষ্য করুন পাঁচটি গায়ে গায়ে ইস্ট কোস্টে , সেন্ট লুই থেকে মিনিয়াপলিস ফেডের দূরত্ব ২৫০ মাইল। ডালাস পারুলে পরবর্তী ফেড শাখা পাবেন ১৮০০ মাইল দূরে সান ফ্রান্সিসকোতে সেটি সাতটি স্টেট সামলায় ইনক্লুডিঙ দি ফিফথ লারজেসট ইকনমি অফ দি ওয়ার্ল্ড ! আমলাতন্ত্র ! আই এফ সি , ইউনিসেফের কর্মীরা আয়কর দেন না । নিজে দেখেছি তাঁরা বিজনেস ক্লাস ছাড়া ট্রাভেল করেন না , দূরত্ব যাই হোক ! একটা দুর্দান্ত কন্টেন্টের খোঁজ দিলেন
-
Subhadeep Ghosh | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ১৩:৫৮542697
- দারুন ভালো লাগলো।❤️
-
যদুবাবু | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ১৮:০০542701
- অমিতাভ-দা, থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে। কিন্তু এতো বেশি সময় লাগে এক-একটা লিখতে।
kk, হ্যাঁ ... সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং।
হীরেনদা, হ্যাঁ, আমলাতন্ত্র যে স্ফীতোদর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।আমার এ দেশের ব্যুরোক্রেসির সাথে প্রত্যক্ষ সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, অবশ্য সেটা রিসার্চের কাজ বেরোনো বা না বেরোনো নিয়ে, ডেটা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে ব্যুরোক্রেটিক রেডটেপিজ়মের ব্যাপার। ছোটবেলায় কাফকার নাটক মঞ্চস্থ করেছি, সেই অভিজ্ঞতা মনে পড়ে।@শুভদীপ - আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।
-
হীরেন সিংহরায় | ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ২০:৪৮542704
- ১৯৯০-৯১তে ডবল এ রেটিং হারানোর পরে কসট কাটিং শুরু হলো সিটি ব্যাংকে: সি ই ও জন রিড বলেছিলেন তিরিশ হাজার মিডল ম্যানেজার ছাঁটাই করলে খরচা কমবে কিন্তু বটম লাইন আরনিং বাডবে । তাই হয়েছিল। আর ছাঁটাই করলেই শেয়ার প্রাইস বাড়ে ! আমাদের মধ্যে চলতি সাবধান বাণী ছিল - ডিরেক্ট রেভিনিউ রেসপনসিবলিটি কখনো হাতছাড়া করবে না !কিন্তু সরকারি আমলা রাজে সেটা করা মুশকিল !
 প্রতিভা | 2401:4900:1c62:417b:394c:7374:4a5b:***:*** | ২৮ এপ্রিল ২০২৫ ১১:৪৭542717
প্রতিভা | 2401:4900:1c62:417b:394c:7374:4a5b:***:*** | ২৮ এপ্রিল ২০২৫ ১১:৪৭542717- সময় বহিয়া যাউক, লেখা দীর্ঘতর হউক। এমন লেখনী অমরত্ব লাভ করুক! বিষ যদি আসিল, বিষে বিষক্ষয়ও আসুক। কত যে দিগন্ত খুলিয়া গেল! কত সম্ভাবনা উন্মোচিত হইল।বিষ নয়, অমৃতভাগী হইলাম !
-
যদুবাবু | ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ০৪:২২542732
- @ হীরেনদা, ছাঁটাই করলে, বিশেষ করে ম্যাস লে-অফের পরে স্টক প্রাইস বাড়ে এটা তো দেখিই। এতে করে নাকি ইনভেস্টরদের সিগন্যাল দেওয়া হয় যে দেখো আমরা কস্ট-কাটিং করে বটম লাইন বাড়াচ্ছি, বা এফিশিয়েন্ট করা হচ্ছে। জি-ই-র জ্যাক ওয়েলচ-কে (উচ্চারণ সম্পর্কে নিশ্চিত নই) নিয়ে একটা বইয়ের সারাংশ পড়েছি। বইটার নাম দ্য ম্যান হু ব্রোক ক্যাপিটালিজ়ম -- পড়া হয়নি। আপনি এই মাস লে-অফের মিথ/মিথ্যা বা শর্ট-টার্ম/লং-টার্ম উপকার/অপকার নিয়ে যদি কখনো লেখেন (বা আগেই লিখে থাকলে তার লিংক দেন) তাহলে আগ্রহ সহকারে পড়ব। অবশ্য আপনার সব লেখাই আগ্রহ নিয়ে পড়ি। :)
(এই বইটা - https://www.simonandschuster.com/books/The-Man-Who-Broke-Capitalism/David-Gelles/9781982176426)
@প্রতিভাদি, :) ... হ্যাঁ, অবশ্যই। কত্ত ইন্টারেস্টিং জিনিষ আছে। এই যেমন বিষের ভয় থেকে নাকি এনশিয়েন্ট রোমে কাপে কাপ ঠেকিয়ে উল্লাস করার সূচনা। লিখেছে -- "... (T)he custom of clinking appeared exactly in ancient Rome. When a cup tapped on another cup, wine spilled from one cup into another (Cilliers and Retief 2014). What was a better guarantee that the enemy would be poisoned as well?"
এইসব বাদ গেছে। মিথ্রিডেটিস/মিথ্রিডেটিজ়ম নিয়েও একটু লেখার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সেই নামে দেখলাম একটা আস্ত বই-ই আছে, যদিও পড়া নেই।
এমনি, এই লেখাটা ঠিক ততটা ভালো হয়নি। মানে অনেকটা সময় লাগলো, তার বেশির ভাগ অবশ্য বিভিন্ন তথ্য-সংগ্রহ, অনুবাদ, কিন্তু লিখে ঠিক পুরোপুরি তৃপ্তি পাইনি। কিছু একটা নেই-নেই। আসলে ঠিক করে লিখতে গেলে যে মানসিক স্থৈর্য্য লাগে, সেটা বহুদিন হ'ল নেই।
-
Debasis Bhattacharya | ০১ মে ২০২৫ ১২:৪১542759
- দারুণ!!! আচ্ছা, ওই যে গান আছে, এক টানেতে যেমন তেমন, দু টানেতে রুগি, তিন টানেতে রাজা উজির, চার টানেতে সুখী --- এই সূত্রকেও কি ব্লিস সায়েবের স্কেল-এ ফেলা যায়?
-
হীরেন সিংহরায় | ০১ মে ২০২৫ ১৩:৫৮731006
- যদুবাবুজ্যাক ওয়েলশ ( আক্ষরিক অর্থে ওয়েলসের লোক কিন্তু তাঁর মূলটি আইরিশ এবং ক্যাথলিক ) পুঁজিবাদের সর্বনাশ করেন নি !তাঁর প্রথম বইটি আমার নিদারুণ অপছন্দ ( Straight from the Gut) , কেবলই জি ই তে হেন করেছেন তেন করেছেন তার ফিরিস্তি । বুঝি কেন তিনি নিউট্রন জ্যাক আখ্যা অর্জন করেছিলেন । কিন্তু জি ই ছাড়ার পরে তাঁর লেখা বই Winning আমার কাছে অত্যন্ত অর্থবহ , খুবই উপকারী ! ম্যানেজমেন্ট গুরু পেটার দ্রুকারকে নিশ্চয় প্রণাম করি , অনেক সু পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু নিজে কোন কম্পানি চালান নি ।লোক ছাঁটাই করাটা যতোই বর্বর মনে হোক , তার একটা লজিক থাকা দরকার – ওয়েলশ যেমন বলেছেন চাকরি থেকে ছুটি দিয়ে তিনি উভয় পক্ষের উপকার করেছেন , তা শুনতে যতোই খারাপ লাগুক । আমি নিজে তাঁর যুক্তি অনুসরণ করেছি কখনো। পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া শক্ত কিন্তু পরিবর্তন মুক্তিওদিতে পারে । এমন কাউকে বরখাস্ত করেছি যে অন্য কাজে অন্য কোথাও দারুণ সফল হয়েছে।প্রচুর কণট্রাডিকশন আছে- হাঙ্গেরিতে আমাদের বুদাপেস্ট ব্যাঙ্ক ডিলের সাফল্যের পরেই তিনি ব্যাংকটি কেনেন কয়েক বসার বাদে বেচে দেন কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবসার স্বাদ পেয়ে জি ই ক্যাপিটাল ফুল ফোরসে ব্যাংকিং শিল্পে নেমে পড়ে !অথচ তিনি স্বীকার করেছেন এ ব্যবসা তিনি ঠিক বোঝেন নি ( জি ই য়াজ আমেরিকার পঞ্চম বৃহৎ'ব্যাঙ্ক'!)।এই অভিজ্ঞতা একটা কেতাবের কন্টেন্ট ! সময় যে খুব কম আর বাংলায় ম্যানেজমেন্ট বই কেউ পড়ে না। ইংলিশটা আসে।
 অরিন | 2404:4404:4405:700:50f6:9e7f:8608:***:*** | ০১ মে ২০২৫ ১৫:৪১731008
অরিন | 2404:4404:4405:700:50f6:9e7f:8608:***:*** | ০১ মে ২০২৫ ১৫:৪১731008- যদুবাবুর লেখা বরাবরের মতন ভারি মনোগ্রাহী। প্যারাসেলসাসের সেই "কী যে বিষ আর কী যে বিষ নয়", লাতিনে যাকে বলে "dosis sola facit venenum" (dose makes the poison) অমোঘ সত্য, তবে মানুষ তো শুধু কতটা বিষে মানুষ মারা যায় সেইটাই বিচার করে না, বিষের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াও তো হয়, যে কারণে LD50 শুধু একটি মাত্রা, অন্যান্য আরো কিছু মাত্রা আছে, সেসব এখানে আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক । আরেকটা ব্যাপার যদুবাবুর লেখায় দেখলাম, গাঁজা নিয়ে। শুধুগাঁজা ফুঁকে মারা যাওয়া অসম্ভব, গাঁজার lethal dose প্রায় ৬৫০ কিলো, সেখানে এক ছিলিম মেরে কেটে ১ গ্রামের বেশী মনে হয় না হবে।
-
নিরমাল্লো | ০১ মে ২০২৫ ১৮:২৩731009
- ব্লিস সায়েবের গপ্পোটা শুনতে শুনতে সেই ছারপোকা মারা বিষের জোকটা মনে পড়ে গেল - যে এক একটি ছারপোকা ধরিয়া এক ড্রপ করিয়া গিলাইয়া দিবেন - মৃত্যু অনিবার্য।তবে জোকস এপার্ট - বড্ড ভালো লিখেছিস। এই কীটনাশক ব্যবহার করার গল্প শুনে, আমার এক এডভাইসারের কাজ মনে পড়ে গেল। এক কীটনাশক কোম্পানী দেখেছিল তাদের তৈরী কীটনাশক ল্যাবোরেটরিতে হেব্বি কাজ করে কিন্তু মাঠে খুব একটা কাজ করছে না। আমার এডভাইসার গবেষণা করে দেখল যে গেল আসলে কীটনাশকটা পাতাতে লেগেই থাকছিল না মোট্টে। তখন আবার পাতায় লাগিয়ে রাখার মত আঠালো জিনিস বানাতে হল আরকি! ল্যাবোরেটোরি আর ফিল্ডে কাজের মধ্যে ম্যালা ভ্যারিয়েবেল বেড়ে যায়।
-
যদুবাবু | ০২ মে ২০২৫ ০৬:৫৫731021
- @দেবাশিসদা, আহা ওর থেকেও ভালো আছে অরুণ নাগের চিত্রিত পদ্মে বইতে। এই যে ছবি দিলুম।

@হীরেনদা, প্লিজ় লিখুন। আপনার কেতাবগুলো সম্পদ। আমি বহু বহু লোককে ধরে ধরে পড়িয়েছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার বই পড়ে লব্ধ জ্ঞান বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে যে কলার তুলিনি এটা বললে মিথ্যাচারের দায়ে পড়ব।
@ অরিনদা, না না অপ্রাসঙ্গিক কেন? একাডেমিক্যালি ঐগুলো নিয়েই আসলে আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু পড়াশুনো শেষ হয়নি। পড়ছি।আর আমি লিখতে লিখতে এক জায়গায় এসে মনে হয় এইবারে থামা উচিত। তখন লিস্টে বাকি যা যা থাকে উড়িয়ে দিই। যেমন NOAEL লিখিনি, বা এল-ডি-৫০ এর থেকে যে এল-ডি-১০ বা ১ যে বের করা প্র্যাকটিক্যালি বেশি শক্ত, কেন শক্ত এসব লিখিনি।
আর গাঁজার লিথ্যাল ডোজ় সাড়ে ছশো কিলো এটা জানা ছিল না। এটাও জেনে গেলাম।@মাল্লো - মোক্ষম রেফারেন্স। অ্যাজ ইউজুয়াল।
পাতার গপ্পোটা আগে তোর কাছেই শুনেছিলাম বোধায়। সেই আইআইটি বোম্বেতে যখন দ্যাখা হ'ল। আর "ল্যাবে পাস, ফিল্ডে ফেলটু" - এই রকম বিভিন্ন উদাহরণ আর ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে কেউ লিখলে চমৎকার গপ্পো হত।
 :|: | 2607:fb91:8810:c662:94e7:9444:58cd:***:*** | ০২ মে ২০২৫ ০৮:৩৬731024
:|: | 2607:fb91:8810:c662:94e7:9444:58cd:***:*** | ০২ মে ২০২৫ ০৮:৩৬731024- লেখা তো ভালো কিন্তু "নির্বিষ অঙ্কের সাথে একটু বিষাক্ত ইতিহাস।"যুগ যুগ ধরে ভালোমানুষ ছেলেপিলেদের তেরো পাইয়ে দেওয়া অঙ্ককে নির্বিষ আর ইতিহাসের মতো অসাধারণ "বিষ"য়কে বিষাক্ত বলার জন্য তীব্র পোতিবাদ!ডোজ বেশী হয়ে গেলে বিষ হয়ে যায় কথাতেই বলে -- বিষ টক বা বিষ তেতো। তেমন দজ্জাল ছেলেমেয়েকেও অবশ্য বলে বিষকন্যা ইত্যাদি। তবে সেটা অন্য গান।এখন একটা টইতে বইছে মধুবাতা আরেকটিতে বিষ। মজার সমাপতন।
-
Debasis Bhattacharya | ০৬ মে ২০২৫ ২০:২১731125
- যদুবাবু, দারুণ দিয়েছেন! একে কি থ্রি পয়েন্ট স্কেল বলা যাবে?
 অরিন | 2404:4404:4405:700:444d:666b:5966:***:*** | ০৭ মে ২০২৫ ০৪:৩৫731133
অরিন | 2404:4404:4405:700:444d:666b:5966:***:*** | ০৭ মে ২০২৫ ০৪:৩৫731133- যদুবাবু, noael বা loael এর আলোচনা করতে হলে যে বিষয়টি নিয়ে আসতে হয়, আমার মনে হয় আপনার লেখায়, অন্তত এই লেখাটিতে তার অবকাশ ছিল না, কারণ, সেক্ষেত্রে বিষ শুধুই মৃত্যুর কারণ নয়, অন্যান্য অসুখের কারণরূপে তার ভূমিকা নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন হয় । যে কারণে noael বা loael, যে ধরনের dose-response-curve বিবেচ্য, sigmoid curve যাতে কিছুটা "নিরাপদ" বিষের আলোচনা হতে পারে, প্যারসেলসাস এর বাক্য অনুযায়ী , সেই ব্যাপারটি কিন্তু কর্কট রোগকারী বিষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তার কারণ বিষের প্রভাবে কর্কট রোগের উৎপত্তি অজানা ফলে এবং কতটা যে "safe dose", সেইটে তো নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, যে কারণে একটি linear model স্থির করতে হয়, এবং তার slope টি বিবেচ্য, যে প্রতি dose ই কর্কট রোগের কারণ, এবার dose বাড়লে কতটা risk বাড়ে সেইটে তখন দেখতে হয় । সে জটিল রাশিবিজ্ঞানের অঙ্ক আপনার চেয়ে কেই বা ভালো জানে? আপনি এ নিয়ে লিখুন, আমরা সবাই আগ্রহ সহকারে পড়ি ।
-
যদুবাবু | ০৭ মে ২০২৫ ০৫:৩৯731135
- চতুর্মাত্রিক - এই না না ইতিহাস দুর্দান্ত বিষয়, অঙ্কের পরেই আমার দ্বিতীয় পছন্দ। এমনিতে বিষ/বিষাক্ত যে কতরকমের বিশেষণ থুড়ি বিষেশণে চলে আসছে তার কী শেষ আছে, এই যেমন স্পিনার ভালো বোলিং করলে ধারাভাষ্যকার বলেন 'বিষাক্ত স্পিন'। @দেবাশিস-দা, অবশ্যই। তবে, আমি কোনোদিন টাইম-ট্রাভেল করতে পারলে পক্ষীদের সময় উপস্থিত হয়ে একবার স্কেলটা ঝালিয়ে নিতাম।@অরিনদা, হ্যাঁ এক্কেবারেই। ঐগুলো আলাদা স্বতন্ত্র একটা লেখার মতন। এগুলোও আসলে একরকমের ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে মনে হয় - যেখান থেকে বিভিন্ন মিসইনফর্মেশন ইত্যাদি তৈরি হয়। আবার উল্টোদিক-ও আছে।তবে কি না, এরপর ইচ্ছে আছে কলমোগোরভকে নিয়ে লিখব। এই আজকে স্প্রিং সেমিস্টারের ক্লাস শেষ হল। সামনে সামার। এখন একজন মাত্র পিএইচডি স্টুডেন্ট। তার সাথে একটু পেপারটেপার লিখব আর এইসব। :)
-
Debasis Bhattacharya | ০৮ মে ২০২৫ ১৫:১৬731165
- যদুবাবু, পক্ষী কিন্তু এখনও আছে! তাদের দিয়ে কাজ চোলবেনাকো?
-
Debasis Bhattacharya | ০৮ মে ২০২৫ ১৫:১৯731166
- এবং, কলমোগরভ নিয়ে বাংলায় কিছু পড়তে খুবই আগ্রহী। বিশেষত, সঙ্গে যদি অস্তিত্ব ও সম্ভাবনার মৌল ধারণা বিষয়ক কিছু ভেতরকার কথাবার্তা থাকে, আহা, জবাব নেইকো!
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc, kk, দ)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












