- বুলবুলভাজা ধারাবাহিক স্মৃতিকথা শনিবারবেলা

-
পেন্সিলে লেখা জীবন (১৭)
অমর মিত্র
ধারাবাহিক | স্মৃতিকথা | ২০ মার্চ ২০২১ | ৫২০২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - পর্ব ১ | পর্ব ২ | পর্ব ৩ | পর্ব ৪ | পর্ব ৫ | পর্ব ৬ | পর্ব ৭ | পর্ব ৮ | পর্ব ৯ | পর্ব ১০ | পর্ব ১১ | পর্ব ১২ | পর্ব ১৩ | পর্ব ১৪ | পর্ব ১৫ | পর্ব ১৬ | পর্ব ১৭ | পর্ব ১৮ | পর্ব ১৯ | পর্ব - ২০ | পর্ব ২১ | পর্ব ২২ | পর্ব ২৩
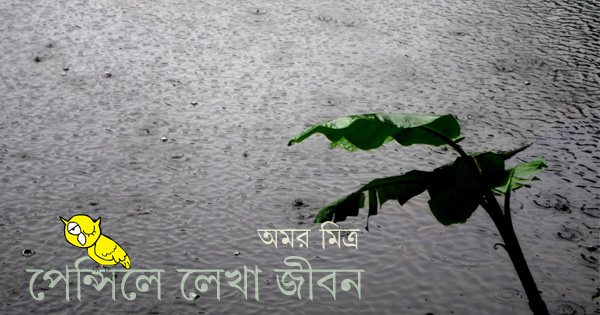
সতেরো শালতোড়ায় প্রথম শুনেছিলাম পছন্দপুরের কথা। শালতোড়া হয়ে একটি বাস যেত দুর্গাপুর মধুকুণ্ডা। মধুকুণ্ডা আসানসোল পুরুলিয়া রেলপথের একটি রেল স্টেশন। মধুকুণ্ডার গায়েই পছন্দপুর। পছন্দপুরের অদূরেই বরন্তী লেক এবং পাহাড়। এখন সকলে ছুটি কাটাতে যায়। জেলা পুরুলিয়া। শালতোড়ার অদূরে তিলুড়ি গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম এক গ্রাম। গায়ে গায়ে বেশিরভাগ মাটির বাড়ি। সেখানে থাকতেন কবি রণজিৎ সরকার, করুণা সেন, জীমূতবাহন আচার্য। তিলুড়িতে এক ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাতে ভাদু গান শুনেছিলাম। সারারাত। ওই অঞ্চলে ভাদু নিয়ে রীতিমতো উৎসব হয়। ঘরে ঘরে কুমারী মেয়েরা সারাদিন ভাদু সাজায়। সন্ধ্যার পর ভাদুর পুজো হয়। গান হয়। এ হল রীতিমতো লৌকিক এক উৎসব। মেয়েদের অধিকারের উৎসব। ভাদু ছিল পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজার কন্যা। শিশু বয়সেই তার মৃত্যু হয় জলে ডুবে। এ হল প্রচলিত লোককথা। তার নানা বয়ান আছে। তিলুড়ি গ্রামে যার গান প্রায় সারারাত শুনেছিলাম, সে ছিল কুন্তী বাউরি। তার বাবা ছিলেন মথুর বাউরি। মথুর ওস্তাদ ঝুমুর গায়ক ছিল। সেও গলা ছাড়ত ভাদুর গানে। আসলে তার বৃত্তি ছিল সাফাই কর্ম। এককথায় মেথর। আমি যখন যাই, তখন সে দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত। প্রায় ব্রাত্য। তার কথা আমাকে কবি রণজিৎ সরকার বলেছিলেন। কুন্তী কী গান না গেয়েছিল! অভিভূত হয়েছিলাম। তার গানে তার কষ্ট, তার বেদনা, তার অশ্রু ঝরে পড়ছিল। ভুলিনি তাকে। আমার উপন্যাস, সমাবেশ, নাম পরিবর্তনে ‘নয় পাহাড়ের উপাখ্যান’-এ সেই ভাদু গান শোনার অভিজ্ঞতা লিখেছিলাম। আঞ্চলিক কবিদের লেখা, মেয়েদের মুখে মুখে রচনা করা ভাদু গানের বই আমি কিনে এনেছিলাম অনেক। তিলুড়ি গ্রামে সেই বছর সরস্বতী পুজোর সময় আমি রণজিৎ সরকারের বাড়ি অতিথি হয়েছিলাম। বাড়িতে শিশুকন্যা, স্ত্রী, বাবা মা, আমি বাড়ি আসিনি কারণ সেখানে সেদিন মাছ ধরার পরব। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে যে মাছ ধরার উৎসব হতে পারে তা আমাকে অবাক করেছিল। আসলে মাছ ধরার পর মাছ ভাগ করা ছিল সেই পরবের মূল উদ্দেশ্য। একটি পুকুর কিংবা দিঘিতে থাকে অনেক অংশীদার। ১৬ আনা যদি মূল অংশ হয়, আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিল-শুভঙ্করী মতে হিসেব হত অংশ। এখন দশমিকে হিসেব হয়। তো সরকারি খতিয়ানে যেমন থাকবে সেইভাবেই মাছ ভাগ হয়। সেই মাছ সরস্বতী পুজোর দিন রান্না হয়। পরদিন ঠান্ডা পরব। ঠান্ডা পরব আমাদেরও আছে। গোটা সেদ্ধ হয় বিউলির ডালের সঙ্গে। পালং, বেগুন, রাঙা আলু ইত্যাদি। সামনে গ্রীষ্ম। আগুনের দিন। পুরুলিয়ার ওই অঞ্চলে ওই ঠান্ডা ভাত, মাছ খেয়ে শরীর শীতল করে ভয়ানক গ্রীষ্মকালের জন্য অপেক্ষা করে মানুষ। এই পরবকে স্থনীয় মানুষ বলে সিজানো পরব। এদিকে যা শীতলা ষষ্ঠী। আমি একটি গল্প লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায়, মৎস্য পুরাণ। গ্রীষ্মের শুরু থেকে, চৈত্রমাসের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমা বাতাস প্রবেশ করত শালতোড়ায়। প্রথম যখন তা ঢুকল, বেলা বারোটা নাগাদ অফিসে বসে চমকে উঠেছিলাম। শোঁশোঁ শব্দ, গুমগুম আওয়াজ। পশ্চিমা বাতাস শালতোড়ায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে টিলা পাহাড়ে। পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে গতিময় বাতাস। তার শব্দ শুনছি আমি। শালতোড়া, বাঁকুড়া আমার জীবনের এক সেরা সময়। প্রকৃতি, মানুষ ছিল আমার শিক্ষক। সত্যি কথা বলতে আমার শিক্ষক প্রকৃতি আর মানুষই। কলকাতার মনোহর একাডেমিতে ইস্কুলে মুখচোরা বালকটিকে মাস্টারমশায়রা তেমন চিনতেন না। দণ্ডীরহাটে চিনতেন। দণ্ডীরহাট ইস্কুলে রেজাল্ট ভালো হত। কলকাতায় তেমন হয়নি, কারণ বাড়িতে এত লোক। পড়ার জায়গা কোথায়, পড়া দেখিয়ে দেবেই বা কে? বাবা উদাসীন, অফিস, রামকৃষ্ণ মিশন, কথামৃত নিয়ে ব্যস্ত। মনোহর একাডেমিতে ক্লাস নাইনে রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। পরের দু-বছর খুব মন দিয়ে পড়ে হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট। ইস্কুলে বাংলার স্যার, হেডস্যার অজয়বাবু চিনতেন বাংলা ভালো লিখি বলে। ইংরেজির একজন মাস্টারমশায় শৈলেনবাবু এসেছিলেন ক্লাস নাইনে। তিনি ছিলেন অন্যরকম। আধুনিক। ইংরেজি ডায়ালগ লেখার একটি ক্লাস ছিল। তিনি দূর মঙ্গল গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কথোপকথন লিখিয়েছিলে। বিপ বিপ বিপ… মহাজাগতিক সংকেত আসছে পৃথিবীতে। বাড়িতে ‘আশ্চর্য’ পত্রিকা আসত। সেই পত্রিকায় কল্পবিজ্ঞান ছাপা হত। সত্যজিৎ রায়ের অনুবাদে রে ব্র্যাডবেরির গল্প পড়েছিলাম তখন আমি শারদীয় সন্দেশে। সব মিলিয়ে কল্পিত সংলাপ লিখেছিলাম। ইংরেজি ভালো হয়নি। কিন্তু প্রয়াসেই খুব খুশি হয়ে শৈলেনবাবু আমাকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন। স্নেহ পেয়েছিলাম দু-বছর। তিনি ইস্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী করেছিলেন বড়ো করে। মুকুট নাটকে আমি খল চরিত্র, ধুরন্ধর হয়েছিলাম। রবীন্দ্রজয়ন্তীর রবিপ্রণাম মঞ্চে আমি নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেছিলাম। দেয়াল পত্রিকায় লিখেছিলাম। যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করলাম, তখন স্কুল ত্যাগ করে কলেজে চলে গেলাম। স্কটিশের কেমিস্ট্রির অধ্যাপকরা তেমন চিনতেন না। তেমন কোনো শিক্ষক আমি পাইনি যাঁরা এই মুখচোরা সাধারণ ছেলেটিকে অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু সেই অভাব মিটে গিয়েছিল গ্রাম ভারতবর্ষের কাছে গিয়ে। মানুষের কাছে গিয়ে। তাঁরাই আমার শিক্ষক। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি আমার আত্মপ্রত্যয় জাগিয়েছিলেন সেই দূর আরম্ভের দিনে। হ্যাঁ, আমাদের ব্যাচ ইস্কুল থেকে বেরোনোর এক বছর বাদে এক শীতের সময় বন্ধু নিমাই বলল, শৈলেন স্যার মারা গেছেন। আমরা কয়েক বন্ধু কাশী মিত্তির ঘাটে ছুটেছিলাম। রাত হয়ে গেছে। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাওয়া ছিল বিপজ্জনক, বিশেষত রাতে। বাড়িতে বললাম স্যার মারা গেছেন, শ্মশানে যেতেই হবে। সে আমলে পাড়ায় পাড়ায় কিছু যুবক ছিল কেউ মারা গেলে তারা শ্মশানে যেতই। কেউ কেউ বিশ্বাস করত ১০৮ বার শ্মশানবন্ধু হওয়া মহাপুণ্য। দেবাশিস চ্যাটার্জি, আমাদের চেয়ে বয়সে বড়ো, আমার মেজদার সহপাঠী ছিল এক সময়। আমাদের সঙ্গে এইচএস। সে ছিল শ্মশানে। আগেই গিয়েছিল। আমাদের আটকেছিল রাজবল্লভপাড়ার কিছু যুবক। জেরা করেছিল মিনিট কুড়ি। তারপর ছেড়েছিল। সারারাত শ্মশানে থাকা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আর-একটা কথা বলি, সত্য। তখন কাঠের চুল্লি। আগুনে পুড়ছেন স্যার। দেবাশিস ডোমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে চুল্লির কিছু দূরে। আমি সরে এসেছি দেখতে না পেরে। স্যার মহাজাগতিক হয়ে যাচ্ছেন। বিপ বিপ বিপ। মহাকাশ থেকে সংকেত আসছে। একটি লোক উদাত্ত গলায় গাইছে, ‘মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে’--সুমন কল্যাণপুরের এই গান আমি আগে শুনিনি। সেই বছর হয়তো পুজোয় বেরিয়েছিল রেকর্ড। ওই গানের সঙ্গে শৈলেনবাবুর স্মৃতি জুড়ে গেল। জুড়ে রয়েছে এখনও। শালতোড়ায় থাকতে ১৯৮৮-র ১২ জানুয়ারি সমরেশ বসুর প্রয়াণ হয়। তখন আমি কলকাতায় ছিলাম কয়েকদিনের জন্য। সমরেশ চলে গিয়েছিলেন আগের রাতে। আমাদের একটি ল্যান্ডলাইন ছিল। সেখানে খবর দিয়েছিল বন্ধু, অকালপ্রয়াত লেখক রাধানাথ মণ্ডল। বেলভিউ নার্সিং হোমে আমরা বন্ধুরা গিয়েছিলাম। সমরেশ বসু ছিলেন সেই সময়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর পুত্র লেখক নবকুমার বসু, আমাদের বন্ধু। বন্ধুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। সমরেশের শেষকৃত্য হবে নৈহাটিতে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর পরিবার। একটি লরিতে করে তাঁর দেহ গিয়েছিল নৈহাটি। সামনে ছিল পুলিশের সাইরেন বাজানো গাড়ি। রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা করেছিল। লরিতে সমরেশের পায়ের কাছে তাঁর পুত্র এবং পুত্রপ্রতিম লেখক আমরা, রাধানাথ, সুতপন চট্টোপাধ্যায় আর আমি ছিলাম। আর ছিলেন সমরেশ অনুরাগী বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাক। সে ছিল এক মহাযাত্রা। নৈহাটি পৌঁছোলে দেখি লোকে লোকারণ্য। কত মানুষ আর কত মানুষ। কলকাতা থেকে ট্রেনেও অনেকে গিয়েছিলেন। স্বপ্নময়ের কথা মনে আছে। ওই অঞ্চলে বসবাস করতেন যাঁরা, হালিশহরের সুব্রত মুখোপাধ্যায় তো ছিলেনই। আর ছিলেন যে কতজন, অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, সোমনাথ ভট্টাচার্য, আরও কারা কারা। সমরেশ নৈহাটি অঞ্চলের শ্রমিকদের কাছে ছিলেন ঈশ্বরপ্রতিম। তাঁর উপন্যাস, গল্পে এই অঞ্চল কত ভাবেই না উঠে এসেছে। বি টি রোডের ধারে, উত্তরঙ্গ, শ্রীমতী কাফে, জগদ্দল, সওদাগর এইসব উপন্যাসে একটা সময়ের ইতিহাস লেখা রয়েছে। আমরা লরি থেকে নামতেই সমরেশ বসুকে আর দেখতে পাইনি। তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে কোনোরকমে বেরিয়ে এসে এক পাশে সরে এসে মানুষ দেখতে লাগলাম, মানুষ। সমরেশ বসু নিয়ে আমার দুই স্মৃতি আছে। তখন তিনি মহানগর পত্রিকার সম্পাদক। আমি মহানগর পত্রিকায় একটি গল্প দিলাম ১৯৮৪ নাগাদ। মাস দুই বাদে এক দুপুরে পত্রিকা অফিসে গেছি খোঁজ নিতে, গল্পের ভবিষ্যৎ কী জানব। যিনি সাহায্যকর্মী তিনি বললেন, এখন তো স্যার মিটিঙে বসেছেন মালিকের সঙ্গে, এখন দেখা হবে না। বসব শুনে তিনি বললেন, ঘণ্টা দেড় বসতে হবে কিন্তু, মিটিং অমনিই হয়। তাই সই। অফিস ছুটি নিয়েছি এইসব কাজ করার জন্য। সাহায্যকর্মী তরুণীটি আমাকে একটি স্লিপ দিলেন। নাম ঠিকানা ভরতি করলাম। তিনি সেইটা মালিক দিব্যেন্দু সিংহর ঘরে দিয়ে এলেন। সেখানেই সমরেশ মিটিং করছেন। আমি কী আর করব। চুপ করে বসে আছি। মিনিট দশও বসতে হয়নি। সিল্কের পাঞ্জাবি, ধুতি পরা সাহিত্যের রাজপুত্র বেরিয়ে এসেছেন। কে অমর মিত্র? চমকে উঠে দাঁড়িয়েছি। সমরেশ বসু। তিনি আমাকে বসতে বলে আমার পাশে বসলেন, বললেন, গল্প পছন্দ হয়েছে, পরের মাসে যাবে, বললেন, আমাকে পুজোসংখ্যার জন্য একটি গল্প দেবেন। পিঠে হাত রেখেছেন সমরেশ। পুজোসংখ্যায় আমার গল্প ছাপা হয়েছিল। পিতৃপ্রতিম এই লেখকের স্পর্শের কথা মনে পড়লে এখনও শিহরিত হই। যখন ‘তিনি দেখি নাই ফিরে’ লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, রামকিঙ্কর বেইজকে অনুসন্ধান করতে, বাঁকুড়া যাচ্ছেন, শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন, সেই সময় এক রাত্রে বন্ধু রাধানাথ মণ্ডলের অতিথি হয়েছিলেন তিনি। নৈশাহার করে ফিরবেন। কিঞ্চিৎ পান হয়েছিল। আমি কত প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উপন্যাস লিখতে তাঁর পরিশ্রমকে আমি মনে রেখেছি। যদিও একটি কথা বলে রাখি, জীবনীমূলক উপন্যাস আমি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি না। কিন্তু সমরেশ বসু সেই রাত্রে বলেছিলেন মূল্যবান সব কথা। তিনি শিল্পীর আত্মাকে ছুঁয়ে দেখতে চাইছেন। শিল্পের আত্মাকে। তা তিনিই পারতেন। শেষ হয়নি ওই লেখা। প্রয়াণ হল লিখতে লিখতে। প্রকৃত লেখকই তাঁর জীবনদর্শন এবং শিল্পকে মেলাতে চান। সমরেশ বসুকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭৬ নাগাদ, সরস্বতী পুজোর দিনে নৈহাটিতে। সেখান থেকে একটি সাহিত্যপত্রিকা বের করতেন বাপী সমাদ্দার, অলোক সোমরা। সেই পত্রিকা আয়োজন করেছিল সাহিত্যসভার। আমি গিয়েছিলাম প্রভাত চৌধুরী এবং কার কার সঙ্গে। কয়েকটা মাত্র গল্প লিখেছি। কথা বলতে ভয় করে। বিকেল নাগাদ সমরেশ বসু এলেন। ধুতি পাঞ্জাবি পাম শু। সুসজ্জিত মানুষ। অবাক হয়ে দেখছি তাঁকে। প্রণাম করেছিল। কেউ কেউ পান করেছিল, কে যেন বলল, তুই কী লিখতে চাস বল, যা মাইক ধর, ঘোষণা করে দিচ্ছি, জিজ্ঞেস কর বিবর, প্রজাপতি না মহাকালের রথের ঘোড়া, আমরা কোন্ উপন্যাস ভালোবাসব? আমি বলব? সমরেশ বসুর সামনে। আমি কে? শত প্ররোচনা সত্ত্বেও মঞ্চে যাইনি। শেষ দেখা হয়েছিল প্রকাশকের ঘরে। ১৯৮৬ সাল। আমার সদ্য প্রকাশিত শারদীয় সংখ্যার উপন্যাস তিনি করবেন কি না জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখি সমরেশ বসু। বললেন, ভালো লিখেছ উপন্যাস, তবে আরও নিবিষ্ট হতে হবে, তুমি পারবে উপন্যাস লিখতে। আমার পক্ষে ওই কথাগুলি যেন আশীর্বাদ হয়েছিল। প্রকাশক, কলেজ স্ট্রিট পাড়ার কর্তৃত্বময় ব্যক্তিত্ব। গম্ভীর কন্ঠস্বর। সমরেশ বসুর কথা শুনে বললেন, দিয়ে যাও, ছাপব। তারপরের কাহিনি হৃদয় বিদারক। বই ছাপা আর হয় না। আমি থাকি শালতোড়া। কলকাতায় আসি। এসে খোঁজ নিই। হবে হবে শুনি। এক বছর গেল, দু-বছর গেল, তিন বছর গেল, বই আর বেরোয় না। ১৯৯০-এর বইমেলার পর ফেব্রুয়ারি এক হঠাৎ হয়ে যাওয়া তপ্ত দুপুরে গেছি তাঁর কাছে। তাঁর সামনে বসে আছেন এক অগ্রজ লেখক। খুব সিনিয়র ছিলেন না তিনি। আমি বইয়ের কথা প্রকাশক মশায়কে জিজ্ঞেস করতে তিনি ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, আপনি প্রায়ই আসেন কেন বলুন দেখি, বিরক্ত করেন কেন?
আমি হতবাক। তিনি উচ্চকন্ঠে বললেন, একদম আসবেন না, আমাদের কাজ আছে, সবার বই করতে হবে নাকি, আমি কি বই আপনার কাছে চেয়েছিলাম?
বললাম, না, আমি দিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছাপবেন কি না, আপনি বলেছিলেন দিতে। অপমানে মাথা নীচু হয়ে গেছে।
আমাকে বিরক্ত করবেন না, দরকার হলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান।
সকলে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তিনি বললেন, আগামীকাল এসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবেন, বের করে রাখতে বলব।
চার বছর ঘুরিয়ে চূড়ান্ত অপমান করে বললেন ওই কথা। আমার দু-চোখে জল এসে গেছে অপমানটা সকলের সামনে হল। আমি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে করুণা প্রকাশনীতে গিয়েছি। সব বললাম। বললাম আমি আগামীকাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসব, আপনি কি ছাপবেন? বামাবাবু বললেন, তিনি তো আগেই ছাপতে চেয়েছিলেন, দিলেই ছাপবেন, কিন্তু ঘটনাটা ভালো হবে না আমার পক্ষে। পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে ক্রোধ বেড়ে যাবে তাঁর। আমি নতুন লিখতে এসেছি। আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। উনি ক্ষতি করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। একটু অপেক্ষা করা ভালো। দেখা যাক কী হয়। বামাচরণবাবুর কথা শুনে আমি শালতোড়া ফিরে এলাম। আবার পনেরো দিন বাদে কলকাতা। বাড়িতে এসে দেখি একটি চিঠি সেই প্রকাশন সংস্থার কাছ থেকে। আমার জীবনপঞ্জি এবং বই সম্পর্কে কিছু কথা পাঠাতে বলেছেন। বই পয়লা বৈশাখে বের হবে। দিয়ে এসেছিলাম এক পরিচিত কর্মীর কাছে। নীচেই দেখা। মনে হয় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন সেদিনের ঘটনায়। বই বের হয়েছিল পয়লা বৈশাখে। ঘটনা হল এরপর দেখা হলে বা মুখোমুখি হলেই তিনি এগিয়ে এসে কুশল নিতেন। অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পর ফোন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। মনে হয় সেদিন তিনি কোনো কারণে মেজাজ হারিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই করে বলেছিলেন। পরে ভুল বুঝতে পারেন। সত্য সেটাই। মানুষের ভিতরে আলোই বেশি আছে, অন্ধকার কম। এতেই বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু অতবড়ো এক পদের অধিকারী ব্যক্তির একটা দায়িত্ব আছে। লেখক সে যতই অনামি হোক বা জনপ্রিয় না হোক তার সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলাই অভিপ্রেত মনে হয়। একজন লেখক হলেন প্রকাশকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তা আমি সমস্তজীবন ধরে দেখেছি বামাচরণ মুখোপাধ্যায় (করুণা প্রকাশনী), সুধাংশু দে (দেজ পাবলিশিং) কিংবা সবিতেন্দ্রনাথ রায় (মিত্র ও ঘোষ)-দের সঙ্গে মিশে। কী মধুর সম্পর্ক নবীন ও প্রবীণে। লেখকের সঙ্গে তাঁরা পারিবারিক ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলেন।
ফিরে যাই বেলিয়াতোড়ে। শালতোড়া থেকে আমি বেলিয়াতোড়ে বদলি হলাম। বাসে আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে দুর্গাপুর স্টেশন। শালতোড়া লাগত আড়াই ঘণ্টা। বেলিয়াতোড়ে মেস নয়, একা থাকি একটি ঘরে। পাড়াটির নাম রাধাবাজার। বেলিয়াতোড়ে রাধাবাজার, শ্যামবাজার, বড়োবাজার ইত্যাদি এলাকা আছে। ওই বেলিয়াতোড়েই শিল্পী যামিনী রায়ের জন্ম। ওখানকার পোটো পাড়ায় গিয়ে পটুয়াদের কাছেই তাঁর শিক্ষা আরম্ভ। কালীঘাটের পটচিত্রের প্রভাব যেমন আছে তাঁর অপরূপ চিত্রকলায়, তেমনি আছে বেলিয়াতোড়ের পটচিত্রের ছায়াও। এই ব্যাপারে শেষ কথা বলবেন শিল্পীরা। যামিনী রায় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথি আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায়ের জন্মও বেলিয়াতোড়ে। আমি একা থাকি। পাশের ঘরে প্রবীণা মাসিমা থাকেন। তিনিই বাড়ির মালিক। বাপের বাড়ি পাত্রসায়রে। এখানে স্বামীর ঘর। তাঁর মৃত্যুর পর এখন তাঁর বাড়ি। মাসিমা আমাকে ভালোবাসতেন। সকালে উঠে অফিসার (!) ছেলেটি সুটকেসটি জলচৌকির মতো রেখে, তার উপর কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসে, এমন তিনি দেখেননি। আমি চিরকাল ভোরে উঠি। উঠে জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে চা করি। দু-গ্লাস চা আর গুটিকয় থিন অ্যারারুট বিস্কুট খেয়ে লিখতে বসি। একটি খাটিয়ায় তোশক ফেলা। তার উপর চাদর। বালিশ। কম্বল ভাঁজ করা। একধারে একটি সেলফের উপর খাতা বই, ব্রিফ কেস, দেয়ালে ঝোলানো সাইড ব্যাগ। মুড়ির একটি টিন ছিল। আর ছিল খাদ্যদ্রব্যের গুটিকয় কৌটো বয়েম। বেলিয়াতোড়ের কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায় আমার সবসময়ের সঙ্গী ছিল। তার একটি ছোটো মণিহারি দোকান ছিল, আর ছিল জীবনবিমার লাইসেন্স। কোনোটাই ঠিকঠাক করতে পারত না, কিন্তু পড়ত খুব। কবিতা লিখত। সাহিত্যের আড্ডার খুব ভালো সঙ্গী ছিল। আমি যা লিখতাম, সে হত প্রথম পাঠক। মূল্যবান মতামত দিত। প্রণব বছর দুই আগে চলে গেছেন। অভাবকে অভাব বলে মনেই করত না। বাঁকুড়ায় বহু সাধারণ মানুষকে দেখেছি জীবন সম্পর্কে এক প্রসন্নভাব বহন করেন। উদাসীন। সংসারে থেকেও যেন সন্ন্যাসী। মন্দ এবং ভালো দু-রকম মানুষেই চারপাশ আকীর্ণ। বেলিয়াতোড়েই ছিলেন গায়ক সুভাষ চক্রবর্তী। অরুণ চক্রবর্তীর লেখা ‘ও তুই লালপাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা, হেথায় তুরে মানাইছে না গো…’ গানটি তিনিই প্রথম গেয়েছিলেন উদাত্ত গলায়। ক্যাসেট বেরিয়েছিল মনে হয়। আমার ঘরে বসে তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর গান। মফসসল বলে তাঁর খ্যাতি জন্মাতে জন্মাতেই ফুরিয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল গণসংগীত গায়ক অজিত পাণ্ডের কথা। ১৯৭৭ নাগাদ, কিংবা তার আগে পরে দিসেরগড়ের নিকটে চাষনালা কয়লাখনির ধসে বহু খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি একটি গান রচনা করেছিলেন, পাঞ্চেতের পাহাড়ে মেঘ জমেছে আহারে, ও চাষনালা খনির ভিতর মনের মানুষ হারাঞ গেল রে (স্মৃতি থেকে লিখছি গানের কথাগুলি, ভুল হতে পারে)। সেই গান আমাদের শুনিয়েছিলেন তিনি। আহা সে এক অপূর্ব গায়কী। বহুদিন চলে গেছেন অজিত পাণ্ডে। একটি গানেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বেলিয়াতোড়ে আমার অফিসের প্রবীণ ক্লার্ক সুশীলবাবুর কথা মনে থাকবে আজীবন। তিনি ইংরেজি লিখতে পারতেন খুবই ভালো। সেই আমলে বাংলা মিডিয়মে পড়া ম্যাট্রিক। সুশীলবাবুর জীবন ছিল গভীর এক বেদনায় পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিটি সন্তান জন্মের পর মারা গিয়েছিল। সাত-আটজন মনে হয়। তিনি আমাকে বলতেন তা। আমার কন্যা বছর তিন সাড়ে তিন। পরিবার নিয়ে গিয়েছিলাম ক-দিনের জন্য। সুশীলবাবুর কোলে ঘুরত চকোরি। বেলিয়াতোড়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে—বি ডি আর আর। সংক্ষেপে বি ডি আর। স্থানীয় মানুষ বলত বড়ো দুঃখের রেল। ন্যারো গেজ লাইন। কয়লায় চলা ইঞ্জিন। কয়লা ফুরোলে জঙ্গল থেকে কাঠপাতা নিয়ে এসে বয়লারে ঠেসে গাড়ি পরের স্টেশন অবধি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমন কাহিনি বলেছেন ওই লাইনের প্রাক্তন রেল কর্মচারী। আমি সেই রেলপথ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি অনেক। বেলিয়াতোড় থেকে রায়না অবধি গিয়েছি। মনে পড়ে ভাদ্রের রাতে ফিরছি সোনামুখীবাসী লেখক গৌর কারক, সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়, জিতেন চক্রবর্তী আরও অনেকের সঙ্গে। দেখছি রেললাইনের পাশে বিস্তীর্ণ চট্টান জমির উপর জংলা গাছে ঝাঁক বেঁধে আছে জোনাকি। আহা। প্রকৃতির কী অপূর্ব রূপ। মনে হচ্ছিল দীপাবলির রাত ছেয়ে আছে চরাচর জুড়ে। আমি ‘আগুনের গাড়ি’ উপন্যাসে ওই রেলপথের দু-পাশের জনপদের অতীত এবং অনতি-অতীতকে ছুঁয়ে যেতে চেয়েছিলাম। এখন সেই রেলপথ ব্রডগেজ হয়েছে। দামোদরের উপর রেলসেতু হয়ে তা চলে যায় হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনের মশাগ্রাম স্টেশন অবধি। কলকাতা থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার আর-একটা পথ হয়েছে। বেলিয়াতোড় স্টেশনের গায়ে একটা সিনেমা হল ছিল। নাম বিস্মৃত হয়েছি। দুপুর তিনটের শো-এ দর্শক ডাকা শুরু হত হামরাজ সিনেমায় মহেন্দ্র কাপুরের মধুর কন্ঠে অপূর্ব এক গান ‘এ নীলে গগন কি তলে…’ লাউড স্পিকারে বাজিয়ে। একই গান এক দেড় বছর ধরে শুনেছিলাম। বেলিয়াতোড় থেকে ১৯৮৯-এর জুন নাগাদ চলে আসি বড়জোড়ায়। বড়জোড়া দুর্গাপুর বেলিয়াতোড়ের মাঝখানে। বড়জোড়ায় ছিলাম ১০ মাসের মতো। বাঁকুড়াবাসের সময় গল্পলেখক দীপঙ্কর দাস গাড়ি নিয়ে একদিন আমার অফিসে হাজির। দীপঙ্কর চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। ট্রাইবুনালের বিচারক হয়েছিল। আমার লেখা দীপঙ্কর ও তার স্ত্রী সান্ত্বনা খুব পছন্দ করতেন। দীপঙ্কর বলত, তোমার জন্য আমার পারিবারিক জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে। সান্ত্বনা তোমার লেখা পছন্দ করে বেশি... হা হা হা। এমন ভালো বন্ধু আমি কম পেয়েছি। দীপঙ্কর এসেছিল বাঁকুড়ায় সরকারি কাজেই। চলে এল আমার অফিসে। বলল, পাব বলে ভাবিনি, চলো। নিয়ে গেল সোনামুখী।
লেখকের জীবনে মান-অপমান লেগেই থাকে। অপমান একটা জেদ তৈরি করে দেয়। গিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গে সাহিত্য উৎসবে। একা নই। ক-জন সতীর্থ ছিলেন। বাংলোর ব্যালকনিতে মদ্যপা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ছিলেন। আর ছিলেন উত্তরবঙ্গের কয়েকজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবী। রাত দশটা বাজতেই আমি ডিনার করে শুতে গেলাম। এই সময়ের ব্যত্যয় বিশেষ ঘটে না। তো শুয়েছি ভিতরের ঘরে। সামনেই ব্যালকনি। সেখানে আড্ডা হচ্ছে। সম্পাদক বললেন, আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে উনি কেন?
কে কার কথা বলছেন?
অমর মিত্র, উনি কেমন লেখক, কী লিখেছেন যে আপনাদের সঙ্গে ওঁকে ডাকতে হবে, আপনাদের পাশে বসার যোগ্য উনি?
আমি সব শুনলাম। কেউ এর বিপক্ষে একটি কথাও বলল না। উত্তরবঙ্গের সেই শহরে আমন্ত্রিত হয়েই গিয়েছিলাম সকলের সঙ্গে। কিন্তু অনুষ্ঠানসূচি যখন পরের দিন ঠিক হল, দেখি একটি গল্প পড়ার সুযোগ পেয়েছি। অন্যরা অনেক গুরুগম্ভীর সেমিনার করলেন। এসব পীড়িত করে না এখন। একবার এক রেস্তোরাঁয় আমাকে ক্রমাগত কুকথা বলে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি। বন্ধু রাধানাথ উঠে সেই ব্যক্তির কলার চেপে ধরেছিল, আর -একটি কথাও বলবে যদি দাঁত ভেঙে দেব। হ্যাঁ, সেই সম্পাদক পরে আমাকে যেভাবেই হোক পড়ে, বন্ধু হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, যখন আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম সেই রাতের কথা। আমি তখন ঘুমোইনি। জেগে ছিলাম। ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়েছিল সেই রাত্রে। তবে বিজ্ঞ সেই সম্পাদক যতই সাফাই পরে দিন, তিনি অসুস্থ হয়ে পি জি হাসপাতালে ভরতি হলে আমি ছুটে যাই সব ভুলে, সেই রাতে একজন আমন্ত্রিত মানুষ নিয়ে এই কথা রুচিগর্হিত সত্য। তার বিপক্ষে কথা না বলাও অরুচিকর।
(ক্রমশঃ)
ছবিঃ ঈপ্সিতা পাল ভৌমিককোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন। টেলিগ্রাম অ্যাপে পেতে চাইলে এখানে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনগ্যেরনিকা - অমর মিত্রআরও পড়ুনবিদায় সুবিমল মিশ্র - অমর মিত্রআরও পড়ুনআমার তারাশঙ্কর - অমর মিত্রআরও পড়ুনচাষবাস অধিবাস - অমর মিত্রআরও পড়ুনলম্বা হাত খাটো হাত - অমর মিত্রআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
Prativa Sarker | ২০ মার্চ ২০২১ ১৩:১২103898
অপমান জেদ বাড়িয়ে দেয়, তবে কোনো লেখক টবের গাছের মতো। নিরন্তর জল সার চায়। তারা কেউ এ লেখা লিখতে পারবে না।
-
 হীরেন সিংহরায় | ২০ মার্চ ২০২১ ১৫:১২103903
হীরেন সিংহরায় | ২০ মার্চ ২০২১ ১৫:১২103903 ধন্য হয়ে যাই আপনার কথা শুনে জেনে। একেবারে অমৃত কুম্ভ!
অনুমতি দিলে যোগ করি- চাষনালা খনি দুর্ঘটনা ১৯৭৫ সালে ২৭শে
ডিসেম্বর ৩৮০ জন মারা যান। সরস্বতী পুজোর সময় ওই সেদ্ধ খাওয়াটা আমরা বীরভূমেও সিজনো বলি!
 সমরেশ মণ্ডল | 2409:4061:20e:264a:d768:a682:4706:***:*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৭:১৯103906
সমরেশ মণ্ডল | 2409:4061:20e:264a:d768:a682:4706:***:*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৭:১৯103906খুব ভালো লাগলো দাদা, রঞ্জিতকুমার সরকার,অজিত পাণ্ডে,প্রণব চট্টোপাধ্যায়দের কথা।আমি ভুল করে না থাকলে মনে হয়,ভি আই পি রোড, উপন্যাস প্রকাশের কথা বলেছেন এখানে...
 অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৮:১৩103907
অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৮:১৩103907সমরেশ মণ্ডলঃ হ্যাঁ।
-
ইন্দ্রাণী | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:০৮103908
শ্রদ্ধেয় লেখক,
আপনি লিখছেন অপমান জেদ তৈরি করে দেয়। সে তো ঠিকই। একজন না -লেখক মানুষের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য।
কিন্তু যিনি শিল্পী, যিনি লেখক তার কাছে অপমানের অন্যরকম একটা তাৎপর্য থাকে না কি?
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখককে বিপন্ন হতে বলতেন; বলতেন, বিপন্ন হও বিপন্ন হও বিপন্ন হও। বলেছিলেন, "অনর্গল বিপন্ন অবস্থার মধ্যে অ্যাঙ্গুইশ অ্যাগনির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বুকের ভেতর থেকে যে সব অসম্পূর্ণ বাক্য উঠে আসে, সেগুলো ম্যাজিশিয়ানের মতো শাদা কাগজের ওপর যদি কেউ মেলে ধরতে পারে -তার পাশে বঙ্কিমও দাঁড়ায় না, টলস্টয়ও দাঁড়ায় না।"
ব্যক্তিগতভাবে, অপমানকে আমি এই বিপন্নতার মধ্যে রাখি যা একজন লেখককে একজন শিল্পীকে সৃষ্টি তে সাহায্য করে ভীষণভাবে - সেটা শুধু জেদ বাড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয় যেন। বিপন্নতা সঞ্জাত সেই সব শব্দ বাক্য সম্ভবত লেখায় ম্যাজিক তৈরি করে-শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন বলেছেন।
মনে হ'ল আর কি-
 অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৩৭103909
অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৩৭103909ইন্দ্রাণী। ঃঃ শ্যামল নিজে বিপন্ন হয়েছেন। ঝুকি নিয়েছেন। বা হয়ে গেছে। যুগান্তর উনি বন্ধ করেননি। উনি বিপন্ন হয়েছে। আবার আপোষ করতেন না। আপোষ আমিও করিনি নিজের মতো করে। তাই সারাজীবনেে কোনো স্থায়ী জায়গা হয়নি উপন্যাস লেখার। এই পথ কি ঝুঁকির পথ নয়? বিনা পয়সায় অনীক পত্রিকায় উপন্যাস লেখা। একজনের রসায়ন এক এক রকম। সব শেষে তো লেখাতেই আশ্রয়। সে যেভাবে হোক। জেদেই হোক বা অন্যভাবে হোক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সবাই পারেন না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। শ্যামল সেই রাত্রে থাকলে যা করতেন, আমি তা পারি না। দুর্বল মানুষ। তবে লেখার ভিতর মুক্তি সে যেভাবেই হোক। অপমানে রক্তের ভিতরেে কী জন্মায় কে জানে?
 অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৩৯103910
অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৩৯103910ইন্দ্রাণীঃঃ জেদ হলো লেখার জেদ। তা কি বলে দিতে হবে?
 অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৪৩103911
অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ১৯:৪৩103911ইন্দ্রাণীঃঃ বিপন্ন কি হওয়া যায়, মানুষের জীবনে তা আসে। কীভাবে আসে তা কেউ কি জানে? চাষ করার সময় কে ভেবেছিল সব ধান মাজরা পোকায় খেয়ে নেবে।
ঈশ্বরীীীতলার রূপোকথ।
-
ইন্দ্রাণী | ২০ মার্চ ২০২১ ২০:১৫103912
শ্রদ্ধেয় লেখক,
আপনি যে লেখার জেদের কথা বলছেন, সেটি বুঝতে পেরেছি।
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনাতে যাই নি। শুধু ওঁকে উদ্ধৃত করেছিলাম।
আসলে, মাঝে মাঝে মনে অনেক প্রশ্ন ঘাই দেয়-
অপমান, বিপন্নতা লেখককে কী দেয়- এই প্রশ্ন তার একটি।
লেখকের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য তো হয় না সচরাচর। আপনাকে সামনে পেয়ে আপনার ভাবনা বুঝতে চাইছিলাম আমার মত করে। যদি অন্যায্য কিছু বলে থাকি, মার্জনা করবেন।
 অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ২১:০৭103913
অমর | 103.242.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ২১:০৭103913ইন্দ্রাণীঃঃঃঃঃ আরে না না না। একটা কথার উত্তর তিনবারে দিলাম। কথার ভার আছে বলেই না।
 বিকাশ রায় | 103.125.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ২২:২০103915
বিকাশ রায় | 103.125.***.*** | ২০ মার্চ ২০২১ ২২:২০103915আপনার এই লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় সিনেমার পর্দায় দেখছি এক ভাললাগা জীবনের ছায়াছবি।
 অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ০৫:৪৩103922
অমর মিত্র | 103.242.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ০৫:৪৩103922বিকাশ রায়ঃ এই জীবন কি সিনেমার উত্তম সুচিত্রা মনে হচ্ছে। ভালো লাগা সিনেমার মতো। তাহলে তো হলো না লেখা।
 অলোক গোস্বামী | 103.87.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ১২:২৩103931
অলোক গোস্বামী | 103.87.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ১২:২৩103931এককথায় অনবদ্য।
দুইকথায়, সেই প্রকাশকের অনুগ্রহপুষ্টরা মৃত্যুর পর তাকে দেবপ্রতীম করে তুলেছেন। আপনার লেখায় তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত কারণে কারো মুড অফ থাকলেও তাঁর অধিকার থাকেনা অন্যকে অপমান করে সেই রাগ উশুল করা। এটা অভদ্রতা। তবুও সেই অভদ্রতার যোগ্য জবাব দিতে যে আপনি সেই প্রকাশকের নামোল্লেখ করেননি এটা দেখে ভালো লাগলো। আপনার ভদ্রতাকে সম্মান জানাতে আমিও নাম প্রকাশ করলাম না।
তিন কথায়, অজিত পান্ডের গানের লাইনটা এরকম-- ওই চাসনালার খনিতে মরদ আমার ডুব্যা গেল গো।
 অলোক গোস্বামী | 103.87.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ১২:২৯103932
অলোক গোস্বামী | 103.87.***.*** | ২১ মার্চ ২০২১ ১২:২৯103932...." ওই পাঞ্চেতের পাহাড়ে/ মেঘ জমেইছে আহা রে/ এমন দিনে হায় হায়/ মরদ আমার ঘরে নাই/ ওই চাসনালার খনিতে......"
 প্রবীর দত্ত, বেলেতোড় | 2409:4060:394:d233:b367:6048:79a8:***:*** | ২৬ মার্চ ২০২১ ১০:৩০104101
প্রবীর দত্ত, বেলেতোড় | 2409:4060:394:d233:b367:6048:79a8:***:*** | ২৬ মার্চ ২০২১ ১০:৩০104101আপনার লেখায় বেলেতোড়ের কথা পড়ে সেসময়ের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সুন্দর স্মৃতিচারণ!
 সুজিত দাশগুপ্ত । | 103.17.***.*** | ৩১ মার্চ ২০২১ ০৭:০৩104332
সুজিত দাশগুপ্ত । | 103.17.***.*** | ৩১ মার্চ ২০২১ ০৭:০৩104332উত্তরবঙ্গের এই সভা কোন বছরের ঘটনা জানার কৌতূহল হচ্ছে । আমি একানব্বই সালে উত্তরবঙ্গ থেকে চলে আসি।সেই সময় পর্যন্ত প্রায় সবাইকে চিনতাম । বিশেষত , শিলিগুড়ির মানুষজনদের।
অমর মিত্র আমার প্রিয় লেখক । লেখাটি পড়তে ভালো লাগছে ।
 সন্দীপ গোস্বামী | 2402:3a80:1162:f2bc::6acf:***:*** | ৩১ মার্চ ২০২১ ১১:৩৫104348
সন্দীপ গোস্বামী | 2402:3a80:1162:f2bc::6acf:***:*** | ৩১ মার্চ ২০২১ ১১:৩৫104348মানুষের মধ্যে আলো বেশি থাকে, অন্ধকার কম। সেইসব মানুষদের আলো এবং অন্ধকারের গভীরে ডুব দিয়ে অমরত্বের সাধনায় মুখচোরা একজন মানুষ, যার আত্মজীবনী জীবন চরিত হয়ে উঠছে। সত্যম, শিবম, সুন্দরম।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












