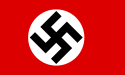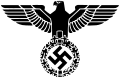- হরিদাস পাল ধারাবাহিক স্মৃতিকথা

-
হারিয়ে যাওয়া কোলকাতার গল্পঃ ৮ম পর্ব
Ranjan Roy লেখকের গ্রাহক হোন
ধারাবাহিক | স্মৃতিকথা | ১৫ জুন ২০২১ | ৪০৯৪ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন) (৬) বাঙালের আত্মীয়স্বজন, জিভের আড়, জিভের স্বাদ ইত্যাদি
কৈশোরে গড়ের মাঠে (তখন মনুমেন্ট ময়দান নয়, গড়ের মাঠই বলা হত) ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে মাউন্টেড পুলিশের তাড়া খেয়ে (ঘোড়সওয়ার পুলিশ) গ্যালারিতে বসার পর টের পেলাম — এটা ঘটিদের, থুড়ি মোহনবাগান সাপোর্টারদের এলাকা। মুখে কুলুপ এঁটে ওদের কথোপকথন শুনতে গিয়ে জানলাম — খেলার মাঠে বাঙালদের কোড নেম ‘জার্মান’! কেন? কে জানে! আরও শুনলাম যে বাঙালরা উদ্বাস্তু হয়ে ঘটিবাটি, মাদুর-শীতলপাটি, টিনের বাক্স-প্যাঁটরা, ছেঁড়া কাঁথা সব নিয়ে দলে দলে শ্যালদা স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মেই সংসার পেতে বসে। তারপর সেখানকার সাউথ স্টেশন থেকে লোক্যাল ধরে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া। আবার মাঝেরহাট ব্রিজ পেরিয়ে বেহালার দিকে। এভাবেই এরা গোটা কোলকাতাকে চারদিক থেকে ঘিরে দমবন্ধ করে দেয় । শহর ভরে যায় আবর্জনায়, আর এদের জন্যেই আমাদের কল্লোলিনী কোলকাতা তিলোত্তমা হতে পারে।নি।
হক কথা; কিন্তু জার্মান অভিধা কেন জুটলো? জিগাইতে সাহস হয় নাই। হয়ত অন্যরকম কথ্যভাষার স্বাদ সেই সময়ে ‘আমরা-ওরা’ হওয়ার কারক। আমাদের পরিবারকেই ফিরে দেখি।
দেশ স্বাধীন হয়েছে আগে এক দশক। বাঙাল পরিবারটি বর্ডার পেরিয়ে এই দাদুর দস্তানায় মাথা গুজেছে মাত্র বছর পাঁচেক আগে। ফলে অধিকাংশ সদস্যেরই জিভের আড় ভাঙ্গেনি। এক কাকাকে জিজ্ঞেস করা হল ম্যাট্রিক তো হল, এবার কলেজে কী পড়বি?
-- আই এচ ছি পড়বাম।
নাঃ, ক্যালকেশিয়ান হতে সময় লাগবে। নদীর এপার থেকে ওপার ‘বানাইল্যা হাওয়ার মাঝে’ মুখ খুইল্যা হাঁক কইর্যা কথা বলা ছেড়ে দিয়ে ছোট করে খুলে ঠোঁট গোল করে একটু নীচু গ্রামে কথা বলতে হবে।
নিজেদের দ্যাশের কথা কইতে গেলে নামের যে বিকৃতিগুলো সহজ অভ্যাসে বলা হত তা তাদের লিখিত নামের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন, ময়মনসিং জেলার বিশিষ্ট গ্রাম কায়স্থপল্লীকে ‘কায়েতপাগলি’, ‘কাপ্যাওলি’ এসব বলা যাবে না। গুইছ্যাডা না বলে বলতে হবে গুচিহাটা। একইভাবে, সত্যজিৎ সুকুমারের পৈতৃক গ্রাম মসূয়াকে ‘মৌস্যা’ বলা নৈব নৈব চ। এবং বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের ‘অপিনিহিতি’ (বাঙাল) রূপের কথা ভুলে ব্যবহার করতে হবে ‘অভিশ্রুতি’ (ঘটি) রূপ।
ক্রিয়াপদ (সাধু) অপিনিহিতি (বাঙাল) অভিশ্রুতি (চলিত বা ঘটি)
রাখিয়া রাইখ্যা রেখে
বাঁধিয়া বাইন্ধা বেঁধে
কাঁদিয়া কাইন্দা কেঁদে
কিন্তু নিজেদের ঘরে ডাকাডাকিতে নামের অপিনিহিতি রূপই মর্যাদা পেত। তাই মণি হত মইণ্যা, ননী নইন্যা বা লইন্যা, রঞ্জন অনায়াসে হয়ে যেত রঞ্জইন্যা!
এই দুঃখেই কবি গাহিয়াছেন --ইচ্ছা করে পরাণডারে গামছা দিয়া বান্ধি। আইরণ বাইরন কইলজাডারে মশলা দিয়া রান্ধি।।
বাঙালের বিপদ পদে পদে। বাজারে গেলে ইচামাছ বা কাইখ্যা মাছ বললে দোকানি হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। বলতে হবে চিংড়ি, বলতে হবে বকমাছ; সুবর্ণখইড়ক্যা নয়—সোনাখড়কে; বজুরি নয় কুচোমাছ, ইলশা নয় ইলিশ, রৌ নয় রুইমাছ, কাতল নয় কাতলা, আইর নয় আড়মাছ, ঘুইঙ্গা বা গুলশা নয়, দুটোকেই ট্যাংরা বলতে হবে। বেলে ও ল্যাটামাছকে বাইল্যাড়া ও ল্যাডা বলা নয়। কত বলব!
নিরিমিষ কিছু কিনতে গেলেও সেই সমস্যা। হেলঞ্চা নয়, হিঞ্চে শাক। নাইল্যাপাতা নয়, পাটপাতা। কাঢলের আলি নয়, কাঁঠালবীচি, শিমুরালি নয়, শিমবীচি, ভ্যারাইল নয় থোড়। বেগুনকে বাইগন বলা নিয়ে বহুকথিত পিজে বাদ দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু আজকের প্রজন্ম কি পঞ্চাশের দশকের এই ‘ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে’ যাওয়া পিজের সঙ্গে পরিচিত? তাই কিন্তু কিন্তু করেও জুড়ে দিলাম।
বাঙাল--বাইগন কত কইর্যা?
দোকানি-- বাইগন? বেগুন বলতে পার না ?
--ক্যান, বাইগন কী দোষ করল?
-- ভাল শোনায় না , তাই।
-- তাইলে বেগুন ক্যান, ‘প্রিয়তমা’ কইলেই পার।
ঘটির ঘটি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত ‘সধবার একাদশী’ নাটকে বাঙালের ক্যাল্কেশিয়ান হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিয়ে নির্মম পরিহাস করেছেন। বাঙাল চরিত্রটি ধনীর মোসাহেবি করতে গিয়ে সখেদে বলছে—কত চেষ্টা করলাম। সাহেববারির বিস্কুট খাইলাম, মদ খাইলাম, মাগিবারি গেলাম, বৌ বাইগ্যদরিরে বেশ্যার পায়ে হাত দিয়া দিদি ডাকাইলাম-- তবু কইলকাত্তাই হইতে পারলাম না ।
এই সুযোগে আমি বাঙাল একটু ‘বদলা’ নিয়ে নিই।
দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে এই গল্পটি ভবানীপুরের এক বয়োজ্যেষ্ঠ খানদানি ঘটি ভদ্রলোকের মুখে শোনা। উনি আবার শুনেছেন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের মুখে।
বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর নাম নাকি রজনী। উনি ডাকসাইটে সুন্দরী। একদিন দুইবন্ধু কাঁঠালিপাড়ায় বঙ্কিমের বাড়ির ছাদে রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া সেরে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছেন। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। রসিক দীনবন্ধু, বঙ্কিমের পেয়ারের ‘দীনে’, চিমটি কেটে বললেন—আহা, কী সুন্দর রজনী, তায় আবার চন্দ্র এসে জুটেছে।‘
বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা আর বলতে! একেবারে ‘দিনের’ মুখে হেগে দিয়েছে!
অথচ দেশভাগের আগে বাঙালদেরও র্যাগিং করার সু্যোগ ছিল। কায়েতপাগলি বা কায়স্থপল্লী নামক বর্ধিষ্ণু জনপদের বাসিন্দা জনৈক ক্ষেত্রমোহন পেটের ধান্দায় দক্ষিণ কোলকাতার গড়িয়াহাটের কাছে অধুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া আলেয়া সিনেমায় টর্চ হাতে সীট দেখানোর চাকরি করতেন; থাকতেন মার্কেটের পেছনে একটি মেসের ছাতের ঘরে। তাঁর গাঁয়ের স্কুলের সতীর্থ জনৈক রায়মহাশয় তখন কলকাতার কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়নরত। মাসের প্রথমে উনি জনাকয়েক উচ্চিংড়ে বন্ধু জুটিয়ে হাজির হতেন সেই মেসবাড়িতে। রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়তেন – ওরে ক্ষ্যাতরা, ক্ষ্যাতরা ঘরে আছস নি?
ক্ষেত্রমোহন শশব্যস্ত হয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে এসে হাত জোড় করে বলতেন—চুপ! চুপ! মাইনে পেয়ে গেছি। কী খাবি বল।
আবার পূজোপার্বণে গ্রামের বাড়িতে গিয়েও রক্ষে নেই । রায়মহাশয়ের পিতৃদেব গ্রাম সম্পর্কে জ্যাঠামশায়। বিজয়ার দিন তাঁকে প্রণাম করতে গেলে বিটলে বুড়ো ইচ্ছে করে চোখ কুঁচকে বলবেন – তুমি ক্যাডা? ঠিক চিনলাম না তো!
--আজ্ঞে আমি অমুকের ছেলে।
--অ! তা কী নাম?
-- (ঘটি উচ্চারণে) খেত্রো ।
-- কী কইল্যা ? জোরে কও।
-- খেৎ-রো—ও!
--বাবা, তুমার কী শরীর খারাপ হইছে? কইলাকাতার বাসায় প্যাট ভইর্যা খাও না ?
অল্পদিনেই আমরা ছোটদের দল জেনে গেলাম যে বেশ কিছু আত্মীয় আমাদের মত উদবাস্তু হয়ে এপারে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোলকাতার আশেপাশে সম্মানের সঙ্গে মাথা গোঁজার জায়গা করে নিয়েছেন। কাউকেই সীমান্তে রিলিফ ক্যাম্পে ঠাঁই নেওয়ার দুর্ভোগ পোহাতে হয় নি।
বাবা-কাকাদের মুখে শুনি তাঁদের তিন পিসিমার কথা। বড় পিসিমা আলিপুরদুয়ারের দাম পরিবারে; ধনপিসিমা ওপারের দেশের বাড়িতে। আর ছোটপিসিমা বেলঘরিয়ার কাছে নিমতায়। উনি আমাদের নিমঠাকুমা, পদবী অদ্ভুত—‘বীর’। সেই পরিবারের মেয়ে আমাদের লক্ষ্মীপিসি সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশুনো, নাচগানে কৃতিত্ব অর্জন করে পাশের একটি মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস হলেন। আমাদের বাড়ির মা-কাকিমা-পিসিরা কেউ চাকরি করেন না । কেউ কলেজের মুখ দেখেন নি। তাই হয়ত লক্ষ্মীপিসির গল্প বলতে গিয়ে শেষপাতে সবাই একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ফেলত; হয়ত নিজেদের অজান্তে। তারপরই শুরু হত অবধারিত পিএনপিসি। -জান ঠাকুরঝি? নিজে নিজে বিয়া ঠিক করছে। হেইজনও অন্য স্কুলে হেডমাস্টার। কিন্তু নাম অইল ‘রিপুদমন রায়’!
হাসির হররা!
কিন্তু হাসির রেশ বেশি দিন রইল না। খবর এল ওদের একমাত্র ছেলে উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় হয়েছে। আমাদের ঘরে কেউ প্রথম দ্বিতীয় নেই । সেই ছেলে আজকের খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কলামনিস্ট গৌতম রায় ।
ঢাকুরিয়ায় বাবাদের তুতোবোন --পারুলপিসি ও ঝুনুপিসি। হালতু যাদবপুরের দিকে আমাদের মন্টুকাকু; কালো পাথরে কোঁদা শালপ্রাংশু মহাভুজ! মা- বাবা তিনভাই তিনবোনের দায়িত্ব সামলাতে মার্চেন্ট নেভিতে কাজ নিয়েছেন। শিবপুরে আছেন নন্দীপিসেমশায়, পুলিসে কাজ করেন।
হরিণঘাটায় আছেন আর এক দাদু – বাবাদের ধনকাকা। গলায় তুলসী মালা, মুখে একগাল অজাতশত্রু হাসি। দেখলে কে বলবে উনি তিরিশের দশকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা চার বিষয়ে স্টার নিয়ে পাশ করেছিলেন! তারপর ময়মনসিং থেকে এসে কোলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলেন।
দিব্যি চলছিল।
কিন্তু ১৯২০ সালে নাগপুর অধিবেশনে ন্যাশনাল কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করল। চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধিজী একটু দ্বিধাগ্রস্ত, গণ-আন্দোলনের জোয়ার যে ‘সবিনয়-অবজ্ঞা’র রাজপথ ছেড়ে সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিহিংসার গলিপথে চলে যেতে যায়! এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে!
তা আমাদের ধনদাদু নীলমণি রায় একটু দেশের দশের কথা ভাবতেন, চলে গেলেন নাগপুর অধিবেশনে। সেখানে তখন ‘স্বরাজী’ অর্থাৎ মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের বোলবোলাও। স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের মুখে শুনলেন অমৃতবাণীঃ এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট স্বরাজ ক্যান নট!
ব্যস, নীলমণি রায়কে আর পায় কে! সোজা নাগপুর থেকে হাওড়ায় নেমে শ্যালদা গিয়ে পূর্ববাংলার ট্রেন ধরে ফিরে এলেন দ্যাশের বাড়িতে। বইখাতা বিছানাপত্তর পড়ে রইল বিদ্যাসাগর লেনের হোস্টেলে। বাবরি চুল মাথায় পড়াশুনা ছেড়ে ঘরে ফেরা নব্যযুবক, পুলিশের নজর পড়ল। সেসব দিনে ময়মনসিং জেলায় অনুশীলন পার্টির প্রভাব খুব; নীরদ সি চৌধুরির ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ বইয়ে এর কিছু উল্লেখ আছে। ত্রৈলোক্য মহারাজ মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়ি আসতেন। কিছু আর্থিক সাহায্য, কিছু পত্রিকা নেওয়া এসব হত। নীলমণি রায় কেস খেলেন, তবে উকিল জ্যেঠুর যোগাযোগে বাড়ি ফিরে এলেন ও বড়ভাইয়ের সঙ্গে কীর্তন গেয়ে, ফুটবল খেলে এবং বৈঠকখানায় ঢালাবিছানায় গড়িয়ে বাকি জীবন কাটালেন।
বিধির বিধানে তখনই লেখা হয়ে গেল যে অর্ধশতাব্দী পরে কোলকাতায় রায়পরিবারের বরতরফের নাতিদের মধ্যে সেই একই প্রহসন অভিনীত হবে। চেয়ারম্যান মাও যে বলেছেন—এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয়।
তবে উনি বোধহয় ওঁর জ্যেঠিমা, মানে আমাদের বড়মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ওঁর মা ছিলেন কড়াপ গাঁয়ের মেয়ে। বড়মার খুব চোপা ছিল। নিজের জায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হত একই ধুয়ো ধরে—আরে আমার কড়াপের খড়াপ রে!
তুলসীমালাধারী পরম বৈষ্ণব নীলমণি রায়ের গলায় চিনি কিছু কম পড়েছিল।
নীলমণি বাঙাল জিভে হলেন লনী, তারপর ‘লইন্যা’!
বড়মা সুখময়ী ফুট কাটলেন—হগলে গান গায় মধুরস বাণী,
লইন্যায় গান গায় ভেড়ার চেঁচানি ।।
নীলমণি নির্বিকার। কীর্তন চলতে থাকল আরও বছর দুই। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। সকালে ঘন দুধের বাটিতে আম দিয়ে নীলমণি জলখাবার সেরে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় গড়াচ্ছেন। চোখ জুড়ে এসেছিল, কুঁই কুঁই আওয়াজে চোখে মেলে দেখলেন সদ্য চোখফোটা একটি পাটকিলে সাদা কুকুর ছানা তাঁর মুখের কাছে এসে লেজ নাড়ছে। মনটা একধরণের ভালোলাগায় ভরে উঠল। উনি চোখ বুঁজে হুঁ হুঁ করে সুর ভেজে অক্রুর পালার গান ধরলেন—নিরানন্দ হইল পুরী-ই-ই-ই!
আর তখনই ঘটল ব্যাপারটা; ওই ই-ই-ই গিটকিরির সময় সারমেয় সন্তানটি লাফিয়ে ওঁর জিভ চেটে দিল। হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ বলে উনি লাফিয়ে উঠে গোবরের ছোঁয়া লাগিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে জিভ শুদ্ধ করলেন। ওঁকে সারাজীবন আর কীর্তন গাইতে শোনা যায় নি।
ঠাকুমার এক বোন ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী; তিনি দুইকন্যা নিয়ে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে এলে ওঁর কুচি দিয়ে শাড়ি পরার ধরন অন্তঃপুরের আলোচনার বিষয় হয়। আর তাঁর এক মেয়ের আঙুলে একটা তারের আঙটি মত। জানা গেল উনি সেতার বাজান, এবং ওটাকে মেজরাপ বলে। রান্নাঘরের গসিপ থেকে উনিও নিস্তার পেলেন না । সেতার বাজাইলে বুঝি সারাক্ষণ আঙ্গুলে পইর্যা থাকতে হয়! যত ভইগল্যাম।
ব্রাইট স্ট্রিটে একটি দোতলা বাড়িতে বড় বড় ঘর। চওড়া বারান্দা। করিডরে দেওয়াল থেকে ঝোলে হরিণের সিঙওলা মাথা। বাড়ির নীচে গাড়িবারান্দায় গাড়ি; ঠাকুর-চাকর-ঝি পরিবৃত সম্পন্ন সংসার। না , এঁরা উদ্বাস্তু ন’ন। এই বাড়ির মালিক আমার দাদুর প্রায় সমবয়সী মামা মোক্ষদা প্রসাদ ঘোষ ইংরেজ আমল থেকেই অবিভক্ত বাঙলার ভেটারিনারি জেনারেল। শেষ বয়সে গলায় ক্যান্সার নিয়ে আমাদের বাড়িতে শেষ দেখা করতে এলেন। আমার মাকে বারণ করে বললেন—কেউ যেন দোক্তা দিয়ে পান না খায়, পানের বাটা ফেলে দাও।
আমরা বাচ্চারা গলার ওপর মৌমাছির চাকের মত কিছু দেখে প্রণাম না করেই ছাদে পালিয়ে গেলাম।
আরেকটি গাড়ি কখনও সখনও আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়াত। হাসিমুখে নেমে আসতেন এক সুদর্শন পুরুষ, নিখিলরঞ্জন রায়। ঠাকুমার খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়, তিনি তখন হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের( তখনও লাইফ ইন্সিওরেন্স নাম হয় নি) বড়কর্তা। খানিকক্ষণের জন্যে আমাদের বদ্ধ তিনকামরার ঠাসাঠাসি ফ্ল্যাটে বয়ে যেত হাসিঠাট্টা-খোশগল্পের মুক্ত হাওয়া। কিন্তু এঁর বড়দা বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় নিজের ছেলের বিয়ের চিঠি বাড়ির ড্রাইভারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ায় ঠাকুমা বললেন—নীহার আইজ এত বড় হইছে যে নিজে আইতে পারল না ?
বাঙালের গোঁ!
এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঘটনাচক্রে এই শতকের প্রথম দশকে ই-টিভির বাংলা ক্যুইজ প্রোগ্রামে অংশ নিতে হায়দ্রাবাদের রামোজি রাও স্টুডিওতে গিয়ে দেখি পালা পড়েছে রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার ও ক্যুইজ মাস্টার জনৈক রায়মশায়ের সঙ্গে। উনি নীহাররঞ্জনের ভাইপো এবং নিখিলরঞ্জনের বড় ছেলে। দারুণ খেলছিলেন, কিন্তু কপাল খারাপ। ফাইনালে একটা কঠিন ‘আনপ্লেয়েবল বল’ এল, বাম্পার নয় বীমার।
প্রশ্নটা ছিল বার্বি ডলের আবিষ্কর্তা কে? উত্তর আমিও জানি না । তবে আমার প্রশ্নটি সহজ ছিল – হনুমানের মায়ের নাম কী?
ফলে আমি বাই ডিফল্ট কয়েক লাখ টাকা জিতে গেলাম। স্বর্গ থেকে সরযূবালা হাততালি দিলেন।
এত সব আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে দেখা করতে এলে বাচ্চাদের পোয়াবারো। তখন কড়েয়া রোডের কে সি মাইতি মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে রসগোল্লা আসে, সিঙারা আসে। আর আসে জিলিপি এবং বিশেষ দিনে ‘লাল দই’। তাতে বাচ্চাদের শেয়ার থাকা অবধারিত। কিছুদিন পরে বাড়ির অন্দরমহলে একটি ‘গুল্প’ চালু হল, মিষ্টির দোকানে ওই লাল দই জমাতে দোকানদার কেঁচো কেটে তার কয়েক ফোঁটা রস ফেলে, তাতে নাকি দুধ কেটে দই হওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়।
আমাদের জিভে শ্বেতাঙ্গী রসগোল্লার স্বাদ ম্যাড়মেড়ে, পছন্দ শ্যামাঙ্গী পান্তুয়া বা লেডিকেনি। আর সিঙারার সঙ্গে জিলিপি। যদি কখনও সখনও চমচম জোটে, আর ল্যাংচা? কিন্তু বাচ্চাদের জন্যে কোনটা ভাল সেটা তো বড়রা ঠিক করে দেয় । ফলে রঙিন মিষ্টি নয়, লজেন্স (আমরা বলতাম লেবেঞ্চুষ) মানা, দাঁত খারাপ হবে। সার্কাস বিস্কিট নয়, খেতে হবে একঘেয়ে ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট। কোন কাকা সদয় হলে এক আনা নিয়ে ছুট লাগাতাম মমতাজ স্টোর্স আর কিনে ফেলতাম ছোট ছোট হাতি ঘোড়া বিস্কুট, ফুটো করা তামার পয়সা দিয়ে টকঝাল ত্রিফলা লজেন্স। দোকানে চোখে পড়ত সরু কাঁচের একটা নলের মধ্যে রঙিন ছোট ছোট লজেন্সের গুলি। যারা খেয়েছে তারা বলল ওই কাঁচ ভেঙে লজেন্সের গুলি চুষলে শেষে একটা মৌরির দানা পাওয়া যায়।
বেকবাগান ও আমির আলি এভেনিউয়ের মোড়ের মিঠাই নামের অসাধারণ দোকানটি তখনও জন্মায় নি।
ও হো, আত্মীয়স্বজনের কথাই যখন উঠলো তখন দু’জনের কথা না বললেই নয়।
একজন সম্পর্কে জ্যাঠামশায়, আমাদের বলা হল চিনি জ্যাঠামশায় বলে ডাকতে। কিন্তু পরিবারে সবাই বলত ‘প্রিন্স অফ জারুইতলা’। এবার একটু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হচ্ছে।
জারুইতলা হল ময়মনসিংহের এক বর্ধিষ্ণু জনপদ। সতীশচন্দ্রের এক বোনের বিয়ে হল সেখানকার ভূস্বামী জ্ঞানদাস মশাইয়ের পরিবারে। পরিবারটির আয়ের মুখ্য স্রোত হল সুদের কারবার। কিন্তু ১৯৩৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক –প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এলে চাষীদের সুদ মাপ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ইউনিয়ন বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া হল সালিশী বোর্ড গঠন করে চাষীদের আবেদন ও মহাজনের বক্তব্য শুনে ফয়সালা করতে । আমার দাদু উকিল সতীশচন্দ্র সালিশী বোর্ডের সেক্রেটারি হয়ে অনেক কেসের নিরপেক্ষ ফয়সালা করে প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেন এবং সরকারবাহাদুরের থেকে একটি জমকালো ট্যাঁকঘড়ি উপহার পেলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসে বিচার করতে গিয়ে উনি নিজের ভগ্নীপতি দাস পরিবা্রের খাতকদের কয়েকহাজার টাকা ঋণ মাপ করে দিলেন। দাস পরিবার এটা আশা করেন নি। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখি কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে রইল।
সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র ধ্রুববাবু বা আমাদের চিনিজ্যেঠা ছিলেন আলালের ঘরের দুলাল। অতীব সুদর্শন এই ভদ্রলোকের পরণে কাঁচি ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে পাম্পশু আর মুখে অল্প অল্প হাসি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি উনি হাজির হলেন কোলকাতায়, পার্কসার্কাসে আমাদের দাদুর দস্তানায়। বাড়ির উলটো দিকে দত্তদের দোতলা বাড়ির গ্যারেজের উপর একটি ম্যাজেনাইন ফ্লোর। তাতে দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যায় ছাদে। সেখানে আমার অবিবাহিত কাকারা , বিশেষ করে যাঁরা তখনও স্কুল-কলেজের গন্ডী পেরোন নি, মাটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে পাশে কেরোসিন কাঠের বইয়ের তাক নিয়ে দিব্যি থাকেন। জ্যাঠামশায় জায়গা নিলেন সেই ব্যাচেলর্স ডেনে। আমরা বলতান—নয়া বাড়ি।
জানলাম উনি দেশভাগের অনেক আগেই এম এ পাশ করেছেন। দেশে জমি-জিরেত-পুকুর ছিল । কাজেই গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না । জীবন বয়ে চলত সরল রেখায়—মৎস মারিব, খাইব সুখে লয়ে।
এখন চাকরি খুঁজতে এখানে ঠাঁই নিয়েছেন। কয়েক মাস হয়ে গেল, উনি নড়েন না , আর চাকরি নিয়ে তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না । ওঁর ছিল চায়ের নেশা। মাঝেমধ্যেই আমাদের বলতেন মূল বাড়ির রান্নাঘরে গিয়ে ভাইবৌদের কাছে চায়ের আবদার পৌঁছে দিতে। নিজেই কিনে আনতেন দার্জিলিং চা। আমরা বখশিস পেতাম পিপারমেন্ট লজেন্স। আর বড়ভাইবউ—চা-আসক্ত আমার মা—ভীষণ খুশি। কারণ ওই চা’য়ের অনেক দাম। আমাদের বাড়িতে এতগুলো মুখ, কেনা হত শস্তা চা।
টানাটানির সংসার, বাড়ির কর্তা বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।
একদিন ওনাকে বিদায় নিতে হল।পরে জেনেছি উনি পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে শিক্ষক হয়ে একজন সমবয়েসি শিক্ষিকাকে বিয়ে করে বেশি বয়সে সুখের সংসারের স্বাদ পেয়েছিলেন।
এক শরতের বিকেল। আমি ও নীচের তলার তোতামামু, নবাব আলি ও আরও ক’জন গলিতে চার আনার রবারের বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছি। গলির মুখের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বলে অফব্রেক করানোর গ্রিপ নিয়ে দাঁড়িয়েছি কি কানের পাশে মৃদু ফিসফিস –খোকা, উকিল সতীশচন্দ্র রায়ের বাড়ি কোথায় বলতে পার?
তাকিয়ে দেখি, ঘেমো চেহারায় এক যুবক, পরনে ধুতি, মলিন শার্ট, বগলে গোটানো নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা এক বিছানা ও একটি টিনের তোরঙ্গ। আমি একটু অবাক। আমার দাদুর নামই বটে। কিন্তু তিনি নিয়মিত বাজারে যান, হিসেব লেখেন, সন্ধ্যেবেলা পার্কে বেড়াতে নইলে ঘোষাল বাড়িতে ভাগবত পাঠ শুনতে যান। তাঁকে এখানে কেউ উকিল তো বলে না ! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে বলল- এই যে ঠিকানাটা-১/সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস।
আরে, এটাই তো আমাদের বাড়ি । উপরে নিয়ে যেতেই সবাই স্তুম্ভিত। জানলাম উনি দাদুর ময়মনসিংহে ওকালতির দিনের মুহুরী সুরেন্দ্র সাহা মশায়ের ছেলে কালিদাস সাহা। ওপার থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতায় এসেছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে এই আশায়, সম্বল বাবার হাতে লেখা চিঠি ও চিরকুট।
আমাদের বাড়ির কেউ কেউ মুরুব্বির চালে বলল—যাদবপুরে বা শিবপুরে মেকানিক্যালে কত নম্বর পেলে ভর্তি হওয়া যায় খবর রাখ? এবছরের কাট অফ ৬৩০। এরচেয়ে কেমিক্যালে কি সিভিলে চান্স পাওয়া সোজা। কালিদাসদা ঠাঁই পেল সেই নয়াবাড়ির ব্যাচেলর্স আড্ডায়। এক সপ্তাহ পেরোল না , কালিদাসদা মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমার দাদু ও ঠাকুমাকে প্রণাম করে টিনের বাক্স ও দড়ি বাঁধা বিছানা নিয়ে বিদায় নিল। চান্স পেয়েছে মেক্যানিক্যালে, শিবপুর যদুপুর –দু’জায়গাতেই। ভর্তি হয়েছে যাদবপুরে, থাকবে হোস্টেলে।
বিয়েবাড়িতে ও অন্য কোন উৎসবে আসতেন একজন। ফর্সা মিতবাক যুবক। নীলরঙা হাতাগোটানো ফুলশার্ট ও বকলস লাগানো প্যান্ট। উজ্বল একজোড়া চোখ। কিন্তু অদ্ভুত লাগতো মাথার কদমছাঁট চুল, একেবারে জুতোর বুরুশের মত।
ওকে দেখা মাত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন বাড়ির কর্তা সতীশচন্দ্র। গিন্নিকে চোটপাট করতেন—হে কেন আইসে, আইজকের কামকাজের দিনে?
সরযূবালা ঝামটা দিয়ে উঠতেন- আপনের শ্যালক, আপনে জিগান গিয়া।
অসহায় সতীশ সবাইকে নীচুগলায় নির্দেশ দিতেন –সবাই হ্যারে চৌক্ষে চৌক্ষে রাখ। জিনিসপত্র সামলাও ।
যাকে নিয়ে সবার মাথাব্যথা, সে কিন্তু নির্বিকার। এক কোণে চুপটি করে বসে আছে, খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে। খাবার ডাক পড়লে উঠে গিয়ে পংক্তিভোজনে বসে মাথা নীচু করে খেয়ে হাত ধুয়ে পান চেয়ে নিচ্ছে। একসময় সবার অলক্ষে বিদায় হলে আধঘন্টার মধ্যে দেখা গেল আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে কারও আংটি, কারও দামী ঝর্ণাকলম, কারও মানিব্যাগ গায়েব।
বড় হয়ে জেনেছি, উনি আমার ঠাকুমার কোন তুতো ভাই। পেশা ও নেশা পকেটমারি। এলাহাবাদ-লখনৌ লাইনে সব পেশাদার পকেটমারের গুরুঠাকুর। কয়েকবার জেলের ঘানি টানার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর খোদার কী খোদকারি, উনি অবিভক্ত বাংলায় ম্যাট্রিকে চার বিষয়ে স্টার ও জলপানি পেয়েছিলেন।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।- আরও পড়ুনশিবাজী ও শম্ভাজীের হিন্দুরাষ্ট্রঃ ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকারের চোখে -- পর্ব ২ - Ranjan Royআরও পড়ুনশিবাজী ও শম্ভাজীের হিন্দুরাষ্ট্রঃ ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকারের চোখে -- পর্ব ১ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৯ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৮ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৭ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৬ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৫ - Ranjan Royআরও পড়ুনফেরারী ফৌজঃ পর্ব ১৪ - Ranjan Royআরও পড়ুনবাংলাদেশে হিন্দুহত্যা - দীপআরও পড়ুনচিলেকোঠা - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনশপিং মল - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনসাধারণ মানুষের জীবন - দীপআরও পড়ুনগীতা - ৫ম পর্ব - Kishore Ghosalআরও পড়ুনদিলদার নগর ১৯ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনপোর্তুগীজ ও মানসোল্লাস - অরিন
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
Ranjan Roy | ১৫ জুন ২০২১ ১৬:৫৭494965
অ্যাডমিন,
আবার ছড়িয়েছি। এই কিস্তির নম্বর ৬ নয়, ৮ হবে।
প্লীজ, শুধরে দিন।
 জার্মান | 2405:8100:8000:5ca1::17a:***:*** | ১৬ জুন ২০২১ ০৮:৫২494972
জার্মান | 2405:8100:8000:5ca1::17a:***:*** | ১৬ জুন ২০২১ ০৮:৫২494972ইস্টবেংগল ক্লাবের কিট আর জার্মান পতাকার রঙ কখনো মিলিয়ে দেখেন নি?
-
Ranjan Roy | ১৬ জুন ২০২১ ২০:০৭494983
থ্যাংক ইউ! আমার অনেক দিনের ধাঁধার সমাধান করে দিলেন!!
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৬ জুন ২০২১ ২৩:২০494986
হীরেন সিংহরায় | ১৬ জুন ২০২১ ২৩:২০494986 রঞ্জন বাবু
কি যে অসাধারণ লিখছেন!! নির্বাক বিস্ময়ে পড়ে যাচ্ছি । আমার ছেড়ে আসা কলকাতা জেগে উঠছে বার বার। এ এক অনবদ্য দলিল, হিউম্যান ডকুমেন্ট , যার তুল্য কিছু আমার চোখে এ যাবত পড়ে নি । ফাইল করে রাখছি ।
চার দশক আগে দেশ ছেড়েছি কিন্তু বুক চিরলে মোহন বাগান লেখা দেখতে পাবেন । আমি ঘটিস্য ঘটি ।
একটু বিতর্কে যেতে চাই। পতাকার কারণে আমরা উত্তর কলকাতার লাল হলুদ সমর্থকদের জার্মান পার্টি বলতাম বলে মনে হয় না। জার্মান পতাকার রঙ এবং চেহারা গত শতাব্দীতে বদলেছে অনেকবার । প্রাশিয়ানদের লাল শাদা কালো, ভাইমার রিপাবলিকের লাল কালো , নাৎসিদের লাল শাদা কালো প্লাস স্বস্তিকা । আজকের যে পতাকাটি আমরা দেখি সেটির অনুমোদন মেলে অক্টোবর ১৯৪৯ সালে, আমাদের দেশ ভাগের দু বছর বাদে । জার্মান পার্টি নাম কেন তা বোঝাতে পাড়ার কল্যাণ দা বলেছিলেন ওই যে বাঙ্গালরা উদ্বাস্তু হয়ে ঘটি বাটি শীতল পাটি নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে সংসার পেতেছেন ( ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলি কারণ দেশ ভাগের দুঃখ আমাদের বোধের অগম্য ) - জার্মানরা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ঠিক সেই ভাবে ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমে আসে দলে দলে। এই যাত্রা পূব থেকে পশ্চিমে -পোল্যান্ড চেক হাঙ্গেরি থেকে খ্যাদানো জার্মানের সংখ্যা দেড় কোটির বেশি। ভারত পাকিস্তানের দু পক্ষ মিলিয়ে ছিন্নমূলের সংখ্যা এর চেয়ে কম। মোহন বাগানের ঘটিরা যে এতো পড়াশোনা করে বিপক্ষকে জার্মান পার্টি নাম দিয়েছে সেটা মেনে নেওয়া শক্ত হতে পারে , বিশেষ করে সেই সব ঘটি যারা স এর সঠিক উচ্চারণে অপারগ । তবু পতাকার তত্ত্ব মেনে নেওয়া শক্ত । এর অনেক পরে নুরেমবেরগের গোরা ঘোষ আমাদের উত্তর কলকাতার কল্যাণ দার থিওরির সমর্থন করেছিলেন।
ইউরোপের ফুটবল দলের ডাক নাম বিচিত্র হয় । সে তালিকা দীর্ঘ । লেসটারে একদা শেয়াল মারা হতো তা থেকে ফুটবলে দলের নামই হয়ে গেল শেয়াল ।
আরেকটা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে হচ্ছে ( গুণীরা মার্জনা করবেন ): ত্রিনিদাদে বেগুণকে বাইগণ বলতে শুনেছি ! গায়ানাতেও সেই নাম চালু। অবশ্যই সেটা ভারত থেকে জাহাজে আসা আখ চাষিদের মুখে এখানে আবির্ভূত হয়েছে।
অপিনিহিতি , অভিশ্রুতি শুনলাম পাঁচ দশক বাদে ! স্বরভক্তি বিপ্রকর্ষ বাদ দিলেন কেন ?
শেষে বলি , আমার কানে আজো লেগে আছে ইস্যা করে পরানডারে গামসা দিয়া বাণধি ( ইচ্ছা করে নয় , ইস্যা ! গামছা নয় গামসা )।
অলমিতি বিস্তরেন
-
Ranjan Roy | ১৬ জুন ২০২১ ২৩:৪৫494988
হীরেনবাবু
খুদা কী কসম, মজা আ গয়া।
-
Ranjan Roy | ১৬ জুন ২০২১ ২৩:৫০494989
হীরেনবাবু
মজার ব্যাপার হোল আমি আজও মোহনবাগানের, চূণী গোস্বামীর পায়ের কাজের ফ্যান। একটু বড় হয়ে জেনেছি চূনী আমাদের মতই ময়মনসিঙ্ঘের বাঙাল। তাতে আমি আরও বেশি করে মোহনবাগানী হলাম। চূণী যদি মোহনবাগানে খেলতে পারেন, আমি কেন সাপোর্টার হতে পারিনা?
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ০০:৫৬494994
হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ০০:৫৬494994 পুনশ্চ:পতাকা সম্পর্কিত
জার্মানি ও বেলজিয়ামের পতাকায় ওই একই লাল হলুদ কালো রঙ আছে । তার ক্রমটা আলাদা বিন্যাসটাও । বেলজিয়ান পতাকায়ে প্রায় দুশো বছরের ( ১৮৩০) পুরনো। পতাকার হিসেবে লাল হলুদের দলকে বেলজিয়ান বলতেও বাধা নেই !

 Amit | 203.***.*** | ১৭ জুন ২০২১ ০২:৫৯494995
Amit | 203.***.*** | ১৭ জুন ২০২১ ০২:৫৯494995জব্বর রঞ্জনদা। এটা তো পুরো তপন রায়চৌধুরী র "বাঙালনামা" র লেভেল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাস্ট টপ ক্লাস। যত এগোচ্ছে তত খুলছে। এইটা বই হয়ে বেরোনোর অগ্রিম শুভেচ্ছা আর লাইন পাতা রইলো।
আমার ঠাকুরদা সপরিবারে এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৭ এর পরে। মাস্টারদা সূর্য সেন র সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবের সময় , অনেক বছর জেলে কাটিয়েছিলেন। অবশ্য ওনার স্মৃতি কিছুই নেই আমার। আমার দু বছর বয়েসে উনি মারা যান। কিন্তু সেই ঘোর বাঙাল রক্ত আমরা সবাই পেয়েছি। কোনো সময় ফ্যামিলির সবাই কোনো উপলক্ষে এক সাথে হলে পুরো পাড়ায় কাক চিল পালিয়ে যায়।
সেই চট্টগ্রামের ভাষা ও যে বাংলার একটা চলিত ফর্ম হতে পারে সে না শুনলে বোঝা যাবেনা। সে যে কি মধুর - আহা। সবথেকে দুঃখ হলো কলকাতায় আমি বা আমার জেনারেশন এর কেও কেও সেটা বুঝতে পারলেও বলতে একদম পারিনা। ওটা বলতে গেলে সুপুরি মুখে নিয়ে বহু বছর প্রাকটিস করতে হবে।
 রঙ | 2405:8100:8000:5ca1::498:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ০৬:৩৭494996
রঙ | 2405:8100:8000:5ca1::498:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ০৬:৩৭494996- Coat of arms
(1848–1866)German ReichDeutsches Reich1918–1933 Flag
(1919–1933)Coat of arms
(1919–1928)Motto: Einigkeit und Recht und Freiheit
("Unity and Justice and Freedom") ইস্টবেংগল ক্লাবের জন্ম ১৯২০ সালে। সুতরাং ভাইমার রিপাবলিকের প্রায় কাছাকাছি। আর জার্মান নাম ঘটিরা দিব ক্যান? ইটা আপনি কী কইলেন হীরেনবাবু? ইসব্যাংগলের ফ্যানরা নিজেরাই নিজেগো জার্মান কয় ২০-৩০ এর দশক থেইকা।
ইস্টবেংগল ক্লাবের জন্ম ১৯২০ সালে। সুতরাং ভাইমার রিপাবলিকের প্রায় কাছাকাছি। আর জার্মান নাম ঘটিরা দিব ক্যান? ইটা আপনি কী কইলেন হীরেনবাবু? ইসব্যাংগলের ফ্যানরা নিজেরাই নিজেগো জার্মান কয় ২০-৩০ এর দশক থেইকা।
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ০৯:৩৩495000
হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ০৯:৩৩495000 অনেক ধন্যবাদ ! আরেকটি ঘটি থিওরি মাঠে মারা গেল ( নো পান ইনটেনডেড !) । আমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে নিজেরই সন্দেহ প্রভূত তাই আমি লিখেছিলাম ঘটিরা যে এতো পড়াশোনা করে বিপক্ষের নাম দিয়েছে আর সেটা লাল হলুদের মেনে নিয়েছে সেটা মেনে নেওয়া শক্ত হতে পারে! কয়েক যুগের ভ্রম সংশোধিত হল।
একটা প্রশ্ন থেকে যায় - জার্মান নামটা কি ১৯৩৩-১৯৪৯ মুলতুবি ছিল ?
-
দ | ১৭ জুন ২০২১ ১০:০০495002
@হীরেন সিংহরায়,
দেশভাগের প্রত্যক্ষ বলি চল্লিশ মিলিয়ন ধরা হয় অর্থাৎ চার কোটি। এটা ৪৭ এর জুন জুলাই থেকে ৪৮ এর গান্ধীহত্যার পরবর্তী কিছুদিন পর্যন্ত। এর মধ্যে খুন আর মাইগ্রেশান দুইই আছে, এর পরেও ১৯৫০ এ আরো মাইগ্রেশান হয়েছে। এই পুরিয়ডে পূর্ববঙ্গ থেকে বেশী।
যাই হোক ঠিক সংখ্যা কোথাও নেই। প্রচুর মৃত্যু বা মাইগ্রেশান সম্ভবত আনডকুমেন্টেড থেকে গেছে।
কাজেই আপনার বক্তব্য যে দেশভাগে দেড়কোটির কম সংখ্যক উদবাস্তু হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেটি ঠিক নয়।
 :) | 2405:8100:8000:5ca1::506:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ১০:১১495003
:) | 2405:8100:8000:5ca1::506:***:*** | ১৭ জুন ২০২১ ১০:১১495003রঞ্জনবাবুর লেখা ডিরেইল্ড হইতেছে :) কিন্তু জার্মান নাম মুলতুবি হইবে ক্যান? ছিল তো, সাংঘাতিক রকমেই ছিল। ফ্ল্যাগ, সিল আলাদা ছিল।
German Reich
(1933–1943)
Deutsches Reich
Greater German Reich
(1943–1945)
Großdeutsches Reich1933–1945 Anthems:
Das Lied der Deutschen
("The Song of the Germans")
Horst-Wessel-Lied [a]
("The Horst Wessel Song") Germany's territorial control at its greatest extent during World War II (late 1942):
Germany's territorial control at its greatest extent during World War II (late 1942):
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১২:০৬495004
হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১২:০৬495004 শ্রী দ
সামগ্রিক ভাবে আপনি সম্পূর্ণ সঠিক । ভারত ভাগের ফলে ছিন্নমূলের সংখ্যা দেড় কোটির অনেক অনেক বেশি । আমার তুলনাটা ছিল একটি সময় সীমার- ১৯৪৫-১৯৪৮ । এই সময়ে পূব থেকে জার্মান বহিষ্কার সম্পন্ন হয় সাত কোটী লোকের দেশ দেড় কোটি উদ্বাস্তু গ্রহণ করে । মৃতের সংখ্যা অজ্ঞাত । জন ধন বা সম্পত্তি বিনিময় হয় নি । এক মুখো অভিযান। তবে এই ধারাটি থেমে যায় সরকারি ভাবে জার্মানি ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে ( কিছু পলাতক আসতেই থাকেন !)। ভারত ভাগের পরে ছিন্নমূলের যাত্রা থামে নি। তাই শেষ সংখ্যাটা অনেক বেশি।
-
Ranjan Roy | ১৭ জুন ২০২১ ১২:৩৮495005
অমিত,
আমি লইট্যা মাছের শুঁটকির ভক্ত, যদিও ইলিশ, মুড়িঘন্ট ও মাছের তেলের চালবাটা দিয়ে বড়া খাইনে, গন্ধ লাগে।ঃ)) চট্টগ্রামের কর্নফুলির মোহানার লইট্যার স্বাদ নাকি দারুণ!
চাটগাঁর বন্ধুদের কথা শুনে বুঝতে পারিনি। চন্দ্রবিন্দু ও ণ বেশি বলে মনে হোল। যেমন 'আঁরারে"।
শুনেছি ওই উপভাষায় নাকি আরাকানি বা সীমান্তের বার্মিজ ভাষার প্রভাব আছে। এসব আমার সিলেবাসের বাইরে। ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাল বলতে পারবেন।
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১৫:১২495007
হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১৫:১২495007 রঞ্জন বাবু
আমার প্রথম কর্মস্থল জলপাইগুড়ি । ক্যানটিন ম্যানেজার ছিলেন আরেক হীরেন । তাঁর কাছেই আত অক্কল টেখা অউ এই সব জরুরি শব্দ শিখেছি কথা চালানো গেছে। উত্তর কলকাতার ইংরেজি উসচারন জনিত সকল শঙ্কা অপনীত হল যেদিন জন হেরন নামক একজন গ্লাসগো বাসীর সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপ হয়। সেটা যদি ইংরেজি হয় তবে আমি কিছু খারাপ বলছিনা । আরেক শিক্ষা হল ছেলেকে নিয়ে লিভারপুলে খেলা দেখতে গিয়ে । হোটেল ট্যাক্সিওলা দোকানী যে যাই বলে আমি ছেলেকে জিগ্যেস করি, হ্যাঁরে কি বলল ? সুইস জার্মান আরেক বিপজ্জনক বস্তু । শুধু উচ্চারণ নয় সেটাও ওই হক্কল টেখা য় ভর্তি ।
ভিভ ল্য দিফরাঁস
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১৫:২৪495008
হীরেন সিংহরায় | ১৭ জুন ২০২১ ১৫:২৪495008 অন্য হীরেন খাস চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। রান্না অনবদ্য ।
-
Ranjan Roy | ১৭ জুন ২০২১ ১৮:৩৫495011
জার্মান নিয়ে আরেকটা থিওরিঃ
কেউ জানিয়েছেন যে বাঙালেরা যে এনামেল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন নিয়ে শ্যালদায় নামত, সেগুলোকে নাকি জার্মান সিলভার বলা হত। এখন এই জার্মান সিলভার বস্তুটি কী? কেউ জানেন?
-
দ | ১৭ জুন ২০২১ ১৯:০৭495013
জার্মান সিল্ভারে জার্মানও নেই সিলভারও নেই। এটা হল নিকেল সিলভার। ৬০% তামা, ২০% নিকেল আর ২০% দস্তার সংকর ধাতু। কার একটা নামে যেন নামকরণ হয়েছে জার্মান সিলভার।
-
Ranjan Roy | ১৭ জুন ২০২১ ২০:২২495017
দ,
অনেক ধন্যবাদ সঠিক তথ্য দেয়ার জন্যে।
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৮ জুন ২০২১ ০৪:০৮495033
হীরেন সিংহরায় | ১৮ জুন ২০২১ ০৪:০৮495033 শ্রী দ সঠিক বলেছেন। এতে না আছে সিলভার না আছে জার্মান । তা হলে নামটা এলো কোথা হতে?চীনেরা প্রথম ওই ৬০:২০:২০ হিসেবে নিকেল বানিয়ে বাজার ধরে। ১৭৫০ নাগাদ জারমানীর সুল শহরে একটি এ্যালয় বানানো হয় যা চৈনিক আমদানীর সংগে পাল্লা দেয়। পরে একটি প্রতিযোগিতায় বারলিনের হেনিংগার ভাইয়েরা একটি মোক্ষম পেটেন্ট দখল করেন। এ্যালয়টির চীনে নাম পাকটং। একে ইউরোপ নিকেল সিলভার বলত। পরে জার্মান কারিগরের সমমানে এটি জার্মান সিলভার আখ্যাত হয়।
এদের এই বাতিক আছে। এক্স রেকে জারমানীতে
রয়েনটগেন বলে। তিনি যেটা আবিষ্কার করলেন সে নাম নয় আপন নামেই ধন্য হয়ে রইলেন তিনি
 শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় | 117.194.***.*** | ২০ জুন ২০২১ ১৮:৩৩495131
শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় | 117.194.***.*** | ২০ জুন ২০২১ ১৮:৩৩495131রঞ্জনবাবু,
আমি হাওড়ার 'গোটি'। সেই হাওড়া, যেখানকার গঙ্গার যে কোন ঘাট থেকে কলকাতার যে কোন ঘাটে যাতায়াতের লঞ্চ বন্ধ থাকতো মোহনবাগানের খেলা থাকলে, পাছে মোহনবাগানের সাপোর্টারদের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। ইশকুলের বন্ধুদের মধ্যে অনেক বাঙাল ছিল৷ তাদের কেউ জার্মান নামের ব্যুতপত্তি (ধুত্তোর, খণ্ড ত লিখতে পারিনা!) জানতো না। এমনকি, আমাদের ক্লাশের বাঙাল ফার্স্টবয়ও নয়।
একটু বড় হয়ে আমাদের এক দাদার মুখে ব্যুতপত্তিটা জেনে নিলুম। ইনি আবার টুটুবাবুর কোন তুতো দাদা। মোহনবাগানের সেই বিখ্যাত টুটুবাবু, যিনি ঈস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলার দিন শাউড়ির হাতে জল খেতেন না!
দাদাটি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তোদের ক্লাশে ফার্স্ট যে হয় সে ঘটি না বাঙাল? উত্তর দিলুম। বললেন, জানাই ছিল। ঘটিরা যে লেখাপড়ায় মূর্তিমন্ত, তা তোকে দেখলেই বোঝা যায়। ইশকুলের পড়ার বই যে পড়িস না সে তো আগেই জানতুম। অন্য কিছুও পড়িস না? মুজতবা আলিও পড়িসনি? না কি আলি সাহেবকেও বাঙাল বলে বয়কট করেছিস?
রহস্যের প্রকাশ ধীরে ধীরে হতে জানতে পারলুম আলি সাহেব নাকি ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন জার্মানিতে। আর সেই কথা পাঠককে জানাতে লিখেছিলেন, সেই ডক্টরেট ডিগ্রী জাপানি মালের মত সদাভঙ্গুর ছিল না, ছিল পোক্ত জর্মন মাল!
পোক্ত! এটাই ছিল মূল কথা। তাই বেডিংটুকু সম্বল বাঙালের পোলাপানরা ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্মে থাকুক আর উদ্বাস্তু কলোনিতেই থাকুক, ওরা পোক্ত। ক্লাশে ঠিক ফার্স্ট হয়। চাকরির পরীক্ষাতেও তাই। ওরা পোক্ত। তাই ওরা জার্মান। তাই ঈস্টবেঙ্গল মানেই জার্মান। বুঝলে খোকা?
 Nirmalya Nag | 202.8.***.*** | ২১ জুন ২০২১ ০১:৩৪495144
Nirmalya Nag | 202.8.***.*** | ২১ জুন ২০২১ ০১:৩৪495144'জার্মান' যে বাঙালের প্রতিশব্দ সেটা ছোটবেলায় (মানে ৮০-এর দশকের শুরুতে) বাবার কাছে শুনেছি। তবে নামকরনের কারণ উনি বলতে পারেননি। আমরা মধ্য বীরভূমের লোক (আমাদের গ্রাম ছিল সেকালে ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত)। অপিনিহিতি অভিশ্রুতির কথায় সেখানকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমার এক কাকার সাথে কোনও দরকারে এক বাড়িতে গেছি। আমার কাকা বাইরে থেকে হাঁক পাড়লেন, "ভক্ত্যা, মুক্ত্যা"। পরে জানলাম তাঁদের নাম ভক্তিনাথ ও মুক্তিনাথ। ভক্তি ও মুক্তির 'ই-কার' হয়ে গেছে 'অ্যা-কার'।
-
Ranjan Roy | ২১ জুন ২০২১ ১৭:৪২495168
ফির মজা আ গয়া। শেখরনাথ ও নির্মাল্য দুই 'গোটি' এসে আরও জমিয়ে দিলেন।
তবে নির্মাল্যকে বলি-- আমার প্রপিতামহের হাতে লেখা আত্মকথা থেকে জেনেছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা বীরভূমের 'গোটি' ছিলেন। সেই কোম্পানির আমলের মন্বন্তরের সময় গ্রাম ছেড়ে কী করে যেন ময়মনসিংহের এক গ্রামে এসে জঙ্গল সাফ করে নতুন বসতি স্থাপন করেন।
তাতে আমি আর আমার ভাই দাদুকে বললাম যে রাঢ় বাংলায় ভূস্বামীরা কায়স্থ কোথায় ? হয় ব্রাহ্মণ নয় উগ্রক্ষত্রিয় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মানে আগুরি বা সেই হারাধন পোঁদ। আমরা কোনটা? দাদু ঘৃণায় সাতদিন কথা বলেননি।ঃ))
 Abhyu | 47.39.***.*** | ২৪ জুন ২০২১ ০৫:০৫495250
Abhyu | 47.39.***.*** | ২৪ জুন ২০২১ ০৫:০৫495250"বড় হয়ে জেনেছি, উনি আমার ঠাকুমার কোন তুতো ভাই।" - শেষের গল্পটা খেরোর খাতায় যাবার মতো।
-
domain seven | ২৪ জুন ২০২১ ০৮:৫৬495256
wow Amazing Article i বৌল্ড লোভে তো Read More from this site
 a | 202.53.***.*** | ০৪ জুলাই ২০২১ ০৬:০৪495587
a | 202.53.***.*** | ০৪ জুলাই ২০২১ ০৬:০৪495587আমার কেন যেন ধারণা ছিল হাল না ছেড়ে শেষ অবধি লড়ে যাবার মানসিকতার জন্যেই জারমান নাম
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)
(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, অরিন, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত