- বুলবুলভাজা পড়াবই কাঁটাতার

-
উদ্বাস্তু কলোনির কথা - একটি স্মৃতিকথা সংকলন - পাঠপ্রতিক্রিয়া এবং
বিশ্বজিৎ রায়
পড়াবই | কাঁটাতার | ১৫ আগস্ট ২০২১ | ৫৫৭৭ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন) - উজানতলির উপকথা | আগুনপাখি | উদ্বাস্তু কলোনির কথা : একটি স্মৃতিকথা সংকলন | এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা | সিজনস অফ বিট্রেয়াল | সূচীপত্র১৯৪৭ উত্তর ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছিল নতুন কিছু শব্দবন্ধের। এই প্রবীণরা কখনও স্বাধীনতা বলেননি, বলেছেন পার্টিশন, তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে শব্দ ভারতের অবদান। পার্টিশনের হাত ধরে এসেছে উদ্বাস্তু। রিফিউজি কলোনি। তারও পরে এসেছে অনুপ্রবেশ। বসেছে কাঁটাতার। এসেছে এনআরসি, নতুন নাগরিকত্ব আইন। শুরু হয়েছে "বৈধ-অবৈধ" বিচার। শোনা যাচ্ছে, নতুন শব্দবন্ধ, "অবৈধ অনুপ্রবেশ"। যাঁরা বিচার করছেন, তাঁদের বিচার কে করে। এসব শব্দের, আখ্যানের জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশভাগের এই আদি পাপ, মুছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এভাবেই থেকে গেছে বেদনায়, ভাষায়, আখ্যানে। থেকে গেছে, এবং এখনও যাচ্ছে। সেই আখ্যানসমূহের সামান্য কিছু অংশ, থাকল পড়াবই এর 'কাঁটাতার্' বিভাগের প্রথম সংখ্যায়।
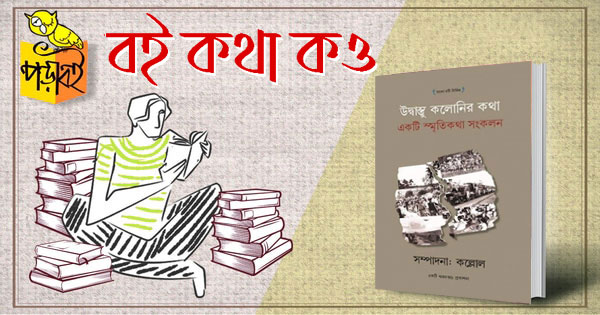 "উদ্বাস্তু কলোনি পত্তন ঘিরে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, ডান-বাম রাজনৈতিক বিরোধ, দলাদলি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত কোঁদল, নেতাদের দাপট- দুর্নীতি- ধান্দাবাজি ছিল। কিন্তু সেটাই সমাজে নির্ধারক ছিল না। জমিদারের গুন্ডা-পুলিশের সঙ্গে যুঝে রাতপাহারার ফাঁকে জলজংলা, পতিত জমি দখল করে নয়া বসত পত্তন ও ভিটেমাটির বিলি-বন্দোবস্তের কালে নানা মতের পূর্বপুরুষদের যূথবদ্ধ অস্তিত্বের লড়াই এখন পুরাকথার সামিল।"
"উদ্বাস্তু কলোনি পত্তন ঘিরে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, ডান-বাম রাজনৈতিক বিরোধ, দলাদলি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত কোঁদল, নেতাদের দাপট- দুর্নীতি- ধান্দাবাজি ছিল। কিন্তু সেটাই সমাজে নির্ধারক ছিল না। জমিদারের গুন্ডা-পুলিশের সঙ্গে যুঝে রাতপাহারার ফাঁকে জলজংলা, পতিত জমি দখল করে নয়া বসত পত্তন ও ভিটেমাটির বিলি-বন্দোবস্তের কালে নানা মতের পূর্বপুরুষদের যূথবদ্ধ অস্তিত্বের লড়াই এখন পুরাকথার সামিল।"
উদ্বাস্তু কলোনির কথা : একটি স্মৃতিকথা সংকলন - বইটি নিয়ে লিখলেন বিশ্বজিৎ রায়।এমন একটা ভয়ঙ্কর সময়ে দক্ষিণ কলকাতার নানা উদ্বাস্তু কলোনির আদিপুরুষদের কয়েকজনের স্মৃতিকথার এই সঙ্কলনটি হাতে এল যখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তথা আর এস এস- নিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘ পরিবার দেশের হিন্দু জন্মমানসে দেশভাগের স্মৃতি খুঁচিয়ে তুলে মুসলমান- বিদ্বেষ তুঙ্গে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙালি-বিতাড়নে মদত যোগালেও আমাদের রাজ্যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের মায়াকান্নায় রাজনীতির বাতাস ভারী। দেশভাগ পর্বের পর ভঙ্গবঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনও এতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এহেন পরিস্থিতিতে এই বইটি খুবই জরুরি ছিল। সম্পাদক-প্রকাশকদের ধন্যবাদ তাঁদের কালচেতনার জন্য।
দেশভাগ-পর্বের বাঙালি উদ্বাস্তু প্রজন্মের অনেকেই কালপ্রবাহে হারিয়ে গেছেন। সম্পাদক কল্লোল যাঁদের বলেছেন, ‘এক অন্য হিবাকুশা’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে জাপানে মার্কিন পারমানবিক বোমায় সৃষ্ট নারকীয় আগুনে জ্বলে- পুড়ে খাক হয়েও বেঁচে- যাওয়া সেই মানুষদের মতোই দেশভাগের শিকার বাঙালি (এবং পঞ্জাবি ও সিন্ধি)দের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি ‘কূটবুদ্ধি’ ব্রিটিশ সরকার আর ‘মদগর্বী হবু শাসকেরা’। “বহু প্রজন্মের ভিটে, জীবন-জীবিকা, যাপন, পরিবেশ, পরিচয় থেকে উচ্ছিন্ন হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। দায় বহন করে চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম’’।
আমরা যারা দেশত্যাগীদের পরবর্তী প্রজন্মের, তাদের কাছে পারিবারিক স্মৃতিচারণ ভিন্ন দেশভাগের ব্যক্তিগত স্মৃতি নেই, অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসের পর্বান্তর রূপে পাঠ্য হিসেবে জানার রেশটুকুও ফিকে। ভিটে-মাটি, রুটি-রুজি হারিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে আসা (উল্টোপথের যাত্রীও কম ছিল না) ছিন্নমূল দাদু- ঠাকুমা, বাবা-জ্যাঠা-কাকা, মা-জেঠিমা-কাকিমাদের জীবনসংগ্রামের কাহিনী আজকের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা জানে না, তাগিদও বোধ করে না। বিজয়গড় কলোনির আদি বাসিন্দাদের দুজন শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও গৌরাঙ্গ দে চৌধুরীর স্মৃতিচারণে সেই আক্ষেপ ধরা পড়েছে—“ এখন ছেলেরা বাবার চেক বই দ্যাখে। তারা কি আর এইসব কষ্ট উপলব্ধি করবে?”
সত্যি কথা বলতে, আমাদের প্রজন্মে রিফিউজি পরিবারের বামপন্থীরাও শৈশব-স্মৃতির ‘এইসব’ নিজেদের সন্তানদের জানানোর দায় অনুভব করিনি। বাস্তুহারা, রিফিউজি, বর্ডার স্লিপ, জবরদখল, পি এল ক্যাম্প ইত্যাদি শব্দ কার্যত জনস্মৃতি তথা রাজনৈতিক প্রতর্ক থেকে মুছে গেছে। উদ্বাস্তু কলোনি কোথাও কোথাও পুরোন সাইনবোর্ডে থাকলেও সেখানকার কিছু আদি বাসিন্দা ভিন্ন বাকিরা কলোনি পত্তনের দিনগুলো কেউ জানে না। নয়া বাসিন্দাদের অনেকেই জন্মসূত্রে উদ্বাস্তু পরিবারের নন, ভিন ভাষা- সংস্কৃতির মানুষও বাড়ছে। বিশেষ করে নয়ের দশক থেকে বাজার অর্থনীতি জাঁকিয়ে বসার সূত্রে প্রমোটার-রাজের কল্যাণে জমি-জায়গা, দোকানপাট হাতবদলের হিড়িক বেড়েছে। কলকাতা ও শহরতলির একদা উদ্বাস্তু পাড়ায় এখন সারি সারি ফ্ল্যাটবাড়ি আর চোখ-ধাঁধানো রঙ্গিন আলোয় সাজানো রকমারি ভোগ্যপণ্যের বিপণিমালায় ক্রেতার ভিড় চোখে পড়ে। পণ্যরতির ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খোপবন্দি মানুষের সামাজিক দূরত্ব। তিন দশকের বাম-শাসনের কালে নগরায়নের নামে এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা হয়েছে। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিষ্ঠানে নিয়োজিত দলদাসতন্ত্র তলা থেকে গড়ে ওঠা দলনিরপেক্ষ সামাজিক সহযোগিতা ও প্রতিরোধের স্থানীয় ইতিহাসকে মুছে দিয়েছে।
অথচ আলোচ্য বইয়ের স্মৃতিকথাগুলি থেকে স্পষ্ট, উদ্বাস্তু কলোনি পত্তন ঘিরে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, ডান-বাম রাজনৈতিক বিরোধ, দলাদলি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত কোঁদল, নেতাদের দাপট- দুর্নীতি- ধান্দাবাজি ছিল। কিন্তু সেটাই সমাজে নির্ধারক ছিল না। জমিদারের গুন্ডা-পুলিশের সঙ্গে যুঝে রাতপাহারার ফাঁকে জলজংলা, পতিত জমি দখল করে নয়া বসত পত্তন ও ভিটেমাটির বিলি-বন্দোবস্তের কালে নানা মতের পূর্বপুরুষদের যূথবদ্ধ অস্তিত্বের লড়াই এখন পুরাকথার সামিল।
সেই সুযোগে জায়গা নিচ্ছে উপর থেকে চাপানো দেশভাগ নিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের একপেশে ও বিকৃত ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতি যা জাতপাত, গরিব-বড়লোক,নারীপুরুষ, তথা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি সমসত্ত্ব বৈরি সম্প্রদায় রূপে হাজির করে। তাঁদের হাজার বছরের দেওয়া-নেওয়া মিলনের ইতিহাসকে গায়েব করে শুধু বিভেদ- বিচ্ছেদের চিহ্নগুলিতে দাগা বুলোয়, দাঙ্গার পর্বগুলিকেই ইতিহাস বলে দাবি জানায় এবং অবধারিত ভাবে হিন্দুদের আক্রান্ত ও মুসলমানদের আক্রমণকারী বলে প্রচার করে। অথচ মুসলমানপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানে ভিটে-মাটি, সম্পত্তি- সম্মান হারানোর দগদগে ঘা বুকে বয়েও এপারে এসে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে ঝাঁপ দেননি কলোনির আদি পুরুষ ও নারীরা। সে সময় সাভারকর- শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সক্রিয় থাকলেও প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল কংগ্রেস ও নানা মতের বামপন্থীরা। বাস্তুহারাদের মধ্যে এখানে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা-ক্রোধ চাগিয়ে তোলার কাজ করেননি তাঁরা।
নয়ের দশক থেকে সঙ্ঘ-রাজনীতির উত্থান, বিশেষ করে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদী সরকারের পত্তনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাবরণ ও সমীকরণ ব্যাপক বদলেছে। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতালাভের প্রথম দফায় মোল্লাতন্ত্রকে তোল্লাই দেওয়ার প্রতি বিরূপ হিন্দু প্রতিক্রিয়া চাগিয়ে তোলে বিজেপি। তা সামলাতে দ্বিতীয় দফায় পুজো-আচ্চার হিড়িক ও ক্লাবগুলিতে সরকারি টাকায় সারা বছর মুফতে মোচ্ছবের ব্যবস্থা স্থানীয় পুরোন ও নতুন সঙ্ঘীদের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে। এতটাই যে সম্প্রতি বাঘা যতীন- বিজয়গড়- আজাদগড়- দেশবন্ধুনগর- নেতাজিনগর- রাণিকুঠি তথা যাদবপুর-গড়িয়া-নাকতলা টালিগঞ্জের নানা পাড়ায় সি এ এ- এন আর সি- এন পি আর নিয়ে পাল্টা প্রচারে নেমে আমরা অনেকেই স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যেও অদ্ভুত শীতলতা টের পেয়েছি। চায়ের দোকানের আলাপচারিতা বা উড়ে আসা মন্তব্যে বৈরি মনোভাব স্পষ্ট। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে ও পথসভায় পরপর সঙ্ঘীদের আক্রমণ হয়েছে ওই এলাকা থেকেই। একদা বামেদের গড় এই অঞ্চলে আজ আর এস এস- বি জেপির শক্তি বাড়ছে এটা অনস্বীকার্য।
দেশভাগ ও দেশত্যাগঃ সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থসংঘাত
সংকলনটির মূল লেখা ইন্দুবরণ গাঙ্গুলির –কলোনি স্মৃতি—উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠা গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪)। আজাদগড় সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি কলোনির গোড়া পত্তনের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটি বহু কলোনির যৌথ সংগঠন দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি ও পরে ওই অঞ্চলে রাজ্যভিত্তিক সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি আর সি)র অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। জীবনের নানা পর্বে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকলেও দলদাস ছিলেন না। বস্তুত স্মৃতিকথায় বেয়াল্লিশের ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, পাকিস্তান প্রস্তাব ও দেশভাগ প্রশ্নে পার্টির লাইন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনে পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের ভূমিকায় তাঁর বীতশ্রদ্ধ মনোভাব গোপন করেননি। পরে পার্টি ছেড়ে দিলেও বামপন্থী আদর্শের প্রতি, বিশেষ করে ধর্মভেদের ঊর্ধ্বে গরিব, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট ছিল।
দেশভাগ ও বাঙালি হিন্দুর দেশান্তরে যাত্রার সামাজিক- অর্থনৈতিক পটভূমি প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তাতে স্পষ্টতই আজকের সঙ্ঘী প্রচারের একমেটে বয়ানের সঙ্গে মেলে না। “ পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও শিক্ষা- সংস্কৃতি- শিল্প-ব্যবসা-বানিজ্য ও রাজনীতির সর্বত্রই ছিল তাঁদের অগ্রগণ্য ভূমিকা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু প্রভুত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ মুসলমানই ছিল অশিক্ষিত ও গরিব। সম্পদশালী হিন্দু ও মুসলিমদের দ্বারা তারা শোষিত হত... অর্থনৈতিক ক্ষমতা নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গের সমগ্র মুসলিম সমাজ পাকিস্তান ঘোষণার পর যেন একটা জগদ্দল পাথরচাপা থেকে মুক্তিলাভের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। পুরুষানুক্রমে মুসলমানগণ হিন্দু বাড়িতে যে সীমাহীন অমর্যাদা, অপমান ও অবহেলা ভোগ করেছে, পাকিস্তান হওয়ায় সেই অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটল বলেই তাঁরা আনন্দিত বোধ করল। হতদরিদ্র সাধারণ মুসলমানদের সেই আনন্দ প্রকাশের রীতি পদ্ধতি ও ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই প্রভুত্বশালী হিন্দু সমাজের মান মর্যাদাকে আঘাত করল। এবং ওই সকল ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হিন্দু গণ তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করল”।
তাঁর অভিজ্ঞতা, সব গরিব মুসলমানের আচরণ মোটেই এক রকম ছিল না। বিশেষ করে যারা জীবিকাসূত্রে হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা আতান্তরে পড়েন। “হিন্দুগণ দেশ ছেড়ে চলে যাবে এ রকম প্রচার শুনে তাঁরা হিন্দুদের নানা রকম প্রশ্ন করতেন। তাঁরা ভাবতেন তাহলে তাঁদের রুজি-রোজগারের কি হবে! ... তাঁরা যদি চলে যায় তাহলে গ্রাম্য শ্রমজীবী মানুষদের কাজ জুটবে কোথায়? তাই এঁরা হিন্দুদের দেশ ত্যাগ না করতে বহু অনুরোধ- উপরোধ করেছেন। বহু ক্ষেত্রে এঁরা হিন্দুদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন’’। উল্টোদিকে ছিল সম্পন্ন হিন্দু ভ্রদ্রলোকদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম মধ্যবিত্ত ও মোল্লাতন্ত্র। “ স্থানীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ গ্রামের মাতব্বর সম্প্রদায়, হিন্দু সম্পত্তির উপর অধিকার কায়েম করার দ্বারা লাভবান হওয়ার প্রলোভনকে আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। তারা একদিকে জলের দরে হিন্দুদের জমিজমা ক্রয়ের প্রস্তাব দিতে শুরু করলেন এবং অপরদিকে হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য অতি উৎসাহী মুসলমান ছেলেদের লাগিয়ে হিন্দু বসতি সমূহের পারিপার্শ্বিকতাকে বিষিয়ে দিতে লাগলেন। হিন্দু মেয়েদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত, নানা ধরণের গান ও ছড়া কাটা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ চালু করা হতে থাকল”।
গোড়ার উদ্বাস্তুরা উচ্চবর্ণের
এই সূত্রে তিনি হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আই সি এস এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্বের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সচিব ও মহাধ্যক্ষ) অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। হিরন্ময়বাবু তাঁর ‘উদ্বাস্তু’ বইতে ওপার থেকে আসা মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন, প্রথম দফায় দেশত্যাগীরা মূলত সম্পন্ন, বর্ণহিন্দু ভূস্বামী ও পেশাদার মধ্যবিত্ত, যারা ‘ভ্রদ্র শ্রেণীর উন্নত রুচির মানুষ’, এদের অপমানবোধ তীক্ষ্ণ’। “পাকিস্তান হওয়ার পরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হেতু এখন সেখানে তাঁদের মান- সম্ভ্রম- ইজ্জত নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়।’’ অন্যদিকে গরিব, চাষী-জেলে-তাঁতি প্রমুখ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কিন্তু এত সহজে দেশ ছাড়েননি। “ তখনও পূর্ব বঙ্গে পরিস্থিতি এত খারাপ হয়নি যে অত্যাচারের চাপে হিন্দু পরিবারগুলি আসতে বাধ্য হবে। যারা কৃষিজীবী এবং গ্রামের মানুষ তারা রাজনীতিতে এমন অভিজ্ঞ নয় যে পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক মুসলমান রাজ্য হওয়ায় হিন্দু হিসাবে তাদের কি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হবে তা হৃদয়ঙ্গম করবে। তাই ব্যাপক ভাবে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে।”
বিজয়গড়ের ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-র কথাতেও এই সামাজিক সত্যের অনুরণনঃ “পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুরা educated Hindu, এরা কেউ ভিখিরি ছিল না”। আলোচ্য বইটির বাকি স্মৃতিকথাগুলি থেকেও স্পষ্ট, দক্ষিণ কলকাতার কলোনিগুলির আদি পত্তনদার ও বাসিন্দাদের অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ- বৈদ্য ইত্যাদি উচ্চবর্ণীয় ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু। ওপারের নিম্নবর্ণীয় গ্রামীন শ্রমজীবীদের অভিবাসন পরে ঘটেছে। তাঁরা কলকাতার মধ্যে বিশেষ ঠাঁই পাননি।
সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান সুর ছিল না
হিরণ্ময়বাবুর কথায়, ১৯৪৯ সালের শেষে ‘উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত স্তিমিত হয়ে এসেছিল’। কিন্তু পরের বছর, ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্বের বাগেরহাটে ফের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধে এবং অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। পাল্টা শুরু হয় কলকাতা ও আশেপাশের জেলায়। ফলে ফের উভমুখী উদ্বাস্তু প্রবাহ নামে। “ মার্চ মাসে এই আশ্রয়প্রার্থীর স্রোত একমুখী হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দু পরিবারগুলি একান্তি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে খুন-জখমের ভয়ে এইভাবে দলে দলে বাস্তুত্যাগ করে চলে আসত, পশ্চিমবাংলা হতেও তেমন দলে দলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের অভিমুখে রওনা হত।” তাঁর হিসেবে নদীয়ার তেহট্ট ও করিমপুর এবং চব্বিশ পরগণার বাগদা-বনগাঁ ইত্যাদি এলাকা থেকে প্রচুর মুসলমান পরিবার ‘বাস্তুত্যাগী’ হন। এ থেকে স্পষ্ট আজকের সঙ্ঘীদের একতরফা হিংসা ও ভিটেমাটি-রুটি হারানোর বয়ান কতটা মিথ্যে।
ঢাকার বিক্রমপুর থেকে অনেক ঘুরে টালিগঞ্জের চার নম্বর মিনাপাড়া রোডে বাসা ভাড়া নিয়ে একটি জবরদখল কলোনি পত্তনের দিনগুলিতে ইন্দুবাবু মুসলমান পাড়াকে বেছে ছিলেন। “ আমাদের প্রতিবেশিরা সকলেই ছিলেন গরিব মুসলিম। এঁরা অধিকাংশি ছিলেন মজদুর, ছোট দোকানদার ও ফেরিওয়ালা। এঁদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি ছোট মাঠ ছিল। পরে জেনেছিলাম ওই মাঠে দেশবিভাগের পূর্বে মুসলিম লিগের সভা হত এবং পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানো হত। ওই মাঠটি এই অঞ্চলে পাকিস্তান মাঠ বলে পরিচিত ছিল। জনাব গোলাম আলি (মিনা, বর্ধিষ্ণু স্থানীয় মুসলমান তথা পুরোন টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার) এঁদের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং মিনা পরিবারই এই অঞ্চলের জমির মালিক। আমাদের বাড়ীতে প্রবেশের ডান হাতে বড় ঘরখানায় তখন থাকতেন এক বৃদ্ধ মৌলবি। তিনি আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে অবস্থিত মিনাপাড়া রোডের মসজিদটির মৌলানা ছিলেন। বাড়ির পশ্চিমদিকে ছিল একটি বেশ লম্বা ও গভীর ডোবাপুকুর। তার উত্তরদিকে মানুষপ্রমাণ জঙ্গলাকীর্ণ একটি পেয়ারাবাগান। বাড়ির উত্তর দিকে কয়েকটি মুসলিম পরিবার ছিল। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫-৩০ বিঘা খালি জমিটি নিয়ে মিনাবাড়িটি।” এই জমি-দখল করে উদ্বাস্তু কলোনি গড়াকে কেন্দ্র করে ‘জমিদার’ মিনাদের সঙ্গে তাঁর ও বসতকারী হিন্দুদের সংঘাত, মামলা-মোকদ্দমা হলেও প্রতিবেশি মুসলমানদের তাঁরা উচ্ছেদ করেননি বলে লিখেছেন।
মিনাদের জমির দখল পেতে দলিলপত্র জালিয়াতি করার প্রস্তাব নিয়ে স্থানীয় আর এক উদ্বাস্তু নেতার পক্ষে সাম্প্রদায়িক উস্কানি এলে তিনি তা নাকচ দেন। “ অমুকবাবুকে বলবেন,আমি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি। গোলাম আলি মুসলমান বলে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং আপনাদের মতো জোচ্চোর হিন্দুরাই দেশের শত্রু বলে আমি মনে করি। আরও শুনে যান, গোলাম আলিকে আমি এসব জমি উদ্বাস্তুদের কাছে ২০০ (শত) টাকা কাঠা দরে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি। সে জমির ফাটকা খেলতে চাইছে। হাজার টাকা কাঠা না হলে সে বিক্রি করবে না। তাই ভেবেছি, গরিব উদ্বাস্তুদের মধ্যে এ জমি আমি বিলি করে দেব।” তা বলে কি উদ্বাস্তুদের মধ্যে মুসলমান-বিদ্বেষ একেবারেই ছিল না? সত্যিটা এমন নয়।
“ প্রতিবেশি মুসলিমদের আমাদের প্রতি আস্থা ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে আমাদের অগোচরে তাঁদের উপর হামলা হলে আমরা তাঁদের রক্ষা করতে পারব না। বাস্তবিক পক্ষে তাই ঘটল। তৎকালে আমাদের কলোনির বাইরে উত্তর পশ্চিম দিকে জুম্মান আলি নামে একজন বিত্তশালী মুসলিমের একটি লাল রঙের দোতালা বাড়ি ছিল। সে বাড়ি লুট হয়ে গেল দিনের বেলাই। আমরা যখন খবর পেলাম, তখন দুষ্কৃতিকারীরা মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। আমাদের ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাঁদের লাগাম পেল না। বাড়িটিতে কোনও লোক ছিল না। তাই তাঁরা নিঃশব্দে বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে পারল। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই গরিব মুসলিম যারা তখনও ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।” ইন্দুবাবু ও তাঁর পার্টি-সতীর্থরা মিলে শান্তি সভা ও পাহারার ব্যবস্থা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। “… দু-চারদিন ভালো ভাবে গেলেও উদ্বাস্তুদের একাংশের আচরণে মুসলিমরা চলে যাওয়াই ঠিক করলেন। শেষের দিকে আমরাও আর বাধা দিলাম না, যখন শুনলাম, বিজয়গড়ের আর এস এসের কিছু তরুণ মাঝে মাঝে এসে উদ্বাস্তুদের একাংশকে নানা রকম উস্কানি দিচ্ছিল। পরে জেনেছিলাম, লাল দালানের লুঠের ব্যাপারেও এরাই জড়িত ছিল।’’ একই ধরণের ঘটনা অন্যত্রও ঘটেছে বলে ইন্দুবাবু লিখেছেন। “ রিজেন্ট কলোনির জমিতে গরিব মুসলমানদের বাড়ি ছিল। দাঙ্গার ভয়ে মুসলিমগণ অন্যত্র চলে যান”।
বিজয়গড় কলোনির শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও গৌরাঙ্গ দে চৌধুরীর মতো আদি পুরুষেরাও সঙ্কলনে তাঁদের সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এলাকায় মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে উদ্বাস্তু ছেলেদের খেলার মাঠের দখল নিয়ে ঝগড়া বাঁধলেও তা বড় গণ্ডগোলে পরিণত হতে তাঁরা দিতেন না। গৌরাঙ্গবাবুর কথায়, “ এই খানটায় তখন, অর্থাৎ শান্তিদার বাড়ির পাশটাকে মুসলমান ছিল। ওরা ঠিক বাধা দেয়নি। খেলার মাঠে একটু বাগবিতণ্ডা হয়। পল্লীশ্রী অঞ্চলে সব মুসলমান ছিল। এখনও তাঁরা আছে… শক্তিগড়ে ছিল দেরাজ মিঞা। ওই পাশে আরও মুসলমানদের জমি ছিল। তাদের জমি নেওয়া হয়নি।” সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কালিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মূলত ৪৭-৪৮ সালে যাদবপুর মিলিটারি ক্যাম্প ও পরে বিজয়গড় কলোনিতে এঁরা আসেন।
বিজয়গড়ের ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-র জবানিতে জানা যাচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে মারামারির তুলনায় তাঁদের লাঠালাঠি বেশি হয়েছে লায়ালকার মতো দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জমির মালিকদের গুণ্ডা-লেঠেল বাহিনী এবং পুলিশের সঙ্গে। হিমাংশু মজুমদার জানিয়েছেন, পুলিশ কমিশনার সামসুজ্জোহার জমি দখল করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে। তবে টালিগঞ্জ থানার তৎকালীন ওসি অমূল্যবাবু উদ্বাস্তুদের পক্ষে ছিলেন। ওই গোটা অঞ্চলে নলিনাক্ষ সান্যাল, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোক সেন এমন কি বিধান রায়ের মতো তাবড় কংগ্রেস নেতাদের জমিও জবরদখল করা নিয়ে সংঘাত বাঁধে।
কালাভাইয়ের স্মৃতিচারণায় দেখছি, লায়ালকার মাঠ দখল করা নিয়ে বিধান রায় খুব বিরক্ত হন। তিনি লায়ালকার কথামতো উদ্বাস্তুদের নাকতলায় যেতে রাজি না হয়ে সরকারি উদ্যোগে পুনরবাসনের দাবি তোলায় রেগে যান এবং মিলিটারি পাঠিয়ে উৎখাত করার হুমকি দেন। তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্বাস্তু নেতা তথা পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতা সন্তোষ দত্ত, যিনি ডাঃ রায়ের খুবি অনুগত ছিলেন, খেপে ওঠেন। “ বিধান রায় ডাকলে যে সন্তোষ দত্ত চোরের চাকর হয়ে যেত, সেই দিন [তিনি] দেখি যে আস্তিন গুটিয়ে বলে, ডক্টর রায় এই বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের হাড় মাংসের উপরে আপনার মানমর্যাদা তৈরি হয়েছে। আপনি আজ সেই মসনদে বসে আছেন। আপনি আমাদের মিলিটারি পাঠিয়ে দিয়ে উৎখাত করবেন। আই ইনভাইট ইওর মিলিটারি। আমার এখনও মনে আছে, এই কথা বলেই এভরিবডি অ্যাবাউট টার্ন।” বিধান রায় অবশ্য মিলিটারি পাঠাননি। তবে ‘পনেরটা লরি করে লায়ালকার হিন্দুস্তানি লেঠেল বাহিনী এসেছিল’। উদ্বাস্তুরা লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রতিরোধ করেন এবং কিছু গুন্ডাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। রেণুকা রায় , তৎকালীন পুনবাসন মন্ত্রী এসে গুন্ডামির খুব নিন্দা করলেও উদ্বাস্তু নেতাদের পুলিশি টানাহ্যাচড়া কিছুদিন চলে।
ছেচল্লিশের দাঙ্গার উন্মত্ততা উত্তর- মধ্য কলকাতার তুলনায় দক্ষিণকে কম ছুঁয়েছে। দেশভাগের প্রথম দুবছর দাঙ্গা-হাঙ্গামা তেমন হয়নি। ১৯৫০ সালে ঢাকায় দাঙ্গার খবরে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। ইন্দুবাবুর কথায়, “ ১লা মে শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনে মাষ্টারদার সঙ্গী ও পরে কম্যুনিস্ট উদ্বাস্তু নেতা) যুগান্তরে এক বিবৃতি দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের জন্য আবেদন করেন। উত্তর কলকাতার মুসলিম বস্তিগুলো থেকে মুসলিমদের হঠিয়ে দিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুরা ওইগুলি দখল করে নেয়। বেলগাছিয়ায় একটি মুসলিম বস্তি রক্ষা করতে গিয়ে ট্রাম শ্রমিক গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য নিহত হন।” কলকাতার দাঙ্গার আগুন এরপর ছড়িয়ে পড়ে বরিশালে ও অন্যত্র। ফের শুরু হয় উদ্বাস্তু প্রবাহ এবং তা আগের থেকে প্রবল বেগে। মাঝে কিছুটা তা থিতিয়ে গেলে ফের দাঙ্গার জেরে ’৬০-৬১ সালে তা আবার বাড়ে।
তবু আতঙ্ক ও বিদ্বেষের অন্ধকারেও মানবতার আলোগুলি নেভেনি। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড লাগোয়া এবং প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ মুসলিম কবরস্থানের অদূরে বাদাবন ও কিছুটা নাবালজমিতে গড়ে ওঠে রাজেন্দ্রপসাদ কলোনি। এখানকার আদিপুরুষদের নেতা কুমুদবন্ধু ঘটকের স্মৃতিচারনায় তাঁর ভাইপো বাসুদেব ঘটক লিখেছেন, ‘১৯৫০ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে ঠেলাগাড়ি ভর্তি মালপত্র সহ মাত্র দশজন সঙ্গী নিয়ে কলোনি’ গড়তে এগোন তাঁর জ্যাঠামশাই, আমৃত্যু কলোনিবাসীদের ‘বড়দা’ বলেই যার কথা ছিল শেষকথা।
মুসলমানদের কবরস্থান, মসজিদ ও মাজারের ঘেরাটোপে হিন্দু উদ্বাস্তুদের সেই কলোনি গড়ে উঠলেও প্রতিবেশিদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষায় দুই সম্প্রদায়ের বড়দের ভূমিকা ছিল। “এই মাজারের যিনি প্রধান ছিলেন তাঁর নাম হাজি মমতাজ হোসেন সাহেব। আমরা সবাই বলতাম দাদুসাহেব। এই দাদু সাহেব মুসলিমদের প্রতিটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র নিজের হাতে লিখে কলোনির সভাপতি বড়দাকে পাঠালেন। ... বড়দার সঙ্গে দাদুসাহেবের সৌজন্য এবং প্রীতির সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল। মুসলিমদের এক ইঞ্চি জমি বা গোরস্থানের এক ইঞ্চি জমি দখল না করায় দাদুসাহেব বড়দাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন দিতেন। আমাদের কলোনির মধ্যে একটা মুসলিম বাড়ি ছিল। তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেখানে পরবর্তী কালে কিছু উদ্বাস্তু মানুষ ঢুকে পড়েন। কিন্তু কোনদিনই এই বাড়িটিকে কলোনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাঁরা এখনও দলিল পায়নি।”
সংখ্যালঘু জনবিনিময় এবং নেহরু- শ্যামাপ্রসাদ বিতর্ক
সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সি এ এ) বিতর্কে প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে নেহরু-নিন্দা ও শ্যামাপ্রসাদ- বন্দনা প্রসঙ্গে নেহরু- লিয়াকত আলি খান (পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) চুক্তিকে তুলোধোনা করে বলেছেন, ওই চুক্তি পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতনের বাস্তবতাকে আড়াল করে এবং শ্যামাপ্রসাদের লোকবিনিময়ের বাস্তবধর্মী প্রস্তাবকে নাকচ করে সহিষ্ণু ভারত আর ইসলামিক পাকিস্তানকে একাসনে বসিয়ে দেয়।
পঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের তুলনায় বাঙালি বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন প্রশ্নে কেন্দ্রে নেহরু-প্যাটেলের সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ এবং সেই সূত্রে ভঙ্গবঙ্গে কংগ্রেস নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁর উত্তরসূরি ডাঃ বিধান রায়ের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা দীর্ঘকাল সরব ছিলেন। একই অভিযোগ করেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তাঁর হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘ। এখন জনসঙ্ঘের বর্তমান রূপ বিজেপিও সেই অভিযোগ করছে।
নেহরুর ভূমিকা প্রসঙ্গে ইন্দুবাবুর মনোভাব উদার। “তিনি পরিস্থিতির চাপে পড়ে লোকবিনিময় প্রস্তাব, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ এবং লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফল স্বরূপ পঞ্জাবের স্বতঃস্ফূর্ত লোকবিনিময় মেনে নিতে বাধ্য হলেও, কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতভূমিকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করতে রাজি ছিলেন না।” অন্যদিকে, পূর্ব বাঙ্গালার পরিস্থিতি নিয়ে গাঙ্গুলির মন্তব্যঃ “দেশবিভাগের সময় অথবা তার অব্যবহিত পরে পূর্ব বঙ্গে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। সুতরাং হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসুক এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান গণ পূর্ববঙ্গে চলে যাক এটা পন্ডিত নেহরু আন্তরিক ভাবেই চান নি। তাই লক্ষ লক্ষ হিন্দু যখন পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসছিল, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখারজির উভয়বঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব পন্ডিত নেহরু প্রত্যাখান করেন।”
নিচুতলার বামপন্থী কলোনি নেতা জীবনের উপান্তেও লোকবিনিময়কেই শান্তির একমাত্র পথ ভাবেননি। আবার বাস্তুবতাকেও লুকোননি। “ আন্ত-ডমিনিয়ম চুক্তি কার্যকর করার ফলে বাস্তবিকই পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে এসেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হল না। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের একাংশ এতে অসন্তুষ্ট হল। সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ না করলে তাঁদের জমিজমা বাড়িঘর, অপরাপর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই স্থানীয় প্রশাসনকে হাত করে, ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর মারফত সংখ্যালঘুদের উপর সামাজিক নিপীড়নের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল।”
বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গবেষক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ‘মারজিনাল মেন’ (বাংলায় ‘প্রান্তিক মানুষ’ নামে অনূদিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত) থেকে উল্লেখ করে গাঙ্গুলিমশাই লিখেছেন, “পূর্ব পাকিস্তান সফর করে এসে পন্ডিত নেহরুকে ডঃ ঘোষ একটি মেমোরেন্ডাম পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ‘ বাঙালি উদ্বাস্তুগণ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেই তাঁদের পরিত্যক্ত গৃহে ফিরে যাবার যৌক্তিকতা মেনে নেবেন’। পূর্ব পাকিস্তানগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ডঃ ঘোষের ওই মন্তব্য, পন্ডিত নেহরুকে সবিশেষ সুখী করেছিল। কারণ, তিনিও তাই চাইছিলেন। কিন্তু অপর দিকে সংশ্লিষ্ট উদ্বাস্তুদের ভাগ্য এক ন্যক্কারজনক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। ভারত সরকার ড: ঘোষের সুপারিশ মতো বহুদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, শুধু রিলিফ দেওয়ার মানসিকতা নিয়েই চলে ছিলেন। ফলে উদ্বাস্তুদের দুর্ভোগের পরিমাণই বৃদ্ধি পেয়েছিল।”
উল্টোদিকে বিধান রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে কম্যুনিস্ট কর্মী ইন্দুবাবু সপ্রশংস। “ ডঃ রায় ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রনায়ক। তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন, উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি অবান্তর ও অবাস্তব... [তিনি] বুঝেছিলেন যে লক্ষ লক্ষ অবহেলিত উদ্বাস্তু সমস্যাই তখন পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জটিল এবং ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সূচক। তাই এক ধারে, তিনি পন্ডিত নেহরুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের জন্যে চাপ দিতে শুরু করলেন এবং কলকাতার বাইরে [তৎকালীন শহরসীমার বাইরে আজকের মহানগর ও বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে] পড়ে থাকা সামরিক ব্যারাক (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) – সমূহকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে হস্তান্তরের প্রস্তাব করলেন। সেই অনুমতি পাওয়া গেলে, বিভিন্ন স্থানে জড়ো হওয়া উদ্বাস্তুদের ওইসব পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকে আশ্রয় দেওয়া শুরু করলেন। ” তবে তার আগেই, “কলকাতায় অবস্থিত ... লেক ক্যাম্প, যোধপুর ক্যাম্প, যাদবপুর ক্যাম্প , বি আর ক্যামপ, দুর্গাপুর ক্যাম্প প্রভৃতি [পরিত্যক্ত ব্যারাক] ডঃ ঘোষের আমলেই উদ্বাস্তুদের দখলে চলে যায়।”
হিরণ্ময়বাবুর বদান্যতায় ‘কালাভাই’ ও ‘বাঘা’ ওরফে সন্তোষ দত্ত (ফরিদপুরের কংগ্রেস নেতা ও দক্ষিণ কলকাতার উদ্বাস্তু নেতা) কলকাতায় রাজভবনে নেহরুর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। সে বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণঃ “ প্রশ্নঃ তিনি আপনাদের অবস্থা উপলব্ধি করলেন? মানে, আপনাদের calamity উপলব্ধি করলেন? হ্যাঁ, তিনি উপলব্ধি করেন। তবে মজা কি জানেন তিনি বললে কি হবে! রাজা করে উপলব্ধি, কিন্তু নিচে মেহেরচাদ খান্না-টান্না পঞ্জাবের লোক। তারা সব সুযোগ- সুবিধাগুলি পঞ্জাবে নিয়ে নিতে পাগল। উনি সেদিন বিজয়গড়ের কথা মিটিঙয়ে উল্লেখ করেন। তখন ১৯৫১ সালে একটা আইন পাশ হয়, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জবরদখল কলোনিতে যারা বসতি করেছে তাঁদের পুর্নবাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা চলবে না। এই সময় প্রায় ১৪৯ টি উদ্বাস্তু কলোনি সারা পশ্চিম বঙ্গে স্থাপিত হয়ে হয়েছে।”
প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই বিভক্ত পঞ্জাবের মতো বাংলাতেও সাম্প্রদায়িক লোকবিনিময়ে রাজি না হওয়ার জন্য নেহরুর সমালোচনা, শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ মেঘনাদ সাহা ও আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রশস্তি করেছেন। দেশভাগের অব্যবহিত আগে গান্ধী ও নেহরু পাকিস্তানের হিন্দু-শিখদের সেখানে না থাকতে পারলে ভারতে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেন, সে কথাও মনে করান। প্রথম জন তাঁর ‘প্রান্তিক মানুষ’ বইতে লিখেছেনঃ “ ১৯৫০-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদে এবিষয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছিল। নেহরু বললেন, জনবিনিময়ের প্রস্তাব ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আরও বড় আদর্শ জড়িয়ে আছে। এতে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ মুখারজি বলেছিলেন যে পঞ্জাবে জনবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় পন্ডিত নেহরুর বিশ্বাস ভঙ্গের ব্যাপারটা হিমঘরে রেখে দিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতেও বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারটা সেভাবেই ঠান্ডা ঘরে তুলে রেখে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মতো পরিস্থিতির মোকাবিলা করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নেহরু ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডঃ মুখারজির যুক্তিতে তিনি কান দিলেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা যাতে পূর্ববঙ্গে চলে না যায় তার ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বের দরবারে তাঁর ভাবমূর্তি অটুট রইল। তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদে আছে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্য ১৯৫০-এর জনবিনিময়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সহজ সমাধানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন নেহরু। তিনি পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের রক্ষা করলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঠেলে দিলেন এক শ্বাসরোধকারী অন্ধকারের দিকে।”
তুলনায় নরম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য। “ যারা আশাবাদী তাঁরা ভাবেন, হয়ত সদিচ্ছা থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রোষবহ্নি হতে রক্ষা করা যায়। শ্রী জহরলাল নেহরু হয়ত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু আমি তো দেখেছি, রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। আমি তো জানি ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবিরের কাছে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কেবল রোষবশেই মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম কে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিদ্বেষপ্রণোদিত হলে মানুষ যে উন্মাদের মতো আচরণ করে এবং সকল সদগুণ বিসর্জন দিয়ে জঘন্য আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, তাও দেখেছি। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা যিনি, নিজের আশ্রিত মুসলমানকে [গাড়ির চালক] রক্ষা করবার জন্য জনতার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি হলেন আলেকজান্ডার লেসলি ক্যামেরন, অ্যান্ড্রু ইউল কোম্পানির বড় সাহেব’’।
দুই জনেই লিখেছেন, দেরিতে হলেও উদ্বাস্তু আন্দোলন ও বঙ্গীয় নেতা-বুদ্ধিজীবীদের চাপে নেহরু দু বার কলকাতায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখেন এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এপারে স্থায়ী পুনর্বাসনের পক্ষে নীতি বদলান।
বামপন্থী ও অন্যদের ভূমিকা
কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের প্রতি, বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে, ইন্দুবাবুর অভিযোগঃ “ কলোনি আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির কোনও উদ্যোগ নেই। তাছাড়া পার্টি নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের পলাতক, ভীরু ও কাপুরুষ বলে মনে করে।” তবে দলের কর্মীদের ভূমিকা তিনি ভোলেননি। “ কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব তখন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কমিউনিস্ট কর্মীদের দাঙ্গা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি কোনোদিন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষায় স্থানীয়ভাবে চিরদিনই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং গুন্ডামি প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণও দিয়েছেন অনেকে”।
পরে বাস্তুহারা কর্মপরিষদ, বিশেষ করে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি আর সি) গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় সি পি আই। সেই প্রসঙ্গে ইন্দুবাবুর বক্তব্যঃ “ ইউ সি আর সি-তে দশটি বামপন্থী দলের সক্রিয় সমাবেশ ও সর্বসম্মত আচরণ প্রভৃতিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজ্য নেতৃত্বের মনে ইউ সি আর সি-র উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে, বিকল্প পার্টির নেতৃত্বের কেন্দ্র রূপে সন্দিহান করে তুলেছিল। তারই ফল কিনা জানি না, কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব উদ্বাস্তু সমস্যার উপর কোনও দিনই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি! অথচ তাদের প্রয়োজনে উদ্বাস্তুদের কাজে লাগানোর আগ্রহে অভাব ছিল না। প্রথম দিকে পার্টি সন্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিতে উদ্বাস্তু সমস্যার কোনও হদিসই মিলত না। এনিয়ে উদ্বাস্তু ফ্রণ্টের কমরেডদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ ছিল। পরে অবশ্য এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছিল, তাও নাম-কা- ওয়াস্তে কয়েকটা লাইন ব্যয় করা হত। আসলে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে বামপন্থী বিচ্যুতির ঝোঁক তো কমবেশি বজায় ছিলই, অধিকন্তু উদ্বাস্তুদের প্রতি একটা অনীহা ও নাক-সিঁটকানোর ভাব বর্তমান ছিল।”
নাগরিকত্বের রাজনীতিঃ রাজীব- বাজপেয়ী পর্ব
বইটিকে সঙ্গত কারণেই উৎসর্গ করা হয়েছে ‘এন আর সি, কা আর এন পি আর-র বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষদের’। বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য দীর্ঘকাল চাপান- উতোর চললেও তাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে কোঁদল আমরা এই রাজ্যে বিশেষ শুনেছি বলে মনে পড়ে না। উদ্বাস্তুরা ভোটাধিকার সহ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারগুলি পেয়েছেন। ধর্মভিত্তিক দেশভাগ ও দাঙ্গাদীর্ণ হলেও স্বাধীন ভারতের আদিপুরুষেরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তথা নাগরিকতার পথ নিয়েছেন। সারা দুনিয়াতেই জন্মস্থান বা রক্তধারা সূত্রে, অথবা দুটি মিলিয়ে ব্যক্তির রাষ্ট্রীয়তা ও নাগরিকতাকে মেনে নেয়ার ব্যবস্থা। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনেরও মূল কথা ছিলঃ নিজের জন্মসূত্রে বা বাবা-মায়ের সূত্রে যারাই ভারতের বাসিন্দা তাঁরাই এদেশের নাগরিক। আরও বড় কথা, জন্ম বা রক্তসূত্রে অবিভক্ত ভারতের বাসিন্দাদের যারা ভারতকে স্বদেশ মানেন, এমনকি তারা দেশভাগের পর ওপারে চলে গেলেও কিছু শর্ত মেনে ফিরতে পারেন। এছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের বসবাস সূত্রে অভারতীয়দেরও এই অধিকার মিলতে পারে। বিদেশে থাকা ভারতীয় মূলের মানুষও শর্ত সাপেক্ষে এই অধিকার পাবেন।
পরবর্তী কালে উপমহাদেশে চারটি ভারত-পাক যুদ্ধ ও বাংলাদেশের জন্ম ঘিরে সংখ্যালঘু-উদ্বাস্তু সমস্যার বৃদ্ধি এবং পরে অসমে বিদেশি-খেদা আন্দোলন ও অসম-চুক্তির জেরে ধাপে ধাপে নাগরিকত্ব পাওয়ার শর্তগুলিতে কড়াকড়ি হয়েছে। কিন্ত আইনটিতে সবচেয়ে মারাত্মক পরিবর্তন করা হয়েছে ২০০৩ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে। তাতে ওই আইন লাগু হওয়ার সময় বা তারপর জন্ম হলে বাবা-মায়ের দুজনকেই ভারতের নাগরিক হতে হবে। অথবা দুজনের কেউ একজন সন্তানের জন্মকালীন অবৈধ ভাবে ভারতে এসে থাকলে জাতক আর জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাবে না। এছাড়া বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধের পর্বকে মাথায় রেখে শর্ত আরোপিত হয়, বাবা-মায়ের কেউ যদি শ্ত্রুদেশের নাগরিক হন বা তাঁদের সন্তানের জন্ম যদি শত্রু-অধিকৃত দেশে হয়ে থাকে, তবেও তিনি বঞ্চিত হবেন।
রাজীব গান্ধী-আসুর অসম-চুক্তি মোতাবেক, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত, অর্থাৎ পাকবাহিনী পূর্ববঙ্গে বাঙালিদের গণহত্যা অভিযান শুরু পর্যন্ত ভারতে ঢুকে থাকলে ছাড় মিলবে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় সেদিন থেকেই। সরকারি ভাবে ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবস পালন করে। বাস্তুবে পূব থেকে পশ্চিমে ও উত্তর-পূবে উদ্বাস্তু প্রবাহ বন্যা বেগে ঢুকেছে ওই তারিখের পর। ভারত তা দেখিয়ে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এবং ডিসেম্বরে সরাসরি যুদ্ধজয়ের আগে কূটনৈতিক সাফল্য পেয়েছে বটে। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্থাপনে সাফল্যের জন্য বিরোধী নেতা বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ‘দেবী দুর্গা’র সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু ২০০৩ সালে নিজের রাজত্বে সেই একাত্তরের উদ্বাস্তুর সন্তানদের তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বানিয়ে দেন।
ওই সংশোধনীতে সূত্রেই এসেছে বাধ্যতামূলক নিবন্ধিকরণ (রেজিস্ট্রেশন) ভিত্তিতে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এন আর সি) প্রণয়ন, জাতীয় নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ স্থাপন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, আইনের অনুসারী বিশদ- নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে, এন আর সি তৈরি করার প্রথম ধাপ হবে জাতীয় জন পঞ্জি বা এন পি আর। সেটা তৈরির সময় আমলাদের সন্দেহ হলে নাম সন্দেহজনক তালিকায় ঢুকে যাবে। তা থেকে বাঁচলেও প্রকাশিত খসড়া তালিকায় কারো নাম দেখে প্রতিবেশি কেউ আপত্তি তুললে এবং তার সন্তোষজনক জবাবদিহি ও কাগজপত্র না দেখাতে পারলেই, ব্যস ঘচাং ফু। পরে অসম-এন আর সি এই চিত্রনাট্যই অনুসৃত হয়েছে।
হ্যাঁ, এটাও দাগিয়ে রাখা জরুরি যে কংগ্রেস-বাম ইত্যাদি বি-জেপি বিরোধী দলগুলি তখন উচ্চবাচ্য করেনি। সম্ভবত অসম সহ পরবর্তী উত্তর-পূর্বের ভোট-রাজনীতির অঙ্ক মাথায় রেখে। আর তৃণমূল তো তখন বিজেপির সঙ্গেই। ২০০৪ সালে কংগ্রেস- নেতৃত্বে প্রথম ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় এসে বিজেপি-জমানার অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতে মূল নাগরিকত্ব আইনে ১৪ ক ধারা যোগ করে। ২০১০ সালে দ্বিতীয় ইউ পি এ আমলেই হয় জাতীয় জনপঞ্জি (এন পি আর)-এর উদ্যোগ। তবে এখন কংগ্রেস নেতারা দাবি করছেন ওদের এন পি আর বাবা-মায়ের ঠিকুজি-কুষ্টি জানতে চায়নি যেটা মোদী সরকার চাইছে বাংলাদেশি বলে মুসলমানদের ছেঁটে ফেলতে। বিজেপি অবশ্য বলছে কংগ্রেসের পথেই তাঁরা হাঁটছে, একটু জোরে এই যা!
মোদী-শাহ পর্ব
২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই মোদী একে একে পাসপোর্ট আইন, বিদেশি নিবন্ধীকরণ আইন ইত্যাদি সংশোধন করে ২০১৫-১৬ সালে ফের নাগরিক আইন বদলে ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্বের পথ প্রশস্ত করেন। না তখনও বিরোধীদের ঘুম ভাঙ্গেনি। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বার বাড়তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সি এ এ) পাস করে আর এস এস- পরিচালিত বিজেপি সরকার প্রতিবেশি তিন ইসলামী দেশ—বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে বেআইনি পথে আসা অভিবাসীদের মধ্যে অমুসলমান- মুসলমানে ভাগাভাগি করেছে। সরকার এই আইনের বলে মূলত হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তারপর দেশ জুড়ে অসম ধাঁচে জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এন আর সি) এবং তার প্রথম ধাপ জাতীয় জনপঞ্জি (এন পি আর) বানিয়ে অভিবাসী মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে তাড়ানোর বা আজীবন বন্দি বানানোর ফন্দি এঁটেছে। সেই তালে দেশীয় মুসলমানদেরও একটা বড় অংশের যথাযথ কাগজপত্র না থাকার অজুহাতে নাগরিকত্ব, বিশেষ করে ভোটাধিকার ও অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের রাষ্ট্রহীন বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানানো যাবে।
এর স্বপক্ষে সঙ্ঘ-সরকারের যুক্তিঃ ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা হিন্দুদের তো বটেই, পরবর্তী কালে ধর্মীয় নিপীড়নের জেরে চলে আসতে বাধ্য হওয়া হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান প্রমুখদেরও স্বীকৃতি দিচ্ছে। এভাবে তাঁরা নাকি কংগ্রেস-কৃত দেশভাগের ঐতিহাসিক অন্যায়কে শুধরে নিচ্ছে, বাংলাদেশ-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করায় নেহরু ও তাঁর উত্তরসূরিদের ব্যর্থতাজনিত সমস্যার সমাধান করছে। এমনকি বিশ্বের নিপীড়িত হিন্দুদের একমাত্র স্বদেশ বলে ভারতকে নিশ্চিত করছে। আসলে এভাবেই মুখে দেশভাগের নিন্দা করলেও সঙ্ঘ পরিবার উপমহাদেশের তিন রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বিনিময়ের অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করতে চাইছে। জিন্না ও সাভারকরের দ্বিজাতি তত্ত্বকে পুরোপুরি কায়েম করতে সাতচল্লিশের জাতক ধর্মনিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রকে আমূল বদলে তাঁদের স্বপ্নের হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার ব্যবস্থা করছে। পূর্বপুরুষদের পাকিস্তান চাওয়ার ও পাওয়ার অপরাধে ভারতীয় মুসলমানদের আজকের প্রজন্মকে শাস্তি দিতে চাইছে।
বাঙালি এখন ভাগের মা
সঙ্ঘী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান অভিঘাত পড়েছে অসম-সহ উত্তর- পূর্বে এবং পশ্চিমবাংলায়। মূলত বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানরাই এর টার্গেট। বাংলাদেশি সন্দেহে আসামের এন আর সি থেকে বাদ পড়া ১৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে আনুমানিক ১২ লক্ষই বাঙালি। এবং তাঁদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। অসমে ইতিমধ্যে ‘ডাউটফুল ভোটার’ তালিকা ভুক্ত আরও কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যেও বাঙালিই বেশি। এর অব্যবহিত আগে বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি হিন্দু তথা উদ্বাস্তু-প্রেমে ভুলে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার হিন্দু বাঙালিরা সেখানে গেরুয়া প্রবাহে গা ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু অসম এন আর সি-র শেষতম তালিকায় বাদ-পড়াদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু হওয়ায় তাঁরা এখন দিশেহারা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরীব বাঙালি এবং কিছু পরিমাণে নেপালি-বিহারী শ্রমজীবীদের জীবন ইতিমধ্যে নারকীয়। এদিকে এতকালের কয়েক কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর গালগল্প চুপসে যাওয়ায় বিজেপির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির ছকও ঘেঁটে গেছে। তাই তাঁরা সি এ এ-র খুড়োর কল ঝুলিয়ে হিন্দু বাঙালিদের বরাভয় দিচ্ছে।
কিন্তু এতে ভয়ঙ্কর চটেছেন কেন্দ্র ও রাজ্যে সঙ্ঘী সরকারের সোদর অসমীয়া ভাষিক-এথনিক উগ্র জাতীয়তাবাদীরা। এঁদের জনসংখ্যাগতভাবে বাঙ্গালি-প্রাধান্যের ভীতি-জারিত বিদ্বেষ দেশভাগের আগে থেকেই প্রবল। এর নেপথ্যে ইংরেজ সরকার-কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভা-মুসলিম লিগের কুটিল রাজনীতির টানাপড়েনের সঙ্গে দুই ভাষার এলিট বর্ণহিন্দু ভ্রদ্রলোকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। স্বাধীনতার পর তার সঙ্গে জুটেছে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের প্ররোচনা। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পর্বে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বে শরণার্থীর ঢল তাঁদের নিজভূমে পরবাসী হওয়ার আশঙ্কা ও বাঙালি-বিদ্বেষ আরও বাড়িয়েছে। আটের দশকের অসমে বিদেশি-খেদা আন্দোলন এর ফল। সঙ্গে বাজপেয়ী-আডবানী জমানার বিজেপির তালবাদ্যি।
এখন অসমীয়ারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোনও বাঙালিকেই আর সি এ এ-র সুযোগ নিতে দিতে রাজি নন। উল্টে অসমের বিজেপি-অগপ সরকার অসম এন আর সি-র পর্যালোচনা চাইছেন। কেন না তাঁদের দাবি, অনেক কম অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। বাকিরা সারা ভারতের সঙ্গে ফের অসমে এন আর সি চান যাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আরও বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু এতে বিজেপি-র বঙ্গবিজয়ের স্বপ্ন আটকে যেতে পারে। একারণেই সঙ্ঘের হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও অসমীয়া ভাষিক-এথনিক জাতীয়তাবাদের ঠোকাঠুকি লেগেছে। সংশোধিত আইনে অসম-সহ উত্তর-পূর্বের জনজাতীয়প্রধান এলাকাগুলি এবং চীন-মায়ানমার সীমান্তবর্তী মূলত খ্রিষ্টানপ্রধান রাজ্যগুলিতে, যেখানে ব্রিটিশ আমলের ‘ইনার-লাইন পারমিট’ ব্যবস্থা জারি রয়েছে, সে সব জায়গায় উদ্বাস্তু বা বেআইনি অভিবাসী হিন্দু বাঙালিদের পাকাপাকি শেকড় নামানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। মেঘালয়ের মতো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যে জনজাতীয় ছাত্র ও অন্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলি সেখানেও ইনার-লাইন পারমিট ব্যবস্থা দাবি করছে। মূলত বাঙ্গালি-বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাঝেমধ্যেই ঘটছে।
এমন নয় যে সঙ্ঘী-শাসনে বাকি ভারতে বাঙালিরা নিরাপদ। বিজেপি-শাসিত কর্ণাটক-উত্তরপ্রদেশ-উত্তরাখণ্ড এবং সঙ্ঘী মতাদর্শের শরিক শিবসেনা-শাসিত মহারাষ্ট্র ও খোদ রাজধানী দিল্লি থেকেও বাংলাদেশি বা মায়ানমার থেকে উৎখাত রোহিঙ্গা সন্দেহে গরীব বাঙালিদের বিতাড়ন চলেছে। বাঙালিরা এখন ভাগের মা। অথচ বাস্তবতা হল নামে দেশভাগ হলেও আসলে ভাগ হয়েছিল পঞ্জাব ও বাংলা। বাকি ভারতকে এই বিভীষিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক অভিঘাত বিশেষ সইতে হয়নি।
দেশভাগকালীন দাঙ্গা-গণহত্যা-ধর্ষণ-লুন্ঠনের ব্যপ্তি ও ভয়াবহতা এবং অন্যান্য কারণে মুসলমানপ্রধান পশ্চিম ও শিখ ও হিন্দুপ্রধান পঞ্জাবে জনবিনিময় কার্যত সম্পূর্ণ। বিপরীতে মুসলমানপ্রধান পূর্ববাংলা ও হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গা-গণহত্যা-ধর্ষণ-লুন্ঠনের ব্যপ্তি ও ভয়াবহতা (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও নোয়াখালী কান্ড সত্ত্বেও) তুলনায় কম হওয়ায় সাতচল্লিশে উভমুখী উদ্বাস্তু প্রবাহও কম ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ও কলকাতায় পঞ্চাশের দাঙ্গার জেরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে হিন্দু ও উল্টোদিকে মুসলমান বাঙালি ও উর্দুভাষীদের যাত্রা বাড়ে। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাকে অনেকটা প্রশমিত করলেও পাকিস্তানপন্থী লিগ ও জামাতি রাজনীতি ’৬৪-৬৫ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল কান্ড এবং ভারত-পাক যুদ্ধ দাঙ্গাবাজদের ফের সুযোগ এনে দেয়। বিশেষত একাত্তরে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ফৌজি তাণ্ডবের দিনে বিপুল জনস্রোত এপারে আছড়ে পড়ে। দফায় দফায় এপারে এসে পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই না মিললে আন্দামান থেকে দণ্ডকারণ্য, উত্তরাখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব ছড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের উত্তর প্রজন্ম স্থানীয় ভাষা- সংস্কৃতি শিখেও ‘বহিরাগত’ বা ‘বিদেশি’ বলে লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের শিকার।
উপমহাদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা
ফৌজি জেনারেল ও সামন্ততান্ত্রিক এলিট প্রভুদের কল্যাণে জন্ম থেকেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র শেকড় পায়নি মাঝেমধ্যে নির্বাচন সত্ত্বেও। জিন্নার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও হিন্দু-শিখ ও খৃষ্টান উপরদের নিপীড়ন বন্ধ হয়নি। নয়া শাসকদের শোষণ-দুর্নীতি-দমনের বিরুদ্ধে গ্রামীন ও শহুরে আমজনতার ক্ষোভ ঘুরিয়ে দিতে সব কালে সব দেশে সংখ্যালঘুদের বলির বকরা বানানো হয়। আটের দশকের গোড়া থেকে জেনারেল জিয়াউল হকের জমানায় ফৌজি- জিহাদি যুগলবন্দির শুরু। কাশ্মীর ঘিরে ভারত-পাক দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয় আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে মার্কিন-সৌদি-পাক মদতে সুন্নিপ্রধান জিহাদ। কালক্রমে তার ফ্রাঙ্কেনস্তাইন ফসল হল আল কায়দা ও তালিবান এবং আইসিস। এরা বিধর্মী তো দূর, স্বধর্মী শিয়া-আহমেদিয়াদের কচুকাটা করে। নারীর সমানাধিকার ও স্বাধীনতার প্রবক্তাদের খুন করা এদের কাছে পবিত্র কর্তব্য। পাকিস্তানে ও বাংলাদেশেও এদের ভাবশিষ্যরা বেড়ে উঠেছে। ফৌজি-জিহাদি-মৌলবাদী মোল্লাদের হাত ধরেই ইমরান খানের ক্ষমতালাভ। পাকিস্তানের শিক্ষিত নাগরিক সমাজ দুর্বল হলেও বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-আইনজীবী ও ছাত্রদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে ও সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই থেমে থাকেনি। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ থেকে আসমা জাহাঙ্গির, আই আর রহমান, নাজম শেঠিরা এর উদাহরণ।
দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, শেখ মুজিব-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশেও জিয়া-এরশাদ দুই জেনারেলের ফৌজি শাসন বা বকলমায় জিয়াপত্নী খালেদার বি এন পি ও পাকপন্থী জামাতিদের জমানার পর্বে আওয়ামি লিগের ভোটার বলে পরিচিত হিন্দু-বৌদ্ধদের উপর নিপীড়ন হয়েছে। তার জেরে দফাওয়ারি উদ্বাস্তু প্রবাহ চলেছে। মুজিব-কন্যা হাসিনার শাসনকালে তা অনেক কমে এলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। একাত্তরের চেতনার শরিকদের মধ্যে ভাষিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব-ধন্দ ছিল যা পরে প্রকট রূপ ধারণ করে এবং মুজিব-হত্যার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ক্ষমতায় ফিরলেও বাংলাদেশি মুসলমান জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব বেড়েছে বই কমেনি। এর সাথে সৌদি ও পারস্য উপসাগরীয় তৈল-পিচ্ছিল দেশগুলির রক্ষণশীল জমানাগুলির মদতে মূলত সুন্নিপ্রধান ইসলামিক মৌলবাদ এবং জিহাদি সন্ত্রাসবাদের আবেদন বেড়েছে। ফলে নানা নামে জামাতি-হেফাজতি মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে অনেক আপস করে চলেছেন হাসিনা। যদিও শাহবাগ প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে সম্প্রীতি, মানবিক ঐক্য ও মুক্তবুদ্ধি দেশ-কালচেতনার পক্ষে লড়াই করছেন।
এদেশে কংগ্রেস আমলে এদেশে মূলত উত্তর ভারতে মুসলমান ও শিখদের বিরুদ্ধে অনেক দাঙ্গা, গণহত্যা হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরের হিন্দু প্রাধান্যবাদীরা ছিল প্রধান চক্রী। অসমে ভাষিক-এথনিক জাতীয়তাবাদীদের উস্কানিতে গণহত্যার শিকার হয়েছেন মূলত বাঙালি মুসলমান। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদ ও সংখ্যালঘু নিপীড়ন সঙ্ঘ পরিবার কেন্দ্রে পূর্ণ ক্ষমতায় আসার আগে প্রবল হয়নি। নয়ের দশকে এপারে সঙ্ঘ পরিবারের রাম জন্মভূমি আন্দোলনের জেরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, ভারত জুড়ে দাঙ্গা এবং একুশ শতকের গোড়ায় গুজরাতে মুসলমানদের গণহারে হত্যা এই রাজনীতির ধারাবাহিক মাইলফলক। তার জেরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে শিখ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ বাড়ে।
দুই সীমান্তের ওপারে হিন্দু- বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ- অত্যাচারের ঘটনা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সঙ্ঘিরা প্রচার করে। কিন্তু এপারে মুসলমান-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-গণহত্যায় নিজেদের ভূমিকা ধামাচাপা দেয়। ওপারে তাদের ভিন রঙের গুরুভাইদের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। এভাবে এখন বৃহত্তর উপমহাদেশে ইসলামিক মৌলবাদ ও হিন্দু মৌলবাদ এবং শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারে বৌদ্ধ আধিপত্যবাদ পরস্পরের জুজু দেখিয়ে যে যার দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। ভারতের মতো যেখানে তাঁরা ক্ষমতায় সেখানে এটা এখন তুঙ্গে। আরও যেটা আশঙ্কার যে সব কটি জাতিরাষ্ট্রেই সংখ্যাগুরু ধর্মীয়-এথনিক বা ভাষিক জনগোষ্ঠীগুলির জনমত মোটের উপর সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী শাসকদেরই পক্ষে। পশ্চিমি দুনিয়া জুড়ে ইসলামভীতির সূত্রে নয়া নাজিদের রাজনৈতিক উত্থান একে আন্তর্জাতিক মান্যতা দিচ্ছে।
অধুনা ভঙ্গবঙ্গের রাজনীতি
অধুনা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান জনভিত্তি তথা ক্ষমতার চাবিকাঠি হল মুসলমান সমাজ। এর সঙ্গে হিন্দু নমঃশুদ্র সম্প্রদায় যারা দক্ষিণবঙ্গে তফশিলি হিন্দুদের প্রধান গোষ্ঠী যারা রাজ্যের নিম্নবর্ণীয় হিন্দু জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ। উত্তরে রাজবংশীরা তপশিলিদের ১৮ শতাংশ। বাম আমলে এই তিন সামাজিক শক্তি মূলত কংগ্রেস ও বামেদের সঙ্গে থাকলেও পরে তা মমতার দিকে সরে যায়। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু উন্নয়নে বামফ্রণ্ট সরকারের ব্যর্থতা (সাচার কমিটি রিপোর্টে যা ধরা পড়ে) এবং মরিচঝাঁপিতে দলিত উদ্বাস্তু উপনিবেশ উৎসাদনে জ্যোতি বসু মন্ত্রীসভার বীভৎস পুলিশি অভিযান এর অন্যতম বড় কারণ। কিন্তু দেশে ও রাজ্যে বিজেপির উত্থান মমতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে নয়ের দশকে বিজেপি-র হাত ধরে রাজ্য রাজনীতিতে তখনও এই প্রান্তিক দলটিকে তিনিই প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে বাজপেয়ী-আদবানি আমলে বিজেপির- নেতৃত্বে এন ডি এ সরকারের মন্ত্রিত্ব চালিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের উত্থানের সূচক গুজরাত গণহত্যার পর্বেও। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় এখন বিজেপি তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ।
মমতার মুসলমান জনভিত্তির বিপরীতে বিজেপি এখন উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয় নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে ওপারের মুসলমানদের দ্বারা অতাচারের স্মৃতি খুঁচিয়ে তুলেছে। নিম্নবর্ণীয় গরিব চাষি-জেলে-তাঁতি প্রমুখ হিন্দু শ্রমজীবীরা উচ্চবর্ণীয়দের পরে এপারে এসেছেন দফায় দফায় এমনকি একুশ শতকের গোড়ার দিকেও। তাঁদের নিগ্রহের জনস্মৃতি অনেক টাটকা। তুলনায় থিতু উচ্চবর্ণের একদা-উদ্বাস্তুদের চেয়ে চলতি জীবনসংগ্রামের নানা সমস্যা সূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে দাবিদাওয়া এঁদের মধ্যেই বেশি। বিশেষ করে বিজেপির টার্গেট নমঃশূদ্রদের প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী মতুয়া সম্প্রদায়। গত লোকসভা ভোটে এঁদের মধ্যে বিভাজনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে বিজেপি। সেই প্রভাব বাড়াতে সি এ এ বা নয়া নাগরিকত্ব আইন এখন গেরুয়া শিবিরের তুরুপের তাস।
দেশের মধ্যে বাংলার প্রতিই এখন বিজেপির শ্যেন দৃষ্টি। কিন্তু বাংলা ও বাঙালির ঘোর সঙ্কটের দিনে রাজ্যের শাসক দল ও অবিজেপি বিরোধীদের, বিশেষ করে কংগ্রেস ও বামেদের নিরন্তর কাজিয়া থেকে মনে হতে বাধ্য, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ ভিন্ন আর এঁরা আর কিছু ভাবতে রাজি নন। দিল্লি ও কলকাতায় সেকুলারদের মুষলপর্ব চলতে থাকলে একুশে শেষ হাসিটা হয়তো সঙ্ঘ পরিবারই হাসবে।
উদ্বাস্তুদের কাছে আমাদের কথা
এই সম্ভাবনাটা আটকাতে আমরা যারা নাগরিক সমাজের শরিক এবং নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে, তাঁদের গ্রামে ও শহরে উদ্বাস্তু বাঙালিদের কাছে পৌঁছোতে হবে। দেশভাগের ক্ষতবহনকারী বাঙালি হিন্দুদের এখন সি এ এ- এন আর সি-র পক্ষে মুসলমান-বিরোধিতায় খেপিয়ে তোলা সহজ এটা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে পরে আসা নিম্নবর্ণীয়দের, ২০০৩ সালে যাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটাও বাস্তব যে তাঁদের অনেকে আজ সি এ এ-র পক্ষে। পথে নেমে ওই মানুষগুলোর কথা আমাদের ধৈর্য ও দরদের সঙ্গে শোনা জরুরি। তাঁদের আগের প্রজন্মের স্মৃতিকথাগুলিকেও পড়তে হবে, জানতে হবে। আমরা যারা উচ্চবর্ণের তাঁদের পাপের বোঝা এতে কিছুটা হয়ত কমবে।
তাঁদের বোঝাতে হবে উদ্বাস্তু-বেদনার শরিক হয়েও কেন আমরা এই ধর্মভিত্তিক নাগরিকতার রাজনীতির বিরোধিতা করছি। দেশভাগের শিকার বাঙালিদের রাজনীতির ফুটবল বানিয়ে অসমে হিন্দু-মুসলমান দুই বাঙালির মধ্যে খাই আরও বাড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তা বাড়লে, দাঙ্গার রাজনীতি ছড়ালে আমাদের সকলের ক্ষতি। একই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সকলের নিঃশর্তে নাগরিকত্বের দাবির পক্ষে দাঁড়াতে হবে। শুধু সি এ এ- এন আর সি- এন পি আর বিরোধিতা নয়, গোড়ায় গলদ আটকাতে ২০০৩-সালের মূল সংশোধনী বাতিলের দাবি জানানোর পক্ষে জনমত গঠন জরুরি।
পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা তাঁদের পরিবারগুলিতে অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জেনেছেন। সেই স্মৃতি ঝালিয়ে তাঁদের কাছে বলা দরকার, সঙ্ঘী ইতিহাসের বাইরে আজ এটা প্রমাণিত দেশভাগের দায় জিন্না- নেহরুর শুধু নয়, কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে হিন্দু প্রাধান্যবাদীদেরও। সরকারি উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক জনবিনিময়ের পথে না হাঁটায় গান্ধী-নেহরুর ধারণালালিত ভারতীয় গণতন্ত্র অনেক ব্যর্থতা, ত্রুটি নিয়েও ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতির যুগে এই ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদ আরও অচল।
বিজেপি সরকারের নয়া আইন শুধু ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হবে না। উপমহাদেশের সব রাষ্ট্রে দাঙ্গাবাজদের হাতে ফের ব্যাপক হানাহানি ও সংখ্যালঘু বিতাড়নের অস্ত্র তুলে দেবে। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে তো বটেই, আশেপাশের দেশগুলোতেও ধর্মীয় শুধু নয়, জাতিগত-ভাষিক ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য দুর্বিপাক ডেকে আনবে। এই সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের প্রধান শিকার সব দেশেই নানা ধর্ম-জাতি-ভাষার গরিব মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। এদেশে এর সুযোগ নেবে এদেশে হিন্দু ঐক্যের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদীরা যারা সনাতন ধর্মের নামে নিম্নবর্ণীয় সংখ্যাগুরুর উপর উচ্চবর্ণীয় প্রভুত্বকে আরও জোরদার করতে চায়।
শুধু তাই নয়, আদানি-আম্বানিদের মতো শাসক- ঘনিষ্ঠ ধনকুবেরবৃন্দ ও অন্যান্য পরজীবী লুটেরাদের সঙ্গে সরকারের আঁতাতের বিরুদ্ধে আমজনতার প্রতিবাদগুলির বর্শামুখ ঘুরিয়ে দিতে চায় সঙ্ঘ পরিবার। ফ্যাসিস্ত-নাজি হিটলার-মুসোলিনির মতোই নাগরিক সমাজের অংশীদার প্রতিবাদী ছাত্র-যুবকদের সঙ্গে প্রবীণ নাগরিকদেরও পিটিয়ে, জেলে পাঠিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাইছে মোদী-শাহ-আদিত্যনাথদের সরকার। অন্যদিকে হিন্দুত্বের চোলাই খাইয়ে নোটবন্দি-জি এস টি-ব্যাঙ্ক লুট ইত্যাদির চক্করে খেটে-খাওয়া গরিব ও মধ্যবিত্তের রুটি-রুজি-সঞ্চয় হারানোর যন্ত্রণাকে অনেকটা ভুলিয়ে রাখছে। এই বাংলাতেও। সেই গণনেশামুক্তির পথে বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামের ইতিহাস হোক আমাদের অন্যতম পাথেয়।
সেই ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দিতে, সেই পরিচয়হীণতা থেকে মুক্তির অসাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের স্মৃতিকে উস্কে দিতে এই বইটি আজকের দিনে হাতিয়ারের কাজ করবে।
উদ্বাস্তু কলোনির কথা : একটি স্মৃতিকথা সংকলন
সম্পাদনা : কল্লোল
প্রকাশক – গুরুচণ্ডা৯
মূল্য – ১১০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান :
অনলাইনে — কলেজস্ট্রীট ডট নেট
বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।উজানতলির উপকথা | আগুনপাখি | উদ্বাস্তু কলোনির কথা : একটি স্মৃতিকথা সংকলন | এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা | সিজনস অফ বিট্রেয়াল | সূচীপত্র
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
দ | ১৫ আগস্ট ২০২১ ১৬:২৮496795
লেখটায় একটা ছোট্ট ভুল আছে।
"বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গবেষক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ‘মারজিনাল মেন’ (বাংলায় ‘প্রান্তিক মানুষ’ নামে অনূদিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত)"
বাংলা বইটা ইংরাজী 'মার্জিনাল মেন'এর অ্যাব্রিজড ভার্সান। আমার কাছে দুটোই আছে। বাংলাটা সাইজে ইংরিজির প্রায় অর্ধেক। কাজেই বাংলায় পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হয় নি। বরং সক্ষেপিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে।
তা বাদে খুবই বিস্তারিত আলোচনা। ধন্যবাদ।
-
দ | ১৫ আগস্ট ২০২১ ১৬:৩০496796
*লেখাটায়
** সংক্ষেপিত
 তমোজিৎ সিংহ রায় | 103.25.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২১ ১৬:৫৩496797
তমোজিৎ সিংহ রায় | 103.25.***.*** | ১৫ আগস্ট ২০২১ ১৬:৫৩496797মাননীয় প্রফুল্ল চক্রবর্তী র লেখা বাংলা বইটির প্রকাশক কে ? বা কোথায় পেতে পারি জানালে উপকৃত হই ।
-
দ | ১৫ আগস্ট ২০২১ ১৭:০৪496798
বাংলা 'প্রান্তিক মানব' এর একটা এডিশান দীপ প্রকাশন বের করেছে । এছাড়া নেটে পিডিএফও পাবেন।
 Tsray | 103.25.***.*** | ২২ আগস্ট ২০২১ ১১:৩১496999
Tsray | 103.25.***.*** | ২২ আগস্ট ২০২১ ১১:৩১496999- গতকাল ই বইটা হাতে পেয়ে বসে পড়েছি ..এখনো পর্যন্ত যেটুকু পড়া সম্ভব হোলো....আমার মতে একটা অসাধারণ কাজ। এতো ঐতিহাসিক দলিল ।উত্তেজনায়বাসুদেব দাকে(ঘটক ) ফোন করেও বসলাম গতকাল রাতে । কথা হোলো।যেহেতু আপনারা সংকলন বলেছেন...সম্ভব হলে আরও কলোনি র ইতিহাস বা তাদের কারিগরদের অভিজ্ঞতা যুক্ত করতে পারলে সমৃদ্ধ হয় ।বিশেষ করে....একটু পরবর্তী সময়ের ও ভিন্ন অভিজ্ঞতার //ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই প্রচেষ্টা কে। বিশেষ করে এই সময়এই কাজ হাতে নেওয়ার জন্য ।আরও একবার ধন্যবাদ
-
Indra Mukherjee | ২৯ আগস্ট ২০২১ ১৭:৪৫497358
- অনেক ধন্যবাদ উদ্যোগকে।copy collect করতে চাই । ইন্দ্রনাথ মুখার্জি ।DL - ২৩১/৬Sector2 Salt LakeKolkata 91
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












