- বুলবুলভাজা স্মৃতিচারণ

-
গান বৃক্ষের কথা
ইমানুল হক
স্মৃতিচারণ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ১৮২৪ বার পঠিত | রেটিং ৫ (২ জন) 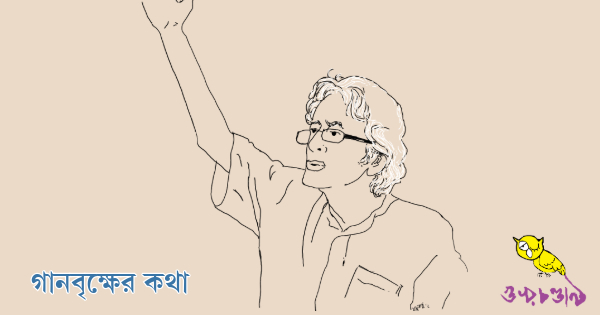
ইকবাল লিখেছিলেন, সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা।
এর জবাবে শাহির লুধিয়ানভি লিখলেন,
আরব হামারা চীন হামারা
তাঁর কথায় জাতীয়তাবাদের স্বর ছেড়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা এল।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় গীতিকার ছিলেন শাহির লুধিয়ানভি।
বাংলাদেশের বন্ধু অধ্যাপক শহীদ ইকবালকে নিয়ে প্র তুল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাই। 'চিহ্ন' পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার নেন ইকবাল। তখনই তিনি বলেন, শাহির লুধিয়ানভির কথা। তাঁর লেখা গান 'ম্যানিফেস্টো' পত্রিকার সম্পাদক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ করার কথা। এবং নিজের শাহির লুধিয়ানভির গান বাংলায় গাওয়ার কথা।
আমি বাংলায় গান গাই... এই গানকে অনেকে জাতীয়তাবাদ প্র চারের কাজে লাগাতে চান। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নিজের বক্তব্য এর বিপরীত।
যে যাই বলুন, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের শেষ জীবন পর্যন্ত অবস্থান ছিল বামপন্থী।
তাঁর গান, কবিতা, লেখা, জীবনযাপন--সবটাই বামপন্থী মনোভাবের।
তৃণমূল সরকারের অনুষ্ঠানে যেমন গেছেন বহু বামপন্থী সংগঠনের অনুষ্ঠানেও গেছেন।
২০০৬ এর সিঙ্গুর আন্দোলনে তাঁর যোগের পর সিপিএমের নেতৃত্বাধীন সরকারের অনুষ্ঠানে তিনি সেভাবে ডাক পাননি।
আমার ঠিক করে দেওয়া এক অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ক্ষ মা চেয়ে বাতিল করা হয়েছে ২০০৭ এই।
তবে দুর্গাপুর রানিগঞ্জ কৃষ্ণনগর রাণাঘাটের বামপন্থী মানুষ, কট্টর সিপিএম সমর্থকরাও ২০১২ এর পর তাঁকে ডেকেছেন।
দলগতভাবে ডাক পাননি।
গোর্কি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরও লেনিনের প্রবল বিরোধিতা করেন।
কিন্তু লেনিন একটুও খারাপ ব্যবহার করেননি। একাধিক চিঠি লিখেছেন। কথা বলেছেন।
একজন শিল্পী বা লেখক বা স্রষ্টার সঙ্গে আচরণে কমিউনিস্ট মনোভাবের বদলে মধ্যবিত্ত ভাবধারা অনেক সময় কাজ করে।
ফলে তাঁর সৃষ্টির চেয়ে তিনি কাদের সঙ্গে মিশলেন সেটাই বেশি বিবেচ্য হয়ে যায়।
ফলে সমস্যা হয়।
সমরেশ বসুকে নিয়ে এই ভুল হয়েছে।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে নিয়েও হচ্ছে।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান বিপ্লবী চিন্তা ও মতাদর্শের গান।
কোনও বিশেষ দলের জন্য তিনি গান লেখেননি।
কোনও পুরস্কার বা পয়সার জন্যও নয়।
তাঁর সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে, তাঁরা জানেন, তিনি কোন বিশেষ দলের লোক নন।
চিন্তা চেতনায় বামপন্থী ছিলেন।
লেখায় গানেও।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কোনও শিল্পী সুলভ ভ্যানিটি ছিল না। হাসপাতালে বসেও গান গেয়েছেন, চলন্ত গাড়িতে যেতে যেতে, হোটেলের ঘরে কেউ দেখা করতে এলেও গান শুনিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে গেছেন । বসে আছেন সাজঘরে। গান শুনিয়ে দিলেন অভ্যাগতকে।
ছোটদের অসম্ভব ভালো বাসতেন।
আমি একাধিকবার দেখেছি।
ছোটদের নিজে থেকেই গান শোনাতে শুরু করতেন।
দুর্গাপুরে আমার ভাইয়ের বাড়িতে দেখেছি।
নাতনির সঙ্গে গান গাইতে লাগলেন।
রাণাঘাটে ভাষা ও চেতনা সমিতি এবং উপেন্দ্র নার্সারির বসন্ত উৎসবে গেছেন। সাজঘরে বসে আছেন।
কট্টর সিপিএম দিব্যেন্দু বিশ্বাসের নাতি এলেন।
সে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান প্রবল ভক্ত।
শুনেই গান শোনাতে শুরু করলেন।
চীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, মাও সেতুং, সোভিয়েত বিপ্লব নিয়ে গভীর পড়াশোনা ছিল।
বহু বামপন্থী পার্টি নেতার চেয়ে ভালো বুঝতেন মার্কসবাদ।
নকশাল আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে সিপিএমের দূরত্ব।
কিন্তু সিপিএমের সমর্থকরা তাঁর গান শুনেছেন ভালোবেসে, এটাও সত্য।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সিপিএম পছন্দ করত না, কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই উপহার দেওয়া বন্ধ হয়নি।
আমি তো পুরস্কার হিসেবে গোটা পাঁচেক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা পেয়েছিলাম।
২০০৬ এর পর stressed নেতাদের একটা অংশের ভাবনায় বদল আসে। তা নিচের তলাতেও চাড়ায়।
বহু বামপন্থী মানুষের মধ্যেও উথালপাতাল হয়। সিঙ্গুর ঘিরে।
এর মানে সবাই তৃণমূল হয়ে গেলেন না।
কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা দলের নয় জাতির মানুষের সম্পদ।
বিশেষ গোষ্ঠীর নন তাঁরা।
সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সবসময় মেলে না জানি।
তবু মনে রাখা দরকার, গোর্কি সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে জ্যোতি বসুর নরম মনোভাব, এবং সমরেশ বসু সম্পর্কে কাকাবাবুর মনোভাব।
সমরেশ বসুর প্রবল শ্রদ্ধা ছিল কাকাবাবু মুজফফর আহমেদের প্রতি।
কাকাবাবুও খোঁজ রাখতেন সমরেশ বসুর। দুজনের ঘনিষ্ঠদের মুখে শুনেছি সে-সব কথা।
শিল্পীকে রক্ষা করতে হয়।
দরদী মন এবং মানসিকতা নিয়ে। গাল মন্দ দিয়ে
শত্রু শিবিরে ঠেলে দেওয়ায় ইগো সন্তুষ্ট হতে পারে, মত ও পথের ক্ষতি হয়ে যায়।
যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি বাংলার গান গাই কি জাতীয়তাবাদী?
প্র তুল মুখোপাধ্যায় কী বলেছেন, পড়ি:
"কেউ একে বলেছেন অতি দীর্ঘ, কেউ বলেছেন দেশাত্মবোধক গান, কেউ বলেছেন কবি নজরুল ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত। আসলে দেশাত্মবোধক গানের ভিতরে সাধারণত গর্ব থাকে, অহংকার থাকে, ‘আমরাই সেরা’ বলার প্রবণতা থাকে। আমার এই গানটি সেই চেতনায় লেখা ছিল না। তখন আমিও ভাবিনি এমন আহামরি দারুণ কিছু একটা হয়েছে।"
প্রতুল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমি বাংলায় গান গাই’ এর কথার অর্থ ব্যাখা করে বলেন,
“গানটা ন্যাশনাল, এক সাথে ইন্টারন্যাশনালও। দুটোরই সম্মিলন ঘটেছে। আমি ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...’ ধরণের গান লিখতে চাইনি। আমি গানে কখনো বলিনি বাংলা শ্রেষ্ঠ। বরং বলেছি,
'... বাংলায় বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়'। এর মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা ছিল।
‘... আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর ...’ লিখে ন্যাশনালের সাথে ইন্টারন্যাশনালের যোগসূত্র ঘটানোর চেষ্টা করেছি। এতে একটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল।
যখন বলেছি ‘আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই’, তখন এই বাক্যবন্ধে উল্লিখিত ‘বাংলা’ বলতে বোঝাতে চেয়েছি বিশ্বে যত রকমের বাংলাভাষী আছেন তাদের। সে তিনি আমেরিকা, জার্মানি, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ—যেখানেই থাকুন না কেন। এই ‘বাংলা’ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা পূর্ববঙ্গ, এমন বর্গীকরণ করা যায় না। কারণ, গানের ক্ষেত্রে আসলে এই বর্গীকরণটাই অর্থহীন। শহর কলকাতায় এমন গুজরাটি পরিবার আমি জানি, যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, বাংলা ছোটো পত্রিকা বের করেন, সাহিত্যচর্চা করেন, গান শোনেন—আমি তাঁদেরও ধরতে চেয়েছি। গানের মধ্যে দিয়ে ‘বাংলা’ বলতে যা আমি বোঝাতে চেয়েছি, সেই বাংলার মধ্যে কিন্তু অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। আপনি হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর কিংবা বীরভূম বা মুর্শিদাবাদ যান, কিংবা সিলেট, চট্টগ্রাম বা ময়মনসিংহ ঘুরে আসুন—দেখতে পাবেন প্রতিটি অঞ্চলের বাংলা ডিকশন আলাদা।
আবার এক স্থানের বাংলাভাষা যুগের পরে যুগ ধরে বদলেছে, ভূগোল বদলেছে, এগুলো থাকবেই। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, যখন বলা হবে, আমি বাংলার গান গাই—তখন সেটা বিশেষ কোনও স্থান বা কালকে নির্দেশ করছে। বাংলাভাষার এই যে ইডিয়োলেক্ট, অর্থাৎ, প্রত্যেকেই বাঙালি, কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন, তা গানে যেমন খুঁজে পাই, তেমন ফিল্মেও দেখতে পাই। গানের ক্ষেত্রে এই বাংলা আসলে এক বৃক্ষের মতো—যার নানা প্রকার, তাদের পাতা, অবয়ব ভিন্ন, শাখাপ্রশাখাও বিস্তৃত, কিন্তু আত্মায় তারা অভিন্ন। বাংলার মধ্যে বিভিন্নতা যেমন আছে, তেমন আছে ঐক্যও। এই বৈচিত্র্য মুছে ফেলা উচিত নয়। আবার হাতধরাধরি করে চলাটাও জরুরি।"
গাবদা বুদ্ধি নিয়ে চায়ের দোকানের আড্ডায় বাজিমাত করার চেষ্টা চলতে পারে, শিল্প ও শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন হয় না।সূত্রনির্দেশ:
- Paromita Sen (telegraphindia.com)
- মিন্টু চৌধুরী (bdnews24.com)
তথ্য সংগ্রহ, ভাষান্তর এবং সম্পাদনা::
- মীর শাহনাজ।
- সংগ্রহ: রৌণক বুবাই।
ছবি: যদুবাবু
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনঢাকের দিনে ঢুকুঢুকু - ঋতেন মিত্রআরও পড়ুনঋতেন্দ্রনাথ - যদুবাবুআরও পড়ুনঋতেন ও তার বন্ধুরা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 aranya | 2601:84:4600:5410:2586:f18f:91b2:***:*** | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ০১:২৬541149
aranya | 2601:84:4600:5410:2586:f18f:91b2:***:*** | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ০১:২৬541149- ভাল লাগল , এই স্মৃতিচারণ
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ০২:২১541153
- ভালো লাগল
-
Eman Bhasha | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১০:৩৭541160
- শিল্পী সুরস্রষ্টা বা লেখক কিংবা কবি অথবা যে কোনও মানুষ, তাঁর একটা নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামত বা মতাদর্শ থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক।শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সিপিএম মহলে নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত দক্ষণপন্থী বলে গণ্য হতে।বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করেন।শক্তি চলে গেছেন।সুনীল নয়ের দশকের শেষদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।সিপিএমের লেখক শিল্পী সমিতির সভায় সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। 'আজকাল' কাগজে সে খবর প্রকাশিত পর্যন্ত হয়।অভিজ্ঞতা কী বলে?সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বামপন্থী বলে গণ্য হলে একুশ শতকে।অনেকটাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব।একইভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ বাড়ান।এগুলো মানুন বা না মানুন, খুব প্রভাব ফেলে।লেনিনের কাছে শেখা জরুরি।ম্যাক্সিম গোর্কির অনেক বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।
-
Touhid Hossain | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৪:১১541167
- অপূর্ব! প্রাণ ভরে পড়লাম। শিল্পীকে শ্রদ্ধা
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












