- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
পাগল মনের দশ খেয়াল: শ্রী কোটা শিবরাম করন্থের বং কনেকশন
দিলীপ ঘোষ
পড়াবই | মনে রবে | ১৬ নভেম্বর ২০২৫ | ৬৭৬ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 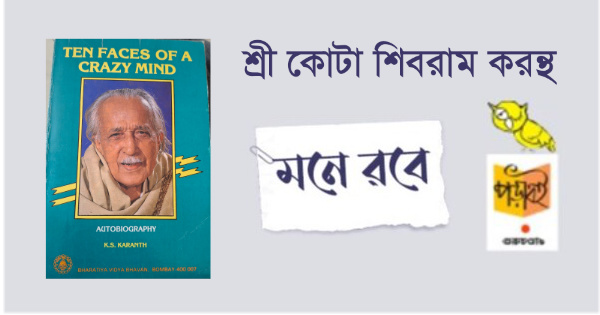
২০১৪ সালের ২৫শে জানুয়ারির কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ কাগজে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ লিখেছিলেন এক বিতর্কিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, “Genius and Charisma”। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন- “Karanth was arguably as great a genius as Tagore.”
গুহ নিজেই স্বীকার করেছিলেন, কান্নাড়া ভাষায় তিনি তেমন পারদর্শী নন। তবু কেন এমন তুলনা করলেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, “করন্থের প্রতিভার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে তাঁর সম্পর্কে যে কথোপকথনগুলি কানে এসেছে। হেগগোডুর মতো কন্নড় সংস্কৃতির প্রাণবন্ত কেন্দ্রে গিয়ে জেনেছিলাম, সেখানকার অভিনেতা ও পরিচালকরা করন্থের দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত (যথার্থভাবেই, স্থানীয় অডিটোরিয়ামটিও তাঁর নামে)। বেঙ্গালুরুতে ঔপন্যাসিক ইউ. আর. আনন্দমূর্তি ও নাট্যকার গিরিশ কারনাড জানিয়েছিলেন, করন্থ কন্নড় সাহিত্যকে যেন নতুন প্রাণ দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লিতে বিশিষ্ট সমালোচক এইচ. ওয়াই. শারদা প্রসাদ বলেছিলেন, কীভাবে করন্থ পশ্চিম উপকূলের লোকনাট্য যক্ষগানা–র প্রাচীন ধারাটিকে পুনর্জীবিত ও আধুনিক করে তুলেছিলেন। সমাজকর্মীরা স্মরণ করেছিলেন পশ্চিমঘাট রক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা; শিক্ষাবিদরা উল্লেখ করেছিলেন জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদান। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, কবি ও গল্পকার- সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন করন্থের গভীর প্রভাব।”
স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করন্থের তুলনাটা আমার প্রথমে ভালো লাগেনি। কোথায় শান্তিনিকেতনের বিশ্বকবি, আর কোথায় কর্ণাটকের এক সাহিত্যিক ও শিল্পসংস্কৃতির কর্মী! কিন্তু অদ্ভুতভাবে, গুহের এই লেখাটিই আমার মধ্যে করন্থকে নিয়ে এক প্রবল কৌতূহলের জন্ম দিয়েছিল।
সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়ে তক্ষুনি, বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে করন্থের কোনো বই হাতে পাই নি । তাই আগ্রহটা অনেকদিন ধরে এক অসমাপ্ত প্রশ্নের মতো থেকেই গেল।
কয়েক বছর পর, ২০১৬-র মাঝামাঝি, দক্ষিণ কর্ণাটকে সফরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ভর্তি হলাম এক বড় হাসপাতালে। আমার পাশের বেডে ছিলেন প্রায় সমবয়সী এক ভদ্রলোক- পরিচয়ের পর জানা গেল, তাঁর পদবীও করন্থ! বাড়ি কুন্দপুর- যে শহর করন্থের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, “শিবরাম করন্থের আত্মীয় নাকি?”
লাজুক হেসে তিনি উত্তর দিলেন, “ডিস্ট্যান্টলি।”
আমার আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, করন্থের অনেক বই তাঁর কাছে আছে, কিন্তু সবক’টাই মূল কান্নাড়া ভাষায়- অনুবাদ নয়। তবে তিনি আমাকে কর্ণাটকের উপকূলীয় লোকশিল্প যক্ষগানা–র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। বললেন, “করন্থ শুধু যক্ষগানাকে পুনরুজ্জীবিত করেননি, ভারত সরকারকে রাজি করিয়ে একে শাস্ত্রীয় শিল্প হিসেবে স্বীকৃতিও এনে দিয়েছিলেন।”
সেই রাতে হাসপাতালের বেডে শুয়ে তাঁর মোবাইলে ধরে রাখা যক্ষগানার নানা ভিডিও দেখতে দেখতে আমি এক নতুন জগতে প্রবেশ করলাম। (যাঁরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কন্নড় চলচ্চিত্র ‘কান্তারা’ দেখেছেন, তাঁদের মনে থাকতে পারে ‘বরাহরূপম’ গানের দৃশ্যটি - ওটি যক্ষগানার শৈলীতেই পরিবেশিত হয়েছিল।)
আরো কিছুদিন পরে হাতে এল করন্থের আত্মজীবনী “Ten Faces of a Crazy Mind”। এই নিবন্ধের নামকরণও ওই বইটি থেকেই।
বইটি পড়ে মনে হলো, রামচন্দ্র গুহের তুলনাটির পেছনে যুক্তি ছিল। করন্থের প্রতিভা ছিল বহুস্তরীয় ও বিস্তৃত- সাহিত্য, নাটক, শিল্প, বিজ্ঞান, পরিবেশ, শিক্ষা- সব ক্ষেত্রেই তাঁর সহজ বিচরণ- রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় প্রতিভার কথা মাথায় আসে না ।
কিন্তু গুহ যেটি বলেননি, আত্মজীবনীর সেই অংশগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ; বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং তাঁর সময়ের বাঙালির চিন্তা-চেতনার প্রতি শিবরাম করন্থের গভীর অনুরাগ। তাঁর আত্মজীবনীতে বাংলার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের যে সব উল্লেখ ছড়িয়ে আছে, এই লেখাটি সেই বিষয়েই।
মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে কোটা শিবরাম করন্থের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা যাক।
ড. কোটা শিবরাম করন্থ ১৯০২ সালে কর্ণাটকের দক্ষিণ কানাড়া জেলার কুন্দপুরের কাছে কোটা-য় জন্মেছিলেন। সেখানেই পড়াশোনা শুরু, সেখানেই শেষ করেন উচ্চমাধ্যমিক। কিন্তু দেশ তখন উত্তাল, অসহযোগ আন্দোলন চলছে। তরুণ করন্থ কলেজ ছেড়ে সরাসরি যোগ দেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে। ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী ছিলেন।
কিন্তু তাঁর পথ এখানেই থেমে থাকেনি। রাজনীতি ছেড়ে তিনি ডুব দিয়েছিলেন সৃজনশীলতার জগতে। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, চিত্রকলা, নাট্যশিল্প, ফটোগ্রাফি- যে ক্ষেত্রেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই রেখে গেছেন নিজের স্বাক্ষর। কর্ণাটকের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যনাট্য যক্ষগানা–র ওপর তিনি ছিলেন অন্যতম সেরা বিশেষজ্ঞ। শুধু গবেষণা নয়, করন্থ এই লোকশিল্পটিকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছিলেন আধুনিক মঞ্চে।
তিনি ছিলেন এক অবিশ্রান্ত লেখক। সারা জীবনে ৩৯০টিরও বেশি বই লিখেছেন - এর মধ্যে ৪৫টি উপন্যাস, অসংখ্য নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও গবেষণাগ্রন্থ। শিশুদের জন্য তিন খণ্ডের এক বিশ্বকোষ, জনপ্রিয় বিজ্ঞানের ওপর চার খণ্ডের আরেক বিশ্বকোষ, আর বিশ্বকলা নিয়ে তৃতীয় এক বিশ্বকোষ- তাঁর এই কাজগুলো আজও কন্নড় সাহিত্য জগতের গর্ব। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন কন্নড় সাময়িকী বসন্ত ও বিচার বাণী।
কন্নড় সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে করন্থ ছিলেন এক আলোকবর্তিকা। তিনি কন্নড় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, সংগীত নাটক আকাদেমি ও সাহিত্য আকাদেমির ফেলো- সব ক্ষেত্রেই তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত।
১৯৬৮ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়, যদিও ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে তিনি তা ফেরত দেন। মাইসোর, কর্ণাটক, মাঙ্গালোর, মীরাট ও জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস মূকাজ্জিয় কানাসুগালু তাঁকে এনে দেয় ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার- জ্ঞানপীঠ। কন্নড় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৯) এবং পরে সাহিত্য অকাদেমির ফেলোশিপ (১৯৮৫)- যা ভারতের সাহিত্যজগতে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিগুলির একটি।
শিল্প ও অভিনয়ের জগতে অবদান রাখার জন্য তাঁকে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়, এবং পরে সেই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্মান সঙ্গীত নাটক অকাদেমি ফেলোশিপ (১৯৭৩)-এ ভূষিত করা হয়।
করন্থ আরও পেয়েছিলেন কর্ণাটক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এবং রাজ্য সরকারের রাজ্যোৎসব প্রশস্তি (১৯৮৬)। ১৯৮৯ সালে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে প্রদান করা হয় পম্পা পুরস্কার- কর্ণাটকের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য সম্মান।
তাঁর সৃজনধর্মী কাজের আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য স্বীকৃতিও কম ছিল না। তিনি লাভ করেন তুলসী সম্মান (১৯৯০) এবং দাদাভাই নওরোজি পুরস্কার (১৯৯০)।
শিবরাম করন্থ ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এক “বহুমুখী প্রতিভা”- যিনি কখনও সাহিত্যিক, কখনও পরিবেশরক্ষক, কখনও বিজ্ঞানবেত্তা, আবার কখনও লোকশিল্পের নবজাগরণকার। তাঁর জীবন জ্ঞান, কৌতূহল ও সৃজনশীলতার এক আশ্চর্য মিলন।
বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে করন্থের পরিচয় শুরু হয়েছিল স্কুলবেলাতেই।
আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন,
“বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি পড়েছিলাম স্ট্যানফোর্ড ও মার্টন-এর গল্প, আর সঙ্গে ছিল নীতিচিন্তামণি-র গল্পগুলিও। আমাদের এলাকায় শিবরামাইয়া মহাশয় যে গ্রন্থাগারটি শুরু করেছিলেন, সেটিতেই প্রথম জানতে পারলাম যে কন্নড় ভাষাতেও বই প্রকাশিত হয়! সেখানেই আমরা পড়েছিলাম নানা গল্প এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অনুবাদ।
সেই অনুবাদগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃতঘেঁষা- যেমনটা তখনকার বাংলার ভাষাতেও দেখা যেত। তবে একটি স্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়েছিল ভেঙ্কটাচার্যের ‘রজনী’-তে ব্যবহৃত কান্নড়া-র সঙ্গে তাঁর ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘মৃণালিনী’-র কন্নড়-র। রজনী ছিল ইংরেজি উপন্যাস Last Days of Pompeii- অনুপ্রাণীত, যেখানে মূল ইংরেজি শব্দভাণ্ডারের সৌন্দর্য পুনর্নির্মাণের সুযোগ প্রায় ছিল না। কিন্তু বিষবৃক্ষ ও মৃণালিনী-র অনুবাদে বাংলার সুরেলা শব্দচয়ন ও ভাবরস কন্নড় ভাষায় অনেক সহজে মিশে গিয়েছিল।”
স্কুলের পালা শেষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে করন্থের পরিচয় হয় পুরো রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে, কলেজের সিলেবাস অগ্রাহ্য করে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই তাঁকে বাঁধা গতের পড়া ছেড়ে নিজের পথে হাঁটতে উৎসাহ দেন। তাঁর নিজের কথায়,
“কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল, আর আমি তেমন কোনো ক্রিকেটার ছিলাম না। তাই ছাত্র-শিক্ষক- উভয়ের কাছ থেকেই আমি একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি শ্রেণিকক্ষের পাঠও আমার মনে কোনো প্রভাব ফেলত না। তবে আমি গ্রন্থাগারের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক রাম আইয়ার আমাদের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছিলেন- যে বইগুলো অবশ্যই পড়তে হবে। সেই তালিকা থেকে আমি বেছে নিয়েছিলাম একটি বই- রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর The Light that Failed। বইটি পড়ে সেই পুরো তালিকার প্রতিই আমার প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মায়, যদিও যুক্তি বলছিল- আমাদের বিশাল গ্রন্থাগারের সব বই কিপলিং-এর মতো খারাপ হতে পারে না। তবু আমি নিজের জন্য এক অযৌক্তিক ও সংকীর্ণ নিয়ম বেঁধে ফেললাম- আমি শুধু ভারত সম্পর্কিত বই, বা ভারতীয় লেখকদের বইই পড়ব। এইভাবেই আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সব রচনাই পড়ে ফেললাম। ফলে কলেজের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আমার অনাসক্তি আরও গভীর হয়ে উঠল।”
গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের সম্মিলিত প্রভাবে কলেজের পড়াশুনা ছেড়েছিলেন করন্থ, আত্মজীবনীতে লিখেছেন,
“১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার সহপাঠী পদ্মরাজ আরিগা সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল। গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা তখন দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যেতে শুরু করেছে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুসংবাদ গভীর বেদনা সৃষ্টি করেছিল। আমার এক বন্ধু তিলককে স্মরণ করে একটি শোকগীতি লিখেছিল, যার একদিনেই এক হাজারেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল। কয়েক দিন পর, খিলাফত আন্দোলনের প্রচারের জন্য গান্ধিজি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মাঙ্গালুরে এসেছিলেন। ছাত্রসমাজের মন তখন স্বদেশি ও স্বরাজের ভাবনায় উদ্বেল।
আমার কলেজজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইগুলির প্রভাবেই আমার মনে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল। সেই সময়ে সেখানে বসবাসরত রেভারেন্ড সি. এফ. অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চালাচালি হয়। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বিষয়টি বাবার সঙ্গে আলোচনা করলাম। কিন্তু তিনি তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করলেন- কারণ তাঁর ধারণা ছিল, বাঙালি ব্রাহ্মণরা মাছ খান। অ্যান্ড্রুজ আমাকে লিখে জানালেন যে সেখানে মৈথিলি ও গুজরাটি ব্রাহ্মণরাও রয়েছেন, যারা মাছ খান না। কিন্তু এই তথ্যেও বাবার ভুল ধারণা দূর করা সম্ভব হলো না।”
জীবনের যে পর্বে তিনি পুরো সময়ের রাজনৈতিক কর্মী, সেই সময়ে গান্ধীজি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি আরেক বাঙালিও প্রভাব ফেলছেন খানিকটা। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
“যৌবনে আমি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক মানুষ ছিলাম- মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমি চার-পাঁচ বছর কংগ্রেসের সদস্য ছিলাম। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কুন্দাপুরায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতাম। বলা ভুল হবে না যে, রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমেই আমি আমার কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলাম। আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল- ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তি লাভ। আমাদের নেতারা সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত তীর সরবরাহ করতেন। গান্ধিজির ইয়ং ইন্ডিয়া ছিল আমার কাছে যেন এক পূর্ণ তূণীর। ঐ পত্রিকার নিবন্ধগুলির বাইরে আমার আর কোনো যুক্তিবোধের প্রয়োজন হতো না, এমনকি মনে হতো তার প্রয়োজনও নেই। সেই সময়ে আমার পাঠ্যজগৎ মূলত কয়েকজন নেতার লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে আমি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকাটিও দেখতাম।”
ক্রমে ক্রমে রাজনীতির ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করছিল তাঁর। রাজনীতি নিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকা এই মোহভঙ্গের বিবরণ রসিয়ে লিখেছেন করন্থ। এই পর্বেই গান্ধীজির দেখানো পথে খাদি কাপড় বয়নে নেমে পড়েছিলেন তিনি। সহায়তা নিয়েছিলেন আরেক বাঙালির, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
“আমাদের জন্য সেই সময়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল মাঙ্গালুরে অনুষ্ঠিত সর্বকর্ণাটক জাতীয়তাবাদী সম্মেলন। শেঢি হিলের জৈন কম্পাউন্ডে এর জন্য বিশাল এক প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ভারতকোকিলা সরোজিনী নাইডু সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। কর্ণাটকের দুই বাঘ- গঙ্গাধর রাও দেশপান্ডে ও কৌজলগি শ্রীনিবাস রাও- ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের গর্জন শুনে দেশপ্রেমের রক্ত আমার শরীরের প্রতিটি শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। সেই প্রথমবার অচ্ছুতরাও আমাদের সঙ্গে বসেছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে মাঙ্গালুরের ময়দানে প্রতিদিন জনসভা বসত।
সেই সময় এক স্থানীয় হিরো ছিলেন, চমৎকার বক্তা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় তিনি কোনো দ্বিধা না করে “sons of bitches” এবং “offspring of adulterous widows” মতো জোরালো সব বিশেষণ ব্যবহার করতেন।” একদিনের সভায় তিনি নাটকীয়ভাবে নিজের সুতির জামা ছিঁড়ে ফেলে খাদি পরেছিলেন। তিনি এক সভায় বলেছিলেন, “যদি তিনশো ত্রিশ কোটি ভারতবাসী একসঙ্গে নাক ঝাড়ে, তবে সেই সিকনির স্রোতে ব্রিটিশরা ভেসে চলে যাবে।”
১৯৫০ সালের দিকে আমি আচার্য কৃপালনীর এক বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি ‘চোর’, ‘ডাকাত’ ইত্যাদি শব্দ এতবার ব্যবহার করেছিলেন যে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। স্বরাজ আন্দোলনের দিনগুলির কথা মনে পড়ল- সেই সময় আমি রাজনৈতিক বক্তৃতার নিষ্ঠাবান শ্রোতা ছিলাম। আমাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল- “বর্তমান পরিস্থিতি”, আর একমাত্র যুক্তি ছিল ব্রিটিশদের নিন্দা করা। পেটব্যথা থেকে শুরু করে সমাজের যাবতীয় অসুখ-বিসুখের একমাত্র কারণ হিসেবে তখন শাসনস্বাধীনতার অভাবকেই ধরা হত।
এই সময়ে উত্তর ভারতের- সম্ভবত ইউনাইটেড প্রভিন্সেস বা বিহারের- একজনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল এই রকম- “এখানকার অধিকাংশ সূতোকাটা মহিলা মুসলমান। আমি মুসলমানদের কাটা সূতোয় তৈরি কাপড় পরতে চাই না। যদি হিন্দুদের কাটা সূতোয় তৈরি খাদি আপনার কাছে থাকে, তবে দয়া করে পাঠাবেন।” অথচ তখন গান্ধিজি শওকত আলিকে নিজের বড় ভাই বলে সম্বোধন করতেন। আমি ওই অসহায় চিঠিকারীকে সাহায্য করতে পারিনি, কারণ আমাদের খাদির সূতোতেও মুসলিম মহিলাদের কাটা সূতো যথেষ্ট পরিমাণে মিশে ছিল।
আমাদের নিজের হাতে তৈরি স্থানীয় খাদি ছিল বিবর্ণ ও ঢিলেঢালা, যেন জালের মতো। ওটা বিক্রি হবে কী করে! আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এল। কাঠের ব্লক তৈরি করালাম এবং কাপড়ে ছাপ দেওয়া শুরু করলাম। পি. সি. রায়ের “দেশি রঙ” বইটি এনে দেশজ রঙ ব্যবহারের পদ্ধতি শিখলাম। কিন্তু খাদির মতো এই স্বদেশি রঙও ছিল খুব ব্যয়বহুল। তাই রঙের খরচ কমানোর উপায় খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়ল। আমি সালফার ও অ্যানিলিন রঙ সংগ্রহ করে নিজে কাপড় রাঙানোর চেষ্টা করলাম। এই কাজটা আয়ত্ত করার পরই দেখা দিল নতুন সমস্যা- বুননের অসুবিধা। ফলস্বরূপ আমার দোকানে সূতো জমে পাহাড় হয়ে গেল।”
এরপর যখন কন্নড় পত্রিকা সম্পাদনা এবং প্রকাশনার কাজ শুরু করলেন তখনো তাঁর সামনে অন্যতম মডেল ছিল বাংলা ভাষার তৎকালীন পত্রিকাগুলি। তাঁর পত্রিকাতেও আলোচিত হচ্ছেন সেই সময়ের বড় বাঙালি ব্যক্তিত্বরা।
“কুন্দাপুরায় আমার এক বন্ধু ছিল- দেবন্না পাই। তিনি এক আইনজীবীর কেরানি ছিলেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি মনোরঞ্জন ও নব্যযুগ নামের মারাঠি পত্রিকা এবং ভারতবর্ষ নামের বাংলা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি আগাদির শেষাচল সিরিজ-এরও সদস্য ছিলেন। আমি তখন কদম্বরী সংগ্রহ নামে একটি কন্নড় পত্রিকা পেতাম। একদিন আমরা আমাদের কন্নড় পত্রিকাটির সঙ্গে মারাঠি ও বাংলা পত্রিকাগুলির তুলনা করে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। কন্নড় পত্রিকাগুলির মধ্যে আমরা কোনো অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক সৌন্দর্য খুঁজে পাইনি। ভালো গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং আকর্ষণীয় চিত্রসহ একটি মানসম্মত কন্নড় পত্রিকা প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা তখন আমাদের দু’জনকেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।
আমরা ১৯২৪ সালে বসন্ত নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম- আমার সম্পাদনায়। “সম্পাদক” শব্দটির প্রতি আমি তখন মুগ্ধ ছিলাম। সম্ভবত আমি ভেবেছিলাম, এই পদ আমাকে সম্মান ও খ্যাতি এনে দেবে। কিন্তু আমার কাছে কোনো অর্থ ছিল না। দেবন্না পাই পত্রিকাটি চালানোর জন্য এক বছরের খরচের টাকা ধার করেছিলেন। আমরা কোনো সময় নষ্ট না করে বসন্ত-এর একটি অফিস স্থাপন করলাম। আমাদের এক শিক্ষক বন্ধু বি. আনন্দ ভান্ডারিকে অনুরোধ করলাম অবৈতনিক ব্যবস্থাপক হতে। ভান্ডারির হাতে কেবলমাত্র স্কুল-সার্টিফিকেট থাকলেও আমরা তাঁর নাম ছাপালাম- “ভান্ডারকর বি.এ.”। আর আমি, সম্পাদক হিসেবে, নিজেকে “আমরা” বলতে শুরু করলাম- যেমনটি আজও সাংবাদিকতায় বহুল প্রচলিত এক রীতি। আমরা কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। তার মধ্যে একটি ছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-এর স্মরণে।”
তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দিশারিও ছিলেন এক বাঙালি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।
“মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে আমি আরেকটি কাজ হাতে নিয়েছিলাম। মা ছিলেন অপরিমেয় ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার অধিকারিণী। সেই সময়ে আমার নিজের মনোভাবও তাঁর মতোই ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসই ছিলেন আমার আদর্শ সাধক। ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে যতই বদলে যাক না কেন, রামকৃষ্ণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আজও অটুট। আমি তাঁর একটি ছয়শো পৃষ্ঠার জীবনী কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেছিলাম এবং বাড়ি গিয়ে সেই অনুবাদ মাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম।”
ভারতীয় শিল্পকলাতেও বিপুল আগ্রহ ছিল করন্থের, এবং সেই টানেই এসেছিলেন কলকাতা মিউজিয়ামে।
“কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে আমি সূর্যের একটি পাঁচ ফুট উঁচু মূর্তি দেখেছিলাম। সূর্য আমাদের দেবতাদের মধ্যে প্রথম। আর্য সংস্কৃতির এই সূর্যদেবই পরবর্তীকালে বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেছিলেন। মূলত উত্তর ভারতেই সূর্যের মূর্তিগুলি বেশি দেখা যায়। যেদিন আমি কলকাতায় সেই মূর্তিটি দেখেছিলাম, সেদিন অস্তগামী সূর্যের সোনালি রশ্মি পড়ছিল লাল বেলেপাথরে গড়া সেই মূর্তির গায়ে। মূর্তিটির এক দিক কমলা আভায় দীপ্যমান ছিল, আর অন্য পাশে তার ছায়া বেগুনি রঙে প্রতিফলিত হচ্ছিল। মনে হয়েছিল, যেন সন্ধ্যার সূর্য নিজেই স্পন্দিত মানবরূপ ধারণ করেছে।”
আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক দু ধরনের আকর্ষণেই ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন করন্থ। তাঁর বিচারে আধ্যাত্মিকতার ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের স্থান মথু’রা বৃন্দাবনের অনেক ওপরে, যদিও তিনি মোটেই কালী ভক্ত নন।
“ইলোরা ও কার্লের চৈত্যগীহে যে শান্তি অনুভব করা যায়, তা বর্ণনার অতীত- বুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এক প্রশান্তি। অন্য এক উপলক্ষে আমি মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে পৌঁছে প্রবল বিতৃষ্ণায় আক্রান্ত হলাম। রেলওয়ে স্টেশন থেকে নামার পর থেকেই এক পাণ্ডা আমাদের পিছু নিল- আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই সে সঙ্গে। আমরা দুধওয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনলাম, টোঙা ভাড়া করলাম- সব জায়গাতেই তার ভাগ ছিল। ঈশ্বরের নামে যেন একপ্রকার লুটপাট চলছিল। আমরা যমুনার ঘাটে গেলাম, সেখানেও সে পেছনে উপস্থিত- তুমি তাকে খেয়াল করো বা না করো। যখন আট মাইল দূরের বৃন্দাবনে গেলাম, তখন আরও কয়েকজন পাণ্ডা তার সঙ্গে যোগ দিল। মন্দিরটি বাহ্যিকভাবে সমৃদ্ধ মনে হলেও, তার মধ্যে শান্তির কোনো আভাস ছিল না। শেষে আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম যে তাদের এক পয়সাও দেওয়া হবে না- তবেই তারা আমাদের ছেড়ে গেল। তারপর আমরা কিছুক্ষণ কাটালাম মল্লিকা ফুলের বাগানে, যা ছিল পুরো বিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র তুলনামূলকভাবে নিস্তব্ধ জায়গা। জায়গাটা বিশেষ সুন্দর না হলেও অন্তত সেখানে কৃষ্ণকে নিয়ে কিছু মানসিক ভাবনার অবকাশ ছিল।
তবে এক জায়গায় সত্যিকারের তৃপ্তি পেয়েছিলাম- যেখানে সংস্কৃতির কোনো বিকৃতি ছিল না- সেটি কলকাতার দক্ষিণেশ্বর। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আমার গভীর অনুরাগের কারণে হুগলির তীরে অবস্থিত এই বিশাল মন্দিরটি আমাকে গভীর আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সেদিন মন্দিরে ভিড় ছিল না। আমি কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগেনি। সম্ভবত কালী তাঁদের মধ্যে একজন নন যাঁদের প্রতি আমার প্রেম বা ভক্তি জাগে। আমরা যেমন দিই, তেমনই পাই। পরে আমি গেলাম পঞ্চবটীতে- সেই স্থান, যেখানে পরমহংস তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা করেছিলেন। প্রকৃতির প্রতি আমার টান এবং পরমহংসের প্রতি শ্রদ্ধা- এই দুই মিলিত হয়ে আমাকে সেখানে এমন এক শান্তি দিয়েছিল, যা বৃন্দাবনে পাইনি।”
চিত্রশিল্পেও বাঙ্গালিদের সে এক উজ্জ্বল সময়। বাঙালি চিত্রশিল্পীদের কাজ দেখার আকর্ষণেই করন্থ হাজির হয়েছিলেন এই রাজ্যে।
“ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রহমান, চুগতাই, শারদা ও রণদা উকিলের আঁকার আমি গভীরভাবে প্রশংসা করি। তাঁদের অনেক আসল চিত্রই আমি দেখেছি। আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম এবং নন্দলাল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে তাঁর অনেক ছবি দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছবি আজও আমার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে- তার বিষয় ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ছবিটিতে শুধু সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের পা দেখা যায়, আর সেই পায়ের রেখার মধ্য দিয়েই শিল্পী যুদ্ধের ট্র্যাজেডি ও যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন।
আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবিগুলিও দেখেছিলাম। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, সেই ছবিগুলির অর্থ আদৌ কিছু আছে কি না। আমার উত্তর হলো- সব ছবির অর্থ আমি বুঝিনি, কিন্তু তা এই নয় যে সেগুলিতে কোনো তাৎপর্য নেই। এমন সমালোচনা অর্থহীন।
আমি রাফায়েল, রুবেন্স ও রেমব্রান্টের আঁকার প্রতিলিপি দেখেছি। আবার প্রাকৃতিকতাবাদী ধারাকে অস্বীকার করা শিল্পী- সেজান, গগ্যাঁ ও পিকাসোর শত শত কাজও আমি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি। আমি বহু চীনা ও জাপানি চিত্রকর্মের মুদ্রণও সংগ্রহ করেছি। তাদের শিল্পেও বাস্তবতার নিয়ম মানা হয় না। চিত্রশিল্পী যে পথকে নিজের কাছে সত্য ও অর্থবহ বলে মনে করেন, সেটিই তিনি অনুসরণ করেন- যে পথে তিনি তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন।”
ছবি দেখতেই হাজির হয়েছিলেন অবন ঠাকুরের বাড়িতেও।
“গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। অবনী বাবু তখন প্রবীণ। ভারতীয় শিল্পকলার নবজাগরণের কৃতিত্ব মূলত তাঁরই। তিনি নন্দলাল বসু, ভেঙ্কটাপ্পা এবং অসিতকুমার হালদারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে আমি আজন্তা গুহার চিত্রগুলির অনেক প্রতিলিপি দেখেছিলাম। এছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ- উভয়েরই আসল চিত্রকর্ম দেখেছিলাম। গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব এক অনন্য শৈলী ছিল; আমার মনে হয়, তিনি কিউবিজম ধারার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রবল আগ্রহে আমি জানতে চেয়েছিলাম, তিনি কি কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন। এক বালক আমাকে জানাল, পক্ষাঘাতজনিত আক্রমণের কারণে তিনি বাকশক্তি হারিয়েছেন। আমি কোনো বেদনাদায়ক স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ফিরতে চাইনি, তাই অন্তত একবার তাঁকে চোখে দেখার ইচ্ছাটিও ত্যাগ করেছিলাম।”
ভারতবর্ষ করন্থকে অবশ্য মনে রেখেছে এক বড় গদ্য লেখকের ভূমিকাতেই, যদিও তাঁর প্রতিভা সর্বার্থেই বহুমূখী। নিজের গদ্য লেখা নিয়ে তাঁর বক্তব্যও এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক,
“শেষ পর্যন্ত, আমার লেখার মধ্যে গদ্যই সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। যখন আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি, তখনই বিয়োগিনী নামে একটি উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলাম। ভূমিকা ও প্রথম দুই অধ্যায় লিখে শেষ করেছিলাম। এটি ছিল শ্রীমতী তিরুমলম্বার বিরাগিনী উপন্যাসের প্রতি আমার জবাব। পরবর্তীকালে যখন আমি বসন্ত পত্রিকা পরিচালনা করছিলাম, তখন কয়েকটি ভয়াবহ গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছিলাম। সেই গল্পগুলির সব চরিত্রেরই বাঙ্গালি নাম ছিল।
ভেঙ্কটাচারের বাংলা উপন্যাসের অনুবাদগুলি এত জনপ্রিয় ছিল যে, মানুষ তাঁদের কুকুর ও বিড়ালদেরও পরিমল ও বিনতা নামে ডাকতে শুরু করেছিল। তাই আমার ইচ্ছে হত, নিজের চরিত্রগুলির নাম রাখি পুরোনো ঢঙে- যেমন সুব্বাম্মা ও ভেঙ্কাম্মা।
আমার প্রাথমিক নাটকগুলির কথাও আমি উল্লেখ করেছি। সেগুলি পড়ে এক বন্ধু মন্তব্য করেছিলেন- “করন্থ কেবল গম্ভীর ও বাস্তবধর্মী লেখার জন্যই উপযুক্ত।” এই কথাটি আমাকে আঘাত করেছিল। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে কল্পনাশ্রয়ী লেখাতেও আমি সমান পারদর্শী। ঠিক সেই সময়েই আমি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বারাণসী তীর্থযাত্রা সেরে ফিরেছিলাম। নাটকের মঞ্চসংশ্লিষ্ট কিছু কাজেও হাত লাগিয়েছিলাম। নাট্যদল ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছু হতাশাজনক অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম সেই সমস্ত তিক্ততাকে হাসিতে রূপান্তরিত করতে। তারই ফল ছিল আমার দেব দূতারু। আমি চলতে চলতেই বইটি লিখেছিলাম- এটি ছিল একদল স্বর্গীয় দূতের প্রতিবেদনধর্মী রচনা।
এরপর আমার পরবর্তী উপন্যাস সুলেয়া সংসার (অর্থাৎ “এক পতিতার জীবন”)। যারা এই বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি পড়েছেন, তাঁরা অনুমান করতে পারবেন যে এই উপন্যাসের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম সেই মেয়েটির কাছ থেকে, যিনি এক অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন- এবং সেই সামাজিক পরিবেশ থেকে, যেখানে অন্য এক জীবন গড়ে উঠেছিল।”
করন্থ মনে করেন তাঁর ষাট বছর বয়সের পরে লেখা উপন্যাসগুলোই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,
“ষাটের দশকে আমি লিখেছিলাম ‘আলা-নিরালা’, ‘ইদ্দারু চিন্তে’, ‘ইন্নোন্দে দারি’, স্ব’প্নদ হোলে’, ‘মূকাজ্জিয় কানাসুগালু’ এবং ‘উক্কিদা নোরে’। এর মধ্যে এক-দুটোর বিষয়বস্তু ও কাহিনি এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না।
আলা-নিরালা (গভীর ও অগভীর) একই ট্রেনে ভ্রমণরত ভিন্ন মানসিকতার যাত্রীদের জীবনের ভেতরে উঁকি দেয়। এর প্রেরণা এসেছিল আমার এক প্রবীণ বন্ধু নচাগারা শম্ভু শর্মার কাছ থেকে, যাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ছিলেন পুরনো ধাঁচের এক গভীর পণ্ডিত- যে দর্শন তিনি অধ্যয়ন করতেন, সেটিই তিনি জীবনে পালন করতেন। একদিন তিনি কাঠ বোঝাই একটি লরির চাকায় পড়ে যান। এক চাকা থেমে যায় তাঁর এক পায়ের ওপর। ভিড় জমে যায়। অসহায় জনতার উদ্দেশে তিনি শান্তভাবে বলেন, “তোমরা কীসের জন্য দাঁড়িয়ে আছ? পা কেটে দাও, শরীরটা টেনে বের করো।” পরে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। স্থির কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, “অবশ্যমনুভোক্তব্যং কৃতকর্ম শুভাশুভম্”- অর্থাৎ, “যা অনিবার্য, কর্মফল হিসেবে শুভ বা অশুভ যা-ই আসুক, তা ভোগ করতেই হবে।” এই বিশ্বাসেই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। সেই দর্শনই উপন্যাসটির প্রেরণা হয়ে উঠেছিল।
স্বপ্নদ হোলে (স্বপ্নের স্রোত) মূলত শিল্পকে কেন্দ্র করে লেখা। এতে আদি মানবের উল্লেখ আছে। এটি এক পথভ্রষ্টা মেয়ের গল্প। এর উৎস এক অদ্ভুত বাস্তব ঘটনা। এক স্কুলশিক্ষিকা, যিনি বয়সে তরুণী, এক প্রবীণ সহশিক্ষকের প্রলোভনে পড়ে গর্ভবতী হন। তাঁদের বিবাহের পথে বাধা ছিল- তারা ভিন্ন জাতের এবং পুরুষটি ইতিমধ্যেই বিবাহিত, স্ত্রীর সন্তানও ছিল। মেয়েটির এক আত্মীয় ঘটনাটি জানতে পেরে প্রচণ্ড রেগে যান, প্রতিশোধ নিতে চান। কোনো এক কারণে তিনি আমার পরামর্শ নিতে এলেন। আমি বলেছিলাম, প্রতিশোধ নিলে শুধু মেয়েটির ভবিষ্যৎ আরও নষ্ট হবে। প্রথম কাজ হওয়া উচিত তার যত্ন নেওয়া। আমরা এক ডাক্তারের সহায়তায় তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, যে সহকর্মীটি তখন মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পর তিনিই তাকে বিয়ে করতে এগিয়ে এলেন। তারা আজও সুখে আছেন। এই বাস্তব ঘটনাটিকেই আমি উপন্যাসের মূল কাহিনি হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম।
উক্কিদা নোরে (ফেনিল উত্তাল তরঙ্গ) উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে, যেখানে শালীনতা ও মর্যাদার কোনো মূল্য নেই, আর কদর্যতাই যেন সুগন্ধে পরিণত হয়েছে।
মূকাজ্জিয় কানাসুগালু (মূকাজ্জির স্বপ্নদৃষ্টি) অবদমিত যৌনতার কয়েকটি দিক অন্বেষণ করে। বৃদ্ধা মূকাজ্জি যা বলেন ও করেন, তা ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত হানে। আমাদের সমাজে যেখানে ধনীদের পাপ উপেক্ষিত হয় আর গরিবদের সামান্য ভুল বড় করে দেখা হয়, সেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্কই হয়ে ওঠে একটি প্রধান প্রশ্ন। এই বিষয়ে মূকাজ্জির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত চমকপ্রদ।
বইটি প্রথম প্রকাশের পর যেসব বন্ধু পড়েছিলেন, তারা কিছুই বলেননি। বহু বছর পরে এই একই বই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করে, এবং প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়। সমালোচকদের একমাত্র আপত্তি ছিল- মূকাজ্জিকে আমি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (Extra-sensory perception) বা অতিরিক্ত সংবেদনশক্তি দিয়েছি। তারা অলৌকিকতা বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু এই বৃদ্ধার এমন শক্তি থাকতে পারে তা মানতে পারেননি। এই বিতর্কের ভেতরেই বইটির মূল ভাবনা- নারী-পুরুষ সম্পর্ক- আড়ালে পড়ে গেল।
এই উপন্যাসে আমি প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতীয় অভিজ্ঞতাকে এই ক্ষেত্রের আলোচনায় একত্র করে এক আশি বছরের বৃদ্ধার জীবনের ভেতরে সংক্ষিপ্ত করেছি। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাঁর গুপ্তদৃষ্টিশক্তি তাঁকে ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে দেখার ক্ষমতা দিয়েছে। তাঁর সেই দৃষ্টিশক্তিই তাঁকে আরও সহানুভূতিশীল করেছে- যার ফলে তিনি এমন এক নারী-পুরুষকে আবার মিলিয়ে দেন, যারা আত্মীয়ের অত্যাচারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
আমার অদ্ভুত লাগে- যাঁরা পুরাণকে ইতিহাস বলে মানেন, যাঁরা সাইবাবার পায়ে মাথা ঠেকান, তাঁরাই আবার মূকাজ্জিকে অবাস্তব বলে মনে করেন!”
তাঁর সাতষট্টিতম জন্মদিনে তাঁর অন্যতম আপন শহর, উডুপী, তাঁকে ঘিরে তিনদিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করছিল। সেখানেও সভাপতিত্ব করেছিলেন এক বিখ্যাত বাঙালি।
“আমার ষাটতম জন্মদিনে আমার প্রিয় বন্ধু হরিদাস ভাট এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেই সময়ের মতোই, এ বারও প্রস্তুতি যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, থামানোর আর উপায় ছিল না, তখনই আমি তার খবর পাই। উদ্যোক্তাদের অজুহাত ছিল- রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পাওয়া পদ্মভূষণ সম্মান। উডুপী-র মানুষ উৎসব আর ভোজসভা আয়োজনের ওস্তাদ। আমি ভাবছিলাম, এবার সভার সভাপতি হিসেবে কাকে ডাকা হবে, তখনি শুনলাম- বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি বহু ভাষার অধিকারী ছিলেন এবং সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান ও সভ্যতা বিষয়ে অগ্রণী গবেষণা করেছিলেন।
এটি ছিল তিন দিনের এক মহোৎসব- যেখানে কর্ণাটক ও দেশের নানা প্রান্তের শীর্ষ সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের অনেকেই আমার আপনজন। আলোচনা, ভোজসভা, সঙ্গীত-আসরে ভরে উঠেছিল উৎসব। আমার অজান্তেই আমার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন জগৎ- করন্থ প্রপঞ্চ, ছয়-সাতশো পৃষ্ঠার এক সংবর্ধনা গ্রন্থ। যেন বাল প্রপঞ্চ ও বিজ্ঞান প্রপঞ্চ–এর লেখকের বিরুদ্ধে এক মিষ্টি প্রতিশোধ!
এত সম্মানিত মানুষদের সামনে, এত স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়ে, আমি নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছিল। বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারা। পরে কলকাতা সফরের সময় তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনিই আমার বই মারালি মান্নিগে–র বাংলা সংস্করণের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন।”
সম্ভবত বাংলা সাহিত্য থেকে কন্নড় ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেছিলেন বিন্ডিগনাভালে বেঙ্কটাচার্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনা কন্নড়ে অনুবাদ করেছিলেন। বেঙ্কটাচার্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক। তিনি বাংলাভাষার প্রতি এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকেই বাংলা শিখিয়েছিলেন- এমনকি প্রতিবেশীরাও বাংলায় কথা বলতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেঙ্গালুরু সফরে আসেন, তখন তিনি বেঙ্কটাচার্যের বাড়িতেই ছিলেন। স্বামীজি আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন যে, আশেপাশের সকলে তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে!
কন্নড় সাহিত্যের নবোদয় যুগে করন্থের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক যেমন কুভেম্পু, ডি আর বেংদ্রে, ভি কে গোকাক, ভি. শীতারামাইয়া, ভেঙ্কান্নাইয়া, গোবিন্দ পাই, কে. কৃষ্ণমূর্তি এবং কৃষ্ণশাস্ত্রী, সকলেই বাংলায় দক্ষ ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস কন্নড় পাঠকসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল, তাঁদের রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর। শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই কন্নড় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বেংদ্রে বাংলার ১০১টি কবিতা কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সাংবাদিক পা. ভেম. আচার্য নানা ছদ্মনামে বহু বাংলা রচনা অনুবাদ করেছিলেন। এম. এস. কৃষ্ণমূর্তি বাংলার আধ্যাত্মিক কবিদের বিষয়ে লিখেছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাসের কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন।
বাংলা লেখককে নিয়ে কন্নড় ভাষায় এক অসাধারণ কাজ হল এ. আর. কৃষ্ণশাস্ত্রীর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রচনা–বিষয়ক প্রবন্ধ, যার জন্য তিনি ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।
করন্থের সময় থেকে আধুনিক কন্নড় সাহিত্য অনেক পথ অতিক্রম করেছে। এখন বেঙ্গালুরু সহ কর্ণাটকের অন্যান্য শহরেও বহু বঙ্গভাষী থাকেন কর্মসূত্রে। শুধু বেঙ্গালুরুতেই প্রায় শ’দেড়েক দুর্গাপুজো হয়। ইলিশ মাছ থেকে গোবিন্দভোগ চাল, পটল থেকে রেডি-টু-ইট ধোঁকার ডালনা এই মহানগরে সবই সহজলভ্য। কিন্ত বর্তমান কন্নড় সাহিত্যে, অনুবাদে যে টুকু পড়তে পেরেছি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো প্রভাব দেখতে পাই নি ।
কর্ণাটকের সঙ্গে আমাদের ভৌগলিক নৈকট্য যতোটা বেড়েছে, সাংস্কৃতিক দূরত্ব কি ততোটাই বেড়েছে?
কর্ণাটক প্রবাসী আমার সমবয়সী এক বাঙালি অন্য একটা প্রশ্ন তুললেন, “এখানকার বাঙালিদেরও কি বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে নৈকট্য আছে?”
এই সব প্রশ্নের উত্তরে মৌন থাকাই নিরাপদ।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনকী আসে যায় নামে? - দিলীপ ঘোষআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনআশাবরী - Manali Moulikআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
 হীরেন সিংহরায় | ১৬ নভেম্বর ২০২৫ ১১:১৪735819
হীরেন সিংহরায় | ১৬ নভেম্বর ২০২৫ ১১:১৪735819 - এমন মানুষটির সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না ভেবে লজ্জিত হই। বেঙ্গালুরুতে আমার স্কুলের বন্ধু আছে তার ছেলেরা চমৎকার কন্নড় বলে কিন্তু করনথের কথা কেউ বলে নি। অশেষ ধন্যবাদ।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












