- হরিদাস পাল বইপত্তর

-
মুর্শিদাবাদ - উত্থান , ‘ইনকিলাব’ ও পতন
পাপাঙ্গুল লেখকের গ্রাহক হোন
বইপত্তর | ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৪৩৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - The city of Murshidabad is as extensive, populous and rich, as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than any of the last city. ~ Clive
ফারসি ঐতিহাসিকরা বাংলার নামকরণ করেছিল ‘জিন্নত-উল-বিলাদ’ বা ‘প্রদেশগুলির মধ্যে স্বর্গ।’ মুঘল সম্রাট ঔরংজেব বাংলাকে ‘জাতীয় স্বর্গ’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সব মুঘল ফরমানেই বাংলাকে ‘ভারতবর্ষের স্বর্গ’ বলে উল্লেখ করা হত।
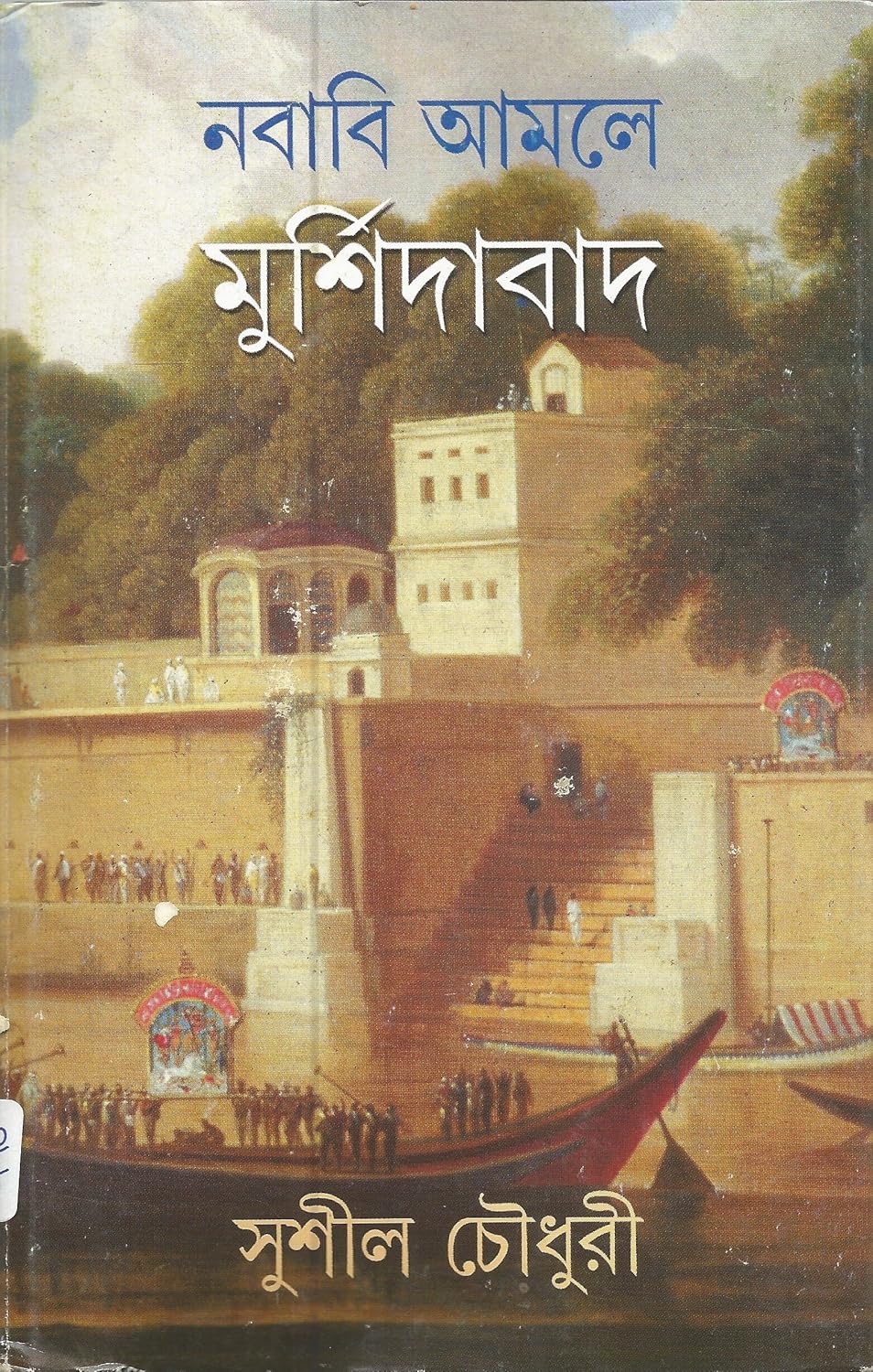
অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়াতেই মুঘল সম্রাট ঔরংজেব মহম্মদ হাদি নামক তাঁর এক বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারীকে, যিনি তখন হায়দরাবাদের দেওয়ান ছিলেন, দেওয়ান করে ও করতলব খাঁ উপাধি দিয়ে বাংলায় পাঠান। উদ্দেশ্য, করতলব বাংলার রাজস্ব বিভাগকে সুবিন্যস্ত করে বাংলা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করবেন এবং তা নিয়মিত ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাবেন। বৃদ্ধ সম্রাট তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে কুড়ি বছর ধরে জর্জরিত ও আর্থিক অনটনে ব্যতিব্যস্ত। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রায় সব অঞ্চল থেকেই তাঁকে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। ঔরংজেবের একমাত্র ভরসা করতলব খাঁ ও বাংলার রাজস্ব। করতলব সম্রাটকে নিরাশ করেননি। তিনি বাংলার রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ সংস্কার করে মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত রাজস্ব পাঠিয়ে গেছেন। কিন্তু করতলব রাজধানী ঢাকায় এসে দেখলেন, তখনকার সুবাদার ঔরংজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিম-উস-শান নতুন দেওয়ানের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নন কারণ এতদিন তিনি একচ্ছত্রভাবে বাংলার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভোগ করছিলেন। করতলব বুঝতে পারেন যে ঢাকায় তিনি নিরাপদ নন। সর্বোপরি, ঢাকায় সুবাদার আজিম-উস-শানের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারবেন না, স্বাধীনভাবে কাজ করা তো দূরের কথা। তাই তিনি দেওয়ানি কার্যালয় ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করলেন মখসুদাবাদে।
১৭০৪ সালে মখসুদাবাদে দেওয়ানি স্থানান্তরিত করে তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরংজেবের কাছে বাংলার রাজস্ব ও নজরানা নিয়ে হাজির হলেন। সম্রাট সানন্দে এতে অনুমতি দিলেন। তাঁকে মুর্শিদকুলি খান উপাধি দিয়ে তাঁর নামানুসারে মখসুদাবাদের নতুন নামকরণ, মুর্শিদাবাদ, করতে দিতে সাগ্রহে রাজি হলেন। এভাবেই মুর্শিদাবাদের উৎপত্তি।
দেওয়ানী বিভাগে কারচুপি ও তছরূপ আটকানোর উদ্দেশ্যে এবং জমিদার রায়তের ভূমিস্বত্বের প্রমাণ রাখার জন্য একজন স্বাধীন বঙ্গাধিকারী কানুনগো মহাশয় ছিলেন, যাঁর অধীনে পরগনায় পরগনায় কানুনগোরা ও মৌজায় মৌজায় পাটোয়ারীরা দলিল ও হিসাব রাখত। কতকগুলি মৌজা (গ্রাম) নিয়ে এক একটি পরগনা এবং কতকগুলি পরগনা নিয়ে এক একটি সরকার গঠিত হত, এবং মোগল শাসনতন্ত্র অনুয়ায়ী প্রত্যেক সরকারে নিজামতের একজন ফৌজদার ও দেওয়ানীর একজন আমিল যথাক্রমে শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।
প্রত্যেক পরগনায় বংশানুক্রমিক ভাবে একজন স্থানীয় জমিদার বা চৌধুরী নিযুক্ত রাখা হত। সরকারের খাজনা আদায় করে দেওয়ানী বিভাগের আমিলদের হাতে তুলে দেওয়া এঁদের হক ছিল। তা ছাড়া পরগনায় পরগনায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পাইক রেখে চুরি ডাকাতি রোধ করার দায়িত্ব এদের উপর অর্পিত ছিল। উপরোক্ত খিদমতের জন্য তাঁদের মালজমি ও সায়ের জমার খাজনা থেকে দশ ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য ছিল। নিজামত, দেওয়ানী ও কানুনগোই কর্মচারীরা যে অর্থে সরকারী চাকরী করতেন এবং বদলি হতেন, জমিদার, চৌধুরী ও তালুকদার (জমিদারের অধীন পরগনার এক অংশের হকদার) সেই অর্থে সরকারী কর্মচারী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন আঞ্চলিক ভূশক্তির বংশানুক্রমিক প্রতিভূ।
আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র মুর্শিদকুলী খান প্রথম একাধারে নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায় নিজামত ও দেওয়ানীর পার্থক্য কার্যত মুছে গেল।
মুর্শিদকুলি যখন ১৭০৪ সালে দেওয়ানি কার্যালয় ঢাকা থেকে সরিয়ে মখসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) নিয়ে আসেন তখন জমিদারদের আমলারা, দেওয়ানি কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সব কানুনগো ও অন্যান্য কর্মচারীরা সবাই ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসে, সঙ্গে আসে বেশ কিছু ব্যাঙ্কার-মহাজন ও সওদাগর—এদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ। এত বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোক পাশাপাশি থাকার ফলে পরস্পরের মেলামেশা ও আদানপ্রদানের মাধ্যমে একটি ‘কসমোপলিটান’ (cosmopolitan) সংস্কৃতির উদ্ভব হয় মুর্শিদাবাদে। একদিকে হিন্দু ও জৈন মন্দির, মুসলমান মসজিদ অন্যদিকে আর্মানি ও খ্রিস্টানদের গির্জা—সবকিছুর সহাবস্থান। এমন কী সিরাজদ্দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের চুক্তি (ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭) সম্পাদন করেই তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদ ফিরে তাঁর প্রাসাদ হীরাঝিলে হোলির উৎসবে মেতে ওঠেন। নবাবরা প্রচুর অর্থব্যয় করে হিন্দুদের দেওয়ালি উৎসবও পালন করতেন।
অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই দুই ধর্মসংস্কৃতির সমন্বয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ সময় মুসলমানরা হিন্দুমন্দিরে পুজো দিচ্ছে আর হিন্দুরা মুসলমানদের দরগাতে সিন্নি দিচ্ছে— এটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এই দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপীরের মতো নতুন ‘দেবতা’র জন্ম— যে ‘দেবতা’ হিন্দু মুসলমান উভয়েরই উপাস্য। কবি ভারতচন্দ্রের ‘সত্যপীর’ কবিতা এ মিলন প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন।
১৭০৭ সালে ঔরংজেবের মৃত্যুর সময়ই মুর্শিদকুলি বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরও তিনি দিল্লির মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত বাংলার রাজস্ব পাঠাতে ভোলেননি। দিল্লির বাদশাহি মসনদে যিনিই বসুন না কেন, মুর্শিদকুলির নীতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মুঘল বাদশাহরাও নিয়মিত অর্থ পেয়ে খুশি, বাংলা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বা সামর্থ্য কোনওটাই তাঁদের ছিল না।
মুঘল শাসনকাঠামোর রীতি ভেঙে ১৭১৬/১৭ সালে মুর্শিদকুলিকে দেওয়ানের সঙ্গে সুবাদারের পদেও নিযুক্ত করা হল। ফলে এতদিন ধরে যে রীতি চলে আসছিল—সব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও মনসবদারদের দিল্লি থেকেই বাংলায় পাঠান হত— তার এখন সম্পূর্ণ অবসান হল।
এঁরা, বিশেষ করে মুঘল পরিবারের সদস্যরা, বাংলা ছাড়তে চাইতেন না কারণ এখানে ধনসম্পদ আহরণের অফুরন্ত সুযোগ। তাই মুঘলনীতির ব্যতিক্রম করে তাঁরা তিন বছরের অনেক বেশি সময় বাংলায় সুবাদার হিসেবে থেকে গেছেন। এঁরা বাংলা থেকে যে ধনসম্পদ আহরণ করতেন তার সবটাই প্রায় বাংলার বাইরে দিল্লি, আগ্রা ও উত্তর ভারতে নিয়ে যেতেন। ফলে বাংলা থেকে এই ধন নিষ্ক্রমণের ধারা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই সব সুবাদার, মনসবদাররা কী পরিমাণ ধন আহরণ করে বাংলার বাইরে নিয়ে যেতেন তার একটা ধারণা করা যেতে পারে কয়েকজনের দৃষ্টান্ত থেকে।
নবাবি আমলে বাংলা, অবশ্যই মুর্শিদাবাদ থেকে, এই বিপুল ধন নিষ্ক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এখন আর সুবাদাররা দিল্লি থেকে নিযুক্ত মনসবদার নন, মুর্শিদকুলি বাংলায় প্রায় স্বাধীন নিজামত প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাই এখন নিজামতের সব পদে নিযুক্ত হল। ফলে বাংলা থেকে ধন নিষ্ক্রমণের প্রশ্নই রইল না। নবাবরা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাংলায় ধন আহরণ করা বন্ধ করে দিলেন ঠিক তা নয়। যা ধনসম্পদই তাঁরা আহরণ করে থাকুন না কেন, তা বাংলাতেই থেকে গেল, তাতে বাংলার ধনসম্পদই বৃদ্ধি পেল। ১৭৪০-এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত নবাবরা বাংলা থেকে প্রতি বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন।
জৈন কবি নিহাল সিংহ লিখেছেন, বালুচরে কাঁসার হাট বসে, সেখানে অনেক রকম ভাল ভাল বাসন বিক্রি হয়। বহু ঘর তাঁতিরও বাস সেখানে, তারা নানারকমের কাপড় বোনে। কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ ও খাগড়ায় অনেক লোকের বাস, বিভিন্ন দেশের, জাতির ও ধর্মের। রেশমের ও রেশমি বস্ত্রের কারবার জমজমাট। দিল্লির সঙ্গেই যেন মুর্শিদাবাদ টেক্কা দেয়—‘জৈসা দিল্লিকা বাজার, তৈসা চৌক গুলজার’।
তুঁত গাছের চাষই ছিল তখন মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার অঞ্চলের সবচেয়ে পরিচিত চিত্র। মুর্শিদাবাদ-সৈয়দাবাদে যে সব অভিজ্ঞ ও বড় বড় ব্যবসায়ী এই পণ্যই শুধু সরবরাহ করে, এদের মধ্যে আছে গোঁসাইরাম, রাম সিং, রামনাথ ইচ্ছানাথের মতো ধনী ও এ পণ্যে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কাশিমবাজারের এক গুজরাটি সিল্ক ব্যবসায়ীর গোমস্তা ছিলেন এবং তিনি নিজেও তিরিশ বছর ওই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৭৫০-র দশকের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে মুর্শিদাবাদে তখন দশ জন সওদাগর ছিল যারা বছরে ১৩,০০০ থেকে ২০,০০০ মণ পর্যন্ত সিল্ক রফতানি করত।
সিল্ক কাপড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল ‘টাফেটার’ (tafettas বা taffaties) আর এটা প্রধানত কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেই বেশি তৈরি হত। তাঁতিরা সাধারণত তিনটে রঙের ‘টাফেটা’ বুনত— পাকা সবুজ, হালকা সবুজ ও নীল।
রেশম শিল্পের পাশাপাশি আরও কিছু ছোটখাটো শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল নবাবি আমলের মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার অঞ্চলে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হাতির দাঁতের কারুশিল্প (ivory carving)।
কাঁচা রেশমের বাজারে সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল গুজরাটিরা—দামের কোনও তোয়াক্কা না করে তারাই সবচেয়ে ভাল রেশম কিনত, যার জন্য সবথেকে উৎকৃষ্ট রেশমের নামই হয়ে যায় ‘গুজরাটি সিল্ক’। অবশ্য বাজারে অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীও ছিল, যাদের সাধারণত পাইকার বলা হত। এরা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি ও এশীয় বণিকদের কাঁচা রেশমের জোগান দিত। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাটে যেমন বণিকদের ‘মহাজন’ বা ‘গিল্ড’ গোছের জিনিস ছিল, তেমনি মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরও পঞ্চায়েত ছিল (রেকর্ডে ‘punch or whole body’)। পঞ্চায়েত যা ঠিক করত, সব ব্যবসায়ী তা মেনে নিত।
আগে ইংরেজ ও ডাচরা পারস্যদেশ ও চিন থেকে ইউরোপে রেশম রফতানি করত। কিন্তু যখন তারা দেখল যে বাংলা থেকে রেশম রফতানি করতে পারলে অনেক লাভজনক হবে, তখন তারা এদিকে নজর দিল। ইংরেজ কোম্পানি ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপন করে বাংলা থেকে ইউরোপে রেশম রফতানি করার ওপর জোর দিল। ইংরেজদের সঙ্গে তফাত, ডাচরা বাংলার রেশম শুধু ইউরোপে নয়, জাপানেও তারা তা রফতানি করত। ইউরোপের রেশমশিল্পে সাধারণত ইতালির রেশমই ব্যবহার করা হত। কিন্তু ওই রেশমের মূল্য ছিল অত্যধিক। কিন্তু যখন দেখা গেল যে বাংলার রেশম ইতালির রেশমের বদলে ইউরোপের রেশমশিল্পে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাতে খরচ অনেক কম পড়বে, তখন ইউরোপে বাংলার রেশমের চাহিদা বেশ বেড়ে গেল এবং কোম্পানিগুলিও বাংলা থেকে রেশম রফতানি করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল।
সুজাউদ্দিন খান মুর্শিদাবাদের নবাব হলেন। তখন আলিবর্দি খান রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন এবং জানকীরাম তাঁর জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক হলেন। এরপর আলিবর্দি খান বিহারের নায়েব নাজিম হলেন, তখন জানকীরাম তাঁর দেওয়ান হলেন। যে বছর নাদির শাহ দিল্লীতে চড়াও হন সে বছর কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্র মাতামহ আলিবর্দি খান ষড়যন্ত্র করে পরবর্তী নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে বসলেন। তখন জানকীরাম ‘রাজা’ উপাধি পেয়ে দেওয়ান-ই-তন্ পদে নিযুক্ত হলেন।
রায়দুর্লভ রাম ছিলেন বিহারের ডেপুটি গভর্নর জানকীরামের পুত্র। তবে তিনি পিতার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন না। রায় দুর্লভ মারাঠাদের হাতে বন্দী হলে জানকীরাম নবাবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন— এক কোটি টাকা দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে বিদায় করুন কিন্তু আলিবর্দি তা করেননি। মৃত্যুর আগে জানকীরাম নবাব আলিবর্দিকে লেখেন যে, তাঁর পুত্ররা কেউ পাটনার (অর্থাৎ বিহারের) শাসনকার্য চালাতে পারবে বলে তাঁর মনে হয় না। তাই তাঁর অবর্তমানে তাঁর পেশকার রাজা রামনারায়ণকে যেন বিহারের ডেপুটি গভর্নরের পদে নিযুক্ত করা হয়। এ-পরামর্শ মেনে আলিবর্দি জানকীরামের মৃত্যুর পর ১৭৫৩ সালে রাজা রামনারায়ণকে ওই পদে নিযুক্ত করেন।
বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ইত্যাদি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী রাজ্যগুলি বর্গিবিভ্রাটে পর্যুদস্ত হওয়ায় ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে রাঢ় অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদে খাজনা আসা বন্ধ হয়ে যায়। আলিবর্দি গঙ্গার অপর তীরের রাজ্যগুলি থেকে জোর করে টাকা আদায় করে বর্গিদের মোকাবিলা করতে নামেন। দিনাজপুর, রাজশাহী ও নদীয়ার রাজাদের এই টাকার ঘাটতি মেটাতে হয়েছিল এবং যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ বর্গির হামলা থেকে সম্পূর্ণ ছাড়া পায়নি, তবুও খাজনার দায়ে তিনি ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের পরে মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আটক ছিলেন। মারাঠারা যখন ১৭৪২ সালে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে, তখন মীর হাবিবের নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাড়ি থেকে লুঠ করে নগদ ২ কোটি টাকা।
১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে দেখা যায় মুস্তফা খান, আতাউল্লাহ্ খান, শামসের খান ইত্যাদি প্রধান প্রধান ছয় জন দামামা বিশিষ্ট সেনানীর মধ্যে মীর জাফরও একজন দামামার অধিকারী সেনানীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেবার সওয়ার বাহিনীর প্রথম সারিতে লড়াই করে তিনি রঘুজী ভোঁসলেকে এমন বিধ্বস্ত করে ফেলেন যে কোনোমতে রঘুজী প্রাণ নিয়ে পালান। সেই থেকে নবাবের ধারণা হয় মীর জাফর একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী সেনাপতি। এই সময় থেকে সুবাহ বাংলার বক্সি (Paymaster-General) পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নবাবের দক্ষিণ হস্ত ও প্রধান সেনাপতিরূপে দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন।
নবাব আলিবর্দির সময়, ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত, প্রায় প্রতি বছর যে মারাঠা আক্রমণ হয়েছে, মারাঠারা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়, মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট পথেই বাংলায় লুঠতরাজ করতে আসত। ওই সব অঞ্চলের কৃষক-তাঁতি-কারিগর প্রমুখ বর্ষার আগে, মারাঠারা চলে গেলে, নিজেদের কাজকর্ম শুরু করে দিত আবার শীতকালে, মারাঠারা আসার আগে, তাদের ফসল/উৎপাদন সব গুছিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যেত। ফলে বাংলার অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ক্ষতি হয় নি। মারাঠাদের বছরে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তি কিনে নেবার পর আলিবর্দি বাংলা থেকে মারাঠা আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন এবং ইতিহাস মুছে দেবার প্রতি খুবই যত্নবান হয়ে পড়েন।
লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও হল্যান্ডের হেগ শহরের রাজকীয় মহাফেজখানায় (Algemeen Rijksarchief) ঠিক পলাশির আগে বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দুটি তালিকা সুশীল চৌধুরী পেয়েছিলেন। প্রথমটিতে (রবার্ট ওরম-এর তালিকা) দেখা যাচ্ছে আলিবর্দির সময় (১৭৫৪-তে) দেওয়ান, ‘তান-দেওয়ান’, ‘সাব দেওয়ান’, বক্সি প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুদের দখলে, একমাত্র মুসলমান বক্সি হল মীরজাফর। আবার ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু। দ্বিতীয় তালিকাটি বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের (Jan Kerseboom)। সেই তালিকাতেও নায়েব দেওয়ান রায় রায়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ১৭৫৪/৫৫ সালের এই যে চিত্র, সিরাজদ্দৌল্লার সময় তা আরও স্পষ্ট হয়। তরুণ নবাবের ডানহাত ও সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভাজন ছিলেন কাশ্মীর থেকে আসা হিন্দু মোহনলাল।

রজতকান্ত রায়ের মতে ইংরেজরা চক্রান্তে সাহায্য করেছিল কিন্তু মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। তিনি তৎকালীন জমিদারদের নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকা এবং রাজদরবারে ষড়যন্ত্রের পরম্পরা দেখিয়েছেন। যেমন কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামে ঢাকার সরকারের এক অখ্যাত রাজকর্মচারীর পঞ্চম পুত্র ছিলেন রাজবল্লভ সেন। ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে ইনি ঢাকার নওয়ারা মহলের পেশকার পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি করে ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে হোসেন কুলী খানের অধীনে ঢাকার নিয়াবতের কার্যনিবাহ করতে শুরু করেন। মনিব ও নায়েবের অবর্তমানে এই ঢাকার কর্তৃত্ব গিয়ে পড়ল নওয়াজিশ পত্নী ঘসেটি বেগম এবং তাঁর সেনাপতি মীর নজর আলি ও নায়েব রাজবল্লভের হাতে। এঁদের দখলে ঢাকার নিয়াবতি এবং ঐ নিয়াবতের বিপুল দৌলত। অন্য দিকে মীর জাফর, তাঁর হাতে বক্শীর দফতর। এদিকে পূর্ণিয়াতে বসে আছেন শওকত জঙ্গ, তিনিও নবাবের নাতি এবং সেখানকার ফৌজদার। সেই সময় ঘসেটি বেগম সিরাজকে সরানোর চক্রান্ত করেন। ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত যদি সফল হত, তাহলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের পালিত শিশু পৌত্রকে (এই শিশু সিরাজের ছোট ভাইয়ের ছেলে) মসনদে চাপিয়ে মীর নজর আলি রাজত্ব করতেন, সেটা মীর জাফরের পক্ষে মোটেই সুবিধার হত না।
দিগ্বিজয়ী মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের নবাবী অনুগ্রহপুষ্ট সুবিশাল বর্ধমান রাজ্য গঠিত হবার আগে দক্ষিণ রাঢ় দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে একটি রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের আদি নিবাস প্রাচীন ভুরসুট রাজ্য। বর্ধমানের কীর্তিচন্দ এবং বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ একই বছর (১৭০২) রাজা হন। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে মহারাজ কীর্তিচন্দ তেমন কায়দা করতে পারেননি। অস্বাভাবিক ভাবে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহের মৃত্যু হয়।
যশোহরের বিদ্রোহী রাজা সীতারাম রায়, বন বিষ্ণুপুরের পরম বৈষ্ণব মল্লরাজা গোপাল সিংহ, বীরভূমের পাঠান রাজা বদি-উজ-জামান খান, নাটোরের পুণ্যশ্লোকা রানী ভবানী, নদীয়ার চতুর চূড়ামণি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইত্যাদি অনেক প্রধান প্রধান জমিদার কীর্তিচন্দের [এবং সিরাজের ] প্রতিবেশী ছিলেন। অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করে কৃষ্ণচন্দ্র সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে ‘অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্ৰীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র রায় নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।
১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ সুবাহ্ বাংলার এক পঞ্চমাংশ জুড়ে মহারানী ভবানীর জমিদারী বিস্তৃত ছিল। রেনেলের সার্ভে অনুযায়ী নাটোর রাজ্যের আয়তন ছিল ১২,৯০৯ বর্গমাইল। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রংপুর ও যশোহর জেলার প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে এই জমিদারী অবস্থিত ছিল। বিধবা অবস্থায় রানী তাঁর বিধবা মেয়ে তারাসুন্দরীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের সমীপে গঙ্গাতীরস্থ বড়নগরের বাড়িতে থাকতেন। লোককাহিনী অনুসারে সিরাজ গঙ্গার বক্ষে বজরা থেকে ছাদের উপর আলুলায়িত কেশা পরমরূপসী তারাসুন্দরীকে দেখে উন্মত্ত হয়ে সৈন্য প্রেরণ করেন। নবাবের সৈন্যদের বাধা দিতে রুদ্রমূর্তি ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীরা আবির্ভূত হন, মস্তরাম বাবাজী তাঁদের চালনা করেন। ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, গঙ্গাতীরে এঁর আখড়ার ভিটে এই শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যমান ছিল।
উল্টোদিকে সুশীল চৌধুরীর মতে - “পলাশির ষড়যন্ত্রে মুর্শিদাবাদ দরবারের অভিজাতবর্গের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মীরজাফর ও জগৎশেঠ, যদিও উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রমুখও এতে জড়িত ছিলেন। তাই মীরজাফরই একমাত্র ‘বিশ্বাসঘাতক’, এটা সত্য নয়। জগৎশেঠের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজরা প্রথমে সিরাজদ্দৌল্লার জায়গায় নবাব হিসেবে ইয়ার লতিফ খানকে বসাবার মতলব করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা জগৎশেঠদের মনোনীত প্রার্থী মীরজাফরের দিকে ঝুঁকল কারণ তারা জানত জগৎশেঠদের সাহায্য ছাড়া বাংলায় কোনও রাজনৈতিক পালাবদল সম্ভব নয়।”
মীরজাফর, জগৎশেঠ বা উমিচাঁদের মতো রায়দুর্লভ কিন্তু ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর যোগ অনেকটাই পরোক্ষ। নবাবের দেওয়ান এবং সৈন্যবাহিনীর একাংশের অধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দুর্লভরাম নবাবের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সাধারণত বলা হয় এর মূল কারণ সিরাজদ্দৌল্লা হঠাৎ মোহনলালকে সব অমাত্যদের ওপর বসিয়ে দিলেন এবং এই মোহনলাল আলিবর্দির আমলের সব পুরনো অমাত্যদের হেনস্থা ও অপমান করতে লাগলেন।
পলাশির ষড়যন্ত্রে ইয়ার লতিফের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য। উত্তরভারতীয় এই যোদ্ধা ছিলেন দু’হাজারি মনসবদার। জগৎশেঠদের সুরক্ষার জন্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে একটা মাসোহারা পেতেন। নবাবের সৈন্যবাহিনীতে তাঁর স্থান খুব একটা উঁচুতে ছিল না। উমিচাঁদ চেয়েছিলেন সিরাজদ্দৌল্লার পরিবর্তে ইয়ার লতিফকে নবাব করতে, মীরজাফরকে নয়।
রজতকান্ত রায় , কুমকুম চ্যাটার্জী প্রমুখ কেমব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকদের বিপরীতে গিয়ে সুশীল চৌধুরীর গবেষণার প্রতিপাদ্য - ইংরেজরাই পলাশি ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা এবং তাদের সক্রিয় সমর্থন ও উৎসাহ ছাড়া পলাশির চক্রান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করে বিপ্লব ঘটাতে পারত না। ইংরেজ কোম্পানির ঐতিহাসিক রবার্ট ওরম মাদ্রাজে ক্লাইভকে লিখেছিলেন (১৭৫২): “বাংলা থেকে এ বুড়ো কুকুরটিকে [নবাব আলিবর্দি] তাড়াতে পারলে একটা উত্তম কাজ করা হবে। ভাল করে চিন্তা না করে আমি এ-কথা বলছি না। ব্যাপারটা নিয়ে কোম্পানির বিশেষ চিন্তাভাবনা করা উচিত। তা না হলে বাংলায় বাণিজ্য করা কোম্পানির পক্ষে মোটেই লাভজনক হবে না।’
ইংরেজদের মধ্যে যে তিনজন চক্রান্তে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন উইলিয়াম ওয়াটস, লিউক স্ক্র্যাফ্টন ও রবার্ট ক্লাইভ।
ওয়াটস ছিলেন কাশিমবাজার কুঠির প্রধান। যেহেতু কাশিমবাজারের অনতিদূরেই রাজধানী মুর্শিদাবাদ, তাই তিনি নবাবের দরবারে ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধিও ছিলেন। ফলে, বাংলায় ইংরেজদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল দরবারের সব খোঁজখবর রাখার।
ইংরেজরা এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার আগে স্ক্র্যাফ্টন ঢাকায় ইংরেজ কুঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্লাইভই তাঁকে ঢাকা থেকে আনিয়ে মুর্শিদাবাদে পাঠান।
অন্য মূল ষড়যন্ত্ৰিকারী বণিকরাজাদের মধ্যে জগৎশেঠদের মূল আস্তানা ছিল মুর্শিদাবাদে; অন্য দু’জনের মধ্যে উমিচাঁদের কলকাতা আর আর্মানি বণিক খোজা ওয়াজিদের হুগলি। বাংলার টাকার বাজার ছিল এঁদেরই হাতে এবং এঁরাই একদিকে শিল্পবাণিজ্য ও অন্যদিকে নবাব সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতেন।
এই বণিকরাজাদের মধ্যে সবদিক থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন জগৎশেঠরা। এঁদের বলা হয় ‘Rothchilds of the East’। রাজস্থানের মারওয়ার অঞ্চলের নাগর থেকে এঁদের পূর্বপুরুষ হীরানন্দ শাহু ভাগ্যান্বেষণে ১৬৫২ সালে পাটনা চলে আসেন। তাঁর সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ মানিকচাঁদ তখনকার বাংলার রাজধানী ঢাকায় এসে মহাজনি ব্যবসা শুরু করেন। এঁরা ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। ঢাকায় মানিকচাঁদের সঙ্গে নবাগত দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মুর্শিদকুলি যখন বাংলার তৎকালীন সুবাদার আজিম-উস-শানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ১৭০৪ সালে দেওয়ানি দফতর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন, তখন তার সঙ্গে মানিকচাঁদও ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। তখন থেকেই মুর্শিদকুলির আনুকূল্যে জগৎশেঠদের উন্নতির শুরু—তাঁদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁদের রমরমা এই মানিকচাঁদ ও তার উত্তরসূরী ফতোচাঁদের সময়। ১৭১৪ সালে মানিকচাঁদের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর ভাগ্নে ফতেচাঁদ গদিতে বসেন। ফতেচাঁদের সময়ই জগৎশেঠরা প্রভাব ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। সম্ভবত মুর্শিদকুলির অনুরোধে মুঘল সম্রাট ১৭২২ সালে ফতেচাঁদকে ‘জগৎশেঠ’ (Banker of the World) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি বংশানুক্রমিক।
বাংলায় জগৎশেঠদের বিপুল আয়, প্রচও ক্ষমতা ও বিশেষ মর্যাদার কতগুলো উৎস ছিল। সেগুলি হল: মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির প্রায় একচ্ছত্র অধিকার, বাংলার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ জমা নেওয়ার অনুমোদন, মুদ্রা বিনিময়ের হার ধার্য করার ক্ষমতা ও সুদে টাকা ধার দেওয়ার মহাজনি ব্যবসা।
ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বাংলার রফতানি পণ্য কেনার জন্য ইউরোপ থেকে যেসব সোনা-রুপো নিয়ে আসত (প্রায় সবটাই রুপো) সেগুলোর বেশিরভাগই জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করতে হত কারণ এগুলোর বিনিময়ে তাদের স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত এবং তা দিয়েই রফতানি পণ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত। আর যেহেতু জগৎশেঠদের হাতেই টাঁকশালের কর্তৃত্ব, তাদের আমদানি করা রুপো জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করা ছাড়া কোনও উপায় তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, জগৎশেঠরা যে দাম দিতেন, সেটাই তাদের নিতে হত। বলা বাহুল্য সে দাম বাজারের দামের চেয়ে কমই হত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পক্ষে এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হত কারণ তারা এ দেশে পণ্য কেনার জন্য যে রুপো নিয়ে আসত, জগৎশেঠদের ছলচাতুরির জন্য তারা সেগুলি দিয়ে টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি করতে পারত না। অথচ দাদনি বণিকদের মাধ্যমে রফতানি পণ্য সংগ্রহ করার জন্য তাদের নগদ টাকার খুবই প্রয়োজন হত।
জগৎশেঠদের প্রভূত আয়ের আরেকটি বড় উৎস ছিল বিভিন্ন রকমের মুদ্রার বিনিময়ের হার বা বাট্টা ধার্য করার অধিকার। এ সময় বাংলায় নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্নরকমের মুদ্রা আসত, বাংলায়ও ছিল নানা রকমের মুদ্রা। বাজারে কিন্তু এসব চলত না। সব রকমের মুদ্রাকেই সিক্কা টাকায় পরিবর্তিত করতে হত—এ জন্য দিতে হত বাট্টা। এ বাট্টার হার ঠিক করত জগৎশেঠরা, তাঁদের লাভের অঙ্ক মাথায় রেখে। ফলে বাট্টা থেকেও তাঁদের প্রচুর লাভ হত। জগৎশেঠরা পুরনো বা অন্য প্রান্ত থেকে আসা সব মুদ্রা টাঁকশালে পাঠিয়ে নতুন চলতি মুদ্রায় (সিক্কা) পরিবর্তিত করতেন আর এই মুদ্রা পরিবর্তন করার জন্য তাঁরা বাট্টা নিতেন।
জগৎশেঠদের বার্ষিক আয়ের আরেকটি সোজা রাস্তা ছিল চড়া সুদের মহাজনি ব্যবসা। তারা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে টাকা ধার দিতেন। ১৭১৮ থেকে ১৭৩০ সালের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠদের কাছ থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার মতো ধার করেছিল। আর ১৭৫৫ থেকে ১৭৫৭, এই তিন বছরে জগৎশেঠদের কাছ থেকে ডাচ কোম্পানি ২৪ লক্ষ টাকা ধার করেছিল। ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসে যখন ইংরেজদের কাছে চন্দননগরের পতন হল, তখন শেঠদের কাছে ফরাসিদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।
দ্বিতীয় বণিকরাজা উমিচাঁদ বা আমিরচাঁদ। উত্তর ভারত, সম্ভবত আগ্রা থেকে তিনি বাংলায় আসেন ১৭২০-র দশকে এবং কলকাতার বিশিষ্ট দাদনি বণিক ও ইংরেজ কোম্পানির ‘ব্রোকার’ বিষ্ণুদাস শেঠের অধীনে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। ১৭৩০-র দশকের প্রায় প্রথম দিক থেকেই তিনি নিজেকে কলকাতার একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের দুই প্রধান ক্ষেত্র ছিল কলকাতা ও পাটনা। তার কাজকারবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কলকাতায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে, বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানিকে পণ্য সরবরাহ, মহাজনি কারবার এবং অন্তর্বাণিজ্য আর বিহারে সোরা ও আফিং-এর ব্যবসা। তাঁর ভাই দীপচাঁদ বিহারে সোরা [saltpeter] উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র ‘সরকার’ শরণের ফৌজদারি চালাতেন। ইংরেজ কোম্পানিকে সোরা সরবরাহকারীদের অন্যতম প্রধান ছিলেন তিনি। তিনি ও তাঁর ভাই মিলে বিহার প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সোরার প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা কুক্ষিগত করেছিলেন।
সপ্তদশ শতক থেকেই আর্মানিরা বাংলায় বিদেশি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম। তারা যে-সব পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করত, তার মধ্যে অন্যতম বস্ত্র ও কাঁচা রেশম। তাই কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি অন্তত মধ্য-সপ্তদশ শতক থেকেই। মুর্শিদাবাদের সৈয়দাবাদে এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল কারণ এরাও জানত যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাফল্যের জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারের আনুকূল্য একান্তভাবে প্রয়োজন। সৈয়দাবাদে প্রথম আর্মানি গির্জা স্থাপিত হয় ১৬৬৫ সালে— তার ধ্বংসাবশেষের পাশে ১৭৫৮ সালে তাদের নতুন গির্জা তৈরি হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দির দাক্ষিণ্যেই তৃতীয় বণিকরাজা - খোজা ওয়াজিদ বিহার অর্থনীতির অনেকটাই কুক্ষিগত করতে সমর্থ হন—বিহারে দু’টি প্রধান রফতানি পণ্য, সোরা ও আফিং-এর একচেটিয়া ব্যবসা তিনি নিজের করায়ত্ত করেন ১৭৪০-র শেষ দিক থেকে। ১৭৫৩ সালে তিনি আলিবর্দির কাছ থেকে বিহারে সোরার একচেটিয়া ব্যবসা করার ইজারা পান। তার আগের বছর তিনি নবাবকে ২৫ বা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে লবণের ব্যবসার ইজারাও নেন।
ওয়াজিদের অন্তত ৬টি বাণিজ্যতরী ছিল। এগুলির মাধ্যমে তিনি তখনকার বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর হুগলির সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর জাহাজগুলি হুগলি থেকে বিভিন্ন পণ্যসম্ভার নিয়ে জেড্ডা (Jedda), মোখা (Mokha), বসরা (Basra), সুরাট, মসুলিপট্টনম প্রভৃতি বন্দরে বাণিজ্য করতে যেত। জাহাজগুলির নাম—‘সালামত রেসান’, ‘মোবারক’, ‘গেনজামের’, ‘মদিনা বক্স’, ‘সালামত মঞ্জিল’ ও ‘মুবারক মঞ্জিল’। ডাচ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুম ও ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের লেখা থেকে জানা যায় যে সুরাটে ওয়াজিদের একটি বাণিজ্য কুঠিও ছিল।
ইংরেজ ও ফরাসিরা উভয়েই তাদের সাধ্যমতো দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উৎকোচ দিয়ে নিজেদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জাঁ ল’-র অর্থবল তেমন ছিল না, ফলে তিনি শুধু এমন সব ব্যক্তিদের হাত করতে পেরেছিলেন যাদের সম্বন্ধে ইংরেজদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এরা ফরাসিদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করেছিল। অন্যদিকে ইংরেজরা প্রচুর টাকাপয়সার জোরে ও উমিচাঁদের সহায়তায় মুর্শিদাবাদ দরবারে ফরাসিদের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল - “করমণ্ডল উপকূলে আমাদের ও ফরাসিদের কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নবাবকে বোঝাতে হবে ফরাসিরা কীভাবে নিজাম বাহাদুর সালাবৎ জঙ্গের হাত থেকে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে পুরোপুরি ক্রীড়নক বানিয়েছে…. তা ছাড়া নবাবকে আশ্বস্ত করতে হবে যে আমরা সর্বদা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করব। বিনিময়ে আমরা শুধু চাইব যে, আমাদের সঙ্গে নবাবের যে চুক্তি তা তিনি মেনে চলবেন এবং আমাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দেবেন।”
উমিচাঁদের নিজের স্বার্থই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন যে বিপ্লবের পরে নবাবের ধনদৌলতের একাংশ যাতে তিনি আত্মসাৎ করতে পারেন। তিনি ওয়াটসকে জানালেন যে বিপ্লবের পর নবাবের ধনসম্পদের পাঁচ শতাংশ তাঁকে দিতে হবে। ওয়াটসের ধারণা এর পরিমাণ দাঁড়াবে দুই কোটি টাকা। মুর্শিদাবাদের রাজকোষে তখন চল্লিশ কোটি টাকা ছিল বলে অনুমান করা হয়, যদিও এটা নেহাতই অতিরঞ্জন৷ আবার রায়দুর্লভকে নিজের দলে টানার জন্য উমিচাঁদ দাবি করলেন যে, রায়দুর্লভকেও মীরজাফরের ভাগ থেকে কিছুটা দিতে হবে। এ-সব দেখে ওয়াটস, যিনি এতদিন উমিচাঁদের কাজকর্ম ও সাহায্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, এখন ক্লাইভকে লিখে পাঠালেন: ‘উমিচাঁদের এ-সব দাবির মধ্যে তাঁর উচ্চাভিলাষ, ধূর্ততা ও অর্থলোলুপতার নগ্নরূপ বেরিয়ে পড়ছে। তিনি সব দাবিগুলিই বজায় রাখতে চান, একটি দাবিও ছাড়তে রাজি নন।’
মীরজাফরও ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মধ্যে উমিচাঁদের প্রাপ্য সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ থাকুক তা একেবারেই চাননি এবং তাতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। জগৎশেঠরাও ওয়াটসকে জানিয়েছিলেন মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তিতে যেন উমিচাঁদের কথা কিছু না থাকে। ১৭ মে সিলেক্ট কমিটির বৈঠক বসল উমিচাঁদের দাবি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং তাতে ঠিক হল যে, তাঁর ব্যবহারের জন্য শাস্তি ও অপমানই তাঁর প্রাপ্য, কোনও পুরস্কার নয়। কমিটি দুটি চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিল। দুটিতেই মীরজাফর এবং ইংরেজরা সই করবে তবে একটিতে (লাল কাগজ) উমিচাঁদের প্রাপ্যের উল্লেখ থাকবে কিন্তু অন্যটিতে (সাদা কাগজ) তা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হবে।
নন্দকুমারের বাবা পদ্মনাভ রায় নবাব আলিবর্দি খাঁ’র আমলে তিনটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণের সময় নন্দকুমার হুগলী থেকে ফরাসডাঙার দিকে এক পা বাড়ালেন না। ইংরেজরা বিনা বাধায় চন্দননগর দখল করল। নন্দকুমারের কাজেকর্মে ভারি খুশি হতে তাঁকে হাতে রাখবার জন্য ইংরেজরা হুগলীতে খবর পাঠাল, ‘গুলাব কে ফুল তাজা আছে।’ কিন্তু কার্যসিদ্ধি হবার আগে নন্দকুমার যাতে গোলাপ ফুল না শুঁকতে পান, ওয়াট্স্ সেই ব্যবস্থাও করে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারের কপালে হুগলীর ফৌজদারী লাভ হল না। নবাব নন্দকুমারকে সরিয়ে শেখ আমরুল্লাহ্কে হুগলী পাঠালেন। ওয়াট্স্ নির্বিকার চিত্তে ক্লাইভকে লিখলেন, নন্দকুমারকে সাহায্য করে আর কোনো লাভ নেই। হুগলীর কেল্লায় নন্দকুমার শুতে যাবার তোড়জোড় করছেন এমন সময় ইংরেজদের শিবির থেকে ক্লাইভের মুনশী নবকৃষ্ণ দেব [শোভাবাজার রাজবাড়ির ] এসে হাজির হলেন। মুনশীর মুখে নন্দকুমার শুনলেন, সাবিৎ জঙ্গ তাঁকে জরুরী তলব করেছেন।
চন্দননগরের পতনের পর সিরাজদ্দৌল্লা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। ১৭৫৭ সালের প্রথম দিক থেকেই আহমদ শাহ আবদালির নেতৃত্বে বাংলায় আফগান আক্রমণের আশঙ্কা তাঁর কাছে এক বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক করে হোক বা ভুল করে হোক, তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজদের চাইতে আফগানরাই তখন বড় বিপদ। তাই তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ অংশকে সম্ভাব্য আফগান আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজা রামনারায়ণের নেতৃত্বে বিহার সীমান্তে পাঠিয়ে দেন।
১৬ এপ্রিল মঁসিয় ল’ মুর্শিদাবাদের বড়ো রাস্তা দিয়ে পাটনার দিকে বের হয়ে গেলেন। মঁসিয় ল’ বিতাড়িত হওয়া মাত্র মোহনলাল ও মীর মদন ছাড়া নবাবের সত্যকার মিত্র আর কেউ রইল না। দরবারের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দেখে ইংরেজদের প্রতি যারা মৈত্রীভাবাপন্ন নয় তারাও ভয় পেয়ে নবাবের বিপক্ষে যোগ দিতে শুরু করল, এদের মধ্যে ছিলেন বণিকপ্রবর খোজা ওয়াজিদ।
ইংরেজদের ভাগ্যক্রমে সিরাজদ্দৌল্লাকে প্রতারিত করার আরেকটি সুযোগ তাদের হাতে এসে যায়। এটা দিয়ে তারা নবাবকে তাদের আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন হিসেবে দেখিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পেল। তারা ৯ বা ১০ মে নাগাদ মারাঠা পেশোয়া বালাজি রাও-এর কাছ থেকে মারাঠাদের সঙ্গে তাদের আঁতাতের প্রস্তাব নিয়ে একটি চিঠি পেল। বালাজি রাও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এক লক্ষ কুড়ি, হাজার মারাঠি অশ্বারোহী সৈন্য নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং কলকাতায় ইংরেজদের যা ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ তাদের দেওয়া হবে। ক্লাইভ প্রথমে ভাবলেন চিঠিটা জাল এবং এটা লিখে নবাব ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য যাচাই করতে চাইছেন। স্ক্র্যাফ্টন অবশ্য বলেছেন যে ক্লাইভ পত্রবাহকের সঙ্গে গোপনে একটা বৈঠক করেছিলেন। শেষপর্যন্ত ক্লাইভ এই চিঠিকে দুটো কাজে লাগাতে চাইলেন—প্রথম, ওয়াটসকে বললেন, মীরজাফরকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানাতে। তা হলে হয়তো মারাঠা আক্রমণের ভয়ে মীরজাফরও বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে বাধ্য হবেন। অন্যদিকে স্ক্র্যাফ্টনের মারফত চিঠিটা সিরাজদৌল্লাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে নবাব ইংরেজদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন।
ইংরেজরা হুগলী ছাড়িয়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড় বেয়ে কাটোয়া পর্যন্ত উঠে ১৯ জুন সেখানকার দুর্গ দখল করল। মীরজাফর যাতে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন তার জন্য একদিকে কী ধরনের প্রলোভন ও অন্যদিকে যে প্রচ্ছন্ন ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পলাশীর আগের রাতে ক্লাইভের চিঠিটি - “আপনাকে আমি সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করছি যে এটা করলে আপনি তিন প্রদেশেরই (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা] সুবাদার (নবাব) হবেন। কিন্তু আপনি যদি আমাদের সাহায্যার্থে এটুকুও না করেন তা হলে ভগবান আপনার সহায় হন। আমাদের কিন্তু পরে বিন্দুমাত্র দোষ দিতে পারবেন না।”
মোহনলালের অসুস্থতাও সিরাজের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দরবারে মোহনলালের শত্রুরা তাঁকে বিষপ্রয়োগ করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়। ল’ লিখছেন:
“মোহনলাল ছিলেন শেঠদের জাতশত্রু এবং তাঁদের সঙ্গে লড়াই করার পক্ষে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি। আমার ধারণা মোহনলাল সুস্থ থাকলে এই সওকাররা [জগৎশেঠরা] তাঁদের [বিপ্লবের] প্রকল্পে অত সহজে সফল হতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কিছুদিন ধরে এবং এই সংকটের মুহূর্তে মোহনলাল সাংঘাতিক অসুস্থ…. খুব সম্ভবত তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় সিরাজদৌল্লা তাঁর একমাত্র ভরসা থেকে বঞ্চিত হলেন।”
নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীতে সাঁ ফ্রে-র নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের মতো ফরাসিও ছিল। কামানের সংখ্যা ৪০টির মতো। ইংরেজদের ফৌজে ছিল এক হাজার ইউরোপীয়, দু’হাজার সেপাই, ৫০জন নৌসেনা আর ৮টি কামান। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর, রায় দুর্লভরাম ও ইয়ার লতিফ খানের নেতৃত্বে নবাবের সৈন্যবাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ একেবারে পুতুলের মতো নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নবাবের সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর অনুগত সেনাপতিরা—মোহনলাল, মীর মর্দান, খাজা আব্দুল হাদি এবং নবসিং হাজারী প্রভৃতি।
মুর্শিদাবাদ জয়ের পর শুধুমাত্র সোনা-রুপো নিয়ে নবাবের প্রাসাদে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা। ক্লাইভ লিখেছেন যে নবাবের কোষাগারে ঢুকে অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, সোনা ও হিরে-জহরত দুধারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এমনকী ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী লিউক স্ক্র্যাফ্টন ঠিক পলাশি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই, যখন মীরজাফর মসনদেও বসেননি, মন্তব্য করেছেন যে এখন ‘সারা বাংলা আমাদের হাতের মুঠোয়।’
তিনদিন তিনরাত অনাহারে পথ চলার পর রাজমহলের কাছে নৌকো থেকে নেমে সিরাজ দানশাহ নামে এক ফকিরের কাছে খাবার চাইতে গেলেন। সিরাজকে চিনতে পেরে দানশাহ তাঁকে মীরজাফরের জামাই মীরকাশিমের হাতে তুলে দেন। এরপর তাকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মীরজাফরের পুত্র মীরণের গুপ্তঘাতক মহম্মদি বেগ সিরাজকে হত্যা করেন। সিরাজের ছিন্নভিন্ন দেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদ শহরে ঘোরানো হয়। মৃতদেহ নবাব পরিবারের কাছে ঋণী এক বৃদ্ধ, মীর্জা জয়নাল আবেদিন বাকাওয়াল, সিরাজের মৃতদেহকে স্নান করিয়ে শবাধারে রেখে খোশবাগে আলিবর্দির সমাধির পাশে সমাধিস্থ করেন।
পলাশীর ষড়যন্ত্র সমাপন হল। এবার সুবাহ্ বাংলাএ যা শুরু হল তদানীন্তন ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাব্তাবায়ীর ভাষায় তার নাম ‘ইনকিলাব’, অথাৎ উলট-পালট—আক্ষরিক এবং অনিষ্টকর অর্থে ‘revolution’।

মীরজাফর মসনদ দখল করলে তাঁর পুত্র মীরণ আলিবর্দি পত্নী শরফুন্নেসা, তাঁর দুই কন্যা ঘসেটি ও আমিনা বেগম এবং সিরাজপত্নী লুৎফুন্নেসা ও তাঁর শিশুকন্যাকে বন্দি করে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। ঘসেটি ও আমিনাকে পদ্মায় সলিল সমাধি দেওয়া হয়। বাকিরা কোনওরকমে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের হস্তক্ষেপে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতে পারলেন। কিন্তু তাদের যে মাসোহারার ব্যবস্থা হল, তাতে জীবন নির্বাহ করা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। ১৭৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শরফুন্নেসাকে ইংরেজ গভর্নরের কাছে তাঁর ভাতা বৃদ্ধির জন্য আর্জি পাঠাতে দেখা যায়।
ক্লাইভ খুব উৎফুল্ল হয়ে ওয়াজিদের পতন বর্ণনা করেছেন: ‘আমি জানতাম যে নবাবের সঙ্গে আমাদের কলকাতায় যে সাম্প্রতিক ঝামেলাটা হয়েছিল তার প্রধান হোতা হচ্ছে ওই ‘রাসকেল’ ওয়াজিদটা। আবার আমাদের সঙ্গে ডাচদের বিরোধ বাঁধাতে সে এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি ভাবলাম তাকে হাতকড়া পরানো দরকার যাতে সে ভবিষ্যতে মহামান্য নবাব [মীরজাফর], আপনি [মীরণ] এবং আমার [ক্লাইভ] মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে তা যেন ভাঙতে না পারে।’ ওয়াজিদকে ধরে জেলে পোরা হল। সেখানে তিনি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।
প্রায় তিরিশ বছর ধরে বাংলার বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব বিস্তার করে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ১৭৪৪ সালে মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর দুই পৌত্র জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচাঁদ। ১৭৬৩ সালে মীরকাসিমের আদেশে গঙ্গাবক্ষে তাঁদের সলিল সমাধি হয়।
পলাশির পরে ইউরোপ ও ইংল্যান্ড থেকে রুপো ও নগদ টাকাপয়সা আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে ইংরেজ কোম্পানি মাছের তেলে মাছ ভাজা শুরু করল। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলায় বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল—বাংলার রাজস্ব, নানা উপঢৌকন, উপহার ও ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে। আর এই অর্থ দিয়েই ইংল্যান্ডে রফতানির জন্য বাংলায় পণ্যসংগ্রহ করতে শুরু করল। ইংল্যান্ড ও ইউরোপ থেকে আর সোনা-রুপো আনার কোনও প্রয়োজনই হল না। ফলে, এতদিন ধরে বাংলার উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে বাংলায় যে অজস্র সম্পদ, সোনা-রুপো আসত, তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।
কোম্পানির কর্মচারীদের আয়ের সবচেয়ে লোভনীয় উৎস ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসা। তারা বেপরোয়াভাবে যে বিশাল পরিমাণ অন্তর্বাণিজ্য করতে শুরু করল তা এর আগে কোথাও দেখা যায়নি। মুর্শিদাবাদ দরবারের ইংরেজ প্রতিনিধি সাইকস (Sykes) মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলায় সোরা, কাঠ ও রেশমের একচেটিয়া ব্যবসা করে দু’বছরে ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন প্রতি বছরে। আরেকজন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস (William Bolts) ব্যক্তিগত ব্যবসা করে ৬ বছরে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জমিয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা এভাবে যে পরিমাণ টাকাপয়সা উপার্জন করত তার প্রায় সবটাই বিলস অব এক্সচেঞ্জ (Bills of Exchange) বা হুণ্ডির মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে পাঠিয়ে দিত। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারি কমিটির একটি অনুমান অনুযায়ী কোম্পানির কর্মচারীরা পলাশি বিপ্লবের পর এক দশকে ইংরেজ ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ওপর হুণ্ডির মাধ্যমে প্রতি বছর ৮০ লক্ষ টাকা ইংল্যান্ড ও ইউরোপে পাঠিয়েছিল।
ইংরেজ কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (যিনি পরে বাংলার গভর্নরও হয়েছিলেন) ভেরেলস্ট (Verelst) মন্তব্য করেছেন যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে বাংলায় সোনা-রুপো আসা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এখান থেকে ধনসম্পদ বাইরে চলে যাওয়া—এই দুটো মিলে বাংলার ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার লোকসান হয়। একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পলাশির পর এক দশকে বাংলা থেকে কোম্পানিগুলির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ইউরোপীয় ও ইংরেজদের হিরের চোরাচালান ও চিনদেশে রফতানি বাদ দিয়ে যে ধনসম্পদ বাইরে চলে যায় তার মূল্য হবে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বাংলার নবাবের কাছ থেকে যা টাকা পাওয়া গেছে ‘তার সবটাই শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে চলে এসেছে, কারণ বাংলায় যে টাকাটা পাওয়া গেছে তা দিয়ে চিন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ছাড়াও সারা ভারতবর্ষের বাণিজ্যই আমরা তিন বছর চালিয়েছি, ইংল্যান্ড থেকে এক আউন্স রুপোও নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়নি।’
পলাশির পরে ইংরেজ কোম্পানি ও তাদের কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যে এশীয়/ভারতীয় বণিকরা বাংলার রেশমের বাজার থেকে প্রায় উৎখাত হয়ে যায়। তাদের রেশম রফতানির পরিমাণও প্রায় তলানিতে এসে ঠেকে। নবাবি আমলে তাঁতিদের এতটা স্বাধীনতা ছিল যে, তারা ইচ্ছেমতো কাপড় তৈরি করতে পারত এবং তারা এই কাপড় তাদের ইচ্ছেমতো যে-কোনও ক্রেতাকে বিক্রি করতে পারত। কিন্তু পলাশির পর তাদের এই স্বাধীনতা পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।এদের এখন একেকজন নির্দিষ্ট গোমস্তার কাছে নাম লেখাতে বাধ্য করা হল। একজন তাঁতি যে গোমস্তার কাছে নাম লেখাতে বাধ্য হল, সে সেই গোমস্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য কাপড় বুনতে পারবে না, এ নিয়ম চালু হল। আবার এক গোমস্তার খাতায় নাম লেখানো তাঁতিকে অন্য গোমস্তার কাছে ‘ক্রীতদাসের’ মতো ‘হাতবদল’ও করা হত।
কিছুদিন বাদেই বাংলায় দেখা দিল ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেসময়ের গ্রামের একজন লিপিকরের বক্তব্য এখনকার ভাষায় রূপান্তর করলে মর্ম বোধহয় এই দাঁড়ায়: সুখা বছরে কোনো বৃষ্টি না হওয়ায় গরিব লিপিকর পুঁথি লিখে দিনাতিপাত করল। দেবতা বিমুখ বলে বৃষ্টি পড়েনি। গাঁয়ে কোনো কাজ নেই যে লোকে খেটে খাবে। তাই গাঁয়ের গরিব লোকরা গৈতনপুর যেতে লাগল। কারণ চালের দাম চড়চড় করে টাকায় চব্বিশ সের দাঁড়িয়েছে। তাই মেলে না। গ্রামের অর্ধেক লোকের কোনো অন্ন নাই। এ দিকে দুর্ভিক্ষে যেসব জায়গায় অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়েছে সেখানকার লোক কাজের ধান্দায় এখানে এসে হাজির হল। গ্রামের যারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন গেরস্ত তারা ভিন্ গাঁয়ের লোকেদের কাজে বহাল করতে রাজি হল না। তারা বলে—এরা কোদালিয়া মজুর। এদের রাখতে গেলে ঘরের মাহিন্দরকে [গৃহস্থ পরিবারের ঘরের নানা কাজের সহায়ক] ছাড়তে হয়। তারপর যদি হঠাৎ কার্তিক মাসে বৃষ্টি পড়ে তবে ঐ লোক বলবে, ‘আমাদের দেশে জল হয়েছে। বাড়ি যাই চলরে। ক্ষেতে কাজ বসাতে হবে।’ তাই বাইরের মুনিষরা এখানে এসে কাজ পায় না। গাঁয়ে আর কোনো ধর্মকর্ম নেই। লোকজন এদিক ওদিক চলে যাওয়ায় গাঁ উজাড়। গাঁয়ের যে মোড়ল, সে খোসামুদে লোক,—খাজনা আদায় করে কর্তৃপক্ষকে খুশি রাখতে চায়। গাঁয়ে গাঁয়ে এরকম অনেক মণ্ডল আছে যাদের দৌরাত্ম্যে লোকের খুদকুঁড়ো জোটে না। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি গাঁয়ের এই দশা—গরিব লোকের যেটা সবচেয়ে কষ্টের সময়। এরই মধ্যে খবরদারি করতে এসে হাজির হয়েছে জমিদারের তহসিলদার তারাচাঁদ আর অধীনস্থ তালুকদার নারায়ণ পোদার। আর কি বলার আছে—পৌষ মাসে আমন ধানের জন্য জোরে লাগা ছাড়া গতি নেই। আবার ঠিক তখনি ফৌজদারের গোমস্তা নাগলি চাটুজ্যে আর এ অঞ্চলের গোমস্তা রূপণ নিয়োগী এসে জোর করে খাজনা আদায় করে কিছু বাকি রাখবে না। কারণ এইখানেই তাদের নাগালধরা সুয়ো সোহাগিনী মাণিক মণ্ডল গাঁয়ের মোড়ল হয়ে বসে আছে।
ফিরিঙ্গিদের সহায়তায় বহিরাগত ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার মগ , বর্গীদের মত কিংবদন্তী হল। উত্তরবঙ্গে ফকির , সন্ন্যাসী এবং অন্যন্য প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল। রংপুরে ফকির সন্ন্যাসীর প্রকোপের সঙ্গে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের প্রাবল্য যুক্ত হল। বিশেষ করে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী এই দুই ডাকাতের নাম শোনা যেতে লাগল। মজনু শাহের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল, আবার ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবী চৌধুরানী যুক্ত ছিলেন। দেবী চৌধুরানী বেতনভুক বরকন্দাজসহ নদীবক্ষে বজরায় থাকতেন। তাঁর নাম থেকে অনুমান হয় তিনি রংপুরের স্ত্রী জমিদার ছিলেন। ভবানী পাঠকের সঙ্গে তাঁর লুণ্ঠিত মালের বখরা থাকলেও তিনি স্বাধীনভাবে ডাকাতি করতেন। মন্বন্তরের পর উচ্ছন্ন ফেরারী প্রজারা এবং নবাব ও জমিদারদের বরখাস্ত নগদিয়ান সেপাইরা ডাকাত দলে যোগ দিয়েছিল। নাটোর রাজ্য জুড়ে পণ্ডিতা ও কার্তিকা নামে দুই ভয়ংকর ডাকাত বহু দিন ধরে প্রজাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।
পলাশির পর থেকেই মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমতে থাকে। সিরাজদ্দৌল্লার পর মীরজাফর নতুন নবাব হলেও ইংরেজদের হাতের পুতুলমাত্র। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম নবাব হয়ে মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ১৭৬৩-তে মীরজাফর আবার নবাব হন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি পেল। ১৭৬৬ সালে ক্লাইভ দেওয়ান হয়ে মুর্শিদাবাদে পুণ্যাহ করলেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য দেওয়ানি ও খালসার সব বিভাগগুলি কলকাতা নিয়ে গেলেন। ফলে মুর্শিদাবাদ থেকে বহু কর্মচারী কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হল। রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের যেটুকু গুরুত্ব ছিল, ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) পাশ হওয়ার পর কলকাতা ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সদর দফতর হওয়ায় তাও নষ্ট হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ১৭৯৯ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে বাংলার রাজধানী থেকে মুর্শিদাবাদ শুধুমাত্র একটি জেলাশহরে পরিণত হয়।
যে দুর্ভিক্ষে ফুলী জেলেনীরা না খেয়ে মরেছিল সেই দুর্ভিক্ষে রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদির রাজ্যপাটও উচ্ছন্নে গিয়েছিল। সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে বাঙালির প্রাণের যে কথাটা সাধক রামপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানের বালুশয্যায় তার সান্ধ্যকালীন অনুরণন রেখে গিয়েছিল তা এই :
মা, খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তা হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥
গ্রন্থ সূত্র -
নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ/ সুশীল চৌধুরী
পলাশির অজানা কাহিনী/ সুশীল চৌধুরী
পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ/ রজতকান্ত রায়
এছাড়াও মুর্শিদাবাদ নিয়ে পড়তে চাইলে -
কিসসা মুর্শিদাবাদী
বাংলার নবাবি কেল্লা ও কেল্লাবাসীর কিসসা
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনপত্তাদকাল - %%আরও পড়ুনবাদামি - %%আরও পড়ুনবিজাপুর - %%আরও পড়ুনহামপি - %%আরও পড়ুনবেলুর - %%আরও পড়ুনঅ্যান্টি-গল্প নিয়ে - পাপাঙ্গুলআরও পড়ুনভোগবাদের প্যারাডক্স - পাপাঙ্গুলআরও পড়ুনপ্রথম রেখা - albert banerjeeআরও পড়ুনবাংলাদেশ সমাচার! - ১৯ - bikarnaআরও পড়ুনহিন্দুস্কুলের দৈন্যদশা - দীপআরও পড়ুনইরান প্রশ্ন - Tirtho Dasguptaআরও পড়ুনতেঁনারা - Kishore Ghosalআরও পড়ুনগণভোটের বাংলাদেশ! - bikarnaআরও পড়ুনফলিবেই ফলিবে (২০২৬) - যদুবাবু
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
 হীরেন সিংহরায় | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৪:১৯733960
হীরেন সিংহরায় | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৪:১৯733960 - অসাধারণ । ফাইল করে রাখলাম।
 পাপাঙ্গুল | 2406:7400:98:d237:49c7:2bd5:5e30:***:*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৯:৫৫733970
পাপাঙ্গুল | 2406:7400:98:d237:49c7:2bd5:5e30:***:*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৯:৫৫733970- ধন্যবাদ হীরেনদা
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ)
(লিখছেন... Juin, Dr. Barnali Ray Basu, Bratin Das)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... MP, lcm, রঞ্জন)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Bratin Das, দ, দ)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত















