- বুলবুলভাজা আলোচনা সিনেমা

-
ইঙ্গমার বার্গম্যান – আত্মপ্রকাশের নানাবিধ পথ
শুভদীপ ঘোষ
আলোচনা | সিনেমা | ১৩ জুলাই ২০২৫ | ১৫৬২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৯ জন) 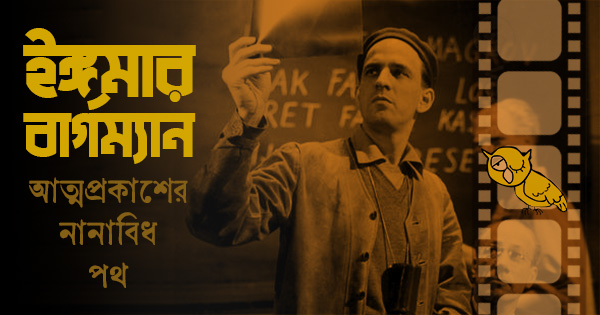
ছবি: রমিত
ভাষার শিল্পরূপ, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের আগে না পরে এই নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। সম্ভবত পরেই। কিন্তু শিল্পরূপ হিসেবে দেখা দেওয়ার পর এমনকি চিত্রকর চিত্রকলা নিয়ে কিংবা সঙ্গীতকার সঙ্গীত নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও যে ভাষার লিখিত রূপের আশ্রয়ই নিয়েছেন এ অনস্বীকার্য। জাঁ লুক গোদার একদা ঠিক করেছিলেন একটি চলচ্চিত্রকে ব্যাখ্যা করতে তিনি তৈরি করবেন আরেকটি চলচ্চিত্র। কেননা একটি সাহিত্যকে (ছোট গল্প, উপন্যাস বা নাটক) ব্যাখ্যা করতে আরেকটি সাহিত্য (প্রবন্ধ) হতে পারলে, এটা হবে না কেন? বলা-বাহুল্য এই প্রকল্প তিনি খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেন নি। এসব কথা উঠলো, চলচ্চিত্রকার হিসেবে প্রসিদ্ধ ইঙ্গমার বার্গম্যানের (১৪ই জুলাই ১৯১৮ – ৩০শে জুলাই ২০০৭) লেখক সত্তা নিয়ে কিছু লেখার অভিপ্রায় থেকে। ঐ যে বললাম, একজন চিত্রকর, একজন সঙ্গীতকার, একজন সাহিত্যিকের মত একজন চলচ্চিত্রকারেরও থাকে লেখক সত্তা। চিত্রনাট্য লেখার বাইরেও সে সত্তার উপস্থিতি থাকে, আত্মপ্রকাশের থাকে ভিন্নতর উদ্যোগ।
বার্গম্যানের কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল একজন নাট্যকার ও গদ্যলেখক হিসেবেই। কর্মজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, স্মৃতি-চারণা, নাটক এবং উপন্যাস-রূপে লিখিত চিত্রনাট্যের মাধ্যমে তিনি আবার পুরাদস্তুর লেখালেখিতে ফিরে আসেন। আত্মজৈবনিক ‘দা ম্যাজিক ল্যান্টার্ন’ গ্রন্থে নিজেই জানিয়েছিলেন, ৪২-র গ্রীষ্মে একদিন দেখলেন হঠাৎ বারোটি নাটক লিখে ফেলেছেন! এর মধ্যে দুটি নাটক ‘দা ডেথ অফ পাঞ্চ’ ও ‘তিভোলি’ , ৪২-৪৩ সালে স্টকহোমের স্টুডেন্ট থিয়েটারে নিজেই মঞ্চস্থ করেন। শুরুর দিকে লেখা নাটকগুলির মধ্যে খুব কমই যদিও পরে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বনিয়ার্স প্রকাশনা থেকে ৪৬ সালে তাঁর ‘জ্যাক এমং দা অ্যাক্টার্স’ প্রকাশিত হয় এবং ওখান থেকেই ‘মোরালিটেটার’ নামে তাঁর তিনটি নাটক, ‘র্যাকেল অ্যান্ড দা মুভি থিয়েটার ডোরম্যান’, ‘দা ডেজ এন্ডস আর্লি’ এবং ‘টু মাই টেরার’ প্রকাশিত হয়। ৫০ সাল নাগাদ তাঁর নাটকগুলি প্রকাশিত হওয়া মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায়। ৫১ সালে তাঁর ‘দা সিটি’ সভেনস্কা রেডিওপজের-এ রেডিও-নাটকের এন্থলজিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁর প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ‘দা সেভেন্থ সিল’-র অগ্রদূত হিসেবে ৫৪ সালে সভেনস্কা রেডিওপজের থেকেই সম্প্রচারিত হয় ‘পেইন্টিং অন উড’ নাটকটি। অন্য নাটকগুলি শুধুমাত্র তাঁর নিজের হাতেই দিনের আলো দেখেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল ৫২-য় মাল্ম মিউনিসিপাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়া ‘দা মার্ডার ইন বার্জানা’। শুরুর দিকের এই নাটকগুলির সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর চলচ্চিত্রের তুলনা চলে আসে। এটা ঠিক যে, শুরুর এই নাটকগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিটেল থেকে শুরু করে এগুলির সামগ্রিক ভাবনার পরিসরের সঙ্গে তাঁর সেসময়ে করা ছবিগুলির মিল পাওয়া যায়। আমরা যদি তাঁর নাটকের নাম গুলি একটু মন দিয়ে পড়ি তাহলে দেখব, ‘জ্যাক এমং দা অ্যাক্টার্স’, ‘র্যাকেল অ্যান্ড দা মুভি থিয়েটার ডোরম্যান’ ইত্যাদির মধ্যে ধরা পড়ছে চলচ্চিত্র ও নাটকের মত সমবেত চিত্তবিনোদন-মূলক মাধ্যমগুলির প্রতি তাঁর আসক্তি। তাঁর নিজের ছবি প্লট হিসেবেও ঠিক এই কারণেই প্রায়শই প্রতিভাত হয় চলচ্চিত্র, নাটক, সার্কাস বা অপেরা। প্রধান চরিত্ররাও অনেক ক্ষেত্রেই হয় চিত্রাভিনেতা, নয় নাট্যাভিনেতা, নয় সার্কাসের প্রধান বা অপেরার নৃত্যশিল্পী। বার্গম্যান কিন্তু একেবারেই ফেদেরিকো ফেলিনির (১৯২০-১৯৯৩) মত করে সার্কাস বা অপেরাকে দেখতেন না। সার্কাস বা অপেরার কার্নিভ্যাল-সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ফেলিনির যেরকম টান ছিল, বার্গম্যান সেখানে অনেক বেশি করে পারফর্মারদের অন্তরাত্মার গভীরে আলো ফেলার প্রয়াসী।
‘দা ডেথ অফ পাঞ্চ’-র প্রধান চরিত্র পাঞ্চের মধ্যে বার্গম্যানের অল্টার-ইগোর আভাস পাওয়া যায়। পাপেট শো বা মরিওনেত্তি (দড়ি দিয়ে বাঁধা পুতুলদের শো) ছিল এই প্রধান চরিত্রটির কাজ। বার্গম্যানের অনেক কম বয়স থেকে আগ্রহ ছিল এই সব শো নিয়ে। হেলসিংবর্গের মিনিসিপ্যাল থিয়েটারে থাকার সময় ‘ক্রিস ক্র্যাস ফ্যালিবম’ নামে তিনি যখন একটি ব্যঙ্গাত্মক revue লিখতেন, সে সময় ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতেন এই পাঞ্চ নামটি। জ্যাক, ৪৬ সালের ছবি ‘ক্রাইসিস’-র একটি চরিত্র। বার্গম্যান এই চরিত্রটি নিয়েছিলেন তাঁরই লেখা নাটক ‘জ্যাক এমং দা অ্যাক্টার্স’ থেকে। চতুর ও ভণ্ড জ্যাক, বার্গম্যান নিজেই বলেছেন তাঁর অল্টার ইগোর আরো কাছাকাছি! এরপর তাঁর আরেক আত্মপ্রতিকৃতি হিসেবে দেখা দেয় ‘জোয়াখিম ন্যাকেড'। এই নামেরই নাটকটি বনিয়ার্স প্রকাশনা সংস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদিও ৫৩ সালে বনিয়ার্স লিটেররা ম্যাগাসিন এই ‘জোয়াখিম ন্যাকেড’ থেকেই নেওয়া ‘দা স্টোরি অফ দা আইফেল টাওয়ার’ প্রকাশ করে। জোয়াখিম পূর্বে উল্লেখিত ‘দা সিটি’ নাটকেরও একটি চরিত্র ছিল। ‘দা ফিস, ফার্স ফর ফিল্ম’ নামে একটি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন যা কোনোদিনো ছবি হয়ে ওঠে নি, তাতেও ছিল এই জোয়াখিম! চিত্রনাট্যটি ৫০/৫১ সালে ‘বায়োগ্রাফব্লাডেট’ নামে একটি ফিল্ম জার্নালে প্রকাশিত হয়। তাঁর নাটকের অনেক অংশকে, অনেক চরিত্রকেই জায়গা দিয়েছেন নিজের ছবিতে। যেরকম র্যাকেল এবং তার প্রাক্তন প্রেমিকা কাজ্, অবিশ্বস্ততার থিমের পাশাপাশি এই দুটি চরিত্রকে তিনি ‘র্যাকেল অ্যান্ড দা মুভি থিয়েটার ডোরম্যান’ নাটক থেকে স্থান দিয়েছিলেন ৫২-য় নির্মিত এপিসোডিক চলচ্চিত্র ‘সিক্রেটস অফ ওমেন’ ছবিতে। এই নাটকটির যে রূপকধর্মীতা, যা একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় তাঁর চিরকালের প্রিয় বিষয় মানুষ, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, তা এই সময়ের নাটক ও চলচ্চিত্র উভয়েরই উপজীব্য। ৪৯-এ নির্মিত চলচ্চিত্র ‘প্রিজন’ বা ‘দা ডেভিলস ওয়ান্টন’। এই গোত্রের ছবিকে তৎকালীন সমালোচকরা বলেছিলেন ’৪০-র চলচ্চিত্রীয় নীতিশাস্ত্রধর্মী নাটক’, আসলে তারই আরো গভীর দার্শনিক প্রতিন্যাস ৫৭-র ‘দা সেভন্থ সিল’-কে কেন্দ্র করে বিখ্যাত গড ট্রিলজিতে (৬৩-তে নির্মিত বাকি দুটি ‘উইন্টার লাইট’ ও ‘দা সাইলেন্স’) সংঘবদ্ধ হয়। বস্তুত, মানুষ, ঈশ্বর ও শয়তান এই ত্রয়ীর ভাবনা থেকে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত সরে আসেননি।
নিজে নাটক লেখা অবশ্য কিছুকাল পড়ে বন্ধ করে দেন। এর মূল কারণ ছিল, খারাপ সমালোচনা! সমালোচকরা তাঁর চলচ্চিত্র-নির্দেশক ও নাট্য-নির্দেশক সত্তাকে যেরকম অচিরেই অনেক উপরে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু একইভাবে তাঁর নিজের লেখা নাটকগুলিকে কোনোদিনো সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করেন নি। তাঁর নাটক ‘টু মাই টেরার’ সম্পর্কে একজন সমালোচক যেরকম লিখেছিলেন, “বার্গম্যান ছাড়া যদি তাঁর কোনও নাটক অন্য কেউ নির্দেশনা দেয়, তাহলে সেই নাটকের আসল মানে হারিয়ে যাবে, আর চিত্রনাট্যগুলো হয়ে উঠবে কেবল ফালতু কাগজপত্র। নির্দেশক হিসেবে তিনি সত্যিই বিশাল প্রতিভাধর এবং সেই কারণেই তাঁর ভেতরের কবি প্রায়ই প্রলোভনে পড়ে নাটকগুলোকে অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়, যেখানে থাকে অগোছালো, সাময়িক খেয়ালের ভারে ভারাক্রান্ত কিছু দৃশ্য ও সংলাপ।”! বহু-বছর বাদে বার্গম্যান নিজেই জানিয়েছিলেন, এই ধরনের সমালোচনাই তাঁকে নাটক লেখা থেকে বিরত করেছিল। মাল্মতে থাকাকালীন সময় নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে জানান, “প্রতিবারই যখন আমার কোনও নাটক মঞ্চস্থ হতো, পড়তাম - আমি একজন খারাপ লেখক, কিন্তু ভালো নির্দেশক, যিনি মনে হয় যেন লেখককে বাঁচাতে এসেছেন! স্বাভাবিকভাবেই, এই কথা বারবার শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে পড়ি। যখন কেউ আপনাকে গালমন্দ শোনাতে বাধ্য করছে না, তখন স্বেচ্ছায় এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে ফেলার ইচ্ছেও আর থাকে না।”। তাঁর এই মনোভাব নব্বইয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত অটুট ছিল। ৯৩ সালে নিজের লেখা নাটক ‘দা লাস্ট স্ক্রিম’ (একক-অভিনয়) তিনি পুনরায় সুইডেনে মঞ্চস্থ করেন। তেইশ বছর আগে মাল্ময় তাঁর শেষ প্রোডাকশনের পর অবশ্য বিখ্যাত টিভি সিরিজ ‘সিনস ফ্রম অ্যা ম্যারেজ’-র নাট্যরূপ ৮১ সালে জার্মানির মিউনিখে মঞ্চস্থ হয়েছিল।
চিত্রনাট্যকার, নাট্যকারের পাশাপাশি তিনি একজন গদ্যকারও। বস্তুত, তাঁর শিল্পী-জীবনের শুরুর দিকে ৪০ সালে, ‘৪০-তাল’ নামক সুইডেনের একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকায় একটি গদ্য প্রকাশিত হয়! গদ্যটির নাম ছিল ‘এ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অফ ওয়ান অফ জ্যাক দা রিপার’স অ্যারলিয়েস্ট চাইল্ডহুড মেমোরিস’। এছাড়াও পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে বনিয়ার্স লিটেররা ম্যাগাসিন-এ প্রকাশিত ‘জোয়াখিম ন্যাকেড’ থেকে নেওয়া ‘দা স্টোরি অফ দা আইফেল টাওয়ার’-র কথা। সমালোচকদের কাছে তাঁর লেখা অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত সে ভাবে সমাদর পায় নি। এর একটা প্রধান কারণ, বার্গম্যান নিজেই তাঁর লেখা চিত্রনাট্যগুলিকে অর্ধ-সমাপ্ত হিসেবে দেগে দিয়ে সেগুলির আলাদা গুরুত্বকে ম্লান করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিনের গদ্যগুলি যদিও খুবই প্রণিধানযোগ্য ছিল। সেগুলোর মধ্যে তাঁর গঠন-পর্বটিকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। এই গঠন শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকার হিসেবে উঠে আসা নয়, চলচ্চিত্র নাটকের পিছনে যে সমৃদ্ধ একটি মন ক্রিয়াশীল, তার একটা আলেখ্য পাওয়া যায় এই গদ্যগুলির মধ্যে। মোটিফ ও স্টাইলের বিচারে লেখক বার্গম্যান তাঁর নির্দেশক সত্তার অনেক কাছাকাছি, সে চলচ্চিত্রই হোক বা নাটকই হোক। কখনো ছবি না হয়ে ওঠা ‘দা ফিস, ফার্স ফর ফিল্ম’-র চিত্রনাট্যে দেখা যায়, লেখক মন্তব্য করছে এবং সমালোচক সমালোচনা করছে এরকম ভঙ্গির অজস্র দৃশ্যের সমাহার। এর স্টাইলের সঙ্গে তাঁর শেষের দিকে লেখা (৯১-৯৪) চিত্রনাট্য/উপন্যাসগুলি যেরকম, ‘দা বেস্ট ইন্টেনশান্স’, ‘সানডেস চিলড্রেন’, ‘প্রাইভেট কনফেশন’ ও ‘ইন দা প্রেজেন্স অফ অ্যা ক্লাউনের’ মিল আছে। লেখা গুলি সাহিত্য হিসেবে পড়া হচ্ছে বা অভিনেতারা অভিনয়ের জন্য চিত্রনাট্যগুলি ভাল করে ঝালিয়ে নিচ্ছে, এটা যেন বিবেচ্য হয়। বিবেচ্য হল টেক্সটটা এমন ভাবে লেখা হবে যেন সেখানে দর্শকের সশরীর উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে! আরেকভাবে বললে, চলচ্চিত্র, নাটক ও সাহিত্যের নিজস্ব মাধ্যম-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে বার্গম্যানের পদ্ধতি প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তিনি যেন ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাঠক-দর্শককে স্থান দিয়ে একধরনের সেতুবন্ধ তৈরি করতে চেয়েছেন। বার্গম্যান সম্পর্কে ব্রেখটীয় শব্দটি প্রয়োগ করা যায় কিন্তু সেটা ডিসইলিউশনমেন্টের ধারণার বিপরীতে প্রয়োগ করতে হবে। বার্গম্যান উল্টে পাঠক-দর্শকের অবস্থানটিকে ব্যাবহার করেছেন চলচ্চিত্র নাটক ও সাহিত্যের কাঠামোগত তফাতের বিপরীতে একটা ইলিউশান তৈরির অভিপ্রায়ে। মার্কিন স্বাধীন চিত্রনির্মাতা জন ক্যাসাভেটস-র (১৯২৯-১৯৮৯) ছবিতে আমরা পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রবণতা দেখতে পাই।
স্পষ্ট বোঝা যায়, বার্গম্যানের সাহিত্যিক পুনরাগমন ছিল এক ধরনের হিসেব মেলানোর প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর অধিকাংশ সমৃদ্ধ সৃষ্টিকর্মেই দেখা যায় এক ধরনের সমাপ্তি বা পরিশেষের ব্যঞ্জনা, যেন জীবনের উপসংহার লিখে চলেছেন। ৮৪ সালের ‘আফটার দা রিহার্সাল’নাটকে তিনি যা ব্যক্ত করেন, ‘ফানি অ্যান্ড অ্যালেকজান্ডার’-এ তাই যেন ব্যক্ত হয় চলচ্চিত্রের ভাষায়! অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) ছিলেন বার্গম্যানের অত্যন্ত প্রিয় নাট্যকার। স্ট্রিন্ডবার্গের বহু নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেছেন। স্ট্রিন্ডবার্গীয় ঘরানার থিয়েটারের জাদু ও শিল্প বার্গম্যানের নির্দেশিত নাটকে এবং ছবিতে গভীর ছাপ ফেলে। এই স্ট্রিন্ডবার্গীয় ঘরানার প্রতিফলই দেখা যায় ‘আফটার দা রিহার্সাল’ ও ‘ফানি অ্যান্ড অ্যালেকজান্ডার’-এ। এক ধরনের উইল বা আত্মজবানী যেন, যার সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় ‘আফটার দা রিহার্সাল’ নাটকের চরিত্র নাট্য-নির্দেশক হেনরিক ফোগেল-র (এবং বার্গম্যান নিজেও বারবার যে কথাটি বলেছেন) সেই সংলাপে “সবকিছুই প্রতিনিধিত্ব করে, কিছুই নিজের মতো করে থাকে না।”। ৮৭ সালে প্রকাশিত আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘দা ম্যাজিক ল্যান্টার্ন’ এবং ৯০-এ ‘ইমেজেসঃ মাই লাইফ ইন ফিল্ম’, তাঁর জীবনের, কাজের ও ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক-কে তুলে ধরে। নিজের অহং-কে সততার সঙ্গে উন্মোচিত করতে তিনি কসুর করেন নি। তাঁর কাছে শিল্প ও নিজের জীবন সমার্থক ছিল। এই ব্যাপারটাই ঘুরে ফিরে এসেছে ‘দা বেস্ট ইন্টেনশান্স’ , ‘সানডেস চিলড্রেন’ ও ‘প্রাইভেট কনফেশন’-এ। এরই মধ্যে স্বতন্ত্র টেক্সট ‘দা ফিফথ অ্যাক্ট’-এ থিম হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত নাটক ও চলচ্চিত্রের জগতের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ‘দ্য লাস্ট স্ক্রিম’ নাটকটি নির্বাক ছবির পরিচালক আফ ক্লারকার ও প্রযোজক চার্লস ম্যাগনুসনের মধ্যকার সংঘাতকে কেন্দ্র করে তৈরি। বার্গম্যানের ছবিতে প্রতিফলিত অপমান, লাঞ্ছনার যে থিম, তা আবার ফিরে আসে। বলা-বাহুল্য এ তাঁর নিজের ইন্ডাস্ট্রি অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। ‘ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যা ক্লাউন’ নাটকটি শিল্পজীবনের ট্র্যাজিক ও একইসঙ্গে কমিক বাস্তবতার অঙ্গনে বিচরণ করে। একটি ব্যর্থ চলচ্চিত্র প্রকল্প একসময় রূপান্তরিত হয় অপেশাদার মঞ্চ-নাটকে। সেই মঞ্চের আড়ালেই ঘোরাফেরা করে বার্গম্যানের প্রিয় মৃত্যু, সাদা ক্লাউনের ছদ্মবেশে।
তাঁর সংকলন ‘দ্য ফিফথ অ্যাক্ট’ নামটি নেওয়া হয়েছিল ইবসেনের ‘পিয়ার গিন্ট’ নাটক থেকে (“You don't die in the middle of the fifth act”)। আবার ‘ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যা ক্লাউন’–র সুইডিশ শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় “That Struts and Frets” (যে হাঁটে আর হাহাকার করে)। যা একার্থে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের বিখ্যাত মনোলগকে স্মরণ করায় “…it is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing” (অঙ্ক ৫, দৃশ্য ৫)। শূন্য দশকেও তাঁর লেখালেখি চলতে থাকে। ২০০০ সালের শরতে তাঁর নতুন বই ‘পারফরম্যান্সেস’ প্রকাশিত হয়। এরই পাশাপাশি, নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের রেডিও নাটক ‘এ মেটার অফ দা সোল’ এবং দীর্ঘ চিত্রনাট্য ‘লাভ উইদাউট লাভার্স’ (যা তিনি কখনো ছবি করেন নি, যদিও এটি থেকে ২০০০ সালে লিভ উলম্যান ‘ফেইথলেস’ বলে একটি ছবি করেছিলেন) প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ চিত্রনাট্য ছিল ‘সারাব্যান্ড’। ২০০৩ সালে পঁচাশি বছর বয়সে এটি তিনি টিভির জন্য নির্দেশনা করেন। ‘সারাব্যান্ড’-কে তাঁর ৭৩ সালের বিশ্ব-বিখ্যাত টিভি সিরিজ ‘সিনস ফ্রম অ্যা ম্যারেজ’-র দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে দেখা হয়। যদিও মিলের জায়গাটি হল দুটি চরিত্র মারিয়ান ও জোহান তিরিশ বছরের ব্যবধানে পুনরায় মিলিত হয়েছে! কৌতূহল উদ্রেককারী ব্যাপার হল বার্গম্যান যখন ‘সারাব্যান্ড’ লিখছেন, সে সময়ই পরিকল্পনা করছেন শেষ নাটক হেনরিক ইবসনের ‘ঘোস্ট’ মঞ্চস্থ করার! দুটির মধ্যে কিছু অদ্ভুত মিল আছে। বিষয় হিসেবে অজাচার সম্পর্ক ও ইথানেশিয়া দুটিতেই প্রতিভাত হয়। ‘সারাব্যান্ড’-এ যদিও ইথানেশিয়ার ইঙ্গিতটুকু আছে। গুরুত্বপূর্ণ হল ‘সারাব্যান্ড’-র মারিয়ান ও জোহান-র মতই ‘ঘোস্ট’-র দুই প্রধান চরিত্রের একটা দীর্ঘ অতীত আছে। মৃত্যু আসন্ন, এই অনুভূতিটি অদৃশ্য ভরের মত ‘সারাব্যান্ড’ ছবির সারা শরীরে লেগে আছে। যারা ‘সারাব্যান্ড’ দেখেছেন তাঁরা জানেন যিনি তাঁর শৈল্পিক সিদ্ধির মধ্য-গগনে অবসর নিতে পারেন, একমাত্র তিনি পারেন ফিরে এসে এরকম একটি অন্তিম শিল্প উপহার দিতে। ২০০৪ সালের শরতে তিনি মেয়ে মারিয়া ভন রোসেনের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত ডাইরি প্রকাশ করেন। এই ডাইরিটি একজন মহত্তম শিল্পীর শেষ জীবনের ক্রম-অগ্রসরমান মৃত্যু ও মৃত্যু-ভাবনার দিনলিপি।
ঋণস্বীকারঃ- মারেট কস্কিনেনের বার্গম্যান সংক্রান্ত একটি গবেষণা পত্র।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
হীরেন সিংহরায় | ১৩ জুলাই ২০২৫ ১২:৩৫732403
- একটা অসামান্য জীবনকে সামান্য পরিসরে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন । ধন্যবাদ । যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ ইনজেমার বেয়ারিমান। সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহরের নাম মালমো বা মালমৌ!
-
Subhadeep Ghosh | ১৩ জুলাই ২০২৫ ১৫:৪৪732405
- হীরেনদা, দারুন আনন্দ পেলাম আপনার লেখাটি ভালো লেগেছে শুনে। আর আপনি তো জানেন, আপনার যে কোনো মতামত আমার শিরোধার্য। ❤️
 কল্যাণ | 223.223.***.*** | ১৫ জুলাই ২০২৫ ১৪:১৭732428
কল্যাণ | 223.223.***.*** | ১৫ জুলাই ২০২৫ ১৪:১৭732428- দারুন প্রবন্ধ। আপনার সিনেমা নিয়ে লেখাগুলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি।
-
Subhadeep Ghosh | ১৬ জুলাই ২০২৫ ১২:০১732439
- কল্যাণ - অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য। লেখার তো সবসময় চেষ্টা থাকে, কিন্তু সময়ে হয়ে ওঠে না। আবারও অনেক ধন্যবাদ।
-
Sumitra Dutta | ২০ জুলাই ২০২৫ ১৮:১৪732584
- খুব ভালো প্রবন্ধ। লেখককে অনেক ধন্যবাদ।
-
Subhadeep Ghosh | ২২ জুলাই ২০২৫ ১৪:৩১732604
- Sumitra Dutta - অনেক ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য।
-
smarita datta | ২৬ জুলাই ২০২৫ ২৩:৪৩732736
- আপনার লেখা পড়ে প্রত্যেকবার ঋদ্ধ হই। অনেক ধন্যবাদ।
-
Subhadeep Ghosh | ২৮ জুলাই ২০২৫ ২২:১১732803
- Smarita Datta - অনেক ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য।
-
সোমনাথ ঘোষ | ০৬ আগস্ট ২০২৫ ০৭:১১733034
- বার্গম্যানের এই দিকটি সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল। খুব ভালো লেখা।
-
Subhadeep Ghosh | ১১ আগস্ট ২০২৫ ০১:২০733192
- সোমনাথ ঘোষ - অনেক ধন্যবাদ তোমার মতামতের জন্য।
-
Tirtho Dasgupta | ২৪ আগস্ট ২০২৫ ১৬:২৩733607
- ভাল লেখা । তার এই নাটকের ব্যকগ্রাউন্ড টা জানতাম না । এই যে আপনি লিখেছেন যে তিনি তার জীবনকে সততার সাথে উন্মোচন করতেন শিল্পে সে বিষয়ে ঘটকের মত ছিল একেবারে উল্টো । ঘটক তার লেখায় চাছাছোলা মন্তব্য করেছেন বার্গমানকে নিয়ে । ঐ যে ক্রাইসিস সিনেমায় তিনি বলছেন যে চতুর ও ভন্ড জ্যাক তার অল্টার ইগোর কাছাকাছি ঘটকের মূল্যায়ণে বার্গম্যান সেরকমই । তিনি বরং বুনুয়েলকে অনেক বেশি পছন্দ করতেন তার শিল্পের সততার জন্য । এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন ?
-
Subhadeep Ghosh | ২৭ আগস্ট ২০২৫ ২২:০৯733683
- আপনার মতামতের জন্য অনেক ধন্যবাদ তীর্থবাবু।
অত্যন্ত ভালো একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন।
বার্গম্যান ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। বার্গম্যানের ঈশ্বর-ভাবনা তাঁর সৃষ্টিতে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বার্গম্যানের ঈশ্বর-ভাবনা মানে খৃষ্টীয় ধারায় যে ঈশ্বর, সেই নিয়ে ভাবনা। ফলত তাঁর ছবিতে বিবলিক্যাল বিভিন্ন চিহ্ন বর্তমান। ক্রস, খৃষ্টীয় মূর্তি, চার্চ ইত্যাদি তাঁর ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর ভাবনাটা নিছক ঈশ্বর ভক্তির জায়গায় থাকেনি। তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত নানাবিধ দার্শনিক অবস্থানের মধ্যে ঘুরে বেরিয়েছে। অন্যদিকে পরাবাস্তব্বাদী ও ক্রমে মার্ক্সবাদী বুনুয়েলের কাছে ঈশ্বর ব্যাপারটাই পরিত্যাজ্য। নাস্তিক বুনুয়েলের কাছে চার্চ, খৃষ্টধর্ম ও ঈশ্বর আসলে সামাজিক ডিস্প্যারিটি ও এক্সপয়টেশনকে বজায় রাখার একটা সুচারু কৌশল ছাড়া কিছু নয়। যা মানুষকে বোকা বানায়। ফেলিনিও অনেকটা এরকমই ভাবতেন। ফলত, মার্ক্সবাদী ঋত্বিক ঘটকের কাছে বার্গম্যান ভন্ড এবং বুনুয়েল সৎ। এই ভণ্ডামি ও সততার ব্যাপারটা একজন শিল্পীর যে জীবন ও দর্শন ভাবনা, যে অবস্থান, সেই জায়গা থেকে ঘটক বলেছিলেন বলে মনে হয়। ঘটক মনে করেছিলেন বার্গম্যানের ছবির বিবলিক্যাল চিহ্নগুলি মার্ক্সীয় অর্থে প্রগতি বিরোধী। মানে তাঁর মার্ক্সীয় আদর্শের জায়গা থেকে এটা মনে হয়েছিল বলে মনে হয়। বুনুয়েলে স্বভাবতই যেটা তিনি পাননি।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় , গুরুর রোবট)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... শ্রীমল্লার বলছি)
(লিখছেন... বক্তব্য, &/, প্যালারাম)
(লিখছেন... lcm, Bratin Das, সেই এক)
(লিখছেন... শান্তির দূত)
(লিখছেন... পৌলমী , AVIJIT CHAKRABORTY , Somnath mukhopadhyay)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... aranya, রঞ্জন, Bratin Das)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, বোদাগু, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।















