- বুলবুলভাজা ঘোষণা লেখালিখি

-
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
গুরুচণ্ডা৯
ঘোষণা | লেখালিখি | ০৯ জুলাই ২০২৫ | ৭৮২ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) 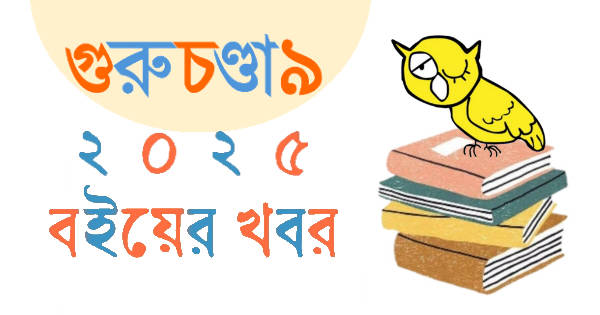 সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বহু পাঠকের কাছেই পরিচিত। টিভির দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও তাঁর অনেক গুণগ্রাহী আছেন, এবং আছেন সমালোচক থেকে অপছন্দ করা লোকেরাও। তাঁর লেখা পছন্দ করা আর না-করা নিয়ে এই গুরুচণ্ডা৯-র পাতাতেই বিতর্ক হয়েছে কোনো অতীতে।
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বহু পাঠকের কাছেই পরিচিত। টিভির দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও তাঁর অনেক গুণগ্রাহী আছেন, এবং আছেন সমালোচক থেকে অপছন্দ করা লোকেরাও। তাঁর লেখা পছন্দ করা আর না-করা নিয়ে এই গুরুচণ্ডা৯-র পাতাতেই বিতর্ক হয়েছে কোনো অতীতে।
ওনার এই বইটি নিয়ে কিছু লেখার আগে এর সূচিপত্রটি দেখে নেওয়া যাক।
আখ্যানের ঘুরপথ: দেবেশ রায়
জর্জ ফ্লয়েডের অবিস্মরণীয় হত্যা
সাহিত্যের বাজারদর: সমরেশ বসু
ঋত্বিকের নিসর্গ নিসর্গের ঋত্বিক
বাঙালির মাঝারিয়ানা
সংশোধিত ভূমিকালিপি
একা, নিজের মুদ্রাদোষে
অসময়ের আগন্তুক: সমর সেন
ঈশ্বরের অতিশয়োক্তি: মারাদোনা
সাদা-কালোর মায়া
পলাতকদের ডায়েরি
অপরাধের মাধুর্য
হারানো সুর: সিনেমা পত্রিকা
দীনেশচন্দ্র সেন: ভাষাতীর্থের যাত্রী
বিশ্বকর্মা পুজোর গোপনকথা
কাহিনির জাবদা খাতা
বৈশাখের কালীঘাট
ছবি-কবিতার সংলাপ: পূর্ণেন্দু পত্রী
করুণ রঙিন পথ: শঙ্খ ঘোষ
অয়ি মদিরেক্ষণা: কবিতা ও বিনয় মজুমদার
ব্যোমকেশচরিতমানস
চলচ্চিত্র, কবিতা ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
অধিরথ সূতপুত্র: রাজেন তরফদার
উত্তমচরিতমানস
সুচিত্রা সেন: মায়াবনবিহারিণী
খররৌদ্রের নায়িকা: সুপ্রিয়া চৌধুরী
অনিল উপমারহিত
বাংলা ছায়াছবি: আদিপর্ব
বাংলা ছায়াছবি: আদিপর্বের আদিযুগ
আয়নায় দেবকীকুমার
বাংলা ছায়াছবির ঘরকন্না
সিনেমার পালাবদল
সিনেমা বোঝার ধারাপাত
মধ্যবিত্তের গেরস্থালি: তপন সিংহ
বীরেন সরকারের বিষয়-আশয়
গোদার পরিচয়: প্রথম অধ্যায়
পাণ্ডুলিপি বনাম আইটেম সং
৩৭টি প্রবন্ধ জুড়ে এ বইয়ে লেখকের বিচরণ। শিরোনামগুলির প্রতিটি একাই যেখানে একাধিক প্রবন্ধের সম্মিলিত বিস্তৃতি নিলে অবাক হওয়ার নয় সেখানে একটি করে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে লেখক যা করেছেন তা মূলত পাঠকের মনে বিভিন্ন চিন্তাকে উস্কে দেওয়া। তাকে বিভিন্ন সম্ভবপরতার রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছে দেওয়া। নিজস্ব সরস ভঙ্গিতে সঞ্জয় সেটি করেছেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। কখনও তা ফুটে উঠছে আমাদের চেতনার রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের ক্যানভাসে আবার কখনও ঘুরে বেড়ায় চলচ্চিত্রের সাদায়-কালোয়, রুপালি পর্দার মিথ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার রহস্য অনুসন্ধানে।
মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা নিয়ে লেখা প্রবন্ধে তিনি বলেন
"সুতরাং জর্জ ফ্লয়েড যিনি কিনা কলসেন্টারে, শপিংমলে, পোস্টারে, রেলপথে আর ওয়াশরুমে স্বপ্ন দেখেছিলেন নদী হওয়ার আর নদীর মতো ঘুমোবার, তিনি থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো পুলিশগাড়ির তলায় পড়ে রইলেন। হায়! এক অজ্ঞ চিতাবাঘ ঢুকে পড়েছিল সাদা মানুষের অরণ্যে। যেমন বেঞ্জামিন মলোয়াজ। যেমন প্যাট্রিস লুলুম্বা। ওয়াল স্ট্রিটে, হাডসন নদীর পাশে, ব্রডওয়েতে, টাইমস স্কোয়ারে মানুষ তখন দেখছিল টাকার নিষ্ঠুর নাচ যা সন্তানকে শেখায় মায়ের শবদেহের কাছে ক্ষুধার অন্ন চাইতে। আর টাইমস স্কোয়ারে এক কাঙালিনী তার সকল নিয়ে বসে থাকে সর্বনাশের আশায়।
জর্জ ফ্লয়েড অতশত জানতেন না। তিনি জানতেন না করোনা ও চর্মকুষ্ঠের চাইতেও, খনিমজুরদের চাইতেও আতঙ্কের হল তাঁর চামড়ার রং। এই সেই সাংকেতিক প্যালেট যা মানুষকে স্বর্গাভিযানের গান শোনায়। এই সেই শরীর যা লম্বা লাফ দেয়, পোলভল্টে ছিটকে পড়ে আর দৌড়োয়। এই সেই মানুষের অবয়ব যে জ্বলতে দেখে হার্লেম কিন্তু যে কদাপি সমুদ্রস্নানে যায় না স্বর্ণকেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে। তাঁর জন্য দুটি মহাদেশ অবরুদ্ধ, মুক্ত শুধু পাহাড় চিরতে থাকা টানেল, গলা চিরতে থাকা গান আর কবরখানা থেকে উড়ে নক্ষত্রলোকে লুকিয়ে থাকার গুহা।
"
প্রবন্ধটি যেভাবে সমাপ্ত হয় -
"আপনার স্মরণে RIP বলব না। বাঙালি বুদ্ধিজীবী রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতোই। কুড়ি বছর ঘুমিয়ে থাকার পর আবার তারা বর্ণবৈষম্য বিষয়ে গবেষণা শুরু করবেন ফর্সা দুধে আলতা রঙের বউ-বরের প্ররোচনায়। বিদায় ফ্লয়েড। আপনি গ্যাস স্টেশন থেকে আরও তেল ছড়িয়ে দিন চারিদিকে। তেলই আগুন নিভিয়ে দেওয়ার সেরা উপায়।"
সমর সেনকে নিয়ে লেখায় তিনি বলেন
"এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে বলা যায়, সমরবাবুই আমাদের কবিতায় প্রথম স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বুর্জোয়া সভ্যতার জীব। যেজন্য তিনি আমাদের চিরঋণী করে রেখে যান তা হল, বাংলা কবিতার সেই রবীন্দ্রনাথ আচ্ছন্ন সুনিশ্চিত শান্তিনিকেতনে, শস্যশ্যামল সেই ফিউডালতন্ত্রে গতিসুদ্ধ শাহরিক জলবায়ুর প্রবর্তনে সফল হয়েছিলেন সমর সেন। আজ প্রায় আশি বছরের ব্যবধানে এই সাফল্যটুকু বিস্মরণযোগ্য মনে হতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ধারণা থাকলে শ্রদ্ধায় নত হওয়া ছাড়া পথ থাকে না।
অবশ্যমান্য ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের পরিশীলনের অভাব থাকলেও সাংবাদিকতার ধর্ম সুমুদ্রিত ছিল। তবু আর্থ-সামাজিক কারণেই তাঁরা শ্লথগতি, নিছক কৌতুকপরায়ণ ও চারুত্বে আস্থাশীল। অপরদিকে পুঁজিবাদী দাঁতচাপা সেই বৃদ্ধা গণিকা সমরবাবুর ধাত্রী বলেই তাঁর রচনা বেগবান, ধারালো। আক্রমণোদ্যত এবং অবদমিত আবেগের ভাস্কর্য। কারেন্সি সভ্যতার তিক্ততা ও অবিশ্বাস, ক্রোধ ও বিদ্রূপ, আর্তি ও অস্বীকার তাঁর বিশ্বস্ত সহচর বলেই সমর সেনের ভাষা, উপমা এবং সদর্থে কাব্যরীতিতে অপরিচয়ের জগৎ খুলে দেয়।"
ব্যোমকেশচরিতমানসে লেখেন
"প্যারিস কীরকম ছিল বোদলেয়ারের সময়? শিকড়শূন্য এক জনসমাজ যারা গৃহস্থ নয়, যারা সরাইখানায় মদ, উকুন ও সর্বনাশে মজে আছে-এরাই নতুন সভ্যতার ষড়যন্ত্রী গন্ধর্ব ও কিন্নর। মার্ক এদের কথাই লিখে গেছেন, দেবতার মতো প্রতিভায়, `লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার’ নামের রচনায়। এই প্যারিসের সঙ্গে চল্লিশ দশকের কলকাতার বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৌজন্যে কসমোপলিটন। কিছু উজবুক ভাগ্যান্বেষী, কতিপয় সন্দেহভাজন অন্যদেশি, বেশ কিছু মার্কিন সেনা, প্রচুর পল্লিবাসী সহসা কলকাতা শহরকে একটি শান্ত নগরছন্দ থেকে ভীতিতরঙ্গ উপহার দিল। আমরা মেনে নিলাম হ্যারিসন রোডে আরও গভীর অসুখ। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার চামড়ায় যে উল্কির দাগগুলি ছিল তার অন্যতম হল মেসবাড়ি। এক অস্থায়ী, অন্তর্বতী, নিরুপায় নাগরিক ঠিকানা। ইতিহাসের কী অপার কৌতুক যে আমার চোখে পড়ে ছেষট্টি নম্বর হ্যারিসন রোডের মেসবাড়িটি- প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউস- যার বাসিন্দা কাছাকাছি সময়ে ছিলেন জীবনানন্দ ও শরদিন্দু। শরদিন্দু একদম ছাদের ওপর তিন নম্বর ঘরে থাকতেন ১৯১৯-২১, এই দু-বছর। সেখান থেকে হাওড়া ব্রিজ দেখা যেত। শিয়ালদা স্টেশন দেখা যেত। ছাদের আলসে দিয়ে ঝুঁকলে একদিকে হ্যারিসন রোড, পাশ দিয়ে সরু গলি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। তিনতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে যোলো নম্বর ঘর, এখানে জীবনানন্দ থাকতেন ১৯৩০-৩৮, এই আট বছর। লম্বাটে ঘর, পুরনো। দরজা খুলে দিলেই হ্যারিসন রোডের সেই বিখ্যাত ট্রামলাইন নজরে আসে। চোখে পড়ে চলমান জনতার অশেষ যাতায়াত। `বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী/কে আছে পড়ন্ত রোদের পাড়ে সূর্যের দিকে;/খণ্ডহীন মণ্ডলের মত বেলোয়ারি।’
দূর থেকে, বারান্দা থেকে দেখার একটা নিরাসক্ত, গোয়েন্দাপ্রতিম চলন না থাকলে `রাত্রি’ বা `সাতটি তারার তিমির’ বইটির পাতায় যেমন দৃষ্টির কোলাজ তা গড়ে তোলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এডগার অ্যালান পোর `ভিড়ের মানুষ’-ই বোদলেয়ারকে প্ররোচনা দেন ডিটেকটিভের খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কবির ছবি আঁকতে। কবি, গোয়েন্দার মতো নিজেকেই যদি অদৃশ্য করতে না পারেন তবে অন্যকে দৃশ্য ভাবতে পারবেন না। জীবনানন্দের নগরীর মহৎ রাত্রিতে যেরকম সন্দেহভাজনদের আনাগোনা- ভিখিরি, লোল নিগ্রো, ল্যাম্পপোস্ট, চুরুট- তা গোয়েন্দা কাহিনির মেজাজের কাছাকাছি। প্যারিসে মধ্য উনিশ শতকে যা ঘটেছিল, চল্লিশ দশকের শুরু থেকেই কলকাতায় অপরাধের চরিত্র পালটাতে থাকে। জীবনানন্দ নরকের রাস্তা চিনতেন। কিন্তু রহস্যোপন্যাস লেখেননি।
শরদিন্দু তুলনায় পার্থিব সভ্যতার জীব বলেই তাঁর দায় ছিল আপাত বিশৃঙ্খলার একটি যুক্তি নির্মাণ। হয়তো পরিবেশ তাঁকে সুযোগও দিয়েছিল। "
সুচিত্রা সেনকে নিয়ে লিখেছেন
"ষাট দশকে যখন তিনি উত্তমকুমারের বাইকের পেছনে বসলেন, সেই পথ আর শেষ হল না। তিনি সমস্ত বাধানিষেধের ঊর্ধ্বে এমনই এক পরিসর `সপ্তপদী’-তে (১৯৬১), যেখানে মুহূর্তে খুলে যায় স্বপ্নের স্বাধীনতা। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আমাদের যে স্বাধিকারপ্রমত্তা তরুণীর দরকার হয়েছিল, তিনি সিনেমার সুচিত্রা সেন। তাঁকে আমরা প্রায় দর্পিতা ও অভিমানিনী- এই ভূমিকায় যুগপৎ সচল দেখি। তাঁর আহার, ভ্রমণবিলাস, তাঁর অপার স্বায়ত্তশাসন এবং কর্তৃত্বকে ছলনা করার ছলনা, সন্দেহ নেই, একটি বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি নির্দেশ করে। সে সময় আমাদের জরুরি হয়ে পড়েছিল এমন এক তন্বী নাগরিক যিনি নতুন গণতান্ত্রিক সমাজের নতুন আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নতুনতর রং দিতে পারবেন। এটা শুধু বাংলা ছবির ক্ষেত্রে নয়, `আঁধি’-র (১৯৭৫) মতো হিন্দি ছবি দেখলে বোঝা যাবে, সুচিত্রা আশ্চর্যভাবে সেই স্বাধিকারের কথা বলেন। এখনও প্রৌঢ়া মহিলাদের দেখা যায় তারা সুচিত্রা সেনকে অনুসরণ করতে চাইছেন। কাঁধ বেঁকিয়ে কথা বলা, আপাতভাবে সব কিছুকে তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন করা এসবই সুচিত্রা সেনের সাংস্কৃতিক হস্তাক্ষর। এটাই একজন স্টারের বেঁচে থাকার শর্ত। "
এবং তিনি মানেন
"পাঠক ছাড়া তো আমার গতি নেই। তিনি চূড়ান্ত। তিনিই নমস্য।"
আমরা আনন্দিত এই নানা বৈচিত্র্যের বইটি যেখানে উত্তমকুমার বা মারাদোনার পাশাপাশি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে এসে যায় অপরাধের মাধুর্য কি মধ্যবিত্তের গেরস্থালির কাহিনির রূপায়ন, পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে।
বই: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
লেখক: সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক: গুরুচণ্ডা৯
প্রকাশ: ২০২৫প্রচ্ছদ: রমিত চট্টোপাধ্যায়
যাঁরা গুরুর বইপ্রকাশের পদ্ধতিটা জানেন, তাঁরা অবগত আছেন, যে, গুরুর বই বেরোয় সমবায় পদ্ধতিতে। যাঁরা কোনো বই পছন্দ করেন, চান যে বইটি প্রকাশিত হোক, তাঁরা বইয়ের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অর্থভার গ্রহণ করেন। আমরা যাকে বলি 'দত্তক'। এই বইটি যদি কেউ দত্তক নিতে চান, আংশিক বা সম্পূর্ণ, জানাবেন। এই লেখার নিচে। অথবা guruchandali@gmail.com -তে ইমেল করে।
দত্তক প্রসঙ্গে - কী ও কেন >> (https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=28892)
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনআমার আফ্রিকা - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনপূর্বে আসো মেঘ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনম্যাকলাস্কিগঞ্জ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনআলোর পথযাত্রী - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুননৈঃশব্দের তর্জমা - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনএকা মেয়ে বেঁকা মেয়ে - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনইহুদি রসিকতা - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত














