- বুলবুলভাজা পড়াবই বাংলাদেশের হৃদয় হতে

-
কাঁটাতারে ছিঁড়ে যাওয়া জীবনের কাহিনি
দময়ন্তী
পড়াবই | বাংলাদেশের হৃদয় হতে | ২৩ জানুয়ারি ২০২২ | ২৪৯১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 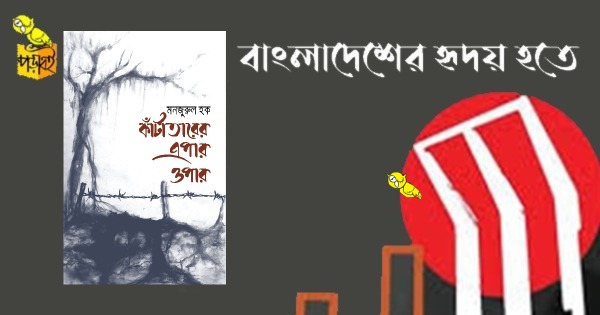
‘দর্শনা চেকপোস্টে চেকিং শেষে লোকগুলো রেললাইন ধরে হেঁটে চলে যেত। পেছন ফিরে কাঁদত কেউ কেউ। শৈশবে এর উত্তর জানতাম না। পরে জেনেছি নাড়িছেঁড়া কান্নার স্বরূপ কেমন! জন্মেরও আগে সেই ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দলে দলে হিন্দু জনগোষ্ঠী ভূমিচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়েছে। একইভাবে মুসলিমরাও দেশ ছেড়ে এসেছে। এই আসা যাওয়ার অভিযাত্রা কতটা হৃদয়বিদারক, বুকের ভেতর কতটা রক্তক্ষরণ হয় তার পরিমাপ কেউ করে না।“ ২০২১ সালের মার্চে বেরোন মনজুরুল হকের বই ‘কাঁটাতারের এপার ওপার’ বইয়ের ব্লার্বে এই কথা লেখা থাকলেও আসলে লেখক গোটা বই জুড়ে সেই রক্তক্ষরণের ফোঁটাগুলির ইতিহাস খুঁজে ফিরেছেন।
ডায়মন্ডহারবারকে আড়াআড়ি রেখা টানলে খুলনার নীচের দিকে মেশে , খুলনার মাটিরকুল গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে তেরখাদা সেখান থেকে গওনা নৌকায় খুলনা, খুলনা থেকে ট্রেনে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে ট্রামে বাসে বা আবার ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার, যেখানে এসে কিতাবের লাইব্রেরী খুলেছিলেন এক মৌলবীসাহেব সেই তিরিশের দশকে। তারও পরে এক সময় তিনি উপস্থিত হন কলকাতার রফি আহমেদ কিদওয়াই স্ট্রীটে, ১৪৩ নম্বর বাড়িটি কিনে বসবাস শুরু করেন। আরো কয়েকমাসের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হন তিন পুত্র ও এক পুত্রবধূ। বছর দুই বাদে কনিষ্ঠ পুত্র পরীক্ষায় খারাপ ফল করায় তাকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ‘ডিটেনশানে’ পাঠান মৌলবী সাহেব। সেই কনিষ্ঠ পুত্রের বড়পুত্রই এই বইয়ের কথক, উত্তম পুরুষে বয়ান করেছেন ‘দেশভাগের নাড়িছেঁড়া’ পনেরখানা কাহিনি।
কথকের বাবা, ওই যে মওলানার ছোটছেলেটি, দেশভাগের পর তার জ্যাঠারা কলকাতা ছেড়ে পূর্ববঙ্গের কারোর সাথে সম্পত্তি বদলাবদলি করে চলে যান, কিন্তু ছোট ভাইটির সেই সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। এই অংশটুকু আমার ঠাকুর্দার জীবনের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়, যেন আয়নায় দেখছি। ছোট ছেলে নিজের জীবন নিজেই গড়ে নেয়, মুক্তিযূদ্ধের নয় মাসের বেশ খানিকটা সময় ভারতে থাকলেও কলকাতায় যাবার কথা ভুলেও ভাবে নি। তীব্র অভিমানেই হয়ত বা ‘কলকাতা’ নামই তার মুখে কেউ শোনে নি কোনোদিন। কিন্তু তারই বড় ছেলে বাবা জ্যাঠা ঠাকুর্দার অতীত বাসস্থান খুঁজতে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ঘুরেফিরে আসেন প্রতি বছর। আমিও চিনি এমন এক মহিলাকে, যিনি জন্মভূমি থেকে উচ্ছিন্ন হবার তীব্র অভিমানে কোনোদিন আর সেখানে যেতে চান নি, জানতে চান নি সেখানকার কোনো খবর। এই ছেঁড়া দেশের এপার ওপারের গল্পগুলোয় কী মিল কী মিল!
শ্যামল সাহা, গুড়ের দোকানি শ্যামল সাহা না থাকতে পারে নিজের মফস্বলে না ঢুকতে পারে ভারতে। শ্যামল নদীতে ঝাঁপায় পুলিশের দেওয়া মিথ্যে মামলা আর গ্রেপ্তারি এড়াতে। তারপরের গল্প হাড়হিম করা। নদীর দুইপারে পুলিশ হাঁটে, গপ্প সপ্প করে শুধু শ্যামলকে উঠতে দেয় না। কী করে তাহলে শ্যামল? হরেন আর জবাকে পালাতে হয় সুবল ঠাকুরের লালসায় পুড়ে। গুরুবরনের মা মনে করায় আগুনপাখি উপন্যাসের সেই অনামা বধূটিকে। এমন কতজন আছেন গোটা উপমহাদেশ জুড়ে যাঁদের ‘কেউ বুঝাইতেই পারলেক নাই’ দেশ কেমন করে ভাগ হয় আর হয়ে আলাদা দেশ হয়ে যায়, তার ঠিকঠাক হিসেব কোত্থাও নেই। খুব একটা কেউ পরোয়াও করে না সে হিসেব রাখার। আর আলাদা দেশ হলেই কি আর সবার খুব সুরাহা কিছু হয়? খিদিরপুর দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া রেজাউলকে বাঁচাতেও তো তার পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছিল ‘পূর্ব পাকিস্তান, মুসলমানদের দেশে’।
রেজাউল, সরযুবালা, সবিতা, নরেন, দীপালী এরা সকলেই কোথাও না কোথাও একই সুতোয় বাঁধা। র্যাডক্লিফ লাইনের সুতো যাদের জীবনটাকে কেটে দু'আধখানা করে দিয়ে গেছে। আমার কাছে বইটার দুর্বলতম আখ্যান মনে হয়েছে মীনাক্ষী ১ ও ২। ‘জাতিস্মর মীনাক্ষী’র যে কাহিনী লেখক শুনিয়েছেন দুই পর্ব ধরে সেই দুটো বাদ দিলে বইটির ধার বাড়ত বলেই মনে হয়। দেশভাগের গল্পগুলো এতই জীবন্ত, রক্ত পুঁজমাখা যে তাতে আর ভূত ভগবান জাতিস্মর ঢুকিয়ে অতিরিক্ত সেনশ্যুয়ালিটি তৈরির প্রয়োজন নেই বলেই মনে করি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল আরেকটি আখ্যান টুনির। তবে এই কাহিনি শেষপর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উতরে গেছে।
পশ্চিমবঙ্গে বা সাধারণভাবে ভারতে হিন্দু বাঙালির মধ্যে আজকাল একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে মুসলমান বাঙালি দেশভাগের সুফলভোগী এবং হিন্দু বাঙালির উপর অত্যাচারে তাদের প্রত্যক্ষ হাত যদি নাও থাকে, তবুও সেই নিয়ে তাদের দুঃখবোধ একেবারেই নেই। মনজুরুল হকের বইটা এই অভিযোগের সপাট জবাব। এবং বইটা এইখানেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মহামায়া পিসির অকথ্য লাঞ্ছনাময় জীবন, সহপাঠী দিলীপ দাশের প্রতি জনৈক রঞ্জুভাইয়ের প্যাসিভ অ্যাগ্রেসিভ আচরণ, পরবর্তীতে দিলীপের বাবা সুবল দাশকে ফাঁসাতে সুপার হামিদুলের মিথ্যেসাক্ষী দেওয়া এই সবই উঠে এসেছে স্পষ্টভাবে, কোন আড়াল, কোন হেঁয়ালি না রেখেই।
কাঁটাতারের এপার ওপার
মনজুরুল হক
প্রকাশক: অনুপ্রাণন প্রকাশন কাঁটাবন ঢাকা
প্রকাশ: মার্চ ২০২১
দাম: ৩১৫/-টাকা (বাংলাদেশ)
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনলক্ষ্মীর ঝাঁপি - দময়ন্তীআরও পড়ুনআদর্শনগর উচ্চ বিদ্যালয় - দময়ন্তীআরও পড়ুনপ্ল্যাস্টিকে মোড়া জীবন - দময়ন্তীআরও পড়ুনবনসৃজনের টুকিটাকি - দময়ন্তীআরও পড়ুনবেশরম - দময়ন্তীআরও পড়ুনহাঁটতে হাঁটতে - দময়ন্তীআরও পড়ুনমায়াবী অনাবিল কথকতা - দময়ন্তীআরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।














