- বুলবুলভাজা পড়াবই প্রথম পাঠ

-
মার্কসবাদের গোড়ায় ফিরে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার পথের খোঁজ
দেবর্ষি দাস
পড়াবই | প্রথম পাঠ | ৩০ আগস্ট ২০২০ | ৪৮৮৮ বার পঠিত 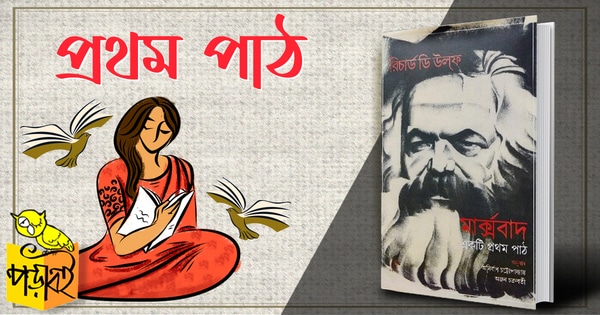 রিচার্ড ডেভিড উল্ফ। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। সহজ ভাষাতে আমজনতার কাছে মার্কসবাদ তুলে ধরতেও সচেষ্ট তিনি। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি বই ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং মার্কসিজম’। এবার বাংলা তরজমায়। পড়লেন অর্থনীতির অধ্যাপক দেবর্ষি দাস।
রিচার্ড ডেভিড উল্ফ। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। সহজ ভাষাতে আমজনতার কাছে মার্কসবাদ তুলে ধরতেও সচেষ্ট তিনি। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি বই ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং মার্কসিজম’। এবার বাংলা তরজমায়। পড়লেন অর্থনীতির অধ্যাপক দেবর্ষি দাস। যাঁরা বাম অর্থনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন রিচার্ড উলফের নাম তাঁদের কাছে অজানা নয়। দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়, আমহার্স্ট-এ প্রোফেসর ইমেরিটাস উল্ফ। সহকর্মী স্টিফেন রেসনিকের সঙ্গে গবেষণা পত্রিকা ‘রিথিংকিং মার্কসিজম’ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারও বত্রিশ বছর হয়ে গেল। ২০০৮ সাল থেকে বাম অর্থনীতির আর-এক কেন্দ্র নিউ ইয়র্ক শহরের নিউ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর পদে আছেন। উলফের পরিচিতির আর-একটা কারণ উনি খালি শুকনো তত্ত্বের পসরা পিঠে সেমিনার জগতে ঘোরাফেরা করেন না। টিভি, ইন্টারনেটের আলোচনাতে উল্ফকে প্রায় দেখা যায়। অর্থাৎ হুদো হুদো পাঠাগার, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমজনতার সেই যে পুরোনো প্রশ্ন, ইহা লইয়া কী করিব, তার জবাব উনি আমজনতার কাছে গিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।
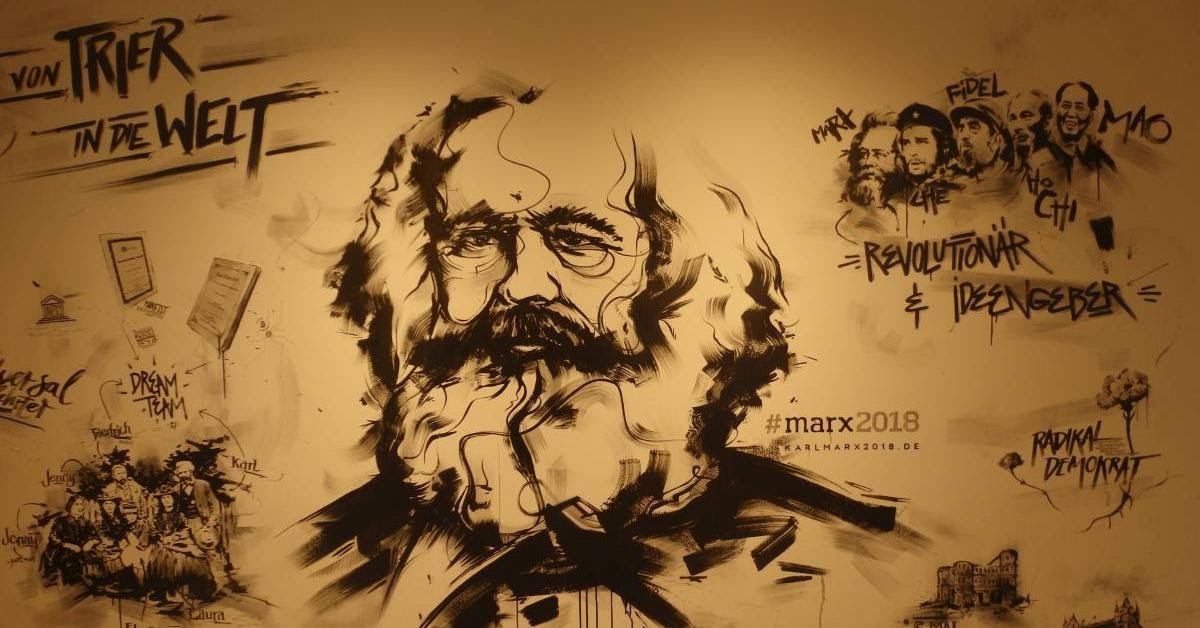
জার্মানির ট্রিয়ের শহরে কার্ল মার্কসের বাড়ির একটি দেয়ালউলফের বই ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং মার্কসিজম’ বেরিয়েছিল ২০১৮ সালে। বাংলা অনুবাদ করেছেন অর্থনীতির দুজন স্বনামধন্য মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তী ও সুপ্রাবন্ধিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। অনির্বাণবাবু বাংলা পাঠকের কাছে আনন্দবাজারের প্রাক্তন সম্পাদক হিসেবেও পরিচিত। বইটি প্রকাশ করেছে অনুষ্টুপ। ১২৭ পাতার ছোটোখাটো তন্বী বই।
মূল বইয়ের ভূমিকায় উল্ফসাহেব লিখেছেন পুঁজিবাদের অস্থির দোলাচলের কথা, ২০০৮ সালের দুনিয়াজোড়া আর্থিক সংকটের কথা। সংকটের পরে আমেরিকা ও ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় দক্ষিণপন্থী রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জাতিবাদী, ইসলামবিদ্বেষী, ভিনদেশি-বিদ্বেষী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বাড়বাড়ন্তের পেছনে কারণ কী? হয়তো নয়া-উদারতাবাদী মডেলের ওপর লোকজনের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। এই সেই মডেল যেখানে বাজার শেষ কথা বলত। যার সুবাদে দুনিয়া সমতল হয়ে যাচ্ছিল। বাজারের সাপ্লাই চেনে যুক্ত লোকেদের ধর্ম, ভাষা, জাতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছিল। নিজের আর্থিক উন্নতিই শেষ কথা, তাই বিশ্বায়নের হাওয়ার সুবিধে নেওয়াই মোক্ষ। অতএব বাজার মারফত বিশ্বশান্তিও হাতের নাগালে এসে গেছিল আর কী। কিন্তু তা আর হল কই। যখন মনে হয় ইতিহাসের এন্তেকাল ঘটেছে, ওমনি ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া’ বলে দাশুগিরি ফলাতে হাজির হয় সে। ট্রাম্প, ব্রেক্সিটের তাই আবির্ভাব হয়।
অনুবাদকেরাও পুঁজিবাদের অস্থিরতা ও সংকটের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই পুঁজিবাদ জীবটাকে বোঝার জন্য মার্কসের বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মনে রাখা যাক, একদিকে যেমন অনেকে বাজারের অরাজকতা থেকে বাঁচতে পিছু হটে জাতি-ধর্ম আঁকড়ে ধরছেন, অন্যদিকে খানিকটা এগিয়ে বাম চিন্তাভাবনাকে ঝেড়েপুঁছে পরখ করে দেখার প্রবণতাও দেখা গেছে (বার্নি স্যান্ডার্স, জেরেমি করবিন, পিকেটি)। আসলে মানুষ রাস্তা খুঁজছেন।
এ বইয়ে মোট সাতখানা পরিচ্ছেদ রয়েছে। বেশির ভাগে রয়েছে কার্ল মার্কসের অর্থনীতির ভাবনার অ আ ক খ। মার্কসবাদের প্রাথমিক শিক্ষাগুলো দিয়ে কীভাবে আজকের পুঁজিবাদী শোষণ ও অস্থিরতাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা-ই বইয়ের উপজীব্য। মূল্য, উদ্বৃত্তমূল্য, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক, শোষণ ও শ্রেণি, দ্বন্দ্ব, ও শেষ পরিচ্ছেদে পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণ—মানে, কী করিতে হইবে। পরিচ্ছেদগুলোর কোনোটাই দীর্ঘ নয়। বইয়ের শেষে ইংরেজি শব্দ থেকে বাংলা অনুবাদের সূত্র দেওয়া রয়েছে, পাঠকের কাজে আসবে।
অনুবাদ বইয়ের আলোচনা মূলত দুটো দিক থেকে হতে পারে। এক, মূল বইয়ের বক্তব্যের আলোচনা, ও দুই, অনুবাদের আলোচনা। প্রথমটা থেকে শুরু করছি।
মার্কসবাদীদের মত কস্মিনকালে মেলে না। এই দিক দিয়ে ওঁরা অর্থনীতিবিদদের থেকে এক কাঠি সরেস—সেই যে শোনেননি, একটা ঘরে ১০ জন অর্থনীতিবিদকে রাখলে তাঁদের থেকে ১১ খানা অভিমত পাবেন! কমিউনিস্ট দলগুলোর সংখ্যাই দেখলেই মার্কসবাদীদের ঐকমত্যের জোর মালুম হয়। স্বাভাবিক ভাবেই উল্ফসাহেবের বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ, মানে কী করিতে হইবে, মতানৈক্যের জন্ম দিতে পারে।
উল্ফ লিখছেন, ‘অফিসে হোক, কারখানায় হোক, স্টোরে হোক, বাড়িতে হোক, প্রতিটি পরিসরে উৎপাদনের প্রক্রিয়া যেভাবে সম্পাদন করা হয় তার একটা মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক… লক্ষ্য হল এক অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে কাজের জায়গাটি হবে মূলত সাম্যধর্মী এবং গণতান্ত্রিক। উদ্বৃত্তের উৎপাদকরা সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই সেই উদ্বৃত্ত আহরণ এবং বণ্টন করবেন, আর তারফলে অবসান ঘটবে শোষণের। কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং উদ্বৃত্ত কীভাবে বণ্টন করা হবে—কর্মস্থলের সমস্ত প্রধান সিদ্ধান্ত সমবেত ভাবে নেবেন উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদক শ্রমিকরা’ (পৃ ১১৩ - ১১৪)
কেমন হবে এই গণতান্ত্রিক কাজের জায়গা? উল্ফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা অন্য দেশের সমবায়ের উদাহরণ দিয়েছেন। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কী সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্যবাদ আসবে? ভেঙে দেখা যাক। সমবায় তৈরি হবে কী করে? পুঁজিপতিরা ভালোবেসে মজুরদের হাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেবেন না নিশ্চয়ই। তাহলে বোধ হয় ব্যাপারটা এই রকম— কর্মীরা প্রতিস্পর্ধী সমবায় তৈরি করবেন, তারপর পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করবেন, ও শেষমেশ অর্থনৈতিক গণতন্ত্র আসবে।
লক্ষ করুন, উল্ফসাহেব রাষ্ট্রকে হিসেবে আনছেন না। বস্তুত উনি রাষ্ট্রমালিকানার বিরোধী। সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষাকে উনি আমল দেন না — ‘অন্য অনেকে আবার সমাজতন্ত্র নামটি সেইসব দেশের জন্য নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন, যেখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রই সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে বলবৎ হয়েছে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চিনের গণপ্রজাতন্ত্র’, (পৃ ১১৬-১১৭)। রাষ্ট্রকে হিসেব থেকে বের করে দেওয়ার একটা কারণ পাই, ‘রাষ্ট্র নিয়ে তিনি [মার্কস] নিজে কখনও কোনো বই লেখেননি, কারণ রাষ্ট্রের ধারণা তাঁর বিশ্লেষণের কেন্দ্রে ছিল না।’ (পৃ ১১২)
উলফের অবস্থানকে অন্তত দু-দিক থেকে প্রশ্ন করা যায়। এক, সমবায় ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের অগাধ ক্ষমতাকে পরাস্ত করতে পারবে, বা পারে? এই দুনিয়ায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু তারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কার্ল কাউটস্কি থেকে এই শতাব্দী পর্যন্ত মার্কসবাদীরা সমবায় নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা কিন্তু সীমাবদ্ধতাগুলোও বিশ্লেষণ করেছেন।
দুই, মার্কস যখন তাঁর ম্যাগনাম ওপাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, যাকে পরে আমরা ক্যাপিটাল নামে জানব, তা ছ-টি খণ্ডের হওয়ার কথা ছিল। প্রতি খণ্ড পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আলাদা এক দিককে বিশ্লেষণ করবে, এই ছিল ছক। চতুর্থ খণ্ড নির্দিষ্ট ছিল রাষ্ট্রের জন্য। ভূতের মতো হাড়ভাঙা খাটার ফলে প্রথম খণ্ড, ক্যাপিটাল, লিখেই মার্কস থামেন। চতুর্থ খণ্ড বেরোল না বলে মার্কসের রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা গোরস্থ হয়ে গেছে তা নয়। মৃত্যুর পর মার্কসের খসড়া লেখা ব্যবহার করে বেরোয় এঙ্গেলসের “দ্য অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট”। রাষ্ট্র নিয়ে লেনিন-সহ যে মার্কসবাদীরা লিখেছেন তাঁরা এঙ্গেলসের ধারণাকে ব্যবহার করেছেন। অস্যার্থ, রাষ্ট্র মার্কসের বিশ্লেষণের কেন্দ্রে ছিল না এটা অনেকেই মানবেন না।
এবার আসি অনুবাদের প্রসঙ্গে। বাংলায় মার্কসচর্চার অভাব নেই। সমস্যা হল অতিপণ্ডিতির ধাক্কায় গোড়ার সোজাসাপটা কথাগুলো তলিয়ে যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কথার মারপ্যাঁচে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এই বইটিতে মার্কসবাদের গোড়াতে ফিরে গিয়ে অনুবাদকেরা কাজের কাজ করেছেন। খালি একটা ছোট্ট কথা। ক্যাপিটালিজমের অনুবাদ ‘ধনতন্ত্র’ করা হয়েছে। বাংলায় ‘ধন’ শব্দ সচরাচর ‘সম্পদ’ অর্থে ব্যবহার হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়েলথ বা মানি। এখন, মার্কসীয় অর্থে সম্পদ (ওয়েলথ) ও পুঁজি (ক্যাপিটাল) এক জিনিস নয়। দুটোই টাকা, তাই গুলিয়ে যেতে পারে। তফাত করার জন্য একটা উদাহারণ দেওয়া যাক। হবুচন্দ্র রাজার প্রভূত ধনসম্পদ আছে। কিন্তু রাজামশাইয়ের প্রচুর পুঁজি আছে বলব না। কেননা সেই টাকা ব্যবহার হয় লোকলস্কর, মন্ত্রী-সান্ত্রী, কোটাল, আমলা পুষতে, বা ঠাট দেখাতে। তা দিয়ে কাঁচামাল কেনা হয় না, শ্রমিককে নিয়োগ করা হয় না, পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে মুনাফার সৃষ্টি না। ভ্যালোরাইজেশন বা মূল্য-সৃষ্টি হয় না। ফলে ওই টাকা ধনসম্পদ যদিও পুঁজি নয়।
ক্যাপিটালের বাংলা পুঁজিই ভালো।
—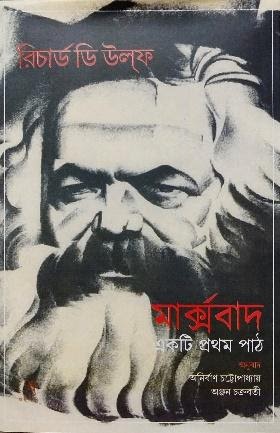
মার্ক্সবাদ: একটি প্রথম পাঠ। রিচার্ড ডি উল্ফ।
অনুবাদ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন চক্রবর্তী
অনুষ্টুপ। ২০০ টাকা
—⦁‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং মার্কসিজম’ বইটির বিষয়ে রিচার্ড ডি উলফের বক্তব্য শুনুন এখানে
⦁রিচার্ড ডি উলফের বইপত্তর, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি মিলবে তাঁর নিজস্ব এই সাইটে
⦁কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেল্সের নিজস্ব সমস্ত লেখা ছাড়াও মার্কসবাদ সংক্রান্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি লেখালিখি ৮০টি ভাষায় পাওয়া যাবে ইন্টারনেটে মার্কসবাদ চর্চার এই সেরা সাইটে
গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুননোটবন্দীর ন’মাস - দেবর্ষি দাসআরও পড়ুনপাট ঠাকুর - Sandip Sarkarআরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ২ - দআরও পড়ুনচান্দ্রেয়ী - Srimallarআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 কল্লোল | 2401:4900:3141:f170:a870:2c45:61cd:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৯:৫৮96801
কল্লোল | 2401:4900:3141:f170:a870:2c45:61cd:***:*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ০৯:৫৮96801এই কথাগুলো সেই ২০০৮ থেকে বলে যাচ্ছি। গুরুতেই ছাপা হয়েছে। আজ অবধি ১৩ বার পঠিত। তবু লিংক দিয়ে যাই <https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=18514>
 Sk | 37.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১০:০২96802
Sk | 37.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১০:০২96802- ভালো কাজ ক রেছেন
ট্রন্স্লতোর
ও পাঠ্ক
।
ঊল্ফ শুন্তে অনেক স হ্জ
 রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:৫৫96812
রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৩:৫৫96812কল্লোল,
তুই ক্রিটিক অফ গোথা প্রোগ্রামের কথা জোর দিয়ে বলেছিস।
আমি অমর্ত্য সেনের কথা চুরি করে বলতে চাই-- এই লেখায় মার্ক্স প্রকৃত সাম্যের জন্যে ক্ললাস এনালিসিস ছাড়িয়ে অন্য আরও প্যারামিটারের গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন। জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি তখন ভাবছিল সমান কাজ বা উৎপাদনের জন্যে সমান বেতন দিলেই সাম্য হবে। কিন্তু মার্ক্স বললেনঃ শারীরিকভাবে আলাদা হওয়ার ফলে একজন শ্রমিকের একই পরিমাণ উৎপাদন করতে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সময় লাগতে পারে। কাজেই শ্রমকে মূল্যের মাপকাঠি হতে গেলে কতটা সময় এবং 'ইন্টেনসিটি' দিইয়ে বিচার করতে হবে। কাজেই এই সমানাধিকারের দাবি আসলে এক অসম শ্রমের জন্যে বিষম অধিকারের দাবি।
এবং মার্ক্স ওদের সমালোচনা করেছিলেন আরও একটি কারণে-- মানুষকে শুধু একমাত্রিক ভাবে শ্রমিক হিসেবে দেখার জন্যে, তার অন্য সব বৈশিষ্ট্যের দিকে চোখ বুঁজে থাকার জন্যে।
আসলে অর্থনৈতিক দিকটা প্রবহমান সমগ্র মানব জীবনের একটা দিক, গুরুতপূর্ণ হলেও।
-
Tapas Das | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৪:০০96813
কম পরিসরেও যে আলোচনার ব্যাপ্তি অনেকটা নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, দেবর্ষি সেটা করে দেখালেন। পুস্তক পরিচিতির স্পেসেও যে আলোচনা করা যেতে পারে, এই লেখাটা তার উদাহরণ।
দেবর্ষি ক্যাপিটালিজমের বাংলা পুঁজিবাদই ভাল বলায় এই পরিভাষা নিয়েই আরেকটা প্রশ্ন, আলোচ্য বইটাতে ওভারডিটারমিনেশনের বাংলা করা হয়েছে পারস্পরিক ক্রিয়া। এইটার কি আর কিছু উপায় করা যায়? একটু অসুবিধে হচ্ছিল।
 রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৬96814
রঞ্জন | 122.18.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৬96814তাপস,
দেবর্ষির লেখা নিয়ে সহমত।
ওভার-ডিটারমিনেশন= অতি-নির্ণয়/অতি-নিয়ন্ত্রণ ? চলবে?
 Pinaki | 136.228.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৫:২৩96815
Pinaki | 136.228.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৫:২৩96815- ওভারডিটারমিনেশনের বাংলা অতিনিয়ন্ত্রণই তো জানতাম।
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩৩96816
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩৩96816- -
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৮96819
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৮96819- আমি ভাবছিলাম পূর্বনির্ণয় বা পূর্ব নির্ধারণ হয় কিনা, বা দুটো শব্দে, অতিরিক্ত দুইটার মইদ্যে একটা।
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত
 রঞ্জন | 182.69.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৫96824
রঞ্জন | 182.69.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২০:৫৫96824বোধি,
তাহলে প্রি_ডিটারমিনেশন বা আ প্রায়োরির বাঙলা কী হবে?
-
Tapas Das | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২৩:০৭96828
ওভার ডিটারমিনেশনের বাংলা আমরা করেছিলাম অতিনির্মাণ। সে সময়ের প্রকল্পে অঞ্জনদাও ছিলেন। সেটা পাল্টানোর কারণ কী হতে পারে, সেইটা ভাবছিলাম। কারণ শব্দ তো ব্রহ্ম।
 রঞ্জন | 182.69.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২৩:১৩96829
রঞ্জন | 182.69.***.*** | ৩১ আগস্ট ২০২০ ২৩:১৩96829অতিনির্মাণ মন্দ লাগছে না।
 sk | 37.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২৮96843
sk | 37.***.*** | ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:২৮96843অবরোহী= a priori -> from google translate
অতি নির্ধারন = overditermination
predetermination = পূর্ব নির্ধারন
 Overdetermination | 162.247.***.*** | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:০৫96906
Overdetermination | 162.247.***.*** | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:০৫96906Overdetermination = প্রমাণাধিক্য।
When more evidence is available than is necessary to justify a conclusion.
 Pinaki | 136.228.***.*** | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:৩৮96907
Pinaki | 136.228.***.*** | ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:৩৮96907- এটা ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত নয়। নির্ধারক একই সাথে নিজেও নির্ধারিত হচ্ছে; নির্ধারক (বা নির্ণায়ক) আর নির্ধারিত (বা নির্ণিত)র একটা জটিল মিথস্ক্রিয়া বোঝাতে এই শব্দটা ব্যবহার হয় বলে জানি। মানে সরল একরৈখিক নির্ণয়ের ধারণাকে যা নাকচ করে।
 ddt | 14.139.***.*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০১:৩৬96966
ddt | 14.139.***.*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০১:৩৬96966তাপসদা,
ওভারডিটারমিনেশনের ভাবার্থ হিসেবে পারস্পরিক ক্রিয়া মন্দ লাগে নি। আক্ষরিক অর্থ হল না যদিও, মানে তো অনেকটা তাই।
-
দীপাঞ্জন | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৫:৪৩96967
- ওভারডিটার্মিনেশন মানে একাধিক (সাফিসিয়েন্ট বাট নট নেসেসারি) কারণের সহাবস্থান | এবার সেই সাফিসিয়েন্ট কারণগুলো পরস্পরনিরপেক্ষ, না তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া আছে, থাকলে সে পারস্পরিক ক্রিয়া একমুখী না ফিডব্যাক লুপ আছে, ফিডব্যাক লুপ না থাকলে একটা রুট কস প্রতিষ্ঠা করে ওভারডিটার্মিনেশন ডিসপ্রুভ করা যাবে কিনা, সেসব প্রব্লেম ও এনালিসিস সাপেক্ষ | সেটা শব্দের অনুবাদে না ঢোকানোই ভালো মনে হয় | স্ট্রাকচারালিস্ট মার্ক্সিজম এর বাইরেও তো, যেমন ড্রিম এনালিসিস, ওভার-ডিটার্মিনেশন ব্যবহার করা হয় | সেদিক থেকে দেখলে, অতিনির্ধারণ / কারণবহুত্ব / কারণাধিক্য ঠিক মনে হয় |
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc, kk, দ)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar, r2h)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












