- বুলবুলভাজা আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শরৎ ২০২০

-
শিশিরকুমার মিত্রঃ বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি বিজ্ঞানীর ১৩০ তম জন্মদিবসে
সহস্রলোচন শর্মা
আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৪ অক্টোবর ২০২০ | ৪৪৩৩ বার পঠিত | রেটিং ৪.৩ (৩ জন) 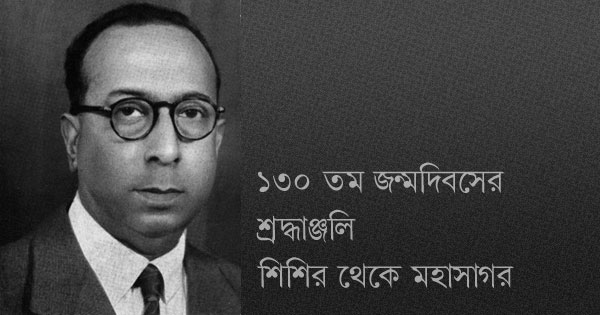
শিশির থেকে মহাসাগর
২২শে জুলাই ২০১৯, সোমবার, সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে। আজই যে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান ২। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর নেতৃত্বে দ্বিতীয় চন্দ্র অভিযানের উদ্যোগ এটা। ইতিপূর্বে ২২শে অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রথম বারের জন্য চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে ছিল চন্দ্রযান ১। চন্দ্র পৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরুর নিকট সফল ভাবেই অবতরণ করেছিল চন্দ্রযান ১। প্রথম বারের সেই অভিযানকে ‘৯৫% সফল’ বলে ব্যাখ্যা করেছিল ইসরো। এবার তাই ‘১০০% সফল’ অভিযানের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিয়েছে তাঁরা। একটা চাপা উত্তেজনা তাই ছড়িয়ে রয়েছে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের প্রতিটা কক্ষেই। দুপুর ২.৪৩ মিনিট, লঞ্চ প্যাড থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলে উঠল ‘জিএসএলভি মার্ক ৩ এম ১’ রকেট। এই রকেটই চন্দ্রযান ২কে পৌঁছে দেবে পৃথিবীর কক্ষপথে। সেই কক্ষপথ ধরে পৃথিবীকে কয়েক পাক পরিক্রমণ করার পর চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে সে। উৎক্ষেপন করার পর উৎকন্ঠায় তাই প্রহর গুনতে শুরু করেছে সবাই। ঠিক মতো কক্ষপথে পৌঁছতে পারবে তো চন্দ্রযান? কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রযান ২কে সফল ভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করল জিএসএলভি রকেট। সাথে সাথে একটা স্বস্তির হাওয়া বয়ে যায় স্পেস সেন্টারে। নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হলো প্রথম পর্যায়ের কাজটা। নির্দিষ্ট এই কক্ষপথে পৌঁছে এবার পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে চলবে চন্দ্রযান। সেই মতো পৃথিবীকে আবর্তন করতে শুরুও করেছে সে। ২৪শে জুলাই ২০১৯, পৃথিবীকে একবার আবর্তন সম্পন্ন করে দ্বিতীয় আবর্তনের পথে এগিয়ে চলল চন্দ্রযান। প্রতিবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে নিজের আবর্তন কক্ষের ব্যাসার্ধ বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে থাকে চন্দ্রযান। নিজের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বাড়াতে বাড়াতে এক সময় লাফ মেরে পৃথিবীর কক্ষ পথ ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে সে। ৩রা অগস্ট ২০১৯, চালু হল চন্দ্রযানের ক্যামেরা। পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে নিজের কক্ষপথ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠের অপূর্ব সব ছবি তুলে ইসরোর দপ্তরে পাঠাতে থাকে সে। ১৪ই অগস্ট ২০১৯, পৃথিবীকে ৫ বার পূর্ণ আবর্তন করে অবশেষে পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল চন্দ্রযান ২।
তিনটে পৃথক অংশকে জুড়ে বানানো হয়েছে চন্দ্রযান ২কে। চন্দ্রযানের প্রথম অংশটার নাম অরবিটার। চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে, একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে চাঁদকে অবিরত পরিভ্রমণ করে চলবে অরবিটার। চন্দ্রযানের দ্বিতীয় অংশের নাম ল্যান্ডার। অরবিটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে এই ল্যান্ডার অংশটাই। বিক্রম সারাভাইয়ের নাম অনুসারে এই ল্যান্ডারটার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বিক্রম’। প্রথমবারের মতোই এবারও, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতেই অবতরণের পরিকল্পনা রয়েছে বিক্রমের। চন্দ্রযানের তৃতীয় অংশের নাম রোভার। রোভার একটা ৬ চাকার ছোটো গাড়ি। ল্যান্ডারে পেটের ভিতরে রাখা এই গাড়িটা নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্রজ্ঞান’। চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণের পর ল্যান্ডারের পেট থেকে বেডিয়ে আসবে প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানের মূল কাজ হলো চন্দ্র পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা ও ছবি তোলা।
২০শে অগস্ট সকাল ৯.১২ মিনিটে সফল ভাবে চন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করে চন্দ্রযান ২। পরিকল্পনা মাফিক, চন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করার পর চাঁদকে আবর্তন করতে থাকে সে। ২২শে অগস্ট ২০১৯, চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রথম ছবি পাঠায় চন্দ্রযান ২। ২৪শে অগস্ট ২০১৯, চন্দ্রযান তখন চাঁদের উত্তর মেরুর কাছ দিয়ে উড়ে চলেছে। যেতে যেতে যথারীতি চন্দ্র পৃষ্ঠের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকছে সে। এই সময়েই চন্দ্রযানের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ‘মিত্র ক্রেটার’। ‘ক্রেটার’ মানে গর্ত। চাঁদের গায়ে অসংখ্য কালো কালো দাগ যাকে সহজ ভাষায় আমরা ‘চন্দ্র কলঙ্ক’ বলে থাকি, তা হলো আসলে চাঁদের গর্ত। চাঁদের বিভিন্ন গর্তকে চিহ্নিত করতে প্রতিটা গর্তের একটা করে নাম দেওয়া হয়েছে। চাঁদের তেমনই এক গর্তের নাম ‘মিত্র ক্রেটার’। চন্দ্রযানের পাঠানো সেই ছবি বিশ্লেষণ করার পর, ২৬শে অগস্ট সেই ছবি প্রকাশ করে ইসরো।

ওইদিন বিকেল ৫.২১ মিনিটে টুইটারে সেই ছবি আপলোড করে ইসরো লেখে ‘Lunar surface imaged by Terrain Mapping Camera-2(TMC-2) of #Chandrayaan2 on August 23 at an altitude of about 4375 km showing craters such as Jackson, Mach, Korolev and Mitra (In the name of Prof. Sisir Kumar Mitra)’[১]ইসরোর করা এই টুইটের সাথে সাথে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ওয়াকিবহাল মহলে। ইসরোর টুইটে চাঁদের চারটে ক্রেটার বা গর্তের নাম উল্লেখ করা হয়। জ্যাকসন[২], মাখ[৩], কোরোলেভ[৪] ও মিত্র[৫] বা প্রফ. শিশির কুমার মিত্র। মিত্র?! প্রফ. শিশির কুমার মিত্র!? ভারতীয়? বাঙালি? কে ইনি? সেভাবে তো কেউ নামই শোনেন নি প্রফ. মিত্রের। সেই শুরু চাঞ্চল্যের। কৌতূহল বাড়তে থাকে জনমানসে। কে এই প্রফ. মিত্র? শুরু হয় খোঁজ খবর। একে একে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে প্রফ. মিত্রের জীবনী, কার্যকলাপ। ক্রমেই প্রচারে আলোয় আসতে থাকেন প্রফ. মিত্র। চাঁদের মাটিতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলার দিগন্তে বোধহয় এখনও সে ভাবে উদ্ভাসিত হন নি অধ্যাপক মিত্র। এহেন শিশিরের সুলুক সন্ধানেই আজ আমাদের যাত্রা। তো চলুন, আজ আমরা অধ্যাপক মিত্রর কর্ম ও জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করি।[৬]
।। ২ ।।
২৪শে অক্টোবর ১৮৯০ সালে হুগলি জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন শিশির কুমার মিত্র। বাবা জয়কৃষ্ণ মিত্র ছিলেন স্কুল শিক্ষক। মা শরৎকুমারী ছিলেন মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা। শরৎকুমারীর পরিবার ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। বিপরীতে জয়কৃষ্ণর পরিবার ছিল রক্ষণশীল হিন্দু ভাব ধারায় বিশ্বাসী। শরৎকুমারীদের মতো ব্রাহ্ম পরিবারে নিজের ছেলের বিয়ে দিতে মোটেও রাজি ছিলেন না জয়কৃষ্ণের পরিবারের সদস্যরা। ১৮৭৮ সালে পরিবারের অমতেই শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন জয়কৃষ্ণ। তিনি নিজেও ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিয়ের পর বাড়িতে আর ঠাঁই হয় নি জয়কৃষ্ণর। বিয়ে করে শরৎকুমারীকে নিয়ে মেদিনীপুর শহরে চলে আসেন জয়কৃষ্ণ। মেদিনীপুরেই যে শরৎকুমারীর বাপের বাড়ি। এই মেদিনীপুর শহরেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের দুই পুত্র সন্তান- সতীশ কুমার ও সন্তোষ কুমার এবং এক কন্যা সন্তান। মেদিনীপুর শহরে বছর দশেক অতিবাহিত করার পর, ১৮৮৯ সালে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন জয়কৃষ্ণ। এখানে একটা স্কুলে শিক্ষকের পদে যোগ দেন তিনি। কলকাতায় থাকার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র (বিদ্যাসাগর), শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন জয়কৃষ্ণ। কলকাতার প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবিদের সংস্পর্শ দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল মিত্র দম্পতিকে। ফলস্বরূপ, কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে (অধুনা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি হন শরৎকুমারী। সেই সময়ে মহিলাদের পড়াশোনা করার চল বড় একটা ছিল না। এমনকি শবব্যবচ্ছেদ করতে হয় বলে ডাক্তারি (এলোপ্যাথি) পড়াটাকেও বড় একটা সুনজরে দেখতেন না অনেকেই। ফলে শরৎকুমারীর ডাক্তারি পড়ার প্রশ্নে এক অসম সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল মিত্র পরিবারকে। শরৎকুমারী সেই সমস্ত মুষ্টিমেয় বাঙালি মহিলাদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সেই সময়ে চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। ইতিপূর্বে, মাত্র ৩ বছর আগে, ১৮৮৬ সালে প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক হিসেবে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন কাদম্বিনী বসু। বাঙালি মহিলাদের মধ্যে চিকিৎসক হওয়ার প্রবণতা ধীর গতিতে হলেও, বাড়ছে তখন। শরৎকুমারী সেই প্রগতিশীল ধারার শরিক ছিলেন। শরৎকুমারী তখনও ডাক্তারি পড়ছেন, এই সময়েই শিশিরের জন্ম হয়। শিশিরের জন্মের সময় শরৎকুমারী কোন্ননগরের শ্বশুরালয়ে চলে আসেন। শিশিরের জন্মের পর, ১৮৯২ সালে মেডিক্যাল পাশ করেন শরৎকুমারী এবং ভাগলপুরের লেডি ডাফরিন হাসপাতালের চিকিৎসক নিয়োজিত হন। ফলে মিত্র পরিবারকে চলে আসতে হয় ভাগলপুরে। ভাগলপুর পুরনিগমে কেরানীর পদে চাকরি পেয়ে যান জয়কৃষ্ণ। ভাগলপুরে আরেকটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে জয়কৃষ্ণের। মিত্র পরিবারের সেই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হলো সুকুমার।
ভাগলপুরেই প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন শিশির। ‘ভাগলপুর জেলা স্কুল’এ ভর্তি করা হয় শিশিরকে। শিশিরের তখনও জন্ম হয় নি, ১৮৮৯ সালে কলকাতার গড়ের মাঠ থেকে কলকাতার বুকে প্রথম বারের মতো উড়েছিল মানুষে চড়ার বেলুন। সমসাময়িক কলকাতায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল সেই বেলুন ওড়ার ঘটনাটা। শিশিরের বয়স তখন ৫-৬ বছরের মতো হবে, দাদা সতীশের মুখে সেই বেলুন ওড়ার কাহি্নি শোনেন শিশির। বেলুন ওড়ার ঘটনা শিশিরের মনে অদম্য এক কৌতূহলের জন্ম দেয়। দাদা সতীশকে অনবরত জিগেস করতে থাকেন বেলুন ওড়ার রহস্য সম্পর্কে। সতীশ তাঁর সাধ্য মতো বায়ুর ঘনত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বায়ুমণ্ডলের সেই রহস্যের কথা শুনতে থাকেন শিশির। বায়ুমণ্ডলের গঠন রহস্যই কিশোর শিশিরের মনে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা বাড়িয়ে তোলে। সেই শুরু, তারপর থেকে আজীবন বিজ্ঞান নিয়েই গবেষণা করে গেছেন শিশির। একটু বড় হয়ে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান ধর্মী রচনা পাঠ করতে দেখা যেতো তাঁকে। এই সময়ের এক বিজ্ঞান পত্রিকায় জগদীশ্চন্দ্র বসুর লেখা পড়ে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন শিশির। সুযোগ পেলেই জগদীশ্চন্দ্র বসুর লেখা প্রবন্ধ পাঠ করতেন শিশির। পরবর্তী কালে, গল্পছলে একথা নিজেই তাঁর বন্ধুদের জানিয়ে ছিলেন শিশির।
শিশির তখনও দশম শ্রেণী পাশ করেন নি। কয়েক বছরের ব্যবধানে শিশিরের দুই দাদা- সতীশ কুমার ও সন্তোষ কুমার মারা যান। শিশিরের পরিবারে নেমে এক দুঃসহ শোকের পরিবেশ। শোকসন্তপ্ত পিতা জয়কৃষ্ণ প্যারালেসিসে আক্রান্ত হন। দুঃসহ বেদনার এক পরিবেশের মধ্যে দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করেন শিশির। এবার এফ.এ. (FA = First Arts বা First Examination in Arts, অধুনা উচ্চমাধ্যমিক তুল্য) পড়ার জন্য ভাগলপুরের তেজ নারায়ণ জুবিলি কলেজে (অধুনা তেজ নারায়ণ বানাইলি কলেজ) ভর্তি হন শিশির। সেই সময়ের পাঠ্যক্রমে আলাদা করে কোনও বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। সমস্ত বিজ্ঞানকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে ‘আর্টস’ পড়ানো হতো। তেজ নারায়ণ কলেজে পড়ার সময়েই মারা যান শিশিরের পিতাও। এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েন শিশির ও তাঁর পরিবার। ঘনিয়ে আসে আর্থিক সংকটও। শিশির তখনও এফ.এ. পাশ করেন নি। শিশিরে পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় তখন। শিশিরে মা তো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েই নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছেলের শিক্ষার প্রশ্নে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে আপস করবেন কেন তিনি? শিশিরের মা চান কম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিগ্রিটা যেন লাভ করেন শিশির।
তাঁর মায়ের ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণাতেই, তেজ নারায়ণ কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করে, ১৯০৮ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন শিশির। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এসসি. বিভাগে ভর্তি হলেন তিনি। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন বাংলার দুই দিকপাল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোস ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জগদীশচন্দ্র তো ছোটোবেলা থেকেই শিশিরের আইডল ছিলেন। এখানে তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁর আরেক আইডল প্রফুল্লচন্দ্র। এই দুই অধ্যাপকের সংসর্গ গভীর প্রভাব ফেলেছিল শিশিরের জীবনে। ১৯১০ সালে বি.এসসি. পাশ করেন শিশির। এবার পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন এম.এসসি.তে। ১৯১২ সালে স্বর্ণপদক সহ এম.এসসি. পাশ করেন শিশির। এম.এসসি.তে ভালো ফল করেও পিএইচডি করতে সুযোগ পাচ্ছিলেন না শিশির। তাঁকে পিএইচডি করার সুযোগ করে দিলেন জগদীশ্চন্দ্র স্বয়ং।
জগদীশচন্দ্র নিজে তখন ‘গাছের প্রাণ’ নিয়ে গবেষণা করছেন। সহজ ভাষায় আমরা যাকে ‘গাছের প্রাণ’ বলছি আদতে তা হলো ‘প্রতিক্রিয়া’। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ গাছের উপর কি প্রভাব ফেলছে তা অনুধাবনেই ছিল জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয়। জগদীশ্চন্দ্রের অধীনে সেই গবেষণায় এবার সামিল হলেন শিশির। জগদীশচন্দ্রের এই পৃথিবী বিখ্যাত গবেষণায় সামিল হতে পেরে যথেষ্টই খুশি হন শিশির। কিন্তু গবেষণার শুরুতেই এক বাধার সম্মুখীন হলেন শিশির। প্রবল আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে তখন দিন গুজরান করতে হচ্ছে তাঁর মাকে, তাঁর পরিবারকে। তাঁর মায়ের একার আয় সংসার চালানো আর সম্ভব হচ্ছে না। সেই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে একটা চাকরি ভীষণই জরু্রি তাঁর। অগত্যাই চাকরি সন্ধান করতে হয় শিশিরকে। জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয় তাঁর। গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখেই ভাগলপুর ফিরতে হয় তাঁকে। ১৯১৩ সালে তেজ নারায়ণ জুবিলি কলেজে লেকচারার পদে চাকরি পান শিশির। লেকচারার পদে চাকরি পাওয়ার ফলে কিছুটা সামলে দেওয়া গেল আর্থিক সংকটকে। শিশির এখন ২৪ বছরের যুবক। ১৯১৪ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন শিশির। বরিশালের রায় বাহাদুর হর কিশোর বিশ্বাসের কন্যা লীলাবতী বিশ্বাসকে বিবাহ করেন শিশির। পরবর্তী সময়ে মিত্র দম্পতির দুই পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল অশোক কুমার মিত্র ও কল্যাণ কুমার মিত্র। ১৯১৫ সালে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন শিশির। অধ্যাপক হিসেবে এখন যথেষ্টই সুনাম হয়েছে তাঁর। কিন্তু নিজের এই কর্মকাণ্ডে কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না শিশির। অধ্যাপনার থেকেও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে অধিক আগ্রহী যে তিনি। জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণার সুযোগ হারানোকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। এই সময়ে, ছাত্রদের সহজভাবে বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার জন্য, বিভিন্ন কারিগরি মডেল স্বহস্তে প্রস্তুত করে দেখাতে থাকেন শিশির। তাঁর সেই মডেলগুলোর মধ্যে ছিল স্বকীয়তার ছাপ। বিজ্ঞানকে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করতে বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করলেন প্রবন্ধ। তাঁর সেই অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা আর প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই অবদমিত মানসিক অস্থিরতাই ফুটে উঠছিল যেন।।। ৩ ।।
১৯০৫ সাল, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জেরে তখন উত্তপ্ত বাংলা। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্বদেশী ধাঁচে পঠন পাঠনের জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেন স্বদেশীরা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সামিল সেই উদ্যোগের সমর্থনে। উত্তাল আন্দোলনের মধ্যে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তা ভাবনাকে ভালো চোখে দেখেন নি ইংরেজ সরকার। শিক্ষা নিয়ে বাঙালির এই ক্ষোভকে সামাল দিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলর) হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন তাঁরা। ৩১শে মার্চ ১৯০৬ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়[৭] ভারতীয় হিসাবে উপাচার্যের দায়ভার (১৯০৬-১৯১৪) গ্রহণ করেন আশুতোষ। ইংরেজদের দেওয়া এই সুযোগকে পরিপূর্ণ ভাবে সদ্ব্যবহার করার উদ্যোগ নিলেন আশুতোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকাঠামোয় এক আমূল পরিবর্তন আনতে শুরু করলেন তিনি। একে একে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, পালি, ইতিহাস, দর্শন, অর্থিনীতি, গণিত প্রভৃতি বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম (মাস্টার ডিগ্রী) চালুর জন্য সেনেটের কাছে সুপারিশ করেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় নরম মনোভাব দেখায় সেনেট। আশুতোষের সংস্কার অনুমোদিত হয়। নতুন বিভাগ ছাড়াও, অধ্যাপনার জন্য বেশ কয়েকটা ‘চেয়ার’ও চালু করেন আশুতোষ। সেই সমস্ত পদও মঞ্জুর করে সেনেট। এবার আশুতোষের লক্ষ্য ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাগার, আধুনিক যন্ত্রপাতি, হালফিলের পাঠ্যক্রম, উপযুক্ত গ্রন্থাগার চালু করা। কিন্তু ইতিমধ্যেই এতোগুলো বিভাগে সংস্কারের জন্য প্রতি বিছর বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যয় ভার বহন করতে হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে। ফলে বিজ্ঞানের নতুন পরিকল্পনা রূপায়নে আর্থিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেন আশুতোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বিস্তৃতির প্রশ্নে সরকারও আর নতুন ভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি ছিলেন না। অত্যন্ত প্রতিকূল এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন আশুতোষ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির প্রশ্নে তাঁর ইচ্ছা আছে, পরিকল্পনা আছে, উদ্যোগ আছে, উদ্যম আছে, শুধু পয়সাটাই নেই। মনে মনে তখন যেন ক্ষোভে প্রায় ফুঁসছেন আশুতোষ। তিনি বললেন, “এখানে যদিওবা মানুষ আছে, কিন্তু ব্যবস্থা নেই, গবেষণাগার নেই, ওয়ার্কশপ নেই, মিউজিয়াম নেই, যন্ত্রপাতি নেই”। কিন্তু ‘বাংলার বাঘ’ কি আর সহজে হার মানবেন এই প্রতিকূলতার কাছে! ব্যক্তি উদ্যোগে ফান্ড সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন আশুতোষ। তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত ও প্রখ্যাত আইনজীবী ও কংগ্রেস সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ (প্রসঙ্গত, রাসবিহারী বসু নন, এনার নামেই দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত একটা রাস্তার নাম রাখা হয়েছে রাসবিহারী এভিন্যু)। ১৯১২ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ৭ লাখ টাকা দান করলেন তারকনাথ পালিত। চার মাস পর, অক্টোবর ১৯১২ সালে ফের সাড়ে ৭ লাখ টাকা ও বহুল পরিমাণে স্থাবর সম্পত্তি (অধুনা বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের বাড়ি ও জমি) দান করেন শ্রীপালিত। কয়েক বছর পর, ১৯১৯ সালে পুনরায় সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা দান করেন তারকনাথ। অগস্ট ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ১০ লাখ টাকা দান রাসবিহারী ঘোষ। আশুতোষ তখন ক্রমান্বয়ে চতুর্থবারের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। উপাচার্য হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৯১৪ সালের ৩০শে মার্চ। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য পৃথক এক বিদ্যালয় স্থাপন করে যেতে চান আশুতোষ। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য পৃথক কলেজ খোলায় বিশেষ সায় নেই সরকারের। তাঁরা জানেন এই সমস্ত বিজ্ঞান কলেজগুলোই প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারের আশঙ্কা, প্রস্তাবিত এই কলেজ না ইংরেজ বিরোধী শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ঢাকা কলেজ থেকে বিতাড়িত ‘কুখ্যাত’ ছাত্র মেঘনাদ সাহা তখন কলকাতায় পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েই পড়ছেন। এই সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে তখন যথেষ্ঠই চিন্তিত সরকার। তাই ওই সব বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে বেশি মাতামাতির প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন ইংরেজ সরকার। কিন্তু আশুতোষও ছাড়ার পাত্র নন। প্রভাবশালী মহল থেকে জোগাড় করলেন সবুজ সংকেত। আর দেরি করেন নি তিনি। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র ৪ দিন আগে, ২৭শে মার্চ ১৯১৪ সালে, ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি’র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন আশুতোষ। সাধারণ ভাবে এই কলেজটা ‘রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ’ নামে পরিচিত। রাসবিহারী ঘোষের স্মরণে পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় ‘রাসবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গন’। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ফলিত গণিত ও বায়োকেমিস্ট্রি- এই ৬টা বিভাগ রাসবিহারী ঘোষের নামাঙ্কিত ‘চেয়ার’ চালু করেন আশুতোষ। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে বিভাগে চালু হয় তারকনাথ পালিতের নামাঙ্কিত আরও দুটো ‘চেয়ার’।১৯১৬ সালে উদ্বোধন হলো ‘রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ’এর। এই মুহূর্তে উপাচার্য পদে না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডি’র সভাপতি পদে এখনও বহাল আছেন আশুতোষ। এবার তাই আশুতোষের লক্ষ্য দক্ষ অধ্যাপক নিযুক্ত করা। ১৯১৬ সালে রসায়নের পালিত চেয়ারের জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আহ্বান করলেন আশুতোষ। ১৯১৬ সালে এখানে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন দুই তরুণ প্রতিভা মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯১৬ সালেই এখানে অধ্যাপনার ডাক পড়ল শিশির কুমার মিত্রর। তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার পদে নিযুক্ত করলেন আশুতোষ। ১৯১৭ সালে পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত চেয়ারের জন্য নিযুক্ত হলেন ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র সি.ভি. রমন। শিশিরের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল যেন তখন। তাঁর গুরু প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সি.ভি রমন প্রমুখ ছাড়াও তরুণ তুর্কি মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে একই কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে জন্য মনে মনে তখন আরও কিছু বুঝি ভেবে চলেছেন তিনি। তাঁর যে পিএইচডি করা হয় নি তখনও পর্যন্ত! আর্থিক কারণে সেবার অধরাই রয়ে গিয়েছিল সেই স্বপ্ন। তাঁর অধরা সেই স্বপ্ন এবার সাকার করা সুযোগ পেলেন শিশির। রমনের সাহচর্যকে পরিপূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন তিনি। রমনের অধীনে নতুন করে গবেষণা শুরুর কথা ভাবলেন শিশির। সেই মতো ‘রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ স্কলার’ বৃত্তিও পেয়ে গেলেন তিনি। রমনের অধীনে এক বর্ণ আলোর অপবর্তন (বিচ্ছুরণ) ও ব্যাতিচার নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন শিশির। এই গবেষণার মূল বিষয় হলো অতি ক্ষুদ্র একটা ছিদ্র দিয়ে নির্গত হওয়ার সময় একবর্ণের কোনও আলো কিভাবে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে তা নির্ধারণ করা। তাঁর গবেষণার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন স্বয়ং রমন। বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া বার্ষিক রিপোর্টে তিনি লেখেন, ‘Mr. Sisir kumar Mitra has shown most praiseworthy activity during the current year’.
১৭৯৮ সালে লন্ডন শহর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন’ (Philosophical Magazine)। বিজ্ঞান বিষয়ক এতো নামজাদা পত্রিকা পৃথিবীতে কমই আছে। পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা নিয়মিত লিখে থাকতেন এই ম্যাগাজিনে। হামফ্রে ডেভি, মাইকেল ফ্যারাডে, জুল, ম্যাক্সওয়েল, জে.জে. থম্পসন, সি.ভি. রমন কে না লিখেছেন এই ম্যাগাজিনে। রমনের অধীনে গবেষণা করা কালীন ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে ৩টে প্রবন্ধ লিখে পাঠান শিশির। ১৯১৮ সালে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিশির কুমার মিত্রর লেখা প্রথম প্রবন্ধ On the asymmetry of the Illumination-curves in oblique diffraction. ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ On sommerfeld’s treatment of the problem of diffraction by a semi-infinite screen. ১৯১৯ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধ On the large-angle diffraction by aperture with curvilinear boundaries. ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনের মতো পত্রিকায় তিনটে প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ায় বিজ্ঞান জগতে বেশ কিছুটা পরিচিতি পান শিশির। ইতিমধ্যেই ১৯১৯ সালে রমনের অধীনে গবেষণার কাজও সম্পূর্ণ করে ফেলেন তিনি। ফলে ১৯১৯ সালেই তিনি লাভ করেন তাঁর কাঙ্খিত ডি.এসসি. ডিগ্রী।
দুই দাদা ও বাবার মৃত্যুতে আচমকাই শিশিরের পরিবারে নেমে এসেছিল ভয়ানক এক আর্থিক বিপর্যয়। সেই বিপর্যয় তাঁর উচ্চতর শিক্ষার সম্ভাবনাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ এক স্বপ্নের উড়ানে যেন পাখা মেলেছে শিশিরের ভবিষ্যৎ। রমনের অধীনে গবেষণা শেষ করে ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অব প্যারিসে (অধুনা, সোরবন ইউনিভার্সিটি) গবেষণার সুযোগ পান শিশির। ইউনিভার্সিটি অব প্যারিসে গবেষণার জন্য ১৯২০ সালে ফ্রান্সে আসেন শিশির। এখানে ফরাসি পদার্থবিদ চার্লস ফ্যাব্রির (পুরো নাম : Maurice Paul Auguste Charles Fabry, ১৮৬৭-১৯৪৫) অধীনে শুরু করেন নতুন গবেষণা। ইতিপূর্বে ১৯১৩ সালে অঁরি বিশঁর (Henri Buisson, ১৮৭৩-১৯৪৪) সাথে গবেষণা করে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর আবিষ্কার করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন ফ্যাব্রি। এহেন ফ্যাব্রির অধীনে গবেষণা শুরু করেন শিশির। এবার তাঁর গবেষণার বিষয় তামার বিচ্ছুরণ। যে কোনও পদার্থকে উতপ্ত বা উদীপ্ত করলে সেই পদার্থ থেকে বিশেষ এক ধরণের আলোর বিচ্ছুরণ নির্গত হয়, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে স্পেকট্রাম বা বর্ণালী বলা হয়। প্রতিটা পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বর্ণালী সৃষ্টি করে। প্রত্যেক পদার্থেরই রয়েছে স্বকীয় এক বর্ণালী, যা একান্ত ভাবেই তার নিজস্ব। কোনও দুটো পদার্থের বর্ণালী এক হয় না। আর ঠিক এই কারণেই পদার্থের বর্ণালী দিয়েও পদার্থকে শনাক্ত করা সম্ভব। সেই ভাবে তামারও নিজস্ব এক বর্ণালী আছে, যা নিতান্তই তামার নিজস্ব ধর্ম। ফ্যাব্রির নেতৃত্বে প্যারিসের গবেষণাগারে তামার বর্ণালীর তরঙ্গ দের্ঘ্য পরিমাপের চেষ্টা করেন শিশির। তামার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২০০০-২৩০০ আমস্ট্রং নির্ধারণ করেন তিনি। ১৯২৩ সালে শেষ হয় তাঁর গবেষণা। ১৯২৩ সালে Journal of the Chemical Society, Transaction পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণাপত্র Determination of spectroscopic standard wave-length in the short wave-length region. ১৯২৩ সালের শুরুতেই দ্বিতীয় বারের জন্য (ডাবল) ডি.এসসি. লাভ করেন তিনি। দ্বিতীয় বার ডি.এসসি. ডিগ্রী লাভ করেও থেমে থাকতে চান নি তিনি। তামা নিয়ে গবেষণা শেষ করার পর নিলেন তৃতীয় দফায় গবেষণার প্রস্তুতি। কারণ, এবার যে তিনি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরির অধীনে গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯২৩ সালেই ‘রেডিয়াম ইনস্টিটিউট’এ (অধুনা কুরি ইনস্টিটিউট) মাদাম কুরির অধীনে গবেষণা শুরু করেন শিশির। সে যেন এক স্বপ্নের যাত্রা শিশিরের।
ফ্রান্সে আসার পর থেকেই রেডিও তরঙ্গ, রেডিও ভাল্ভ প্রভৃতি বিষয় প্রচুর চর্চা শুনছিলেন শিশির। জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করার সময় এই তরঙ্গের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে শিশিরের। তবে জগদীশচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাধারণত যাকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রান্সে এসে শিশিরের পরিচয় ঘটে অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত রেডিও তরঙ্গের সাথে, রেডিও বার্তার সাথে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসম্ভব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল রেডিও বার্তা। সেই সময়ে কীভাবে ব্যবহার হয়েছিল রেডিও তরঙ্গ, সে বিষয় অবগত হতে থাকেন শিশির। রেডিও বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন নিয়ে ক্রমেই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন তিনি। বিষয়টাকে আরও গভীর ভাবে জানতে উৎসাহ জন্মায় তাঁর মনে। তৃতীয় দফায়, মাদাম কুরির অধীনে গবেষণা করা সময়, তিনি জানতে পারেন পূর্ব ফ্রান্সের ন্যান্সি শহরের ইউনিভার্সিটি অব ন্যান্সিতে অধ্যাপক ক্যামি গুতোঁ (পুরো নাম : Camille Antoine Marie Gutton, ১৮৭২-১৯৬৩) রেডিও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন তখনও। ইতিপূর্বে মিলিটারিদের অধীনে রেডিওটেলিগ্রাফির সাথে যুক্ত ছিলেন গুতোঁ। অধ্যাপক গুতোঁর গবেষণার খবরটা জানতে পেরে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন নি শিশির। রেডিও বা ওয়্যারলেস বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে মনস্থির করে ফেলেন। জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরির অধীনে গবেষণায় ইস্তফা দিয়ে ন্যান্সি শহরে হাজির হলেন শিশির। লক্ষ্য- রেডিও গবেষণা। অচিরেই অধ্যাপক ক্যামি গুতোঁর অধীনে শুরু করলেন রেডিও বা ওয়্যারলেস নিয়ে গবেষণা। মাদাম কুরির অধীনে গবেষণা ছেড়ে অধ্যাপক গুতোঁর অধীনে ওয়্যারলেস নিয়ে গবেষণাই ছিল শিশিরের জীবনের এক মোড় ঘোরানো সিদ্ধান্ত। রেডিও বা ওয়্যারলেস নিয়ে তাঁর এই উন্মাদনাই তাঁর ভবিষ্যতের পটচিত্র এঁকে দিয়েছিল। তাঁর এই উন্মাদনাই জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় রেডিও বিজ্ঞানের এক দিকপালের। আমরা দেখবো কি ভাবে ভারতীয় রেডিও বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসেবে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিশির।
ন্যান্সিতে অধ্যাপক গুতোঁর অধীনে গবেষণার সময়ে রেডিও জগতের দুই দিকপাল বিজ্ঞানীর সাথে সাথে আলাপ হয় তাঁর। প্রথমজন হলেন ফরাসি পদার্থবিদ এদওয়াঁ বঁলি (পুরো নাম : Edouard Eugene Desire Branly, ১৮৪৪-১৯৪০) এবং দ্বিতীয়জন ব্রিটিশ পদার্থবিদ রেডিও অলিভার লজ (পুরো নাম : Oliver Joseph Lodge, ১৮৫৫-১৯৪০)। এঁরা তখন রেডিও বিজ্ঞানের মহীরুহ তুল্য বিবেচিত হতেন। এঁদের সাহচার্য দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল শিশিরকে।
খুব অল্প দিনই অধ্যাপক গুতোঁর অধীনে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছিলেন শিশির। কারণ, দেশে তো ফিরতে হবে তাঁকে। সে ব্যবস্থা তো প্রায় পাকা। কিন্তু তবুও অধ্যাপক গুতোঁর অধীনে গবেষণায় যেন সঞ্জীবনীর স্বাদ পেয়েছিলেন শিশির। ওয়্যারলেস নিয়ে যত পড়ছেন ততই উত্তেজনা অনুভব করছেন শিরায় শিরায়। ওয়্যারলেস নিয়ে তাঁর উত্তেজনা নিজের মধ্যে আর চেপে রাখতে পারেন নি শিশির। ন্যান্সি থেকেই তাঁর অন্যতম গুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে ওয়্যারলেস নিয়ে সম্ভাবনার কথা জানান তিনি। সেই চিঠিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ওয়্যারলেস পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন শিশির। শিশিরে অনুরোধ যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে থাকেন আশুতোষ। ১০ই মে ১৯২৩ সালে শিশির চিঠির জবাবে আশুতোষ লেখেন-
আমার প্রিয় ড. শিশির, ১০ই মে, ১৯২৩
১৮ই এপ্রিল তোমার লেখা চিঠি পেয়ে আর তোমার কাজের সাফল্যের খবর শুনে ভীষণ ভালো লাগলো। তোমার প্রস্তাবিত ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফির সাহায্যে সংকেত প্রেরণের পাঠ্যসূচী ভীষণ আকর্ষণীয়। অনুগ্রহ করে তুমি যদি (পাঠ্যক্রমের) রূপরেখা তৈরি (করো) আর ব্যয়ভার যথাসাধ্য কমানোর চেষ্টা করো। আমরা কী করতে পারি সেটা আমি দেখবো ক্ষণ। তুমি নিশ্চিত জেনে রেখো যে এতে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তাতে যেন আমরা ভীত না হই; লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের লড়াই করতে হবে। নভেম্বরে তোমার প্রত্যাবর্তনে আশায় রইলাম।
তোমার অনুরক্ত
আশুতোষ মুখার্জি
হ্যাঁ, নভেম্বরেই দেশে ফেরার কথা শিশিরের। আর সেই জন্যই অধ্যাপক ক্যামি গুতোঁর অধীনে বেশিদিন গবেষণার সুযোগ পান নি শিশির। তবু সেই সময়টুকুর মধ্যেই ফ্রান্সের ‘জার্নাল ডি ফিজিক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রেডিও তরঙ্গ নিয়ে লেখা তাঁর দু’টো প্রবন্ধ। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা প্রথম নিবন্ধ On the Demagnetization of Iron by electromagnetic oscillation. ওই বছরই প্রকাশিত হয় On the high-Frequency discharge in rarefied gases শীর্ষক তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধ। দ্বিতীয় এই নিবন্ধের সহলেখক ছিলেন তাঁর শিক্ষক ক্যামি গুতোঁ এবং ফিনল্যান্ডের গবেষক ভিয়ো ইলোস্তালো (পুরো নাম : viljo Viktor Ylostalo, ১৮৮৭-১৯৫৯, পরবর্তীকালে ফিনল্যান্ডের রেডিও ব্রডকাস্টিঙের পথিকৃৎ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ইনি)। অধ্যাপক গুতোঁর অধীনে অল্পদিনের এই গবেষণাই পরবর্তীকালে শিশিরের জীবনের অক্ষ হয়ে ওঠে।
।। ৪ ।।
১৯২৩ সালের শেষের দিকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন শিশির। ১৯২৩ সালেই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ‘খয়রা[৮] প্রফেসর অব ফিজিক্স’ পদে নিযুক্ত হন তিনি। এই সময়ে দ্বিতীয় দফায় পঞ্চমবারের (১৯২১-১৯২৩) জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বেই ওয়্যারলেস নিয়ে শিশিরের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল আশুতোষের। আমরা দেখেছি, ওয়্যারলেস নিয়ে শিশিরের মতোই সমান আগ্রহী ছিলেন আশুতোষও। এবার শিশির-আশুতোষ যুগলবন্দীতে শুরু হলো ভারতের মাটিতে ওয়্যারলেস যাত্রা। আশুতোষের অনুরোধে শিশির তখন লিখে চলেছেন ওয়্যারলেসের পাঠ্যক্রম। বাকিটা বুঝে নেবেন আশুতোষ। অচিরেই ভারতের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হলো ওয়্যারলেস বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম। ১৯২৪ সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এম.এসসি.র ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হলো ওয়্যারলেস বিজ্ঞানকে। ওয়্যারলেস নিয়ে গবেষণার জন্য খোলা হলো নতুন এক গবেষণাগার। শিশিরে হাত ধরে উন্মোচিত হলো ভারতীয় বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত- রেডিও বিজ্ঞান। আমরা দেখবো, শিশিরের তৈরি এই গবেষণাগার কীভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী একদল বাঙালি বিজ্ঞানীর আঁতুরঘর হয়ে উঠেছিল।
১৯২৩ সালে কলকাতায় ফিরে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন শিশির। কলকাতার কিছু উৎসাহী ইংরেজ মিলে গঠন করেছিলেন ‘রেডিও ক্লাব অব বেঙ্গল’। এই রেডিও ক্লাবের উদ্যোগেই প্রথম রেডিও সম্প্রচার শুরু হয় কলকাতায়। নভেম্বর ১৯২৩ সাল থেকে নিয়মিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে এই রেডিও ক্লাব। রেডিও যে শিশিরে স্বপ্ন, রেডিও যে শিশিরের নেশা। সত্ত্বর তাই রেডিও ক্লাব অব বেঙ্গলের সাথে যুক্ত হলেন শিশির। ১৯২৪ সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের রেডিও গবেষণাগার খোলার পর, এক নতুন ভাবনা মাথায় এলো শিশিরের। এই গবেষণাগারেই নতুন রেডিও স্টেশন খুললে কেমন হয়? রেডিও সম্প্রচারের সমস্ত খুঁটিনাটি কার্যকলাপ তো নখদর্পনে তাঁর। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ১৯২৫ সালে প্রায় একার হাতে এই গবেষণাগারেই স্থাপন করলেন এক বিনোদনমূলক রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র বা রেডিও স্টেশন। শিশির এই রেডিও কেন্দ্রের নাম দিলেন 2CZ. কলকাতার বুকে বিনোদনমূলক দ্বিতীয় রেডিও সম্প্রচার শুরু করা হয় শিশিরের গবেষণাগার থেকে। শিশিরের এই ছোট্ট গবেষণাগার হয়ে উঠল ভারতের রেডিও সম্প্রচারের পথিকৃৎ। শিশির হয়ে উঠলেন ভারতীয় রেডিও ইতিহাসের অঙ্গ। রেডিও ক্লাবের অভিজ্ঞতায় শিশির দেখেছিলেন যে রেডিও ক্লাব খুবই লো ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করতেন। তাঁদের রেডিও সিগন্যাল ছিল খুবই দুর্বল। ফলে ৭-৮ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাঁদের সেই সম্প্রচার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, প্রথম দিন থেকেই মিডিয়াম ওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার শুরু করলেন শিশির। ফলে বৃহত্তর কলকাতা জুড়েই সম্প্রচারিত হতো শিশিরের বিনোদনমূলক রেডিও অনুষ্ঠান। তখনও ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’ আত্মপ্রকাশ করেনি। অল ইন্ডিয়া রেডিওর আত্মপ্রকাশের পূর্বে, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো মাত্র দু’টো রেডিও স্টেশন থেকে- একটা রেডিও ক্লাব অব বেঙ্গলের সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে আর দ্বিতীয়টা শিশিরের গবেষণাগার বা 2CZ থেকে।
এইখানে একটা বিষয় একটু স্পষ্ট করে বোঝার প্রয়োজন আমাদের। রেডিও বিজ্ঞান ও রেডিও সম্প্রচার কিন্তু হুবহু একই বিষয় নয়। রেডিও বিজ্ঞান হলো তাত্ত্বিক বিষয় আর রেডিও সম্প্রচার তারই ফলিত জ্ঞান। সন্দেহ নেই রেডিও সম্প্রচার বা ফলিত জ্ঞানে চমক অনেক বেশি থাকে। কিন্তু সে চমকে খুব বেশি আগ্রহ দেখান নি শিশির। ফলে রেডিও সম্প্রচার নিয়ে আর বেশি দূর এগোন নি তিনি। ১৯২৭ সালে 2CZ সম্প্রচার বন্ধ করে দেন শিশির। তাছাড়া, ১৯২৭ সাল থেকেই ‘ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড’ নামের এক বড় বেসরকারি সংস্থা বম্বে ও কলকাতা থেকে তাঁদের রেডিও সম্প্রচার শুরু করে। রেডিও সম্প্রচার বড় এক শিল্পে পরিণত হতে শুরু করেছে তখন। সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজন হয়ে বড় পুঁজির। রেডিও সম্প্রচার বিকশিত হতে থাকে তার নিজের ধারায়। শিশির সেই ধারার শরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন গবেষক, বিজ্ঞানী। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনই তাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন। ফলে শিশির এগিয়ে চললেন বিজ্ঞান সাধনার পথ ধরে। শিশিরের সেই বিজ্ঞান সাধনার অলি গলি ধরেই এবার এগিয়ে চলবো আমরা। তবে ওয়্যারলেস বা রেডিও বিজ্ঞান নিয়ে শিশির কুমার মিত্রের ভূমিকা অনুধাবন করতে গেলে দু’টো বিষয়ে সাধারণ কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন আমাদের- ১) বায়ুমন্ডলের স্তর ভেদ ২) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এই দু’টো বিষয় নিয়ে চটপট কিছু আলোচনা সেরে ফেলা যাক এবার।

বায়ুমন্ডলের ৫টা স্তরের কথা স্কুল জীবন থেকেই জেনে এসেছি আমরা। বায়ুমণ্ডলের সেই ৫ স্তরের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ এই রকম-
১) ট্রোপোস্ফিয়ার- ভূপৃষ্ট সংলগ্ন এই স্তরেই মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত হয়ে থাকে। সমগ্র বায়ুমন্ডলের উপাদানের ৭৫% পদার্থই থাকে এই অঞ্চলে থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কিমি উপর পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত হলেও মেরু অঞ্চলে ১০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায়এই স্তর। গড়ে এই স্তরের বিস্তৃতি ১২ কিমি ধরা হয়।
২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার- ট্রোপোস্ফিয়ারের পর থেকে প্রায় ৫০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে স্ট্রাটোস্ফিয়ার বলা হয়।
৩) মেসোস্ফিয়ার- স্ট্রাটোস্ফিয়ার উপরে ৫০ কিমি থেকে ৮৫ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে।
৪) থার্মোস্ফিয়ার – ৮৫ কিমি থেকে ৭০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর থার্মোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এই স্তরেই স্থাপন করা হয়েছে ‘ইন্টারনেশান্যাল স্পেস স্টেশন’।
৫) এক্সোস্ফিয়ার- ভূপৃষ্ঠের ৭০০ কিমি উপরে অবস্থিত এই স্তর ধীরে ধীরে মহাকাশে মিলিয়ে গেছে। মোটামুটি ভাবে থেকে ১০,০০০ কিমি পর্যন্ত এই স্তরের বিস্তার ধরা হয়ে থাকে।
এই ৫ স্তরের মধ্যে কিন্তু কোথাও ওজনোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ারের নাম দেখতে পেলাম না আমরা। অথচ আধুনিক সমাজ জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে বায়ুমন্ডলের এই দুই স্তর। ভূপৃষ্ঠের ১৫ কিমি থেকে ৩৫ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে ওজন স্তর বা ওজনোস্ফিয়ার বলা হয়। ওজন দিয়ে গঠিত এই স্তরের সম্পূর্ণটাই স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অন্তর্বতী। আমরা জানি এই ওজন স্তরে প্রতিহত বা শোষিত হয় অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray)। তবে ওজন স্তর নয়, আজ আমাদের আলোচনার ভরকেন্দ্র হলো আয়নোস্ফিয়ার। তাই আয়নোস্ফিয়ারের মধ্যে আলোচনকে সীমাবদ্ধ রাখছি আমরা।
আয়নোস্ফিয়ার প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা বুঝতে হবে আমাদের তা হলো, বায়ুমণ্ডলের অংশ হয়েও, বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদের মধ্যে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় না আয়নোস্ফিয়ারকে? আসলে, বায়ুমণ্ডলের কোনও নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় গঠিত হয় না আয়নোস্ফিয়ার। তিনটে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত তিনটে পৃথক স্তরকে একত্রে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয়। এই তিনিটে স্তরকে উচ্চতার ঊর্ধ্বক্রমে ডি, ই, এফ (D, E, F) নামে অভিহিত করা হয়। ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরকে ডি স্তর এবং সবচেয়ে দূরবর্তী স্তরকে এফ স্তর বলা হয়। ডি ও এফ স্তরের মধ্যবর্তী উচ্চতায় ই স্তরের অবস্থান। দিন-রাত ও ঋতু ভেদে এই তিন স্তরের অবস্থান পরিবর্তন হতে দেখা যায়। অর্থাৎ সকালে যে উচ্চতায় আয়নোস্ফিয়ারের দেখা পাওয়া যায় রাতে কিন্তু সেই উচ্চতায় আয়নোস্ফিয়ারের দেখা পাওয়া যায় না। সাধারণ ভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরে ৫০-৯০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ডি স্তর। অর্থাৎ ওজন স্তরের উপরে, মেসোস্ফিয়ার মণ্ডলে গঠিত হয় ডি স্তর। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কেবলমাত্র দিনের বেলাতেই এই ডি স্তর গঠিত হয়। রাত্রে ডি স্তরের দেখা পাওয়া যায় না। রাত্রে ডি স্তরের অনুপস্থিতি ও পরিবর্তনশীল উচ্চতার জন্যই বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদের মধ্যে আয়নোস্ফিয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। ভূপৃষ্ঠের উপর ১০০-১২৫ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ই স্তর এবং ১৫০-৫০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এফ স্তর। থার্মোস্ফিয়ারের অঞ্চলে ই ও এফ স্তরের দেখা পাওয়া যায়। দিনের বেলায় আবার এফ স্তরের মধ্যে দু’টো উপস্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দুই উপস্তরকে এফ১ ও এফ২ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ৩০০ কিমি আশেপাশের স্তরকে এফ১ এবং ৪০০ কিমি আশেপাশের স্তরকে এফ২ বলা হয়। রাতের বেলায় অবশ্য এই দুই স্তর মিশে হয়ে যায় এবং একটা গোটা এফ স্তর সৃষ্টি হয়।
এখন জানা প্রয়োজন, দিন-রাত ও ঋতু ভেদে আয়নোস্ফিয়ারের অবস্থানের তারতম্য ঘটে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে। সাধারণ ভাবে আমরা যাকে ‘আলো’ বলে থাকি পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় তা হলো আদতে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। আলোচ্য রেডিও ওয়েভও এই রকমই এক তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে গঠিত রশ্মিগুলো তরঙ্গ বা ঢেউয়ের আকারে প্রবাহিত হয় বলে এই জাতীয় রশ্মিকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়। পরপর দু’টো তরঙ্গের শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়। এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি বলে। জানা প্রয়োজন, যে রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোটো তার কম্পাঙ্ক তত বেশি হয় আর যে রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বড় হয় তার কম্পাঙ্ক তত কম হয়। ছোটো থেকে বড় বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মির নাম, তাদের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচের তালিকায় দেওয়া হল
নাম কম্পাঙ্ক (হার্জ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার) গামা রশ্মি ৩x১০১৯ ১x১০-১১ এক্স রে ৩x১০১৬ - ৩x১০১৯ ১x১০-১১ - ১x১০-৮ অতিবেগুনি রশ্মি ৭.৫x১০১৪ - ৩x১০১৬ ১x১০-৮ - ৪x১০-৭ দৃশ্যমান আলো ৪x১০১৪ - ৭.৫x১০১৪ ৪x১০-৭ - ৭x১০-৭ অবলোহিত রশ্মি ৩x১০১১ - ৪x১০১৪ ৭x১০-৭ - ১*১০-৩ মাইক্রো ওয়েভ ৩x১০৯ - ৩x১০১১ ১x১০-৩ - ১x১০-১ রেডিও ওয়েভ < ৩x১০৯ > ১x১০-১ এই সমস্ত রশ্মিগুলোর মধ্যে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম (বা, কম্পাঙ্ক যত বেশি) তাদের শক্তি তত বেশি হয়। গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এই রশ্মিগুলোর শক্তি অনেক বেশি হয়। এই তিন শক্তিশালী রশ্মির অন্য কোনও বস্তুকে (মূলত গ্যাসকে) আয়নিত করার ক্ষমতা বিদ্যমান। সাধারণ আলো, অবলোহিত রশ্মি, মাইক্রো ওয়েভ ও রেডিও ওয়েভের অন্য গ্যাসকে আয়নিত করার ক্ষমতা নেই। ‘আয়নিত করা’ কথাটার অর্থ হলো নিস্তড়িৎ কোনও গ্যাসের স্তরকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভাজিত করা। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা আমাদের প্রত্যেকেরই প্রায় আছে। আমরা জানি, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণা। এই ইলেকট্রন গুলো খুবই চঞ্চল প্রকৃতির হয়। বাহ্যিক শক্তির (তাপ, চাপ, আলো ইত্যাদি) প্রভাবে দ্রুত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এরা এবং এদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত পরমাণুর কক্ষ ত্যাগ করে মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে প্রকৃতিতে অবস্থান করে। পরমাণু থেকে ঋণাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রন বেড়িয়ে গেলে পরমাণু ধনাত্মক আধান যুক্ত আয়নে পরিণত হয়। সূর্য থেকে আসা অধিক শক্তি সম্পন্ন রশ্মিগুলোর প্রভাবে বায়ুমন্ডলের নিস্তড়িৎ গ্যাসগুলোর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে পরমাণুর কক্ষ ত্যাগ করে। ফলে বায়ুমন্ডল মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নে বিভাজিত হয়। আয়ন দিয়ে নির্মিত এই স্তরকে ‘আয়নোস্ফিয়ার’ বলা হয়। আয়নোস্ফিয়ার নামটা প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ ওয়াটসন-ওয়াট (পুরো নাম : Robert Alexander Watson-Watt, ১৮৯২-১৯৭৩)। ৮ই নভেম্বর ১৯২৬ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি প্রথম ‘আয়নোস্ফিয়ার’ নামটা প্রথম ব্যবহার করেন। পরে বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটা আয়নোস্ফিয়ার নামেই পরিচিত হয়ে উঠে।
স্পষ্টতই সূর্য থেকে আসা কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত রশ্মির প্রভাবে আয়নোস্ফিয়ার গঠিত হয়। ঠিক সেই কারণেই সূর্য ওঠার দু’এক ঘন্টার মধ্যেই এই ডি স্তর গঠন পক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে দ্রত এই স্তর গায়েবও হয়ে হয়ে যায়। ঠিক একই কারণে দিনে ও রাতে ই ও এফ স্তরের ইলেকট্রন ঘনত্বের তারতম্য ঘটে থাকে। সূর্যালোকের প্রভাবে সকালের দিকে এই স্তরগুলোর ইলেকট্রন ঘনত্ব অনেক বেশি হয়। রাতের দিকে আবার এই স্তর গুলোর ইলেকট্রন ঘনত্ব কমে যায়। তবে ডি স্তরের মতো অস্থায়ী নয় ই বা এফ স্তর দু’টো। ২৪ ঘন্টাই এই স্তর দুটোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ডি স্তরের মতো সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যায় না এরা। কিন্তু কেন? কেন ডি স্তরের মতো রাত্তির বেলায় গায়েব হয়ে যায় না ই ও এফ স্তর? আসলে বায়ুমণ্ডল আয়নিত হয় দু’টো পদ্ধতিতে- ১) আলোর প্রভাবে (Photo Ionization) ২) কণার প্রভাবে (Corpuscular Ionization)। তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি ছাড়াও সূর্য থেকে অবিরত নির্গত হয়ে চলেছে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি আয়নিত কণা। সূর্য থেকে সেকেন্ডে প্রায় ৯০০ কিমি বেগে উদ্গীরিত হয়ে অনন্তের পথে ধেয়ে চলেছে এই কণার স্রোত। আয়নিত এই কণার স্রোতকে সোলার উইন্ড বলা হয়। এই সোলার উইন্ডের স্রোতকে ভেদ করেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে পৃথিবী। এই সোলার উইন্ডের সংস্পর্শে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরে গঠিত হয় আয়নোস্ফিয়ারের এফ ও ই স্তর। যেহেতু পৃথিবীর চতুর্দিক দিয়েই বয়ে চলেছে সোলার উইন্ড, তাই দিনই হোক আর রাত, সবসময়েই এফ ও ই স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দিনের বেলায় সূর্যালোকের প্রভাবে এফ স্তর আবার দু’টো উপস্তরে ভেঙ্গে যায়। এই এফ স্তর ভেদ করে অতিবেগুনি ও এক্স রশ্মি ঢুকে পড়ে বায়ু মন্ডলে। এই রশ্মির প্রভাবে গঠিত হয় ডি স্তর, ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ই স্তরের। মূলত নাইট্রিক অক্সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়ন এবং মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি দেখা যায় ডি স্তরে। ই স্তর গঠিত হয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের প্রভাবে।
বায়ুমণ্ডলে গঠিত এই আয়নোস্ফিয়ার (এবং ওজনোস্ফিয়ার) তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মিদের অন্তরকের কাজ করে। নির্দিষ্ট কিছু তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে ছাড়া অন্য কোনও তরঙ্গকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছতে বাধা দেয় এরা। এই বাধা দেওয়ার ফলেই এক্স রশ্মি, হার্ড ইউভি বা কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি, মাইক্রো ওয়েভের একটা অংশ, রেডিও ওয়েভের একটা অংশ পৌঁছতে পারে না পৃথিবী পৃষ্ঠে। ওজনোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ারের এই বাধা টপকে আলো, কিছু নির্বাচিত অবলোহিত রশ্মি ও কিছু নির্বাচিত রেডিও ওয়েভই কেবল মাত্র পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে। ওজনোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ার যেন পৃথিবীর জানালার কাজ করে। সব তরঙ্গকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না। এই ঘটনাটাকে অ্যাটমোস্ফিয়ারিক উইন্ডো বলা হয়। এই অ্যাটমোস্ফিয়ারিক উইন্ডো মানুষের পক্ষে যেমন স্বস্তির কারণ, একই সাথে এই উইন্ডো মানুষের অস্বস্তির কারণও বটে। বায়ুমন্ডলের এই বাধা দেওয়ার ফলে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে প্রয়োজনীয় রেডিও ও অন্যান্য তরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছতে পারে না। ফলে মহাকাশের বিভিন্ন তরঙ্গ অধরাই রয়ে যায় পৃথিবী পৃষ্ঠে। মহাকাশ থেকে আগত এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আয়নোস্ফিয়ারের উপরে উঠতে হবে আমাদের। আর ঠিক এই কারণে ইন্টারনেশান্যাল স্পেস স্টেশন বা হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে রাখা হয়েছে আয়নোস্ফিয়ারের ঠিক উপরের স্তরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০ কিমি দূরে।
শুধুমাত্র বাইরের থেকে আসা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকেই যে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয় আয়নোস্ফিয়ার তা নয়, একই সাথে ও একই ভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকেও মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় সে। সেই কারণেই পৃথিবী থেকে রেডিও ওয়েভও মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে (প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন ঘটে থাকে, যে ভাবে মরুভূমিতে মরীচিকা গঠিত হয়) সে তরঙ্গ ফিরে আসে পৃথিবীতে। ঠিক এই ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে রেডিও ওয়েভের প্রতিফলন ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি (পুরো নাম : Guglielmo Marconi, ১৮৭৪-১৯৩৭)। ১৯০১ সালে ইংলন্ডের কর্নওয়াল প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তের ফোলডু (Poldhu) গ্রাম থেকে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করেন মার্কনি। ফোলডু থেকে ৩৫০০ কিমি দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ে কানাডার নিউফাউনল্যান্ডের পূর্ব প্রান্তের সেন্ট জন’সে সেই তরঙ্গকে রিসিভ করেন মার্কনি। মার্কনির এই পরীক্ষা আলোড়ন সৃষ্টি করে পদার্থ বিজ্ঞান মহলে। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যই ১৯০৯ সালে নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে। না, সঠিক অর্থে, রেডিও ওয়েভ প্রেরণের জন্য এতো আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি পৃথিবীতে। কেননা, রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করাটা খুব নতুন কোনও ঘটনা ছিল না তখন। ইতিপূর্বে ১৮৯৪ সাল থেকে বহুবার রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ করে নিজের কাজকে ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং মার্কনি।
সমসময়ের অনেকেই রেডিও ওয়েভ নিয়ে কাজ করেছেন এবং রেডিও ওয়েভ প্রেরণে সফলও হয়েছেন তাঁরা। ১৮৯৫ সালে কলকাতার টাউন হলে সর্ব সমক্ষে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করেন জগদীশচন্দ্র বসু। ফলে ১৯০১ সালে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করাটা কোনও চমকপ্রদ ঘটনাই ছিল না। তবুও মার্কনির সেই পরীক্ষায় বিস্মিত হয়েছিল গোটা দুনিয়া। তাঁদের বিস্ময়ের কারণ হলো- দূরত্ব। মার্কনি সেবার ৩৫০০ কিমি দূরে রেডিও ওয়েভ পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এতো দূরে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করেন নি কেউই। তাঁর নিজের করা বিভিন্ন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৫-৬ কিমি দূরে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করেছিলেন মার্কনি। ১৮৯৫ সালের টাউন হলের পরীক্ষায় ৭৫ ফুট দূরে রেডিও ওয়েভ প্রেরণে সফল হয়েছিলেন জগদীশ্চন্দ্র বোস। এই সমস্ত দূরত্বের তুলনায় ৩৫০০ কিমি দূরত্ব একটা বিস্ময় বই কি!কেন, দূরত্বের প্রশ্নে এতো বিস্ময় সৃষ্টি হলো কেন? মার্কনির পরীক্ষায় বিস্ময় উদ্রেক হওয়ার পিছনে নিহিত ছিল আর একটা কারণ। মার্কনির সমসময়ে আলোর সরলরৈখিক গতি, আলোর প্রতিফলন, আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানতেন আলো হলো এক বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। তারা জানতেন সমস্ত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গই আলোর মতো সরলরেখায় চলে। রেডিও ওয়েভ যেহেতু তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ তাই সেই ওয়েভও সরলরেখায় চলে। কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ৫-৬ কিমি দূরের কোনও আলো যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনই ৫-৬ কিমি দূরে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করাটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু তাই বলে ইংলন্ডে আলো জ্বালালে কি তা কানাডা থেকে দেখা সম্ভব? ঠিক তেমনই ইংলন্ড থেকে রেডিও ওয়েভ প্রেরণ করলে তা কি কানাডায় পৌঁছন সম্ভব? তাছাড়া পৃথিবী পৃষ্ঠ হলো গোলকাকার। আর রেডিও ওয়েভ চলে সরলরেখায়। তাহলে বক্রপৃষ্ঠ বেয়ে সেই তরঙ্গ কি ভাবে পৌঁছল কানাডায়? স্তম্ভিত বিজ্ঞান মহল।
তবে কি আলোর মতোই প্রতিফলিত হয়েছে রেডিও ওয়েভ? তাছাড়া আর তো কোনও ব্যাখ্যা মাথায় আসছে না বিজ্ঞানীদের। কিন্তু কোথায় সেই প্রতিফলক? কোথা থেকে প্রতিফলিত হলো রেডিও তরঙ্গ? মার্কনির পরীক্ষাকে প্রথম সফল ভাবে ব্যাখ্যা করেন ইউএসএর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আর্থার কেনলি (পুরো নাম : Arthur Edwin Kennelley, ১৮৬১-১৯৩৯)। ১৫ই মার্চ ১৯০২ সালে বায়ুমন্ডলে রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলনের কথা বলেন কেনলি। কয়েক মাস পরই, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯০২ সালে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ অলিভার হেভিসাইডও (Oliver Heaviside, ১৮৫০-১৯২৫) স্বতন্ত্র ভাবে একই সিদ্ধন্তে উপনীত হন। গণিতের সাহায্য নিয়ে তাঁরা দেখান পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৮০ কিমি ঊর্ধ্বে কোনও স্তরের প্রতিফলিত হয়ে রেডিও তরঙ্গ ফিরে আসছে পৃথিবীতে। ক্রমেই এই স্তরটা কেনলি-হেভিসাইড স্তর নামে পরিচিতি হয় (বর্তমানে এই স্তরটা ই স্তর নামে পরিচিত)। কেনলি ও হেভিসাইডের গাণিতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে রেডিও ওয়েভ প্রতিফলনকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা গেলেও বাস্তবে সেই স্তরের অস্তিত্ব কিন্ত তখনও প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি। ১৯২৪ সালে কেনলি-হেভিসাইড স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ অ্যাপেলটন (পুরো নাম : Edward Victor Appleton, ১৮৯২-১৯৬৫)।
দক্ষিণ ইংলন্ডের ইংলিশ চ্যানেলের পাড়ে অবস্থিত বোর্নমথ শহরে বিবিসির ট্রান্সমিটারের সাহায্যে রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ করেন অ্যাপেলটন। প্রায় ২৫০ কিমি দূরের কেমব্রিজ শহরে সেই তরঙ্গ রিসিভ করা হয়। তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহনের সময়, ফ্রিকোয়েন্সি, তরঙ্গ উৎক্ষেপনের কোন ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করে কেনলি-হেভিসাইড স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তিনি। প্রাথমিক এই সাফল্যের পর, তাঁর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অক্ষুন্ন রাখেন অ্যাপেল্টন। ১৯২৬ সালে এমনই এক পরীক্ষায় আরও একটা স্তরের হদিশ পান অ্যাপেলটন। কেনলি-হেভিসাইড স্তরের উপরে প্রায় ২৫০-৩০০ কিমিতে এই স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তিনি। নতুন এই স্তরটা তখন অ্যাপেলটন স্তর নামে পরিচিতি পায় (অধুনা এই স্তর এফ স্তর নামে পরিচিত)। ২৯শে জুন ১৯২৭ সালের এক সূর্য গ্রহণের সময় একই ভাবে আবার পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন অ্যাপেলটন। সেই সূর্য গ্রহনের সময় রেডিও ওয়েভ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে দেখেন যে তাঁর আবিষ্কৃত অ্যাপেলটন স্তর অনেকটা উপরে উঠে গেছে। এই পর্যবেক্ষন থেকে তিনি আয়নোস্ফিয়ার গঠনে সূর্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথম দিন রাতে আয়নোস্ফিয়ারের অবস্থান বদলের কারণ ব্যাখ্যা করে। ১৯২৮ সালে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আরেকটা স্তর থাকার কথা বলেন অ্যাপেলটন। ৫০ থেকে ৯০ কিমির মধ্যে এই স্তর থাকা সম্ভব বলে অনুমান করেন তিনি। এই স্তরটাকে ডি স্তর নামে অভিহিত করেন তিনি। আগের দু’টো স্তরে প্রচলিত নামের বদলে ই ও এফ স্তর নাম দেন (নিজের নামাঙ্কিত স্তরের নাম নিজেই খারিজ করে দেন!)। এই ভাবে প্রায় একার হাতে সমগ্র আয়নোস্ফিয়ারকে সজিয়ে তুললেন অ্যাপেলটন। তাঁর অনবদ্য ও সৃজনশীল এই কাজের স্বীকৃতিতে ১৯৪৭ সালে নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে।।। ৫ ।।
১৯২৩ সালে শিশিরে উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এসসি. পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয় রেডিও বিজ্ঞান। এই পাঠ্যক্রম আকর্ষণ করে এক ঝাঁক বাঙালি তরুণকে। প্রথম বছর থেকে শুরু করে প্রতি বছর বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন গবেষকের জন্ম হয় শিশিরের ওই গবেষণাগার থেকে। শিশিরের সহযোগী হিসেবে আয়নোস্ফিয়ার ও রেডিও সংক্রান্ত গবেষণায় সামিল হলেন তাঁদের অনেকেই। শিশিরে প্রথম ব্যাচের উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন ঋষিকেশ রক্ষিত, ভবানী চরণ শীল, এস.এন রায়, এ.সি চ্যাটার্জী প্রমুখ। পরবর্তী বছর গুলোতে যতীন্দ্রনাথ ভর, পি. সাম, সতীশ রঞ্জন খাস্তগির (ঢাকায় অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন স্থাপনের অন্যতম কারিগর), মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত, এস.এস. বড়াল, এ.পি. মিত্র, এম.আর. কুন্ডু, বি.এন. ঘোষ, শৈলেন পুরকায়স্থ, সমেত প্রায় ৬৫–৭০ জন উল্লেখযোগ্য এমন ছাত্র পেয়েছিলেন তিনি যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে তাঁর গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই সমস্ত ছাত্রদের কেউ খড়্গপুর আইআইটির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন, তো কেউ নেভি বা মিলিটারিতে রেডিও বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, কেউ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন তো কেউ দিল্লীর বিজ্ঞান দপ্তরের মুখ্য প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। এই সমস্ত মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে জীবনের আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করলেন শিশির। এই সমস্ত ছাত্রদের প্রায় হাতে ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি শেখালেন তিনি। শেখালেন কত সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের বক্তব্যকে উপস্থিত করা যায় সাধারণের কাছে। এই ছাত্রকুলের সাথে যৌথ উদ্যোগে লিখেছেন প্রবন্ধ। ছাত্রদের নিজেদের লেখা প্রবন্ধ ছাপানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সেই সময়ের ছাত্র মৃণাল কুমার এক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন- টেলিভিশন নিয়ে ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবে ভাষণ দেওয়ার কথা স্যরের। টেলিভিশন নিয়ে কিছু নোট জোগার করে দিতে বললেন আমায়। সেই সময়ে (৪০ দশকে) টেলিভিশন নিয়ে খুব একটা লেখা পত্র পাওয়া যেত না। তবুও স্যরের নির্দেশ মতো যথাসাধ্য চেষ্টা করে সংগ্রহ করি কিছু তথ্য। সেই নোট নিয়েই বক্তব্য রাখলেন স্যর। পরে তিনি আমায় বলেন, প্রচন্ড পরিশ্রম করে তৈরি করেছো নোটটা। এটাকে গুছিয়ে লেখ, আমি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেবো। স্যরের নির্দেশে গুছিয়ে লিখি নোটটা। পরে সেই নিবন্ধটা একক ভাবে এম.কে. দাশগুপ্ত নামে প্রকাশ হয়। লেখক হিসেবে স্যরের নাম ছিল না সেই প্রবন্ধে। ঘটনাটা বিস্মিত করে আমায়। তবে ফুট নোটে লেখা ছিল ‘রোটারি ক্লাবে প্রদত্ত প্রফেসর মিত্রর বক্তৃতার ভিত্তিতে লেখা’।
মৃণাল আরও লিখেছেন, প্রতিদিন ঘড়ি ধরে ঠিক ১০.৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেন স্যর। তাঁর সময়ানুবর্তীতা প্রভাবিত করছিল তাঁর ছাত্রদের। সমস্ত ছাত্ররা প্রতিদিন ১০.৩০ মিনিটের আগেই ক্লাসে উপস্থিত হতেন। কেউ দেরি করেতেন না। তাঁর শিক্ষক প্রসঙ্গে মৃণাল আরও লিখেছেন, অধিকাংশ সময়ে স্যুট বুট টাই পড়ে থাকতেন স্যর। এই ড্রেসকোডের কারণে ‘বাবু’ না বলে তাঁকে ‘সাহেব’ বলেই অভিহিত করতেন সবাই। মৃণাল লিখেছেন, তবে অনুষ্ঠান বাড়িতে কিন্তু পূর্ণ বাঙালি বাবুর মতো ধুতি পাঞ্জাবি পড়েই উপস্থিত হতেন স্যর। আর সেই নিখাদ বাঙালি বেশেও চমৎকার মানাতো তাঁকে।
কয়েক বছরের মধ্যেই বালিগঞ্জে নিজের একটা বাড়ি নির্মাণ করে ফেললেন শিশির। সেই বাড়ির একটা অংশে তাঁর নিজস্ব মানমন্দির ও গবেষণাগার গড়ে তুললেন তিনি। কলেজের কাজ শেষ করেই নিজের গবেষণাগারে ঢুকে যেতেন শিশির। গভীর রাত পর্যন্ত কাটাতেন সেই গবেষণাগারেই। তাঁর ছাত্রদেরও অবাধ যাতায়াত ছিল সেই গবেষণাগারে। আর এই ব্যাপারে তাঁর পাশে দাঁডিয়ে তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর স্ত্রী লীলাবতী। শিশিরে এই কাজের চাপের মধ্যে এক নাগাড়ে তাঁকে সহযোগিতা করে গেছেন লীলাবতী। শুধু শিশির কেন শিশিরের ছাত্রদেরও সমান ভাবেই পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্চা করতেন লীলাবতী।
শিশিরের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হৃষিকেশ রক্ষিত দীর্ঘদিন ধরে শিশিরে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন। রক্ষিত ও শিশির মিলিত ভাবে একাধিক নতুন গবেষণা শুরু করেন। রক্ষিতের প্রথম উল্লেখযোগ্য ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ হলো কলকাতা ও তার উপকন্ঠের প্রায় ৭৫ মাইল এলাকা জুড়ে ২০০টা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ‘রেডিও ফিল্ড স্ট্রেন্থ’ পরিমাপ করা। বলা যায় প্রায় একার হাতে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের রেডিও স্ট্রেন্থ নির্ণয় করেন রক্ষিত। দীর্ঘ দিন ধরে এক নাগাড়ে বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংগ্রহ করেন রক্ষিত। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা পর, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় রক্ষিতের প্রবন্ধ Radio field-strength survey of the city of Calcutta and its suburbs. আজ আমরা যে রেডিও পরষেবা গ্রহণ করে থাকি, সেই পরিষেবার ভিত্তভূমি রচনা করে গেছেন শিশির এবং রক্ষিত।
রক্ষিতের মতোই পরিশ্রমী ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন শিশিরের ছাত্র মহল। এই সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করতে থাকেন তিনি। কি দিন কি রাত সর্বদাই আয়নোস্ফিয়ারে তরঙ্গ প্রেরণ ও তথ্য সংগ্রহে নিমগ্ন ছিলেন শিশির ও তাঁর ছাত্রকুল। শুধু দিন বা রাত নয়, ঝড়, বজ্রপাত, উল্কাপাত, সূর্য গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার সাথে আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করতে থাকেন তাঁরা। বস্তুতপক্ষে ক্রান্তীয় অঞ্চলে আয়নোস্ফিয়ার নিয়ে এতো বিস্তারিত গবেষণা ইতিপূর্বে করেন নি কেউই। অত্যন্ত আধুনিক ও নিতান্তই প্রয়োজনীয় এই গবেষণা কলকাতা তথা ভারতের রেডিও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন তাঁরা। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এস.কে মিত্র, এইচ. রক্ষিত, পি. সাম, বি.এন. ঘোষের নিবন্ধ Effect of the Solar Eclipse on the Ionosphere. ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এস.কে মিত্র, পি. সাম, বি.এন. ঘোষের প্রবন্ধ ‘Effect of a Meteoric Shower on the Ionosphere’. শিশিরের ছাত্ররাও একক ও যৌথভাব বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন তাঁদের লেখা প্রবন্ধ। শিশির ও তাঁর ছাত্রদের নিরবিচ্ছিন্ন এই গবেষণার ফসল হিসেবে ধরা পড়ল আয়নোস্ফিয়ারের ডি স্তর। তাঁদের গবেষণায় উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাঁদের পাওয়া হিসাব অনুসারে ভূপৃষ্ঠের ৫৫ কিমি উপর থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে রেডিও ওয়েভ। এই স্তরটাই আপলটন বর্ণিত ডি স্তর। অ্যাপেলটন ডি স্তরে কথা অনুমান করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই স্তরের সঠিক হদিশ দিতে পারেন নি। ডি স্তরের উপস্থিতি প্রমাণ করে যারপরনাই উচ্ছ্বিসিত শিশির ও তাঁর ছাত্র মহল। শুধু তাই নয়, শিশির ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণা থেকে উঠে এলো আরও চাঞ্চল্যকর এক তথ্য। ২০-৩০ কিমি উপরের এক স্তর থেকেও প্রতিফলিত হচ্ছে রেডিও তরঙ্গ। তাঁদের গবেষণায় অন্তত ধরা পড়েছে সেই সত্য। ডি স্তরের থেকেও নিচে রয়েছে আরেক স্তর! স্বয়ং অ্যাপেলটনও হদিশ পান নি এই স্তরের। অ্যাপেলটনের নামকরণের ধারাবাহিকতা মেনে, শিশির ও তাঁর সহযোগীরা নতুন এই স্তরে নাম দিলেন সি স্তর। ডি স্তরের উচ্চতা ও নতুন সি স্তরের উপস্থিতির প্রমান নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন শিশির। ১৯৩৫ সালের ৮ই জুন নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিশির কুমার মিত্র ও পি. সামের নিবন্ধ Absorbing Layer of the Ionosphere at low Height. ২৩শে মে ১৯৩৬ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিশিরে প্রবন্ধ Return of radio waves from middle atmosphere. এই দু’টো নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে শিশির তাঁর জীবনের সেরা গবেষনার কথা প্রকাশ করেন বিশ্বের দরবারে। শিশিরে গবেষণার ফলাফলে বিস্মিত সারা দুনিয়া। সি স্তর?! বলে কি এই ভারতীয় গবেষক? সি স্তর আবার হয় নাকি? একরাশ সন্দেহ নিয়ে সি স্তর খুঁজতে বসলেন পৃথিবীর নানান প্রান্তের গবেষক। অবশেষে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংলন্ড, ইউএসএসের বিজ্ঞানীরা শিশিরে পর্যবেক্ষণকে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁরা জানান ডি স্তরের নিচে আরও একটা অস্থায়ী স্তর গঠিত হয়। খুব লো ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভে ধরা পড়ছে এই স্তর। বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞায় অবশ্য সি স্তরকে পৃথক কোনও স্তরের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। এই স্তর আছে এটা সত্য, কিন্তু এই স্তরটাকে ডি স্তরের অংশ হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে।
সি স্তর নিয়ে গবেষণাই শিশিরের জীবনের সেরা প্রাপ্তি। এই গবেষণাই তাঁকে দেয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিশ্বজোড়া খ্যাতি। শিশির তখন ভারতের অ্যাপেলটন হিসেবে মান্যতা পাচ্ছেন। ১৯৩৫ সালে ইংলন্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের ২৫ বছর রাজত্বকাল পূর্ণ হয়। এই ঘটনার স্মরণে কমনওয়েলথ দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সেই তালিকায় যুক্ত করা হয় শিশিরের নাম। ৬ই মে ১৯৩৫ সালে ‘কিং জর্জ ফাইভ সিলভার জুবিলি মেডেল’ দিয়ে সম্মানিত করা হয় শিশিরকে। জামসেদজি টাটা সমেত একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯০৯ সালে গড়ে উঠে বেসরকারী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইন্ডিয়া’। ১৯৩৫ সালের অগস্ট মাসে আয়নোস্পিয়ারের উপর একটা সভা আয়োজন করে এই সংস্থা। শিশিরকে সেই সভা উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সভায় এক উদ্বোধনী রিপোর্ট পাঠ করেন শিশির। ৭৪ পাতার Report on the present state of our knowledge of the ionosphere নিবন্ধে আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে অত্যাধুনিক মতামত রাখেন তিনি। সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই এই রিপোর্টের প্রশংসা করেন। এটা রিপোর্ট হিসেবে না ছাপিয়ে বরং পূর্ণাঙ্গ বই আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন অনেকেই।
১৯৩৫ সালের পর থেকে শিশিরের জীবন প্রবেশ করে ভিন্ন এক পর্যায়ে। এই পর্যায়ে গবেষক শিশিরের পাশাপাশি এক দক্ষ সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন শিশির। শিশির তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক গবেষক। কিন্তু খ্যাতি নিয়ে আদৌ ভাবিত নন শিশির। তিনি বরং চান আরও প্রসারিত হোক গবেষণার সুযোগ। আয়নোস্ফিয়ার ও রেডিও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিশেষ সুযোগ নেই ভারতে। নেই গবেষণার পরিকাঠামো, নেই আধুনিক যন্ত্র, নেই অর্থ। খ্যাতি নয়, শিশির চান বিজ্ঞান পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। এই সমস্ত মতামত ব্যক্ত করার এক দারুণ সুযোগও এসে গেল শিশিরের কাছে। ১৯৩৬ সালে ৬ মাসের জন্য ব্রিটেন যান শিশির। ইংলন্ডের বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা করেন তিনি এই সময়ে। ৫ই মে অনুষ্ঠিত এক ‘আফটার ডিনার স্পিচ’এ বক্তৃতা করেন শিশির। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, ১০ বছর আগে কলকাতায় রেডিও গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন তিনি কিন্তু তারপর থেকে সরকার তরফে তেমন কোনও আর্থিক সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া যায় নি। শুধু মাত্র কলকাতায় বসে তো আর আয়নোস্ফিয়ার বা রেডিও বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। সাড়া ভারতবর্ষ জুড়ে প্রয়োজন রেডিও গবেষণার। ইংলন্ডের ‘রেডিও রিসার্চ বোর্ড’এর মতো শুধুমাত্র রেডিও গবেষণার জন্য ভারতেও ‘রেডিও রিসার্চ বোর্ড’ স্থাপনের অনুরোধ করেন তিনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেডিও গবেষকদের পারস্পরিক সহযোগিতার কথাও বলেন তিনি। সেদিনের সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন অ্যাপেলটন, ওয়াটসন-ওয়াট, চ্যাপম্যান সমেত বিখ্যাত সব রেডিও বিশেষজ্ঞরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন নেচার পত্রিকার সম্পাদক গ্রেগরি, উপস্থিত ছিলেন প্রভাবশালী প্রশাসকরাও। শিশিরে কর্মকান্ডের সাথে তখন অনেকেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জানেন সমকালীন পৃথিবীতে রেডিও গবেষণায় শিশির এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এহেন শিশিরে গবেষণাগারের হাল ও ভবিষ্যৎ শুনে বিস্মিত হন অনেকেই। সভায় চাপা গুঞ্জন উঠে। পরবর্তী কালে নেচার পত্রিকার সম্পাদক কলম ধরেন শিশিরের পক্ষে। এক সম্পাদকীয়তে ভারতে রেডিও রিসার্চ বোর্ড গঠনের দাবির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলে তৈরি হয় সহানুভূতির হাওয়া। টনক নড়ে ইংরেজ সরকারের। ভারতে রেডিও গবেষণার উদ্যোগ নেয় ব্রিটিশ সরকার।
ইংলন্ড সফর সেরে ভারতে ফিরে এসেও লাগাতার ভাবে ভারত সরকারের কাছে রেডিও রিসার্চ বোর্ড গঠনের জন্য তদবির করতে থাকেন শিশির। শুধু তাত্ত্বিক গবেষণাই নয়, শিশির চান রেডিও বিজ্ঞানকে যেন শিল্প ক্ষেত্রেও সফল ভাবে প্রয়োগ করা হয়। ৩০ দশকের শেষের দিকে থেকে ভারতের মাটিতে প্রাপ্ত কাঁচামাল মাল ব্যবহার করে রেডিও গবেষণার যন্ত্রপাতি ও রেডিও সেট নির্মাণের উপর জোর দিতে থাকেন শিশির। শিশিরে উদ্যোগকে পূর্ণ সমর্থন জানান তাঁর পূর্বতন সহকর্মী ও বন্ধু মেঘনাদ সাহা। শিশির ও মেঘনাদের তদবিরে, ইংরেজ ও ইওরোপীয় গবেষকদের সমর্থনে, ৩ বছর পর, ১৯৩৯ সালে শিশিরের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় ভারত সরকার। সরকারের তরফ থেকে, ভারত জুড়ে রেডিও গবেষণার রূপরেখা ও তার সাংগঠনিক প্রস্তুতির ভার ন্যস্ত করা হয় শিশিরের উপর। শিশিরও সাগ্রহে তাঁর পরিকল্পনার রূপরেখা আঁকতে শুরু করলেন। অসম্ভব কর্মব্যস্ত এই সময়ে শিশির জড়িয়ে পড়লেন দুঃসহ এক মানসিক যন্ত্রণায়। আগাগোড়াই হাঁপানি রোগে ভুগতেন তাঁর স্ত্রী লীলাবতী। ১৯৩৯ সালে হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন লীলাবতী। শিশিরের সহধর্মিনী হিসেবে শিশিরে পাশে থেকে নীরবে তাঁর কর্মকান্ডে সহযোগিতা করে গিয়েছেন লীলাবতী। লীলাবতী মৃত্যুতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন শিশির। লীলাবতীর অনুপস্থিতিতে সাংসারিক দিক দিয়ে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে শিশিরের জীবন। কয়েক বছরের মধ্যেই উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে শিশিরের। ধরা পড়ে প্রোস্টেটের সমস্যাও। পরবর্তী সময়ে প্রোস্টেট অপারেশনও করাতে হয় তাঁকে। সাংসারিক ও শারীরিক প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বীয় ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন শিশির। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত হয় ‘কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ’। বিজ্ঞান ও শিল্পের মেল বন্ধন ঘটাতে গঠিত হয় এই কাউন্সিল। ভারতের যাবতীয় সরকারী গবেষণার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো এই কাউন্সিলের উপর। সেই গবেষণা যাতে শিল্পমুখী হয় সেই দিকে বিশেষ ধ্যান দেওয়া হয়। সেই জন্ম লগ্ন থেকেই ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে এই কাউন্সিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে এই সংস্থা। ১৯৫৮ সাল থেকে এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ‘শান্তি স্বরূপ ভাটনগর প্রাইজ ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি’ প্রদান করা হয়ে থাকে।
ভারত সরকারের উদ্যোগে ‘কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ’ গঠিত হওয়াটা ভারতের বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই খুশির খবর ছিল। খুশি শিশিরও। তবে শিশিরে মূল আকর্ষণ রেডিও বিজ্ঞান। তিনি চান ইংলন্ডের ধাঁচে ‘রেডিও রিসার্চ বোর্ড’ গঠন হোক ভারতেও। শিশিরের সেই প্রস্তাব এবার পাঠানো হলো কাউন্সিলের কাছে। শিশিরের প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দিয়ে কি আর উপায় আছে কাউন্সিলের কাছে? সাথে সাথেই অনুমোদন করা হলো শিশিরে প্রস্তাব। ১৯৪২ সালেই শিশিরে তত্ত্ববধানে এবং কাউন্সিলের অধীনে খোলা হলো ‘রেডিও রিসার্চ কমিটি’। শিশির হন তাঁর প্রথম চেয়ারম্যান (পরে মেঘনাদ সাহা এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন)। শিশিরে প্রাক্তন ছাত্র যতীন্দ্রনাথ ভর কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। শিশির আগাগোড়াই চাইতেন ভারতের মাটিতেই তৈরি হোক গবেষণার যন্ত্রপাতি। শিশিরে সেই কর্মসূচিতে এবার সামিল হলেন ভর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রেডিও সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরির কি রকম পরিবেশ আছে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন ভর। প্রায় একার দায়িত্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে এই বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করলেন ভর। ১৯৪৩ সালে কাউন্সিলের দপ্তরে জমা দেওয়া হলো ভরের রিপোর্ট ‘Possibility of Radio Set manufacturing in India’. পরবর্তীকালে একই ভাবে জমা পড়ে এস.পি. চক্রবর্তীর রিপোর্ট ‘Manufacture of Wireless Apparatus in India’. সরকার কবে উদ্যোগ নেবে সেই আশায় বসে না থেকে, নিজের গবেষণাগারেই মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার, ডায়োড, ট্রায়োড ইত্যাদি যন্ত্র প্রস্তুত করা শুরু করেন শিশির। গবেষনাগার যে শিল্পতালুক নয় সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন শিশিরের। শিশির জানতেন দু’একটা মাইক্রোফোন বা ডায়োড বানানো আর কারখানায় ‘লার্জ স্কেল প্রোডাকশান’ এক নয়। তবুও এই ছোট্ট গবেষণাগারে এই উদ্যোগ নেওয়ার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য বানানো সম্ভব।
আয়নোস্ফিয়ার নিয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনার পাশাপাশি ভারতের মাটিতে শিল্প সহায়ক বিজ্ঞান পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অন্তরিকতার কোনও অভাব ছিল না শিশিরের মনে। শিল্প সহায়ক গবেষণায় নিরন্তর জোর দিয়ে গেছেন তিনি। কর্মব্যস্ত এই জীবনের ফাঁকেই আবার, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তিনি পরিমার্জন করে চলেছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইন্ডিয়ার উদ্বোধনী সভায় পঠিত তাঁর রিপোর্ট। পরিমার্জন না বলে বরং বলা ভালো নতুন করে লিখে চলেছেন এক বই। আয়নোস্ফিয়ারের উপর অত্যাধুনিক তথ্যযুক্ত সম্পূর্ন একটা বই। এই বই লেখাতে তাঁকে বিশেষ উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন তাঁর একান্ত সুহৃদ মেঘনাদ সাহা। আয়নোস্ফিয়ার ও রেডিও বিজ্ঞানে শিশিরে আধুনিক ধারণাকে আগাগোড়াই সম্ভ্রম করতেন মেঘনাদ। মেঘনাদ চাইতেন শিশির যেন তাঁর ধারণাকে গুছিয়ে উপস্থিত করেন বিজ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে। একপ্রকার মেঘনাদের তাগাদায় বই লেখার কাজ চালু রেখেছিলেন শিশির। ১৯৪৫ সাল নাগাদ অবশেষে শেষ করলেন তাঁর লেখার কাজ। ‘দ্য আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার’ নামে ৬০০ পাতার সুবিশাল এক গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন শিশির। অ্যাটমোস্ফিয়ার বা বায়ুমন্ডলের হালফিল তত্ত্বে ও তথ্যে ঠাসা সে বই। কিন্তু মুশকিল হলো কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই শিশিরে বই ছাপাতে রাজি হচ্ছেন না। হালফিলের বিজ্ঞানের বই পড়বে ক’জন? ক’কপি বিক্রি হবে এই সব বই? লাভ তো পরের কথা বিনিয়োগের টাকাটাও উঠবে না এই বই ছাপিয়ে। বিদেশের এক প্রকাশক তো জানিয়েই দিলেন-
প্রিয় মহাশয়,
১৬ই মে আপনার লেখা পত্র অত্যন্ত যত্ন নিয়েই পড়েছি আমরা। আপনার নাম যথেষ্টই পরিচিত আমাদের কাছে, আর স্বাভাবিক ভাবেই আমরা মনে করছি আপনার আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার এক প্রশংসনীয় কাজ। এতদ্সত্ত্বেও, দুঃখের সাথে আমরা জানাচ্ছি, বিবিধ কারণবশত আমরা মনে করি না এই প্রকশনার দায়িত্ব নেওয়া আমাদের পক্ষে বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত হবে।
এই পত্রের পরবর্তী অংশে তাঁর ‘এক্সট্রিমলি এক্সপেনসিভ’ ‘ফিনান্সিয়াল লস’এর কথাও উল্লেখ করেছেন। বেশ খানিকটা হতাশই হয়ে পড়লেন শিশির। এতো দিন ধরে পরিশ্রম করে এতো আধুনিক তথ্য দিয়ে সাজানো বইটা ছাপানোই হবে না শেষ পর্যন্ত? তাঁর এই চিন্তার দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর প্রিয় বন্ধু মেঘনাদ সাহা। মেঘনাদ সাহা তখন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি ছিলেন (১৯৪৫-৪৬)[৯]। মেঘনাদ ঠিক করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি ছাপাবে এই বই। এটা সত্যি যে এই বই ছাপানো এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষেও লাভজনক তো ছিলই না বরং ঝুঁকি পূর্ণ বিনিয়োগই ছিল। মেঘনাদ জানতেন তাঁর কর্মকালের মধ্যে এই বই ছাপার নির্দেশ জারি না হলে, এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেও এই বই প্রকাশ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। মেঘনাদ দ্বায়িত্বে থাকাকালীনই এই বই ছাপার দায়িত্ব নেয় সোসাইটি। প্রেসে ছাপতে দেওয়া হলো শিশিরে বই। ১৯৪৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয় ‘দ্য আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার’। আয়নোস্ফিয়ার জগতের গুরু অ্যাপেলটনকে বইটা উৎসর্গ করেন শিশির। বইটা প্রকাশের পরই রীতিমতো সাড়া পড়ে যায় ওয়াকিবহাল মহলে। ২০০০ কপি ছাপানো হয়েছিল বইটা। ৩ বছরে মধ্যেই বইটার প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। উত্তুঙ্গ চাহিদা দেখে বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমসময়ের বিজ্ঞান জগতে আয়নোস্ফিয়ার নিয়ে যে ক’টা বই বাজারে ছিল ‘দ্য আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার’ তাদের অগ্রগণ্য। বইটা প্রসঙ্গে অ্যাপেলটন স্বয়ং লেখেন, “This book is a Bible for the research workers on upper atmosphere”. ১৯৫২ সালের বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আরও পরে সোসাইটির তরফ থেকে বইটার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হয় শিশিরকে। ১৯৫৫ সালে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয় ‘দ্য আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার’। ইউএসএসআর তখন মহাকাশে স্পুৎনিক পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। স্পুৎনিক যেখানে ছাড়া হবে সেই আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা তো প্রয়োজন তাঁদের। সে আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার সম্পর্কে সব থেকে নিখুঁত ধারণা কোথায় পাওয়া যাবে? কেন, শিশিরের আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার গ্রন্থে। স্পুৎনিক উৎক্ষেপনের আগে তাই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল শিশিরে সেই বাইবেল তুল্য গ্রন্থ। ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর কক্ষ পথে সফল ভাবে স্পুৎনিক স্থাপন করে ইউএসএসআর। এই স্পুৎনিক থেকে পাঠানো বার্তা বিশ্লেষণ করে আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার সম্পর্ক নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের পথে অনেকটা এগিয়ে যায় ইউএসএসআর। এরপর পৃথিবীর কক্ষপথে একে একে প্রথম প্রাণী, প্রথম মানুষ পাঠিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দেয় তাঁরা। আর শিশির তখনও দেশের মাটিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে অক্লান্ত খেটে চলেছেন। শুধুমাত্র ভারতের মাটিতে তাঁর স্বপ্নকে সাকার করার লক্ষ্যে পরিশ্রম করে গেছেন তিনি। কোনও উন্নত দেশের সমতুল্য বিজ্ঞান পরিকাঠামোর সুবিধা পেলে শিশির হয়তো মহাসাগরে পরিণত হতো।
১৯২৫ সালে শিশিরের উদ্যোগেই ভারতে প্রথম ওয়্যারলেস পাঠক্রম চালু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে সেই পাঠ্যক্রম ছিল ঐচ্ছিক। কেউ সেই পাঠ্যক্রমে সামিল হতেও পারতেন, আবার ইচ্ছা না হলে নাও হতে পারতেন। শিশির মনে করেন, আর ঐচ্ছিক বিষয় নয়, ওয়্যারলেসকে এম.এসসি. পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করার সময় হয়েছে এখন। শুধু তাই তাই নয়। সেই পাঠ্যক্রম চালু করার পর ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারপর থেকে কত পরিবর্তন ঘটছে গেছে রেডিও বিজ্ঞানে। সংযুক্ত হয়েছে কত নতুন ধারনা। শিশির তাই চান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এসসি.তে চালু হোক নতুন পাঠক্রম, খোলা হোক নতুন বিভাগ। আয়নোস্ফিয়ার ও রেডিও বিজ্ঞানের পাশাপাশি কম্পিউটার, সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদিও পৃথক ভাবে চর্চা হোক। ১৯৪৬-৪৭ সাল, ভারতে তখন এক রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। খুব শিঘ্রই স্বাধীন হতে চলেছে ভারত। প্রশাসন পর্যায়ে রদবদলের পালা চলছে তখন। তবুও শিশির তাঁর আর্জি নিয়ে হাজির সরকারি দপ্তরে। ১৯৪৭ সালে শিশিরে প্রস্তাবে সায় দেন সরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হবে নতুন বিভাগ। অবশ্য এরপরই বিদায় নেয় ইংরেজ সরকার। স্বাধীন ভারতের মাটিতে, ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জন্ম নেয় শিশিরে স্বপ্নের পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠান ‘ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স’। শিশিরকেই এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে বসানো হয়। আমৃত্যু তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন। এতো কান্ডের পরও সামান্য একটু আফসোস যেন রয়েই গেল শিশিরের মনে। অর্থ না থাকায় রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি তিনি।
রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ আর গ্রহণের জন্য দূরবর্তী স্থানে আরেকটা গবেষণাগারের তো প্রয়োজন। সেই দ্বিতীয় গবেষণাগারে জন্য ফের ছুটোছুটি শুরু করলেন শিশির। দূরবর্তী স্থানে দ্বিতীয় সেই গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন সরকার। ‘কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ’ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় হরিণঘাটায় ৭৭ একর জমিতে স্থাপিত হয় ‘আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশন’। ১৯৪৯ সালে হরিণঘাটা গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় বলেন, “আশা করি ইন্সটিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে আমি আজ সেই বীজ বপন করলাম যা এক মহীরুহে পরিণত হবে, আমাদের বর্তমান প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে বহুদূর তার শাখা বিস্তৃত হবে”। ১৯৫৫ সালে চালু হয় হরিনঘাটা গবেষণাগার। শিশির হন সেই সংস্থার প্রথম ডিরেকটর। শিশিরের নির্দেশে দিনের ২৪ ঘন্টাই চালু রইল সেই গবেষণাগার। ২৪ ঘন্টা ধরে আয়নোস্ফিয়ারের সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হতে থাকে এই কেন্দ্র থেকে।
নভেম্বর ১৯৫৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থকে অবসর নেন শিশির। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এমিরেটস’ অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। শিশিরে প্রজ্ঞা ও কর্ম দক্ষতার সাথে বিলক্ষন পরিচিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সংস্কারে শিশিরে ভূমিকার কথা বিলক্ষণ জানা আছে তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন অবসর নিয়েছেন শিশির। বিধানচন্দ্র চান শিশির এবার হাল ধরুন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। বিধানচন্দ্রে অনুরোধে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসনিক দায়ভার গ্রহন করেন শিশির। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৫৭ সালে হায়ার সেকেন্ডারির বিজ্ঞান সিলেবাসে ব্যাপক রদবদল ঘটান শিশির। হায়ার সেকেন্ডারির পাঠ্যক্রমকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের উপযুক্ত করে তোলেন তিনি। হায়ার সেকেন্ডারির আর্টস বিভাগের পাঠ্যক্রমে তখন সংস্কৃত পাঠ বাধ্যতামূলক ছিল। শিশির এই পাঠ্যক্রমের বিরোধী ছিলেন। তাঁর যুক্তি, আধুনিক সমাজ জীবনে সংস্কৃত চর্চা কখনই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। ঐচ্ছিক করা হোক সংস্কৃত পাঠকে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার ভার কমবে। শেষ পর্যন্ত শিশিরে সিদ্ধান্তই বহাল থেকে যায়।
জানুয়ারি ১৯৬১, শিশিরে জীবন ছেয়ে গেলো ভয়ানক এক দুঃসংবাদে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোক কুমার মিত্র। পুত্র শোকের এই ধাক্কা সামালতে পারেন নি শিশির। মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। উত্তেজনা পরিহার করে তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেন চিকিৎসকরা। ১৯৬২ সালে এই কর্মবীরকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন ভারত সরকার। স্বাস্থ্য অনুকূলে না থাকায় তখন ধীরে ধীরে প্রায় সব কাজ থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন শিশির। শুধু একটা কাজ থেকেই কোনও দিনও নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি তিনি। আর তা হলো তাঁর সাধের আপার আটমোস্ফিয়ারের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ। একাকী এক অধ্যাপক তখন সারাদিন ধরে পরিমার্জন করে চলেছেন তাঁর স্বপ্নের রচনাকে। কিন্তু সেই স্বপ্নকে সাকার করার সুযোগ আর পান নি তিনি। ১৩ই অগস্ট ১৯৬৩ সালে অক্লান্ত এই গবেষক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
শিশির চলে গেলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন ভারতের রেডিও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। তার আগেই তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন অগণিত ছাত্রকুলের যাঁরা পরবর্তীকালে হাল ধরেছেন দেশের রেডিও ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়। রেডিও যুগের ভোরের সেই শিশির আজ মিশে আছেন বিরাট একদল ছাত্রদের মহাসাগরে। এ বিন্দু শিশির আজ মহাসগরে পরিণত হয়েছেন।
সমাপ্ত
[১] ইসরো টুইটে ও ছবিতে তারিখ হিসাবে ২৩ অগস্ট উল্লেখ করা আছে। ছবিতে সময় দেখানো হয়েছে ১৯.৪২ ইউটি (UT)। ইউটি অর্থ ইউনিভার্সাল টাইম। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম (IST) অনুসারে ২৩শে অগস্ট ১৯.৪২ ইউটি অর্থ দাঁড়ায় ২৪শে অগস্ট রাত ১.১২ মিনিট।
[২] স্কটিশ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী জন জ্যাকসন (১৮৮৭-১৯৫৮) গ্রিনউইচ মানমন্দিরে প্রধান সহকারী হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে চাঁদ নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই ১৯৭০ সালে চাঁদের একটা ক্রেটার বা গর্তের নাম রাখা হয় জ্যাকসন ক্রেটার।
[৩] ১৯৭০ সালে অস্ট্রিয় পদার্থবিদ আর্নস্ট ওয়াল্ডফ্রাইড জোসেফ ওয়েঞ্জেল মাখের (১৮৩৮-১৯১৬) নামে চাঁদের একটা গর্তের নাম রাখা হয়েছে মাখ ক্রেটার। শব্দোত্তর তরঙ্গ (Supersonic wave) নিয়ে কাজ করেন মাখ। তাঁর নামানুসারে, বিমানের গতির প্রশ্নে মাখ ১, মাখ ২ ইত্যাদি একক ব্যবহার করা হয়।
[৪] ১৯৭০ সালে ইউএসএসআরের (অধুনা ইউক্রেন) রকেট বিশেষজ্ঞ সার্গেই পাভলোভিচ কোরোলেভের (১৯০৭-১৯৬৬) নামে চাঁদের একটা ক্রেটারে নাম রাখা হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ স্পুৎনিক ১, পৃথিবীর প্রথম প্রাণী লাইকা (কুকুর) ও পৃথিবীর প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগরিনের রকেট উৎক্ষেপনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন কোরোলোভ।
[৫] ১৯৭০ সালে ৯৭.১ কিমি ব্যাসার্ধের চাঁদের একটা ক্রেটারের নাম রাখা হয় ‘মিত্র ক্রেটার’।
[৬] নিবন্ধের প্রয়োজনে চন্দ্রযান ২এর বাকি কাহিনীটা এখানে আর উল্লেখ করা হয় নি। একথা সবাই জানেন, অরবিটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করার সময় পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বিক্রমের। সেনি। চন্দ্র পৃষ্টে আছড়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ‘বিক্রম’। পরে, বিক্রমের বিভিন্ন টুকরোর ছবি সংগ্রহ করতে সক্ষম ই দিনটা ছিল ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯। এরপর আর কোনও ভাবেই বিক্রমের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় হয় নাসা। ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়, ‘সফটওয়্যার সমস্যা’র কারণেই বিক্রমের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ইসরোর।
[৭] ১লা জানুয়ারি ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালি উপাচার্য নিযুক্ত হন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি বিভাগে অধ্যাপনার জন্য ‘স্যর গুরুদাস ব্যানার্জী’ নামাঙ্কিত ‘চেয়ার’ রয়েছে।
[৮] ১৯২০-২১ সালে বিহারে খয়রা অঞ্চলের (দেওঘরের নিকটবর্তী) জমিদার কুমার গুরু প্রসাদ সিংএর স্মৃতিতে তাঁর স্ত্রী রানি ভাগ্যেশ্বরী দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ দান করেন। কুমারের স্মৃতিতে- ভাষাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও কৃষিবিজ্ঞানে অধ্যাপনার জন্য ৪টে চেয়ার ও ভাগ্যেশ্বরী দেবীর নামে ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস বিভাগে ১টা চেয়ার চালু করেন বিশ্ববিদ্যালয়।
[৯] ১৯৫১-৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি নির্বাচিত হন শিশির কুমার মিত্র। ১৯৫৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির তরফ থেকে ‘ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস (ক্যালকাটা) মেডেল’ প্রদান করা হয় শিশিরকে।
যে সমস্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পুস্তিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে –
- Professor Sisir kumar Mitra - As I Remember Him, by Mrinal Kumar Das Gupta, Resonance, July 2020.
- History of the Calcutta School of Physical Science, by Purabi Mukherji, Atri Mukhopadhyay, Springer, 2018.
- Sisir Kumar Mitra, Scientific Achievements and the Fellowship of the Royal Society of London, by Rajinder Singh, October 2017.
- Sisir Kumar Mitra, by A.P. Mitra, Resonance July 2000.
- Calcutta University and Science, by S.C. Ghosh, 1994.
- National Professor S K Mitra(FRS) and his diciples, by S S Baral, December 1990.
- Professor Mitra and Ionosphere Research in India, by A K Saha, December 1986.
- Sisir Kumar Mitra, by John Ashworth Ratcliffe, The Royal Society 01 November 1964.
- Sisir Kumar Mitra, by J.N. Bhar 1966
- Mitra Sisir Kumar by Vigyan Prasar, Govt. of India. 1966
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনশুক্র ভারতী - সহস্রলোচন শর্মাআরও পড়ুনশারদ গুরুচণ্ডা৯ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনছায়ানট - কহিপ্তাশাআরও পড়ুনঅন্তর্যামী জানেন - শুভাশীষ দত্তআরও পড়ুনদূরাগত - মিঠুন ভৌমিকআরও পড়ুনস্থানীয় সংবাদ - শাশ্বতী সরকারআরও পড়ুনপশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদী শক্তি - দীপআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
অরিন | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ০২:৩৬98900
অসাধারণ! ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে কি আশ্চর্য লেখা। বাংলায় এত নিখুঁত ও ঝরঝরে গতিশীল অথচ সহজ করে জটিল বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা বহুদিন পড়িনি।
 i | 203.219.***.*** | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ০৮:১৪98912
i | 203.219.***.*** | ২৫ অক্টোবর ২০২০ ০৮:১৪98912বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে সহস্রলোচন শর্মার প্রতিটি লেখাই - কী তথ্যে, কী উপস্থাপনায়- পাঠককের মনোযোগ টেনে নেয় গোড়া থেকেই। অত্যন্ত আকর্ষণীয়, উপভোগ্য সিরিজ।
 সহস্রলোচন শর্মা | 113.2.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৭99273
সহস্রলোচন শর্মা | 113.2.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৭99273পাঠককুলের মতামতের জন্য কৃতার্থ হলাম।
 সহস্রলোচন শর্মা | 113.2.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৭99272
সহস্রলোচন শর্মা | 113.2.***.*** | ২৮ অক্টোবর ২০২০ ১৭:২৭99272পাঠককুলের মতামতের জন্য কৃতার্থ হলাম।
-
একলহমা | ৩১ অক্টোবর ২০২০ ০০:০৬99444
অসাধারণ এক মানুষকে নিয়ে অসাধারণ এক লেখা। উপরে অরিনের মন্তব্যের সাথে পূর্ণ সহমত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)
(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, অরিন, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
















