- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
রক্ষণশীল, মৌলবাদী, একরৈখিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে তিনি জলজ্যান্ত প্রতিবাদ
হিন্দোল ভট্টাচার্য
পড়াবই | মনে রবে | ২৯ নভেম্বর ২০২০ | ৩৯৪৬ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 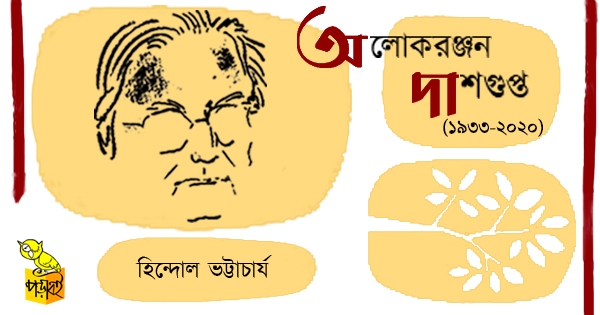 অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কেমন ভাবে পাঠ করব আমরা তাঁর কবিতা? সে কবিতা একদিকে যেমন ভুবনায়নের কাউন্টার কালচার তৈরি করছে, তেমনই নিজে হয়ে উঠছে বিশ্বের মাইক্রোকজম। ‘কবিদের সমস্ত জায়গায় একটা সমান্তরাল এবং আদিগন্ত রাখিবন্ধনের ব্যাপার আছে। সেই জায়গাতে আমাকে শনাক্ত করার কাজটা কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে,’ এমনই ছিল কবির নিজের অভিপ্রায়। লিখছেন হিন্দোল ভট্টাচার্য
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কেমন ভাবে পাঠ করব আমরা তাঁর কবিতা? সে কবিতা একদিকে যেমন ভুবনায়নের কাউন্টার কালচার তৈরি করছে, তেমনই নিজে হয়ে উঠছে বিশ্বের মাইক্রোকজম। ‘কবিদের সমস্ত জায়গায় একটা সমান্তরাল এবং আদিগন্ত রাখিবন্ধনের ব্যাপার আছে। সেই জায়গাতে আমাকে শনাক্ত করার কাজটা কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে,’ এমনই ছিল কবির নিজের অভিপ্রায়। লিখছেন হিন্দোল ভট্টাচার্য
অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল যখন তখন সকাল বেলা সাড়ে ১১ টা। ফোন তুলে ‘হ্যালো’ বলতেই ভেসে এল সেই পরিচিত কণ্ঠ। ‘তোমার কি রজনী এখনও প্রভাত হয় নাই? না কি দিবানিদ্রায় সাঁতার কাটছ?’ এ কণ্ঠ শুনে কোন্ নম্বর থেকে ফোন আসছে তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। “আরে, অলোকদা, এটা আবার কোন্ নম্বর? আমি তো ফোন করতামই আজ। আজ বিকেলের দিকে যাব ভাবছিলাম।” “এখন আর অত তাড়া করার কোনো কারণ নেই। ধীরে সুস্থে এসো। পরের বছর এলেও হবে।” “আরে না, না, আমি আজই যাচ্ছি।” “কিন্তু আমি তো কলকাতা ছেড়ে এসেছি। দিল্লি থেকে ফোন করছি। কাল জার্মানির ফ্লাইট। ফোনে কথা হবে শীঘ্রই। কেমন? ততক্ষণে সুরদাসের টীকাগুলো করে ফেলো।”
অলোকদা যে কখন কলকাতা আসতেন আর কখন কলকাতা ছেড়ে চলে যেতেন, আমার কাছে এখনও এক অধরা রহস্যের মতোই থেকে গেছে। কলকাতা থাকতেন যতদিন, তার বেশ কয়েকটা দিন কিন্তু আমাদের দেখা হতই। কথাও হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আমি প্রত্যেকবার ভুলে যেতাম তাঁর ফিরে যাওয়ার দিনটির কথা জানতে। আর তিনিও হয় দিল্লি নয় জার্মানি থেকে ফোন করে আমাকে চমকে দিতেন। বলতেন, “অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা থেকে মজা পাও না?”
কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক আগে। তখন তাঁকে কেমন দেখতে তা জানতাম না। প্রমার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-এর কবিতাসমগ্র পড়ে নেশাসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’ পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এদেশ ওদেশ। আন্তর্জাতিক কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আমায় এই বইটিই। আর তখনই পড়ে ফেলেছিলাম প্রমা থেকেই বেরোনো সুরদাস সঞ্চয়িতা। সে কী আশ্চর্য এক বই!
যৌবনবাউলের দর্শনের একটি টুকরো অংশ হয়তো এখানে পড়ি আমি—
দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার
দিয়েছ আমার হাতে—
এই ভেবে আমি যত খেয়া পারাপার
করেছি গভীর রাতে,
প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়
কান্নায় ডোবে জলে,
হাসিমুখে তবু কেন হে বিশ্বময়
তোমার তরণী চলে?
(অপূর্ণ)
এই কবিতাগুলির দর্শনের সঙ্গে যে ব্যক্তিত্ব তিনি অর্জন ও প্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলা কবিতায় তা এক স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নিয়ে তো এলই, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল এক ভিন্ন দার্শনিক যাপন। তিনি যেন দান্তের ইনফের্নোর মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন রবীন্দ্রগান গাইতে গাইতে। তিনি জানেন ‘হে পূর্ণ তব চরণের কাছে/ যাহা কিছু সব আছে আছে আছে’, কিন্তু তিনি এও জানেন, তাঁকে এক অন্ধের মতো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। তিনি জানেন যে এ জন্মে তিনি সুগতর কেউ না। তিনি জানেন, তিনি বহু বছর ধরে হাঁটছেন এই অন্ধকারে। হাজার শুধু না, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাঁর এই হেঁটে আসা, তাঁর এই থাকা। আর তিনি যে বাড়িতে থাকেন, সেই বাড়িটাও বহু বছরের। যেন আবহমান অবচেতনার অংশ হয়ে তিনি কথা বলে উঠছেন। এই আবহমানতার শুরু কোথায় তিনি জানেন না। ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ কাব্যগ্রন্থটিতে যেন মিতকথনের বিস্তার এক অনবদ্য অন্তর্বয়নের রূপ পায়। যৌবনবাউলে তবু অন্ধকার অস্তিত্ববাদের প্রেক্ষাপট ছিল, তা যেন এখানে নেই। এখানে কি কবি আরও গভীর অন্ধকারে গেছেন? নাকি সেই আলোর কাছাকাছি পৌঁছেছেন, যার কাছাকাছি গেলে মানুষ অনেক শান্ত হয়ে যায়, অনেক কম তুলির আঁচড়ে এঁকে ফেলে মহাকাব্যিক ক্যানভাস। অলোকরঞ্জনের কবিতার এই আর-এক বৈশিষ্ট্য। এক মহাকাব্যিক ক্যানভাস থেকে যায় তাঁর সৃষ্টিগুলির মধ্যে। যেন তিনি আঁকছেন একটি ছোট্ট ফুলদানি। কিন্তু তার প্রেক্ষাপটে আছে হয়তো সুদূর দিগন্ত বা যুদ্ধক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী বর্তমান। কিন্তু সেই ফুলদানিতে আঁকা আছে শান্ত এক পৃথিবীর সংসার। তবু এই শান্ত পৃথিবীর সংসার যেন ব্যাহত হচ্ছে ক্রমশ। তিনি নিজেকে আটকাচ্ছেন বারবার। কিন্তু যে অরূপরতনের সন্ধান একবার পেয়েছে, সে চরম অন্ধকারের মধ্যেও আলোর লীলা দেখতে পায়। ফলে, ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’-তে আমরা এক অনবদ্য অলোকরঞ্জনীয় ভাষাপ্রবাহে দেখতে পাই তাঁর কবিতা অনেক বেশি রহস্যময় হয়ে গেল। আধুনিকতা কি অনেক বেশি সুললিত আচ্ছাদনে মুড়ে ফেললেন কবি? কিন্তু সুললিত এই আচ্ছাদনের ভিতরে আধুনিকতার নগ্নতা দেখতে পেলাম আরও বেশি করে।
আত্মনিহত দুটি মৃতদেহ
রাঢ়ভগবতীপুরে
দুপুরবেলায় পৌঁছিয়ে গেল
নদীর উজান ঘুরে।
একটি পুরুষ, তার চোখে তবু আক্রোশ, রুক্ষতা
অন্যটি নারী, তার চোখেমুখে অটুট স্বর্ণলতা।।
(নারীশ্বরী)
একদিকে বিশ্বকবিতার অন্তর্জগতের ভিতর তিনি ডুব দিচ্ছেন, অনুবাদ করছেন পাউল সেলান থেকে এনজেনৎসবার্গার, জার্মান থেকে পোলিশ, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সুরদাসের ভজন পর্যন্ত বিশ্বকবিতার ভুবন, অন্যদিকে শিল্পিত সুষমা জাতীয় অনবদ্য সব প্রবন্ধে একের পর এক তুলে ধরছেন কবিতার আত্মার অন্তর্কথন।
‘সুন্দর ও কার্ল মার্ক্স’ প্রবন্ধে অলোকরঞ্জন লিখছেন, ‘আজ যখন লুকাচ প্রমুখ নন্দনতাত্ত্বিকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরেও মার্কসীয় সমালোচনা, বিশেষত বাংলাদেশে, প্রগতির নামে একটি কূপমাণ্ডুক্যের অভিসন্ধিচর্চায় অবসিত হয়েছে, তখন একবার অন্তত মুমুক্ষু মার্কসের প্রাথমিক ও মানবিক অভিপ্রায়ের সেই ব্যাপ্তির কথা মনে রাখা ভালো যিনি সুন্দরের প্রয়োজনকেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন, প্রয়োজনের সুন্দরকে নয়।’ দেখা যাচ্ছে, এই ভাবনায় উপনীত হওয়ার আগেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অন্ধকারের সঙ্গে এক গভীর দার্শনিক নান্দনিক অভিযাত্রায় মেতেছেন। কারণ তিনি জানেন যে নশ্বর ব্যথা এবং যন্ত্রণার বিশ্বে আমাদের যাপন করতে হয়, তা নরকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু ঈশ্বর এর মধ্যেই রয়েছে। ঈশ্বরের জন্য বা সুন্দরের জন্য, সত্যের জন্য, সে সত্য এক না বহু, তা নিয়ে সংশয় আমাদের থাকলেও, তার জন্য আমাদের যেতে হবেই, রাধা যেমন কণ্টক জর্জরিত পায়ে ছুটে গিয়েছিলেন অভিসারের নিয়তিনির্দিষ্ট পথে। এই অভিযাত্রার শেষ নেই কোনো কিন্তু অভিযাত্রার শেষে সেই সুন্দর যে রয়েছে, তার জন্য কবির মননে এবং মেধায় রয়েছে গভীর বিশ্বাস।
জার্মান কবিতাই শুধু নয়, ইউরোপীয় কবিতা নিয়েই কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের যে প্রজ্ঞা, তা ছিল অকল্পনীয়। একবার, মরমিয়া কবিতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন ক্রিশ্চান মিশনারিদের কবিতা। পূর্ব ইউরোপে একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ক্রিশ্চান মিশনারিদের কবিতা পড়লে মনে হবে সেগুলি লেখা যেন আমাদের পদকর্তাদের। সেইসব কবিতার অনুবাদ সম্ভবত এখনও কোথাও বেরোয়নি। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে জার্মান কবিতাকে বাংলায় অনুবাদ করার কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর সেই কাজে, অলোকদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। একটি কবিতাকে তিনি প্রায় সাত-আটবার করে সংশোধন করাতেন শুধু তাই নয়, প্রতিটি কবিতার অনুবাদে, বিবেচিত হত তার সমসময়ের রাজনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। অর্থাৎ, একটি কবিতা যে আসলে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, তা তিনি অনুবাদের সময় বারবার মনে করিয়ে দিতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় যেন খুলে যেত বিশ্বকবিতার জানলা। বুঝতে পারতাম, কেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ‘গিলোটিনে আলপনা’-র পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাব্যচিন্তার অনুসারী। সেই পর্যায়কে অনেকেই এখনও হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু আগামী কবিতার বীজ সেখানে আছে বলেই আমার মনে হয়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ‘গিলোটিনে আলপনা’-র পরবর্তী পর্যায়ের কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে যায় বিখ্যাত গ্রিক চিত্র পরিচালক থিও অ্যাঞ্জেলোপোলসের চলচ্চিত্রগুলির কথা। যেভাবে রাজনীতির সঙ্গে মৃত্যুচেতনা, প্রেম, যুদ্ধের সঙ্গে একাকী মানুষের বেদনা সংযুক্ত অবস্থায় আছে, ঠিক সেভাবেই অলোকরঞ্জনের এই পর্যায়ের কবিতা। শিকড়ের আরও শিকড়ে চলে গেছেন যেমন তিনি, তেমনই বিস্তৃতও হয়েছেন এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে। কবিতায় এমন বিশ্বনাগরিকের দেখা পাওয়া সত্যিই যায় না। বিশেষ করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, এভাবে নিজের শিকড়ের মধ্যে অবগাহন করেও যে বিশ্বকবিতার দিগন্তে মাথা তুলে রাখা যায় এক কাব্যবনস্পতির মতো, তা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা ও কাব্যচিন্তাগুলি অনুসরণ করলে বোঝা যেত। তাই সুরদাস এবং ব্রেশট, গুটফ্রিড বেন, পৌল সেলান এবং রবীন্দ্রনাথ বা কবীর, উলফ বিয়ারম্যান এবং কে এল সায়গল বা সাঁওতালি গান—সমস্ত কিছুকেই তিনি ধারণ করে থাকতেন।
আমার নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “আমি বলছি জীবনানন্দ যখন ইয়েটসের হাত ধরে এগিয়ে যান, বা মালার্মে যখন ডে লা মেয়ারের হাত ধরে এগিয়ে যান, তার কথা। সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত কবিদের মধ্যে একধরনের স্বগোত্রিতা থাকে। কিন্তু এটাও ঠিক যে দেশে যদি তার শিকড়টা না থাকে, এমন যদি হয় অধমর্ণ হয়ে শিকড় থেকে আমি লিখে যাচ্ছি তাহলে সেটা খুব আপত্তির ব্যাপার হবে। তুমি যে কবিতাটার কথা প্রথমেই উল্লেখ করলে, তার কি কোনো পূর্বসূরি কবিতা তুমি পেয়েছ? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পেয়েছ কি? পাওনি। কবিদের সমস্ত জায়গায় একটা সমান্তরাল এবং আদিগন্ত রাখিবন্ধনের ব্যাপার আছে। সেই জায়গাতে আমাকে শনাক্ত করার কাজটা কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে।”
আমি সত্যিই ঠিক জানি না, বাংলা কবিতাকে তিনি যা দিয়ে গেছেন, তা বাংলা কবিতা সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পেরেছে কি না। তাঁর সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি বলেই আমার মনে হয়। কারণ শুধু প্রথম তিনটি কবিতার বই বা অলোকরঞ্জনের মেধাবী প্রজ্ঞাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলে মুশকিল। তিনি ধারাবাহিক ভাবে কীভাবে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে গেছেন এবং বিশ্বকে নিজের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, এইটা গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি নিজের শিকড়কেও আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে গেছেন আজীবন। অর্থাৎ একজন কবি, কবিতার সামগ্রিক খননের পাশাপাশি, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে নিজের শিকড় ও নিজের দিগন্তকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। একজন ইউলিসিসের মতোই তিনি ছড়িয়ে পড়ছেন সমস্ত সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তগুলিতে। তাঁর প্রতিটি কবিতার বই একইসঙ্গে যেমন রাজনৈতিক, তেমন একইসঙ্গে আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক এই বীক্ষাকে তিনি অনুসন্ধান করে গেছেন আমৃত্যু। আর তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাবনার জগৎ, চিন্তার পৃথিবী, ভাষার পৃথিবী। এই রক্ষণশীল, মৌলবাদী, একরৈখিক পৃথিবীতে তিনি এক জলজ্যান্ত প্রতিবাদ হিসেবে ছিলেন। শিল্পের সুষমার মাধ্যমেই তিনি যে কাব্যভুবন তৈরি করে গেছেন, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের পর তা এক ভিন্ন খননের পৃথিবী।
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর আরও একটি কবিতা—
“ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অস্থাবর পোকামাকড়
সাঁওতালডির আলোকমালায় অতীন্দ্রিয় ছল
কেউ বলেছে এবারে খুব ফসল হবে না-ই বা হলো ফসল
ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুক দুর্ভিক্ষের অকূল চরাচর
আমি তবু এই শরীরের খড়
সংকলিত সত্তা আমার একাগ্র পবিত্র করে রাখি
‘আমাকে ভোগ করবে তুমি’—বলে জ্বালাই শেষদুটি জোনাকি!”
(জ্বর)
হয়তো এই কারণেই আমাদের অলোকরঞ্জনের কবিতার ভরকেন্দ্রকে খুঁজে পেতে সময় লাগছে, কারণ আমরা বহিরঙ্গে যতই ভুবনায়নের বাসিন্দা হই না কেন, আসলে আমরা সংকীর্ণ এক নাটমন্দিরে তরজায় রত। কিন্তু অলোকরঞ্জনের কবিতা, ভুবনায়নের কাউন্টার কালচার যেমন তৈরি করছে, তেমন সে নিজে হয়ে উঠছে বিশ্বের মাইক্রোকজম। বাংলা বা ভারত কেন বিশ্বের খুব কম কবির মধ্যে এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শূন্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। কারণ তিনি শুধু আমাদের কাব্যভুবন দিয়েই পূর্ণ করে রাখতেন তা নয়, আমাদের ভাবনাচিন্তার জগতেও তিনি ক্রমাগত ছাপ রেখে গেছেন তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি দিয়ে। যদিও পৃথিবীটা খুব সুন্দর নয়। তবু তিনি বারবার জার্মানি থেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন, “একটা সুসংবাদ দাও।”
আমার কাছে জার্মানি থেকে আর ফোন আসবে না কোনোদিন। দুহাজার দুই সালে সেই যে সাহিত্য অকাদেমির কবিতাচর্যায় আলাপ হয়েছিল, সেই শিকড়টা ছিঁড়ে গেল। একা লাগছে।
স্কেচ: হিরণ মিত্র
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ৩ - দআরও পড়ুনবিচ্ছেদ - Manali Moulikআরও পড়ুনশহীদ কবি মেহেরুন্নেসা - দীপআরও পড়ুনদিলদার নগর ২১ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 মন্দিরা গাঙ্গুলী | 115.187.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ০৭:৩৭100741
মন্দিরা গাঙ্গুলী | 115.187.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ০৭:৩৭100741ঋদ্ধ হলাম।
 সবর্ণা চক্রবর্তী | 2409:4060:10e:fc32::c6:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২০:১৬100757
সবর্ণা চক্রবর্তী | 2409:4060:10e:fc32::c6:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২০:১৬100757- গভীরভাবে স্পর্শ করলো।
-
শিবাংশু | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ২৩:২৪100799
ভালো লাগলো,
-
Jayanta Bhattacharya | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ২৩:৩৮100803
চমৎকার লেখা। আমরা নাটমন্দিরের তরজা অতিক্রম করে কবে যে বেরবো! কৃষকদের মহাযাত্রার পরেও হয়তো নয়।
-
Ranjan Roy | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ০৩:৪২100812
জয়ন্ত যা বলেছেন, সহমত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।














