- বুলবুলভাজা আলোচনা শিক্ষা

-
যাদবপুরে র্যাগিং – ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অন্বেষণ
সোমনাথ রায়
আলোচনা | শিক্ষা | ২০ আগস্ট ২০২৩ | ৬১৫৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৩ জন) 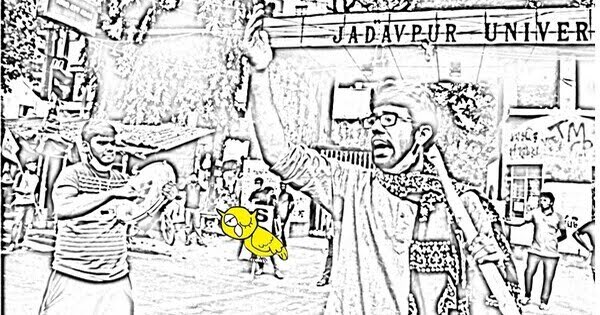
আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির মতন র্যাগিং-এর উৎসমুখ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কথিত আছে প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে নতুন শিক্ষার্থীদের পুরোনো শিক্ষার্থীরা সবক শেখাতেন। আমরা যদি আধুনিক ইতিহাস দেখি, র্যাগিং (যা হেজিং নামে বহির্বিশ্বে বেশি প্রচলিত) জিনিসটার প্রচলন তিনটি আলাদা ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা আমরা একে একে বলছি। বেশ কিছু দেশে সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন রিক্রুটদের পুরোনোরা নতুনদের অত্যাচার করবে, এই রীতি দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রিসে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের একবছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক হয়। সিভিলিয়ানদের সান্ত্রীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রথম ধাপটিই শুরু হয় পেশাদার সেনাদের হাতে এই নতুন রিক্রুটদের র্যাগিং-এর মাধ্যমে। পুরোনো সেনাদের ফাইফরমাশ খাটা, তাতে ভুলচুক হলে প্রহৃত হওয়া, তাদের কথামতো অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে নাচগান করা থেকে শুরু করে নিজের টুথব্রাশ দিয়ে কমোড পরিষ্কার করে দেওয়া, ইত্যাদি ছিল সেই র্যাগিং-এর অঙ্গ। অনুরূপ প্রথা রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে বলতে গেলে আজও প্রচলিত আছে, ডেডোভশকিনা নামে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহে যখন দাগি আসামিদের সেনাবাহিনীর উপরের দিকের পদে বসানো শুরু হল, তখন থেকে নাকি এই প্রথা জাঁকিয়ে বসেছে। এরকমও দাবি পাওয়া যায় যে সেনাবাহিনীর মধ্যে পদোন্নতির জন্যে ডেডোভশকিনায় কে কীরকম পারদর্শিতা দেখিয়েছে সেইটাও বিচার করা হত। ১৯৯০-এ কমিউনিজম পতনের পর সেই দেশের সেনাবাহিনীতে নাকি এই প্রথা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আরও বিভিন্ন দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে এই প্রথা আছে। বিশেষ করে, যেসব দেশের নাগরকিকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছুদিনের জন্য সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হয়, সেইসব দেশে বাহিনীর মধ্যে র্যাগিং প্রচলিত। র্যাগিং-এর সপক্ষে এক চিরাচরিত যুক্তি হিসেবে সিনিয়র-জুনিয়র সৌহার্দ্যের কথা বলা হয়। এর উপর সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে আলাদা করে বলা হয় আদেশ পালন করবার অভ্যেস, কঠিন মুহূর্তে নিজের দলের স্বার্থরক্ষা করতে পারার দৃঢ়তা ইত্যাদি নাকি এই প্রথার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই সবকটি স্বতঃসিদ্ধ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশে, ভারত ব্যতীত আর একটি দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাত্রাতিরিক্ত র্যাগিং-এর সমস্যা দেখা গিয়েছে, তা হল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রীলঙ্কান সৈন্যরা মিত্রশক্তির ইউরোপীয় সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে বাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধের পর তাঁরা ফিরে এসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। তখন থেকে নাকি সেই দেশে র্যাগিং-এর পরম্পরা তৈরি হয়।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং-এর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমরা তাকাই সেই দেশটির দিকে, যাদের অনুকরণেই আমাদের দেশের আজকের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনের সরকারি বিদ্যালয়ে র্যাগিং-কে বলা হয় ফ্যাগিং। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের আবাসিক স্কুলগুলির হোস্টেলে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দায়িত্ব থাকত নিচু ক্লাসের ছাত্রদের (যাদের ফ্যাগ বলা হত) ভালোমন্দের খেয়াল রাখবার, তাদের সহবৎ শেখাবারও। এই দায়িত্ব পরের শতাব্দীগুলিতে ব্যক্তিগত ফাই ফরমাশ খাটানো, শারীরিক ও যৌননিগ্রহে এসে ঠেকে। বিংশ শতাব্দীতে, এমনকি আজ থেকে কয়েকবছর আগেও, ব্রিটেনের বোর্ডিং স্কুলে ফ্যাগিং এবং তজ্জনিত নিগ্রহগের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।
আমেরিকান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হেজিং খুব পরিচিত ঘটনা। সেখানকার ছাত্রসমিতিগুলির মধ্যে (গ্রিক লেটার অর্গানাইজেশন নামে যেগুলি বর্তমান) প্রায়শঃই হেজিং-এর ঘটনার হদিশ এমনকি মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগ অবধিপাওয়া যায়। একদম প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। বলা হয় মদ এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্যের অতিব্যবহার এই ঘটনাগুলির মাত্রা তীব্রতর করে তুলেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হেজিং মূলতঃ ব্রিটেনের (অ্যাংলো-স্যাক্সন) পরম্পরা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আরও অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশেও এর প্রসার ঘটেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইন স্বত্তেও একে নির্মূল করা তো যায়ইনি বরং এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিদ্বেষের প্রভাব যুক্ত হয়েছে, যেমন বর্ণবিদ্বেষ, নারীবিদ্বেষ, তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের পরিসরও হয়ে উঠেছে হেজিং-এর ঘটনাগুলি। বছর দুয়েক আগে বেলজিয়ামের কে ইউ ল্যুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণবিদ্বেষী সিনিয়ররা এক কৃষ্ণাঙ্গ নতুন ছাত্রকে হেজিং-এর সময়ে হত্যা করে।
তৃতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে র্যাগিং-এর নিদর্শন আমরা আধুনিক ইতিহাসে পাই। ফ্রান্সের বিভিন্ন কারখানায়, বিশেষ করে মুদ্রণশিল্পে, নতুন শ্রমিক এলে তার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের নির্যাতনমূলক ব্যবহার করতেন পুরোনো শ্রমিকরা। যৌনাঙ্গে কালি মাখিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্র্যাক্টিকাল জোক, শারীরিক হেনস্থা ইত্যাদি করা হত। খনি এবং জাহাজশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যেও এইধরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। অল্পবয়সি শ্রমিককে কখনও মহিলারা এসে পরীক্ষা করে যেতেন সে যথেষ্ট পুরুষালি কিনা। কখনও বা যন্ত্রের আঘাত সহ্য করে নিজের শক্তি প্রমাণ করতে হত নতুন শ্রমিককে। আমরা ধারণা করতে পারি, সেইসব কারখানা থেকেই এই প্রথা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করেছিল। দেশ-জাতি বিশেষে বিভিন্ন পেশা কিম্বা সামাজিক যূথে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করবার আলাদা প্রথা আছে, সেগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আত্মনির্যাতনমূলকও। পৃথিবীর বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে এইধরণের অভ্যেস প্রচলিত ছিল বা আছে। কিন্তু উপরোক্ত র্যাগিং-এর নিদর্শনগুলির সঙ্গে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য যে সেই সব সেরিমনিতে একটি নির্দিষ্ট রিচুয়ালিস্টিক ধারা আছে, কিন্তু বরিষ্ঠ কর্মীদের দল তাদের মর্জিমাফিক উপর শারীরিক/মানসিক অত্যাচার বা যৌন হেনস্থা চালাবে, র্যাগিং-এর ক্ষেত্রে এইটা আলাদা বৈশিষ্ট্য। পেশাদারি জগতের র্যাগিং, যা নিয়ে আমরা ফ্রান্সের উদাহরণ টানলাম, সেখানে আমরা দেখি, সেইসব কারিগরি পেশার ক্ষেত্রে র্যাগিং-এর প্রচলন হচ্ছে, যেগুলি পুরোনো উৎপাদনব্যবস্থায় সেভাবে ছিল না- যেমন ছাপাখানা, মুদ্রণযন্ত্র বানানো ইত্যাদি। গিল্ডভিত্তিক পুরোনো কারিগরিতে র্যাগিং-এর নিদর্শন পাইনা। আমরা কারখানা বা বোর্ডিং স্কুলের প্রথাগুলি থেকে ধারণা করতে পারি যে পুরোনো সামাজিক কাঠামো ভেঙে যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক একজায়গায় আসতে শুরু করল, তারা নতুন করে গোষ্ঠীপরিচিতি বানানোর লক্ষ্যে হয়ত এইরকম প্রথার আশ্রয় নিল। সেনাবাহিনীর র্যাগিংও একভাবে পুরোনো সমাজ ছেড়ে নতুন গোষ্ঠীতে ঢুকবার চিহ্ন হয়ে দাঁড়ালো। অপরাধমূলক সংগঠনগুলিতেও এইরকম কিছু প্রথা আছে। র্যাগিং-এর হিংস্রতা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে উক্ত পেশাগুলির সহিংসতার সঙ্গে জড়িয়ে। ব্রিটিশ স্কুলগুলির প্রসঙ্গেও এইরকম সম্ভাবনার কথা বলা যায়- সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের পরিচালকরা সেই স্কুলগুলিতেই শিক্ষিত হতেন। ঔপনিবেশিকতার আরও বিভিন্ন অবদানের মতনই র্যাগিং ভারত তথা উপমহাদেশের শিক্ষার্থীসমাজে ঢোকে।
এই লেখার শিরোনাম ছিল যাদবপুরে র্যাগিং-এর ইতিহাস আলোচনা করা। কিন্তু, এতক্ষণ আমরা প্রথম বিশ্বে র্যাগিং-এর দৃষ্টান্ত খুঁজতেই ব্যাস্ত রইলাম। এইবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথায় আসি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একভাবে তার উৎকর্ষের জন্যে বিখ্যাত। আরেকদিকে লাগাতার ছাত্র আন্দোলনের খবর এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায়শঃই আলোচনার পরিসরে নিয়ে আসে। খেয়াল করলে দেখব, ছাত্র-আন্দোলন আসলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের সঙ্গেই জড়িত। বস্তুত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ঐতিহ্য আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত আছে। ভারতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশশাসনপর্বে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। বাংলায় সেই আন্দোলনের একটি পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের আওতার বাইরে এসে সামাজিক উদ্যোগে স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। ঋষি অরবিন্দ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জাতীয় আন্দোলনের বহু বিখ্যাত সংগঠক এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসাবে বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে এই কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনলজির কাঠামোর উপরেই গড়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাগুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আমরা এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক মনে করব- ১) এই দেশের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিকাশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা এবং দেশনির্মাণের কাজে লাগতে পারে এইরকম ইঞ্জিনিয়ার তৈরির চেষ্টা এখানে হয়েছিল। ২) স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রচুর উজ্জ্বল তরুণ, যাঁরা বিভিন্ন কারণে সরকারি কলেজে পড়াশুনো চালাতে পারলেন না, তাঁরা এই কলেজে পড়তে পারতেন। বলতে গেলে, শুরু থেকেই এই কলেজ আন্দোলনে থাকা ছাত্রদের জন্যে ছিল। উল্লেখ করা যায়, এই কলেজের দুই অতিবিখ্যাত ছাত্র, যাঁরা ভবিষ্যতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন- ত্রিগুণা সেন এবং গোপালচন্দ্র সেন, দুজনেই ছাত্র অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পরে, যখন এই কলেজ ক্যাম্পাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তখনও জাতীয় আন্দোলনের ধারা এখানকার পরিচালক ও ছাত্রদের মধ্যে বহমান থাকে। উল্লেখযোগ্য হিসেবে বলা যায় একদিকে মার্টিন লুথার কিং এবং হো চি মিনকে অতিথি হিসাবে আনে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য। আরেকদিকে, দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশ ও উদ্ভাবনের কাজ চলতে থাকে এখানে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থাকা কারিগরদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলবার চেষ্টা জারি থাকে, তেমনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সংযুক্ত হন ভারতের নবনির্মিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে। আবার পাঁচ-ছয়ের দশকের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে এখানকার ছাত্ররা জড়িয়ে পড়তে থাকে, তাদের সঙ্গেও একভাবে আদান প্রদান চালানোর চেষ্টা চলে। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে পুলিশি নির্যাতন যখন চলছে, তখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেন ছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন।
এখানে, এইটা আমাদের বলার যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে আন্দোলনে মুখর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্র আন্দোলনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ঐতিহ্য। প্রাথমিক পর্বে সেই আন্দোলন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাত ধরে শুরু হয়। অসহযোগ থেকে আইন অমান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপে এখানকার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে জাতীয় আন্দোলনের ধারা শীর্ণ হয়ে এলে বামপন্থী চেতনা সেই আন্দোলনগুলিকে দিশা দেখায়। যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দুই ধারার মধ্যে এক জলবিভাজন, অন্ততঃ এই দেশে, থেকে গিয়েছে। যাই হোক, আন্দোলনের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে দেখলে পঠনপাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে থাকেনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখানকার বেশ কিছু বিভাগ যথেষ্ট অগ্রণী হিসেবে পরিচিত। রাজ্যসরকারের দেওয়া স্বল্প পরিমাণ আর্থিক বরাদ্দ এবং প্রভূত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ স্বত্তেও এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে তার গুণমান ধরে রেখেছে, তার একটা বড় কারণ এটাও যে কোনও একভাবে এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকরা জাতীয় আন্দোলনের গঠনমূলক সারবত্তাটি বহন করেছেন। তাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছেন- যে আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র ক্যাম্পাসের দাবির বাইরে বৃহত্তর সামাজিক চেতনার বীজও বহন করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়ে যেখানে আর্থিক ক্লেশ বহন না করে, ধার না নিয়ে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা পেতে পারে। ছাত্র আন্দোলনের নিরবিচ্ছিন্ন ধারা ব্যতীত এই সহস্রাব্দে এই দেশে তা হয়ত সম্ভব ছিল না।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের ঐতিহ্যের মধ্যে র্যাগিং-এর ঘটনাগুলিকে (একটি বীভৎস মৃত্যুর ঘটনার পাশাপাশি যখন বহু বছর ধরে হয়ে আসা অত্যাচারের বিভিন্ন বয়ান উঠে আসছে) কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, এইটা আমাদের ভাববার বিষয়। ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে র্যাগিং একটি অতিসংক্রামিত সামাজিক ব্যাধি। বিভিন্ন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকে ভারতের বিচারব্যবস্থা এবং শিক্ষানিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি র্যাগিং প্রতিরোধে কড়া ব্যবস্থার নিদান দেয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ব্যবস্থাগুলির প্রায় কোনওটিই লাগু হয়নি। এবং ছাত্রদের মধ্যেও র্যাগিং বিরোধী কোনও সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। বরং, এই কথা শোনা গেছে, ২০০৭ সালে নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধিরা র্যাগিংকারীদের শাস্তির বিরোধিতা না করায় বাকি ছাত্রদের একটি অতিসরব দলের চাপে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। আমরা জানি, র্যাগিং পরম্পরামেনে চলে। জুনিয়র ব্যাচের ছাত্ররা পরের বছরের জুনিয়র ব্যাচকে র্যাগ করে। এক প্রতিষ্ঠানের র্যাগিং-এর গল্প শুনে আরেক প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা র্যাগিং-এ উদ্বুদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ সেই ধারা ধরেই কলোনিপ্রভুদের বহু বদঅভ্যেসের মতন এই প্রথাও এদেশের শিক্ষিত সমাজে ঢুকেছিল। আর, পরম্পরা হিসেবে একটি অপরাধকে বহুজনের মধ্যে মান্যতা দিয়ে দিলে, তথাকথিত বিবেকবান ব্যক্তিও অনেকক্ষেত্রে তাতে লিপ্ত হতে সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিকভাবে এ পরম্পরার বাহক, তা তো ঠিক এর বিপরীতমুখী। আমরা বিদেশের উদাহরণগুলি থেকে দেখলাম, ছাত্র, শ্রমিক কিম্বা সৈনিকরা যখন নিজেদের মূল সামাজিক কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে আসছে, তখনই তারা নতুন করে গোষ্ঠীপরিচিতি নির্মাণের এই বিকৃত পদ্ধতির উপায় নিচ্ছে। সমাজের নিজস্ব ডায়নামিক্সের বাইরে গুরুজন-লঘুজনের নতুন সংজ্ঞা ঠিক হচ্ছে দমন, নির্যাতন এবং যৌন অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু, সমাজবিচ্ছিন্ন পেশাদার গড়ার এই যে কল, তাকেই ঔপনিবেশিক আক্রমণের অংশ হিসেবে বর্জন করার কথা বলেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা। বরং ডাক ছিল পেশাগত দক্ষতা নিয়ে গ্রামসমাজে ফিরে যাওয়ার। বামপন্থী রাজনীতিও কিন্তু তার বিকাশপর্বে ছাত্রকর্মীদের আরও বেশি করে সামাজিক ও মানবিক হয়ে ওঠার ডাক দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের চিন্তাধারার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পাশাপাশি ছিল সমাজনির্মাণের প্রয়াসও। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে বর্ণিত সামাজিক উদ্যোগকে রাষ্ট্রক্ষমতার উপরে তুলে ধরার প্রয়াস যেমন দেখি, তেমনি রাজা সুবোধ মল্লিক কিম্বা আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে দেওয়া অনুদান যেন গান্ধীজির অছিতত্ত্ব ধরে স্বীকার করে নেওয়া যে ধনীব্যক্তির উপার্জন আসলে সমাজের বাকি মানুষের গচ্ছিত সম্পদের ভাগ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, জাতীয় আন্দোলনের এই শিক্ষাগুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সফল হয় নি। আমরা যে আন্দোলনের ধারার কথা বললাম, তা কেবল বাইরের সমাজের প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম্পরাক্রমেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে জাতীয় আন্দোলনের ধারাটি স্তিমিত হওয়ায় সেই পরিসরে বামপন্থী রাজনীতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু, আজকের দিনে, এইসময়ে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বাজারমুখিতার যুগে বামপন্থী রাজনীতিও বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে, নতুন নির্মিতির রাজনীতি উঠে আসছে না, ছাত্র আন্দোলনেও তার সংকট দেখা দিয়েছে। সেই সংকট প্রভাবিত করছে ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিজীবনকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম যুগের সঙ্গে বা বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে। গবেষণা চলেছে ফান্ডিং এজেন্সি কিম্বা রাষ্ট্রের ঠিক করে দেওয়া দিশায়। কিন্তু, সমাজনির্মাণের যে লক্ষ্যে এই উদ্যোগের সূচনা, সেই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থেকেছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সমাজনির্মাণের লক্ষ্য কিন্তু শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাভাবনাতে ছিল। একদম শুরুর দিক্ থেকেই বাজার-চাহিদার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির পাশাপাশি মানববিদ্যা এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পঠনপাঠন চালু হয়। সেইসময় সমাজবিদ্যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমে সম্ভবতঃ ছিল না। কিন্তু, প্রথম উপাচার্য ত্রিগুণা সেন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইঞ্জিনিয়ারদের সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্ব শেখা জরুরি, যাতে তাঁরা বৃহত্তর জগতে দেশের কাজে লাগতে পারেন। প্রথম পর্বে নবাগত ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক এবং বাকিদের সংযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হত, যে ধরণের ওরিয়েন্টেশন আজকাল অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়। কিন্তু এইসব উদ্যোগ পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের কাছে উপেক্ষিতই থেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ কার্যক্রমে ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষাদানের উৎকর্ষ এবং বাজারচাহিদা মেনে উচ্চবেতনের কর্মী প্রস্তুত করা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, সেই তুলনায় উপনিবেশবিরোধী জাতীয় শিক্ষার চিন্তাধারা কিছুই গুরুত্ব পায় নি। অথচ, ‘উৎকৃষ্ট’ এই খেতাবটুকু শুধু অর্জনের জন্য কিম্বা কেবলমাত্র র্যাংকিং টেবিলের প্রথম সারিতে থাকবার জন্য উৎকর্ষ আনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে শিবপুর বি ই কলেজের পাশে আরেকটি প্রযুক্তি কলেজ গড়বার কোনও দরকার তখন অনুভূতই হত না।
ঔপনিবেশিক ভাবধারার উল্টোদিকে সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলাই বরং ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কিন্তু, বিগত বহুবছর ধরেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের চেতনা ছাত্রদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সামান্যতম উদ্যোগ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয়নি। ফলে, ঐতিহ্যগত ভাবে আন্দোলনের ধারা এখানকার ছাত্রসমাজ পেলেও, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের চেতনাগত অবস্থান তারা সহজে খুঁজে পায়নি। নচেৎ, এই ঔপনিবেশিক কুপ্রথা এই মাটিতে এত সারজল পেতে পারত না।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনতিন ঋতুর কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনজুলাই-আগস্টের কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনঋতেন ও তার বন্ধুরা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনএই বর্ষার কবিতা - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনসমুদ্রে সনেট - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনটিফিনবেলার গান - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনবড়ঘড়ির নিচে - সোমনাথ রায়আরও পড়ুনএপস্টাইন এর ফাইল - একটি কেলেঙ্কারি, নাকি একটি ব্যবস্থা: বৈশ্বিক পুঁজির Eros - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনতালিকা সংশোধন নাকি কাঠামো সংশোধন – প্রয়োজন কিসের? ভোটার হাজির - কন্ঠ কৈ? - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
হীরেন সিংহরায় | ২০ আগস্ট ২০২৩ ১৭:৫৩522717
- অসাধারণ।প্রসংগত একটি ছবির উল্লেখ করা যায় - লিনডসে এ্যানডারসনের ইফ।
 ক্ষপণক গুপ্ত | 45.64.***.*** | ২০ আগস্ট ২০২৩ ১৮:২০522721
ক্ষপণক গুপ্ত | 45.64.***.*** | ২০ আগস্ট ২০২৩ ১৮:২০522721- লিখছেন তো একদম ঠিকঠাক। কিন্তু যদুবংশীয় উন্নতনাসা রা কি এতো সহজে মানবে ?অন্যায়কে যুক্তি দিয়ে অধিকারের মোড়কে পেশ করতে শিক্ষিত সাবআর্বানের জুড়ি নেই কিনা।
-
Indra Mukherjee | ২২ আগস্ট ২০২৩ ১৯:৪৪522840
- খুব সময়োপযোগী লেখা ।
-
 lcm | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০১:১৮522851
lcm | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০১:১৮522851 - এইখানে পোস্ট করতে চেয়েছিলাম While close to 40% students in colleges across India faced some kind of ragging, only 8.6% reported the incidents, a study funded by University Grants Commission (UGC) on the directions of Supreme Court has found out. --- The Indian Express reported in January, 2016
Response to application under the Right to Information (RTI) act revealed [Jan, 2016]:
The phone calls were made from 1st January, 2014 to till date to Anti Ragging Helpline = 13,49,437
Out of 1349247 phone calls, total complaints registered as formal complaints = 770
-
যোষিতা | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০১:২৯522852
- ও ও ও ইতিহাসিক যুক্তিধারা বহিছে ভূবনে।
-
 Bratin Das | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০২:২২522856
Bratin Das | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০২:২২522856 - তাহলে কী দাঁড়ালো? :))
 আরে! | 2401:4900:314a:7a22:9089:88ff:fe40:***:*** | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০৮:৪৩522859
আরে! | 2401:4900:314a:7a22:9089:88ff:fe40:***:*** | ২৩ আগস্ট ২০২৩ ০৮:৪৩522859- আরে আরে আরে ঐতিহাসিক র্যাগার যোষিতাজী যে!! নিজেই পেহলে র্যাগিং করকে র্যাগিং র্যাগিং র্যাগিং করকে চিল্লানা বহোত দোগলাবাজি হ্যায় যোষিতাজী! কোই উনকে র্যাগিং জবানবন্দীকে পোস্ট পেস্ট করেংগে?
 কাজল দাস | 2405:201:8008:f054:9049:7663:f4bb:***:*** | ২৫ আগস্ট ২০২৩ ০০:৩২522905
কাজল দাস | 2405:201:8008:f054:9049:7663:f4bb:***:*** | ২৫ আগস্ট ২০২৩ ০০:৩২522905- খুব সুন্দর। সময়োচিত প্রতিবেদন।ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। সর্বস্তরে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন।সর্বোপরি জাতীয়তাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
-
Tamoghno chaudhuri | ২৫ আগস্ট ২০২৩ ১০:১৯522915
- https://www.4numberplatform.com/?p=34287
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












