- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
তাঁর ছিল নিজের সিদ্ধি পিছনে ফেলে আসার দুর্জয় সাহস
গৌতম বসু
পড়াবই | মনে রবে | ২৯ নভেম্বর ২০২০ | ৩৫৩৫ বার পঠিত | রেটিং ৪.৩ (৩ জন) 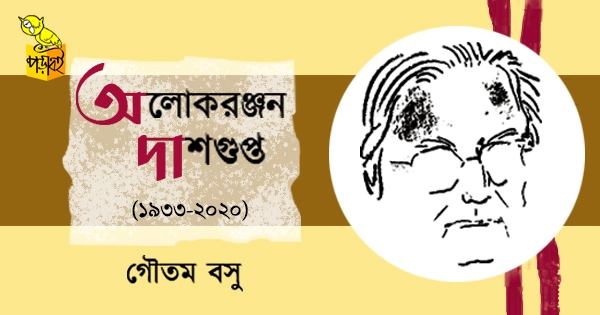 অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কেবল সুকবি নন, মহৎ কবি। গভীর খেদ এই যে, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজ এবং গ্রন্থপ্রকাশকরা মধ্যমানের পক্ষেই তাঁদের রায় দেওয়ায় তাঁর লেখার কপালে যে উপেক্ষা জুটল, তা অবমাননার নামান্তর। লিখছেন কবি গৌতম বসু
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কেবল সুকবি নন, মহৎ কবি। গভীর খেদ এই যে, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজ এবং গ্রন্থপ্রকাশকরা মধ্যমানের পক্ষেই তাঁদের রায় দেওয়ায় তাঁর লেখার কপালে যে উপেক্ষা জুটল, তা অবমাননার নামান্তর। লিখছেন কবি গৌতম বসু
“সৌগত গেল তলিয়ে, আমরা ন’জনের সংসার,
সে আছে নিখোঁজ, ধ’রে নিই আজও মৃত্যু হয়নি তার।”
—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র জীবনাবসান, বাংলা কবিতার ডানহাতের আঙুল কটি ভেঙে যাওয়ার তুল্য এক বিপর্যয়। কবি কথিত ওই ‘ন’জনের সংসার’-এ অন্তর্গত নন যাঁরা, আমি জানি, তাঁদের কাছে বাক্যটি অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে, তবু এমন একটি অভিমত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারলাম না, কারণ, মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজনীয়তার কথা কবিই আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন। আমরা সকলেই এ বিষয়ে অবহিত যে, কবিতা এমনই এক অঞ্চল যেখানে সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে কাউকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা অর্থহীন। ব্যক্তি নিজের অভিমতটুকু প্রকাশ করতে পারেন, এই মাত্র; তার ভাষ্যে সারবত্তা যদি থেকে থাকে কিছু, তবে, আজ না হোক আগামীকাল, তা আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হবে। এর বাইরেও প্রণালী রয়েছে বটে, যা ক্ষুদ্র স্বার্থ কর্তৃক প্রেরিত উচ্চকণ্ঠী জবরদস্তির এবং, আপাতদৃষ্টে আগ্রাসী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষামূলক আধিপত্য বিস্তারের, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আমরা এখনই মনোযোগ দিতে চাইছি না।
এই মৃত্যুসংবাদ তাঁর সব লেখা ফিরে-পড়ার এক শূন্যময় অবসর, এবং, কোনো প্রতর্ক এখন অনুপযুক্ত হলেও, সেই ‘মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজনীয়তা’র দ্বারা চালিত হয়ে বলে উঠতে ইচ্ছা হয়, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজ এবং গ্রন্থপ্রকাশকরা মধ্যমানের পক্ষেই তাঁদের রায় দিয়েছেন; অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র লেখার কপালে যে উপেক্ষা জুটল, তা অবমাননার নামান্তর। ‘স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন’ প্রকাশকরা তাঁর পাশে না থাকলে, তাঁর লেখা সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হত। এ কথা মানতে হয় যে, তাঁর লেখার বিশেষত্ব চিহ্নিত না করেই এমন গুরুতর অভিযোগ আনা অযৌক্তিক। তিনি কেবল সুকবি নন, তিনি একজন মহৎ কবি, এই প্রস্তাবটি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সবই ফাঁকা আস্ফালনের মতো শোনাবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কয়েকটি মানদণ্ড প্রস্তাব করা যায়, এবং তাদের প্রেক্ষিতে, তাঁর রচনা সম্পর্কে দু-চার কথা সেরে নিতে পারি। আপাতত, আমরা কেবল দুটি মানদণ্ডের প্রস্তাব রাখছি।
।। ২ ।।প্রথম প্রস্তাব: অপর মহাজন থেকে ধার নেওয়া বার্তা প্রতিধ্বনিত না করে, একজন মহৎ লেখক নিজের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করেন এবং তার জন্য, সবরকমের ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত; এমনকি, তাঁর যাবতীয় অর্জন ও ‘সাফল্য’, তাঁর অনুগত পাঠকদের প্রত্যাশা, সমস্তই হেলা ভরে পিছনে ফেলে আসতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। এই মানদণ্ড অনুসারে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একজন উত্তীর্ণ শিল্পী। আমরা সকলেই তাঁকে বাংলা কবিতার বিস্ময়বালক রূপে চিনি, কিন্তু ওই অভিধা তিনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন তা হয়তো এতদিনে কিছুটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। প্রথমত, ‘যৌবনবাউল’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, যখন কবির বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। কবি নিজে আমাদের জানিয়েছেন, বিশালাকার এই বইটিতে(১০৮ টি কবিতা) একাধিক কাব্যগ্রন্থ মিশে রয়েছে। আরও লক্ষণীয় যে, এই বইয়ের অনেক কবিতা পাঁচের দশকের প্রথম দিকের রচনা, যেমন, ‘আমার ঠাকুমা’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘শতভিষা’-র তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৫৯/১৯৫২), যখন কবির বয়স ১৯ বছর, এবং, যখন ‘কৃত্তিবাস’-এর জন্মই হয়নি। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধদেব বসু-র ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’-য় প্রবেশাধিকার লাভ করা যদি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, এখানেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভাবে সফল। ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ কাব্যসংকলনটির পাঁচটি সংস্করণ আছে, যথাক্রমে ১৩৪৬, ১৩৬২, ১৩৬৬, ১৩৭০ এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। প্রথম সংস্করণের তরুণতম কবি ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭), দ্বিতীয় সংস্করণে লোকনাথ ভট্টাচার্য-কে (১৯২৭-২০০১) স্থান দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণ (১৩৬৬/১৯৫৯) যখন সম্পাদনা করা হয়, তখন পাঁচের দশক ফুরাতে চলেছে, অথচ সংকলনে স্থান পেয়েছেন মাত্র দুজন তরুণ কবি, অরবিন্দ গুহ (১৯২৮-২০১৮) এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০)। ওই সময়ে অলোকরঞ্জন-এর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। চতুর্থ সংস্করণে (১৩৭০/১৯৬৩) বুদ্ধদেব বসু নতুন কোনো লেখককে অন্তর্ভুক্ত করেননি। ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’-র যে চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেটি পঞ্চম (পরিবর্ধিত) সংস্করণে (১৩৮০/ ১৯৭৩) ফুটে ওঠে; লেখকের তালিকায় প্রবেশ করেন ন’জন তরুণ, যথাক্রমে, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তারাপদ রায়, জ্যোতির্ময় দত্ত এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’য় তরুণদের প্রবেশের ক্রম লক্ষ করলেও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কবিস্বীকৃতি স্পষ্ট বোঝা যায়।
আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি, প্রাথমিক সাফল্যের ওই নিরাপদ পরিমণ্ডল স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বেরিয়ে এসেছিলেন; ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ বাংলা গীতিকবিতাকে যে উচ্চস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল, তা যেন ফাঁকা পড়ে রইল, ‘গিলোটিনে আলপনা’ (১৯৭৭) থেকে তাঁর লেখা চিরকালের মতো বাঁক নিল। স্পষ্টই, এর একটা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই শ্রদ্ধার্ঘ্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ কাব্যবিচারের পথটি আমরা পরিহার করছি। কয়েক বছর পর প্রকাশিত ‘জবাবদিহির টিলা’-য় (১৯৮২), আমার এই অত্যাশ্চর্য বিভাব কবিতাটি পাই, যা তাঁর কবি জীবনের অবশিষ্ট প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পথ-দেখানো এক ধ্রুবতারকা:
“আর আমার কোনো নিসর্গ নেই, মানুষজন যখন ঘুমিয়ে পড়ে
আপাতমৃত লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে অনুভব করি অনন্ত নিসর্গের আস্বাদ
যেন দেবদারুর দূতীরা ঢেলে দেয় আমার মুখে অমৃত আঃ
আমার ঘুম পায় আর দুদিকে খাটিয়া পেতে ঘুমিয়ে থাকে কাতারে-
কাতারে নরনারী তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার পথটাই আজ
আমার নিসর্গ”
নিজের সিদ্ধি পিছনে ফেলে আসার দুর্জয় সাহস, আমার মনে হয়, একজন মহৎ কবির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। মধ্যমানের একজন লেখক তাঁর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’র সার্থকতা-অর্জনে ভীত হয়ে পড়েন, একজন মহৎ লেখকের তেমন ঘটে না, কারণ, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল তিনি নিজেই। অলোকরঞ্জনের স্বভাবে এই নির্ভীকতা লক্ষ করবার মতো এক বৈশিষ্ট্য। নিজের বিশ্বাসের জগতের প্রতি অনুগত রয়ে যাবার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি বহু পাঠক ―‘রক্তাক্ত ঝরোখা’-পরবর্তী কবির নিন্দায় যাঁরা সরব―হারিয়েছেন। তাঁর সমসময়ের উজ্জ্বল তারকাদের মধ্যে তিনি একজন, যাঁর পুরানো কবিতার বইয়ের, অনুবাদ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই, বিগত বিশ বছরে যাঁর পাঠকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কোনো তরুণ আজ যদি সূরদাস-এর অথবা হাইন-র লেখার অনুবাদের বই দুটি পড়তে চান, তাঁকে আগে পাহাড় সরাবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সমবেত ঔদাসীন্যের ফলে আজ এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, এই সেদিন, ২০১৮-তে প্রকাশিত তাঁর একটি গল্পসংকলনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত নই।
।। ৩ ।।
দ্বিতীয় প্রস্তাব: প্রতিটি উন্নত ভাষার এক অথবা একাধিক সম্পদ থাকে, যেমন আমাদের ভাষার অন্যতম প্রধান সম্পদ তার গীতিকবিতা। একে যদি একটি সরোবরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রত্যেক কবি সেই সরোবর থেকে জল তুলে নিচ্ছেন। প্রক্রিয়াটি একমুখী হত যদি, কোনো–না-কোনো সময়ে এসে দেখা যেত নতুন কবিতা যা লেখা হচ্ছে, তা পুরাতন কবিতারই অনুগমন। নানা যুগের দিশারিদের অবদানের ফলে আমাদের সেই দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাংলা লিরিকের সরোবর থেকে যতটা জল তুলে নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশি জল, দিশারিরা সরোবরকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক; ১৮৫৮ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করা দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর লেখার চেয়ে, একশো বছর বাদে ওই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করা কোনো কবির লেখা উন্নততর জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ১৮৫৮-র কবির চেয়ে ১৯৫৮-র কবির লেখা উৎকৃষ্ট, সাহিত্য ওইরকম কোনো সরলরৈখিক নিয়ম নেই; এর অর্থ এই যে, এক শতাব্দীর পরিসরে, বাংলা ভাষার পথপ্রদর্শকরা আরও অনেক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন, আরও অনেকরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাঁরা আমাদের প্রস্তুত করে তুলেছেন। যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, ততদিন, অন্তত প্রেমের লিরিকের গোত্রে, দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর স্থান থাকবে অমলিন, কিন্তু একইসঙ্গে বলা যায়, নিম্নোদ্ধৃত বহুস্তরসম্পন্ন প্রেমের লিরিকটি লেখা, তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল:
“কোনো–কোনো মেয়ে যুগ্মপদবী রাখে
বিয়ের পরেও, যেরকম কিনা আজ
সুচরিতা আজ মিত্র মজুমদার
একদিন এক গহন পথের বাঁকে
সুচরিতাকেই এই কথা একবার
প্রশ্ন করলে সে বলে অকুতোলাজে:
আমি যদি তাকে নিতাম তাহলে নাকি
সে নিত শুধুই আমার উপাধিনাম
এই কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম”
[‘কোনো-কোনো মেয়ে’ / কাব্যগ্রন্থ: ‘চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো’ ২০১৫]
পাঁচশোটি অচেনা কবিতার একটি সংকলনে সব লেখকদের নাম মুছে ফেললেও তাদের মধ্য থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র একটি কবিতা চিনে নিতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না। এটি কবির স্বকীয়তার অগ্নিপরীক্ষা এবং আমরা জানি যে, খুব বেশি সংখ্যক লেখক ওই পরীক্ষা থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। কিন্তু, চূড়ান্ত পরীক্ষাটি অন্য, এবং তা বহুগুণ কঠিনতর: স্বকীয়তা-চিহ্নিত কজন কবির লেখা নিখুঁত অনুকরণ করা যায়? এই পরীক্ষাতেও অলোকরঞ্জন খুব সহজেই উত্তীর্ণ, কারণ তিনি অননুকরণীয়।
তাঁর ছন্দপ্রয়োগ, তাঁর অন্বয়, এমনকি, খুব দক্ষ অনুকারক হলে, তাঁর শব্দচয়নও অনুকরণীয়, কিন্ত তাঁর কাব্যভাবনা অনুকরণ করা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে, প্রথমেই, ‘অনুকরণ’ আর ‘আহরণ’-এর পার্থক্য চিহ্নিত করা দরকার; তাঁর লেখা থেকে যিনিই চিন্তাসূত্র আহরণ করবেন তিনি লাভবান হবেন, আর, এর বিপরীতে, যিনি তাঁর বাচনভঙ্গিমা অনুকরণ করতে সচেষ্ট হবেন, তাঁর অপঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। অলোকরঞ্জন নিজে অগণিত উৎসমুখ থেকে সম্পদ আহরণ করেছেন, কিন্তু সেগুলি উত্তমরূপে তাঁর ভিতরে জীর্ণ না হয়ে, তাঁর লেখার খাতায় কখনও উপস্থিত হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত রচনায় কেবল একটি উৎসমুখের উল্লেখ করছি: অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় দুটি পরিভাষা প্রচলন করেছিলেন, ‘দুর্যোগের সাহিত্য’ এবং ‘Weltschmerz’, যাদের স্বকীয় প্রতিফলন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ভাবনায় লক্ষ করা যায়। বিদেশি শব্দটির মর্মার্থ আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য, কার্যসিদ্ধির জন্য আমরা এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করতে পারি: বিশ্বসংসার ও তার দুঃখময় পরিণতির কথা ভেবে লেখকের অবসাদ। ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’-পরবর্তী অলোকরঞ্জন-এর উপর Weltschmerz-এর গভীর প্রভাব আছে বলে মনে হয়। কৃষকের জীবনে কৃষিজমির ভূমিকা ও লেখকের জীবনে Weltschmerz থেকে উদ্ভূত মনোলোকের ভূমিকা অভিন্ন; Weltschmerz থেকে মহৎ কবিদের মুক্তি নেই, বস্তুত, সেটাই তাঁদের সৃষ্টিশীলতার উৎস। আমাদের মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে, কলকাতার এক নামি হাসপাতালে গভীর রাতে আগুন লেগে বহু রোগী ও নৈশ এমারজেন্সি বিভাগের কর্মী হতাহত হন। ক্রমে স্পষ্ট হয় যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিরাপত্তারক্ষা বিধি লঙ্ঘন করে বেসমেন্টটি হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে পরিণত করা হয়েছিল এবং সেটাই ‘দুর্ঘটনা’ ও প্রাণহানির মূল কারণ। গৌণ কারণটি আরও ভয়ানক, যে প্রতিবেশীরা বিপন্ন রোগীদের বাঁচাতে এসেছিলেন, প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে, এই ভয়ে, কর্তৃপক্ষ তাঁদের গলাধাক্কা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের করে দেন। এই সংবাদ ভেসে আসে, পরবর্তী দুঃসংবাদের বাতাস লেগে দূরে সরে যায়। কবির কাছে সেটাই হয়ে ওঠে প্রবল কুজ্ঝটিকা, তাঁর মাথার চারপাশে উচ্চরবে ঘুরতে থাকে:
“বেসমেন্ট শব্দটা দ্যাখো অতর্কিতে বাংলা ভাষায়
ঢুকে গেছে, দাহ্য পদার্থের ভিড়ে মানুষের মুখ
জড়পিণ্ড হয়ে গেল, লাগোয়া বস্তির বাসিন্দারা
ছুটে এসেছিল ঠিকই, আগ্নেয়গিরির শীর্ষচূড়ে
আজন্ম প্রতিপালিত হয়েছে ব’লেই দমকলের
আগেই পৌঁছুতে জানে প্রলয়ের মর্মস্থলে ওরা,
কিন্তু অপাঙ্ক্তেয়, তাই উদ্ধার করার অনুমতি
পেল না, সেই সুযোগে বেসমেন্ট শব্দটা আমাদের
ভাষার ভিতরে এসে পাকাপোক্ত জায়গা ক’রে নিল।
ঢাকুরিয়া ব্রিজে কোনো হেমন্তের অন্ধকারে আর
আমাদের দেখা হবে না, শুধু ঋষ্যমূক চেয়ে দেখি
এখন সমস্ত গাছ সারি সারি গ্যাস সিলিন্ডার।”
[‘রাত তিনটে, বৃহস্পতিবার’ / কাব্যগ্রন্থ: ‘সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বরকণা?’/ ২০১২]
স্কেচ: হিরণ মিত্র
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনচিড়িয়াখানার লোকটা - শর্মিষ্ঠাআরও পড়ুনআজকের দূর্গা - Rajat Dasআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 শিবাংশু | 115.187.***.*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ১০:৩৩100825
শিবাংশু | 115.187.***.*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ১০:৩৩100825মেধাবী বিশ্লেষণ ...
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2405:201:8008:c01e:f112:fdd2:f747:***:*** | ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ ০৪:৪১100947
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2405:201:8008:c01e:f112:fdd2:f747:***:*** | ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ ০৪:৪১100947দেরি হয়েছে পড়তে, কিন্তু খুবই ভালো লাগল।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... dc, Aditi Dasgupta, Ranjan Roy)
(লিখছেন... Mou)
(লিখছেন... বর্ণনা হালদার , হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু)
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, kk, অরিন)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, নীল, অরিন)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
















