- বুলবুলভাজা পড়াবই কাঁটাতার

-
বর্ডার, কাঁটাতার, খণ্ডিত দেশ
সোমনাথ গুহ
পড়াবই | কাঁটাতার | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | ২৭৭১ বার পঠিত - ১৯৪৭ উত্তর ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছিল নতুন কিছু শব্দবন্ধের। এই প্রবীণরা কখনও স্বাধীনতা বলেননি, বলেছেন পার্টিশন, তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে শব্দ ভারতের অবদান। পার্টিশনের হাত ধরে এসেছে উদ্বাস্তু। রিফিউজি কলোনি। তারও পরে এসেছে অনুপ্রবেশ। বসেছে কাঁটাতার। এসেছে এনআরসি, নতুন নাগরিকত্ব আইন। শুরু হয়েছে "বৈধ-অবৈধ" বিচার। শোনা যাচ্ছে, নতুন শব্দবন্ধ, "অবৈধ অনুপ্রবেশ"। যাঁরা বিচার করছেন, তাঁদের বিচার কে করে। এসব শব্দের, আখ্যানের জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশভাগের এই আদি পাপ, মুছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এভাবেই থেকে গেছে বেদনায়, ভাষায়, আখ্যানে। থেকে গেছে, এবং এখনও যাচ্ছে। সেই আখ্যানসমূহের সামান্য কিছু অংশ, থাকল পড়াবই এর 'কাঁটাতার্' বিভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায়।
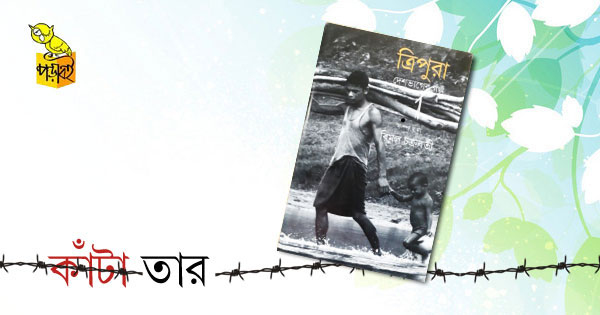
‘না হুনলাম কিনা ঢাকায় ‘গরম’ তাই…’ গ্রাম্য লোকটার এই কথাটায় কোনও আমল না দিয়ে গেন্ডারিয়া স্টেশনে নেমে পড়েছিল মকবুল। তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে, পশ্চিম থেকে ঢাকায় বাড়িতে ফিরছে সে। স্টেশন শুনশান, গেটে চেকারও নেই। পথঘাট ফাঁকা, চায়ের দোকান বন্ধ, ছোটো বাড়িগুলো ঝিমুচ্ছে। ডানদিকের শেষ বাড়িটা পেরিয়ে কয়েকটা কথা শুনে রক্ত হিম হয়ে গেলো মকবুলের। ঘণ্টাখানেক আগে পুলের ওপর একটা হিন্দু ছেলেকে কেটে ফালা ফালা করে ফেলেছে; আটটা হিন্দু এবং ছ’টা মুসলমানের লাশ পড়ে গেছে এর মধ্যেই। হিসাব বরাবর করার জন্য ওত পেতে আছে উন্মত্ত কিছু যুবক। মকবুল ভাবছে, সে বোধহয় নির্ঘাৎ সাত নম্বর হবে। কে জানি আবার আওয়াজও দেয় ‘ঘণ্টাখানেক আগে নাকি একটা মুসলমান ইস্টিশানে নাইম্যা এই রাস্তা দিয়া আইছ্যে…’ মকবুল পানাপুকুরের মধ্যে গলা অবধি সেঁধিয়ে যায়, ভাবে এ জীবনে আর আম্মার দ্যাখা পাইলাম না!
দাঙ্গা-কবলিত পূর্বে মকবুল ভুল দিনে ফিরে এসেছে। গ্রাম্য লোকটা তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল, সে আমল দেয়নি। ‘ত্রিপুরা: দেশভাগের গল্প’ সংকলনে বিমল চৌধুরীর গল্প ‘অনুভাব’ এ মকবুলের জান সুতোয় ঝোলে। ’৪৭-এর দেশভাগ এবং তারপর সিকি শতাব্দী ধরে ত্রিপুরার সীমান্তের এপার-ওপার জুড়ে যে রক্তগঙ্গা বয়েছে, মকবুলের ঘটনা তার মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম মাত্র। বাকিটা শুধু হানাহানি – উন্মত্ত, ধর্মান্ধ মানুষের তাণ্ডব। সংকলনের সম্পাদক বিমল চক্রবর্তীর মতে, বিপুল সংখ্যক মানুষ তখন সাময়িক ভাবে হলেও হয়ে উঠেছে তিমিরবিনাশী। সাম্প্রদায়িক বিষ মানুষের যাবতীয় শুভবুদ্ধি, বোধ শুষে নিংড়ে বার করে নেয়। ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে তার মধ্যেকার যাবতীয় হীন, ক্লেদাক্ত, পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি উপচে পড়ে, শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্যকে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। গতকাল অবধি যে প্রতিবেশীর সঙ্গে গলাগলি সম্পর্ক ছিল, ধর্ম তার মাঝে পাঁচিল তুলে দেয়, একে অন্যকে বলে কাফের, ম্লেচ্ছ!
সোমা গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে বলরাম ভাবে, “কী ছিল একদিন আর কী থেকে যে কী হয়ে গেল! যে হিন্দু-মুসলমান ছিল ভাই-ভাই, এক জাতি এক প্রাণ হয়ে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল, বুকের রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল জন্মভূমির মাটি, তারাই পরে পরস্পরের শত্রু হয়ে গেল। আব্বাস, করিম, রেজানুল – ওরা কত দ্রুত বদলে গেল। মৌলবাদের প্রেত তাড়া করেছিল ছেলেবেলার সঙ্গীদের। … অথচ একই মায়ের ভাষা দু’জনেরই। হারাধন মাস্টারের হাত ধরে সেদিন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল বৃদ্ধ ইউনুস মিয়া।” তুষারকণা মজুমদারের ‘সাতপুরুষের ভিটেমাটি’ গল্পে দেশভাগের মর্মান্তিক দৃশ্য ফুটে ওঠে। বাড়ি পোড়ানো হচ্ছে, লুণ্ঠন, খুন চলছে। গোটা পূর্ব বাংলা আতঙ্কে কাঁপছে। চারিদিকে রায়ট, ভৈরব পোলের উপর ট্রেন থামিয়ে বেছে বেছে মানুষকে কেটে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। লেলিহান আগুনের মতো হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে, জোর খবর কলিকাতা আর বিহারেও নাকি দাঙ্গা লেগে গেছে। সুষমার এখনো মনে পড়ে সেই ভয়ানক দিনগুলির কথা। সেই বিশেষ রাতটি ছিল পূর্ণিমা, সারা গ্রাম থমথমে। ভ্রাতৃঘাতী এই হিংসা, খুনোখুনির মধ্যেও বেঁচে থেকে মানবতা, ফুটে ওঠে অমলিন সম্প্রীতির ছবি: “বর্গাচাষি এন্তু মিঞা বলল, বাবু, অবস্থা ভালো না। বাসনকোসন বস্তা ভইরা পানিতে ফালাইয়া আঁর আগে চলেন ঘরে তালা দিয়া।” অনিল তো এদিকে ভাবছে এন্তু মিঞা তার বর্গাচাষি হলে কি হবে, সে তো বিধর্মী, তার সাথে যাওয়া … মিঞা তাকে অভয় দেয়, “সময় নাই বাবু, হেরা কাছে আইছে, খোদার কসম, আঁর দ্বারা আমনাগো কোনও ক্ষতি অইব না, হারা জনম আমনার বাপজানের জমির ধান খাইছি। বেইমান নই, হারামি করুম না – আর দেরি অইলে বাঁইচবেন না।”
মাটি ভাগ হয়, দেশ ভাগ হয়, মানুষ, পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজন, পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জন্ম জন্মান্তর ধরে গড়ে ওঠা গ্রাম, ঝিল, পুকুর, বনবাদাড়, ঘরবাড়ি বিদীর্ণ করে দেয় দিল্লির শাসকের কাঁচি। দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী আসিফ সামিনার পরিবার এপার-ওপার হয়ে যায়, তাদের সদ্য প্রস্ফুটিত প্রেমের মাঝে রাষ্ট্র খুঁটি পুঁতে দেয়। প্রবল ঝুঁকি নিয়ে তারা খণ্ডিত হয়ে যাওয়া নাজির বিলের কাছে দেখা করে, সুখী দাম্পত্যের স্বপ্ন দেখে, তারপর একদিন সীমান্তরক্ষীর গুলিতে দুই উজ্জ্বল তরুণ তরুণী পাচারকারীর লাশ হয়ে যায় (‘কাঁটাতারের সীমানা’ – প্রদীপ সরকার)। একই লেখকের ‘শেকড়’ গল্পে দেখি অনিন্দ্য কুড়ি বছর পরে ফেলে আসা দেশে ফিরে গিয়ে স্মৃতি হাতড়ায়। মনে পড়ে সেই দিনটার কথা – বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে যেদিন তারা পাড়ি দিয়েছিল ওপারে। তাদের ঘোড়ার গাড়ির পিছনে পাগলের মতো ছুটছিল নয় বছরের গ্রাম্য কিশোরী রহিমা। সে উদভ্রান্ত, বড় চাচি আর অনি ভাইকে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, “তুমরা বলে আর আইবা না! এই দ্যাশ ছাইড়া এক্কেবারে চইল্যা যাইতাছ? আর আইবা না বড় চাচি … তুমরা কেউ আর আইবা না?” মুক্তিযুদ্ধের পরে অনিন্দ্য যখন দেশের ভিটে দেখতে ফিরে যায়, আর সে খুঁজে পায়না সরল সেই কিশোরীকে। খানসেনার তাণ্ডবে রহিমার মতো আরও হাজারো নারীর হাহাকার তখনো শুনতে পাওয়া যায় সদ্য স্বাধীন হওয়া সেই দেশের অলিতে-গলিতে।
পশ্চিম পারে মানুষ দিশাহারা। উদ্বাস্তু, শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশি নানা তকমা গায়ে সেঁটে যায় তাঁদের, দিগভ্রান্ত হয়ে তাঁরা খুঁজে বেড়ায় আশ্রয় নেবার ঠাঁই। সীমান্তে ঝপাঝপ তৈরি হয়ে যায় কংক্রিটের পিলার, ঘন কাঁটাতারের আচ্ছাদনে প্রায় বিলীন হয়ে যায় ওপারের নীলিমা-সবুজ। বিএসএফ-বিডিআরের দাপটে সন্ত্রস্ত দু’পারের মানুষ। এরই মধ্যে কিছু মানুষ হয়ে যায় নেই-রাজ্যের বাসিন্দা – ছিটমহল! তাঁরা ইন্ডিয়ায় প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যুবকটি ঐ সময় গেট পেরিয়ে রোজগারের খোঁজে যায়, নেই-ভূমিতে দুশ্চিন্তায় সময় কাটে তার স্ত্রী আর বৃদ্ধ বাবার। রাতে পিতা অসুস্থ, হাসপাতালে নিতে হবে, গেট খোলার জন্য কাতর অনুরোধ জানায় যুবক, তার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে। “ইতনা রাত মে গেট খুলুঙ্গা। তু পাগল হো গয়া কেয়া,” সেন্ট্রি-ছারের বন্দুক উঁচিয়ে ধমক। বাপ মারা যায়, লাশ কাটাছেঁড়ার ভয়ে তারা রাতেই দাফন দিয়ে দেয়। সকালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে যখন বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য দু’জনে গেটের কাছে যায়, সেন্ট্রি তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ করে। তিনজন ছিলে, তিনজনকেই আমার সামনে আসতে হবে, অন্যথা … নিরুপায় দম্পতি অপেক্ষা করে তাদের সন্তান আসার জন্য, যেদিন আবার তারা তিনজন হবে! (‘কাঁটাতারের বেড়ার অপারে’ – মীনাক্ষী সেন)। এই নির্বোধ, নির্দয় সীমান্তরক্ষীদেরই হিংস্র, দুর্নীতিগ্রস্ত, ট্রিগার-হ্যাপি রূপ আমরা দেখি কল্যাণব্রত চক্রবর্তির ‘ইশানপুরের মানুষ’ গল্পে, যেখানে ওপারের সচ্ছল পরিবারের মানুষ পরমেশ এপারে এসে পেটের দায়ে চোরাচালানকারী হয়ে যায়। ভ্রাতৃসম সুবিনয়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন সে বলে, “সীমান্তের এ বিশাল অঞ্চল চোরাচালানির গয়া-কাশী। গরীব মানুষের বাঁচার পথ নেই। না খেয়ে মরার চেয়ে মালিকের মাল এপার-ওপার করা অনেক ভালো কাজ”।
মানুষ এখানে শিকড়হীন, টিলার ঢালের পাথরের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানচ্যুত হয়। কত কারণের জন্য মানুষ বারবার বাস্তুহারা হয় – তথাকথিত উন্নয়ন, নদী-পারের ভাঙন, বন্যা, উপজাতি-বাঙালি সংঘর্ষ। কাঁটাতার তো এখানে বিভীষিকা। কখন যে কার জমিন-ঘর খণ্ডিত করে দিয়ে জীবন-সংসার ফালাফালা করে দেবে, তার ঠিক নেই। ‘ছিন্নমূল’ গল্পের নকুল ঘরবাড়ি, মানসম্মান সব কিছু খুইয়ে এপারে এসে বর্ডারের কাছে এক রুক্ষ জমিতে নতুন করে জীবন গড়ে তুলেছিল। একদিন লোকজন এসে খুঁটি পুতে গেল তার জমির মধ্যে; পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়ে দিল, এ দিল্লির ব্যাপার – এতে তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বজ্রাহতের মতো নকুল দেখল, তার পুরো জমিটাই পড়েছে কাঁটাতারের ওপারে। সে খুঁটিতে লাথি মারে, থুতু দেয়, প্রস্রাব করে; ছোট্ট একরত্তি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করে, “বাবা এইবার আমরা কই যামু?” আর সেই মহিলা যে রেল কলোনিতে এসে কোনও মতে মাথা গুঁজেছিল। সে কী নরকযন্ত্রণা, জন্তুর মতো গাদাগাদি করে বাস! তার ওপর সকাল-বিকাল হুজ্জুতি, এরা অনুপ্রবেশকারী, হঠাও এদের। রাজনৈতিক দাদা, মাফিয়া গুন্ডা-বাহিনীর উচ্ছেদের হুমকি, হেনস্থা। সন্ধ্যায় কাজের বাড়ি থেকে ফিরে দেখে সব ভাঙচুর, লুট, বাবার দেখা নেই। দিগ্বিদিক কাঁপানো তার বিলাপ: “কিন্তু আমরা কোথায় যামু। ওরা বলে আমাদের জন্মভূমি আমাদের দেশ না। এরা বলে আমরা অনুপ্রবেশকারী, তা হলে আমরা কোথায় যামু।”
মীনাক্ষী সেনের ‘পুশব্যাক’ গল্পে যেন আজকের চরম বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব-সংশোধনী আইনের (সিএএ) আভাস পাই। গরাদের পেছনে সুন্দরী মেয়েটি একনাগাড়ে কাঁদছে, তার সামনে দাঁড়ানো শ্যামলা চেহারার শক্তপোক্ত ছেলেটিও কাঁদছে, চাপা কান্না – যা তার সুকুমার মুখকে বিকৃত করছে। তাদের মাঝে দ্বিতীয় প্রাচীর – এক ওয়ার্ডার মহিলা। মেয়েটাকে ফেরত যেতে হবে বাংলাদেশে, কারণ সে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির দশ বছর পার হয়ে যাবার পর ভারতে এসেছে – সে অনুপ্রবেশকারী। ওয়ার্ডার ভাবে, এ এক অদ্ভুত বিচার! জন্মানোর পরে যে দেশে সে মাত্র দশ দিন ছিল, যেখানে সে কাউকে চেনে না, জানে না সেটা তার দেশ হয়ে গেল, আর যেখানে সে কুড়ি বছর ধরে বড় হল, সেটা তার দেশ নয়! এ কী ধরণের বিচার? সে নিজে তো সাতাশ বছর আগে ওপার থেকে এসেছে, তা বলে আজকে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে সেখানে? এই অন্যায্য রায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সত্যটা তার মাথায় ঝিলিক মারে। সে তো হিন্দু, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু, তাই যখন খুশি সে এখানে আসতে পারে, থাকতে পারে। মেয়েটা তা পারে না, সে তো শেখ, মুসলমান, তাই অনুপ্রবেশকারী। কারণটা উপলব্ধি করতে পেরে সে মনে মনে বেশ খুশিও হয়!
সম্পাদক বিমল চক্রবর্তীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ ত্রিপুরার দেশভাগের গল্প একসাথে গ্রন্থিত হয়েছে এরকমটা অন্তত এই প্রতিবেদকের আগে কখনো নজরে আসেনি। সেদিক থেকে এই সংকলনটি অনন্য। কিন্তু একটা খামতি রয়েছে। উপজাতিদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা কোনও গল্প এই সংকলনে নেই। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বাধীনতার পরে যে জনপ্লাবন ত্রিপুরায় আছড়ে পড়েছিল, তাতে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন, কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো স্থানীয় উপজাতিরা। মাত্র দু’দশকের মধ্যে নিজভুমিতে তারা নিদারুণভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল। কিছু সংখ্যার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে – ১৯৪১-এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার তারা ছিল ৬২.০৬%, ১৯৬১-তে সেটা প্রায় হয়ে যায় অর্ধেক, ৩১.৫৫%। ২০১১-র জনগণনায় সেটা প্রায় কাছাকাছি ৩১.৭৮%। একসময় জমি ছিল উদ্বৃত্ত, উর্বর। জনস্ফীতির কারণে তা হয়ে পড়ে দুর্লভ, লাগামছাড়া ব্যবহারের কারণে অনুর্বর। এর ফল কী দুর্বিষহ হয়েছে, সেটা আমরা জানি। উগ্রপন্থা মাথা চাড়া দিয়েছে, জাতিবাদী সংঘর্ষে আবারও রক্তগঙ্গা বয়েছে। এই সংকলনের বাইরে মীনাক্ষী সেনের ‘বনজঙ্গলের বাইরে’ গল্পে নীরব নামক চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে উপজাতি মানসিকতার কিছু আভাস আমরা আগে পেয়েছি। কিশোরীটি যখন তাকে বলে তার বাপকে “উগ্রপন্তি-এ মারছে”, নীরব চমকে ওঠে, তার মুখে আঁধার নেমে আসে। মেয়েটা ভাববে না তো, যে সে-ও উগ্রপন্থী, সমতলের অনেকেরই তো ধারণা – পাহাড়ি মানেই উগ্রপন্থী!
কিছু গল্পে মূলত বাঙালি দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি-উপজাতি সমস্যার আভাস আছে। যেমন ‘মরা গাঙ’ গল্পে মিনতি তার ছেলের প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমাদের কোনও দেশ নাই, এখানকার বাঙালিরও কোনও দেশ নাই। কোনও এক টাইগার ফোর্স নাকি বাঙালিদের ত্রিপুরা ছেড়ে দিতে নোটিশ দিয়েছে। ‘দ্বিতীয় স্বদেশ’ গল্পে নদের চাঁদ যখন খবর পেয়ে তার গ্রামে ছুটে যায়, সেটা যেন এক বিধ্বস্ত রণাঙ্গন। চালাঘরগুলো পুড়ে খাক হয়ে গেছে, যারা পালাতে পারেনি – তারা সব গুলি খেয়ে চিত হয়ে আছে। সুবিমল রায়ের ‘সেতু’ গল্পে সুমন্ত রিয়াং আর সনাতন সরকার পিয়ারি সেতু, অর্থাৎ ভালোবাসার সেতু, নিমার্ণের চেষ্টা করে। বিষ্ণুছড়ার ওপরে সমতল গ্রাম ও পাহাড়ি জনপদের মধ্যে এক মনরোম পরিবেশে অবস্থিত সেই সেতু। এক রাতে প্রবল বিস্ফোরণে সেটা ভেঙে পড়ে, খুঁটি গুঁড়িয়ে যায়, পাটাতন ছিটকে পড়ে বিষ্ণুছড়ার জলে। কেউ বলে, সেতুটা মেরামত করতে হবে। আরেকজন বলে, মেরামতে হবে না, পুরো পুলটা নতুন করে তৈরি করতে হবে।
ত্রিপুরা: দেশভাগের গল্প
সম্পাদনা-বিমল চক্রবর্তী
প্রকাশক-গাঙচিল
মুদ্রিত মূল্য - ৫৫০/
বাড়িতে বসে বইটি পেতে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে অর্ডার করুন +919330308043 নম্বরে।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
দ | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৯:১২498718
- এই বইটা যোগাড় করতে হবে।
-
 santosh banerjee | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৮:৪০498755
santosh banerjee | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৮:৪০498755 - খুব প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন। বর্তমান প্রজন্মের কথা শুধু নয়, আমরা, যারা দেশভাগের কথা শুনেছি মা বাবার কাছে, তাদের ও জানা উচিত , কি নৃশংসতা আর অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করিয়েছে তৎকালীন দেশনেতারা, সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ভিটে মাটি সব ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল , শুধু খমতায় আসার জন্য।
-
 ভাষা ভাষা | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২০:২০498757
ভাষা ভাষা | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২০:২০498757 - অনেক ধন্যবাদ বইটার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য । বইটার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্য কিছু গল্প ছোট পরিসরে নিজের মতো করে বলার মধ্যে একটা ভালবাসা, একটা যত্নেরও ছাপ রয়েছে ।তারও পর উপজাতি- দৃষ্টিকোণের উল্লেখ রাজনৈতিক-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রসারিত হৃদয়েরও পরিচয় বহন করে ।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












