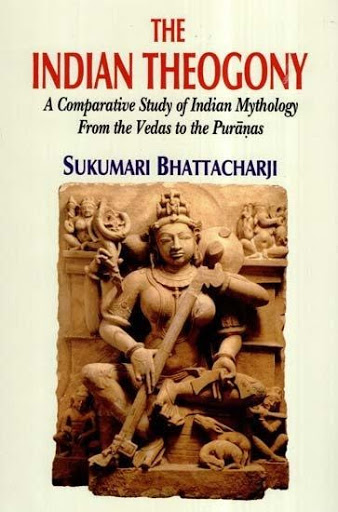- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
শতবর্ষে সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) : ‘কোনো রাজার অনুগত হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়’
সুকুমারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপে কুমকুম রায়
পড়াবই | মনে রবে | ২৩ মে ২০২১ | ৩৯২২ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) - স্মরণাতীত কালে ফ্যাসিবাদের এমন দাপট এ দেশে দেখা যায়নি। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সেই আশঙ্কাতেই উতলা হয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের স্বরূপের নিরন্তর অন্বেষণে অপরিহার্য তো বটেই, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের যাবতীয় লেখালিখি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়েরও জরুরি হাতিয়ার। শতবর্ষে গুরুচণ্ডা৯-র ‘পড়াবই’ বিভাগের শ্রদ্ধা। রইল তাঁর নিজের সাক্ষাৎকার, কন্যা তনিকা সরকারের স্মৃতিচারণ, বিজয়া গোস্বামী, রণবীর চক্রবর্তী ও কণাদ সিংহ-র তিনটি লেখা।
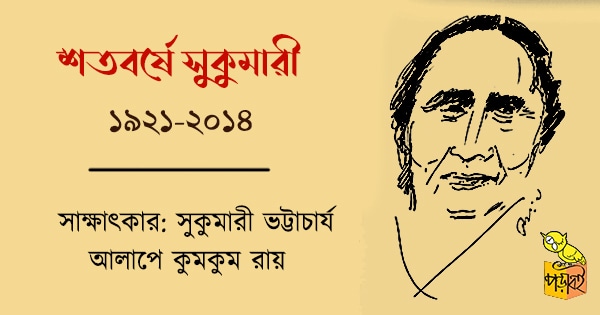 সংস্কৃত প্রথম প্রেম। ইতিহাস দ্বিতীয়। ১৯৩০-এর দশকে খ্রিশ্চান মহিলাদের পক্ষে সংস্কৃত শেখা ছিল এক দুরূহ লড়াই। জিতেছিলেন। প্রথাগত পড়াশোনা ইংরেজি ও সংস্কৃততে। বল নাচের ক্লাস বয়কট করে চেয়েছিলেন উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলীর তালিম। হয়নি। বিপ্লবীদের গোপনে সাহায্য। বাড়িতে লুকিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের আশ্রয়। এবং নিজের লেখালিখির কথা। স্কুলজীবন থেকে শেষ বয়স—স্মৃতিচারণ। আলাপে ইতিহাসের অধ্যাপক কুমকুম রায়
সংস্কৃত প্রথম প্রেম। ইতিহাস দ্বিতীয়। ১৯৩০-এর দশকে খ্রিশ্চান মহিলাদের পক্ষে সংস্কৃত শেখা ছিল এক দুরূহ লড়াই। জিতেছিলেন। প্রথাগত পড়াশোনা ইংরেজি ও সংস্কৃততে। বল নাচের ক্লাস বয়কট করে চেয়েছিলেন উদয়শঙ্করের নৃত্যশৈলীর তালিম। হয়নি। বিপ্লবীদের গোপনে সাহায্য। বাড়িতে লুকিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের আশ্রয়। এবং নিজের লেখালিখির কথা। স্কুলজীবন থেকে শেষ বয়স—স্মৃতিচারণ। আলাপে ইতিহাসের অধ্যাপক কুমকুম রায়(অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্যের এই সাক্ষাৎকারটি নেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক কুমকুম রায়, ২০০৩ সালে, ইংরেজিতে। একটি স্মারক পুস্তিকা ছাড়া এটি আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অধ্যাপক রায়ের অনুমতিক্রমে এর বাংলা তরজমা এখানে প্রকাশিত হল।— সম্পাদক)
কুমকুম রায়— সুকুমারীদি, আমরা হয়তো আপনার শৈশব, গোড়ার দিকের পড়াশোনা, যা-কিছু আপনার গড়ে ওঠার ওপর প্রভাব ফেলেছিল, এই সব বিষয় দিয়ে কথপোকথন শুরু করতে পারি। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, প্রাচীনকালের ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস ইত্যাদির প্রতি আপনার আগ্রহ কত তাড়াতাড়ি এবং কী ভাবে জন্মায়?
সুকুমারী ভট্টাচার্য— যে বিষয়গুলি তুমি বললে, সেগুলি ছাড়াও আমার আরও যে বিষয়গুলির প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল ‘আইডিয়া’-র ইতিহাস।আমার নিজের নানা ধ্যান-ধারণা, আইডিয়া, গড়ে ওঠার পেছনে নিঃসন্দেহে আমার বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমার বাবা সরসীকুমার দত্ত স্কুল শিক্ষক ছিলেন। স্কটিশ চার্চ স্কুলে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়াতেন। তবে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন ইতিহাস আর দর্শনে। সত্যি বলতে কী, তাঁর যে স্মৃতি আমার মনে রয়ে গিয়েছে তা এক বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তির স্মৃতি, যিনি শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের নানা দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।
তাঁর এক ছাত্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রক্তন শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণে আছে যে, তিনি দুর্দান্ত পড়াতেন, সৃজনশীল কল্পনায় ভরপুর, কিন্তু ছাত্ররা ঠিক কতটা নিতে পারে তাও বুঝতেন। সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসে আমার আগ্রহের জন্য আমি ওঁর কাছেই ঋণী। আমার বয়স বছর দশেক হতে না হতেই আমি বাড়িতে ওঁর কাছেই মুখে মুখে সংস্কৃত শেখা শুরু করে দিয়েছিলাম। আমায় ভীষণ ভালোবাসতেন। সচেতন করেছিলেন—খ্রিশ্চান মেয়ে হয়ে সংস্কৃত পড়লে কিন্তু স্বীকৃতি পাওয়া খুব কঠিন হবে। তিনি আমাকে পড়তে উৎসাহ দিতেন খুব, খুব যে ধরা-বাঁধা পড়াশোনা তা নয়, কিন্তু নানা বিষয়ে পড়াশোনা। ভালো কথা, পরবর্তীকালে আমিই আবার ওঁকে মার্কস আর ফ্রয়েডের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলাম।
আমার মা (শান্তবালা) একেবারে ইস্পাত-চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ওঁর বিষয়ে তোমায় কয়েকটা গল্প বলি। আমরা তখন কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটে থাকি। একবার আমাদের এক পড়শির স্ত্রী মৃত সন্তানের জন্ম দিলেন। মা দেখেন, ভদ্রমহিলা বাড়িতে ঢোকার যে সিঁড়ি সেখানে বসে আছেন। মা সেই ভদ্রমহিলার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? জানা গেল, নাপিত আসছে সেই ভদ্রমহিলার চুল ও নখ কাটা হবে, তা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। মা জানতে চাইলেন তিনিই তাঁর চুল ও নখ কেটে দিতে পারেন কি না, তারপর নিজেই দ্রুত সে কাজ শুরু করে দিলেন! শ্মশানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর যেসব আচারগত বিধি-নিষেধ ছিল তাও মা ভেঙে দিয়েছিলেন। মায়ের দেশপ্রেম ছিল প্রবল, বহু জাতীয়তাবাদী নেতার ছবি জমিয়েছিলেন। একবার আমাদের বাড়িতে পুলিশি তল্লাসির উপক্রম হল, তিনি নিজেই নির্দ্বিধায় সব ছবি পুড়িয়ে দিলেন।
সংস্কৃতই যে আমার প্রথম প্রেম তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় প্রেম, আমি বলব, ইতিহাস। তবে দর্শনেও আমার বরাবর আগ্রহ ছিল। নারী হিসেবে এবং খ্রিশ্চান হিসেবে সংস্কৃত শিখতে গিয়ে এবং পড়াতে গিয়ে যে কী সমস্যার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছিল, তা নিয়ে লিখব ঠিক করেছি।
অনেক মনীষার সংস্পর্শে আসার সুযোগও আমি পেয়েছি। শিশুবেলায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, এমনকি গান্ধিজিকে ফুলও দিয়েছি।
ক— আপনার স্কুলজীবন কেমন ছিল?
স— প্রথম দু-বছর খ্রাইস্ট চার্চ স্কুলে পড়েছিলাম। তারপর সে স্কুল দমদমে উঠে যাওয়ায় সেন্ট মার্গারেট স্কুলে ভরতি হয়ে গেলাম। বিশেষ করে মনে আছে মিস্ লিন্ডসে-র কথা। প্রিন্সিপাল ছিলেন। খুব ভালো পড়াতেন। আমাদের মধ্যে কবিতার বিষয়ে একটা উত্তেজনা তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। যেমন, তাঁর কাছে সত্যি সত্যি স্কাইলার্কের ডাক রেকর্ড করা ছিল। আবার, যেসব কবিতা পড়াতেন সেগুলির সঙ্গে মানানসই নানা ছবি দেখাতেন আমাদের। স্কুল পাস করার আগেই শেলি, কিট্স, বায়রন এসব প্রায় আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। আর-একটা অভ্যাস হয়েছিল আমাদের—শুক্রবার কোনো না কোনো বই তুলতাম লাইব্রেরি থেকে, শনি-রবি সেটা পড়ে ফেলতাম এবং সোমবার সেটা নিয়ে লিখতাম। এর ফলে আমাদের একাধারে পড়া এবং লেখার অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল।আমার অনেক প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসেস থারু। ১৯৩৫-৩৬ সালে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। আর তাঁড় পড়ানোর যেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল, তা হল তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত মাথায় রেখে কী ভাবে সাহিত্য পড়তে হয়। ১৯৯০ সালে তাঁর পুত্রবধু সুজ়ি থারুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জেনে খুব ভালো লেগেছিল যে, মিসেস থারুর আমাকে মনে আছে।
এ ছাড়া আমাদের এক খ্রিশ্চান সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের সংস্কৃত লিখতে শিখিয়ে ছিলেন। অনেক পরে বুঝে ছিলাম স্কুলজীবনে এটা শিখে ফেলা বেশ বিরল ব্যাপার ছিল।
ম্যাট্রিকুলেশনে আমি সংস্কৃত এবং লজিক দুটোতেই খুব ভালো মার্কস পেয়েছিলাম। সংস্কৃততে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কারণ তাকেই আমি মনে করতাম ভারতীয় সংস্কৃতি বোঝার চাবিকাঠি। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের যে বিপুল পরম্পরা তা যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি এমনটা অবশ্য নয়।
ক— স্কুলের লেখাপড়ার বাইরে কী করতেন? খেলাধুলা ইত্যাদি…?
স— ব্যাডমিন্টন খেলতাম অল্প-বিস্তর। কিন্তু তা ছাড়া খেলাধুলায় আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। একবার বল-ডান্সের আসরে একটা কাণ্ড ঘটেছিল, সেটা তোমায় বলতেই হবে! একদিন আমাদের স্কুলে নৃত্যপরিবেশনে আমন্ত্রিত হলেন উদয়শঙ্কর (যাঁর স্ত্রী আমাদের স্কুলের ছাত্রী ছিলেন এক সময়ে)। আমরা খুব ইম্প্রেস্ড হলাম। পরের বছর স্কুলে বল-ডান্স শুরু হল। তখন আমার মধ্যে সবে জাতীয়তাবাদ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আমি আপত্তি তুলে বললাম, নাচ যদি শিখতেই হবে, তবে উদয়শঙ্কর যে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন তাই শিখব। বলাই বাহুল্য, স্কুলের পক্ষে সে তালিমের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আমি বল-ডান্স ক্লাস বয়কট করলাম, সে নাচ আর আমার শেখা হল না!তেমনই, আমি ‘গার্ল গাইড’১-এ যোগ দিতে পারিনি। কারণ, ঈশ্বর, সম্রাট এবং দেশের নামে শপথ নিতে আমি অস্বীকার করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল কোনো রাজার প্রতি আনুগত থাকা আমার দ্বারা হবে না।
বেহালা বাজাবার চেষ্টা করেছি। তবে সেটা অনেক পরে, যখন আমি পিজি মুসলিম স্টুডেন্টস হস্টেলের সুপার। আমার বাবা-মা দুজনেই বেহালা বাজাতেন।
ক— স্কুলে খ্রিশ্চান প্রভাব কতটা ছিল আপনার ওপর?
স— বাইবেল ক্লাস হত স্কুলে। সেটা খুব কাজের ছিল, কারণ তাই করেই পুরো গ্রন্থটা আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া বাড়িতেও খ্রিশ্চান ধর্মের নানা আচার পালিত হত। বাবা-মায়ের সন্তানদের মধ্যে আমিই সব থেকে বড়ো ছিলাম। আমার দুই বোন আর এক ভাই। আর এক কাকু বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার ছিলেন, ১৯৪২ সালে তাঁর কন্যা মারা যায়। সেই থেকেই গোটা পরিবারের ওপর ক্রমবর্ধমান ভাবে খুব গোঁড়া পেন্টাকোস্টাল২ বিশ্বাস, আচার-আচরণের প্রভাব পড়তে থাকে। প্রার্থনার ওপর সাংঘাতিক জোর দেওয়া হত, আর নিজেকে চেনার প্রয়াশের ওপর। কাজেই, বাইরে হয়তো যখন তাক-লাগানো সূর্যাস্ত হচ্ছে, আমরা ঘরবন্দি হয়ে প্রার্থনা করছি। এই বাঁধনে বিরক্ত হয়ে আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও শুরু করেছিলাম। কাজেই, আমরা ভাই-বোনেরা একে অপরকে পছন্দ করি ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু নেই যাতে আমাদের সকলেরই আগ্রহ আছে। আমার লেখাপত্তর তারা পড়ে না। একসঙ্গে করার মতো খুব একটা কিছুই নেই আমাদের মধ্যে। আমার জীবনের সব থেকে শোকের মুহূর্ত ১৯৪৫ সালে বিনা চিকিৎসায়, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায়, মাত্র ৫২ বছর বয়সে আমার বাবার মৃত্যু। চিকিৎসা হয়নি কারণ আমার পরিবার মনে করেছিল ওষুধ নয়, ধর্ম-বিশ্বাসের জোরেই বাবা সেরে উঠবেন।
ক— স্কুল পাস করার পরে কী করলেন?
স— ভিক্টোরিয়া কলেজে চার বছর (১৯৩৮-৪২) পড়লাম। সংস্কৃত নিয়ে পড়েছিলাম। দুই আসাধারণ পণ্ডিত আমায় পড়াতেন, এবং নির্দ্বিধায় পড়াতেন। বিশেষ করে মনে আছে একজন তো আমাকে বেদও পড়িয়ে ছিলেন। পরীক্ষার রেজাল্টের কথা তোমায় বলতেই হবে! সেই (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের) সময় (কলকাতায়) বোমা পড়বে এই আশঙ্কায় পুরুলিয়াকে নিরাপদ ভেবে আমরা সপরিবারে সেখানে চলে গেলাম। সেখানেই পরীক্ষার রেজাল্ট এল, এক বন্ধু দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেল! সেই ফল দেখে তো আমার বাবা বিশ্বাসই করেননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কাজেই তিনি আমাকে জানতেই দেননি, এই ভেবে যে পরে ঠিক ফলাফল যখন জানা যাবে আমার মনখারাপ হবে। আমি যে সত্যিই খুব ভালো রেজাল্ট করেছি এটা তিনি বিশ্বাস করলেন আমার এই সাফল্য উদ্যাপন করতে পণ্ডিত মশাই একটি কবিতা লিখে আমাদের বাড়িতে আসার পর!১৯৪২। তখন আমি সংস্কৃতে এমএ করা শুরু করে দিয়েছি, এমতাবস্থায় খ্রিশ্চান ছাত্রী হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে কিছু শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের ফলে আমাকে দু-বার ভাবতে হল—আমি কী নিয়ে পড়ব, সংস্কৃত না ইংরেজি। টস্ করলাম। ইংরেজির পক্ষে গেল সেই টসের ফল। কাজেই সেই আমার ইংরেজিতে প্রথম এমএ-টা করা শুরু হল। দু-বছরের সিলেবাস আমায় শেষ করতে হয়েছিল সাত মাসে। সব মিলিয়ে যতটা ভালো ফল করব ভেবেছিলাম তা করতে পারিনি। কারণ যদিও বেশ কিছু পেপারে খুবই ভালো করেছিলাম, একটাতে ফল খুব খারাপ হয়েছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন এটা আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ।
যাই হোক, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে আমি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে শিক্ষক হয়ে যোগ দিই, ১৯৫৭ সাল অবধি সেখানেই ছিলাম। এর মধ্যে ১৯৫৪ সালে সংস্কৃত নিয়ে প্রাইভেটে এমএ পাস করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে। তারপর বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দিই। সে বিভাগে তখন মাত্র যে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন আমি তাঁদের একজন ছিলাম। একটা বিষয়ে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম—আমার মনে হচ্ছিল টেক্স্টগুলি তাদের মূল ভাষায় না পড়ে আমি যদি সেগুলির তরজমার ওপর নির্ভর করে ছাত্রদের পড়াই তা হলে বিষয়টির প্রতি অন্যায় করা হয়। পরে ১৯৫৮ সালে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের সংস্কৃত বিভাগে যোগ দিই ডিন অধ্যাপক এস কে দে-র হস্তক্ষেপে, এবং ১৯৮৬ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত সে বিভাগেই ছিলাম।
ক— আপনি বিয়ে কবে করলেন?
স— ১৯৪৮ সালের মে মাসে। আমার স্বামী, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির শিক্ষক অমল ভট্টাচার্য এক অনন্য মানুষ ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল আশ্চর্য। মনে আছে আমরা যখন কেমব্রিজে ছিলাম, এক পোলিশ বন্ধু বলেছিল যে সে পোল্যান্ডের বিষয়ে যা জানে, তার থেকে বেশি জানেন আমার স্বামী। আর-একবার, বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নূর ইয়ালমান বলেছিলেন যে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সাত হাজার বছরের ইতিহাসের বহু কিছু শিখেছিলেন আমার স্বামীর কাছে।
ক— আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হল কী করে?
স— যখন ইংরেজিতে এমএ করছিলাম, উনি আমার প্রাইভেট টিচার ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি গভীর বিশ্বাসী খ্রিশ্চান আর উনি নাস্তিক। আমাদের পরিবার আবার স্বদেশিয়ানায় খুব বিশ্বাসী ছিল। যেমন, বাড়িতে কারও জন্মদিন হলে, পায়েস হত, আমরা চন্দনের টিকা পরতাম, কেক কাটা হত না। কিছু কাল আমরা নিজের নিজের মতো চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর মধ্যে আমি কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী সাহিত্য পড়তে শুরু করেছিলাম। ভবানী সেন কিছু রুশ সাহিত্যের বই ধার দিয়েছিলেন।
ক— ১৯৪০-এর দশকের বিষয়ে কিছু বলুন—সেই মন্বন্তরের বিষয়ে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ, এসব নিয়ে আপনার ভাবনা কী?
স— দেশভাগের সময় মেডিক্যাল কলেজের এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে একত্রে ধর্ষিতা নারীদের সাহায্যের চেষ্টা করেছিলাম। ধর্ষিতা মুসলমান নারীদের জন্য পার্ক সার্কাসে একটা আশ্রয়-আবাসও গড়ে তুলেছিলাম। এর আগে মন্বন্তরের সময় যে সব সংগঠন ত্রাণ বিলির চেষ্টা করছিল তাদের সঙ্গেও কাজ করেছি। তবে সেটা সমাজসেবা হিসেবে।
১৯৪০-এর দশকে গোপনে বিপ্লবী লেখাপত্তর, পোস্টার ইত্যাদি ছাপার ক্ষেত্রেও আমি সাহায্য করেছি। এটা রেণু চক্রবর্তীর প্ররোচণায় (তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে আমার শিক্ষক ছিলেন)। তিনি আমাকে বললেন মিশনারিদের কাছ থেকে ছাপার যন্ত্রপাতি ধার করে আনতে। এদিকে, মিথ্যে কথা বলা তো আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হল। তবুও সেই ভদ্রলোককে বলেছিলাম ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস নোট বিলি করতে ওই ছাপার যন্ত্রপাতি দরকার। আমার কেমন মনে হয়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি পুরোটা সত্যি বলছি না। আমার এক সহকারী এ কাজে আমায় সাহায্য করেছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আমি যা করছি দেশের ভালোর জন্যই করছি।
তা ছাড়া, আমার আর একটা সুবিধা ছিল, আমি হস্টেলের সুপার ছিলাম। কাজেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে, খাবারদাবার, জামা-কাপড়, সাময়িক আশ্রয় ইত্যাদি দিতে পারতাম। পরে আমাদের ফ্ল্যাটে আমরা পার্টির অনেক সদস্যকে রেখেছি। সে কাজে বিপদ ছিল, কারণ ফ্ল্যাটটার একটাই দরজা ছিল, পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর কোনো সুযোগ ছিল না। এ সব কিছুতেই আমি আমার স্বামীর সাহায্য পেয়েছি।
১৯৪৭ সালের পরেও (পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী৩) বিধানচন্দ্র রায়ের নানা কালা আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছি, আবার বিভিন্ন শান্তিমিছিলেও হেঁটেছি। এমনকি পার্টি সম্মেলনে অনুবাদকের কাজও করেছি গোপনে (গোপনে কারণ আমি তখন সরকারি কলেজে শিক্ষক)।
ক— আর আপনার লেখালিখি? সেটা শুরু হল কবে নাগাদ? আপনি তো ইংরেজি বাংলা দুই ভাষাতেই লেখেন, অন্যান্য ভাষাও জানেন। তা, এই সব লেখার মধ্যে কোন্গুলিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আপনার?
স— আমি প্রথম লিখি নাগপুর টাইম্স-এর জন্য, সেটা ১৯৪০-এর দশকে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নানা প্রবন্ধ। ইংরেজিতে। এর পরে আমি যে লেখাটা লিখি সেটার শিরোনাম ছিল ‘The Indian Theogony’। দশ বছর লেগেছিল লিখতে। টাইপ করা পাতায় পাক্কা ৭৬০ পাতা। আমি ভেবেছিলাম এটা একটা বই করব। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির প্রিন্সিপাল বললেন লেখাটা আমার ডিলিট-এর গবেষণা হিসেবে জমা দেওয়া উচিত। যথারীতি সেটা করতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হল। পরে অবশ্য বইটা বেশ বিখ্যাত হয়েছিল, আমি ডক্টরেট ডিগ্রিটাও পেয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ সম্মানিত বোধ করলাম কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস বইটা প্রকাশে আগ্রহ দেখানোয়। সিইউপি থেকে সেটা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত সেই বছরই আমার স্বামী মারা গেলেন।এর পরের কাজটা ছিল মৃচ্ছকটিক-এর বাংলা তরজমা। ১৯৭৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশ করে। ১৯৮০-র দশক জুড়ে আমি আকাশবাণীতে একাধিক বক্তৃতা দিই। সেগুলি ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য বহু বইয়ের আলোচনাও করেছিলাম। আবার বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলনে ‘পেপার’ পড়েছি। আবার, ‘প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য’ নামে একটা বইও লিখেছিলাম। সেটা ১৯৮৮-তে আনন্দ পুরস্কার পায়। এ ছাড়া, ১৯৮০-৯০-এর দশকে আমার যেসব বই প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আছে Literature in the Vedic Age (দুই খণ্ডে), Buddhist Hybrid Sanskrit Literature, Women and Society in Ancient India, Classical Sanskrit Literature, Suniti Kumar Chattopadhyaya, Legends of Devi, In Those Days, Fatalism, Its origin and Development in India (বাংলা তরজমায়, নিয়তিবাদ)। এ ছাড়া বেরিয়েছিল, ‘বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য’, ‘বেদে সন্ন্যাস ও নাস্তিক্য’, ‘বিবাহ প্রসঙ্গ’, ‘উত্তরাধিকার’, ‘হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা’, ‘প্রাচীন ভারত’, ‘রামায়ণ ও মহাভারতের জনপ্রিয়তা’, ‘অপসংস্কৃতি’, ‘গৌতম বুদ্ধ’ এবং ‘রামায়ণ’। এগুলির মধ্যে শেষ চারটি লিখেছিলাম সদ্য সাক্ষর হওয়া মানুষদের জন্য।
তুমি লক্ষ করে দেখবে, অ্যাকাডেমিক লেখালিখি বলতে যা বোঝায়, তার অধিকাংশই করেছি ইংরেজিতে। আর বাংলায় লিখেছি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয় নিয়ে। আমি এখনও জনপরিসরে অনেক বক্তব্য রাখি— রেডিয়োতে, টিভিতে, বাংলায়, ইংরেজিতে, বিশেষ করে মৌলবাদ আর হিন্দুত্ব নিয়ে।
The Indian Theogony বইটার বিচিত্র এক পরিণতি ঘটেছে গত দশকে। একটি বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা বইটির পুনর্মুদ্রণে গভীর আগ্রহ দেখায়। পরে তারা গড়িমসি করতে শুরু করে, কারণ ক্ষমতার অলিন্দ থেকে তাদের জানান হয়েছিল ব্যাপারটা মোটেই ভালো চোখে দেখা হবে না, কারণ আমি খ্রিশ্চান এবং সুনিশ্চিত ভাবে মার্কসবাদী। শেষ পর্যন্ত পেঙ্গুইন সেটি আবার ছেপেছে, কিন্তু শিরোনাম বদলে দিয়ে —Brahma, Vishnu, Siva। আর তার ওপরে ছোটো হরফে সাবটাইট্ল—Indian Theogony!
ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিয়তিবাদের উপর কাজটা। সেখানে অন্যান্য কিছুর পাশাপাশি, আমি অন্যান্য ধর্মের কুসংস্কারের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেছি, এবং নগরায়ণ ও শ্রেণি-সম্পর্কের নিরিখে তার একটা প্রেক্ষিত নিরূপণের চেষ্টা করেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাজগুলির মধ্যে এই বইটাই সব থেকে কম পরিচিত।
আমি অল্প বিস্তর ফরাসি ও জার্মান পড়তে পারি, আর সংস্কৃত ছাড়াও পালি এবং প্রকৃত ভাষা শিখেছি।
ক— শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার বিষয়ে কী বলবেন?
স— আমি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে বেশ জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলাম। কেতকী কুশারী আর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ছাড়া বাকিরা খুব গড়পড়তা ছাত্রী ছিল। তবে আমাকে তারা খুব পছন্দ করত। আমি ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষারও একটা কাঠামো তৈরি করেছিলাম। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পড়ার কথা বাবা আমাকে খুব বলতেন। খুব একঘেয়ে লাগত, তাই পড়তে চাইতাম না। কিন্তু ব্রেবোর্ন কলেজে শিক্ষকতা শুরু করার সময় সেই তালিম খুব কাজে এসেছিল।
নাট্য প্রযোজনায় খুব সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলাম। আমরা ইংরেজি, বাংলা আর সংস্কৃত মিলে কম সে কম দশ-বারোটা নাটক প্রযোজনা করেছিলাম। সব চরিত্রেই মেয়েরা অভিনয় করত, আমাদেরই সব করতে হত। মনে আছে একবার ৫৬ জোড়া গোঁফ আঁকতে হয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীও প্রযোজনা করেছিলাম। খুব কঠিন নাটক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেটি মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে বেশ দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নায়িকা নন্দিনীর ভূমিকায় কেউই অভিনয় করতে পারবে না। কিন্তু একটি মেয়েকে দেখে আমার মনে হল, মেয়েটি এই চরিত্রটির জন্য একেবারে উপযুক্ত। তারপর দেখি তার উচ্চারণ ঠিকঠাক নয়। দু-মাস ধরে তাকে তালিম দিয়েছিলাম, সেও খুব উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতা করেছিল। অবশেষে আমরা সে নাটক মঞ্চস্থ করলাম। রাজার স্বর ছিল আমার। দারুণ সফল হয়েছিল।
ক— আপনি তো অনেক জায়গায় গিয়েছেন। এর মধ্যে কোন্ কোন্টা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আপনার?
স— আমি প্রথম যাই কেমব্রিজে, ১৯৬৬ সালে। সেখানে এক বছর ছিলাম। এ ছাড়া প্রাচ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নানা সম্মেলনে গিয়েছি। প্যারিস আর অক্সফোর্ডে থেকেছি। আমার মনে হয় প্রোফেসর ফান ব্যুটিনেন, মাদলিন বেয়ারদ্যো, প্রোফেসর মতিলাল, প্রোফেসর হাজিমে নাকামুরা, প্রোফেসর সের্ব্রিয়াকভ এবং প্রোফেসর নিডহ্যামের মতো সুপণ্ডিতদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আমি খুবই লাভবান হয়েছি।
বিদেশে থাকার সময় একটা জিনিসে খুবই আনন্দ পেতাম—লাইব্রেরিতে পড়াশোনার সুবিধা, এবং তাকে রাখা বই নিজেই দেখে বেছে নেওয়ার সুযোগ আর একটা বই খুঁজতে গিয়ে আরও অনেক বইয়ের সন্ধান পাওয়া। যত পত্র-পত্রিকা পড়তে চাই তত যে পাই না এখানে, এটাও খারাপ লাগে।
ক— দেশের ভবিষ্যৎ কেমন কল্পনা করেন?
স— এ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার একটাই চাওয়া—যে দুষ্ট শক্তি এখন দেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা থেকে দেশটা মুক্ত হোক। প্রকৃত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং আজ যে লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের জোয়ালের ভারে পিষে যাচ্ছেন তাঁদের উন্নতি হোক।
১) গার্ল গাইড হল বয়েজ স্কাউটের মতোই একটি সংগঠন, তবে মেয়েদের জন্য। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত— সম্পাদক
২) বিংশ শতকের গোড়ার দিকের একটি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিশ্চান আন্দোলন, যাতে বাইবেলকে ‘সম্পূর্ণ অভ্রান্ত’ বলে বিশ্বাস করা হয়। — সম্পাদক
৩) এর আগে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ওই একই পদে ছিলেন ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট থেকে ১৯৪৮-এর ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত, কিন্তু তখন পদটির সরকারি নাম ছিল ‘প্রধানমন্ত্রী’। ১৯৫২ সালে সেটি বদলে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। — সম্পাদক
ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন নীলাঞ্জন হাজরা।
সুকুমারী ভট্টাচার্যের স্কেচটি এঁকেছেন হিরণ মিত্র।
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, :|:)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Aditi Dasgupta)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
(লিখছেন... :/, lcm)
(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।