- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ

-
মহামারী, কোয়ারেন্টাইন ও দেশকাল - পর্ব ২
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত লেখকের গ্রাহক হোন
আলোচনা | বিবিধ | ১১ জুলাই ২০২০ | ৫৬৮২ বার পঠিত - পরাধীন যুগে জাতীয় চেতনার উন্মেষও ঘটিয়েছিল মহামারী
"কোথা ওহে দয়াময় কোথা ওহে দয়াময়।
দেখা দেহ দেখা দেহ বিপদ সময়।।
বুঝি তব সৃষ্টি যায় বুঝি তব সৃষ্টি যায়।
তুমি বিনা কেবা রাখে করে সদুপায় ।।
এ কি হল দেশে জ্বর এ কি হল দেশে জ্বর।
জ্বর জ্বর রব সদা শুনি নিরন্তর।।
জ্বরে কেহ নাহি বাকি জ্বরে কেহ নাহি বাকি।
অচেতন পড়ে আছে কেবা মেলে আঁখি।।
জ্বরে দুঃখি লোক যত জ্বরে দুঃখি লোক যত।
মস্তকেতে হাত দিয়া কাঁদে অবিরত।।
কোথা পাবে টাকা কড়ি কোথা পাবে টাকা কড়ি।
একালেতে নাহি খাটে কবিরাজ বড়ি।।
চাহি ঔষধের দাম চাহি ঔষধের দাম।
কোথা পাবে মিকচর তুমি যারে বাম।।
কত অকালেতে মলো কত অকালেতে মলো।
দীনের দুর্গতি শুনে চক্ষে আসে জল।। …
কত খালি হল শিসে কত খালি হল শিসে ।
দিবানিশি আছে লোক ঔষধেতে মিশে।।
তবু নাহি যায় জ্বর তবু নাহি যায় জ্বর।
জীবের আরোগ্য কর দয়ার সাগর।।"
করোনা-সংক্রমণ এবং গৃহবন্দী দশার জেরে মানুষ দিশেহারা। এর থেকে পরিত্রাণ কবে, কিভাবে এবং কতটুকু মিলবে তা অজানা। মারণ ভাইরাসের ভ্যাকসিন কবে বেরোবে এবং সেটিও আদৌ কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেই প্রতিষেধক কেনার সামর্থ্য কত জনের থাকবে এসব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর এখন পর্যন্ত কারোর কাছেই নেই। দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বল পরিকাঠামোর চেহারাটা বিশ্রী ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নজরে এল ১৮৭১ সালে ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি যেটি লিখেছিলেন ঊনবিংশ শতকের অন্যতম আলোকপ্রাপ্তা এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী লক্ষ্মীমণি দেবী।
“বর্ধমান জ্বর” থেকে পরিত্রাণ পেতে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত লক্ষ্মীমণি দেবীর সেই কবিতা
…যে বর্ধমান ছিল এক সময়ের অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর জায়গা, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুরাতন ভৃত্য হরকালী চৌধুরীকে নিয়ে মাঝেমাঝেই যেখানে যেতেন স্বাস্থ্য ফেরাতে সেখানে ১৮৬৯ সালে হানা দিল “জ্বর বিকার”, “মারণ জ্বর”, বা “পালা জ্বর”। যে জ্বরে ফি বছর রাতারাতি গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে লাগল। সম্পন্ন তাঁতি, কাঁসা-পেতল-তামার বাসনের সফল কারিগর, বর্ধিষ্ণু চাষি এবং ধনী জমিদার-অধ্যুষিত বিভিন্ন জনপদ পরিণত হল মৃত্যুপুরীতে। পরাধীন যুগে মহামারীর প্রকোপে মানুষের করুণ, অসহায় অবস্থার এক আন্তরিক, সহানুভূতিশীল বিবরণ পাওয়া যায় ‘বামাবোধিনী’-তে প্রকাশিত এই কবিতাটিতে। সহজ সরল ভাষায় লেখা হলেও লক্ষ্মীমণি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের শক্ত সমর্থ যুবক থেকে শুরু করে শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষ সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হলেও দরিদ্র মানুষের কাছে বিলিতি এলোপ্যাথি ওষুধ বা মিক্সচার কেনার পয়সা নেই অথচ সেই ওষুধ ছাড়া রোগ উপশমেরও কোন সম্ভাবনা নেই। আবার সুযোগ-সন্ধানী দেশি হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ভেজাল ওষুধ শিশির পর শিশি খেয়েও রোগী ও তার পরিবারের বিড়ম্বনা বাড়ে। অবশেষে অগুনতি মানুষের মৃত্যু মিছিলে বেদনার্ত হয়ে লক্ষ্মীমণি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা জানান তিনি যেন মুমূর্ষু মানুষদের কৃপা করেন।
জ্বরের সংক্রমণ কিংবা মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পান নি ইউরোপিয়ানরাও। তাই ব্রিটিশ শাসকদের নথিপত্রে রোগটি পরিচিতি পেল, “বার্ডওয়ান ফিভার” নামে। বর্ধমানের সিভিল সার্জন মেজর জে জি ফ্রেঞ্চ অবশ্য তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, “Calling a fever by the name of the place in which it is raging is certainly objectionable.”
আসলে সরকারি ভাবে রোগটি পরবর্তী কালে ‘বর্ধমান জ্বর’ হিসেবে নথিভুক্ত হলেও এর সংক্রমণের সূচনা কিন্তু অবিভক্ত দেশের অন্তর্গত যশোরের ৩০ কিমি দূরের একটি গ্রাম মহম্মদপুরে ১৮২৪ সালে। এর আট-নয় বছর বাদে ১৮৩২-৩৩ সালে সেই জ্বর হানা দিল নদীয়ার উলা গ্রামে। তারও অনেক বছর বাদে ১৮৬২-৬৩ সালে হুগলির বলাগড়, বর্ধমানের পান্ডুয়া ও কালনার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই জ্বর। আর তারপর তা আরও ভীষণ ভাবে কাবু করল পূর্বস্থলীর গ্রামবাসীদের। জ্বরের প্রকোপে প্রায় গোটা গ্রাম ছারখার হয়ে গেল। তখনই প্রথম পূর্বস্থলীর কিছু বাসিন্দা ব্রিটিশ সরকারকে রোগের কথা জানিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আর্জি জানালেন।
১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের পরের বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ হওয়ার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল রানির হাতে। রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে দাবি করা হত, ব্রিটিশ সুশাসনে ভারত সম্পদশালী হয়েছে। অথচ সেই আমলেই নেমে আসে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া। বস্তুত ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রাণকেন্দ্র এই বাংলা সহ দেশ জুড়ে বিভিন্ন সময় মহামারীর চেহারায় হানা দিয়েছে ম্যালেরিয়া, প্লেগ, গুটি বসন্ত, কলেরা। ব্রিটিশ শাসকদের অগ্রাধিকার ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী এবং ইউরোপিয়ানদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা। সেখানে পরাধীন মানুষদের জনস্বাস্থ্যের হাল ছিল শোচনীয়।
‘বামাবোধিনী’, ‘ভারতী’, ‘মিত্রপ্রকাশ’ প্রভৃতি বাংলা সাময়িকপত্রে ব্রিটিশ জনস্বাস্থ্য নীতির সমালোচনা করে নানা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, কবিতা যেমন প্রকাশিত হতে থাকল তেমনই অন্তঃপুরের মহিলাদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলতেও নিয়মিত প্রাসঙ্গিক লেখা থাকত। ১৮৭২ সালের ‘বামাবোধিনী’তে ছবি সহ পৌষ্টিকতন্ত্র ও স্বরযন্ত্র ব্যাখ্যা করে দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। তখনকার সমাজে আলো-বাতাসহীন, অপরিচ্ছন্ন সূতিকাগৃহ এবং প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন চারুমতি দেবী ১৯১৩ সালে ‘বামাবোধিনী’ তে প্রকাশিত নিবন্ধে। পুরুষ-শাসিত সমাজের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, বাড়ির মহিলাদের প্রতিও যেন প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে এ ছিল তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রকাশ। একই সঙ্গে তিনি মহিলাদের শিক্ষা এবং সমাজ-সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরেও জোর দিয়েছিলেন। আবার ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত আর একটি লেখায় হাঁপানি, সর্দি-কাশি, পেট খারাপ, জ্বর, অর্শ্ব, আমাশা, বমি প্রভৃতি অসুখ বা উপসর্গ এবং সেগুলির আপৎকালীন ঘরোয়া চিকিৎসার ব্যাপারে বাড়ির মহিলাদের সচেতন করা হয়। পুরোপুরি পাশ্চাত্য চিকিৎসার মুখাপেক্ষী না হয়েও যে দেশীয় পদ্ধতিতে দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সমস্যার কিছু সুরাহা করা যায় সেটিই ছিল লেখাটির উদ্দেশ্য। সে যুগের নারীর কাছে বন্ধ্যাত্ব ছিল চরম অভিশাপ। সেই বছরেই একটি লেখায় ক্ষান্তমণি দেবী বন্ধ্যাত্ব নিবারণে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের একটি ওষুধ সুপারিশ করেন। হয়ত এ ছিল সেই চিকিৎসকের নাম প্রচারের অঙ্গ। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, পত্র-পত্রিকায় এ ধরণের লেখালিখির মাধ্যমে নারীরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিলেন।
১৮৭২ সালে ঢাকা থেকে প্রচারিত ‘মিত্রপ্রকাশ’ পত্রিকায় বসন্তকুমারী দেবীর “কবিতা মঞ্জরী” গ্রন্থের ওপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। জমিদার-পত্নী হলেও বসন্তকুমারী কবি হিসেবে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন। নিজের দীর্ঘ অসুস্থতার সময় তিনি বেশ কিছু মরমী কবিতা লিখেছিলেন। সেই সব কবিতাই পরে সংকলিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় যে চিকিৎসার পরিকাঠামো ছিল নেহাতই অপ্রতুল, জলের মতো টাকা খরচ করা সত্ত্বেও সম্পন্ন মানুষের কাছেও যে সুচিকিৎসা ছিল দুর্লভ তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কবিতায়। লক্ষ্মীমণি দেবীর মতোই তিনিও পরিস্থিতির প্রতি হতাশ হয়ে নিজের আরোগ্য কামনায় ঈশ্বরের শরণাগত।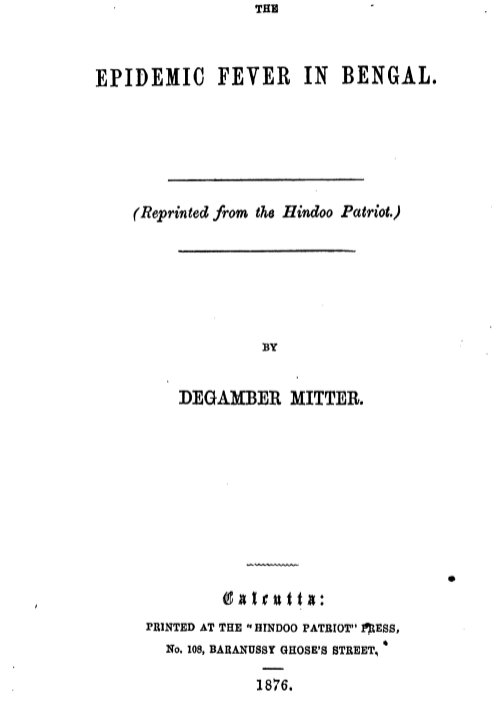
ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে ”হিন্দু প্যাট্রিয়ট” পত্রিকায় প্রকাশিত রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রতিবেদনের সঙ্কলন, “দি এপিডেমিক ফিভার ইন বেঙ্গল”
…বিশ শতকের গোড়ায় মুসলিম নারীদের একটি অংশও স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তার পথিকৃৎ ছিলেন কুমিল্লার বিদ্যানুরাগী, ধনী জমিদার ফৈজুন্নেসা চৌধুরী। বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় সমান দক্ষ ফৈজুন্নেসা ছিলেন রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, বাইবেল সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সনিষ্ঠ পাঠিকা। নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলা “ফৈজুন গ্রন্থাগারে” তাঁর ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর সুদূর-প্রসারী নারীবাদী চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় ‘রূপ জালাল’ শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে। সমাজে মুসলিম নারীর দুরবস্থার কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। মুসলিম নারীর শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি কেউ কখনও নজরই দেয় নি। এই সব সমস্যার কথা উপলব্ধি করেই তিনি অবিভক্ত বঙ্গের কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “জেনানা হাসপাতাল”। স্বর্ণকুমারী দেবীর গড়ে তোলা “সখী সমিতি”র অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। বেগম ফৈজুন্নেসাই একমাত্র ভারতীয় নারী যাঁকে ১৮৮৯ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়া বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজের লেখার মাধ্যমে মুসলিম নারীর মুক্তির বার্তা প্রচার করেন। শরীর সুস্থ রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম নারীর উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ ছিল, পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ নেই তবে এলোপ্যাথি ওষুধের পাশাপাশি দেশজ ঐতিহ্যের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
আবার একবার ফিরি বর্ধমান জ্বরের প্রসঙ্গে কারণ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় চিকিৎসার পরিকাঠামো, পরাধীন মানুষের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ওই মহামারীর সূত্রেই। মারণ জ্বর ততদিনে একেবারে মহামারী হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বর্ধমান সহ অন্যত্র। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে বুঝতে পেরে জেলা শাসক ডব্লিউ ই ওয়ার্ড জৌগ্রাম ও মেমারি সহ চারটি এলাকায় ডিসপেনসারি খোলার নির্দেশ দিলেন। পরের বছর ১৫ মে তিনি রিপোর্ট পাঠালেন, “এমন কোন দেশি লোক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না যে না এই জ্বরে পড়েছে। বর্ধমানে এসে না থাকলে কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, পরিস্থিতি কী ভয়াবহ এবং সাধারণ মানুষ কতটা অসহায়। আমার বাংলোয় কাজ করার মতো আর কোন ভৃত্য নেই … এই অবস্থায় কলকাতা থেকে নতুন কোন ভৃত্য আনানোর চেষ্টা করাটাও নিষ্ঠুরতা। বাধ্য হয়ে আমি আপাতত আমার সদর দপ্তর রানিগঞ্জে স্থানান্তরিত করছি। ধনী-দরিদ্র কেউ বাকি নেই, এমনকি ইউরোপিয়ানরাও জ্বরে আক্রান্ত।”
১৮৭২ সালের ২৮ জুন বর্ধমানের পরবর্তী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি টি মেটকাফ যে রিপোর্ট পেশ করলেন তাতে ভয়াবহতার চিত্রটি আরও পরিষ্কার — “সরকারি অফিসগুলিতে কেরানি, আমলা, আর্দালি, চাপরাশি থেকে শুরু করে পদস্থ আধিকারিকরাও জ্বরে শয্যাশায়ী। কর্মীর অভাবে সব দপ্তর খাঁ-খাঁ। একজন-দুজনকে যদিও বা দেখা যায় তাদের চেহারা শীর্ণ, রক্তশূন্য। জেল হাসপাতালে কয়েদি-রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। জ্বরেই মৃত্যু হল ইউরোপীয় মহিলা গিসবোর্নের। তাঁর স্বামীর অবস্থাও মরণাপন্ন। জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে সিভিল সার্জন ছুটির দরখাস্ত করে বিদায় নিলেন। বর্ধমান ছেড়ে চলে গেলেন ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির কর্মীরাও। অফিসে কর্মী নেই, গৃহ ভৃত্য-শূন্য, পুরসভার ঝাড়ুদার ও সাফাই কর্মী অমিল। অবস্থা এমন, যে পুলিস কনস্টেবলের পাহারায় আসামীকে পাঠানো হচ্ছে, সেই আসামীই হঠাৎ জ্বরের ঘোরে মূর্ছা যাওয়া সিপাইয়ের পরিচর্যায় ব্যস্ত।” বীরভূমের সিভিল মেডিকেল অফিসার ডাঃ আর এ বেকার রিপোর্ট দিলেন, জ্বরের সংক্রমণে গ্রাম-শুদ্ধ লোক এমন কাবু যে ধান কাটবার মজুর পর্যন্ত নেই।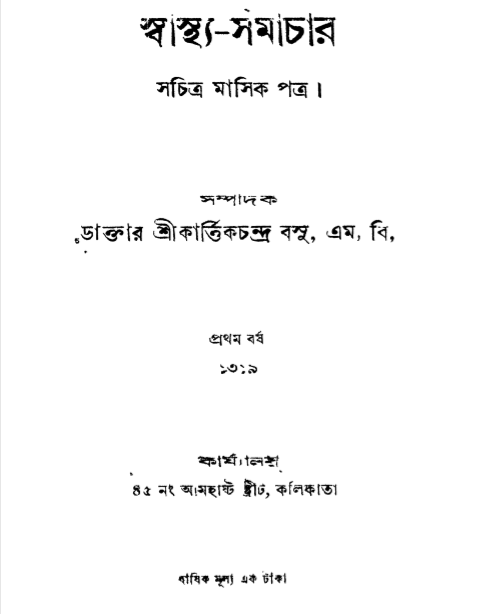
ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বাংলা মাসিকপত্র “স্বাস্থ্য সমাচার”
…ব্রিটিশ মেডিক্যাল অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়াররা জ্বরের সংক্রমণ ছড়ানোর কারণ হিসেবে মূলত ধান খেতে জমে থাকা জল এবংপাড়া-গাঁয়ের নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকেই দায়ী করলেন। নিজেদের প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়াতে মহামারীর জন্যে পরাধীন দেশকেই “land of dirt, disease, and sudden death” বলে দাগিয়ে দেওয়াটা ছিল সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে “হিন্দু প্যাট্রিয়ট” কাগজে ১৮৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১৮৭৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অবধি মোট ১৪ টি নিবন্ধ লিখলেন ১৮৬৪ সালের এপিডেমিক কমিশনের ভারতীয় সদস্য রাজা দিগম্বর মিত্র। ১৮৫১ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতার কাসাইটোলায় (বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট) গঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। নীল চাষের সমস্যায় রায়তদের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশদের কাছে সওয়াল করা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সতীদাহ, শ্মশানঘাটের উন্নয়ন, খাজনার হারের ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রভৃতি সামাজিক বিষয় নিয়ে আইনগত ভাবে ব্রিটিশদের মোকাবিলা করা ছিল সংগঠনের অন্যতম কর্তব্য। কাজেই দিগম্বর মিত্রের মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যখন ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় সোচ্চার হলেন তখন তাঁর বক্তব্যকে ব্রিটিশরা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। হুগলিতে জমিদারি চালানোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়ায় তিনি বুঝেছিলেন, নতুন পাকা রাস্তা এবং রেলপথ নির্মাণ ও যত্রতত্র নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে এলাকার স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর সেজন্যেই গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে জমা জলের সমস্যা, আগাছার প্রাচুর্য আর সব মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মশার বংশ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ। মূলত এই তীব্র সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৩ সালে এম্ব্যাঙ্কমেন্ট আইন বলবৎ করে নিকাশির যে কোন অবরোধ ভেঙে ফেলতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রথম সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হল। এছাড়া ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও লেফটেন্যান্ট প্রক্টরের নেতৃত্বে গঠিত হল ড্রেনেজ কমিটি। কমিটির রিপোর্টেও কিন্তু দিগম্বর মিত্রের বক্তব্যের সমর্থন মিলল। অবশেষে ১৯০৯ সালে পেশ হল ড্রেনেজ বিল। এলাকার জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পরিবেশ তদারকির জন্যে স্যানিটারি কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করেছিলেন দিগম্বর মিত্র।
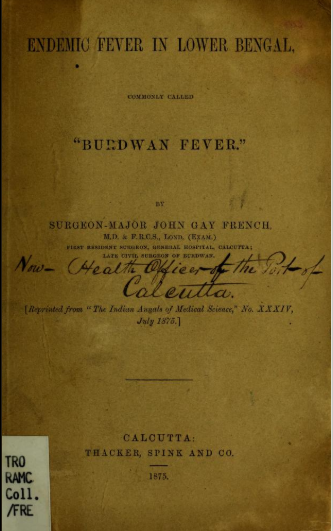
১৮৭৫ সালে সার্জন-মেজর জন গে ফ্রেঞ্চ-এর প্রতিবেদন "এপিডেমিক ফিভার ইন লোয়ার বেঙ্গল"
…মহামারীর খবর কানে যেতেই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ধমানে পৌঁছে যান। অন্য সময় অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। এবার তিনি একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে গড়ে তুললেন দরিদ্র, অসহায় মানুষদের জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয়। দায়িত্ব দিলেন প্যারীচাঁদের ভাইপো ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে। সর্বত্র ঘুরে দেখলেন শোচনীয় অবস্থা। বিনা চিকিৎসায় পথে-ঘাটে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। ব্রিটিশ সরকারকে লিখলেন তো বটেই, তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে নিজে কলকাতায় গিয়ে দেখা করলেন লেফটেন্যান্ট গভৰ্ণর উইলিয়াম গ্রে-র সঙ্গে। দাবি জানালেন, যোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী ডিসপেনসারি চালু করতে হবে। তাঁর চাপেই সরে যেতে হল জেলার অকর্মণ্য সিভিল সার্জনকে। এলেন সহানুভূতিশীল অন্য এক চিকিৎসক। বিদ্যাসাগর নিজে বিলোতে লাগলেন ওষুধ, পথ্য এবং জামা-কাপড়। খরচ হয়ে গেল ২০০০ টাকা। এর পাশাপাশি ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ সরকার ৭৬ টি নতুন ডিসপেনসারি চালু করল। সব মিলিয়ে তার সংখ্যা দাঁড়াল ১০২। মেডিকেল অফিসারের দেওয়া টিকিটের বিনিময়ে সেখান থেকে দেওয়া হত কুইনাইন যা ছিল তখন মহার্ঘ। তার সঙ্গে কিছু জায়গায় চালু হয়েছিল ৩৩ টি ত্রাণ কেন্দ্র। তার দায়িত্বে থাকতেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দুঃস্থ রোগীরা সেখান থেকে পথ্য অনুযায়ী দৈনিক রেশন হিসেবে পেতেন চাল, ডাল, তেল, মশলা, লবন ও কাঁচা আনাজ অথবা দুধ, সাবু বা সুজি ও চিনি। ব্রিটিশ প্রশাসনের সে সময়কার নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, ডিসপেনসারিগুলিতে মোট ১২ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি রোগী দেখা হয়েছিল। প্রতি মাসে শুধু কুইনাইন লাগত ১০০ পাউন্ড বছরে যার খরচ ছিল ৪৩৫২৪ টাকা। বর্ধমান মেডিকেল স্টোর থেকে ওষুধ খাতে বাৎসরিক খরচ হয়েছিল ৬০ হাজার ১৭৩ টাকা। এর সঙ্গে ছিল স্টোর কিপার ও কম্পাউন্ডারের মাসিক বেতন ১৪৬ টাকা, বাড়ি ভাড়া ২০ টাকা আর আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে মাসে ৭০ টাকা। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ওই বছর রাম কেনার খরচ দেখানো হয়েছে ২৭৬৬ টাকা। বলা হয়েছে, ওই ডিসপেনসারিগুলির জন্যে রাম পাঠানো হত ‘stimulant’ হিসেবে।

পুরনো কলকাতায় ম্যালেরিয়া সংক্রমণ ঠেকাতে বাড়ির ছাদে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক সাফাই করা হচ্ছে
…ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে কুইনাইন আবিষ্কার হয়েছিল ১৮২০ সালে। এবার বর্ধমান মহামারীর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলারা জ্বরগ্রস্ত রোগীদের ওপর ‘কুইনাইন’ বলে দেশি ডাক্তারদের চালানো ওষুধের কার্যকারিতাও পরখ করতে লাগলেন। ব্রিটিশ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে বিলি করা খাঁটি কুইনাইন বড়ি বা মিক্সচারকে ঘিরে অচিরেই গড়ে উঠেছিল কালোবাজার। সেই ভেজাল মিক্সচার বেচে এক শ্রেণীর অসাধু হাতুড়ে চিকিৎসক প্রচুর পয়সা কামাতে শুরু করে। কালোবাজারি ঠেকাতে ডাকঘর, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমেও কুইনাইন বিলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ওই হাতুড়ে চিকিৎসকদের পাশাপাশি আবার দেখা যায় কিছু দেশি ডাক্তারবাবু ক্রমে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৮৭০ সালে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল করাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিবিধ মহৌষধে’র। রোগীদের অবস্থার কথা জেনে নিয়ে তিনি ডাকযোগেই ওষুধ পাঠাতেন। এমনই ভাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিনাজপুর, বারাণসী ও লাহোরেও। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্করের “আরোগ্য নিকেতন” — “দেশে তখন ম্যালেরিয়ার মহামারণ চলছে — বিলাতি ডাক্তারির হাঁকে ডাকে, সরকারি অনুগ্রহে তার পসারে কবিরাজদের ঘরগুলি বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। দেশে বৈদ্যের অভাব। সেই সময়ে এই সব আধা-ডাক্তারেরা অনেক কাজে এসেছিল। শতমারি ভবেদ বৈদ্য সহস্র মারি চিকিৎসক।” জ্বরের চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। “সরল জ্বর চিকিৎসা” সহ তাঁর বেশ কয়েকটি বইও ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল। তবু জ্বর হলে কুইনাইন চিকিৎসাই হয়ে উঠল দস্তুর। সাধারণ মানুষের মাসকাবারি বাজার খরচের ফর্দে কুইনাইন স্থায়ী ভাবে জায়গা করে নিল। প্রতিদিন সকালে নিয়মিত কসরতের পর সেনাবাহিনীর জলখাবারে আবশ্যিক ছিল কুইনানাইনের প্রতিষেধক ডোজ। ব্রিটিশ প্রশাসকেরা কিন্তু রোগ সম্পর্কে দেশীয় সমাজের মতামতের ওপর নিয়মিত নজর রাখতেন। সেই কারণেই ১৮৭২ সালের আগস্ট মাসে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রূক “বর্ধমান জ্বরের প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায়” বিষয়ে দেশীয় নাগরিকদের মধ্যে এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন যার পুরস্কার মূল্য ঘোষিত হয়েছিল সে আমলে এক হাজার টাকা। ভুললে চলবে না, দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাধ্যমে ব্রিটিশরা দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ওই কেন্দ্রগুলিতে কলেরা ও গুটি বসন্তের টিকাও দেওয়া হত। ১৮৬৭ সালে ৬১ টি ডিসপেনসারি দিয়ে শুরু হলেও ১৯০০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে তারই মধ্যে ১৮৭০ সাল থেকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ওই সব ডিসপেনসারির আর্থিক দায়ভার থেকে নিজেদের ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। পরিবর্তে সেগুলি পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির হাতে। আগে মানব-কল্যাণে জমিদাররা বড় বড় পুকুর ও দিঘি কাটাতেন। ক্রমে সে সব বন্ধ হয়ে গেল। সরকারও এ ব্যাপারে উদাসীন। কাজেই গ্রামের মানুষকে যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনে দূষিত জলাশয়ই ব্যবহার করতে হত। আর তা থেকেই ছড়িয়ে পড়ত নানান রোগ। জল সরবরাহ ও নিকাশির ব্যবস্থা করার ভারও এসে পড়ল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির ওপরেই। ফলে খরচের সংস্থান করতে বছর বছর নাগরিকদের ওপর খাজনার হার বাড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। আর সেই নিয়ে গ্রামবাসীরা হয়ে উঠল ক্ষুব্ধ। তাছাড়া বিশেষত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর থেকে সমাজের গোঁড়ামি ও বিরোধিতার ভয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন স্বাস্থ্য ও নিকাশি, ব্যক্তিগত সমস্যা বা পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে সরাসরি নাক গলাতে অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এরপরে ১৮৯৭ সালের মহামারী আইন রোগ নিয়ন্ত্রণে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয়। স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না দেখার জন্যে ইন্সপেক্টরদের বাড়ির অন্দরমহলেও প্রবেশের ঢালাও অধিকার ছিল। কঠোর কোয়ারেন্টাইন নীতি ও আবশ্যিক পরিদর্শনের বাড়াবাড়ির বিস্তর নজিরকে ঘিরে দেশীয় নাগরিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় — অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বেঁধে যায়।

কলকাতার জিপিওতে ফিলাটেলিক মিউজিয়ামে কুইনাইনের পোস্টার
…একের পর এক মহামারীর প্রকোপে প্রাণহানি রুখতে এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে রোগের সংক্রমণ ঠেকানোর উপায় বাতলাতে ব্রিটিশ সংসদ ১৮৬০ সালে রয়্যাল কমিশনকে ভারতে পাঠিয়েছিল। তার সুপারিশ অনুযায়ী অবিভক্ত বঙ্গ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে জনস্বাস্থ্য বিধি তদারকির জন্যে তিন জন স্যানিটারি কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ১৮৮০ সালে তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এক জন করে ডেপুটি স্যানিটারি কমিশনারও নিযুক্ত হন। বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিন তদন্তের পর স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়, সরকারি খরচে নিয়মিত কার্পণ্যের দরুণই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার অভাব রয়েছে। সীমিত ক্ষমতায় স্যানিটারি কমিশন কিছু কিছু উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা যে করেছে তার সাক্ষ্য রয়েছে তারাশঙ্করের লেখায় — “একদল এল স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। একদল এল কী নাম যেন তাদের? কোদালির পর কী? কোদালি ব্রিগেড। শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে তারা জল বের করলে। তাই তো? কথাটা তো কারুর মনে হয় নি! স্যানিটারি ইন্সপেক্টরেরা পুকুরে পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে দিয়ে জলকে শোধন করলে। এন্টি-কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিলে। কলেরার টিকে।” তা সত্ত্বেও বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হিসেবে জানা যায়, ১৮৬২ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে জেলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরই মৃত্যু হয়েছিল ম্যালেরিয়ায়। ১৮৭৬ সালে বাংলা সাময়িকপত্র ‘সাধারণী’ কয়েকটি গ্রামের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছিল, সেখানে পরপর দু-তিন বছরে পরিবারগুলোতে নতুন কারও জন্ম হয় নি। ব্রিটিশ স্বাস্থ্যনীতির সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন স্যার রোনাল্ড রসের মতো চিকিৎসকও। তিনি বলেছিলেন, শুধু কুইনাইন দিলেই হবে না, উপযুক্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।
আলোচনা শেষ করার আগে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বসু ও বিশ শতকের শুরুতে তাঁর প্রবর্তিত শুধু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বাংলা সংবাদপত্র “স্বাস্থ্য সমাচার”-এর কথা। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বেঙ্গল কেমিকেলে। সেখানে তিনি ওষুধ তৈরি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলা সংবাদপত্রটিতে প্রাক-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রতিবেদনে ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য নীতির নিয়মিত সমালোচনা করা হয়েছে। ১৯২৫ সালে “গ্রামীণ পুণর্গঠন” শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্ম-জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে হলে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে আত্ম-সচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৬ সালে সে সময়ের জনপ্রিয় মহিলা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে ব্রিটিশদের দায়ী করে জোরাল ভাষায় নিবন্ধ লেখেন। ১৯৩০ সালের একটি সম্পাদকীয়তে নিম্নবঙ্গে প্রায় অর্ধ-শতক ধরে চলা মহামারী জ্বরের প্রাদুর্ভাবের জন্যে রাজা দিগম্বর মিত্রের তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়ে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক গাফিলতির তীব্র নিন্দা করা হয়। পরের বছরই পৃথক এক সম্পাদকীয়তে ডাক্তার রমেশ চন্দ্র রায় কলেরা নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশদের ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরেন। ১৯২৩ সালে “দ্য ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকায় প্রমথ নাথ বসু নিত্য নতুন অসুখের বাড়বাড়ন্তের জন্যে সরাসরি পাশ্চাত্য সভ্যতারই সমালোচনা করেন। তার আগে ১৯১২ সালের ‘প্রবাসী”তেও ব্রিটিশদের প্রশাসনিক উদাসীনতা ও অদক্ষতার নিন্দা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিটি পরাধীন জাতির মধ্যে ক্রমেই জোরাল হয়ে ওঠে।
আনন্দবাজার পত্রিকায় ম্যালেরিয়ার ওষুধের বিজ্ঞাপন
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
দ | ১১ জুলাই ২০২০ ১৯:৩৫95122
- এই ধারাবাহিকটাও ভারি ইন্টারেস্টিং
-
শিবাংশু | ১১ জুলাই ২০২০ ২২:১৩95130
- মূল্যবান লেখা...
-
 Sekhar Sengupta | ১২ জুলাই ২০২০ ১১:৫১95152
Sekhar Sengupta | ১২ জুলাই ২০২০ ১১:৫১95152 খুব ভাল লাগছে পড়তে। তৃতীয় পর্বের জন্য মুখিয়ে আছি।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












