- বুলবুলভাজা ধারাবাহিক উপন্যাস শনিবারবেলা

-
তখন ছোঁয়া অষ্টাদশীর - পর্ব তিন
শ্রাবণী রায়
ধারাবাহিক | উপন্যাস | ২৯ মার্চ ২০২৫ | ৯৭৭ বার পঠিত 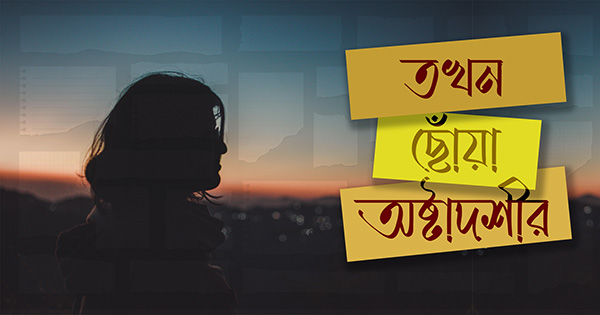
(৩)
সেই পুজো নেই পুজো............
হিমালয়ঘেরা এই শহরটাতে পুজো আসার সাথে সাথে চারদিক থেকে হিমেল হাওয়ার দল উঁকিঝুঁকি মারে।সারাদিন নানা শোরগোলে আর লোকের ভিড়ে, পুজোমন্ডপের চারধার বেশ সরগরম থাকলেও সন্ধ্যে হতে না হতেই ঠিক শীত না, তবে হিম ভাব। আরতি শেষে ফাংশন শুরু হলে প্রথম দিকটায় ভিড়টা চারিদিকে মাঠের ঘাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসে শামিয়ানার নীচে। একটু রাতে বাড়ি ফেরার সময় হাল্কা একটা পাতা পোড়ার গন্ধ মেশে হাস্নুহানার মাতাল গন্ধে। টুপটাপ হিম ঝরে গন্ধরাজের পাতায়, আর ঝিমলির মন কেমন করে, কারণ ভালো বোঝা যায়না, তবু করে। অন্তত ওই সরস্বতী মন্দির থেকে বাড়ির আধো অন্ধকার পথ চলার ক্ষণে তো করেই।
পুজোয় তার তেমন কিছু করার ছিলনা। এমনিতেও সে কোনো বছরই পুজোর ফাংশনের দিকে ঘেঁসেনা খুব একটা, ওই অনন্ত রিহারসাল পর্ব তার মোটেই পছন্দ নয়। আসলে বাঁধাধরা সময়ে কোন কিছু করতেই ঝিমলির ভালো লাগেনা। সেই কারনে এতকাল কোথাও ঠিকমত টিউশনই পড়ে উঠতে পারল না। এবার বারো ক্লাস বলে জোর করে শরাফ স্যরের কাছে অংক করতে পাঠানো হচ্ছে, খুব নিমরাজী হয়েও যাচ্ছে, এন্ট্রান্সের গরজ বালাই!
প্রতি পুজোতেই তাকে আন্টিরা ধরে, নাচ বা গান কিছু একটাতে ভাগ নেওয়ার জন্যে, কিন্তু প্রতিবারেই সে ঠিক কায়দা করে কেটে বেরিয়ে আসে। এ ব্যাপারে অবশ্য বাড়ির লোকেরাও খুব সাহায্য করে। তাকে রাজী না করতে পেরে আন্টিদের কেউ বাড়িতে বলতে এলে, তারাই বারণ করে দেয়। অবশ্য ব্যাপারটাতে স্কুলের কৃতিত্বও কম নয়। ক্লাস সেভেন থেকে তাদের সেকেন্ড টার্মের পরীক্ষা পুজোর আগে আগে হয়। বাড়ির লোকের তাই পরিস্কার বক্তব্য, পরীক্ষার সময় রিহার্সাল চললে যেটুকু পড়ে সেটুকুও হবেনা।
তাহলে অন্য ছেলেমেয়েরা কী করে সব সামলায়? পুজো ও পরীক্ষা তাদেরও কি নেই? থাকবে না কেন? তারা সব লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে, এ বাড়ির এনার মত অমনোযোগী আর ফাঁকিবাজ তো দুটি নেই এ শহরে!
আন্টিরা এর পরে আর তেমন জোরাজুরি করতে পারেনা। তবে এও সত্যি যে ঝিমলি যদি তেমন গুণের গুণবতীটি হত তাহলে কি আর তারা এত সহজে ছেড়ে দিত! নেহাত প্রবাসে বাঙালীর সংখ্যা কম, তার ওপর আবার তাদের বয়সী একেবারেই কমে গেছে আজকাল, নাহলে আন্টিদের বয়ে গেছে ঝিমলিকে সাধাসাধি করতে।
ছোটবেলায় সে তবু কিছুটা উৎসাহ নিয়ে রিহার্সালে যেত। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা যেত, পড়ায় ফাঁকি দেওয়া যেত, তার বদলে একটু গ্রুপ ড্যান্স বা কোরাসে গলা মেলালেই হয়ে যেত। বড় হয়ে যবে থেকে স্বাবলম্বী হয়েছে, সাইকেল তুলে একা একা বেরনোর ঢালাও পারমিশন, আড্ডা মারার অনেক দরজা খুলে গেছে, এখন পুজোর বাঙালীদের ফাংশনের মহড়ার আড্ডা আর তাকে টানেনা।
তবু এবারে অবস্থা বিপাকে তাকে ঢুকতেই হল। সপ্তমীর দিন প্রতিবারেই বড়দের বাংলা নাটক থাকে, এবং পরিচালনা ও অভিনয় দুইয়েই বাসুআন্টি নিজে থাকে বরাবর, নাটক আন্টির প্রাণ।
অষ্টমীর দিন ছোটদের নাটক নাচ ইত্যাদি, সব বাংলায়। নবমীর দিন পুরোপুরি হিন্দিভাষীদের জন্য, যাকে বলে কালচারাল প্রোগ্রাম, নবরাত্রি স্পেশাল। এই একটি দিনের জন্য তেমন কোনো খাটুনি নেই বাঙালী কর্মকর্তাদের। আশেপাশের স্কুলগুলিতে যেসব বাঙালী শিক্ষিকারা আছেন তারাই যে যার স্কুলের প্রতিযোগিতার সেবছরের সেরা প্রোগ্রামগুলি, নৃত্যনাট্য বা নাটক যে কোনো কিছুর রিপিট শোয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। এছাড়া ক্যাম্পাসঘেরা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও কিছু না কিছু করে, নবমীর আইটেমের অভাব সচরাচর হয়না।
বাসুআন্টির এবারের নাটক ছিল অন্যরকম, একেবারে নতুন, অভিনব পরিকল্পনা, সব নারী চরিত্র। বাংলা উপন্যাসের সেরা নারী চরিত্ররা এক এক করে এসে একক অভিনয় করবে, নাটকের নাম তাই “একই অঙ্গে এত রূপ”!
রিহার্সাল ভালোই চলছিল কিন্তু মাঝখানে বাধল গোল। মাম্পিদি লখনউতে কিসে একটা চান্স পেয়ে গেল, এক সপ্তাহের মধ্যে যেতে হবে এবং পুজোতে আসতে পারবেনা। মাম্পিদি ডাক্তারকাকুর মেয়ে, শহরের বাঙ্গালী ডাক্তার। পড়াশোনায় খুবই সাধারণ ছিল, ঝিমলি ওর দুঃখটা বোঝে, ডাক্তারের মেয়ে সবাই ধরেই নিয়েছিল ডাক্তার হওয়া অবধারিত। সে জায়গায় মাম্পিদি কোনরকমে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, কোথাও মাস্টার্সে চান্স পাচ্ছিলনা, মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াত।
বাসুআন্টি অনেক ধরেকয়ে মাম্পিদিকে রাজী করিয়েছিল রোলটা করতে, কারণ একমাত্র ওই চরিত্রটারই বয়স কম, আন্টিরা করলে ভালো দেখাবেনা। অন্যান্য চরিত্রের জন্য এক একজন সব আন্টি ছিল আর বাসুআন্টি নিজে দুটো চরিত্রে। আড়ালে অন্যরা বাসুআন্টিকে নিয়ে নানা মজা করে। সেদিন মন্দিরের পেছনের ঘরে রিহার্সালে এসে সবাই হাসাহাসি করছিল, যে পারলে আন্টি নাকি সব চরিত্রই নিজে করে, সবার ভুল ধরছে, শুধু নিজে নাকি দারুন করছে, আপন প্রশংসায় পঞ্চমুখ!
রীনা কাকীমা আবার মুখচোখ ঘুরিয়ে সেদিন আন্টিকেই বলে বসল,
"হ্যাঁ দিদি পটেশ্বরী বৌঠান তো খুব সুন্দরী, আপনাকে বৌঠানের চরিত্রে একটু কেমন লাগছে না?"
আন্টি নির্ভেজাল শিল্পীমানুষ, এসব খুচরো ঠেস দেওয়া কথা অত খেয়াল করেনা, বলে,
“দ্যাখোনা, সুন্দরী মেয়েগুলো যারা, তারা দু লাইন সংলাপই ঠিক মুখস্থ করতে পারেনা, ভাব আনা তো দুরের কথা। এদের পটেশ্বরী বৌঠান করতে দিই কিভাবে বলো! আমাকেই মেকআপ আর অভিনয়ে ম্যানেজ করতে হবে, কী আর করব!”
জবাব শুনে রীনা কাকিমার মুখের ভাব দেখে ঝিমলির দারুন মজা লেগেছিল, এই না হলে জয়ের মা!
আন্টিকে সে ভালোবাসে, মানে বাসতেই হয়, তাই তো নিয়ম বলে! মাম্পিদি চলে যাওয়ার পরে আন্টি এসে একেবারে ধরে পড়ল, ওই পার্টটা ঝিমলিকে করতে হবে। ঝিমলি তো কিছুতেই রাজী নয়। এদিকে এবারে আন্টির কাতর অনুরোধে বাড়ির লোকেরাও গলে জল। তাছাড়া এগারো ক্লাসে টার্ম পরীক্ষার সময় পালটে গেছে, সর্বোপরি টেনের বোর্ড খারাপ নামেনি, তাই বাড়িতে দুরছাই ভাব একটু কমতির দিকে।
তবু সে একবার শেষ চেষ্টা করে, এত বাংলা সংলাপ ও একসাথে বলতে পারবেনা, স্টেজে ভুলে যাবে। কিন্তু আন্টি সে অজুহাত মাছি তাড়ানোর মত করে উড়িয়ে দিল,
“আরে মাম্পি মুখস্থ করে ফেলল, আর তোর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে পারবিনা এই কটা লাইন মুখস্থ করতে।“
আর না করা গেল না, আন্টি প্রায় কাঁদোকাঁদো। সিকোয়েন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা বাদ দিলে, আর আমরা সব যা মুটকির দল, একেবারে মানাবেনা ফিংফিঙ্গে এই মেয়ের রোলে, খুব বোকা বোকা লাগবে।
শেষমেশ চিরতার জল গিলতেই হল। একটাই রক্ষে, তার ক্লাসের কেউ এদিন ফাংশনে থাকবেনা, তার বন্ধুদের মধ্যে একটাও বাঙালী নেই। বাঙালী দলে স্কুলের যারা আছে তারা সবাই অনেক জুনিয়র, বড়দের নাটক দেখতে বসার চান্স কম, দেখলেও তেমন কিছু বুঝবেনা। কিছু গণ্ডগোল হলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
আন্টি বলেছে যদি সংলাপ ভুলে যায় মাঝে, ঝুড়িটা কোমরে তুলে নিয়ে একটু নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে। বাসু আঙ্কল আর লাহিড়ী আন্টি মিলে প্রতিটা অংকের শুরুতে চরিত্রটা নিয়ে বলবে ব্যাক স্টেজ থেকে, আর ভূমিকার শেষে আলো কম হয়ে চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করবে। তেমন দরকার হলে, কথা ভুলে যাচ্ছে মনে হলে, সে যেন ইশারা করে, তাহলে আলো কমিয়ে, ওরাই আড়াল থেকে বলে দেবে সংলাপের কলাইন!
অবশ্য পরে শুনেছিল এরকম কোনো পরিকল্পনা আদৌ ছিলনা, আন্টি তাকে সাহস যোগাতে এমনিই এসব বলে রেখেছিল।
যাইহোক, নাটক কিন্তু দারুন হল, সবাই খুব প্রশংসা করছে। আন্টির অভিনয় তো যাকে বলে দুর্দান্ত। ঝিমলি এসব বাংলা উপন্যাস একটাও পড়েনি, তবু ব্যাকস্টেজ থেকে অবাক হয়ে দেখেছিল আন্টিকে। মাতাল পটেশ্বরীর দুঃখ কী বিষয়ে কিছু না জেনেবুঝেই বুকের ভেতরটা কেমন হা হা করে উঠছিল। আবার সেই মহিলাই যখন ডাইনী হয়ে ফিরে এল, সাদা কাপড়, খোলা চুল আর জ্বলন্ত চোখে, সেও কেমন দুঃখেরই, অন্যরকম কষ্ট সারা শরীর চুঁইয়ে চুঁইয়ে চারপাশে দুঃখডোবা যেন।
সপ্তমীর রাত থেকে পুজোটা কেমন যেন মনকেমনীয়া হয়ে গেল। অষ্টমীর অঞ্জলি শেষে খাবার স্টলগুলোতে চেনা জটলার দিকে তাকিয়ে,একটা চেনা মুখ না দেখে, বুক হু হু করতে লাগল।
নবমীর সকালে দাদা সিভিল লাইন্সের বইয়ের দোকান থেকে আনন্দমেলা নিয়ে এসে হাতে দিতে, মায়ের ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে গিলতে না বসে, বইয়ের তাকটায় তুলে রাখল। সবাই লক্ষ্য করে একটু অবাক বা অপ্রস্তুত। প্রতিবারে এই বই পড়া নিয়ে প্রচুর বকুনি খেতে হয়, না শেষ করা অবধি খাওয়া নেই ঘুম নেই।
সকালে তো এ কদিন মন্দিরে ভোগ খাওয়া, রাতে খাবার টেবিলে শুনতে হল, “হ্যাঁরে সত্যি বড় হয়ে গেলি নাকি, আনন্দমেলা পড়ছিস না?“
বড় হওয়া নিয়ে এত কথা শুনতে হয়, যে ঝিমলি আজকাল কানই করেনা। তার সব কাজেই বাড়ির সবার মনে হয় বয়সোচিত হল না। ঝিমলির সবচেয়ে প্রিয় জেমস আর পপিন্স, এখনো। এটা নিয়েও বয়সের খোঁটা দেয় সবাই, কমিক্স আর ন্যান্সি ড্রু নিয়েও। এমনকি বারো ক্লাসে ফেল করার পরে তার
বিয়ের আয়োজনের আলোচনাতেও মনে করানো হয় তত্বে জেমস আর পপিন্সের ট্রে রাখার কথা।
এবার দ্যাখো সবাই, কেমন লাগে বড় হলে!
বাড়ির সবার হতভম্ব মুখচোখ দেখে দুঃখেও হাসি এসে গেল!
পুজো শেষে শুরু হয় বাড়ি বাড়ি বিজয়া সম্মিলনীর ঘটা। খাওয়া দাওয়া ভালো হয় বলে এগুলো ঝিমলির মন্দ লাগেনা। ঘুগনি, চপ, লুচি মাংস, বাড়িতে বানানো বাঙালী মিষ্টি, আন্টিরা সব রান্নার কম্পিটিশনে নেমে পড়ে এ কদিন। আড্ডাটা তেমন পোষায় না, তার বয়সী বন্ধু কেউ থাকেনা বলে। ঝিমলি চুপচাপ গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বসে খেয়ে, একসময় আস্তে করে বেরিয়ে পড়ে আসর থেকে। আসরে সে একেবারেই বসেনা, সেখানে যত বড়দের গান, হুল্লোড়, গল্প, আড্ডা, চলে। ভুলক্রমে বসে পড়লে তাকে দেখলেই দাদা বা আর কারোর হঠাৎ মনে হয়, ঝিমলি সারা পুজোয় কিছুই করেনি, অতএব বিজয়ার পার্টিতে সে গান গাইবে।
সেই সব ক্ষণগুলোতে ঝিমলির মনে হয়, মানুষের দাদা থাকে কেন কে জানে!
আসরে তাকে পাকড়াও করবে সবাই, আর দাদা অবধারিত বলবে, “ঝিমলি একটা গান খুব ভালো গায়, গা তো সখী ভাবনা কাহারে টা”।
এতদিনে সারা শহর জেনে গেছে যে ঝিমলি ওই একটা বাংলা গানই জানে। অনেক বকাবকি অনুরোধ উপরোধের পরে ঝিমলি কখনো সখনো এটি গেয়েছে। একটাই রক্ষে যে তাকে গাইতে শুরু করিয়ে দিয়ে, সবাই গল্পে মত্ত হয়ে যায়, ফলে সে দু চারটে লাইন বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি শেষ করে দিলেও কেউ খেয়াল করেনা। তখন শুরু হয় আর এক নাটক, সবাই ঠিকমত না শুনেই হাহুতাশ করবে, আহা কী ভালো গায়, ওকে গান শেখালে না কেন!
ব্যস, সেইসঙ্গে শুরু হয় সে এক পাঁচ বছরের পুরনো বিলাপ। আসলে ক্লাস ফাইভে তাকে পাঠানো হয়েছিল বর্ধন স্যরের কাছে গান শিখতে। বর্ধন স্যর হল লখনউর “হচ্ছি” বাঙালী, তাদের স্কুলের মিউজিক টীচার, তাছাড়া শহরের একমাত্র ক্ল্যাসিকাল গায়ক। তিন চার মাস আ আ করে ইমন আর বসন্ত শেষে অন্যান্য টিউশনের মত এটিতেও ইতি হয়। মোটামুটি এই দুটির ওপর দিয়ে সে স্কুলের বাকী বছরের মিউজিক পরীক্ষা পাস করে যাওয়ায়, গান শেখা, গলা সাধা, এসব কষ্টকর পদ্ধতির দিকে আর পা বাড়ায় নি। তার মধ্যে তেমন প্রতিভাও নিশ্চয়ই স্যর দেখেননি কারণ পরবর্তীতে তার গান ছাড়ার আক্ষেপ শিক্ষক বা ছাত্রী দুজনের কারো মধ্যেই তেমন দেখা যায়নি। তবুও মাঝেসাঝে অতর্কিতে এই সখী ভাবনা কাহারের খাঁড়া ঝিমলির ওপর এখনো নেমে আসে, এবং এ ব্যাপারে তার ঘরের শত্রু দাদাই!
বাসুআন্টি এবার তার বাড়ির বচ্ছরকার বিজয়া সম্মিলনীর আগে শুধু নাটক আর নাচের দলকে আলাদা করে ডাকল চায়েতে, এক পড়ন্ত বিকেলে।
আহা, পুজো আর দেওয়ালীর মাঝের এই সময়টায় দুপুর আর বিকেলগুলো যা দারুন হয়। রোদ ঝলমল, ঠান্ডা মোলায়েম হাওয়া, বাতাসে নানারকম সুন্দর গন্ধ ভাসে, ইউক্যালি, হাস্নুহানা। বিকেলে সাইকেল নিয়ে ক্যানালের ধার দিয়ে দিয়ে অনেকদুরে গিয়ে কালভারটের ওপর বসে সূর্যাস্ত দেখতে বড় ভালো লাগে। আন্টির বাড়ি যাবেনা যাবেনা করেও শেষ অবধি গেল।
মন ভালো নেই, একেবারেই নেই। আচ্ছা পুজোয় বাড়ি আসা যাবেনা যখন তখন আর বাংলার আই আই টিতে পড়ে কী লাভ? কাছে দিল্লিতে পড়া যেত না?
এইসব নানারকম ভাবনায় আজকাল সবসময় চোখ কেমন ভিজে যায় আর নাক ফিচফিচ করে। কালকেও মা ধরে মধু তুলসী খাইয়ে দিল খানিকটা, খামকা। সেও গিলে নিল, বলতে পারলনা ইহা আসল সর্দি নহে!
নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কম, তাও আন্টি কত কী বানিয়েছে। নিজে দারুন রান্না করে, আন্টির বানানো মীট বল ওর ফেভারিট। আন্টি জানে, তাই জোর করে অনেকটা তুলে দিল প্লেটে, কিন্তু খেতে যে একদম ইচ্ছে করছেনা।
আজকে সবাই এমনকি রীনা কাকিমাও আন্টির খুব প্রশংসা করল। আন্টি খুব খুশী, সবাই খুব ভালো করেছে।ঝিমলি পর্যন্ত একদম না ভুলে পুরো সংলাপ বলেছে, এত কম সময়ে তৈরি করে উতরে দিয়েছে, বড়রা সবাই ওকে উৎসাহ দিল, ভালো বলল। আন্টি আবার বলে, বারো ক্লাসটা হয়ে গেলে তোকে আমার নাটকে বড় পার্ট দেব।
এত দুঃখেও একটু হেসে ফেলে সে। বারো ক্লাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা তো তারও, তবে আন্টি ভাবতেও পারেনা ওনার জীবনে সে কোন পার্ট নিতে চলেছে আগামী দিনে!
মেজাজ শরীফ হওয়ার জন্যে না তার কাজে খুশী হয়ে, বা যে কোনো কারণেই হোক, আন্টি বলে ওঠে,
“ঝিমলি তোর সেই গানটা গা তো, বাইরেটা কী সুন্দর লাগছে। তুই গা তারপরে বাকীরাও এক এক করে গাইবে।“
কী যে হল তার, আজ যেন বারণ করতেও ভুলে যায়। বসার ঘরে মোড়াতে যে জায়গাতে সে বসে, সেখান থেকে ভেতরের ঘরটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। ব্রুস লী র ছবির ওপর র্যাকেট গুলো আড়াআড়ি টাঙানো, জানালা দিয়ে পড়ন্ত বেলার একফালি রোদ তেরছা হয়ে এসে পড়েছে টানটান যত্নের বিছানার চাদরের ওপর। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ লাগে, আর তা যেন গান হয়ে আপনিই বেরিয়ে আসে, অন্যদিনের মত তাকে চেষ্টা করতে হয়না।
“তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা.........সখী ভালোবাসা কারে কয়” ।
এই প্রথম কোন আসরে তার গানে পিন পড়া নৈঃশব্দ।
গান শেষ হলে কেউ কোনো কথা বলে না প্রথমটায়, তারপরে আন্টিই সামলে নিয়ে বলে ওঠে,
“কী ভালো গাইলি রে মেয়ে, তোর মা ঠিক বলে, মহা ফাঁকিবাজ তুই, গানটা কেন যে শিখলি না!”
আঙ্কল রান্নাঘরে সোমবতীকে ডেকে হইচই করে তাকে একটা স্পেশাল দইবড়া দিতে বলে। পরের গান শুরু হতে ও প্লেট হাতে গুটি গুটি বাইরে বেরিয়ে আসে। সবুজ লনের ওপর দিয়ে হেঁটে শিউলি গাছটার দিকে যায়, নীচে কমলা সাদার আসন বিছিয়ে ছড়িয়ে আছে সকালের ঝরা শিউলিরা।
ইস কেন যে “মন কেমন করে” গানটা জানিনা! সদ্য গাওয়া গানের জন্যে, না জানা গানের কথা মনে করে, নাকি ঝরা শিউলির দুঃখে, সে হু হু করে কেঁদে ফেলে, গাছতলায় বসে।
একটা রিকশা থামার শব্দ গেটে। উমনো ঝুমনো চুল, রঙ চটা ব্লু উইন্ডচিটার আর পিঠে রুকস্যাক। রিকশাওয়ালা কে পয়সা দিতে দিতে বাড়ির দিকে আনমনে তাকানো। ঝিমলি ভেসে চলে শরতের হাওয়ায়, রাঙা বিকেল গায়ে জড়িয়ে কনে দেখা আলোয়, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখে গেটে। হাসি কান্নায় শিউলি ঝরা চোখে কারুর চোখ পড়ে, খানিক বিস্ময় আর বুঝি অনেক আনন্দে উজ্জ্বল চশমার কাঁচ আলোজ্বলা।
“বিরহ মিলন হল আজি...”, এমনটাও হয়, গানের কথার মত বা গল্পের মত সত্যি?
ঘরের ভেতরে ভট্টাচার্য জেঠু তখন গান ধরেছে, “এবার হর এলে পরে বলব উমা ঘরে নেই”।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনঅন্তরেখা - albert banerjeeআরও পড়ুনকি ভাবিতে হইবে - বোদাগুআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 a | 220.253.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১৯:১৯542005
a | 220.253.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ১৯:১৯542005- পড়ছি
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Anirban M, dc, dc)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... hu, দ, Sara Man)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হেঁয়ালি, Ranjan Roy, Ranjan Roy)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... albert banerjee, দ, দ)
(লিখছেন... Srimallar, r2h)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।













