- বুলবুলভাজা নাটক

-
হেলদি বেবি
শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
নাটক | ২২ মার্চ ২০২৫ | ৯৫২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - পর্ব ১ | পর্ব ২দু- অঙ্কের এই নাটকটি দু-কিস্তিতে প্রকাশ করা হবে, এখন প্রথম কিস্তি। নাটকটি যখন কল্পনা করা হয় তখন এটিকে বাচিক বা শ্রুতিনাটক হিসেবে ভাবা হয়েছিল। বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজনকে শোনাবার পর অনেকেই বলেছেন, মঞ্চেও এ-নাটক ভালোই দাঁড়াবে। অতএব, প্রকাশ করবার সময় মোটামুটি মঞ্চোপযুক্ত নাটকের কাঠামোতেই এটা লেখা হল। পড়ার পর যদি এ-নাটক অভিনয় করায় – নাট্যমঞ্চেই হোক বা বাচিক – কেউ উৎসাহিত বোধ করেন, লেখকের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলে লেখক বাধিত হবেন।
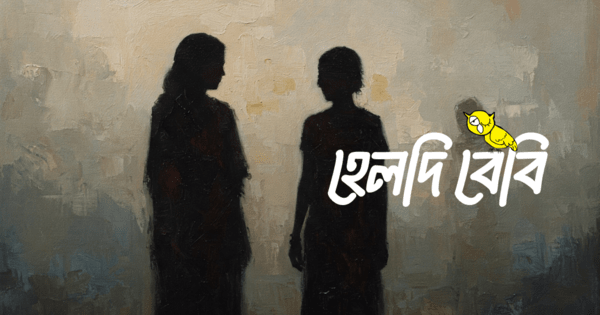
১
নাটকের শুরু দুই অন্ধ বোন অন্তরা-সঞ্চারীর শোবার ঘরে। খাট-টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির সাধারণ
গৃহসজ্জা। চেয়ারে ছোট বোন সঞ্চারী, সে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছে। খাটে দিদি অন্তরা, শুনছে।
সঞ্চারী।আমরা দু'বোন এক বাড়িতে থাকি
অনেক সুখের সেই একটি সুখ,
অ্যাস্ট্রোনমির অঙ্ক কষে দিদি
সেই গর্বে নাচে বোনের বুক।
সূর্য-তারা বোনের কবিতায়
দিদির অঙ্কে তারাই আসে-যায়,
আমরা জানি আমরা কেমন দেখি
অন্যে বলে অন্ধ? ― তা বলুক!
আমাদের এই রাজবল্লভ পাড়া
পশ্চিমে তার বয় গঙ্গার ধারা
পুবের পথে ঠং ঠং ট্রাম যায়,
আমরা মত্ত অঙ্কে-কবিতায়।
সমান্তরাল দুটো সরলরেখা
কোন্ অসীমে মিলবে দিদি জানে,
“সীমার মাঝে কোন্ সে অসীম আছে” ―
বোনের কাছে শুধোয়, “সে কোন্খানে?”
আমি শুধোই, পথের কোথায় শেষ?
এই প্রশ্নের জবাব দিদির জানা,
“লিমিট, লিমিট! যদিও সেথায় যেতে
ইনফাইনি-টেসিমালের মানা!”
আমরা দু'বোন কী আনন্দে থাকি
আমাদের এই রাজবল্লভ পাড়ায়
গঙ্গা এবং ট্রামের মধ্যিখানে
আমরা মত্ত অঙ্কে-কবিতায়!
দিদি এখন বরের বাড়ি যাবে,
রাজবল্লভ থেকে রাজারহাট,
কবিতা নয়, জামাইবাবুর কাছে
হয়তো নেবে অর্থনীতির পাঠ।
দিদির অঙ্ক কাব্যভূমি ছেড়ে
করবে হিসেব লাভ বা ক্ষতির গতি?
ছেড়ে দিয়ে সরস্বতীর বীণা ―
লক্ষ্মীপুজোয় হবে কি তোর মতি?
আমরা দু'বোন একই ঘরে থাকি
ভাগ করে নিই সকল দুঃখ-সুখ,
এখন দিদি বরের ঘরে যাবে
আমার কেন বুক করে ধুকপুক!
অন্তরা। বাঃ, বেশ লিখেছিস তো, শুধু একটাই গণ্ডগোল।
সঞ্চারী। কী গণ্ডগোল?
অন্তরা। হিসেবের।
সঞ্চারী। তুই তো শুধু হিসেবেরই গণ্ডগোল দেখিস। কবিতায় আবার কী হিসেব?
অন্তরা। রেগে গেলি? তাহলে থাক।
সঞ্চারী। মোটেও রাগিনি। তুই রাগাতে চেষ্টা করছিস ঠিকই, কিন্তু পারছিস না। ঠিক আছে, বল্। বল্, কী গণ্ডগোল হল।
অন্তরা। সবই করলি, শুধু দু' স্ট্যাঞ্জা অন্তর একটা করে স্ট্যাঞ্জা ভুলে গেছিস।
সঞ্চারী। কোন্টা? আমাদের সেই গ্রামের নামটি খঞ্জনা/আমাদের সেই নদীর নামটি অঞ্জনা...?
অন্তরা। (যোগ দেয়) আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে/আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। (একটু থেমে) না, কিন্তু তা তো হবে না, অঞ্জনা-রঞ্জনা নয়, তোকে লিখতে হবে...লিখতে হবে...ধর্,...
রাজবল্লভ পাড়া আমাদের বাড়ি
একটি প্রান্তে ঠং ঠং ট্রামগাড়ি
গঙ্গা এবং ট্রামের মধ্যিখানে
আমরা দুবোন ― অন্তরা-সঞ্চারী।
প্রথম দুটো স্ট্যাঞ্জার পর তুই লিখছিলি এরকমই একটা, কিন্তু শেষ করলি না ঠিক মতো। রবীন্দ্রনাথের আসল কবিতাটায় কিন্তু খঞ্জনা অঞ্জনা রঞ্জনা সব কটা নামই আছে, আর প্রতি দু' স্ট্যাঞ্জায় একবার করে ফিরেও আসছে।
সঞ্চারী। বা বাহ্ দিদি, তুই তো দারুণ শেষ করলি।
অন্তরা। আমি কী করলাম, আমি তো তোর লাইনগুলোই প্রায় নিয়েছি, আমাদের এই রাজবল্লভ পাড়া/ পশ্চিমে তার বয় গঙ্গার ধারা/ পূবের পথে ঠং ঠং ট্রাম যায়... সবই তো নিলাম...
সঞ্চারী। হ্যাঁ, তারপর কী সুন্দর ঢোকালি আমাদের নাম দুটো:
রাজবল্লভ পাড়া আমাদের বাড়ি
একটি প্রান্তে ঠং ঠং ট্রামগাড়ি
(অন্তরাও যোগ দেয়)
গঙ্গা এবং ট্রামের মধ্যিখানে
আমরা দুবোন ― অন্তরা-সঞ্চারী।
উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে সঞ্চারী উঠে দাঁড়ায়, খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে, তারপর দিদির পাশেই
বসে পড়ে। দরজায় খট খট শব্দ শোনা যায়, খটখটানির একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, শব্দটা সঞ্চারী এবং অন্তরার পরিচিত।
অন্তরা। কাম ইন। (অন্তরা-সঞ্চারীর বাবার প্রবেশ)
বাবা। মে আই সিট ডাউন ম্যামস।
সঞ্চারী। ডু সিট ডাউন প্লীজ।
বাবা। (চেয়ার টেনে বসতে বসতে) আজ অনলাভ আসছে।
অন্তরা। আসবে বলেছিল, কিন্তু আজই আসবে বলেনি। কী ব্যাপার, বিশেষ কিছু?
বাবা। হুঁ, বিশেষ কিছু। সেটাই তোদের সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।
অন্তরা। কী ব্যাপার, বাবা? তোমার গলাটা একটু কেমন-কেমন ঠেকছে।
বাবা। না না, কেমন-কেমন নয়...
সঞ্চারী। কেমন-কেমন নয়? ঠিক আছে, তো বলো না।
বাবা। ওই বিয়ের ব্যাপারে ডিটেলে সব আলোচনা করবে আর কী...
সঞ্চারী। আলোচনা করবার কী আছে বাবা, আলোচনা তো হয়েই গেছে।
বাবা। হ্যাঁ হয়ে তো গেছেই, হয়ে তো গেছেই...
সঞ্চারী। কী ব্যাপার বল তো বাবা, তুমি একটা কিছু বলতে চাইছ কিন্তু বলতে পারছ না মনে হচ্ছে। কী, বিয়ের দিন-টিন বদলাতে চাইছে এখন?
বাবা। না না, দিন তো ঠিকই হয়ে গেছে।
সঞ্চারী। তবে? কী ব্যাপার? দিদি, তুই কিছু জানিস?
অন্তরা। জানিনা। আমাকে বলেছিল আমাদের বাড়ি আসবে, আজই যে আসবে তা-ও স্পষ্ট করে বলেনি, বাবার সঙ্গে কিছু কথা-টথা আছে বলছিল। কী কথা, আমি জিজ্ঞেস করিনি।
সঞ্চারী। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। সামথিং আনপ্লেজান্ট। বাবা বলতে চাইছে, বলতে পারছে না। কী ব্যাপার বাবা?
বাবা। অনলাভর মা একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। এবং সে প্রস্তাবটা আমার পছন্দের নয়।
সঞ্চারী। পছন্দের নয় তো বলে দিলেই হয়। এত আমতা-আমতা করছ কেন? কী প্রস্তাব শুনি।
বাবা। উনি একটু ওই রিচুয়াল-টিচুয়ালের ব্যাপারে ওঁর মতামত জানিয়েছেন আর-কি।
সঞ্চারী। সে তো সেইদিনই কথা হয়ে গেল। দিদি তো সিঁদুর পরবে মেনেই নিয়েছে।
বাবা। হ্যাঁ, সিঁদুর মেনে নিয়েছে, সে তো রেজিস্ট্রারের সামনেই হবে কথা হলো, কিন্তু উনি ঠিক সেইটুকু মীন করেননি, উনি চাইছেন রিচুয়াল ওয়েডিঙের সব কিছুই হোক।
অন্তরা। সবকিছু?
বাবা। হ্যাঁ, সবকিছু। যাগযজ্ঞ, কন্যা সম্প্রদান, সপ্তপদী-টদি সব। মালাবদল, শুভদৃষ্টি...
অন্তরা। শুভদৃষ্টি! ('দৃষ্টি'-র ওপর জোর দেয় অন্তরা)
সঞ্চারী। বাবা, আমরা তো দৃষ্টিহীন। আমাদের দৃষ্টি তো শুভ হয় না, কিছুই হয় না, টেনে-হিঁচড়ে কেউ যদি করাতেই চায়, সে তো নির্ঘাৎ অশুভ।
বাবা। থাম! থাম, সন্তু থাম! কী বলছিস! কখনো বলিস না এসব কথা আমার সামনে! আমি তোদের কখনও বলেছি এ সব কথা? শিখিয়েছি এ সব?
সঞ্চারী। তুমি শেখাওনি বাবা, তা-ই তোমার সামনেই বলি। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা এসব আলোচনাও করিনা। (হঠাৎ ডোর-বেল বেজে ওঠে)
বাবা। ওই যে, কলিং বেল। অনলাভই এলো মনে হয়। ওকে এ ঘরেই ডেকে আনি।
বাবা বেরিয়ে যায়। সঞ্চারী-অন্তরা খাটের ওপরেই একটু গুছিয়ে বসে, একটু পর বাবা আর অনলাভ।
বাবা। (অনলাভকে – একটা চেয়ার দেখিয়ে) বসো, ওইখানে বসো। (অনলাভ বসে) তোমার মা'র প্রস্তাবটা ওদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।
সঞ্চারী। কফি খাবে তো অনলাভ দা (উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে যায়, অন্তরা বসেই থাকে)?
বাবা। আসলে মুশকিলটা কী জান তো অনলাভ, ছোটবেলা থেকেই আমরা ওদের মানুষ করেছি একটু অন্যরকম ভাবে, কোন ধর্মীয় রাইট্স্ বা রিচুয়ালে ওরা ঠিক অভ্যস্ত হয়নি। তিন বছর আগে ওদের মা যখন চলে গেলেন ― তুমি তো শুনেইছো ― তাঁর শরীরটাকেও আমরা দাহ করিনি, সেটা দান করা হয়েছিল মেডিকাল কলেজে, শ্রাদ্ধশান্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি তখন। আজ যদি এই সব রিচুয়ালের মধ্যে ওদের ঠেলে দিই আমি, কী জান তো, আমার মনে হয় ওদের মা বেঁচে থাকলে...
একটা ট্রে-তে চার মগ ধূমায়িত কফি আর দুটো বাটিতে বিস্কুট-চানাচুর নিয়ে ঘরে ঢোকে সঞ্চারী, বাবা আর অনলাভর সামনে দুটো মগ
আর বিস্কুট-চানাচুরের বাটি দুটো রেখে দুহাতে দুটো মগ নিয়ে একটা অন্তরাকে দেয়, অন্যটা নিজে নিয়ে খাটে অন্তরার পাশে বসে।
সঞ্চারী। প্রশ্নটা মা বেঁচে থাকলে কী হতো সেটা নয় বাবা, রাইট-রিচুয়ালটাও বড় কথা নয়, দিদি তো সিঁদুর পরতে রাজি হয়ে সে সমস্যার সমাধান অনেকটাই করে দিয়েছে, প্রশ্নটা হলো, দৃষ্টিহীনকে দিয়ে শুভদৃষ্টির প্রস্তাব তো আমাদের আইডেন্টিটিকেই অস্বীকার করা।
অনলাভ। তুমি আইডেন্টিটির কথা তুলছ কেন আমি জানিনা সন্তু,...
সঞ্চারী। যার দৃষ্টিই নেই তাকে শুভদৃষ্টির আহ্বান কি তার দৃষ্টিহীনতা স্বীকার করার কথা বলে অনলাভদা?
বাবা। আঃ সন্তু, তুই আর বড় হলিনা, কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শিখলি না এখনো।
অনলাভ। না মেসোমশাই, ওর মাথায় যখন প্রশ্নটা এসেছে, তখন এটার ঠিক ঠিক উত্তরটাও ওর জেনে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া সন্তু নিজেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, ওর যদি মনে হয়েই থাকে আমার কোন কাজ চাহিদা বা অনুরোধ ওদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে পারে, তখন আমার দিকটা খোলাখুলি শুনে নেওয়াই ভালো নয় কি? (সঞ্চারীকে) তুমি তো জানো সন্তু, কলেজে তোমার দিদি অন্তুর চেয়ে আমি এক বছরের সীনিয়র ছিলাম, ডিপার্টমেন্টটাও এক ছিল না, আমি পড়তাম ইকোনমিক্স আর ও ম্যাথ্ম্যাটিক্স। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হবার কোন কারণই ছিল না। পাস সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের ম্যাথ্ম্যাটিক্স পড়তে হত। আমার একটু অসুবিধে হচ্ছিল সাবজেক্টটা নিয়ে। আমাদের ক্যালকুলাস পড়াতেন কৈলাস বাবু। যখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে, উনিই আমাকে ফার্স্ট ইয়ারের অন্তরার সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আমি জানতামও না অন্তরা চোখে দেখে না। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার পর আমি অবাক হয়ে গেলাম। অ্যালজেব্রা, ট্রিগনোমেট্রি আর ক্যালকুলাসের যে সব কনসেপ্ট চোখে না দেখেও যে আদৌ বোঝা যেতে পারে বলে আমি ভাবতেই পারতাম না, সেগুলোই শুধুমাত্র আঙুল আর টুকরো কাগজের সাহায্যে ও আমাকে দিব্যি বুঝিয়ে দিত। যখন ও বোঝাতো, ওর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যেতাম। কী ইনভল্ভ্মেন্ট! কী উত্তেজনা! তখনই আমি বুঝেছি ও চোখ দিয়ে হয়তো দেখে না, কিন্তু তবুও, দেখে। মন দিয়ে দেখে কিংবা বুদ্ধি দিয়ে দেখে। অন্তু দৃষ্টিহীন, আর আমি এই পুরু লেন্সের চশমায় দৃষ্টিমান?! তুমি আমাকে আর যা-ই বল, তোমাদের আমি দৃষ্টিহীন ভাবি, একথা বোলো না। তোমার একটা কবিতায় 'কালপুরুষ' শব্দটা যে ব্যঞ্জনা পেয়েছিল, কালপুরুষ যে দেখেনি সে কীভাবে তা লিখতে পারল? তুমি অন্ধ? অন্তু অন্ধ? পৃথিবীতে এত চক্ষুষ্মান অন্ধ দেখার পর আমি অন্তত তা মানতে পারব না।
সঞ্চারী। আমি ঠিক তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলতে চাইনি অনলাভদা, আমার আপত্তিটা একটু অন্য। তোমাকে বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারিনি আমি। অন্ধকে অন্ধ ভাববে না কেন? কী আপত্তি তাতে? আসল কথা...হঠাৎ বাইরের দিকের দরজায় (যেটা এই ঘর থেকে দেখা যায়না) জোরে ঠক ঠক শব্দ শোনা যায়। লক্ষ্যণীয়,
অনলাভর প্রবেশের সময় যে ডোরবেলটা বেজেছিল, এখন সেটা না বেজে তার বদলে জোরে ঠক ঠক শব্দ।
বাবা। এমন আওয়াজ করছে কে? তোমরা একটু বস তো, আমি দেখে আসি। (বেরিয়ে যায়, এ ঘর থেকে এক দল লোকের এবং বাবার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এই আগন্তুকদের উচ্চারণে শ, ষ, স – সবই দন্ত্য স!)
কণ্ঠস্বর ১। মেসোমসাই, আমরা এলুম।
বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।
কণ্ঠস্বর ১। আপনাদের বাড়িতে তো এখন উৎসব লেগে গেল, সাজানো-ফাজানো হবে, খাওয়া দাওয়া...
বাবা। সাজানো...খাওয়া দাওয়া... আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।
কণ্ঠস্বর ২। সে বুঝতে যে আপনার একটু সময় লাগবে তা জানি। মাসিমা যখন মারা গেলেন আমরা মড়া নিয়ে নিমতলায় যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আসার আগেই আপনি হাসপাতালে মড়াটাকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সাদ্ধসান্তি কিছুই হলনা। এসব ব্যাপার রাজবল্লভপাড়ায় আগে কখনো হয়নি।
বাবা। ও।
কণ্ঠস্বর ২। না না 'ও' নয়, 'ও' নয়, এ সব 'ও' বলে সামলানো যাবে না। এসব ব্যাপার রাজবল্লভপাড়ায় আগে কখনো হয়নি সেটা জেনে রাখবেন। মনোজদা ― মানে আমাদের কাউন্সিলার ― খুব রেগে গিয়েছিল। আমরাই বোঝালুম, দু-দুটো কানা মেয়ে, মাথার ঠিক নেই মেসোমসায়ের, নাহলে মানুস ভালো। যাক্গে, সে কথা ছেড়ে দিন, সুনলুম আপনার বড় মেয়ের নাকি বিয়ে, কথাবাত্তা সব পাকা হয়ে গেছে। আবার আর গণ্ডগোল যেন না হয় তাই বলতে এলুম। ডেকোরেসন-ক্যাটারিং-ফ্যাটারিং সব আমরাই করব। আর মনোজদাকে আপনি আগে থেকে গিয়ে নেমন্তন্নটা করে আসবেন।
বাবা। আমরা তো এখনও এ সব কিছু ভাবিইনি ভাই, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আপনাদের বলব।
কণ্ঠস্বর ৩। না না পয়োজন হলের কথা নয়, পয়োজন তো হবেই। আপনি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করুন যেরকম পারেন, পুরুতমোসাইকে ডাকুন, দিন-ফিন ঠিক করুন, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা কবে আসব বলুন।
বাবা। না না তাড়াহুড়োর কিছু নেই, দরকার হলে আমিই ডেকে নেব।
কণ্ঠস্বর ১। ঠিক আচে ঠিক আচে, আমাদের তো দেখতেই পাবেন, আসেপাসেই থাকি সবসময়।
কণ্ঠস্বর ৩। তাছাড়া মেসোমসায়ের চোখ তো ঠিকই আছে, (হাসি) হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা...
কণ্ঠস্বর ২। আমরা চলি তাহলে। মনোজদার কথাটা মনে রাখবেন, কোন চাপ নেই। যেমন আপনার সামত্ত, যা এস্টিমেট, তা-ই করে দোব। ফাইভ-এস্টার চান, হয়ে যাবে। সুদু সাঁখা-সিঁদুর চান, বলবেন আমাদের, কোন অসুবিদে নেই। চলি, মেসোমসাই।
দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া যায়, একটু পর বাবা ফিরে আসেন, চেহারা দেখে মনে হয়
এইটুকু সময়েই তাঁর ওপর দিয়ে ধকল গিয়েছে অনেকটা, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন তিনি।
অন্তরা। বাবা, একটু জল খাবে?
বাবা। হ্যাঁ মা, দে একটু। (অন্তরা ভিতরে চলে যায়, এক গ্লাস জল নিয়ে ঢোকে, বাবা উঠে দাঁড়িয়ে জলটা তার হাত থেকে নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে রেখে দেয়)
বাবা। (জল খাওয়া শেষ হলে) সব শুনতে পেলে তো তোমরা?
অনলাভ। এ আর কী শুনব মেসোমশাই, এটাই তো এখন রীতি, সব পাড়ায়। সব কিছুর সিণ্ডিকেট, বাড়ি রিপেয়ার করুন, রং করুন, বাড়িতে যে কোন কাজকর্ম হোক, পাড়ায় পাড়ায় সিণ্ডিকেট, তাদের মাথায় একজন পোলিটিকাল দাদা, তাদেরই কন্ট্র্যাক্ট দিতে হবে। আর হবেই বা না কেন, ইণ্ডাস্ট্রী নেই, চাকরি-বাকরি নেই ছেলেদের, নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে...সরকার চুপ...অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও চুপ।
বাবা। আমি কিন্তু এদের সঙ্গে ডীল করতে পারিনা একেবারে, আমার শরীর খারাপ লাগে।
সঞ্চারী। তোমাকে ডীল করতে হবে না বাবা, আমিই কথা বলব ওদের সঙ্গে।
বাবা। তুই কথা বলবি? শুনলি না কী ভাষায় কথা বলছিল তোদের সম্বন্ধে?
অন্তরা। ওতে আমাদের কিছু যায়-আসে না বাবা। ছোটবেলা থেকে অনেক শুনেছি এসব। ওতে আমরা অভ্যস্ত।
অনলাভ। এত সহজে কী করে বলতে পার তোমরা অভ্যস্ত? কথাবার্তায় মিনিমাম শালীনতাটাও থাকবে না?
সঞ্চারী। ওর ভাষায় ও বলেছে, কী তাতে এল-গেল? কানা না বলে যদি অন্ধই বলতো, তাতেই বা কী যায়-আসে?
অনলাভ। কী বলছ তুমি সন্তু?
সঞ্চারী। ঠিকই বলছি। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর তো পড়েছ নিশ্চয়ই, ওতে ঠাকুরদা আর অমলের কথোপকথনে ঠাকুরদার একটা সংলাপ আছে, জানিনা তুমি খেয়াল করেছ কিনা। ছিদাম নামে এক ভিখারিকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছিদাম চোখে দেখতে পায় না। পিসেমশাই সেটা বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেছেন, ও মিথ্যে কানা, মিথ্যে খোঁড়া। ঠাকুরদা অমলকে বোঝালো, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ওইটুকুই যে ও চোখে দেখতে পায় না, তা ওকে কানা বল আর না-ই বল। বাড়ি গিয়ে ডাকঘরটা আর একবার পড়ে দেখো, ঠাকুরদার উচ্চারণে ওই কানা শব্দটা শুনতে তোমার একটুও খারাপ লাগবে না, কারণ ঠাকুরদা শুধু এই সত্যটুকুই মেনে নেয় যে ছিদাম দেখতে পায় না। সত্যকে মানার মধ্যে তো কোন উপহাস নেই, কোন উপেক্ষা নেই। আমাদের এই প্রকৃতিটা কেন এত সুন্দর জানো অনলাভদা, কারণ প্রকৃতিটা একঘেয়ে নয়, সে মাঝে মাঝে তার সৃষ্টির ঐক্যের মধ্যে, বৈচিত্র আনে। আমি কিন্তু বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বলছি না অনলাভদা, বলছি ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র। তোমাকে আমাদের ছোটবেলার একটা গল্প শোনাই। আমাদের মাসি একবার বেড়াতে এসেছে আমাদের বাড়ি। সকালে সবাই মিলে আমরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি। টোস্ট ডিম কলা এই সবের ব্রেকফাস্ট। দেখেছ, কলার ছড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে একই খোসার আস্তরণের মধ্যে একজোড়া কলা থাকে? অনেকে বলে যমজ কলা? সেরকম একটা কলা মা দিদিকে দিয়েছে। মাসি বললো, দিদি, মেয়েদের যমজ কলা দিতে নেই। মা বললো যমজ কলা মানে? মাসি বললো, ঐ যে, অন্তুকে যেটা দিচ্ছ। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। মা হেসে বললো, দূর বোকা, ওটাই তো প্রকৃতির বৈচিত্র, সব খোসার মধ্যে একটা কলা থাকে, ওটায় দুটো। মাঝ থেকে অন্তুর লাভ: একটার জায়গায় দুটো পেলুম, টাক-ডুমাডুম-ডুম! মনে আছে, সেদিন অনেকটা কান্নাকাটি করেছিলাম ঐ কলাটা আমিই খাব বলে। দিদি তো আমার সাথে ঝগড়াঝাটি করত না কোনদিনই, যা-ই চাইতাম অবলীলায় দিয়ে দিত আমাকে। সেদিন কিন্তু দিদি কেমন জেদ ধরে রইলো, কিছুতেই দিলনা আমাকে কলাটা!
অন্তরা। কী করে দেব? আমি তখন কলাটাকে ধরে বুঝতে চাইছি জোড়া কলার সারকাম্ফারেন্স কত। এমনিতে কলা বা যে কোন বৃত্তাকার জিনিসের সারকামফারেন্স হলো পাই ইনটু ডায়ামিটার। ডায়ামিটার যদি এক ইঞ্চি হয়, একটা কলার সারকামফারেন্স তাহলে থ্রী পয়েন্ট ওয়ান-ফোর ইঞ্চি। তাহলে জোড়া কলাটার সারকামফারেন্স কতো?
সবাই হেসে ওঠে।
বাবা। সত্যি। তোমরা যতই হাসো, ছোটবেলা থেকেই অন্তুর এই মাপজোকে ঝোঁক। যা-ই পাবে হাতের কাছে, সমানে বোঝার চেষ্টা করবে সেটার আকৃতি কীরকম। কোন্ ডাইমেনশন কত হতে পারে, এরিয়া কত, ভল্যুম কত, এইসব।
সঞ্চারী। তাহলে কি তুমি বুঝতে পারলে অনলাভদা, আমাদের আপত্তিটা কোথায়?
অনলাভ। সত্যি বলব? এখনো ঠিক বুঝিনি। শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে তোমাদের পাড়ার মস্তানদের তুমি ক্ষমা করে দিয়েছ।
সঞ্চারী। হ্যাঁ, ওদের ভাষাটা নিয়ে আমার কোন অভিমান দুঃখ বা অভিযোগ নেই, শুধু একটু করুণা আছে। ওদের যে ভাষার গণ্ডগোল সে তো শুধু আমাদের বিবরণে নয়, সে গণ্ডগোল ওদের শিক্ষায়: মেসোমশাইকে মেস্সোমসাই বলা বা শাঁখা-সিঁদুরকে সাঁখা-সিঁদুর বলার মতোই ওরা কানা-টানাও বলে, তাতে আমাদের মতো কানাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।
বাবা। আমি একটু কথা বলব অনলাভ?
অনলাভ। বলুন না মেসোমশাই।
বাবা। আমি বলছি, কারণ ছোটবেলা থেকেই আমরা ওদের একটু অন্যরকমের ভাবতে শিখিয়েছি। আমরা ওদের শেখাবার চেষ্টা করেছি যে ওরা ওদের মতই, বেশির ভাগ মানুষের তুলনায় হয়তো একটু অন্য রকমের, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা কারো চেয়ে ভালো বা মন্দ, বেশি বা কম। মনুষ্যজাতির আর পাঁচ জনের মতই ওরা, যদি পাঁচটা মানুষের চেয়ে একটু ভালো কোন কোন ব্যাপারে ওদের হতে হয়, তাহলে ― আর পাঁচ জনেরও যেমন ওদেরও তাই ― একটু বেশি বেশি চেষ্টা করতে হবে। না যদি হতে চায়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।
অনলাভ। সে তো ওরা হয়েওছে, দমে না গিয়ে চেষ্টা করেছে, তাই ওদের প্রতিভার এমন স্ফুরণ হয়েছে, নিজের নিজের বিষয়ে ওরা তো আউটস্ট্যাণ্ডিং। কিন্তু তবুও, আমার একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মানুষের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যিই কি ওদের কোন অভিযোগ নেই?
সঞ্চারী। নেই? কে বলল, নেই?
অনলাভ। কী অভিযোগ সেটাই আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।
সঞ্চারী। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্বন্ধেই কিছু বলতে চাই না, কিন্তু এটা কি খেয়াল করেছ, প্রায় সব মানুষের নালিশ আমাদেরই বিরুদ্ধে?
অনলাভ। তোমাদের বিরুদ্ধে? কীরকম?
সঞ্চারী। যে কানে শুনতে পায় না ― অতএব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখেনি ― সে হাবা। যে চোখে দেখতে পায় না সে কানা। যার পা দুটো বাঁকা অথবা ছোট, সে ল্যাংড়া। আসল কথাটা হল সে কেন আমার মতো নয়, আর নয়ই যখন, সে আমার সমাজে জায়গা পেতে চায় কোন্ অধিকারে? সে ভিখারি হতে চায় তো ভিক্ষে দেওয়া যায়, সে কিছুই হতে না চেয়ে অকর্মণ্য হয়ে থাকতে চায় তো তাকে দয়া করা চলে। কিন্তু সে কেন সাধারণ হতে চাইবে? কেন হতে চাইবে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো? কোন্ অধিকারে?
অনলাভ। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না সন্তু, সব মানুষ এরকম ভাবে না। বেশির ভাগ মানুষেরই এদের প্রতি সহানুভূতি থাকে, তাই এত স্পেশাল স্কুল, এত সরকারী ব্যবস্থা, এমনকী সাধারণ মানুষের চেষ্টাতেও আজকাল কতো প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে।
সঞ্চারী। দয়া। দয়া, অনলাভদা, দয়া। সহানুভূতি নয়। আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান রীতিনীতিগুলোর কথাই ধর না। এই যে এ-পাড়ার ছেলেরা আজ কথা বলে গেল বাবার সঙ্গে, ওদের কথাই ধর না। ওরা যখন অন্ধকে কানা বলে, তখন এটা তো ঠিকই যে অন্ধরা ওদের চোখে ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। কিন্তু তার বিয়েটা, ওদের মতে যেটা আর পাঁচটা বিয়ের মতই বিয়ে ― যেটা চালু বিয়ে ― সেটা সে ভাবেই হতে হবে। শুনতে পাচ্ছিলে তো, ডেকোরেশন চাই। কানা মেয়েটা সে ডেকোরেশন দেখতে পাক বা না-ই পাক, সেটা চাই, কারণ সেটাই রীতি। বাবাকে ওরা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করার কথা বলে গেল। যতটা যোগাড় করতে পারবে, যেরকম স-সামত্ত, সেই অনুযায়ী ফাইভ-এস্টার বা সাঁখা-সিঁদুরের ব্যবস্থা! সব চালু রীতি অনুযায়ী!
অনলাভ। কিন্তু সবাইকেই তুমি একেবারে ওদের সমগোত্রীয় ভাবতে পার না, অন্য অনেক মানুষ আছে যাদের শিক্ষাদীক্ষা রুচিটুচি অন্য রকমের।
সঞ্চারী। তা তো আছেই, আছেই তো, নিশ্চয়ই আছে। সেরকমেরই একটা পরিবারে একটা বিয়ের গল্প তোমাকে বলি, ভালো শিক্ষিত পরিবার, সবচেয়ে বড় কথা হলো বর এবং কনে দুজনেই এ বিয়েতে অন্ধ। কনেটি আমার বন্ধু, স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। স্কুলের পর আমার মতো প্রেসিডেন্সী কলেজে সে ভর্তি হয়নি, আমাদের স্কুলেই যে ভোকেশনাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে কম্প্যুটারে ট্রেনিং নিয়েছে। ওর বরই সেখানকার ট্রেনার। তো, বিয়েতে আমরা কনের এক দঙ্গল অন্ধ বন্ধু নিমন্ত্রিত। প্রথমে সব যাগযজ্ঞ হলো, আরও কতো কিছু হলো...
বাবা। আচ্ছা সন্তু, এই সব কথা কি না বললেই নয়?
সঞ্চারী। না বাবা, না বললেই নয়, কঠিন সত্যটা সবায়েরই শোনা দরকার। হ্যাঁ, তারপর ঐ মালাবদল সাত পাকে ঘোরা ইত্যাদি। কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে ঘোরানো হলো, তারপর শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি যখন হচ্ছে, বেশ উচ্চকণ্ঠে একটা ঘোষণা শোনা গেল: দৃষ্টিহীনের শুভদৃষ্টি। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা। কথাটা কে বলল বোঝা গেল না। কিন্তু কীরকম যেন উৎসবের তারটা ছিঁড়ে গেল।
অনলাভ। তারপর?
সঞ্চারী। তারপর আর কী? বাড়ি ফেরার পথে আমি ভাবছিলাম...
বাবা। তোকে একটা কথা বলি সন্তু, শোন্। অনলাভ আমাদের বাড়িতে অতিথি, সম্মানীয় অতিথি। তুই কি ওকে অপমান করতে চাইছিস? তোর বন্ধুর বিয়েতে কে এই অসভ্যতাটা করেছিল আমি জানিনা, কিন্তু তুই কি মনে করিস আমাদের বাড়ির অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে এ ধরণের কোন লোক থাকবে?
সঞ্চারী। কিন্তু আমি তো থাকব বাবা। আমাদের বাড়ির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে হয়তো সবাই হবে মার্জিত, ভদ্র; কোন্ কথা কোন্ পরিবেশে বলতে নেই তা হয়তো জানা থাকবে তাদের সবায়েরই, কিন্তু মন? মনে-মনেও তারা কেউ এ-কথা ভাববে না এমন গ্যারান্টি তুমি দিতে পার? আর ভাববে না-ই বা কেন? সত্যি-সত্যিই তো আমার দিদি বা আমি দৃষ্টিহীন। ঐ যে অনলাভদা বললো, অঙ্ক বুঝতে গিয়ে দিদির চোখে-মুখে একটা আশ্চর্য উত্তেজনা দেখতে পেত অনলাভদা, কথা শুনে বোঝা গেল সেই উত্তেজনাটা অ্যাডমায়ারও করতো সে, কিন্তু দিদি কি তখন অ্যাডমায়ারিং অনলাভদার চোখটা দেখেছে নিজে? কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণে বুঝেছে নিশ্চয়ই ― যেটাকে অনলাভদা বলল হৃদয় বা বুদ্ধি দিয়ে দেখা ― কিন্তু অবয়ব হিসেবে দিদির চোখ তো দেখেনি অনলাভদার সেই মুগ্ধতা।
অনলাভ। আমার মনে হয় সন্তু, তোমার কথাটা আমি...
সঞ্চারী। না না অনলাভদা, আমাকে বলতে দাও, আমাকে শেষ করতে দাও কথাটা। আসলে আমি একটা অন্য কথা বলতে চাইছিলাম। রিচুয়ালগুলোকে কি আমরা সামান্য বদলিয়ে দিতে পারিনা বাস্তবতাকে মনে রেখে? বর-কনের ব্যক্তিগত নিজস্বতাকে সম্মান দিয়ে? ধর, যাগযজ্ঞ হলো, সাত পাকে ঘোরানো হলো কনেকে, সব বিয়েতেই হয়, কেউ বোঝেও না, বোঝার চেষ্টাও করে না, এই বিয়েতেও হলো। তারপর শুভদৃষ্টির বদলে হলো শুভস্পর্শ, বর-কনের বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন সাক্ষী রইল সেই শুভস্পর্শের, কনের একটা হাত ধরে বর সেই হাতটা বুলিয়ে নিল নিজের মুখে, আর তারপর নিজের হাতটাও বোলালো কনের..., তুমি কী বল বাবা?
অনলাভ। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত সন্তু, আমাকে একটু সময় দাও তোমরা, আমি আমার মাকে...
অন্তরা। তোমরা একটু চুপ করবে? দয়া করে চুপ করবে সবাই? কথাটা তো হচ্ছে আমার বিয়েকে উপলক্ষ করে। আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে, তাই না? শোন অনলাভ, এই বিয়ে যদি হয়, তাহলে তা ওয়েডিং রিচুয়ালের সব রকম রাইট্স্ মেনেই হবে। আমার বা সন্তুর কেমন লাগল, বা এমনকী আমাদের বাবারও কেমন লাগল সেটা জরুরি নয়। সন্তু আর আমি তো অন্ধ, অন্ধ হয়েই জন্মেছি, আর আমাদের বাবাও তো দুটি অন্ধ মেয়ের বাবা, আমরা অনেক কিছু মেনে নিতে শিখেছি সেই প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু অনলাভর মা'র কথা কেউ ভেবেছ তোমরা? তাঁর ছেলে তো অন্ধ নয়, তিনি তো জন্মান্ধের মা ন'ন, তিনি তো কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর একমাত্র ছেলেটি একটি অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করে অকারণে অন্ধত্বের যাবতীয় অপমান মেনে নিতে বাধ্য হবে। তিনি তো কখনও ভাবেননি ছেলের সূত্রে এই অপমানের গ্লানি ভাগ করে নেওয়াটা তাঁরও একরকমের নির্বন্ধ ছিল। তিনি অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছেন, বহু কষ্টে, অনেক লড়াই করে তাঁর একমাত্র ছেলেকে মানুষ করেছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে। আমরা মুখে বলতে চাই বা না চাই, আমরা তো সবাই মনে মনে জানি এই পৃথিবীর, এই সমাজের বহু মানুষ, এমনকী তাঁর নিকট আত্মীয় বহু মানুষও, তাঁর আজকের সুখের দিনে সুখী নয়। এই অবস্থায় আমার অন্ধত্বের বোঝা আমি তাঁর ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না বাবা। তুমি হয় তো একটু অবাক হচ্ছ বাবা, আমার মুখে এই সব কথা শুনে। ছোটবেলা থেকেই মা আর তুমি আমাদের যুক্তিবাদী হতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে সন্দিহান হতেই শিখিয়েছ। আর এই শিক্ষাই এখনও আমার জীবনে সত্য। কিন্তু অনলাভর মা? তিনি তো আর পাঁচটা বাঙালি ঘরের বধূ হিসেবে অন্যরকমের শিক্ষা আর বিশ্বাসে ভর করেই সারাটা জীবন কাটাচ্ছেন। আমাদের কী অধিকার আছে তাঁর জীবনটা উল্টেপাল্টে দেবার?
অনলাভ। কিন্তু অন্তু...
অন্তরা। একটু চুপ কর অনলাভ, একটু চুপ কর প্লীজ। আমাকে বলতে দাও, তারপর তোমার যা বলার আছে বোলো তুমি। বাবা, তুমি তো জান অনলাভ য়্যুনিভার্সিটির সেরা ছাত্র। নিজের যোগ্যতায় সে আজ য়্যুনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। ওর মা'র চিন্তাভাবনা এখন কীরকম হবার কথা? এবার ছেলের একটা বিয়ে দেব ছেলের যোগ্য কোন মেয়ের সঙ্গে, তারপর আমার কাজ শেষ, এখন শুধু সুখভোগ। সেই ছেলে যদি একদিন মায়ের কাছে গিয়ে বলে, আমি একটি অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করব মা, কলেজে আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়ার, তাহলে তার মা'র মনের অবস্থাটা কী হয় ভাবতে পার? আমাকে যেদিন ওর মা'র কাছে প্রথম নিয়ে গেল অনলাভ, তিনি আমায় কী বললেন জান? বললেন, তুমি আমার অনুর পছন্দের বউ, আমারও পছন্দের। তারপর আমার কপালে একটা চুমু খেলেন। ব্যস, আর কিছু নয়। উনি নারকোল নাড়ু করে রেখেছিলেন, আমরা খেলাম, চা খেলাম, এটা-ওটা গল্প হলো, আমি চলে এলাম। আমাকে অন্তত একবারের জন্যেও বুঝতে দেন নি যে, যে পুত্রবধূর স্বপ্ন উনি সারা জীবন ধরে দেখেছেন, সে আমি নয়, আমি হতেই পারে না। বাবা, তুমি কি বলবে, সেই মা যদি অযৌক্তিক ভাবেও বিয়ের প্রতিটি ছোটখাটো নিয়ম-লোকাচারও আমায় মানতে বলেন ওই একটা দিনের জন্যে, আমি কি তাঁর অবাধ্য হব?
বাবা। হবি না মা, একেবারেই অবাধ্য হবি না। আমি নিজে তো নাস্তিক, একেবারেই নাস্তিক, আর তোদের শিখিয়েওছি সেরকম, কিন্তু পরমতসহিষ্ণু হতেও কি শেখাইনি তোদের? আর ইনি, অনলাভর মা, ইনি তো তোর পরও ন'ন!
পরের পর্বে সমাপ্য...
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।পর্ব ১ | পর্ব ২ - আরও পড়ুনজালিকাটু - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়আরও পড়ুনদিলদার নগর - ২০ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনটক ঝাল মিষ্টি - Anjan Banerjeeআরও পড়ুনউৎসব সংখ্যা ১৪৩২ - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 স্বাতী রায় | 117.233.***.*** | ২২ মার্চ ২০২৫ ২৩:৫৩541843
স্বাতী রায় | 117.233.***.*** | ২২ মার্চ ২০২৫ ২৩:৫৩541843- পড়ছি
-
দ | ২৩ মার্চ ২০২৫ ১০:৫১541849
- একটা অন্য দৃষ্টিকোণ পেলাম।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












