- বুলবুলভাজা পড়াবই সীমানা ছাড়িয়ে

-
বাদানুবাদ
সৈয়দ আযান আহমেদ
পড়াবই | সীমানা ছাড়িয়ে | ০৬ আগস্ট ২০২৩ | ১৪২৮ বার পঠিত 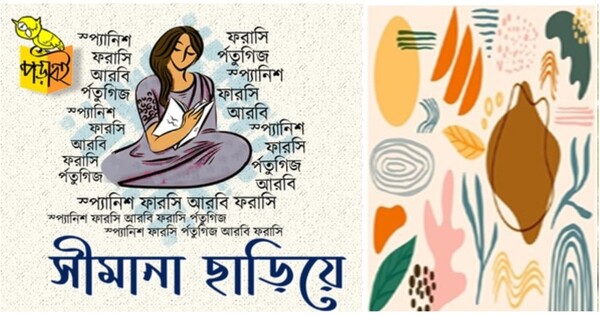
ঈশ্বরের মেজাজ গেল বিগড়ে। মহাপ্লাবনের পর নোয়ার বংশধরেরা শিনার দেশের সমভূমিতে সবে আস্তানা গেড়েছে। থিতু হয়েই তাদের আহ্লাদী মনে এক দুঃসাহসী স্বপ্নের চাগাড় - এমন এক নগর পত্তন করা চাই, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে একটি স্বর্গচুম্বী মিনার। আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গচুম্বী, কারণ তার শীর্ষ স্বর্গের ভূমি ফুঁড়ে যেন পরলোকের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে। ঈশ্বর গেলেন খাপ্পা হয়ে। এত কিসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিসের এত হম্বিতম্বি। সবে তো মহাপ্লাবন থেকে খাবি খেয়ে উঠল তোমার চোদ্দ গুষ্টি।মানুষের শখও ষোলো আনা। ঈশ্বরের নুন খেয়ে কোথায় তাঁর গুণ গাবে, তা না, তাঁর কর্তৃত্বকেই খুন করতে চায়। বেপরোয়া টক্কর নিতে চায় সরাসরি। হিব্রু জেনেসিস বলে, মানবজাতি তখন ছিল ঐক্যবদ্ধ, আর তার ভাষাও ছিল এক। ভাষার অমন আশাতীত একাকার ছিল বলেই ওই বেয়াড়া আবদারের স্পর্ধা দেখায় তারা। খড়্গহস্ত ঈশ্বর আর দেরি করেন নি। খড়গের কোপ নয়, নেমে এলো এক ধুরন্ধর দৈবিক মোচড়। মানবজাতির নিবিড় আঁতাতকে চুরমার করতে, তিনি ভাষাকেই দিলেন টুকরো টুকরো করে। মানুষ তার জিহ্বার বিভ্রান্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর আনাচে কানাচে, ভেঙে গেল গোষ্ঠীতে। পড়ে রইল মিনার, উপহাসের পাত্র হয়ে। ঈশ্বর মুচকি হেসে সেবারের মতো ক্ষান্ত হলেন।
টাওয়ার অফ ব্যাবেলের উত্থান কে রুখে দেওয়াতে লাভ একটাই হল - ভাষার বল্গাহীন বিবর্তন ছুটে চললো টগবগিয়ে। ব্যাবেলের সেই গল্প নতুন করে আঁচড় কাটে নোয়াম চমস্কির ইউনিভার্সাল গ্রামারের কথা পড়লে। মানুষের কথ্য ভাষাকে চমস্কি সেভাবে তোয়াক্কাই করেন না, তাঁর ধারণা মানুষের আসল লব্জ নির্বাক বসে রয়েছে তারই মস্তিষ্কে - নিটোল, সুশৃঙ্খল ব্যাকরণের নিয়ম মেনে, যাকে বলা হয় ইন্টারনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। যার আধারেই তৈরি হয় আমাদের মুখের ভাষা, জিভের উচ্চারণ। চমস্কি বিশ্বাস করেন এই মুহূর্তে এলিয়েন সভ্যতা উড়ে এসে জুড়ে বসলে তারা বেহদ্দ অবাক হয়ে বলবে, আরে! মানুষের ভাষা আসলে তো একটাই। বাকিগুলো তো ডায়ালেক্ট, উপভাষা; ভূগোলের মারপ্যাঁচে খামোখাই আঞ্চলিকতার কচকচানি।চমস্কি এর সপক্ষে যুক্তি দেন,মানুষের মুখের বুলি, সে ল্যাটিনই হোক কি বাংলা, ইন্টার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজের অন্তর্নিহিত কাঠামো থেকে তার সমান বখরা রয়েছে। দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের জবান আসলে সেই আদিম ব্যাকরণেরই ক্রীতদাস। সে বদলেছে কেবল সামাজিক, প্রাদেশিক রীতি নীতির প্যাঁচপয়জার ফাঁদে পড়ে। উগান্ডার শৈশবকে পশ্চিম বাংলার অবৈতনিকে ভর্তি করিয়ে দেখুন, সে গড়গড়িয়ে বাংলা বলবে, আঞ্চলিক টান সমেত। এ শুধুই শুনে শেখা নয়, পড়ে জানা নয়, এ হল ভাষাকে জিনের ক্যানভাসে এঁকে দিয়ে যাওয়া বিবর্তনের খেলা।
উৎফুল্ল মানুষ কোমর-বেঁধে নেমেছিল ভাষার মধ্যেকার এই আদিম খোলনলচের সুলুকসন্ধানে। সে দেখলো ভাষা যদি একই কাণ্ডের গজিয়ে ওঠা ডালপালা হয়, তাহলে অনুবাদের একটা সার্বজনীন সূত্র তার মূলের গভীরে নিশ্চয় কোথাও লোকানো থাকবে! সেই কষ্টকল্পিত ভাবনার একটা উদ্ভাবনী দোআঁশলা ফসল হল - মেশিন ট্রান্সলেটর। তবে মানুষ তো, ভাষা নিয়ে তার কপাল বরাবরের খারাপ। যন্ত্র খাড়া হয়েছে একটা, তবে তাতে অনুবাদের দেবমন্ত্র এখনো ফোঁকা যায় নি। যন্ত্রকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে যারা, তারাই তো ভাষা নিয়ে হরদম গোলমাল করেন। এই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুবাদ করতে গিয়ে উইলিয়াম রাদিচি 'বনমালী' চরিত্রটার লিঙ্গ পাল্টে কেলেঙ্কারি বাধালেন। তার সাফাই হল, উপমহাদেশের বেশিরভাগ মহিলাদের নাম 'ঈ' স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হয়। তাই বনমাল + ঈ। সুতরাং তিনি নার + ঈ। তবে এতে আটকায়নি কিছু, মেশিন ট্রান্সলেশন আসাতে বরং জবাবদিহি ছাড়াই অনুবাদের কেমন হরদম আড়ংধোলাই চলছে, চাহিদার সাথে জোগানের পুরনো আত্মীয়তা বজায় রেখে ফোঁপরা অনুবাদকদেরও তেমন ঠাসবুনুনি ভিড়। যোগ্যতা অবশ্য আজকাল কোনও মাপকাঠিই নয়, বুক জোড়া আত্মবিশ্বাসটাই আসল রাজা। সাহস করে নামতে পারলে বাকিটা গুগল ট্রান্সলেটর দেখে নেয়। দুর্বোধ্য অনুবাদে ন্যূনতম দায়বদ্ধতা কারোর না, বইবাজারের এই ভরা বসন্তে, প্রকাশক দিব্য ঘুমন্ত, অনুবাদক তো চির ক্লান্তই, চাঙ্গা কেবল অনুবাদ যন্ত্র! দিতে যা দেরি, মুহূর্তে বঙ্গানুবাদ। হ্যাঁ, বাংলা অক্ষরমালা থাকবে ঐটুকুই নিশ্চিন্তে বলা যায়, বাকিটা কপালজোরের হিসাব নিকাশ। বললাম, "life is full of problems that are, quite simply, hard". গুগল ট্রান্সলেটরে খাবি খেয়ে দাঁড়াল: "জীবন এমন সমস্যায় পূর্ণ যেগুলো, বেশ সহজ, কঠিন।" চমৎকার! কাজেই সাড়ে তিন পাতার আড়মোড়া ভেঙে অনুবাদ উপন্যাস চলল সেলফের সব চেয়ে দুরূহ কোনায় একটু গা গড়াতে। তারপর ... তারপর মরণ ঘুম! ক্রেতা-কাম-পাঠক গেল ভুলে ওই শিরোনামের কোনও বইকে গাঁটের কড়ি দিয়ে বড় সাধ করে আপ্যায়ন করেছিল সে।
পাঠকদের অবশ্য অনুবাদ আসক্তির পিছনে একটা ব্যাখ্যা রয়েছে, আর অশেষ ধৈর্যের সমর্থনে আরেকটি দীর্ঘ ইতিহাসও। ছেলেবেলা থেকে একটা আনুমানিক থিওরি শুনছে, সহজপাচ্য কক্ষনও সাহিত্য শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। কাজেই সে তার মতো করে বুঝেছে, আঁতেল হতে গেলে সর্বদাই জনপ্রিয় জিনিসের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হয়। লোকের খুব মনে ধরা, বাজারে দ্রুত কাটতে থাকা, নয়তো বক্স অফিসে বাজিমাত করা সব মালপত্রই আদপে যে নিম্ন মেধার দ্বারা এবং নিম্ন মেধার জন্যই - এই উপপাদ্যকে সে বেদবাক্য জ্ঞান করে মুখস্থ রাখে। তাই মনের ভুলে ছয় মাত্রার ডবল দাদরার পা নেচে উঠলে ভিতরে ভিতরে ইজ্জত খোয়ানোর শঙ্কা হয়, বিলায়েতে মাথা দোলানো যেতে পারে। তার মাথা-কোটা বিশ্বাস, সমস্ত গভীর বিষয়ই প্রথমটায় মাথা ছুঁয়ে ট্যানজেন্ট হয়ে বেরিয়ে যায়, ব্যাপারটা গুলে খাওয়াতে কিছু সাংস্কৃতিক পেশাদার কাগজ-কলম-বক্তৃতা মজুত রাখেন, যাদের নিবন্ধ-কাম-ছাত্রবন্ধু পড়লে তবেই আবিষ্কার করা যায় অমুকের তমুক লেখাটার ওই অধ্যায়ে এতদিন তবে এই গোপন বার্তাটিই ঘাপটি মেরে ছিল - কাণ্ড দ্যাখো! কিংবা ওই সিনেমার সেই দৃশ্যটার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা তবে এই দাঁড়ালো। কাজেই আক্ষরিক অনুবাদে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষতবিক্ষত হওয়াটাকে গুরুপাক আহারের বদহজম জনিত স্বাভাবিক লক্ষণ ভেবে সে গায়ে পুলক মাখে। যন্ত্রের অপারগতাকে, অনুবাদকের অজ্ঞানতাকে সে সাহিত্যের অগাধ সৃজনশীলতা বলেই নাগাড়ে গোলায়। ভাষান্তরের সীমাবদ্ধতাকে তার সন্দেহ হয় শিল্পের কোনও চোরা সংকেত নয় তো!
সূক্ষ্মতা বা গভীরতার সাথে জনপ্রিয় ও সহজবোধ্যর চির-কোন্দল একেবারে গালগল্প নয়, তবে 'দুর্বোধ্যতার আড়ালে কোনও নিশ্চিত শৈল্পিক ব্যঞ্জনা' - এই একগুঁয়ে সংজ্ঞায় মস্ত গোঁজামিল। কাজেই যান্ত্রিক অনুবাদের ছত্রে ছত্রে নিষ্প্রাণ ভাষান্তর যতই ঘুমের অব্যর্থ ওষুধ হোক, জিভ ফসকিয়ে আজ অবধি পাঠক রা কাড়ে নি, পাছে লোকজন ঠারেঠোরে তাকেই না আকাঠ ঠাউরে দেয়।পাঠক সত্যিই ন্যাড়া হলে, বেলতলাকেই সান্ধ্য ভ্রমণের ফিক্সড স্পট বানাত। কারণ পরের বার বইমেলায় আবার গুচ্ছের অনুবাদ কিনে ঘরে তোলাটা তার একপ্রকারের নিশ্চিত ভবিতব্য।দুর্বোধ্যকে কালো পতাকা দেখাতে গিয়ে তার এই নিত্য হাত কচলানি শুধুমাত্র অনুবাদের ক্ষেত্রেই বরাদ্দ, তার আরও একটা কারণ অনুবাদে দেশী নামের সাথে আরেকটা বিদেশি নাম জড়িয়ে থাকায় ঔপনিবেশিক মানসিকতা প্রথম প্রেমের মতই একটু টনটনিয়ে ওঠে। যা দুর্বোধ্য গুরুপাক তা সৃজনশীল ও নান্দনিক - এই নাকউঁচু মনোভাবের নোয়াপাতি ডিভিডেন্ড কামায় ডামাডোলের বাজারে পঙ্গপালের মত উড়তে থাকা অনুবাদক, যে নামমাত্র পারদর্শিতা, এবং একটা ভাসা-ভাসা সংকল্প না রেখেও অনুবাদের দোকান দিয়ে ফেলে। আর তাই ডজন খানেক বিদেশি ডিম, দেশী খোলায় পেড়ে ফেলার পরেও অনুবাদকের এই ন্যূনতম উপলব্ধিও আসে না যে, শব্দের শুষ্ক রূপান্তর আর যাই হোক কোনোভাবেই অনুবাদ সাহিত্য নয়। সময় ও একাগ্রতার পুরোটাই গুগল পাদদেশে নিঃশর্ত সমর্পণ করলে, বিদ্যে বুদ্ধিও তারই চরণ তলে একচেটিয়া সঁপে দিতে এতটুকুও কার্পণ্য না দেখালে, অনুবাদের দীনতা আমাদের অযাচিত নিত্য সঙ্গী হবে, খুব আশ্চর্যের কি?
বর্ণমালা যদি হাতেগোনা কিছু চিহ্ন হয় তবে ভাষা সেই সীমিত চিহ্নের উপর বয়ে চলা এক উচ্ছ্বসিত বিপুল স্রোতধারা। মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন মানুষকে খুঁটি জুগিয়েছে অভিব্যক্তির এই বিস্ময় ধারাকে তিলেতিলে গড়ে পিঠে নিতে। নিজের তাগিদে অবোধ শিশুও তার ছেঁড়াখোঁড়া নগণ্য শব্দভাণ্ডারকে যে চাতুর্যের সাথে কাজে লাগায় তার ন্যূনতম ধারণাও কোনও সুপার-কম্পিউটারকে চিরতরে হ্যাং করে দিতে পারে। সদ্য অঙ্কুরিত শৈশব যতই আধো আধো বোলে হোঁচট খাক,তার বয়স কিন্তু লক্ষ বছরের মানব-বিবর্তনের সমান, সুতরাং তার কগনিটিভ স্কিল সুপার-কম্পিউটারকে পদে পদে তাচ্ছিল্য করে ঘোল খাওয়াবে, সেটাই বরং প্রত্যাশিত। মেশিনের মূল প্রতিকূলতা হল - তার বোধ বা বিচার শক্তির কোনও জন্ম বা জৈবিক বিবর্তন নেই, সেখানে মানুষ সততই বিবর্তনশীল, এমনকি ভাষাও। ভাষা নির্দ্বিধায় তার উপকরণ সংগ্রহ করে তারই ভৌগোলিক পরিমণ্ডল থেকে। সামাজিক বাতাবরণের উত্থান পতনের ফাঁকফোকরে কখন কায়দা করে আদায় করে নেয় তার নিজস্ব চলনের রীতি রেওয়াজ। লোকগাথা, মূল্যবোধ, নীতি- নৈতিকতার জোরালো প্রতিফলন ঘটবে তার ছত্রে ছত্রে। সংস্কৃতিও তার নিজস্ব সব ঐতিহ্য, যাবতীয় পরম্পরাকে উজাড় করে দেবে ভাষার নির্বন্ধে। আবেগ, অনুভূতির কতশত নতুন নাম হুড়মুড়িয়ে নেমে আসবে শব্দের আনাচে কানাচে। আর তাই অনুবাদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিকও হল ভাষার সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা।
তর্জমাকে যতই নিখুঁত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চলুক, ভাষার সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে অচ্ছুৎ করে রাখলে, তা ভস্মে ঘি ঢালারই নামান্তর। সেক্ষেত্রে অনুবাদ গল্প-কবিতাতে মনোনিবেশ করা দূরস্থান, বরং তা থেকে শতহস্ত দূরেই আমরা স্বস্তির শ্বাস নেব। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা কেমন বেসুরো আচরণ করতে পারে তার একটা প্রাঞ্জল নমুনা: জাপানিদের চোখে পশ্চিমীরা বড্ড রূঢ় স্বভাবের,সবজান্তা, বদমেজাজি, বেশ অহংকারী। এদিকে স্বভাব বিনয়ী জাপানিরা আবার পশ্চিমাদের ভাবনায় অতিরিক্ত মুখচোরা, নড়বড়ে প্রকৃতির, একদম স্মার্ট নয়, একটু ক্যাবলা গোছের। এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতার ঘেরাটোপকে ধূলিসাৎ করতে অনুবাদককে কী অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করতে হয়! ভাষার সংস্কৃতি এবং তার ব্যাকরণের মারপ্যাঁচকেই শুধু গুলে খেলে চলে না, বুঝতে হয় ওই ভাষার বাচনভঙ্গির ওঠাপড়া এবং মেজাজ, স্থানীয় কথকদের অভ্যাস-বদভ্যাস, এমনকি মুদ্রাদোষও। অনুবাদককে নির্ভেজাল শ্রোতা হতে হয় সর্বক্ষণের, আজীবন ব্রত থাকে চূড়ান্ত মনোযোগী পাঠক হওয়ার।পৃথিবীর যে কোনও ভাষার সাংস্কৃতিক পটভূমি বন্ধক থাকে তারই বাগধারার কাছে। পেশাদার অনুবাদককে বাগধারাগত খুঁটিনাটি নিয়েও সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হয়। তাছাড়া লক্ষ্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট শব্দের অভাব তো রয়েছে-ই। কিছু শব্দ হারিয়ে যাবেই অনুবাদের জাবদা খাতায়। যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়, সেখানে উপযুক্ত বিকল্প খুঁজতে হয় সাম্যতার শর্ত মেনেই, প্রয়োজন হতে পারে সৃজনশীল কল্পনার নিক্তিমাপা আঁচড়। তবেই তো অনুবাদে উৎকর্ষতা আসবে। এককালে রাশিয়ান অনুবাদ সাহিত্যকে ঠিক এই কারণেই অগাধ ভালোবাসা দিয়েছিল বাঙালি, সকল বৈপরীত্য উপেক্ষা করেও তাদের মনে হয়েছিল বিভূতিভূষণ আর দস্তয়ভস্কির দূরত্ব কেবল এপাড়া-ওপাড়া। রাশিয়া বোধহয় নতুন কোনও বৃহত্তর বাংলা।
অবশ্য এসব প্রত্যাশার ছিটেফোঁটাও গুগল অনুবাদকের কাছে রাখতে নেই। নিষ্ফলা যন্ত্র-অনুবাদের তর্জন- গর্জনই সার। তাকে “a large bulk of content” এর অনুবাদ করতে দিলে সে নিমেষে উত্তর দেয় “কন্টেন্ট একটি বড় বালক”। তাতে অবশ্য নতুন করে গৌরবহানির কিছু ঘটে না; অনুবাদের আসরে নেমে তার ধারাবাহিক নাকাল হওয়ার এই বেইজ্জতি খতিয়ানটা সুদীর্ঘ। গুগলকে মানুষ করতে সব পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম যায়, কারণ সিলিকন সর্বস্ব যন্ত্র শুরু থেকেই বিস্তর অবহেলা করেছে ভাষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে। শব্দের প্রেক্ষাপট সে যাচাই করতে চেয়েছে আপাদমস্তক উদাসীনতা নিয়ে। বাগধারার অর্থ খুঁজতে গিয়ে তার প্রবল গড়িমসি আর তীব্র অনীহা - এ সবই অবশ্য তার অপারগতা বটে। প্রসঙ্গ এবং উপলক্ষ এই দুইয়ের সম্ভার যে আদপে অনুবাদের প্রধান চাবিকাঠি এ শিক্ষা তাকে দেবে কে! প্রেক্ষাপটকে মুঠিবন্দি না করা অবধি, ভাবার্থের নির্যাসকে শব্দ বন্দি করা যায় না, পদেপদে শিশুসুলভ বেসামালই তার নিয়তি - একথা বুঝিয়ে দেবার কোনও প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ হয় কী! ওদিকে যান্ত্রিক অনুবাদের জীবনপণ উদ্যোগের পুরোটা জুড়েই রয়ে যায় শব্দকে 'ডিকোড' করার মিথ্যে শোরগোল। যেন ভাষা কোনও দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, আর শব্দ হল তার সমাধান সূত্র। তাই অ্যালগরিদমের ছাঁচে উপুড় করে, সিনট্যাক্স-সিমানটেক্সের কল ঘুড়িয়ে পেশাই করেই দিবাস্বপ্ন দেখা যায় এ বড়ই নির্ভুল মার্জিত অনুবাদ হল। পাঠক দেখলেন যা হল তা অন্তঃসারশূন্য, সারবত্তাহীন শব্দকল্পদ্রুম।
শব্দ অঙ্ক নয় যে, হেনস প্রুভড লিখে দাসখত দিতে হয়। ঠিক ভুলের সংকীর্ণ হিসেব যেদিন অনুবাদের গুণগত মান নির্ধারণ করবে সেদিন সাহিত্যে হয়তো তার কানাকড়ি পরিমাণ প্রাসঙ্গিকতাও হারাবে। দুঁদে ট্রান্সলেটরও বেশক জানেন - ত্রুটি বর্জিত, পূর্নাঙ্গ নির্ভুল নিটোল অনুবাদ খানিকটা গল্প গাছার ইউটোপিয়ায় মতই। কাজেই ভাষান্তরে তিনি হাত দেবেন সব বাধ্যবাধকতা মেনে, লোকসানের অঙ্ক কষে। 'কতশত গভীর অনুভূতি, বিবৃতিও হারিয়ে যায় অনুবাদের দুর্গম অভিযানে' - এই ধারণাকে শিরোধার্য করেই অনুবাদক নিয়ম ভাঙার খেলায় নামবেন। শর্ত থাকবে, কোনও জবাবদিহি না করেই রুলবুককে তিনি ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে পারেন। উড়িয়ে দিতে পারেন শব্দের আবছায়া প্রান্তরে। তুলে নিতে পারেন শব্দ ভাণ্ডারের সব চেয়ে অবাঞ্ছিত অপ্রচলিত কোনও শব্দকেও। তার কলমে নিয়মের অপ্রত্যাশিত ভাঙন নামতে পারে আগাম বলাকওয়া ছাড়াই, খাদের কিনারায় গিয়েও আসতে পারে কোনও শিরশিরে বাঁক, এসবই কিন্তু ঘটবে ভাষান্তরের প্রাসঙ্গিকতাকে বজায় রাখতে, নিজের বিনোদনের জন্য নয়। ভাষা আমরা শিখি না, অর্জন করি। খেলার সঙ্গী হয় সে, মিথ্যের নাছোড় সাক্ষী, নিজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মতো ব্যবহার করি তাকে, সে কখন যেন আমার রিফ্লেক্সের অংশ হয়ে ওঠে। আমি দ্বি বা ত্রি ভাষিক হলেও আমার নাড়া কিন্তু বাঁধা থাকে মাতৃভাষার চৌকাঠে। ‘languages are formed in different landscapes through different experiences’, জানি না কে বলেছিলেন। তবে সত্যি করে বলুন তো, এর আদৌ কোনও বাংলা হয়? নাকি কেবলমাত্র দ্বিভাষিক হওয়ার তাজ্জব বয়দাটা পেশ করলেই নিজেকে অনুবাদক বলে হামেশাই কলার তোলা যায়!
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
দ | ০৬ আগস্ট ২০২৩ ১৬:২৫522169
- ইন্টারেস্টিং লেখা।
 --- | 143.202.***.*** | ০৬ আগস্ট ২০২৩ ২২:২১522172
--- | 143.202.***.*** | ০৬ আগস্ট ২০২৩ ২২:২১522172- আরে চোমস্কিকে আর কেউ সিরিয়াসলি নেয়না। এমনিতেই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এসে প্রমান করে দিয়েছে ওসব ইউজি-টিউজি গাঁজা। চোমস্কিয়ানদের দিন শ্যাষ।
 LLP | 2600:1002:b00b:9e9b:312b:9aff:f0b7:***:*** | ০৭ আগস্ট ২০২৩ ০৪:০৮522178
LLP | 2600:1002:b00b:9e9b:312b:9aff:f0b7:***:*** | ০৭ আগস্ট ২০২৩ ০৪:০৮522178- কম্পিউটেশানাল লিঙ্গুইষ্টিক্সে চমস্কির প্রভাব গুরুত্বপূর্ন।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












