- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
শতবর্ষে সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) : মানুষই জীবশ্রেষ্ঠ, দুঃখ-বঞ্চনা-ব্যর্থতা জয় করে, মানুষই দেবতা হয়ে ওঠে
বিজয়া গোস্বামী
পড়াবই | মনে রবে | ২৩ মে ২০২১ | ৩৪১৮ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) - স্মরণাতীত কালে ফ্যাসিবাদের এমন দাপট এ দেশে দেখা যায়নি। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সেই আশঙ্কাতেই উতলা হয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের স্বরূপের নিরন্তর অন্বেষণে অপরিহার্য তো বটেই, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের যাবতীয় লেখালিখি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়েরও জরুরি হাতিয়ার। শতবর্ষে গুরুচণ্ডা৯-র ‘পড়াবই’ বিভাগের শ্রদ্ধা। রইল তাঁর নিজের সাক্ষাৎকার, কন্যা তনিকা সরকারের স্মৃতিচারণ, বিজয়া গোস্বামী, রণবীর চক্রবর্তী ও কণাদ সিংহ-র তিনটি লেখা।
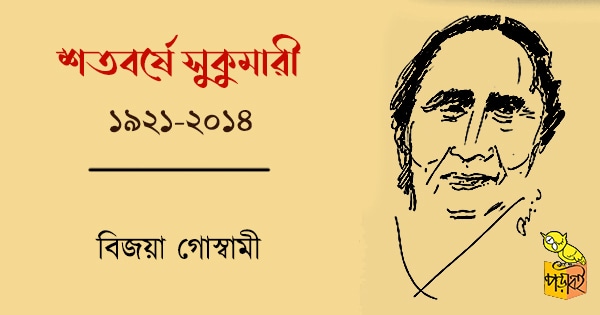 মহাভারত মহাকাব্যের এই সার কথা। সে মহাগ্রন্থের এমনতর পাঠই শিখিয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। এবং শিখিয়েছিলেন প্রাচীন নানা গ্রন্থ যথাযথ পাঠ করে সেগুলিকেই করে তোলা যায় কুসংস্কার ও মিথ্যার প্রবল প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র। লিখছেন তাঁর ছাত্রী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক বিজয়া গোস্বামী
মহাভারত মহাকাব্যের এই সার কথা। সে মহাগ্রন্থের এমনতর পাঠই শিখিয়েছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। এবং শিখিয়েছিলেন প্রাচীন নানা গ্রন্থ যথাযথ পাঠ করে সেগুলিকেই করে তোলা যায় কুসংস্কার ও মিথ্যার প্রবল প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র। লিখছেন তাঁর ছাত্রী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক বিজয়া গোস্বামীসুকুমারী ভট্টাচার্য যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম। সেইসময় থেকে দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল আমার। একসঙ্গে কাজও করেছি ওই সংস্কৃত বিভাগেই। অবসরের পরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। এখন দিদি বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত ১০০ বছর! এটা ভালো ভাবেই জানি, কারণ দিদির আর আমার একই দিনে জন্ম, যদিও ভিন্ন বছরে! ছাত্রাবস্থা থেকে দেখেছি, সাধারণত যেভাবে পড়ানো হয়—মানেটা বুঝিয়ে, প্রশ্ন আলোচনা করে—সুকুমারীদি সে ভাবে পড়াতেন না। বরং ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার উপাদান জোগাতেন, স্বাধীনভাবে ভাবতে উৎসাহ দিতেন। এটা সারাজীবনই তিনি করে গেছেন। তিনি অবসর গ্রহণের পরে আরও বেশি যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সভা-সমিতি, লেখালিখি নিয়ে। আমাকে প্রায়ই বলতেন, “কুসংস্কার ও মিথ্যার একটা প্রবল প্রচার চলেছে! তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়ে যাও! তোমাদের হাতে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হল, তোমাদের জ্ঞান! তোমরা তো প্রাচীন গ্রন্থ পড়েছ, সেখানে কী আছে তাও জান। সেটাই হাতিয়ার করে যুদ্ধ চালিয়ে যাও!” আমি আমার জীবনে সাধ্যমতো সেই চেষ্টাই করেছি, কিন্তু আমার দিনও তো ফুরিয়ে এল—আর এই প্রজন্মে কে এই ভয়ংকর দিন রুখতে চেষ্টা করবে তা জানি না! তাই সুকুমারীদিরই দু-একটা কথা বলছি। বিশেষত তাঁর যে বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা ছিল, অর্থাৎ প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত-রামায়ণ নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন মূল্যায়ন।
সুকুমারীদির প্রিয় মহাকাব্য মহাভারত। যদিও তিনি নিজেই বলেছেন, মহাভারত ঠিক ‘মহাকাব্য’ বলতে যা বোঝায় তা নয়। প্রাচীনকালে মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হত না, বলা হত ‘ইতিহাস’। আজকের ব্যাখ্যায় ইতিহাস মানে history। কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যায় এ হল ‘ইতি হ আস’—অর্থাৎ ‘এরকমই ঘটেছিল’। তাই এখানে কোনো একজন নায়ক নেই, নেই এক চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখানে এত বেশি বৈচিত্র্য আছে যে এক কাঠামোয় সবটা ভরে দেওয়া যায় না। আবার গোটা কাহিনির মধ্যে একত্ব ও সমগ্রতা আছে, যার ফলে বিভিন্ন সময় এই গোটা কাহিনির সংকলন ঘটলেও সমস্তটার মধ্যে এক অখণ্ডতা আছে। তাই নিয়েই কিছু বলার স্পর্ধা রাখছি।মহাভারত আমারও প্রিয়, বোধ হয় এই কারণেই যে এখানে সব চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক। তারা সবাই দোষে গুণে মানুষ—এক একটি খুদে ভগবান নয়! রামায়ণে রাম হলেন ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ বা আদর্শ পুরুষ, যার থেকে উচ্চতর কেউ বা কিছু হতে পারে না! অন্য চরিত্রগুলিও এক একটি আদর্শের রূপায়ণ—সীতা সতীত্বের, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমের, হনুমান প্রভুভক্তির ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারতে সেরকম আদর্শ বড়ো একটা দেখি না! সুকুমারীদি বলতেন, “মহাভারতের চরিত্রচিত্রণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটিকে এককথায় বলা যেতে পারে বাস্তবানুগতা; জীবনে যেমন, মহাভারতেও তেমনি, অবিমিশ্র ভালো বা অবিমিশ্র মন্দ চরিত্র নেই। দুটি মাত্র ব্যতিক্রম: বিদুর ও শকুনি; যেমন জীবনেও এমন ব্যতিক্রম হয়তো বা লক্ষে দু-একটি দেখা যায়। নায়কের ভূমিকায় আমরা হয়তো নিজের অগোচরে অবিমিশ্র ভালো চরিত্রই আশা করি; কিন্তু মহাভারতে তেমন চরিত্র নেই। না, যুধিষ্ঠিরও নয়” (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, পৃ: ৮৬)। যুধিষ্ঠিরকে গ্রন্থকার সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সব কাজ নিশ্চয়ই খুব নীতিবোধের পরিচয় দেয় না। প্রথমত তিনি প্রবল দ্যূতাসক্ত—যাকে বলে জুয়াড়ি! ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ব্যসন! দ্বিতীয়ত, তাঁর কি অধিকার ছিল, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী দ্রৌপদীকে একক ভাবে বাজি রাখার! দ্রোণাচার্যকে ডাহা মিথ্যা কথা বলে তাঁকে অস্ত্রত্যাগ করানো তো প্রত্যক্ষভাবে মিথ্যাচার! কিন্তু এটাই তো মানুষের ধর্ম! কেউ সর্বগুণসম্পন্ন হয় না, তাই যুধিষ্ঠিরও ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে গেছেন। তিনিও আমাদের সাধারণ মানুষের দলেই পড়েন! এরকম সব চরিত্র সম্বন্ধেই বলা যায়। “আবেগের সংবেদন সহজে চরিত্রগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য)।
মহাভারতের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে সব প্রধান চরিত্রের মধ্যেই দ্বিধা দেখা যায়। সেখানেও ব্যতিক্রম বিদুর ও শকুনি—একজন নিছকই ভালো, অন্যজন নিছকই মন্দ! তাই তারা কোনো দ্বিধার সম্মুখীন হয় না—তাদের সামনে সোজা পথ! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত! শেষ পর্যন্ত তিনি জেনেশুনেই অন্যায়ের পক্ষে গেছেন, তাঁর নৈতিকতা পরাজিত হয়েছে। গান্ধারী এই দ্বিধার মধ্যে পড়েননি, আগাগোড়া ধৃতরাষ্ট্রকে এবং নিজের পুত্রদের অন্যায়ের পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিষেধ কেউ শোনেনি! কর্ণ মহাবীর এবং দাতা হয়েও নিজের জন্মসত্ত্বে হীন পরিচয়ের কারণে যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চনার ক্ষোভ কোনোদিন ভুলতে পারেননি। আর ভীষ্ম তো আগাগোড়া ‘ট্রাজিক নায়ক’—তিনি অনেক চেষ্টা করেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ রোধ করতে পারেননি, চোখের সামনে দেখেছেন নিজের বংশের উত্তরপুরুষদের ধ্বংস! দ্রৌপদীর কথায় নাকি তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল! কিন্তু যুদ্ধের যে পরিণাম, তা কি তিনি চেয়েছিলেন, না কোনোদিন চাইতে পারেন! যুদ্ধশেষে দেখা গেল, দ্রৌপদীর দুই ভাই মৃত, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই! তারপর আর রাজ্যের কী মূল্য থাকতে পারে তাঁর কাছে!
এর থেকে আর-একটি বৈশিষ্ট্য চোখের সামনে আসে—মহাভারতের চরিত্রেরা কেউই যা চেয়েছেন তা পাননি, যেভাবে চেয়েছেন, যখন চেয়েছেন, সেভাবে তা পাননি, এবং সে সময়ে পাননি। “স্বল্প সুখভোগের পরেই দুঃখের ছায়া নেমে আসে প্রত্যেকটি নায়কের জীবনে। কারণ, মহৎ কাব্য সুখ দিয়ে সৃষ্টি হয় না, সুখে জীবনজিজ্ঞাসা নেই। এবং এই জীবনজিজ্ঞাসাতেই কাব্য প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করে, সমকালকে অতিক্রম করে সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের কাছে কথা বলতে পারে।’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য)
এই কথাটা একটাই: জীবনের অর্থ কী? কেন বাঁচি আমরা? জীবনকে অর্থবহ করে তোলাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ! যে যতটা এই দায়িত্ব পালন করেছে, সে ততটাই সার্থক! মহাভারতে অমরত্বের এই লক্ষণই মেলে—
দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে।। (৩/১৯৮/১৩)
পুণ্যকাজ বা সুকৃতির যশোধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে
সে শব্দ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই পুরুষ পুরুষ বলে অভিহিত হয়।।
‘‘শুভকাজ, মানুষের মঙ্গলকর কাজের দ্বারাই মানুষ অমরত্ব লাভ করে, এবং সে পুণ্য বা শুভকর্মের স্মৃতি যতদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ততদিনই শুভকারী অমর।’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য)
এরপরে সুকুমারীদি দেখিয়েছিলেন, মহাভারতে সব প্রধান চরিত্রগুলিই ব্যর্থকাম, যে যা চেয়েছেন, কেউই তা পাননি, বরং যে পথে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন, তাতে করে ধ্বংসই ত্বরান্বিত হয়েছে, ভালো কোনো ফল হয়নি! দুর্যোধনের একরকম কামনা ছিল, তা তিনি পাননি—হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিষ্কণ্টকে তাঁর হাতে আসেনি, উপরন্তু প্রবল পরাজয়, শেষ সময়ে অন্যায় যুদ্ধের ফলে মৃত্যু, এই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। যুধিষ্ঠির ‘ধর্মপুত্র’ হয়েও মিথ্যাভাষণের আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন, রাজ্যলাভ করলেও সহস্র সহস্র মানুষের হত্যায় তিনি বিপর্যস্ত! এভাবে সব চরিত্রের ভাগ্যেই বিফলতা জুটেছে। ভীষ্ম, যিনি সংসারে শান্তি আনার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেলেন, তিনি পদে পদে বিফল হলেন, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে দেখলেন, তাঁর সাধের কুরু বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তাই ভীষ্মের শরশয্যার রূপকে আমরা দেখি, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তার শেষ জীবনের অসহায়তা, দেশনেতার সামনে তাঁর আদর্শ ধুলোয় লুটিয়ে যায়, শরশয্যা ছাড়া একে আর কী বলে?
কিন্তু এত দুঃখ, এত বেদনা, এত বিফলতার মধ্যে মহাভারতের অন্ত হয়নি। তার মধ্যেই আশার দিকদর্শন হয়েছে, কালো মেঘের মধ্যে দিয়ে এক ঝলক সূর্যালোক এসেছে। মহাভারতের স্ত্রীপর্বে বিদুর একটি রূপক শোনাচ্ছেন: গভীর অরণ্যে এক ব্রাহ্মণ একটি কূপে পড়ে গেছে; পড়ার সময় একটি লতা ধরে সে মাথা নীচের দিকে, পা উপর দিকে করে কোনো রকমে ঝুলে আছে। কুয়োর দিকে এক মহাগজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, এদিকে যে লতা ধরে এই ব্যক্তি ঝুলে আছে, ইঁদুরে তার মূল কাটছে। আবার নীচে কুয়োর ভিতরে এক মহাসর্প! এই অবস্থায় ওই লতার পুষ্পিত শাখা থেকে একটি মৌচাকও ঝুলে আছে, মৌমাছিরা আনাগোনা করছে, আর ওই মৌচাক থেকেই বিন্দু বিন্দু মধু ওই হতভাগ্যের মুখে ঝরে পড়ছে! তাতে তার তৃষ্ণা মিটছে না, বেড়েই চলছে। “…. এই হল জীবন, মহারাজ।’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, পৃ: ৯৮) এই হল উপসংহার। “মহাভারতে মানুষ যেন বলছে: জীবন আমাকে কিছু দেবে বলে নয়, আমার শ্রেষ্ঠসত্তা থেকে আমি জীবনকে কিছু দেবার স্পর্ধা রাখি, এ স্পর্ধা আমার সমস্ত মানুষের হয়ে। একমাত্র মানুষই সমস্ত বিপদের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারে।… বাইরে তার অবধারিত পরাজয় থাকলেও চরম বিজয়ের উৎস তার অন্তরাত্মার মধ্যেই নিহিত; সেখানে সে নিত্যবিজয়ী।’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য)
মহাভারত বলেছে: ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ (শান্তিপর্ব, ২৮৮/২০)—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। “নিদারুণ দুঃখ ও সংশয়ের সংঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুর বঞ্চনা ও ব্যর্থতার মধ্যে আপন আন্তরতেজে এসব-কিছুকেই জয় করে মানুষ তার মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে দেবতা হয়ে উঠেছে।’’ (‘মহাকাব্য মহাভারত’, পৃ: ৯৯) সেই কারণেই মহাভারতের মহত্ত্ব, সেই কারণেই পৃথিবীর অন্য সব মহাকাব্যের থেকে মহাভারত সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির এক গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জি:
প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য (‘মহাকাব্য মহাভারত’ প্রবন্ধ)
সুকুমারী ভট্টাচার্য
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স
মহাভারত
প্রকাশক: গীতা প্রেস
সুকুমারী ভট্টাচার্যের স্কেচটি এঁকেছেন হিরণ মিত্র।
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনসিঁড়ি - পাগলা গণেশআরও পড়ুনভোগান্তিনামা - upal mukhopadhyayআরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.2.***.*** | ২৩ মে ২০২১ ২০:৪৮106374
জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.2.***.*** | ২৩ মে ২০২১ ২০:৪৮106374বস"
 জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.2.***.*** | ২৩ মে ২০২১ ২০:৪৮106375
জয়ন্ত ভট্টাচার্য | 117.2.***.*** | ২৩ মে ২০২১ ২০:৪৮106375বা!
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :), হীরেন সিংহরায়)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Bratin Das, ফরিদা)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
(লিখছেন... :/, lcm)
(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )
(লিখছেন... দীপ, দীপ, ধোরবা)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।

















