- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
মানব আর আমার বন্ধুত্ব— The personal is political, the political is personal
হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়
পড়াবই | মনে রবে | ০৯ আগস্ট ২০২০ | ৬২২৩ বার পঠিত 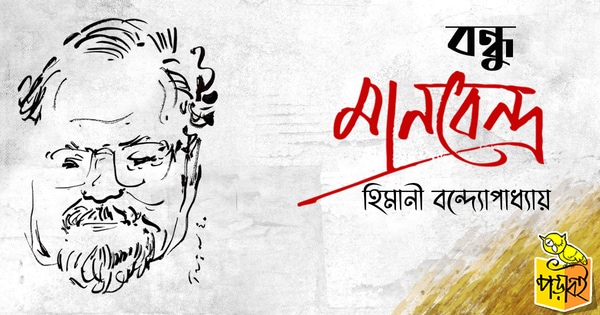
এক্কেবারে সঠিক সাল তারিখ মনে নেই, কিন্তু ১৯৮০-র দশকের একদম গোড়া, ১৯৮২-৮৩ হবে। ইউনিভার্সিটি অফ টোরন্টো-তে সেসময় সেমিয়টিক স্টাডিজ বলে একটা ইনস্টিটিউট চালান হত। সামার ক্লাস হত। বিভিন্ন দেশ থেকে নানা মানুষজন আসতেন। যেমন, জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, কাজা সিলভারম্যান, এমন আরও অনেকে। আর এমএ, পিএইচ-ডি-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটা কোর্স-ওয়ার্কের একটা অঙ্গ ছিল। এর সঙ্গেই একটা কনফারেন্স হত। ইউরোপ ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশ থেকে অনেকে আসতেন। তাতেই সে বছর এসেছিল মানব, আর ছিলেন নবনীতাদি (নবনীতা দেবসেন)। তো মানবের বক্তৃতার বিষয় ছিল—সাহিত্য কাকে বলে এবং ‘ভারতীয় সাহিত্য’ বলে কিছু হয় কি না। আমি জানি মানবের এটা নিয়ে বলার কথা। এদিকে দেখছি ও সব জায়গায় যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কিচ্ছু লিখছে না। মানে লেকচারটার জন্য তৈরি হচ্ছে না। আমি যতবারই বলি—কিছু লিখবে না? বলে, “হবে, হবে। পরে হবে।” এই করে করে ওর বলার দিন এসে গেল। সভা শুরু হল। আমার তখন টেনশন হতে শুরু করেছে। ভাবছি বিশ্রী কিছু একটা কাণ্ড হবে। তারপর দেখি ঠিক স্টেজে ওঠার আগে ও আমাকে বলছে, “তোমার কাছে একটা খাতা হবে?” সেদিন ঘটনাচক্রে আমার কাছে একদম নতুন রোলার বাইন্ডার দেওয়া একটা খাতা ছিল। সেটা নিল, আর একটা কলম নিয়ে পোডিয়ামে চলে গেল। আমার তখন হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। ভাবছি কী করবে লোকটা? তারপর দেখলাম পকেট থেকে কী একটা বার করে, সেটা একপাশে রেখে, আর আমার খাতাটা ঠিক সামনে রেখে, সেটার একটা করে পাতা উলটাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে, অনেক ভাষা, অনেক ইস্যু, অনেক থিম সত্ত্বেও কেন ‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য’ বলে একটা জিনিস আছে। শুধু তাই নয়, তারই জেরে ম্যাজিকরিয়েলিজম-এর অনেক আগে যে ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ লেখা হয়েছে তা নিয়ে একটা ঝরঝরে বক্তৃতা দিয়েদিল। শুধু আমি জানি ওই খাতাটায় একটা শব্দও লেখা নেই! পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এটা কী করে করলে?” বলল, “কেন, আমার যে ‘আধুনিক ভারতীয় গল্প’ বলে বইয়ের সিরিজ আছে তার ইন্ট্রোডাকশনটা বলে দিলাম!” এমনই ছিল মানব!
মানবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৩-৬৪ সালে। তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে। তিনি একটা কবিতা আনতে গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে, আমি ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তো সেই দিনটার যে ছবি আমার মনে আছে, তাতে মানবের থেকেও আমার বেশি মনে আছে মানবের মায়ের কথা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষণ সুন্দর দেখতে। বয়স বেশি নয়। আর অনেক চুল। তারপর মানব বেরিয়ে এল। আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। চা খেয়ে চলে এসেছিলাম।
তার আগে অবশ্য মানবকে দেখতাম কলেজস্ট্রিট কফিহাউসে, আরও অনেক লেখকদের আড্ডায়। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির ছাত্রী। যেতাম কফিহাউসে। কিন্তু ও দলের কাছে যেতাম না। তীর্থঙ্কর যেত। দেখতাম কলাপাতা রঙের শার্ট পরে একজন বসে আছে। শুনেছিলাম, ইনিই হলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মানব তখন খুব শৌখিন ছিল—পরে যাদবপুরে ওর ছাত্ররা ওকে ‘The best dressed teenager’ খেতাব দিয়েছিল!! এ সময়টায় অবশ্য ও আর কল্যাণ (প্রয়াত সাংবাদিক কল্যাণ চৌধুরী) খড়গপুরে একটা ইস্কুলে পড়াত। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসত। আর তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু মানব পুরোদমে লেখালিখি করছে। মানবের বাবা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন করিমগঞ্জ থেকে। এসে থাকতেন ৫৮/১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুরে। এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের পিছনে। আমি যখন থেকে দেখেছি, সেখানে মানবের মা ছাড়াও থাকত আরও চার ভাই, এক বোন। সবথেকে বড়ো ভাই দীপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় থাকতেন না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াতেন। আড়াইখানা ঘর ছিল। মানবের বাবা হঠাৎ মারা যান। তখন মানবের সবে সতেরো-আঠারো বছর বয়স। বাবা মারা যাবার পর খুবই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এত অভাব হল যে মানব অমিয় চক্রবর্তী বলে একজন প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুবাদ করতে শুরু করল। অর্থ রোজগারের জন্য। কাজেই মানবের তরজমার কাজ শুরু ওই সতেরো-আঠেরো বছর বয়স থেকেই। সম্ভবত সেটা ১৯৫৫-৫৬ সাল। সেটাই ছিল রোজগারের একমাত্র সূত্র। মানব তখন জুল ভের্ন, হান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসনের গল্প, লাস্ট অফ দ্য মোহিকান্স এগুলোর অ্যাব্রিজ্ড ভার্শন তরজমা করেছিল। পরে অবশ্য ওগুলো আবার বড়ো করে বার করে। আর এই কাজটা মানব অনেকদিন করেছিল।
আমার সঙ্গে মানবের ভালো মতো দেখাসাক্ষাৎ হল আমি এমএ পাস করার পর যখন যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান নরেশ গুহ আমাকে তাঁর বিভাগে একটা খালি পোস্টে জয়েন করতে বললেন। ১৯৬৫ সালে, ৩৫০ টাকা মাইনেতে জয়েন করে গেলাম। তখন মানবকে অনেকেই চেনেন। ওঁর ঘরে আসতেন। শিপ্রা সরকার আসতেন, মানবের কাছে। ঘরে বসে সিগারেট খেতেন। আমিও একটু শিখছিলাম! শীলা রায়চৌধুরী আসতেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, যাঁর লেখা আমার খুব ভালোলাগত, আসতেন। ডেভিড ম্যাকাচ্চন তো আমাদের বিভাগেই ছিল। তো আমি আর মানব কোলিগ হলাম। অনেক কথাবার্তা হতে লাগল। তারপরে একসময়ে মানব বলল, “বিয়ে করে ফেললে হয়।” আমি বললাম, “না। সেটা ভালো কথা নয়।” তারপর আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পরে আমি রাজি হলাম। বিয়ে হল ওই ১৯৬৫ সালেই।
বিয়ে হয়ে আমি মানবদের বাড়িতেই, যাদবপুরে, থাকতে গেলাম। তা সেই আড়াইখানা ঘরের একটা ঘর আমি আর মানব পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা রাতের বেলা। দিনের বেলা সেটাই বসবার ঘরের কাজ করত। বাড়িতে সারাদিনই অনেক লোকজন আসতেন। আর মানবের মা প্রত্যেককে চা করে খাওয়াতেন। কখনও কেউ চা না খেয়ে গিয়েছে এমন দেখিনি। দারিদ্র্য খুবই ছিল। কিন্তু মনের দারিদ্র্য আমি সেখানে কখনও দেখিনি। মনের দিক থেকে সবাই খুব খোলামেলা ছিলেন। এখন যার নাম সম্বরণ সে বোধহয় তখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ে। তার দাদা সত্যেন—ডাকনাম সতু—খুব নাম করা নকশাল কর্মী ছিলেন, আর বহুদিন খুব ভালো একটা পত্রিকা চালিয়েছিলেন—স্পন্দন। তার কাছেও অনেক ছেলেরা আসত। বাড়ি সারাদিন সরগরম থাকত। আমার বাড়ি মোটেই এরকম ছিল না। এখানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমিও তখন আরও একটু পয়সা রোজগারের চেষ্টায় যাদবপুরের ফুল-টাইম চাকরির পাশাপাশি সাউথ পয়েন্টে পার্টটাইম পড়াতে শুরু করলাম। আর সপ্তাহে দু-দিন রাতে টিউশনি করতাম।
১৯৬৭ সালে আমাদের মেয়ে তিন্নির (কৌশল্যা) জন্ম হল। তাতে অভাব আরও একটু বাড়ল। তো তখন আমি এখানে ওখানে বিদেশ যাওয়ার জন্য অ্যাপলিকেশন করতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম, এতজনের দায়িত্ব, আমরা দুজন চালাচ্ছি, যদি বিদেশে কিছু একটা হয়, আমি মানব আর তিন্নিকে নিয়ে যেতে পারব, কিছু টাকা পাঠাতেও পারব। কিন্তু পেতে সময় লাগল। ১৯৬৯-এ টরন্টো ইউনিভার্সিটি আমাকে স্কলারশিপ দিল। তিন্নিরও যাওয়ার কথা ছিল আমার সঙ্গে। কিন্তু কেনেডিয়ান হাইকমিশন বলল, “তোমার যা স্কলারশিপ তাতে আর কাউকে আনা যাবে না।” তখন ঠিক হল আমি যাব, যদি তারপর ওদের দুজনের আসার অর্থ জোগাড় করতে পারি থাকব, নইলে একবছর পর আমি ফিরে আসব। জুলাই মাসে চলে গেলাম।
দুশ্চিন্তা তো মনের মধ্যে একটা ছিলই। কিন্তু এটাও জানতাম যে, গত দু-বছর তিন্নি অনেকটাই বড়ো হয়েছে মানবের মায়ের কাছে—আমরা সবাই বাড়িতে তাঁকে মা বলে ডাকতাম, সেই দেখাদেখি তিন্নিও তাঁকে মা বলত। আমাকে বলত—দিপু-মা! আর মানবও মেয়েকে খুব দেখাশোনা করত। সেসময় তিন্নির মাঝে সাঝেই শরীর খারাপ হত, মানব তখন খুবই করত। আসলে ও বাচ্চা খুব ভালোবাসত। যাই হোক, টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে যাঁর কাছে কোলরিজের গদ্যের ওপর কাজ করতে গিয়েছিলাম, আমার সুপারভাইজার, তিনি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে সর্বক্ষণ মনমরা দেখি কেন? তা ওঁকে বললাম, তিন্নি আর মানবকে নিয়ে আসতে না পারার কথাটা। তখন ওনার সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে লেকচারার করে টাকাটা বাড়িয়ে দিল। আমি মানব আর তিন্নিকে নিয়ে এলাম। সেটা ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে।
কিন্তু তার আগে থেকেই আমার সঙ্গে মানবের কিছু সমস্যা হচ্ছিল। বনিবনা হচ্ছিল না। ভেবেছিলাম, ক্যানাডাতে গিয়ে যদি একসঙ্গে থাকতে পারি হয়তো সব ঠিকঠাক হবে। মানব এসে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো থেকেই সংস্কৃতে একটা এমএ করল। ধ্বন্যাত্মক লোচন বলে একটা টেক্সট আছে তার ওপর ওর কাজটা ছিল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা আর থাকতে পারছিলাম না। আমাদের মধ্যে কখনও কোনো সাংঘাতিক ঝগড়াঝাটি হয়নি। কিন্তু অনেকসময় দুজন মানুষ চেষ্টা করলেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে না। আমাদেরও তাই হয়েছিল। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা সেপারেশন-এ যাব। যদিও ‘ডিভোর্স’ যাকে বলে আমাদের সেটা হয়েছিল অনেক পরে— ১৯৮০-তে। এটা ১৯৭৩।
এর মধ্যে মানব ভ্যাঙ্কুভারে গিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার বিভাগে ভরতি হল এমএ করতে। আর সেইসময়েই মানব অনেক অনেক বিদেশি লেখা পড়তে শুরু করেছিল। তখনই প্রথম পড়েছিল গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড’। প্রচুর আফ্রিকান সাহিত্যও পড়ছিল সেসময়ে। মনে আছে খুব উত্তেজিত হয়েছিল ফ্রানৎজ ফানন-এর ‘রেচেড অফ দি আর্থ’ বইটা পড়ে। আর পড়ছিল এইমে সেজায়ারের কবিতা। পরে যেটা ও দেবলীনা ঘোষের সঙ্গে অনুবাদও করেছিল। আর ওইখানে গিয়েই পরিচয় হয়েছিল পূর্ব ইউরোপের কবিতা-সাহিত্যের সঙ্গে। সেসব ও প্রচুর পড়ছিল সেসময়ে। আসলে যে ভদ্রমহিলা ওর সুপারভাইজার ছিলেন তিনি পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যে খুব পণ্ডিত ছিলেন।
এর মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জানাল—“হয় তোমরা ফিরে এসো, নয় চাকরি ছেড়ে দাও।” তো মানব ফিরে গেল। তিন্নি আমার কাছেই থেকে গেল। সন্তানের কাস্টডি নিয়েও আমাদের মধ্যে কখনও কোনো মনোমালিন্য হয়নি। এরপর থেকে টানা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত—মানবের বুকে অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত— প্রত্যেক বছর হয় আমি তিন্নিকে নিয়ে কলকাতায় আসতাম, নয় মানব টরন্টোতে আমাদের কাছে গিয়ে থাকত। তারপরে আর ও যেত না। কিন্তু আমি আসতাম। এখনও যেমন এসেছি। আমাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তার কখনও কোনোদিন—এই যে এবারে আমি আর মিকি (মাইকেল কুটনার)— যার সঙ্গে আমি সেই ১৯৭৪ সাল থেকে থাকি, আর ১৯৮০-র শেষের দিকে একদিন দু-জনেই ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে বেরিয়ে বিয়ে করে এসেছিলাম রেজিস্ট্রি আপিসে গিয়ে—মানবকে হাসপাতালে ভরতি করে এলাম, প্রায় রোজই দেখতে যেতাম, অগাস্টের ৪ তারিখ পর্যন্ত—কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তেমনই অটুট ছিল তিন্নিকে কেন্দ্র করে বাবা আর মা হিসেবে আমাদের যে বন্ড, যে পারস্পরিক বিশ্বাস।
আর সেই বন্ধুত্ব অটুট ছিল বলেই ১৯৭০-এর দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে, আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন থেকে যে বিপুল লেখাপত্তর উঠে আসছিল, তার সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল মানবই। আমি তো তখন একেবারে মূলধারার ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী ছিলাম। আর মানব কোনোদিন মেনস্ট্রিম ছিল না। মানব আমাকে, মিকিকে আর তিন্নিকে শত শত বই কিনে দিয়েছে। এই সম্পর্কটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকবে কিন্তু এটাই মানবের সঙ্গে ছিল শেষদিন পর্যন্ত। আসলে সেসময়টাও অদ্ভুত ছিল—সেই সত্তরের দশক। চারপাশে আন্দোলন, বিরাট নারী-মু্ক্তি আন্দোলন হচ্ছে। সেসময় আমি আর মানব দুজনেই বিশ্বাস করতে শিখেছিলাম যে একটা কাগজ দিয়ে কোনো সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় না। আমরা সকলে একটা স্লোগান খুব ব্যবহার করতাম— The personal is political।
আমাদের জগৎটা খুব ইনভলভ্ড ছিল। নিজের নিজের কাজের সূত্রে আমরা একে অপরের সঙ্গে খুব যুক্ত ছিলাম। যেমন নাটকের ওপরে আমার যে কাজ—The Mirror of Class, তাতে মানব অনেক জড়িয়ে ছিল। একসঙ্গে কত থিয়েটার দেখেছি। নাট্যজগতের বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আর তাতে অন্য অনেকেই খুব জড়িয়ে ছিলেন। যেমন, ‘চেতনা’ নাট্যগোষ্ঠীর অরুণ মুখোপাধ্যায়। আবার কমপ্যারেটিভ লিটারেচারের ক্ষেত্রে মানব যেটা তৈরি করেছিল, যেটা আমি মনে করি আগে কেউ ভাবেইনি—South-south comparison, আমি আশা করি তাতে আমি মানবকে অনেকটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম। সংস্কৃতি আর রাজনীতির যে অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে, এই বিশ্বাসটাতে মানব আর আমি দুজনেই চিরকাল এক ছিলাম। ওয়াল্টার বেনইয়ামিন, লুসিয়েন গোল্ডম্যান, জিয়রজি লুকাস, মিখাইল বাখতিন—এ সবের সঙ্গে মানবই আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পুরো সাহিত্য আমি মানবের কাছ থেকে শিখেছি। হাইনে, রিলকে, ব্যোদলেয়ার—বুদ্ধদেব বসুর চমৎকার অনুবাদ—এসবের সঙ্গেই কিন্তু তখন তুলনামূলক সাহিত্যে তুলনাটা করার রীতি ছিল। তাঁরা বিরাট ব্যাপার সাহিত্যে। মানবও কোনোদিন তাঁদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি, অগ্রাহ্যও করেনি, বুদ্ধদেবের বিরাট ভক্ত ছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে মানব এসে বহু চেষ্টা করে তখন যাকে ‘তৃতীয় বিশ্ব’ বলা হত তার সাহিত্যের মধ্যে তুলনাটা শুরু করেছিল এখানে।
আর আমাদের প্রজন্মের অনেকেই অনুভব করেছিলাম The personal is political যেমন, তেমনই the political is personal। মানব ছিল আমার মেয়ের বাবা এবং আমার সাংস্কৃতিক বন্ধু, সাহিত্যিক বন্ধু, রাজনৈতিক বন্ধু।
আর-একটা জিনিস খুব জোর দিয়ে বলতে চাই, মানবের মধ্যে একটা বিরাট দেখার চোখ ছিল। মানব কোনো কিছু ছোটো করে দেখতে পারত না। মানবের স্বভাবে অনেক ‘অ্যাঙ্গুলারিটি’—জানি না এর বাংলা কী হবে—ছিল। কিন্তু মানব কখনও লোক-দেখানো কথা বলেনি, যা বিশ্বাস করেছে সেটা করেছে। আর পড়ানোটাকে মানব একেবারে ভিতর থেকে নিয়েছিল। পড়ানো আর বাঁচার মধ্যে মানবের কাছে কোনো তফাত ছিল না।
সব শেষে বলব, ‘ভেদ-বিভেদ’ বলে ও যে সংকলন দুটো করেছিল তার কথা। আজকে যখন আমরা সাম্প্রদায়িকতার ভয়ংকর ফল দেখতে পাচ্ছি ভারতে, তখন সেই সংকলনে ও ইন্ট্রোডাকশন বা পোস্ট-স্ক্রিপ্ট হিসেবে যা লিখেছিল সেটা মনে পড়ছে। আমি মনে করি সেটা বাংলা সাহিত্যে ওর বিরাট অবদান—সাহিত্য দিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হয় এটা মানব গভীরে বিশ্বাস করত। আমাদের যে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় ফ্যাসিবাদের ট্র্যডিশন তৈরি হয়েছে তার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ওর লেখালিখিতে অনেক কিছু রয়েছে। সেটার গুরুত্ব অপরিসীম।
অনুলিখন: নীলাঞ্জন হাজরা
মানবেন্দ্রবাবুর স্কেচ: হিরণ মিত্র
থাম্বনেল গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 বিষাণ বসু | 2409:4060:2096:5c0c:1316:70a5:63ce:***:*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৫:৪৬96093
বিষাণ বসু | 2409:4060:2096:5c0c:1316:70a5:63ce:***:*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৫:৪৬96093এই লেখাখানা অনবদ্য। মানববাবু এবং সময়টা চোখের সামনে ভেসে উঠল।
এবং পড়া শেষ হওয়ার পরেও মিলিয়ে গেল না।
 দীপঙ্কর দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৮96096
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত | 202.142.***.*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫৮96096অন্তরঙ্গ আড্ডায় দুজন কৃতী মানুষের ভালোবাসার গভীরতা, পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিয়েও নির্ভরতার অভিনবত্ব এবং তাঁদের মেধা চর্চা বিষয়ে টুকরো টুকরো অনেক কিছু নীলাঞ্জনের কাছেই শুনেছিলাম। আজ এই লেখায় সেই টুকরোগুলি সমগ্রের চেহারায় প্রকাশ পেল যা কোন ব্যক্তিত্বকে তাঁর জীবনচর্যা ও কাজের নিরিখে অনেকটা বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর কাজের ক্ষেত্রকে আরও জানার আগ্রহ তৈরি হল।
 aranya | 162.115.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০২:১০96106
aranya | 162.115.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০২:১০96106- ভাল লাগল
 Tim | 174.102.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০৩:৩৪96110
Tim | 174.102.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০৩:৩৪96110- সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক চর্চা, বিশেষ করে দীর্ঘদিনের চর্চার ইতিহাস পাঠকের কাছে এই লেখায় যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা শিক্ষনীয়। ডকুমেন্টেশন তো বটেই, সঙ্গে এ যেন এক প্রাইমার। সত্যিই অনবদ্য লেখা।
 পারমিতা রায় | 2409:4060:304:9f35::163d:***:*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০৭:৫৮96118
পারমিতা রায় | 2409:4060:304:9f35::163d:***:*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ০৭:৫৮96118এমন বন্ধু-জীবন স্বপ্ন দেখায় ,জাগিয়ে রাখে।
 রঞ্জিত শূর | 117.204.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৫96130
রঞ্জিত শূর | 117.204.***.*** | ১০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৫96130দুরন্ত। অনেক অজানা বিষয় জানলাম। খুব প্রয়োজনীয় লেখা। খুব ভাল লাগল। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম।
 মিলন গঙ্গোপাধ্যায় | 110.227.***.*** | ১১ আগস্ট ২০২০ ১২:৫৫96160
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় | 110.227.***.*** | ১১ আগস্ট ২০২০ ১২:৫৫96160খুবই আন্তরিক একটি স্মরণালেখ। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাছে থেকে দেখেছি কিন্তু আপনার লেখা পড়ে মানুষটিকে নানা কোণ থেকে দেখেছি। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই !
 ব্রততী চৌধুরী | 2401:4900:314f:c81f:654a:3636:102:***:*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫০96225
ব্রততী চৌধুরী | 2401:4900:314f:c81f:654a:3636:102:***:*** | ১৩ আগস্ট ২০২০ ১৭:৫০96225দেখার আকাশ অনেক বড় হলে তবেই এভাবে ভাবতে পারা যায়
 অগ্নিভ ঘোষ | 116.204.***.*** | ১৭ আগস্ট ২০২০ ১৫:৪৬96391
অগ্নিভ ঘোষ | 116.204.***.*** | ১৭ আগস্ট ২০২০ ১৫:৪৬96391হিমানীদির এই চমৎকার স্মৃতিচারণটি উপহার দেওয়ার জন্য নীলাঞ্জনবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ। একটা ছোটো ভ্রান্তি চোখে পড়ল। অষ্টম অনুচ্ছেদে ধ্বন্যাত্মক লোচন বলে যে টেক্সট-এর উল্লেখ আছে ওটা আসলে ধ্বন্যালোক লোচন। নবম শতাব্দীর কাশ্মীরি পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত বিরচিত। আমি নিশ্চিত, এ ভ্রান্তি হিমানীদি বা নীলাঞ্জনবাবুর নয়, নেহাতই বর্ণসংস্থাপনগত। যদি পুনরায় সম্পাদনের অবকাশ থাকে বদলে দেবেন।
মানববাবু যে অভিনবগুপ্ত-র লোচন নিয়ে কাজ করেছিলেন এ তথ্য একেবারে অজানা ছিল।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












