- বুলবুলভাজা পড়াবই বই কথা কও

-
আফগানিস্তান রুমিরও জন্মভূমি
পলাশ পাল
পড়াবই | বই কথা কও | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৩২১৩ বার পঠিত 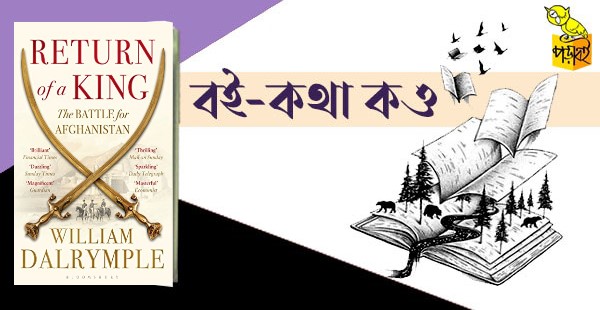
আফগানিস্তান ও তালিবান সম্পর্কে ভারতের বেশির ভাগ মানুষেরই ধারণা হল-- দেশটি এখনও মধ্যযুগে পড়ে আছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনও বালাই নেই, রাজনৈতিক ভাবে তারা এতটাই অজ্ঞ যে বিদেশিদের সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারবে না। গত কুড়ি বছরে সেখানে যে-টুকু উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে, তা পশ্চিমী শাসকদেরই বদান্যতায়। সুতরাং এমতাবস্থায় মার্কিনিরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলে তালিবানের শাসনে দেশটি একেবারে রসাতলে চলে যাবে। সন্দেহ নেই, ধারণাটি পুরোপুরি অমূলক। বস্তুত এই কথাগুলি যখন বলা হয়, তখন দেশটির বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বৈচিত্র্য, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভিন্নতার জটিলতা ও আন্তঃসম্পর্ককে বিবেচনায় রাখা হয় না।
সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পল। ২০১২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ‘রিটার্ন অব আ কিং: দ্য ব্যাটল ফর আফগানিস্তান’ বইটিতে যা লিখেছেন, তার মোদ্দা কথাটি হল: আফগান সমাজকে যতই পিছিয়ে পড়া, রক্ষণশীল বলে অভিহিত করা হোক না কেন, এই স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীটি বিদেশি শাসকদের কাছে কখনওই মাথা নত করেনি। বরং নিজেদের সংস্কৃতি গত ভিন্নতা সত্ত্বেও বারবার তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছে। ডালরিম্পলের গবেষণার মূল বিষয় ছিল, ১৮৩৯ সালে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারত থেকে আফগানিস্তান অভিযানের সঙ্গে ২০০১ সালে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের অভিযানের তুলনা। তাঁর মতে, সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয়ের নেপথ্যে ছিল আফগান জনসাধারণের প্রবল প্রতিরোধ। একই ভাবে মার্কিন সামরিক জোটের পতন এবং তালিবানদের উত্থানের পশ্চাতেও রয়েছে, বিদেশি মদতপুষ্ট শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ ক্ষোভের স্ফুরণ। এটাই তালিবানদের জনভিত্তি গড়ে দেয়।
ডালরিম্পল পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনা করে দেখান যে, ব্রিটিশ সরকার যাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সেই শাহ সুজা আফগানদের কাছে ছিলেন একজন বিদেশি শক্তির তাঁবেদার মাত্র। অন্যদিকে, আফগান গোত্র ভিত্তিক বহুধারার সংস্কৃতিকে মান্যতা দেওয়ার বদলে আমেরিকানরা যে পশ্চিমী ধাঁচের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাও সাধারণ আফগানিদের কাছে একেবারেই বৈধতা পায়নি। হামিদ কারজাই থেকে আশরাফ গনি প্রত্যেকেই পশ্চিমী ভাবধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। ফলে তাঁদের এই শ্রেণিগত অবস্থান সাধারণ আফগানদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের দেওয়াল গড়ে দিয়েছিল। মার্কিন ছত্রছায়ায় থেকেই তাঁরা শাসন চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ডালরিম্পল আরও দেখিয়েছেন, আফগানদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পরে ব্রিটিশ সেনাকে ফিরিয়ে নেওয়া হলেও, এই অভিযানের অভিঘাত ছিল সুদূরপ্রসারী। কান্দাহার ও কাবুলের যে-সব স্থানে ব্রিটিশ সেনারা ঘাঁটি গেড়েছিল, সে-সব অঞ্চলগুলি হয়ে উঠেছিল অপরাধের এক একটি আঁতুড় ঘর। খাদ্যসঙ্কট প্রবল আকার ধারণ করে, সেনারা তাদের বিনোদনের জন্য গড়ে তোলে একাধিক পতিতালয়, যা থেকে আবার জন্ম নেয় বহুরকমের অপরাধ প্রবণতা।
ডালরিম্পল গবেষণার সূত্রে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান, কথা বলেন বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে। কিন্তু যেখানেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন, সব জায়গাতেই কারজাই ও গনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে পেয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর লেখায় উঠে আসে মার্কিন সেনাদের নানা-রকমের কুকীর্তির কথাও। তালিবান সন্দেহে সাধারণ আফগানদের অযথা হয়রানি, বিনা অনুমতিতে ঘরে ঘরে তল্লাসি, ইত্যাদি নানা কুকর্ম — তাদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি নারীরাও। পূর্বসূরি ব্রিটিশ বাহিনীর মতো তাদের মনোরঞ্জনের জন্যও গড়ে ওঠে অগণিত নিষিদ্ধপল্লী। ডালরিম্পল কিলঘাই উপজাতির এক প্রবীণের ক্ষোভ তুলে ধরেন: ‘তোমরা তখন তখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ো, মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে বাইরে বার করো, বাচ্চাদের লাথি মারো…আমরা এর জবাব দেব…তোমাদের পূর্বসূরিদের যেভাবে চলে যেতে হয়েছে, তোমাদেরও সেভাবেই যেতে হবে’। উল্লেখ্য যে, উইলিয়াম ডালরিম্পল যখন গবেষণার কাজে আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন, তখনও দেশটির এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল তালিবানদের একাধিপত্য।
বাস্তবিক, কুড়ি বছর আগে, ২০০১ সালে আমেরিকা ও যৌথবাহিনী যখন তালিবান ও আল-কায়দাকে ধ্বংস করতে আফগানিস্তান অভিযান চালিয়েছিল, তারা এমন একটি ভাব করেছিল যেন শুধুমাত্র তালিবানদের উৎখাত করাই নয়, ‘রক্ষণশীল’ আফগান সমাজের আধুনিকীকরণ এবং সেখানকার নারীদের রাতারাতি পশ্চিমী নারীতে পরিণত করাই তাদের অগ্রাধিকার। সেই সঙ্গে একটি মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি পশ্চিমী ধাঁচের উদার গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও প্রগতির পতাকা তুলে ধরাও ছিল তাদের প্রতিশ্রুতির তালিকায়। কিন্তু গত দুই দশকে যে-সব ছবি উঠে এসেছে, তাতে এ-কথা আজ স্পষ্ট যে, শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নয়ন কোনটাই তাদের লক্ষ্য ছিল না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরে পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে, রাশিয়া, চীন ও ইরান— মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রতিস্পর্ধী এই দেশগুলির চারপাশে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি তৈরি করাই ছিল আফগানিস্তান দখলের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নজর ছিল দেশটির বিপুল খনিজ সম্পদ হস্তগত করা এবং ভূ-কৌশলগত অবস্থানের সুযোগ নিয়ে অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরানো।
সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টেও দেখা গেছে, ২০০১ থেকে ২০২০ সময় পর্বে, আমেরিকা আফগান সমাজ পুনর্গঠনে যা ব্যয় করেছে, তার মধ্যে ৮৫ শতাংশই খরচ করা হয়েছে সামরিক খাতে— মার্কিন সেনাদের সেবা-শুশ্রূষার ও আফগান নিরাপত্তাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে। মোট অর্থের মাত্র দুই শতাংশ ব্যয় হয়েছে আফগানিস্তানের পরিকাঠামো উন্নয়নে। দেশটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র দূরীকরণের মতো প্রকল্পগুলিতে প্রায় কোনও অর্থই খরচ করা হয়নি। বেসরকারি হিসাবে গত কুড়ি বছরে আমেরিকা আফগানিস্তানের সামরিক খাতে ব্যয় করেছে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ এই বিপুল অর্থকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো হত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র দূরীকরণের মতো প্রকল্পে ব্যয় করা হত, দেশটি মানব উন্নয়নের সূচকে কয়েক ধাপ উপরে উঠে আসতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আফগানরা আরও পিছিয়ে পড়ল। এখনও সেখানে শিশু মৃত্যুর হার থেকে শুরু করে প্রসূতি মায়ের মৃত্যু এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ু পর্যন্ত সূচক এশিয়ার সর্বনিম্ন আয়ের দেশগুলির মতোই। আরও স্পষ্ট করে বললে, পূর্বের তালিবান জামানার সঙ্গে কুড়ি বছরের মার্কিন ছায়া-সরকারের শাসনের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্যই নেই।
বস্তুত, আমেরিকা এই গ্রহের যেখানেই উপস্থিত হয়েছে সেখানেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে করেছে ঠিক তার উল্টোটাই। তাদের অপরাধের তালিকাটি দীর্ঘ। যে-কোনও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে দমন করতে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং সিআইএ-র মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয় পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে তাদের অপছন্দের সরকারের পতন ঘটিয়েছে, নয় তো প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদেরই তাঁবেদার সরকার। সেই সঙ্গে বিরুদ্ধ মত দমনের জন্য গণহত্যা ঘটিয়ে বারবার কলঙ্কিত করেছে ইতিহাসকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সে-সব দেশই তার সামরিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, যারা অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে বের হয়ে আসতে সমাজতন্ত্রকে উত্তম পথ বলে বেছে নিয়েছিল। একটি হিসাব অনুযায়ী ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতি দুই বছরে একটি করে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যভাবে বললে, মুখে ‘নেশন বিল্ডিং’-এর বিরোধিতা করলেও, বাস্তবে সেটাই সে বারবার করতে চেয়েছে। আর এ-ক্ষেত্র, বিশেষত ঠান্ডা লড়াইয়ের পরে, অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে, স্যামুয়েল হাংন্টিংটন ও ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার সেই দুই বিখ্যাত তত্ত্ব—‘দ্যা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন’ এবং ‘দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি’। প্রথম জন গোটা পশ্চিমী সমাজের জন্য ইসলামকে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, অন্য জন মার্কিন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে। তাঁর অভিমত ছিল, মার্কিন জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে এই দেশগুলিতে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। জর্জ বুশ ছিলেন এঁদেরই ভাবশিষ্য।
প্রতিটি মার্কিন আগ্রাসনের পরিণতি কেমন হয়েছিল তা বুঝতে আমরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারি। আমরা মনে করতে পারি, গত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বডিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ার ভয়ঙ্কর গণহত্যার কথা, যা সংঘটিত হয়েছিল সিআইএ-র তত্ত্বাবধানে। মনে করা যেতে পারে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বামপন্থী সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করতে সিআইএ-র মদতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কথা, চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেখানে কীভাবে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করেছিল, সেই ইতিহাসের কথা। কিংবা আফ্রিকায় কঙ্গো ও মালির সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা, যার ক্ষত ইতিহাস এখনও বয়ে চলছে। পাশাপাশি এ-কথাও ঠিক, এই সব দখলদারির বিরুদ্ধে কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিল এই সব দেশের শ্রমজীবী মানুষরাই। ভিয়েতনাম থেকে পরাজিত হয়েই তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে, আফগানিস্তান ছাড়াও. মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের উদাহরণ হল, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া সহ বিভিন্ন দেশ।
মানতেই হবে, তালিবানকে আফগানিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করাটা ঠিক হবে না। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রথম পর্বের তালিবানদের চেয়ে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিবানদের মধ্যে ব্যবধানও বিস্তর। তারা এখন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশীদার হতে মরিয়া। সম্ভবত তারা এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে তাদের আফগান নাগরিকদের শাসন করতে হবে, আর তা সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দিয়ে মোটেই সম্ভব নয়। প্রথম পর্যায়ের শাসনের মতো তারা নারীর মৌলিক অধিকার হরণ, ভিন্ন মতের ওপর দমন-পীড়ন, সন্ত্রাসবাদকে লালন-পালনের মতো বোকামিও করবে বলে মনে হয় না, ইতিমধ্যেই তার নানা ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। আফগান নারীরা আগের মতোই টিভিতে খবর পড়তে শুরু করেছেন, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মিছিলে সামিল হয়েছেন। তাছাড়া বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণের বড় অংশের যে সমর্থন তারা পেয়েছে, সেটা যাতে অটুট থাকে সেদিকেও তারা যথেষ্ট সচেতন। এই সঙ্গে তারা তাদের কার্যকলাপ যে শুধুমাত্র আফগানিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক, সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। আল-কায়দা ও ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে তালিবানের এটা একটা বড় পার্থক্য। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আফগান সরকারে যাতে দেশটির সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, সে-ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় তৎপর হওয়া। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন— তালিবানের দ্বিতীয় পর্বের এই শাসন, তার প্রকৃতি যেমন ই হোক না কেন, তাকে ইসলামের একমাত্র ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হিসাবে যাতে গৃহীত না হয়, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ তাতে করে ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তায় যে বহুমাত্রিকতা আছে সেটা হুমকির মুখে পড়তে পারে।
শাসকের কাছে নৈতিকতার প্রত্যাশা করা আর আগুনের কাছে জলের প্রত্যাশা একই কথা। সুতরাং নতুন তালিবান সর্বগুণসম্পন্ন শাসক হবে এমন কল্পনা হবে আরেক মূর্খতা। তবে কিনা, শাসক নীতিভ্রষ্ট হলে নাগরিকরাই যেমন প্রতিবাদ করে, রুখে দাঁড়ায়, তেমনি তালেবানের বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, তা আফগানরাই। তারাই বলবেন তাদের অধিকারের কথা। একইভাবে, ইরান, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহি থেকে শুরু করে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি, সর্বত্রই নারীরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তাঁদের অধিকারের পক্ষে যেমন লড়ে যাচ্ছেন, দাবি আদায় করেছেন, আফগানিস্তানের নারীরাও একইভাবে তাঁদের অধিকারের জন্য তালেবানের বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন। তার জন্য বাইরে থেকে সংস্কৃতিকে ধার করার প্রয়োজন আছে কি নেই সেটার সিদ্ধান্তও নেওয়ার অধিকারও কেবলমাত্র তাদেরই। জোর করে, অনন্তকালের জন্য নাগরিক অধিকারকে যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি নাগরিকদের অধিকার হরণ করে কোনও শাসকও স্থায়ী হতে পারেনি। মনে রাখতে হবে, রুমি কিন্তু এই আফগানিস্তানের মাটিতেই জন্মেছিলেন।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনইরান প্রশ্ন - Tirtho Dasguptaআরও পড়ুননিউ আর এস এস - Eman Bhashaআরও পড়ুনবাংলাদেশ ও বাউলশিল্পী - দীপআরও পড়ুনফিলিস্তিনের কবিতা পর্ব ১ - A Gআরও পড়ুনবর্তমান - Ismail Jabiullaআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 প্রতিভা | 182.66.***.*** | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৬:৫৩497679
প্রতিভা | 182.66.***.*** | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৬:৫৩497679- রুমির প্রসঙ্গ ও তাঁর দর্শন থেকে এই বিপুল বিচ্যুতির ওপর আরো আলোকপাত থাকবে আশা ছিলো।
-
subhamoy bhattacharyya | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৯:৩০497682
- আচ্চা, দাদা, কম্বোডিয়া পল পটেরা কি করেছিলেন? আর আফগানিস্থানে রূশরা কি করছিলো? ঠান্ডা যুদ্ধে বাতাবরনে কম্বল জরিয়ে ওম কি শুধু আম্রীকাই নিয়ে ছিলো??অন্য ভাবে নেবেন না, শুধু জানতে চাইলাম
 মিত্ররা চৌধুরী | 223.223.***.*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২১:৩১497803
মিত্ররা চৌধুরী | 223.223.***.*** | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২১:৩১497803- ভালো লাগলো পড়ে
 গবু | 103.42.***.*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২১:৩৮497850
গবু | 103.42.***.*** | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ২১:৩৮497850- আমি কিছুদিন আগে এই বইটা পড়েছি। তাতে এরকম কোনো তুলনা দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা। হ্যাঁ - শুরুতে বা শেষে অথর'স নোট বলে লেখাতে মার্কিন আগ্রাসনের একটা চেহারা বর্ণনা আছে বটে - কিন্তু সেটা অনেকটা এনেকডোটাল (বাংলা কি হবে?)। এখানে যেরকম টায়ে-টায়ে তুলনা আছে বলে পলাশ বাবু বলেছেন - সেটা অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়।হাতের কাছে বইটা থাকলে দেখে লিখতে পারা যেত - কিন্তু সে এখন বেড়াতে গেছে। পলাশবাবু যদি একটু রেফারেন্স দিয়ে বলেন যে কোন কোন চ্যাপ্টারে এই ধরণের তুলনা রয়েছে - তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়। গল্পের বইয়ের সমালোচনা আর ইতিহাস-সংক্রান্ত লেখার সমালোচনার মধ্যে এটুকু তফাৎ থাকা বাঞ্ছনীয়।বলে রাখি যে আমার ওনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু এই বইটির মধ্যে তুলনা করার মতো কোনো উপাদান নেই বলেই মনে পড়ছে। ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে বইটি অবশ্যই পড়া উচিত, কিন্তু এর থেকে আজকের জমানার সঙ্গে তুলনার কোনো উপকরণ নেই - এটাই বলতে চাইছি।
-
Alokmay Datta | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ১৮:০৩498098
- পলাশ'দার যে বলেছেন আফগান মানুষই তাঁদের ভবিষ্যত স্থির করবেন তাতে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার শুধু প্রশ্ন এই আফগান মানুষ কারা, কারণ এবিষয়ে তাঁরাই একমত নন। পশতু, তাজিক, হাজারা এবং অন্যান্য জনজাতিরা তাঁদের মধ্যের রেষারেষি না মেটালে আফগানিস্তানের কোনও মুক্তি নেই।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












