- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
‘মিট লুফটপস্ট’ স্টিকার লাগানো, বেঁচে থাকার মন্ত্র পোরা সেই খামগুলো
রাজা মুখোপাধ্যায়
পড়াবই | মনে রবে | ২৯ নভেম্বর ২০২০ | ৩১৮১ বার পঠিত 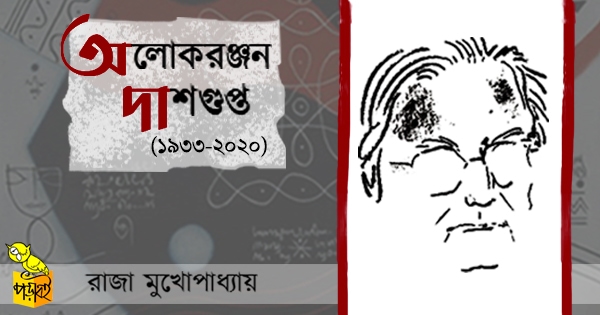 অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর কোলাজ-নাট্য আলোড়ন তুলেছিল কলকাতায়। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তী চার দশক জুড়ে রয়েছে এক সৃষ্টিমোহিত সম্পর্ক। স্মৃতিচারণে তরজমাকার রাজা মুখোপাধ্যায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর কোলাজ-নাট্য আলোড়ন তুলেছিল কলকাতায়। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তী চার দশক জুড়ে রয়েছে এক সৃষ্টিমোহিত সম্পর্ক। স্মৃতিচারণে তরজমাকার রাজা মুখোপাধ্যায়
নিজের অজান্তেই এই আশঙ্কা বারবার ফিরে এসেছে। রাতে ঘুম ভেঙে যেতে উঠে বসেছি। তবু কল্পনা করেছি টাইম মেশিনের তত্ত্বের প্রয়োগ যদি করা যেত? যদি থামিয়ে দেওয়া যেত সময়টা, কিংবা যদি পিছিয়ে দেওয়া যেত ৩৫/৪০ বছর? চল্লিশ বছর! আশ্চর্য, এতদিন! কী করে আঁজলা ভরে ধরব এই সময়টা? ব্যক্তিগত এবং সৃষ্টিশীল পরিসরে তাঁর যে ‘ক্রান্তিসঞ্চারী’ (শব্দটা তাঁরই অন্যতম প্রিয়) বিচরণ দেখেছি, তার স্মৃতিচারণ বা মূল্যায়ন কোনোটাই যে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়, তা তো বরাবরই জানতাম। তাই আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, এ বিষয়ে একটি শব্দও লিখব না। তবু লিখছি কেন? চারপাশে এই প্রায় দু-সপ্তাহের মধ্যে অনেক লেখা বেরিয়েছে। আরও অসংখ্য বেরোবে অসীম প্রতিভাধর এই মানুষটির ঘনিষ্ঠ যাপন এবং সাহিত্যকর্ম নিয়ে—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ঘনিষ্ঠতার মাপকাঠিতে এরকম আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যে বহু মানুষ আসবেন, এ নিয়েও কোনো সংশয় নেই; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। নাট্যকার ও নির্দেশক সুনীল দাশের আহ্বানে তাঁর দলে যোগদান করার সুবাদে পরিচিত হলাম কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে। সেটা প্রায় চার দশক আগেকার একটা ঘটনা।
তখন ‘সংবর্ত’ নাট্যদল মেতে উঠেছে অলোকরঞ্জনের কোলাজ–নাট্য বা নাট্য-কোলাজ নিয়ে। কোলাজ–নাট্য। এই শব্দবন্ধটিও একান্ত তাঁর নিজস্ব। এর আগে কলকাতার নাট্যপ্রেমী দর্শক এই ধারাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে জানা নেই। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবাদপ্রতিম দক্ষতার সঙ্গে জার্মান কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে রচিত এই আলেখ্যগুলিতে মিশে গিয়েছিল এই স্বভাবকবির নিজস্ব সত্তা। তার ফল হয়েছিল অলৌকিক—একথা যে কোনো অতিরঞ্জন নয়, এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে সামান্যতম যোগও যাঁর ছিল, তিনিও জানতেন। এক দশকেরও বেশি সময় জুড়ে চলা এই রচনাগুলির মঞ্চায়ন শুরু হয় মহাকবি গ্যোটের কালজয়ী সৃষ্টি ‘ফাউস্ট’ অবলম্বনে ‘আলো আরও আলো’ দিয়ে; ন্যাশনাল লাইব্রেরি প্রেক্ষাগৃহে যার প্রথম শো হয়। বিপুল আলোড়ন তৈরি করেছিল সেই উপস্থাপনা। মনে পড়ে প্রথম সারির সংবাদপত্রের পাতাজোড়া প্রতিবেদন। এই প্রযোজনাটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল দুর্গাশঙ্কর ঘোষ পরিচালিত ‘প্রমেথেউস’ ফিল্ম। সেই প্রমেথেউস, যিনি মাটি থেকে জন্ম দিয়েছিলেন মানবজাতির আর স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে তুলে দিয়েছিলেন মানুষের হাতে।
এর পরের বছরই অলোকরঞ্জন লিখলেন গ্যোটেরই সাহিত্যকর্ম আর তাঁর বেঁচে থাকা নিয়ে ‘গ্যোটের জীবন-শিল্প’। এইসব কোলাজ-কর্মের মধ্যেই এইসময় অনুবাদ করে ফেললেন হাইনরিশ হাইনের একগুচ্ছ কবিতার সংকলন, যার নাম দিলেন ‘প্রেমে পরবাসে’। তারিখটা এখন আর মনে নেই, কিন্তু মাক্স ম্যুলার ভবনের দর্শক আসনে বসে সেই দিন প্রথম মোহাবিষ্ট হলাম অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষার জাদুকরী মায়ায়। অডিটোরিয়ামের নিভন্ত আলোর মধ্যে অনুষ্ঠান শুরুর আগে মঞ্চে উঠে তিনি বলেছিলেন, “দেখতে পাচ্ছি অনেক তন্ময় দর্শকের সঙ্গে অনেক মন্ময় দর্শকও বসে আছেন।” প্রথম সারিতে বসে থাকা কবি শঙ্খ ঘোষ তখন স্মিত হাসি মুখে নিয়ে তাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে।
এরপর জীবনটা কেমন যেন বদলে যেতে লাগল। প্রতিবছর বউদি-অলোকদা আসেন, সঙ্গে থাকে অন্তত একটি কোলাজ–নাট্য, আর আমরা পরিচিত হতে থাকি জার্মান সাহিত্যের রথী–মহারথীদের সঙ্গে। এখানেই শেষ নয়, অলোকদা প্রায় প্রতিটি মহলায় উপস্থিত থাকতেন, আমাদের কারও একটি শব্দও এদিক-ওদিক করার জো ছিল না। এর ফলে হল কী, তাঁর বাকশৈলীর নেশা ঢুকে যেতে লাগল আমাদের রক্তস্রোতের গভীরে—আমরা একে অপরের সঙ্গেও সেই অননুকরণীয় ভাষার অক্ষম অনুকরণ করে কথা বলা শুরু করলাম। একই সঙ্গে, ক্রমাগত আমরা সাঁতার দিতে থাকলাম বিশুদ্ধ কবিতার সীমাহীন সমুদ্রে, আর দীক্ষিত হতে থাকলাম এক নতুন জীবনবোধে, যার কেন্দ্রস্থলে শিল্পী মানুষের আত্মিক সংকট, যা অনিবার্য। ইতিমধ্যে একঝাঁক নতুন ছেলেমেয়ে এসে গিয়েছে আমাদের নাট্যদলে—শুভ, সুলগ্না, ঈশিতা, শুভাশিস—এরা সব। এদের মধ্যে সুলাগ্নার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটল হঠাৎই। তখন সুলগ্না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সেই তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যার আঁতুড় অবস্থা থেকে অলোকদার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরে বাংলা বিভাগে চলে গেলেও, এই বিভাগটির বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা লক্ষ করেছি বরাবর। জার্মান ছিল সুলাগ্নার বিশেষ বিষয়, যে ভাষায় আমার আগ্রহ এবং শিক্ষার আরম্ভ কয়েক বছর আগে থেকেই। এই ব্যাপারটি অলোকদার নজর এড়ায়নি। মহড়ার পর মাক্স ম্যুলার ভবনের বড়ো গাড়িটায় যখন অনেক সময় আমরা অলোকদার বাড়ি ফেরার পথে তাঁর সহযাত্রী হতাম, তাঁর এবং বউদির সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে লাগল জার্মান ভাষায় টুকটাক কথাবার্তার মাধ্যমে। একদিন তিনি বললেন, “বাড়িতে এসো।”
তখন সন্ধ্যা। প্রাকৃতিক অন্ধকারের সঙ্গে নেমে এসেছে লোডশেডিং। আমরা দুজন পৌঁছেছি অলোকদার যাদবপুরের বাড়িতে। দেখলাম আলো-আঁধারির মধ্যে চালের কাঁকর বাছছেন বউদি। সেই শুরু এক অবিস্মরণীয় যাত্রাপথের। আর কী স্নেহ–মায়া–মমতা ভরা সেই পথ চলা, যা অংশত বদলে গিয়েছিল পনেরো বছর আগে, বউদি চলে যাওয়ার পরে আর তা আর-একটা মাত্রা পেল গত সপ্তাহে যখন খবর এল অলোকদাও হঠাৎ চলে গেছেন। এটা কি একটা যুগের অবসান, নাকি এক অতুলনীয় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ!
ফ্ল্যাশব্যাক ১৯৮৯। ততদিনে কেটে গেছে অনেকটা সময়। বছরের যে সময়টা তখন অলোকদা ওদেশে থাকেন, আমাদের চিঠি লেখেন। আমরাও উত্তর দিই। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। টইটুম্বুর উত্তেজনা নিয়ে আমরা ‘মিট লুফটপস্ট’ স্টিকার লাগানো সেই খামটির প্রতীক্ষায় থাকতাম, যার শেষে অলোকদা লিখবেন ‘তোমাদের অলোকদা’ আর বউদি তাঁর নিজস্ব বাংলা হস্তাক্ষরে লিখবেন ‘বৌদি’। চিঠি ছাড়াও তাঁদের নিয়মিত সাড়া পেতাম ফোনে। সেইরকমই একটা ফোন এল একদিন। সেটা সম্ভবত ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাস। বললেন, তাঁর এক প্রিয় ছাত্র হান্স্ কলকাতায় এসেছে; আমাদের নাকি দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। সেইমতো মাক্স ম্যুলার ভবনের ক্যাফেতে দেখা হল আমাদের। হান্স্-এর সঙ্গে ওর এক বন্ধুনি, গাব্রিয়েলে। বাকিটা তিন দশকের এক বন্ধুত্বের ইতিহাস। সতেরো তারিখ রাতে হান্স্ যখন খবরটা জানাতে ফোন করল, একটা অদ্ভুত কথা বলল ও। বলল, “আমাদের এই বন্ধুতা তো আসলে অলোকদারই উপহার।” সত্যিই তো! তিনি যেন আপন খেয়ালে আলাদা আলাদা গড়লেন আমাদের আর তারপর মিলিয়ে দিলেন যথাসময়ে। এই ঘটনা অবশ্য ওই একই বছরে আবার ঘটল। এবার একটু অন্যভাবে। শুনলাম গ্যোটে ইন্সটিটিউট এর এক কর্তা কলকাতায় এসেছেন পেশাগত কারণে, তিনি আবার অলোকদার বিশেষ পরিচিত আর তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী আর তাঁদের এক বান্ধবী বারবারা। বারবারা কাপ্টাইন। বার্লিনে থাকেন। আমাদের কাজ হল এঁদের সঙ্গী হয়ে কলকাতায় কয়েক জায়গায় যাওয়া এবং প্রয়োজনে দোভাষীর কাজ করা। যদিও প্রথম পরিচয়েই জেনেছিলাম, বারবারা দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিলেন এবং ইংরেজি জ্ঞান মাতৃভাষাতুল্য। মাত্র আড়াই দিনের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে আজ সেই তিন দশকের। বার্লিন, কলকাতার পর আমাদের দ্বিতীয় ঠাঁই আর এই কাপ্টাইন পরিবার আমাদের একান্ত আপন। এও অলোকদারই দান। একই বছরে এই দুই বন্ধুত্ব ঘটে যাওয়ার পরের বছরই আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে ওই দেশটা ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়ে যাই। হ্যোক্স্রটার-এর লায়ন্স ক্লাবের আমন্ত্রণে সুলাগ্না আর আমি প্রথমবার পাড়ি দিই ওদেশে। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।
ওখানে পৌঁছোনোর মুহূর্ত থেকে নাটক। আমরা যখন জার্মানি পৌঁছোই, তখনও কাগজে-কলমে দেশটা বিভক্ত। আর নিজেদের অজান্তেই আমরা নেমেছিলাম পূর্ব বার্লিনের শ্যোনেফেল্ড বিমানবন্দরে। আমাদের সেসময় কোনো ধারণাই ছিল না, সেখান থেকে পশ্চিম বার্লিনের এক প্রান্তে বারবারার বাড়ি, যা পরবর্তী তিন দশক ধরে আমাদের বাসস্থান হয়ে উঠবে, তা কতদূর। যদিও জানতাম কুর্ট শার্ফ, যার মাধ্যমে বারবারার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তিনি আমাদের নিতে আসবেন।
অভিবাসন অফিসার আমাদের পাসপোর্ট দুটো হাতে নিয়ে একটু আমাদের মুখের দিকে তাকালেন আর আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। আমরা প্রমাদ গুনলাম। কারণ, ততক্ষণে বুঝেছি যে দেশে আমরা অবতরণ করেছি সেই দেশের ভিসা আমাদের নেই; পশ্চিম জার্মানির ভিসা নিয়ে আমরা পূর্ব জার্মানিতে হাজির হয়েছি। যাই হোক, প্রায় ঘণ্টাখানেক রুদ্ধশ্বাস কাটানোর পর আমাদের মুক্তি দেওয়া হল। বাইরে ইতিমধ্যে কুর্ট ভাবতে শুরু করেছেন আমরা আদৌ পৌঁছেছি কি না।
এরপর বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে, লায়ন্স ক্লাবের অনুষ্ঠান মিটিয়ে আমরা পৌঁছোলাম বউদি–অলোকদার কাছে। কিন্তু এই পুরো সময়টা জুড়েই আমরা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম আমাদের অভিনীত নাট্য-কোলাজগুলির অভিঘাতে। যেখানেই গেছি, আমরা পৌঁছে গেছি সেইসব স্থানে, তাঁর লেখায় যার উল্লেখ আর বর্ণনা পেয়েছি। সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি আর মুগ্ধতা, যা আজও এতুটুকু কমেনি। আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি এটাই যে, একজন নিরন্তর সৃষ্টিশীল মানুষের কাজ আর বেঁচে থাকা আমাদের মধ্যে একাকার হয়ে আছে। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না কিছুতেই, যিনি আমাদের বেঁচে থাকার মন্ত্র দিয়েছিলেন বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যেও, মূলত তাঁর অনুবাদের শক্তিতে।
সোফোক্লেস-এর ‘আন্তিগোনে’ নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন অলোকদা। সেই প্রসঙ্গে এক চিঠিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “আপনার বাঙ্গলা অনুবাদ মোটের উপর চমৎকার লাগিল। আপনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডির দেহ ও আত্মা দুই-ই বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে আনা সহজ কথা নহে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের পিছনে আছেন, সেই জন্যই আপনার দ্বারা এ কার্য সম্ভব হইল…।”
অলোকদার বিপুল কর্মজগতের একটি অংশ ছিল অনুবাদ এবং দুরূহতম সাহিত্যকর্ম তিনি অনায়াসে মূল থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন। কিন্তু জীবনকে মূল থেকে অনুবাদের যে উত্তরাধিকার আমাদের মধ্যে রেখে গেলেন অলোকদা, তা পালন করার গুরুদায়িত্ব এখন আমাদেরই।
স্কেচ: হিরণ মিত্র
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনদুই দাপুটের কাশীভ্রমণ - ৩ - দআরও পড়ুনবিচ্ছেদ - Manali Moulikআরও পড়ুনশহীদ কবি মেহেরুন্নেসা - দীপআরও পড়ুনবিহিতা - Srimallarআরও পড়ুন২১ - অখিল রঞ্জন দেআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
শিবাংশু | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২২:০২100763
এক আন্তরিক বিস্তৃত শিকড়ের গল্প ...
-
Ranjan Roy | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ০৩:৫২100813
ঋদ্ধ হলাম।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।














