- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
অলোকের কবিতায় স্থান-কালের ক্রমিক প্রসার
শঙ্খ ঘোষ
পড়াবই | মনে রবে | ২৯ নভেম্বর ২০২০ | ৭৪৩৫ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (৮ জন) 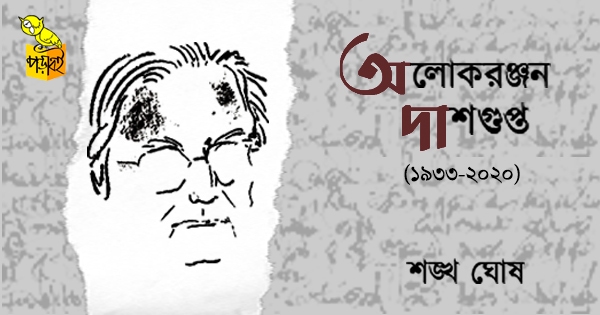 পঁয়ষট্টি বছর ধরে যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আর ষাট বছর জুড়ে যার সঙ্গে প্রতিদিনের নিবিড়তম সখ্য, প্রায় পঞ্চাশ বছর বিদেশবাসের দূরত্ব সত্ত্বেও যার সঙ্গে সংযোগ থেকে গেছে প্রায় প্রাত্যহিক সম্পর্কের মতো, তার আকস্মিক এই প্রয়াণ কী বিমূঢ়তায় রেখে গেছে আমাকে, আশা করি পাঠকমাত্রেই সেটা অনুমান করতে পারবেন। এই সময়টায় আমার পক্ষে নীরব থাকাও যেমন শক্ত, তেমনই কঠিন কিছু বলাও। তবু সম্পাদকের আগ্রহের কাছে পরাভূত হয়ে কোনোমতে এই সামান্য-কটি কথা লিখতে হলো। পাঠকেরা আমাকে যেন মার্জনা করেন। শঙ্খ ঘোষ
পঁয়ষট্টি বছর ধরে যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আর ষাট বছর জুড়ে যার সঙ্গে প্রতিদিনের নিবিড়তম সখ্য, প্রায় পঞ্চাশ বছর বিদেশবাসের দূরত্ব সত্ত্বেও যার সঙ্গে সংযোগ থেকে গেছে প্রায় প্রাত্যহিক সম্পর্কের মতো, তার আকস্মিক এই প্রয়াণ কী বিমূঢ়তায় রেখে গেছে আমাকে, আশা করি পাঠকমাত্রেই সেটা অনুমান করতে পারবেন। এই সময়টায় আমার পক্ষে নীরব থাকাও যেমন শক্ত, তেমনই কঠিন কিছু বলাও। তবু সম্পাদকের আগ্রহের কাছে পরাভূত হয়ে কোনোমতে এই সামান্য-কটি কথা লিখতে হলো। পাঠকেরা আমাকে যেন মার্জনা করেন। শঙ্খ ঘোষদিনটা ছিল ৭ অক্টোবর, একুশে আশ্বিন, বাংলামতে অলোকের সাতাশি বছরের জন্মদিন। দূরভাষে বহু দূর থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে আসছিল: ‘এবার তাহলে কী করব আমি? কী বলব? কীভাবে বলব?’
উদ্ভ্রান্ত সেই প্রশ্নটা যে আমারই উদ্দেশে সে-বিষয়েও ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কেননা, হির্শবার্গ থেকে সুদূর কলকাতায় ভেসে-আসা সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শুনে ঈষৎ অপ্রতিভ অলোক হঠাৎ নামিয়ে রাখে ফোন। তবে কি অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে আমারই কাছে পৌঁছেছিল ফোনটা? এই প্রশ্নের মীমাংসা আজও পর্যন্ত করতে পারিনি আমি, শুধু মনে পড়ে যাচ্ছে অলোকের একেবারে প্রথম কবিতার বই ‘যৌবনবাউল’-এর একটি লাইন: ‘কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে?’
অকারণ ছিল না তার এই অস্থিরতা। বিশ্বমতে ৬ অক্টোবর বিশে আশ্বিন ছিল অলোকের জন্মদিন। সেইদিন, বিশ্বনাগরিক এই একান্ত পারিবারিক মানুষটি জন্মদিনে নানাপ্রান্তের শুভেচ্ছা পাবার জন্য যখন প্রস্তুত এবং আকুল হয়ে আছে, ঠিক সেইসময় তার নিবিড় স্নেহভাজন ছোটো বোন কিটির আকস্মিক হৃদ্রোগে মৃত্যু হয়। মুহূর্তে যেন তছনছ হয়ে যায় সে।
প্রায় ছত্রিশ বছর আগে দিল্লিতে এক আকস্মিক ভয়ংকর পথ-দুর্ঘটনায় তার মেজো ভাইয়ের মৃত্যুর স্মৃতিতে যে-মানুষ কবুল করে: ‘সেই প্রথম আমার অনাহত ঈশ্বরবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল’, সেরকম কোনো দিন কি তবে ফিরে এল আবার? আবারও কি ফিরে আসছে এইসব লাইন: ‘তোমার সঙ্গে বোবা ঈশ্বর যবে/কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে?’
‘যৌবনবাউল’-এ আরেকটি কবিতায় ছিল: ‘বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;/তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে/আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?’ সেই থেকে পাঠকসমাজে বা একান্ত বন্ধুদের কাছেও ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসেবে তার পরিচয়। সে-বিশ্বাসের মধ্যে কত-যে ওঠা-পড়া, কত-যে বোঝাপড়া করতে করতে পথ চলেছে সে, সেটা তেমনভাবে লক্ষ করিনি কেউ। সন্দেহ নেই বহির্জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বারেবারেই তাকে নতুন করে বুঝতে হয়েছে তার ঈশ্বরকে। কিন্তু তবু, বুঝবার সেই পথে, প্রবল প্রতিঘাতে নতুন করে এক-একবার সামঞ্জস্যের পথ তো খুঁজতে হয়েছে তাকে। তবে কি সেইরকম এক খোঁজার পথে সাক্ষী রইলাম আমি, তার সেই উদ্ভ্রান্ত জিজ্ঞাসায়: ‘এবার তাহলে কী করব আমি? কী বলব? কীভাবে বলব?’২ চল্লিশের দশকের প্রায় সূচনা থেকে যেন ভিন্ন দুটো পরস্পরবিরোধী গোত্রে ভাগ হয়ে গিয়েছিল কবিতার লেখকসমাজ বা পাঠকসমাজ। একদিকে ছিল তারা, যাদের মনে করা হতো বাস্তব সংসারজীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত ভাবনায় মগ্ন থাকা আর অন্যদিকে যাদের বলা যেত সামাজিক চেতনায় সমৃদ্ধ কবি। এই দুইয়ের মধ্যে অনায়াস যাওয়া-আসা-করা তৃতীয়পক্ষও যে তৈরি হয়ে উঠছিল ক্রমশ, সেটা হয়তো অনেকের নজরে আসেনি। অলোকরঞ্জনের কাব্যজীবনের সূচনা থেকেই সে চিহ্নিত হয়ে যায় সমাজজীবনের পরিপন্থী আর সেই কারণে নিছক আত্মগত ঈশ্বরবিশ্বাসী এক কবি হিসেবে, এক দুর্বোধ্য কবি হিসেবে।
একেবারে সূচনাদিনের কথা ভাবলে এ-নালিশ হয়তো একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু কী মসৃণতায় আস্তে আস্তে সমাজ আর ব্যক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সে গড়ে তুলছিল, তার ধারাবাহিক বিস্ময়কর ইতিহাস হয়তো একদিন সবারই চোখে ধরা পড়বে। নিজে সে লিখেছে একবার:
‘ধুনুরি দিয়েছে টংকার’ (১৯৮৮) বইয়ের অন্তরঙ্গ পাঠক সহজেই ঠাহর করে নিতে পারবেন, কোন্ পরমা নিষ্কৃতির (catharsis) তাড়না এইসব কবিতায় মথিত হয়ে আছে। যদ্দূর মনে আছে, এই পর্বের উপান্ত্যেই আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর আর্তি জেগে উঠলে… এরই ফসল নিজস্ব এই মাতৃভাষায় (১৯৯০) যেন কী-একটা ঘোরে লেখা হলো। কিন্তু কোথায় নান্দনিক সমাধা, কোথায় কী! মার্কিন আগ্রাসনের দাপটে ঘনিয়ে এল গালফ্ যুদ্ধ, আমার জন্যে রেখে গেল পূর্বধার্য কাব্যমীমাংসার বদলে চ্যালেঞ্জসঞ্চারী কাব্যজিজ্ঞাসা। বিশেষত এই সংগ্রহের শেষ দুটি বইতে আমার প্রতীতি ও অনাস্থার সেই দোলাচল লুকিয়ে থাকেনি, আমার ঘনিষ্ঠ পাঠকদের কাছে এই তথ্যও গোপন থাকেনি যে জগৎজোড়া শরণার্থীদের সঙ্গেই আমি তখন থেকে অষ্টপ্রহর সম্পৃক্ত হয়ে আছি।
অলোক নিজেই এখানে তার কবিতাজীবনকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দিয়েছে। তাই এ-বিষয়ে আমাদের আর কিছু বলার হয়তো অধিকার থাকে না। কিন্তু তবুও একটু ঝুঁকি নিয়েই আমি বলতে চাই—মৌখিকভাবে বলেওছি ওকে কয়েকবার—যে, এখানে হয়তো নিজের ওপর একটা অবিচারই করছে সে। কেননা আমার ধারণা এই: জগৎজোড়া শরণার্থীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে বরাবরই সে। সেই সম্পর্কের বা সেই শরণার্থীচরিত্রের হয়তো বদল ঘটেছে মাঝে মাঝে। আস্তে আস্তে অনেক বিস্তারিত হয়েছে সেটা। ‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর’ আর্তি কি ১৯৯০ সালের আগে ছিল না তার কবিতায়? জগৎজোড়া শরণার্থীরা কি কেবল মার্কিন আগ্রাসনে গালফ্ যুদ্ধের পর থেকেই এসেছে? আমার তো মনে হয় নানা স্তরে, নানা নামে অলোকের কবিতা কেবলই আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর সাধনা করে গেছে। কেন বলছি একথা? সেটা হয়তো আরেকটু খুলে বলা দরকার।
‘যৌবনবাউল’, ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’, ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’, ‘ছৌ-কাবুকির মুখোশ’—অলোকের প্রথমদিকের এই চারটি বইয়ের বিভাব-কবিতাগুলি একটু লক্ষ করা যাক। ‘যৌবনবাউল’-এ আছে:
মরণমদমাতাল ডোম সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না,
গঙ্গাজলে উঠুক পাপ সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।
ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না,
এই কবিতার শেষদুটি লাইনে: ‘মানুষ গেলে নামের খনি,আমার পরে এই ধরণী/সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা॥–য় পৌঁছে অনেকে ভুলভাবে এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত উচ্চারণ বলে ভেবেছেন। কিন্তু ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’-র প্রথম লাইনটাই ছিল: ‘এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।/তুমি এক থেকে দশ গোনো আমি তারি মধ্যে দেবো তার মাথায় মুকুট’ থেকে শুরু করে শেষদুটি লাইন: ‘মন্ত্রের ভিতরে আমি তোমাদের দারুণ আরামে রেখে মন্ত্রের বাহিরে/শীতের উঠোনে কাঁপবো, ডেকো, ওকে ভয় করলে, সুন্দরের দরকার পড়লে॥’ পর্যন্ত লক্ষ করলে বোঝা যায় এই কবি কীভাবে নিজের বাইরে বেরিয়ে জগৎসংসারকে আপন করে নিচ্ছেন।
মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালোবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
হাফ-আখড়াই গাও—
… … …
আমি সেদিন বলেছিলাম ‘আল্লা মেঘ দে’ ‘আল্লা মেঘ দে’;
আমি তোমার দয়ায় আজকে আমার ঘরে হাজার মেঘের মজুত,
আমি সেসব মেঘের ধারায় অবিশ্বাসের সকল খোয়াই
মুছে দিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াবো খুব অপ্রস্তুত!
‘রক্তাক্ত ঝরোখা’-র এই লাইনগুলি পড়লে বোঝা যায় কীভাবে স্থানিক স্তরকেও অতিক্রম করে যেতে চাইছে এই কবিতা।
‘ছৌ-কাবুকির মুখোশ’ বইটিতে দেখব আমরা স্থানিক এক বিস্তার:
১
তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে
অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে
চূর্ণ করে দাও যতো অলীক সীমান্ত
আমি যদি কৃত্রিম প্রাচীর গড়ি
মৃদু পক্ষপাতে ভেঙে দিয়ো
ডানার অটুট রাখো ভাঙে যদি আমাদের প্রেম।
২
উত্তর অতলান্তিকে বৃষ্টি হলে
তোমার-এখানে কেন রৌদ্র হবে
জানি তুমি ডোরাকাটা স্বাতন্ত্র্য কায়েম রাখবে বলে
থেকে-থেকে কীরকম অচেনাসমান হয়ে যাও
এমন কি কেঁপে ওঠো তোমার ডানায় যদি হাত রাখি॥
কবি এখন প্রবাসে। বাধ্যতই, বা বলা যায় স্বভাবতই, তার ‘দুয়ার গেছে খুলে’। বার্লিনের শাদা-কালো খঞ্জন মিশে যায় ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে। এইভাবে তার চারপাশ থেকে সমস্ত ‘অলীক সীমান্ত’ খুলে যেতে থাকে।৩ সব বইতেই বিভাব-কবিতা লিখেছে অলোক তা নয়, তবে বিভাব-ধরনে দু-একটি কবিতা থাকেই তার বইয়ের সূচনায়, যাকে বলা যায় কবির অভিপ্রায়। কিন্তু সে-অভিপ্রায় যে সমস্ত কবিতাতেই প্রতিপন্ন হবে একথা কি জোর করে বলা যায়? আমরা বলতে চাই যে তা যায়, আর সেইখানেই অলোকের কবিতার মূল চরিত্রটা বোঝা যায়। কীভাবে বাইরের সমাজজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকে জড়িয়ে নিতে চাইছিল সে, কীভাবে সে স্থান আর কালকে বাড়িয়ে চলছিল, তার উদাহরণ ভরে আছে তার সমগ্র কবিতায়। তারই কিছু নমুনা আমরা পাব এইসব উচ্চারণে: ‘নাছ-দুয়ার খুলে তুমি পুরনো আঙ্গিক অনুযায়ী/পালিয়ে যেয়ো না,’ বা তার বিখ্যাত ‘‘পিতৃপুরুষ’’ নামের কবিতাটিতে যখন বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপনিষদ আবৃত্তির সময়ে নিজেকে মনে হয় যেন এক ‘সুভদ্র মাতাল’। বা ক্ষিতিমোহন সেনের ‘পিতা ন বোধি’ শুনে তার ভাবাসঙ্গে মনে আসে চৈতন্যদেব, যিশু, বুদ্ধ, কবীর, নানক, দাদূ, তুলসীদাসের ‘পরিশ্রমে বহতা নির্মলা নদী’ দেশ আর কালকে একত্র প্রসারিত করে দেওয়ার এই ধরন ‘যৌবনবাউল’ থেকেই তো অলোকের কবিতার স্বরূপ। পরবর্তী কাল শুধু এইটেকেই প্রসারিত করতে করতে চলেছে। ‘আয়না যখন নিশ্বাস নেয়’-এর মতো বইতে (১৯৯১) এই স্থান কাল শুধু আরো প্রসারিত হয়ে আছে। যেমন এর ‘‘পেরেস্ত্রোইকা’’ কবিতায় অনায়াসে আর্মেনিয়া আর আজারবাইজানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা এসে যায়। কিংবা যখন ভ্যান গঘ-এর ছবি দিয়ে আমস্টারডামের কোনো বিশেষজ্ঞের বিচার শুনতে শুনতে কবির মনে পড়ে ‘কৃষ্ণচূড়ার নীচে/ভিখিরি এক বাজাচ্ছে খঞ্জনি।’ এইভাবেই বাড়তে বাড়তে চলেছে অলোকের কবিতা। এক কালের সঙ্গে অন্য কালের যোজনায়, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের।
শ্রুতিলিখন। কৃতজ্ঞতা: স্নেহাশিস পাত্র
(শ্রীশঙ্খ ঘোষ এখন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া নিজের চোখে কিছু পড়তে পারেন না। কমপিউটারে বা নিজের হাতে একেবারেই লিখতে পারেন না। টেলিফোনে কথা বলাও এতটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ফোনের সামনে একজন কাউকে থাকতেই হয় তাঁর বলা কথাগুলি বুঝিয়ে দেবার জন্য। এরকম অবস্থায় তবু যে কিছু লেখা এখানে-ওখানে ছাপা হচ্ছে কিছুদিন ধরে, সেটা সম্পূর্ণতই হচ্ছে স্নেহাশিসের জন্য। কিন্তু তার দুরবস্থাও আশা করি অনুমান করতে পারবেন যদি আপনারা জানেন যে এ-লেখাটুকুর জন্যেও সময় লেগেছে আড়াই দিন!—নীলাঞ্জন হাজরা)
স্কেচ: হিরণ মিত্র
গ্রাফিক্স: মনোনীতা কাঁড়ার
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুনহে চিরসারথি - গুরুচণ্ডা৯
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 নিশীথ ষড়ঙ্গী, বাঁকুড়া | 45.124.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১০:১৫100742
নিশীথ ষড়ঙ্গী, বাঁকুড়া | 45.124.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১০:১৫100742ঋদ্ধ হোলাম,,,,,,প্রণাম,,,,,,
 সব্যসাচী মজুমদার | 42.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১৪:২৮100753
সব্যসাচী মজুমদার | 42.***.*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১৪:২৮100753যথাযোগ্য স্মরণ।অলোক আলোকের তৃতীয় ও বিশ্বে এ বক্তব্যই উপসংহার।
 কালিদাস আচার্য | 2405:201:8005:885e:c974:b76d:56d2:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১৪:৫৩100754
কালিদাস আচার্য | 2405:201:8005:885e:c974:b76d:56d2:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১৪:৫৩100754মন ছুঁয়ে গেল
-
Shoumyo Dasgupta | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ১৯:৪৯100756
এই কথাগুলি শোনার আগ্রহ ছিল, ভাবিনি তিনি এই শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় আদৌ বলতে পারবেন কি না কিছু। আপনাদের ধন্যবাদ।
সৌম্য দাশগুপ্ত
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2405:201:8008:c01e:5d5d:ca9a:d88a:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২০:২১100758
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 2405:201:8008:c01e:5d5d:ca9a:d88a:***:*** | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২০:২১100758একজন অসুস্থ কবি লিখছেন একজন সদ্যপ্রয়াত বন্ধু কবি সম্পর্কে। স্টানিং একটা পিস। অনেক ভাগ্য করে বাঙালি হয়ে জন্মেছি। অন্তত মরার আগে ভাবতে পারবে এই সব কবির জীবৎকালের কিছু দিন আমরা বেঁচে ছিলাম। এইসব লাইনের সাক্ষী ছিলাম। আনবিলিভেবল।
-
শিবাংশু | ২৯ নভেম্বর ২০২০ ২৩:৫৩100769
দুই প্রিয় কবির দৈবী সংলাপ। চতুর্থ মাত্রার বৃষ্টির মতো শব্দের ঝরে পড়া। তাঁরা আমাদের কাছে নৈসর্গিক মাত্রা হয়ে গেছেন বহুদিন। আচমন করে আমরা ধন্য হই ...
-
 sanjiban roy | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ০১:২৯100773
sanjiban roy | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ০১:২৯100773 ক্রমশই সুদূর হয়ে আশা বন্ধুতার সময়ে এই স্মৃতিভাষ আমাদের নতুন করে উজ্জীবিত করে , প্রিয় দুই কবির চিন্তন ও বহুমাত্রিক অনুভবের নির্ঝর আমাদের অস্থির যাপনেও জাগিয়ে তোলে সেই ঢেউ I
-
Anath Bandhab Sahoo | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ১০:২৪100781
অসাধারণ স্মৃতিমন্থন।..
সশ্রদ্ধ প্রণাম
 অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।লেখাই তো গেল না।কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারিনি | 2405:201:800a:b862:dd01:e186:ddb:***:*** | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ১৬:৪৬100792
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।লেখাই তো গেল না।কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারিনি | 2405:201:800a:b862:dd01:e186:ddb:***:*** | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ১৬:৪৬100792অলোকরঞ্জনের প্রয়াণ সর্বংসহা শঙ্খ ঘোষও সইবেন করে ভেেবে যখন কূলকিনারা
-
Jayanta Bhattacharya | ৩০ নভেম্বর ২০২০ ২৩:২০100798
ঋণী হয়ে থাকলাম এই ঋদ্ধ লেখার কাছে। গুরুচণ্ডালীকে ভালোবাসা।
 অলককুসুম বড়ুয়া | 202.142.***.*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:১৮100806
অলককুসুম বড়ুয়া | 202.142.***.*** | ০১ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:১৮100806একজন কবিই পারেন আর একজন কবির মানসজগতটিকে সমূহ আত্মস্থ করে তাকে সাধারণ্যে বিশদ করে দিতে। তাই শঙ্খবাবু যথার্থই অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে নিরীশ্বরতার দ্বন্দ্বসংকট কিংবা আত্মগততা থেকে বিশ্বজনের দ্বন্দ্বময় জাগতিক প্রতিবেশে পৌঁছে যাওয়া সরণির দিকনির্দেশ করে দেন অনায়াস কথনে।
 কৌশিক ব্যানার্জী | 2409:4060:2e01:5901::724a:***:*** | ০২ ডিসেম্বর ২০২০ ২০:১৬100866
কৌশিক ব্যানার্জী | 2409:4060:2e01:5901::724a:***:*** | ০২ ডিসেম্বর ২০২০ ২০:১৬100866ধন্য হলাম। ঋষিবাক্য, ঋষির সম্পর্কে। শেষে শঙ্খবাবুর শারীরিক পরিস্থিতি জেনে খুব বিমর্ষ হলাম
 মন্দার মুখোপাধ্যায় | 202.142.***.*** | ০২ ডিসেম্বর ২০২০ ২৩:৫৬100873
মন্দার মুখোপাধ্যায় | 202.142.***.*** | ০২ ডিসেম্বর ২০২০ ২৩:৫৬100873'আয়না যখন নি:শ্বাস নেয়' - এ লেখাও তো তাই।
'অলোক' এবং 'শঙ্খ' এ দু'জনকেই প্রণাম - আনখশির।
ধন্যবাদ 'গুরুচণ্ডালী'কে।
-
Mehedi Hasan | ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ ২৩:৫২101004
ভালো লেগেছে।
 অনির্বাণ বব মজুমদার | 2401:4900:3141:31e8:b0ae:96c3:35d9:***:*** | ১০ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:১৯101035
অনির্বাণ বব মজুমদার | 2401:4900:3141:31e8:b0ae:96c3:35d9:***:*** | ১০ ডিসেম্বর ২০২০ ০০:১৯101035গুরুত্বপূর্ণ লেখা। ধন্যবাদ স্নেহাশিস ... ধন্যবাদ গুরুচণ্ডা৯ !
-
শ্রীমল্লার বলছি | ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ২৩:৪৬735040

- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)
(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, অরিন, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
















