-
 বুলবুলভাজা আলোচনা সমাজ
বুলবুলভাজা আলোচনা সমাজ
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ৭৬৫৪৩২১
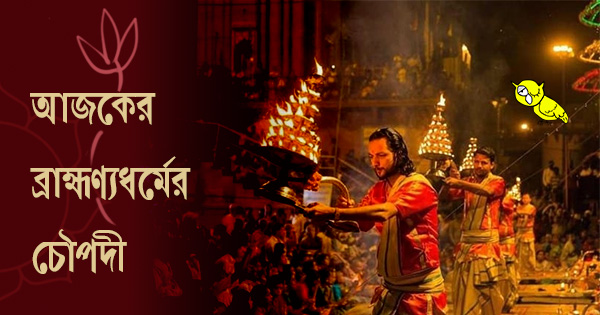
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - শেষ পর্ব - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ৪৬০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, Ranjan Roy)সাভারকর স্পষ্ট করছেন যে পূণ্যভূমির অর্থ একটি জাতির নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উপজিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, এবং মানসিক গঠনে সেই উত্তরাধিকারকে বহন করা। তাই শুধু ধর্ম নয়, ভাষা এবং ইতিহাস এর অন্যতম অঙ্গ। সেই সংস্কৃতিকেই উনি বলছেন ‘হিন্দুত্ব’। এর মুখ্য অঙ্গ হল ইতিহাস, তাতে বেদ এবং পুরাণকথাও সামিল। শুধু তাই নয়, বৈদিক সভ্যতা থেকে শুরু। এবং একই আইন-কানুন, আচার -অনুষ্ঠান, রীতি-রেওয়াজও এই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ... ...
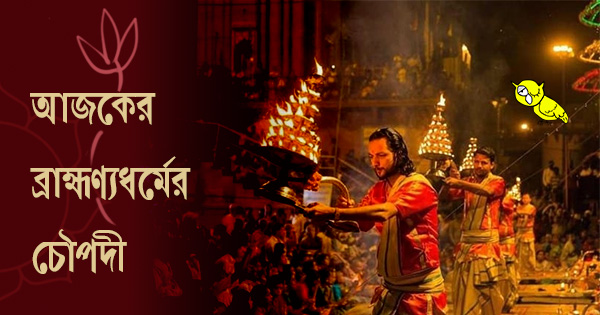
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব ষোল - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ | ৪২৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Faruk Munshi, albert banerjee)সাভারকরের মতে সমস্ত হিন্দুজাতি সেই সিন্ধুদেশ এবং বৈদিক কাল থেকে পিতৃপুরুষ ক্রমে একই রক্তধারার বন্ধনে আবদ্ধ। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে সত্যিই কি সমস্ত হিন্দুদের শিরায় একই রক্তের ধারা বইছে? তাদের কি একটি জাতি বলা যায়? তো সাভারকরের উত্তর হল— আজকের বিশ্বে ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান বা চাইনিজদের রক্তও কি আগের মত শুদ্ধ রয়েছে? ওরা যদি জাতি হয় তো হিন্দু কেন নয়? ... ...
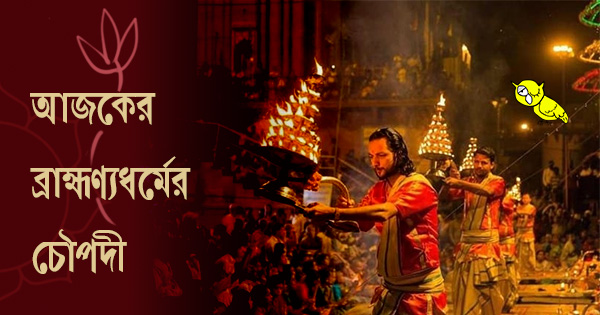
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব পনেরো - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৩ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৫৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (পাগলা গণেশ)সাভারকর প্রথমে প্রশ্ন তুললেন –নামে কিবা আসে যায়! উত্তরে বললেন—অনেক কিছু আসে যায়; জুলিয়েটকে যদি রোজালিন্ড বলে ডাকা হয় বা ম্যাডোনাকে ফতিমা, অথবা অযোধ্যাকে হনলুলু—তাহলে কি একই অনুভূতি প্রকাশ পাবে? অবশ্যই নয়। মহম্মদকে ইহুদী বললে কি তিনি খুশি হতেন? তাই হিন্দুত্ব, হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দ নিয়ে তাঁর বিচার শুরু হল। বললেন ‘হিন্দুত্ব’ একটি শব্দ মাত্র নয়, এটি আমাদের ইতিহাস। খালি আধ্যাত্মিক ইতিহাস নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতি, যুগ যুগ ধরে জীবনযাপনের যে ঐতিহ্য যে মূল্যবোধ—তার পূর্ণরূপ। হিন্দুধর্ম এর একটি সাবসেট, বা ক্ষুদ্র অংশ। আবার সনাতন ধর্ম বলে যা চালানো হয় তা বিশাল বৈচিত্র্যময় হিন্দুধর্মের একটি অংশ মাত্র, পুরোপুরি হিন্দুধর্ম বা তার একমাত্র রূপ নয়। আগে হিন্দু এবং হিন্দুস্তানের উৎস বোঝা দরকার। ... ...
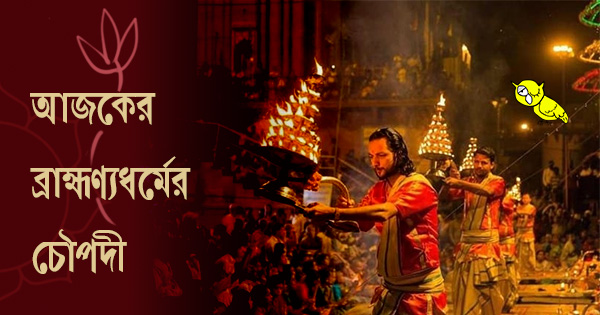
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব চোদ্দ - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০১ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৮৬ বার পঠিত“পারস্যে” ভ্রমণকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ গীতার নীতিবোধকে স্পষ্ট বিদ্রূপে বিঁধছেন—“গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এইরকম একটি উড়োজাহাজ – অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল—যেখানে মারেই-বা কে, মরেই- বা কে, কেই-বা আপন কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে । সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে”। ... ...
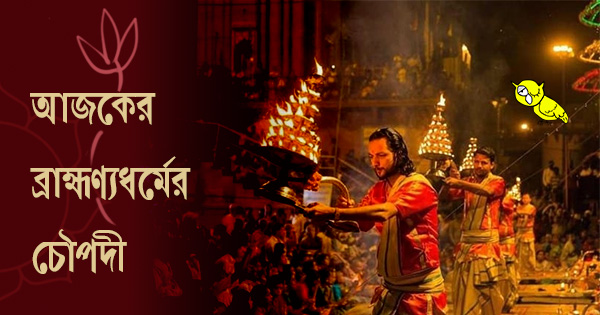
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব তেরো - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৪১৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (:), হীরেন সিংহরায়)বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘পারাপার’ উপন্যাসে একটি চরিত্র বিমানের সন্দর্ভে বলেছেন যে গীতা হোল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য! গীতার বেশিরভাগটাই অনুষ্টুপ এবং অল্প একটু অংশ ত্রিষ্টুপ ছন্দে লেখা। কিন্তু কাব্যগুণ? ভিন্নরুচির্হিঃ লোকাঃ। ... ...
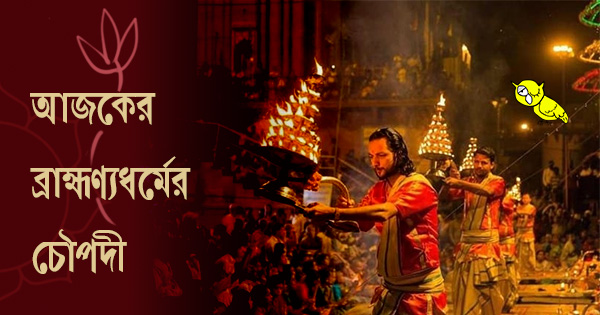
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব বারো - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৪৪৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (Ranjan Roy, Faruk Munshi, Ranjan Roy)আমার প্রশ্ন যদি সবই ব্রহ্মময় হয়, যদি ব্রহ্মের সঙ্গে নম্বুদ্রিব্রাহ্মণ শংকরাচার্য্য ও শূদ্রের কোন ভেদ না থাকে তাহলে তাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় শাস্তি দেওয়ার বিধান কেন? তাহলে কি ব্যবহারিক দুনিয়া শংকরাচার্য্যের জন্যেও বিশেষভাবে অস্তিত্ববান? ... ...
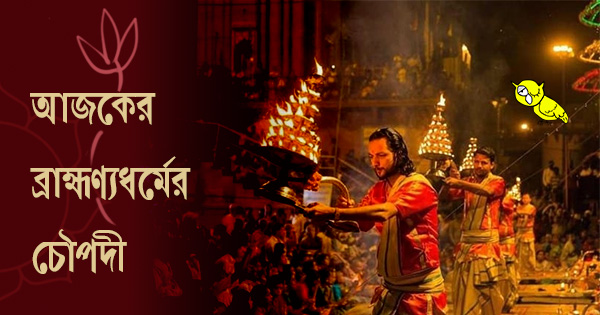
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব এগারো - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৩৭০ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (পাগলা গণেশ)দেখা যাচ্ছে বেদ ও স্মৃতির অনেক শ্লোক পরস্পরবিরোধাভাসী এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদে অনেক দার্শনিক স্কুল গজিয়ে উঠেছে। এমনকি একই ব্রহ্মসূত্র এবং তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক আদি উপনিষদে আস্থাশীল দার্শনিকেরাও নিরাকার ব্রহ্মের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন না। মহাভারতের বনপর্বে বকরূপ ধর্মের কঃ পন্থা প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন-“বেদাঃ বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়োর্বিভিন্না, নাসৌমুনির্যস্য মতংনভিন্নম”। এককথায় নানা মুনির নানা মত। ... ...
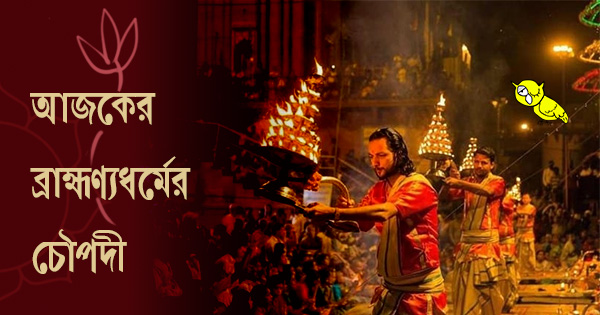
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব দশ - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৮৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (বর্ণনা হালদার)শংকর বলছেন—অবিদ্যা সৎ-অসৎ কোনটাই নয়, এ হল অনির্বচনীয়। মানে অবিদ্যার অস্তিত্ব আছে কি নেই—সেটা বলা মুশকিল। এ হল এমন যা শব্দ দিয়ে বোঝানো মুশকিল। রামানুজ বলছেন—এসব ফালতু কথা। এই অবিদ্যাটি থাকেন কোথায়? একি জীবের ব্যক্তিচেতনায়, নাকি ব্রহ্মের অনন্তচেতনায়? ... ...
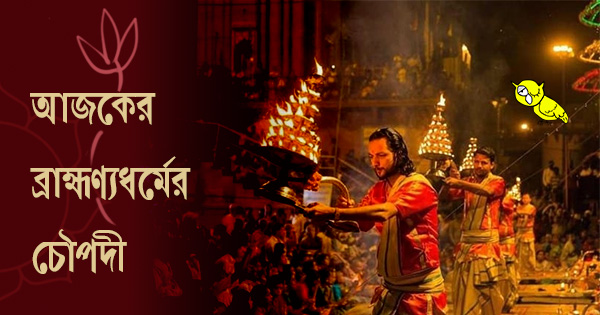
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব নয় - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৭৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (Mridha, Ranjan Roy)এই অবিদ্যার কারনেই আমাদের দৃষ্টি আবিল হয়, আমরা রিয়েলিটি বলতে চৈতন্যস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দেখার বদলে ব্রহ্ম এবং বস্তুজগত –এই দুই বাস্তবের চক্রে ফেঁসে যাই। অতএব, আসল দোষী হল ওই ‘অবিদ্যা’। এই অবিদ্যাও ব্রহ্মের মতন ‘অনাদি’। কেউ কেউ ‘অবিদ্যা’ এবং ‘মায়া’কে একই মনে করেন। দেবীপ্রসাদও কখনও কখনও এই দুটি পদকে একে অপরের বদলে পালা করে ব্যবহার করেন। ... ...
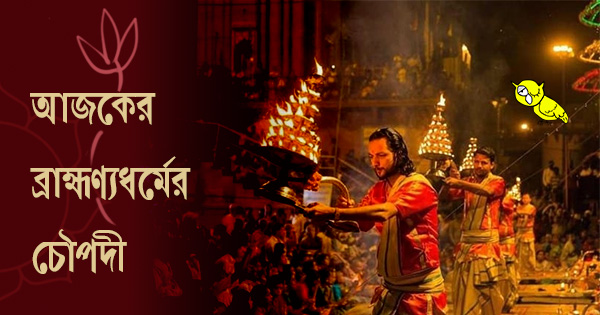
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব আট - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৪৭ বার পঠিতঅবিদ্যার দুটো কাজ। এক, আসল রূপকে আবৃত করা। যেমন মেঘ এসে সুর্যকে ঢেকে দেয়। দুই, মায়াজালের মত কাল্পনিক কিছু সৃষ্টি করা। যেমন সর্প-রজ্জু উদাহরণে বিভ্রান্তির ফলে দড়ির আসল চেহারা আবৃত হয়। তারপর সেখানে সর্প বলে এক ইমেজ সৃষ্টি হয় যা আসলে ওখানে নেই, যা পুরোপুরি কাল্পনিক। অবিদ্যা ও মায়া একই প্রক্রিয়ার দুটো অংশ। অবিদ্যার ফলে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, সত্য আবৃত হয় আর তার জায়গায় যা দেখতে পাওয়া যায় তাই হল মায়া। ... ...
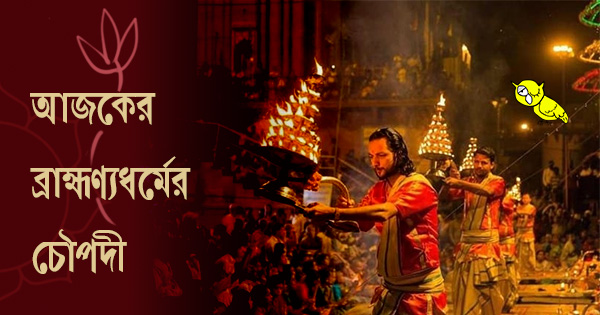
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব সাত - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৩৬৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (অরিন)এই দর্শনটির নাম অদ্বৈত বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা। এর প্রবক্তা হলেন আদি শংকরাচার্য, যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গী ওঁর আগে বেদবিরোধী বৌদ্ধদর্শনের মহাযানী শাখার দুটি স্কুল—শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বিকশিত হয়েছে।তাই ওঁর অদ্বৈত বেদান্ত মতকে অনেকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত’ও বলে থাকেন। ... ...
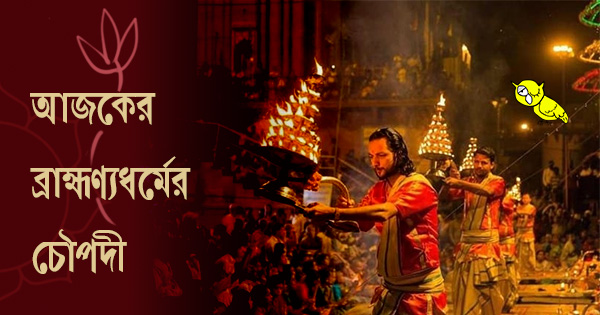
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব ছয় - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৭৪৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ১১, লিখছেন (পাগলা গণেশ, হীরেন সিংহরায়, বর্ণনা হালদার)আমরা দেখলাম মহর্ষি মনু কোথাও গরুকে মাতা বলেননি। গো-হত্যাকে মহাপাতক বলেননি, গোহত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ডের বিধান দেননি।আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখছি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গরুকে গোধন বলছেন। সর্বত্র দেখছি গরু সম্পত্তির একক। মহাভারতে বিরাট পর্বে ‘উত্তর গোগৃহ’ রণে গরু লুঠেরাদের থেকে বিরাট রাজার কয়েক হাজার গরুকে বাঁচাতে অর্জুন (বৃহন্নলা) গান্ডীব তুলে নিলেন। গরু মাতা হলে কি তাকে বিক্রি করা বা দান দেয়া যায়? এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ‘হিন্দুত্ব’ ধারণার প্রণেতা সাভারকর কখনই গরুকে মাতা বলতে রাজি হননি। বলেছেন চারপেয়ে পশুটি উপকারী, কিন্তু আমার মা হবে কি করে? তাহলে কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে গরু গোমাতা হচ্ছে বা তার বধের জন্যে মানুষের প্রাণ নেয়া হচ্ছে? ... ...
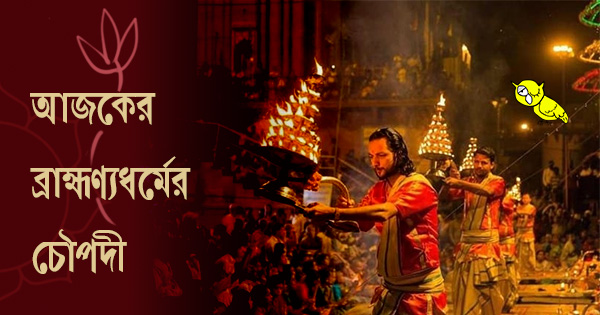
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব পাঁচ - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ২৮ নভেম্বর ২০২৫ | ৭৫৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ১১, লিখছেন (sangeeta das, Ranjan Roy, sangeeta das)কী মুশকিল! কূর্ম এবং বরাহও তো অবতার, একই লাইনে; মানে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে। তাহলে ওদুটো খাওয়াও ছাড়তে হবে নাকি? এসবই নাকি শাস্ত্রে মানা রয়েছে। কোন শাস্ত্রে? বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত কোথাও গরুকে মাতা বলতে দেখলাম না। তাই মনুস্মৃতিতেই খোঁজ করা যাক। কারণ, আগেই বলা হয়েছে—যা আছে তা মনুস্মৃতিতেই আছে, এবং যা এতে নেই তা কোথাও নেই। ... ...
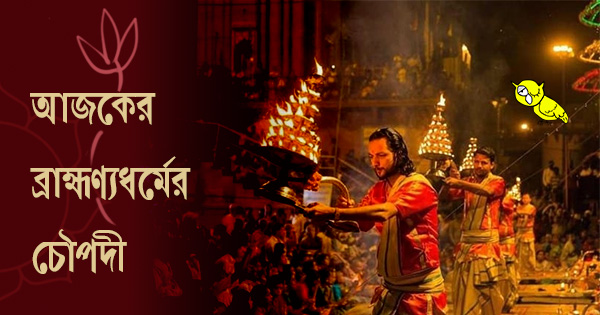
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব চার - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ২১ নভেম্বর ২০২৫ | ৬৯০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, sangeeta das, sangeeta das)গোড়ায় সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হচ্ছে স্রষ্টা নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ হলেন, বাকি অর্ধে নারী। তার থেকে বিরাট পুরুষ সৃষ্ট হল, যিনি মনুর স্রষ্টা।(১/৩২)। তাহলে তো নারী পুরুষ সমান সমান, কোন পক্ষপাতের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পুরুষ যখন সামাজিক প্রথা, আইনকানুন বানাতে শুরু করল তখন নিজেদের দিকে টেনে খেলল। নারী আর সুখে দুঃখে সমান অংশীদার রইল না। ‘ওরা’ এবং ‘আমরা’র খেলা শুরু হয়ে গেল। ‘এ বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী তুমি আছ, আমি আছি’ শুধু কবির ইচ্ছেয় রয়ে গেল। মনুসংহিতায় এবার সেই খেলাটাই পর্বে পর্বে দেখব। ... ...
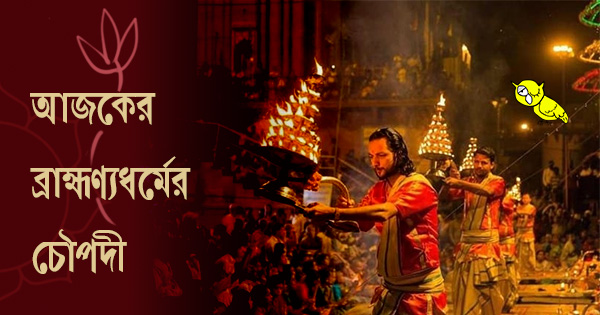
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব তিন - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৯ নভেম্বর ২০২৫ | ৫৫৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (Faruk Munshi, Ranjan Roy, হীরেন সিংহরায়)মনু বলছেনঃ নিজধর্ম গুণবর্জিত হলেও ভাল, পরের ধর্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলেও ভাল নয় , অপরের ধর্মানুসারে জীবনধারণ করলে (মানুষ) তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হয় (১০/৯৭)। খেয়াল করুন , ভগবদগীতাতেও ঠিক এটাই বলা হয়েছে। “শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ।। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতিধর্ম যদি নিকৃষ্টও হয়, তবু অন্য জাতির উন্নত ধর্ম পালনের চেয়ে নিজের জাতিধর্ম পালনে মৃত্যুবরণ শ্রেয়স্কর। ... ...
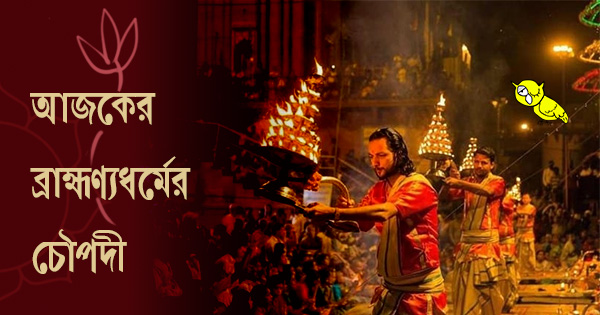
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব দুই - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৩ নভেম্বর ২০২৫ | ৬৩৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (Ranjan Roy, অরিন, Aditi Dasgupta)মনুসংহিতাতে বাস্তবে কী বলা হয়েছে তা নিয়ে খতিয়ে না দেখেই বাজারে অনেক কথা বলা হয় । আমি চেষ্টা করব এই স্বল্প পরিসরে মনুসংহিতার স্বরূপের বর্ণনা করে তিনটি ভাগে খাদ্যাখাদ্য, জাতিপ্রথা এবং নারীর অবস্থান নিয়ে উনি কি বলেছেন তা তুলে ধরতে। মনে হয় জাতিপ্রথা নিয়ে আগে কথা বলা উচিত। কারণ, ওটাই আমাদের সমাজের প্রাচীন কাঠামো। খাদ্যাখাদ্য বা নারীর অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে ওই কাঠামোকে মেনে। ... ...
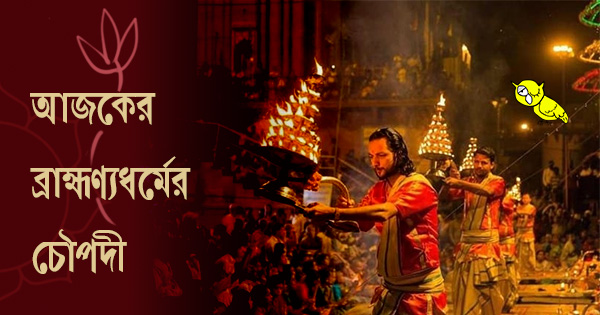
আজকের ব্রাহ্মণ্যধর্মের চৌপদী - পর্ব ১ - রঞ্জন রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৮ নভেম্বর ২০২৫ | ৯৮৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৩, লিখছেন (dc, swapan, স্বপন সেনগুপ্ত ( ঝানকু ))বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এক এক করে চারটেকেই খুঁটিয়ে দেখা—আজকের আধুনিক ভারতের বিকাশে এগুলো কতটুকু উপযুক্ত। সবচেয়ে আগে জানা দরকার মনুস্মৃতিতে কী আছে? মায়াবাদের দার্শনিক ভিত্তি কতখানি মজবুত? শংকরাচার্য দলিতদের ব্যাপারে কী বলেন? গীতায় বর্ণাশ্রম নিয়ে কী বলা হয়েছে? এবং সাভারকরের হিন্দুত্বের তত্ত্ব আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কতখানি খাপ খায়। ... ...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প জমানায় গর্ভপাতের অধিকারের হাল-হকিকৎ - নূপুর রায়চৌধুরী
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০৪ অক্টোবর ২০২৫ | ৩৩৫ বার পঠিত‘’রো বনাম ওয়েড’’ মামলার পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যভেদে গর্ভপাতের সুযোগের দৃশ্যপট উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক রাজ্যের আইনসভাই নতুন নতুন গর্ভপাত বিধিনিষেধ তৈরি করেছে এবং অনেকে আবার বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর করতে শুরু করেছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, কিছু রাজ্য গর্ভপাত পুরোপুরি নিষিদ্ধ বা অত্যন্ত কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করেছে; আবার কিছু রাজ্যে গর্ভাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে (৬, ১২, ১৮ সপ্তাহ বা ভ্রূণের প্রায় কার্যকর হওয়ার মতো সময় অর্থাৎ ২৪ সপ্তাহের কাছাকাছি) গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যরা আবার গর্ভপাতের সুযোগ বজায় রেখেছে বা প্রসারিত করেছে। মোদ্দা কথা গর্ভপাতের জন্য নির্দিষ্ট গর্ভকালীন বয়সসীমা সম্পূর্ণরূপে সেই রাজ্যের উপর নির্ভর করে যেখানে এই প্রক্রিয়াটি চাওয়া হচ্ছে। ... ...
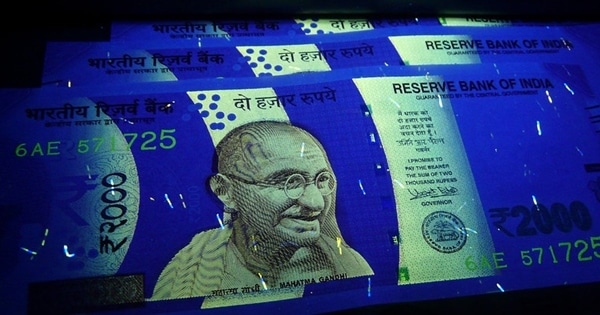
গান্ধীজির পথ বাংলার পথে - সোমনাথ রায়
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ০২ অক্টোবর ২০২৫ | ৬১২ বার পঠিতখেয়াল করলে দেখা যাবে, গান্ধীজির লড়াইয়ের যে মূল সূত্রগুলি যেগুলো বস্তুত বাংলার সমাজেরই নিজস্ব অর্জন ছিল। গান্ধীজির আগেও বাংলার মানুষ এই পথগুলিতে ঘোরাফেরা করেছেন। বিশেষ করে, বঙ্গভঙ্গের পর যখন বাংলার সমাজ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তখন এমন অনেক আন্দোলনই গড়ে তোলা হয়, যার কথা পরে গান্ধীজি সারাদেশকে বলেছেন। আমরা প্রথমে আসতে পারি চরকার প্রসঙ্গে। গান্ধীপন্থা ও চরকা অবিচ্ছেদ্য। ভারতের জাতীয় পতাকার এক জনপ্রিয় পরিকল্পনায় তার কেন্দ্রে ছিল চরকা। গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছিলেন চরকাকে। কিন্তু, গান্ধীজির আগেই ১৯০৬ সালের শিল্পমেলায় শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী দেবী বাঙালিকে চরকায় সুতো কাটবার পরামর্শ দেন। (সূত্র- শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ্ম গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী)। লক্ষ্যণীয় যে তিনি বলেন, চরকা কোনও নতুন কাজ নয়, কিছুদিন পূর্বেই (নবাবি শাসনে) বাংলার মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে চরকায় সুতো কাটতেন। চরকায় সুতো কাটা মেয়েদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করবে এবং ম্যানচেস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। আলাদা করে যে খেয়াল করার, হিরণ্ময়ী দেবী এখানে বাংলার পুরোনো অর্থনীতির কথা বলেছেন। প্রাক ব্রিটিশ বাংলা এক শিল্পায়িত কারিগিরি সমাজ ছিল, নারীদের আর্থিক ক্ষমতাও ছিল- চরকার প্রসঙ্গে তিনি এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। গান্ধীজির ভারতের রাজনীতিতে আসীন হওয়ার আগের দশকের কথা এইটি। ... ...
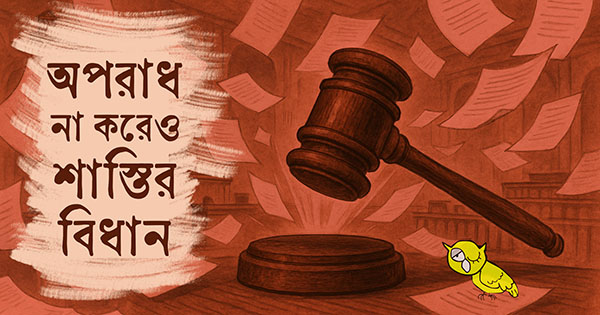
অপরাধ না করেও শাস্তির বিধান - শুভজিৎ সিংহ
বুলবুলভাজা | আলোচনা : সমাজ | ১৫ মে ২০২৫ | ১০১৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Somenath Guha, শর্মিলী , নারায়ন দাস ভৌমিক )একমাস পেরিয়ে গেছে, ৩ এপ্রিল (২০২৫) শীর্ষ আদালতের এক সিদ্ধান্ত বয়ে এনেছে গভীর সামাজিক অভিঘাত। বিপুল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্য বাতিল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকৃত (এসএসসি) ২০১৬-র পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই। পাঁচ বছরেরও বেশি চাকরি করার পর রাতারাতি চাকরিচ্যুত হতে চলেছেন ২৫৭৩৫ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। জালিয়াতিতে অভিযুক্ত রাজ্য সরকারের অতি উচ্চতর পদাধিকারীরা। সংশ্লিষ্ট (সাবেক) মন্ত্রীসহ তাঁরা জেলে বন্দি রয়েছেন। নানান সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের নির্যাস– এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিপুল দুর্নীতির কারণে এবং কমিশনের অসহযোগিতায় জালিয়াত বা দোষী এবং নির্দোষী নিয়োগপ্রাপ্তদের বাছাই করার তথ্যপ্রমাণ ছিল না, তাই সমগ্র প্যানেল বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে আদালত। সম্প্রতি রাজ্য সরকার রিভিউ পিটিশনের মাধ্যমে রায়টি ফের পর্যালোচনার জন্য আবেদন জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। ... ...
- পাতা : ৭৬৫৪৩২১
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।












