-
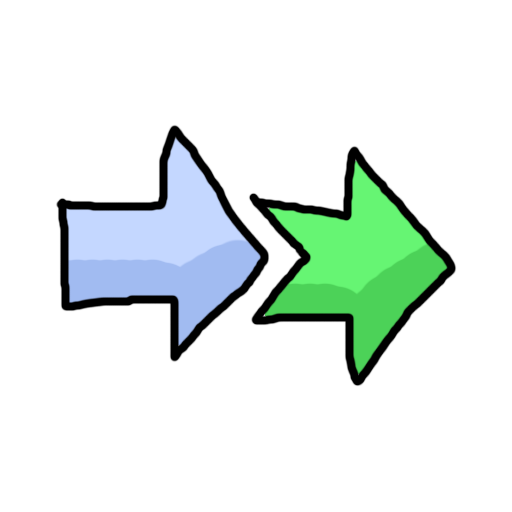 বুলবুলভাজা ধারাবাহিক
বুলবুলভাজা ধারাবাহিক
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ৫৫৫৪৫৩৫২৫১৫০৪৯৪৮৪৭৪৬

মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ১৬৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)তারপর আর কী? কীভাবে সেদিন রক্ষা পেলাম, ট্রেন ধরলাম সে এক কান্ড, তবে কখনোই চাইবোনা যে ঐ ধরণের ঘটনার কোনোভাবে পুনরাবৃত্তি হোক। এই ফিল্ডের শুরুতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। দার্জিলিংয়ে তখন হামেশাই বন্ধ ডাকা হত বলে সিকিমে ওঠার সময়ে বিদ্যুৎ বাবু সিকিম থেকেই জিপ বুক করেছিলেন। কথা ছিল তারা শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিয়ে যাবে। কিন্তু আন্দোলনের আবহে স্থানীয় গাড়ি চালক সঙ্ঘ আমাদের গাড়িগুলো রাস্তায় অবরোধ করে রেখেছিল। ... ...

দিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : অর্থনীতি | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৩০৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৪, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)ব্যাঙ্কার ও ইনভেস্টরদের যৌথ কমান্ড ফার্স্ট ব্র্যান্ডসের অফিসে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র ডিরেক্টরদের আইনি প্রতিরক্ষা বাহিনী যুদ্ধে নামলেন- তাঁরা জানালেন সম্মুখ সমর নয় , কোন ডিরেক্টরের গায়ে হাত দেওয়া দূরের কথা, ডেকে পাঠানো যাবে না,। তাঁরা কেউই সরাসরি বাক্যালাপ করবেন না। জে পি মরগান বা ব্ল্যাকরকের ব্যাঙ্করাপটসি লইয়ারদের আপাতত আলোচনা করতে হবে ফার্স্ট ব্র্যান্ডের সিনিয়র অফিসারদের সুরক্ষা দলের সঙ্গে - তাঁদের মধ্যে প্রধান সুবিখ্যাত আইনি সংস্থা ব্রাউন রাডনিক এবং কোল শোলৎস । জে পি মরগান , জেফরিজের ঋণ উদ্ধারকারী উকিলেরা চমকে গেলেন – ওহাইওর এই প্রাইভেট কোম্পানির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকার এতগুলি খ্যাতনামা আইনজ্ঞ যাদের একদিনের ফি লক্ষ ডলার । এ টাকা আসে কোথা হতে ? এমনও দিন আসতে পারে ভেবেই কি ফার্স্ট ব্র্যান্ডের পরিচালক বৃন্দ তাঁদের অস্ত্রাগারে তূণীর সঞ্চয় করে রাখছিলেন? ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৯৩ বার পঠিতপরীক্ষা শেষ। ফিরছি। কলেজ গেট থেকে রিক্সা ধরলে ছয় টাকা। আর নেদেরপাড়ার মোড় থেকে ধরলে শেয়ারে মেলে। দেড় টাকা করে তিন টাকা। কম বেতন। হাজার আষ্টেক টাকা। তার উপর 'ভাষা ও চেতনা সমিতি' করি। সংগঠনের খরচ চালিয়ে মাসের শেষে পকেটে কিছু থাকে না। তখন কৃষ্ণনগরে শেয়ারে রিক্সা চাপা যেতো। এ-নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে একটা বিখ্যাত গান আছে। রিক্সায় ফিরছি। দেখি একদল ছেলে আমাকে দেখে খুব গাল দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি, সেই ছেলেটি মধ্যমণি। তা স্টেশনে এসে পিছনের দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছি। ছেলেটি দলবল নিয়ে হাজির। আমাকে খুব গালাগাল চললো। বললো, ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছি টুকতে না দিয়ে। কয়েকজন ওদের সমর্থন করলেন। ছি ছি টুকতে দেয় নি, ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে। আমি প্রতিবাদ করলাম, কী বলছেন, এভাবে পরীক্ষা হয়। আমরা টুকছি তোর বাপের কী? বাকিরা তো কিছু বলে না, তোর কেন এতো-- বলে মারতে শুরু করলো দলবল মিললে। কিছুদিন আগেও ছাত্র রাজনীতি করেছি, সাংবাদিকতা পেশা ছেড়েছি, কিন্তু করছি, আমিও রুখে দাঁড়ালাম। দু এক ঘা পাল্টা দিলাম। সবাই বিপক্ষে। শুধু এক গরিব মহিলার কন্ঠস্বর শোনা গেল, কলেজের মাস্টারকে মারছে। আর তুমরা দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে দেখছো। ... ...

মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৩৭৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)কয়েক বছর ধরেই কখনও উড়িষ্যার দার্জিলিং, আবার কখনও উড়িষ্যার কাশ্মীর নামে দারিংবাড়ি নামটা শুনছিলাম। হঠাৎ একদিন আমাদের প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ এসে বলল, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে ও ফিল্ডে গিয়েছিল দারিংবাড়ি। প্রদীপ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ স্কলার। জায়গাটার যা বর্ণনা ও দিল, ঠিক করলাম এবারে যেতেই হবে। চারমাস আগে রেলের বুকিং শুরু হয়ে যায়। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৩৩৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (কৌতূহলী, Eman Bhasha, albert banerjee)বর্ধমান স্টেশনের সামনের দেওয়ালে লেখা ছিল সবচেয়ে কঠিন। পায়খানা আর পেচ্ছাপে ভর্তি। একটা দিনের কথা মনে আছে ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪। মোবারক বিল্ডিং পার্টি অফিস থেকে ১০ টাকা দিয়েছে টিফিন চা ইত্যাদির জন্য। মেহেদি বাগান বলে একটা কুখ্যাত জায়গা ছিল। কংগ্রেসের ঘাঁটি। সেখানে অসাধারণ সর টোস্ট বানাতো। ডিম টোস্ট আট আনা হল টোস্টও তাই। চা বোধহয় চার আনা করে ছিল। পাঁউরুটি চার আনা। স্লাইস রুটি তখনও আধিপত্য বিস্তার করে নি। তা পোস্টার লেখা চলছে। একটু বাকি। হঠাৎ সাইকেল একজন এসে বললো, এক্ষুণি পার্টি অফিস চলে যেতে। স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধী লেখা হয়ে গিয়েছিল, জবাব চাই, লেখা বাকি ছিল। কোনোক্রমে লিখে ছুটলাম সাইকেল নিয়ে। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২৭ বার পঠিতমারতেও পারি না। মারার অভ্যাস আমার ছিল না। দুটোকে টেনে আলাদা করি। বিরাট কঠিন কাজ। কিন্তু পাঁচ ছটা টিউশন পড়িয়ে যা পাই, একজায়গায় তার সমান পাবো, থেকে গেলাম। টিফিন ভালো। নুডলস, চিঁড়ের পোলাও ইত্যাদি। তবে নিরামিষ। আমিষ নিরামিষ ব্যাপারটাই তখন ভাবা ছিল না। খাবার খাবার। তার আবার আমিষ নিরামিষ। মাছ ডিম দৈনিক খুব কম বাড়িতেই হতো। সরকারি ভালো চাকুরে আর ঠিকাদার ছাড়া হতো বলে মনেও হ্য না। যা পেত বা পেতাম হাসিমুখে সবাই খেতো। খালি হোস্টেলে গেরান্ড/গ্রান্ড ফিস্টের দিন--একটু মাংস নিয়ে আদিখ্যেতা ছিল। পিস ছোট কেন? আরেকটু ঝোল দাও। একটা আলু হবে? এইসব আবদার ছিল। ছিল রঙ্গরসিকতা। ব্যাটা তোর পিসটা একটু বড় মনে হলো। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ | ৪৯৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (পম্পা ঘোষ, r2h, Eman Bhasha)রাধিকা এসেছে 'রাধা' শব্দ থেকে। রাধার আগমন আবেস্তা 'রাধ' থেকে। রাধ মানে প্রেমিক। প্রথম ব্যবহার কাশ্মীরে। বাংলায় রাধ-এর সঙ্গে আ যোগ করে রাধা। রাধা, রাধিকা, রাই-- কত কত আদরের নৌকা ভাসানো নাম। সায়ন মনে করিয়ে দিলেন কাদামাটির দিনগুলোতে কেষ্টযাত্রায় রাধা আর কৃষ্ণের প্রেম। কানু বিনে গীত নাই-- কিন্তু কৃষ্ণকে যাত্রা খুব কম হতো গ্রাম বাংলায়। রাধার সঙ্গে যে কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল, সেটা একটা মাত্র নাটকে দেখানো হয়েছে, পণ্ডিত প্রবর রূপ গোস্বামীর নাটকে। ললিত মাধব। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫০০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (রঞ্জন রায়, দ, Eman Bhasha)আজ খারাপ লাগে, ভুলোকে ছেড়ে এলাম কী করে? ভুলো আমাকে পাগলের মতো ভালবাসতো। সেহারাবাজারে নবম দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার সঙ্গে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরের স্কুলে হেঁটে হেঁটে চলে যেত। বিডিআর ট্রেনে চাপলে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াত। সারাদিন স্কুলের গেটে বসে থাকতো। সহপাঠীরা আওয়াজ দিত, তোর বন্ধু বসে আছে। বর্ধমান শহরে পড়তে আসার সময় তাই সতর্ক থাকতাম। চুপিসারে আসতাম যাতে ভুলো টের না পায়। কিন্তু ভুলো সন্ধ্যায় ফেরার সময় নুরপুর ক্যানেল ধারে বসে থাকতো। আমাকে নিয়ে ফিরবে! বর্ধমান শহরে আসার সময় ভুলোকে ছেড়ে আসা কঠিন ছিল। তবু তো পেরেছি। আজ আর পারি না। আমার সিরো এবং পাড়ার পাঁচটি কুকুরকে ছেড়ে এখন বাইরে রাত কাটাতে খুব কষ্ট পাই। ... ...

মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১০ জানুয়ারি ২০২৬ | ৩৭০ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়, Sara Man)তবে গুহা দেখার আগে আরও কিছু অত্যাশ্চর্য জিনিসের কথা বলে নিই। মৌলিন্নং থেকে বেরিয়ে খুব সকালে প্রথমে আমরা সেখানেই গিয়েছিলাম। জিনিসটা হল জীবন্ত সেতু। মানে বনের গাছ কেটে তার কাঠ দিয়ে বানানো সেতু নয়। নদীর ওপরে রীতিমত জ্যান্ত গাছের ঝুরি পাকিয়ে বানানো ঝুলন্ত সেতু। যদিও অনেকটা হেঁটে যেতে হয়, সিঁড়িও প্রচুর। তবে কষ্ট না করলে কী আর কেষ্ট মেলে? ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১০ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫৯৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (পম্পা ঘোষ , পম্পা ঘোষ, Ranjan Roy)এখানে চারপাশে পাইস হোটেল থাকায় খাওয়া-দাওয়ার ভারি সুবিধা হয়ে গেল। শুধু মাছ নয়, মাঝে মাঝে ঝোলের সঙ্গে দু-এক টুকরো মাংসও থাকত। সে-সব খেতে খেতে মাখন একদিন ননীকে 'বাহবা' দিয়ে বললেন, ব্যবস্থা তোর ভালই, তো পাস কোথা থেকে। দু-পয়সা এক পয়সার বেশি তো বরাদ্দ নেই। ননী বললেন, ধুর এতে পয়সা লাগে নাকি। খাওয়া থামিয়ে মাখনবাবু বললেন, তোকে বলতেই হবে। পয়সা না দিয়ে খাবার তুই পাস কোথা থেকে। ননীবাবুর জবাব, আগে খেয়ে নে...। তারপর বলব। খাওয়ার পর মাখনবাবুর সেই একই জিজ্ঞাসা। ননীবাবুর অকপট স্বীকারোক্তি: ঝোলটুকু হোটেল থেকেই দিয়ে দেয়। বাকিটুকু সব পাতকুড়ানো। এই কৃচ্ছসাধনের কাহিনী মাখন পালের কাছেই শোনা। নোয়াখালির বেগমগঞ্জ থানার সোনাইমুড়ি গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান, কৃতী ছাত্র মাখন পালের জবানবন্দি: ননীর মুখে মাছ-মাংসের এই ইতিহাস শুনে মনে হল বমি করে দিই। প্রশ্ন রাখলাম, বমি কি শেষ পর্যন্ত করেছিলেন? মাখনবাবুর জবাব: নারে ভাই, তখন আমাদের চালচুলো নেই। পার্টির অনেক কাজ। পয়সা-কড়ি কিছুই ছিল না। ফলে, বাধ্য হয়ে জেনেশুনে পাতকুড়ানো খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ০৩ জানুয়ারি ২০২৬ | ৫১৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (পম্পা ঘোষ)
মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৫৩০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (Sara Man, kk, Sara Man)আরাবল্লী আছে ওখানে, তবে কিনা বাতাসের অভিমুখের সঙ্গে সে পাহাড় সমান্তরাল। তাই একশো শতাংশ জলীয় বাষ্পে টাপুটুপু বাতাস বয়ে গেলেও, পাহাড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হল কই? ধাক্কাধাক্কি হবে , ঢাল পেরোতে না পেরে পাহাড়ের গা বরাবর হাওয়াটা ওপরে উঠবে, ঠান্ডা হবে , বাষ্প ঠান্ডায় ঘন হয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা বানাবে, তবে না বৃষ্টি হবে! ... ...

দিন গোনার দিন - পর্ব ৬ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : অর্থনীতি | ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৭৮৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (স্বাতী রায়, হীরেন সিংহরায়, স্বাতী রায়)অ্যাসেট ব্যাকড ফাইনান্সিংএ দুটো সমস্যা: ব্ল্যাকরক হেন অ্যাসেট ম্যানেজার ছ মাস, ন মাসের জন্য দু, দশ হাজার ডলার ধার দিয়ে ছুঁচো মারেন না, তাঁরা খোঁজেন গণ্ডার, যার ওজন অন্তত একশ মিলিয়ন এবং আয়ু পাঁচ বছরের। এই সমস্যাটির সমাধান- সহস্রটি ইনভয়েস জুড়ে আঁটা দিয়ে সেঁটে এক ভারি ওজনের কাগুজি গণ্ডার বানানো। কিন্তু তার পরেও আরেক সমস্যা থেকে যায় – যেমন যেমন একটা ইনভয়েসের দাম চুকিয়ে দেওয়া হবে তেমনই আরও নতুন ইনভয়েস জুড়ে গণ্ডারের ওজনের ভার সাম্য বজায় রাখতে হবে। আগে আমার হামবুর্গ সেমিনারের অভিজ্ঞতার গল্প লিখেছি - ক্রেদি সুইসের বন্ডগুরু বলেছিলেন আমরা পাঁচ বছরের জন্য একশো মিলিয়ন ডলারের বন্ড বানাতে রাজি, তার জন্য আমাদের চাই হাজার ইনভয়েসে ভরা এমন একটা বাকসো যার মোট মূল্য আজ একশো মিলিয়ন ডলার, কালও একশো মিলিয়ন। যোগ বিয়োগ লেগেই থাকবে, কিছুর পেমেন্ট হবে তার জায়গা নেবে আরও কিছু, কিন্তু যে কোন সময়ে বাকসোর মূল্য হতে হবে সেই একশো মিলিয়ন ডলার। ... ...

দিন গোনার দিন - পর্ব পাঁচ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : অর্থনীতি | ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৬৬৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৬, লিখছেন (অনির্বান, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)ড্যানিয়েল চু হিসেব করে দেখলেন নিচের তলার এই মানুষদের সংখ্যা আমেরিকান নাগরিকের বিশ শতাংশ -ওয়াল স্ট্রিট কেন, মেন স্ট্রিটের কোন ব্যাঙ্ক এঁদের দু পয়সা ধার দেবেন না কারণ এঁদের ক্রেডিট রেকর্ড নেই। ড্যানিয়েল বললেন, আরও কিছু তো খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে, যেমন কেউ হয়তো ভালো গোছের কাজ করেছিলেন, প্যানডেমিকে বেকার, এতদিন ঠিক চলছিল আচমকা বিবাহ বিচ্ছদের কারণে সংসারে টানাটানি, দশ বছর নিয়মিত বাড়ি ভাড়া দিয়ে এসেছেন কিন্তু সে সব তথ্য ক্রেডিট ব্যুরোর খাতায় উঠবে না কেন না এঁদের কাগজপত্র বা সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই। তাহলে একটা জলজ্যান্ত মানুষের কর্ম বা আয় ক্ষমতার একমাত্র নির্ণায়ক ক্রেডিট ব্যুরো? ... ...

মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৬০৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (Manisha Deb Sarkar, Sara Man, Sara Man)পাহাড়ীয়া খাসি শিশুর দল ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে, তাদের পরনের সামান্য পোশাকগুলি ধুলোবালি লেগে মলিন, তবে মুখের হাসিটি বড় উজ্জ্বল। বেশিরভাগই আমাদের টাটা করছে। এক দুজন হাঁ করে ভয়ও দেখাচ্ছে। মনটা বেশ ভালো লাগছিল। ... ...

সেই দিন সেই মন পর্ব ৩৩ (শেষ পর্ব) - অমলেন্দু বিশ্বাস
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৭৪৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (শিবাংশু, অমলেন্দু বিশ্বাস, শিবাংশু)
দিন গোনার দিন - পর্ব চার - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : অর্থনীতি | ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৭০৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (%%, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)ব্রিটিশ অর্থনৈতিক উদ্যোগে অসামান্য অবদানের পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমার চার্লস সি বি ই ( কমান্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার ) খেতাব দিলেন গ্রিনসিলকে। ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রিত্ব পদত্যাগ করলেন ডেভিড ক্যামেরন। এবার গুরু ঋণ চোকানোর পালা , লেক্স গ্রিনসিল বার্ষিক দশ লক্ষ পাউনড সাম্মানিকের বিনিময়ে ক্যামেরনকে গ্রিনসিল কোম্পানির পরামর্শদাতার পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন মাসে দু দিন হাজিরা দিলেই যথেষ্ট , কাজটা আসলে লবিইং , একে ওকে দুটো কথা বলা, সুপারিশ সিফারিশ করা। এত বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সরকারের যে কোন দফতরে চেয়ার টেনে বসতে পারেন। গ্রিনসিল ক্যাপিটালের ভ্যালুয়েশন সত্তর বিলিয়ন ডলার, আসন্ন আই পি ওর সুবাদে ডেভিড ক্যামেরনের সাত কোটি ডলার পকেটে আসার পথ সুপ্রশস্ত। ... ...
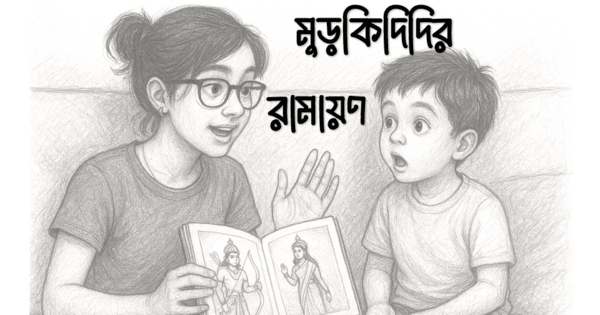
মুড়কিদিদির রামায়ণ - শেখরনাথ মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : গপ্পো | ২৯ নভেম্বর ২০২৫ | ৪৬৬ বার পঠিতসেই যে লঙ্কার অরিষ্ট পাহাড়ের থেকে লাফ দিল হনুমান, নামল একেবারে মহেন্দ্রর চূড়ায়। নামতে নামতেই আকাশ থেকে সে দেখতে পায় জাম্বুবান দাদা আর তার বন্ধুরা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে হনুমানের জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন কোন বাঁদর সবা'র আগে হনুমানকে দেখবে বলে উঁচু গাছে চড়েছে, আকাশপানে তাদের মুখ। আবার আশপাশের নানা সাইজের পাহাড় আর টিলাতেও উঠেছে অনেক ভল্লুক আর বাঁদর। ... ...

মধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২৯ নভেম্বর ২০২৫ | ৫৬৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (কালনিমে , Sara Man, Aditi Dasgupta)বাস এগিয়ে চলে বিশাল এক হ্রদের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে। নাম বড়াপানি বা উমিয়াম। এবারে কিছুক্ষণের বিরতি, ভালোই হল, বাস থেকে নেমে হাত পা ছাড়িয়ে লেকটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ইংরেজি ইউ আকৃতির মতো এক বিশাল হ্রদ। আমরা দেখছি পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে। নিচে জলের কাছে গেলে নৌকা বিহারেরও সুযোগ আছে দেখলাম। ইউ এর মাঝখানে দ্বীপের মতো উঁচু হয়ে আছে। দুপাশের পাহাড় আর মাঝখানের দ্বীপ বড় ঘন সবুজ। ... ...

সেই দিন সেই মন পর্ব ৩২ - অমলেন্দু বিশ্বাস
বুলবুলভাজা | ধারাবাহিক : স্মৃতিকথা | ২৯ নভেম্বর ২০২৫ | ৪৫২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (তপতী বিশ্বাস, সিংগাপুর।)বিচ্ছিন্ন ভাবে লন্ডনে প্রায়শই বর্ণ বৈষম্য প্রণোদিত হত্যা ও জীবনহানি হত। কিন্তু একটা হত্যা সারা দেশকে স্তম্ভিত করেছিল এবং আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। স্টিফেন লরেন্স নামে এক কালো কিশোর নৃশংসভাবে দিনের আলোয় নিহত হয়েছিল। এই কেস বহুদিন চলেছিল এবং কখনো নিঃসন্দেহভাবে এর নিষ্পত্তি হয় নি, যদিও কুড়ি বছর পর দুজন হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছিল। স্টিফেন লরেন্সের মা, ডোরীন লরেন্স এতকাল ধরে ন্যায্য বিচারের জন্য যুদ্ধ করে গিয়েছিল। সাধারণের চোখে মেট্রোপলিটন পুলিশ বর্ণ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল। ডোরীন লরেন্স এখন ব্যারোনেস ডোরীন লরেন্স, হাউস অফ লর্ডসের সভ্যা। ... ...
- পাতা : ৫৫৫৪৫৩৫২৫১৫০৪৯৪৮৪৭৪৬
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... ., :|:, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।












