- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ

-
‘সনাতন ধর্ম’-এর সমালোচনা মানেই কি হিন্দুধর্মের সমালোচনা?
রাজকুমার চক্রবর্তী
আলোচনা | বিবিধ | ০৪ অক্টোবর ২০২৩ | ২৯৫৩ বার পঠিত | রেটিং ৫ (১ জন) 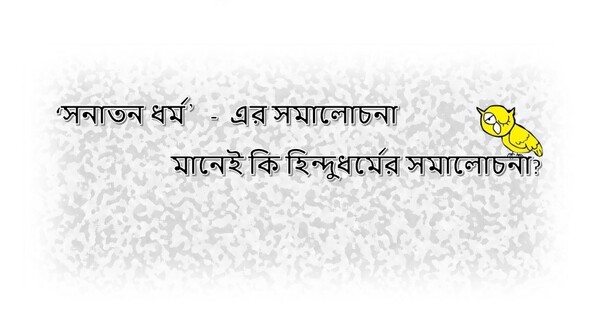
তামিলনাড়ু সরকারের মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের ‘সনাতন ধর্ম’ প্রসঙ্গে মন্তব্যের জেরে জোর শোরগোল পড়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন এই বলে যে, বিরোধী রাজনৈতিক জোট ‘সনাতন ধর্ম’ ধ্বংস করতে সচেষ্ট। তুমুল রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্যে ‘সনাতন ধর্ম’ বিষয়টি প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
আমরা জানি, ভারতীয় ঐতিহ্যে ‘ধর্ম’-এর ধারণা বিবিধ ও ব্যাপক। ‘রিলিজিয়ন’ বলতে যেমন ‘সাম্প্রদায়িক ধর্ম’ তথা সুসংহত কিছু প্রথা-রীতিনীতি-বিশ্বাসের সমষ্টি বোঝায়, এ তেমন নয়। আবার তাকে অস্বীকারও নয়। কখনও কখনও ‘ধর্ম’ বলতে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে বোঝানো হয়েছে ‘সদাচরণ’—কিছু ‘চিরন্তন’ ও ‘সর্বজনীন’ নীতিবোধ। এ-হেন ‘ধর্মবোধ’ ব্যক্তির অন্তরের ব্যাপার। আবার ধর্মশাস্ত্রসমূহ ‘ধর্ম’ বলতে বর্ণ, শ্রেণি, আশ্রম প্রভৃতি ভেদে আইন, বিধি ও কর্তব্যমালাও নির্দেশ করেছে। ‘ধর্ম’ এ ক্ষেত্রে বাইরের নির্দেশ—শ্রেণি বা গোষ্ঠী ও লিঙ্গভেদে কী করণীয় ও কী নিষিদ্ধ তার তালিকা। বলা হয়েছে, ‘ধর্ম হল তা-ই, যা মানুষকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করে’; আবার ‘ধর্ম হল প্রাকৃতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার ধারক, যার অভাবে (অধর্ম) সেই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়’। ভারতীয় ঐতিহ্যে চারটি ‘পুরুষার্থ’-র কথা বলা হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে চতুর্থটি আধ্যাত্মিক—পারমার্থিক মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাকি তিনটি মূলত ইহজাগতিক (যদিও মোক্ষলাভের প্রচ্ছন্ন ছায়া সেখানে আছে)। পুরুষার্থ-র অন্যতম ‘ধর্ম’ হল ‘কর্তব্য, ধর্মীয় আচারবিশ্বাস, ধর্মীয় গুণাবলী, নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব, ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আইন’। ‘অর্থ’ হল ধনসম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, লাভ-লোকসান এবং সাফল্য। ‘কাম’-এর অন্তর্গত প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, সুখ—শুধু যৌনসুখ নয়, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক রসাস্বাদনও বটে (ওয়েন্ডি ডনিগার)। মহাভারতকার লিখে গেছেন, ‘ধর্ম থেকেই অর্থ ও কাম উৎসারিত—কেন ইহা অনুশীলন করিবে না?’ অতএব, বৃহৎ অর্থে চারটি ‘পুরুষার্থ’-ই ধর্ম ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘হিন্দুধর্ম’-এর এই ব্যাপক ধারণা লক্ষ করে এ-কালের কেউ কেউ একে ‘এক সামগ্রিক জীবনধারা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে (বিশেষত মহাভারত ও রামায়ণে) ‘ধর্ম’ শব্দটির আগে বিশেষণ হিসেবে কিছুক্ষেত্রে ‘সনাতন’ (চিরন্তন বা শাশ্বত অর্থে) শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ‘সনাতন ধর্ম’-এর অর্থ ও ব্যঞ্জনা এবং আধুনিক কালের পণ্ডিত ও ধর্মতাত্ত্বিকদের ‘সনাতন ধর্ম’-এর সংজ্ঞায়নের মধ্যে প্রভেদ আছে। এখন ‘সনাতন ধর্ম’-কে মোটের উপর ‘হিন্দুধর্মের’ সমার্থক রূপে দেখা হয়। সে-ক্ষেত্রে এর মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য—হিন্দুধর্মের সব কটি ধারারই স্থান পাবার কথা। এই শাখা বা গোষ্ঠীগুলি কিন্তু প্রাচীনকালে নিজেদের সনাতন ধর্মের উপাসক বলে পরিচয় দেয়নি, অভিন্ন একটি ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মের বহুবিধ শাখার একটি হিসেবেও নয়—যদিও দ্বন্দ্ব বিরোধের পাশাপাশি তাদের মধ্যে আদানপ্রদান ও সমন্বয়ের প্রবণতাও সক্রিয় ছিল, এবং সেই কারণে ধারাগুলির মধ্যে কিছু অভিন্ন লক্ষণ গুপ্তযুগ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘এই সকল ধর্মের উদ্ভব যে আদর্শের ভিত্তিতেই হোক না কেন, বিকাশের একটি পর্যায়ে এগুলি বেদান্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সকলেরই বিচার পদ্ধতি একই রকম এবং একই ধর্মীয় পরিভাষা এই পাঁচটি সম্প্রদায় ব্যবহার করেন’ (প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি)।
কিন্তু এতদসত্ত্বেও এদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দুধর্ম নামক বৃহৎ একটি ধর্ম বা সম্প্রদায় গঠন সতেরো-আঠেরো শতক বা আরও পরবর্তীকালের ঘটনা। ‘সনাতন ধর্ম’ নামক আধুনিক শব্দবন্ধটি (যেখানে অন্ধভজনার দৃষ্টি দিয়ে বৈদিক ঐতিহ্য ও বর্ণাশ্রম নির্ভর সমাজ-সংগঠনের গৌরব প্রচার করা হয়) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে, ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত, পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দু-ধর্মবিরোধী প্রচারের সূত্রে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে এ-দেশীয় চিন্তক সমাজের একাংশ হিন্দু ঐতিহ্যের পুনর্বিচারে রত হয়েছিলেন। নারীর প্রতি হিন্দু সমাজ-কাঠামোর বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রশ্নটি উনিশ শতকের সংস্কারকদের বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁরা বৈষম্যমূলক কিছু প্রথা ও কুসংস্কারের প্রতিবিধানে সচেষ্ট হন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা জোরালো হয়। এ-সবের পালটা-প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয় হিন্দু সমাজের মধ্যে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে যদি ধরা হয় ‘সংস্কারের যুগ’ (Age of Reforms) রূপে, তাহলে উনিশ শতকের শেষ তিন-চার দশক ‘হিন্দু পুনরুত্থানের যুগ’—যখন হিন্দু উচ্চবর্ণের একাংশ প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য ও সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে এক রকম আত্মশ্লাঘা বোধ করছেন এবং তার ‘সংস্কার’ নয়, ‘সংরক্ষণ’-এর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। এই নব্যহিন্দুরা এক-অর্থে ‘আধুনিক’, কেননা হিন্দু সমাজ-সংগঠন ও আচার-সংস্কারের সপক্ষে তাঁরা শুধু প্রাগাধুনিক কালের মতো শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তার সপক্ষে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আমদানি করছেন। যেমন শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি বিধবার নির্জলা একাদশী পালন থেকে শুরু করে খাদ্যাখাদ্য বিচারের সপক্ষে নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করতেন। চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু জাতিভেদ প্রথার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে লিখেছেন, জাতিভেদ আছে বলেই হিন্দু সমাজ এত নিবিড়ভাবে একতাবদ্ধ। পাশ্চাত্যে দেখা যায় আত্মসর্বস্বতা, পরস্পর প্রতিযোগিতা, অবিরত সামাজিক সংঘাত। অন্যদিকে হিন্দুর জাতি ভিত্তিক কর্তব্যের বিভিন্নতা হিন্দুকে শেখায় পরস্পর নির্ভরতা, যেখান থেকে তৈরি হয় পরস্পর প্রীতি। ‘সনাতন ধর্ম’-এর আধুনিক প্রবক্তারা মোটামুটি ভাবে এই কট্টরপন্থী ধারাটিরই প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি মাথায় রাখলে এ-ও বুঝতে পারব যে, ‘সনাতন ধর্মপন্থী’ না হয়েও কেউ কিন্তু হিন্দু পরিচয়ের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারেন। এক কথায়, ‘সনাতন ধর্মে-এর সমালোচনা মানেই হিন্দুধর্মের সমালোচনা নয়, তা হিন্দুধর্মের বিশেষ একটি ভাষ্যের সমালোচনা।
প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য ও হিন্দু সমাজ-সংগঠনের গৌরবের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ উনিশ শতকের শেষাশেষি থেকে শুরু হয়েছিল। আমি এই আলোচনায় বিশ শতকের শুরুতে এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত ‘সনাতন ধর্ম’ সংক্রান্ত কয়েকটি পুস্তকের সাহায্য নেব। তার মধ্যে একটি ১৯০৪ সালে ও আর একটি ১৯১৬ সালে বেনারসের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশিত 'Santana Dharma' নামক পাঠ্যপুস্তক, যা যথাক্রমে অগ্রণী ও ‘নিম্নতর শ্রেণি’-র ছাত্রদের হিন্দুধর্ম ও নীতিশিক্ষার অভিপ্রায় থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের যে-দুটি রচনার সাহায্য নেব সেগুলির একটি ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত, লেখক স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ, দুই সম্পাদক কে এম মুনশি এবং আর আর দিবাকর। দ্বিতীয়টি Indiaspirituality blog (Amrut) থেকে প্রকাশিত Hindu Dharma – Traditional Overview—Most Organized Eternal Way of Life (পি-ডি-এফ কপি, Updated: 04th April 2022)।
এই বইগুলিতে 'সনাতন ধর্ম’-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে: ‘চিরন্তন ধর্ম, প্রাচীন আইন, যার ভিত্তি বেদ।' আরও লেখা হয়েছে যে, এই ধর্মকে ‘আর্য ধর্ম’ অথবা ‘সনাতন বৈদিক ধর্ম’ নামেও অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, হিন্দু শাস্ত্রকার ও আজকের সনাতনপন্থীরা বেদ নামক শাস্ত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল উল্লেখ করেন না (সংকলন কালের করেন)। ভাবা হয় যে, বেদের সূক্তসমূহ শাশ্বত—বিশ্বসৃষ্টির পর থেকেই তা ভাস্বর। অতএব এই ধর্ম প্রাচীন—প্রাচীনতম। সনাতনবাদীরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই প্রাচীনতার মধ্যে খোঁজেন, কেননা অন্য ধর্মগুলির একজন ‘মানুষ-প্রবক্তা’ আছেন, সময়কাল দিয়ে সেগুলির উদ্ভব চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বৈদিক বা সনাতন ধর্মের যায় না। সনাতনীদের গর্বের আরও কারণ এই যে, এই ধর্ম ‘শাশ্বত’ ও ‘অবিনশ্বর’—মহাবিশ্ব তথা বিশ্বজগৎ যতদিন থাকবে জগতের নিয়মাবলীস্বরূপ এই ধর্মও ততদিন বিদ্যমান থাকবে। এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিলুপ্তির পরেও তা অন্তর্হিত হবে না, নিদ্রিত বা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করবে (পরের ‘কল্প’-এর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত)— কারণ স্বয়ং ‘ব্রহ্ম’ থেকে তার উৎপত্তি। বলা হয়েছে যে, ‘সনাতন ধর্ম একটি বহমান নদীর মতো, যেখানে একজন শিশু খেলতে পারে, অবগাহন করতে পারে, কিন্তু এর গভীরতার তল পাওয়া একজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর পক্ষেও অসম্ভব’। ‘এর মধ্যে মানুষের সর্ববিধ চাহিদার স্থান আছে, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে যা যা আবশ্যক—অন্য কোনো ধর্মে (রিলিজিয়ন অর্থে) যা তাকে দিতে পারে না’। উল্লেখ্য, ‘বেদে সব আছে’ উক্তিটির প্রেক্ষিতটি এই। তথাকথিত আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সমস্ত বিষয় (বিজ্ঞান ও দর্শনের শাখাগুলিও) যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, তাই বিশ্বাস করা হয় ‘বেদের বাইরে কিছু নেই’।
এই ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রুতি ও স্মৃতি। ‘শ্রুতি’ মানে চারটি বৈদিক সংহিতা (ঋক, সাম, যজু, অথর্ব) এবং প্রত্যেকটি সংহিতার সঙ্গে যুক্ত বাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহ। শ্রুতির পরে স্থান স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রসমূহের, যেগুলি একাধারে পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য (বর্ণ ও আশ্রমভেদে প্রজার দায়িত্ব), প্রশাসনিক স্তরে পালনীয় আইন-কানুন, দণ্ডনীতি, পুজো-অর্চনা-যাগযজ্ঞের বিধিসমূহ। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বেদের পাশাপাশি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এবং অঙ্গসমূহ—জ্ঞান ও ধর্মের এই হল আঠেরোটি উৎস, এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্য নিয়ে বেদপাঠের বিধানও এর অন্তর্গত।‘ ‘ইতিহাস’ মানে রামায়ণ ও মহাভারত। মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ভগবদগীতা—যা সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে ‘আর্য সাহিত্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রত্ন’। সনাতন ধর্মের শাস্ত্র বলতে এগুলিই উল্লিখিত। এই অর্থে ‘হিন্দুধর্ম’ ও ‘সনাতন ধর্ম’ সমার্থক।
সনাতন ধর্মের প্রবক্তা ও তত্ত্বকারদের একটি মুশকিল হল—তাঁরা বৈদিক ধর্ম ও তার বিবর্তনকে ঐতিহাসিকভাবে (দেশ-কালের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার যোগাযোগ ও রূপান্তর) বিচার করেন না। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি নামক চারটি যুগবিভাগের সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রগুলির পরিবর্তিত ভাষ্যকে যোগ করার চেষ্টা করা হয় বই-কী, বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আপোসের চিহ্নও সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু ‘শাশ্বত চিরন্তন ধর্মের তত্ত্ব’-টিই ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুধর্মকে বোঝার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম যে পৃথক, বেদবিরোধী ‘অনার্য’ বহু বিশ্বাস ও আচার-বিশ্বাসও যে সেখানে যুক্ত হয়েছে—তার স্বীকৃতি সনাতনীদের চিরন্তন বা প্রাচীন ধর্মের তত্ত্বে নেই। বৈদিক ধর্ম যাগযজ্ঞপ্রধান। সেখানে অবতার তত্ত্ব, মূর্তিপূজা ও মন্দিরের স্থান নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিন উচ্চবর্ণের সে-ধর্ম অনুসরণের অধিকার। ‘আর্য’ পরিচয়ের তারাই কেবল দাবিদার। ঐতিহাসিকদের মতে, আর্য সংস্কৃতি বলে যা উল্লেখ করা হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক রীতিনীতির উৎস হিসেবে যাকে দেখা হয়, সেই ধর্ম ‘এলিটিস্ট’; একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর বাইরে তার দরজা বন্ধ ছিল—উত্তর ভারতের জনগণের বিরাট অংশ ও বিন্ধ্যর নিচের সমগ্র উপদ্বীপীয় ভারতের জনগণ ছিল সেই ধর্মের পরিধি-বহির্ভূত।
বৈদিক ধর্মের ‘মালিকানা’ ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে কুক্ষিগত। সামাজিক পরিবর্তন ও বেদবিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ব্রাহ্মণদের সেই কর্তৃত্ব বিপন্ন হয়। বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রসার, মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা—এই সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বে ব্রাহ্মণরা হয়ে পড়েন কোণঠাসা। সংকটকালের অভিজ্ঞতায় ব্রাহ্মণরা বুঝেছিলেন যে, ‘স্থানীয় মানুষদের তাঁদের রীতিনীতি, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানসহ ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে বৌদ্ধদের সঙ্গে সামাজিক ভূমি দখলের লড়াইয়ে ব্রাহ্মণরা টিকে থাকতে পারবেন না’। মৌর্যোত্তর কাল থেকে ব্রাহ্মণরা আবার নতুন ভাবে ফিরে আসার প্রস্তুতি শুরু করেন। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতক থেকে ধর্মশাস্ত্রগুলি লেখা শুরু হয়, যেগুলিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্র হিসেবে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করা যায়। চারণকবিদের মুখে-মুখে ঘোরা রামায়ণ ও মহাভারত-ও এই সময়কালে লেখা হয় ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শের ছাপ মেরে। তারপর খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে ‘পুরাণ’ নামক নতুন একশ্রেণির গ্রন্থ রচনায় তাঁরা নিমগ্ন হন, যেগুলির উদ্দিষ্ট আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো, যারা এতদিন পড়েছিল ব্রাহ্মণ্য প্রভাব-বলয়ের বাইরে। এদের আকৃষ্ট করতে আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীসমূহের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, বিশ্বাস ও দেবদেবীকে ঢেলে সাজিয়ে ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত করা হল। এই সব বিশ্বাস-রীতিনীতির সঙ্গে বৈদিক ধর্মের কোনো মিল ছিল না, কিন্তু সবই করা হয়েছিল বেদের নামে, বেদকে জাদুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। এইভাবে গুপ্তযুগ থেকে যে-ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ-সংগঠনের উদ্ভব হল তার প্রধান দুই শাস্ত্রীয় ভিত্তি হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ। সামাজিক বিধিনিষেধ নিয়ম-কানুনগুলি ধর্মশাস্ত্রের বিষয়বস্তু আর দেবতাদের অলৌকিক কীর্তিকাহিনী পুরাণের। নবভাবে সংগঠিত এই ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অধুনা যে ‘সনাতন’ বা ‘চিরন্তন ধর্ম’ নামে (কিংবা ‘সনাতন বৈদিক ধর্ম’) উল্লেখ করা হচ্ছে, তা কতটা ঐতিহাসিকভাবে গ্রাহ্য তা তাই বিবেচনাযোগ্য।
তবে একটি ধারাবাহিকতা আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক উভয় ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা, যার অভিভাবক হলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণি। বেদের জ্ঞান যেহেতু আর কারও আয়ত্ত ছিল না, তাই সেখানে কী-আছে কী-নেই, তা জানা অন্য কারও সম্ভবও ছিল না। ('বেদে সব আছে' আজও যারা বলেন, তাঁরা বিশ্বাস থেকেই বলেন)। এর ফলে জনসাধারণের উপর বেদের নাম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাষ্যটি চাপিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল (কুমকুম রায়, কুণাল চক্রবর্তী, তনিকা সরকার, বেদ, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব)
II
ঐতিহাসিকভাবে দেখলে বোঝা যায়, ধর্মশাস্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব এ-কালের ‘সনাতন ধর্ম’-কে করে তুলেছে ব্রাহ্মণ্যবাদী। সনাতন-ধর্মীরা মনে করেন, সনাতন ধর্মের মূল কথা বর্ণাশ্রমনির্ভর সমাজ-সংগঠন, যা সমাজে শৃঙ্খলা ধরে রেখেছে, এবং প্রত্যেক বর্ণ বা শ্রেণির জন্য শাস্ত্রসম্মত আলাদা আলাদা কর্তব্য স্থির করেছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থাই যুগের পর যুগ ধরে সনাতন ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছে। কত সভ্যতা এসেছে, গেছে, কিন্তু এত বহিরাক্রমণের মধ্যেও হিন্দু সভ্যতা তার ‘গৌরবময়’ অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্মের দৌলতে। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরোধিতা যেমন সনাতন ধর্মের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত, তেমনই উন্নত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারাটিরও অবমাননা।
সনাতন ধর্মপন্থীরা দাবি করেন এই বলে যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বর্ণ, শ্রেণি ও আশ্রম ভেদে মানুষকে পৃথক পৃথক ধর্মাচরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে; কিন্তু পৃথক মানে বৈষম্য-প্রদর্শন নয়। উল্লেখ্য, গান্ধিজিও নিজেকে ‘সনাতনী হিন্দু’ বলে দাবি করতেন (যদিও গান্ধিজির ধর্মবোধ বিচার করে বোঝা যায় আসলে তাঁর ‘ধর্ম’ পুরোপুরি সনাতনী হিন্দুর মতো ছিল না)। তিনি বর্ণাশ্রম মানলেও জাতপাত বা বৈষম্য মানতেন না। এমন ‘ব্যতিক্রমী’ দু-একজন ‘সনাতনী’-র দেখা হয়তো মিলবে। কিন্তু মুশকিল হল, হিন্দুধর্মশাস্ত্রসমূহের গভীরে বৈষম্যমূলক বর্ণব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা প্রোথিত। এবং, সনাতনপন্থীরা সেই সব শাস্ত্রের প্রতি সশ্রদ্ধ।
যেমন, স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ গীতা-র উদ্ধৃতি তুলে ধরে শাস্ত্রীয় নির্দেশের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন : “শাস্ত্রের নির্দেশ না মেনে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা মতো চললে সফল হবে না; স্বর্গলাভ ও মোক্ষ সম্ভব হবে না। অতএব, শাস্ত্র হচ্ছে সেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যা তুমি কী-করবে ও কী-করবে-না তোমাকে জানায়। শাস্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হও এবং সেই মতো চলো” (পৃষ্ঠা ৩৭)। সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত আর-একটি বইতে (Indiaspirituality Blog লিখিত ) মন্তব্য পাচ্ছি: “আদি শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, যদি শাস্ত্র না থাকত, মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না, মানুষ শাস্ত্র ছাড়া পশুর মতো দিনযাপন করত। অনেকের মধ্যে এই ধারণা জনপ্রিয় যে মানবতাই শ্রেষ্ঠধর্ম। কথাটি ভুল। শাস্ত্রই আমাদের মানুষ করেছে” (পৃষ্ঠা ৬৯)। হিন্দুদের (সনাতন ধর্মের) সুশৃঙ্খল সমাজ-সংগঠনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ আরও লিখেছেন, “বিশ্বের আর কোনো নেশন, নৃগোষ্ঠী, আর কোনো ধর্ম সনাতন ও হিন্দুদের মতো আইন ও শৃঙ্খলার উপর এত জোর দেয়নি। চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক আনুগত্য—সন্তানের পিতার উপর, ছোট ভাইয়ের বড়ো ভাইয়ের উপর, ভৃত্যের প্রভুর উপর, শিষ্যের গুরুর উপর, প্রজার রাজার উপর, এই রকম আরও কত কি—সনাতন ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য” (পৃষ্ঠা ২৩)। ‘আরও কত কি’-র মধ্যে বলাই বাহুল্য তিন উচ্চবর্ণের প্রতি শূদ্রের কর্তব্য, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যও যুক্ত।
উল্লেখ্য, ঋগ্বৈদিক সমাজে জন্মভিত্তিক চতুর্বর্ণ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে বৈষম্যমূলক চতুর্বর্ণ প্রথার বীজ খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা দেখিয়েছেন, সেটি পরবর্তীকালের সংযোজন। শূদ্রের অবস্থান অবস্থান নিশ্চয়ই তখনও ছিল সবার নিচুতে। তবে অস্পৃশ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্ন ঋগ্বৈবৈদিক যুগে নেই। কিন্তু, পরবর্তীকালে, যে-সমাজ সংগঠন মান্যতা পেল সেখানে জন্মভিত্তিক বর্ণাশ্রম, জাতপাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার ছায়াপাত স্পষ্ট ও প্রকট। বর্ণভেদ ও জাতপাত ততদিনে জন্মভিত্তিক বিভাজনের চেহারা নিয়েছে। মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলির নির্দেশাবলীর মধ্যে আছে এই বৈষম্যমূলক সমাজ-সংগঠনেরই স্বীকৃতি। মনুসংহিতার কিছু শ্লোকে গুণ বা যোগ্যতা ভিত্তিক বর্ণপরিচয়ের কথা বলেছে বটে, কিন্তু ‘জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ’ এ-কথা উচ্চারিত হয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক শ্লোকে (যেমন ৯/৩১৭, ৯/৩১৯, ২/১৩৫)। শূদ্র ও চণ্ডালদের প্রতি মনুসংহিতার নির্দেশাবলী কঠোর ও অবমাননাকর। সাধারণভাবে মনুসংহিতায় স্বীকৃতি পেয়েছে কট্টর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ। নারীজাতি ও ‘স্বামী-অনুগত-স্ত্রী’ সম্পর্কে কিছু ভালো ভালো কথাও সেখানে আছে। নারীকে (স্ত্রী ব্যতিরেকে) ‘মা’ হিসেবে দেখার উপদেশও ‘মনু’ দিয়েছেন।
মনুসংহিতা ও অন্য ধর্মশাস্ত্র-মানা এ-কালের সনাতন ধর্মপন্থীদের কলমে এই জন্মভিত্তিক শ্রেণিভেদ ও লিঙ্গবিভাজনের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে দেখি। ইন্ডিয়াস্পিরিচুয়ালিটি ব্লগ কর্তৃক প্রকাশিত বইটিতে লেখা হয়েছে, “ভগবদগীতার ৪/১৩ এবং ১৮/৪১-৪৮ শ্লোক বিশ্লেষণ করে আদি শঙ্কর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বৈদিক আচার্য দেখিয়েছেন যে বর্ণ গুণনির্ভর, কিন্তু গুণ আবার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত; কেননা পূর্বজন্মের ফল পরের জন্মে প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম অতীত-জীবনের উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মের সাক্ষ্য’ (পৃষ্ঠা ১৪৬)। বস্তুত বর্ণভেদকে ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জাতিভেদ (জাতিবর্ণ ব্যবস্থা)-কে মনুষ্যসৃষ্ট বলে চিহ্নিত করেও জাতিভেদ ব্যবস্থাকে অসিদ্ধ দাবি করা হয়নি। তার উৎস খোঁজা হয়েছে বর্ণসংকরের ধারণা (বিভিন্ন বর্ণের রক্তের আনুপাতিক মিশ্রণের তত্ত্ব) প্রয়োগ করে। স্বামী ভারতী কৃষ্ণতীর্থ সবর্ণ বিবাহের শাস্ত্রীয় নির্দেশাবলীর (অসবর্ণ বিয়ের বিরোধিতা) যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন পাশ্চাত্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে—বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষার ধারণায় (পৃষ্ঠা ৫১)। তাঁর মন্তব্য: ‘আধুনিককালের প্রত্যেকটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার ব্যতিক্রমহীন ভাবে সনাতন ধর্মের প্রাচীন সত্যর উপর আলোকপাত করছে’ (পৃষ্ঠা ৬৮)। তিনি বিধবাবিবাহেরও বিরোধী, কারণ ‘কোনো নারী যদি একের বেশি যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়, তার জরায়ুতে কুপ্রভাব পড়ে, তার ফলে নতুন স্বামীর গুণাবলি সন্তানের উপর সঞ্চারিত হয় না’। পাশ্চাত্যের ডাক্তাররা নাকি এমন কথাই বলছেন (পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)!
একইভাবে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের প্রতি ধর্মশাস্ত্রকারদের চাপানো নিষেধাজ্ঞাসমূহেরও ব্যাখ্যা খুঁজতে সচেষ্ট হন সনাতনপন্থী প্রচারকরা। ‘অস্পৃশ্য’ তথা ‘পঞ্চম বর্ণ’দের মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে এই বলে: “আমাদের শাস্ত্র কারও প্রতি কোনও বৈষম্য ও অন্যায় করেনি। তবু যদি অন্যায়ের অভিযোগ ওঠে, তাহলে বলব, তাদের নয়, আমাদের প্রতি এই অন্যায় করা হয়েছে। … যেখানে অন্য চার বর্ণের মানুষের মন্দিরে প্রবেশে ও পূজা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ‘পঞ্চম বর্ণ’কে দেওয়া হয়নি। আমি বলব, অন্য চার বর্ণকে যে-অধিকার মন্দিরে প্রবেশের সূত্রে দেওয়া হয়েছে, সেই একই অধিকার ‘পঞ্চম’কে দেওয়া হয়েছে দূর থেকে স্তম্ভ ও স্তূপ দর্শনের বিনিময়ে। উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন সাঙ্গ করার পরেই একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরে গিয়ে পূজা করার অধিকার অর্জন করেন। কিন্তু একজন ‘পঞ্চম’ নিজের প্রাত্যহিক কাজ করবার ফাঁকে দূর থেকে স্তূপ দেখে ব্রাহ্মণের মতো একই উপকার লাভ করে থাকে”। পুণ্যার্জন তাহলে কার কাছে সহজসাধ্য? (স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ, পৃষ্ঠা ৭৯)।
প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে পাঁচটি ‘কোশ’ বা ‘দেহ’-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে (‘অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ’)। যেহেতু সনাতনধর্মীরা আজও এই পাঁচ প্রকার দেহের তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ছোঁয়াছুঁয়ির সপক্ষে তাঁদের বলতে শোনা যায়: “অন্নময় কোশ বা শরীরী দেহের প্রতিক্রিয়া দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে একজন শূদ্র ও ব্রাহ্মণের শারীরিক স্পর্শ হলে দোষ কিছু হয় না। কিন্তু আমরা শরীরের অন্য বর্গগুলির উপর এই ছোঁয়াছুঁয়ির কী প্রতিক্রিয়া হয়, বলতে পারি না। আধুনিক সংস্কারকেরা ওই সব সূক্ষ্ম দেহগুলির কার্যপ্রণালী নিয়ে চর্চা করেননি। কিন্তু সনাতন ধর্ম তৈরি হয়েছিল উক্ত পাঁচটি দেহের কথা মাথায় রেখে। সুতরাং শুধুমাত্র একটি দেহের প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় এনে ছোঁয়াছুঁয়ির নির্দেশের বিরোধিতা করলে তা খুব অন্যায্য হবে” (Indiaspirituality Blog (Amrut), পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬)।
নারীদের প্রতি সনাতনপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলেও একইভাবে কট্টরপন্থী পিতৃতান্ত্রিক সত্তাটি খুঁজে পাওয়া যায়। ‘সনাতন ধর্মে’ নারীদের প্রতি কোনও বঞ্চনা করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না; ধর্মশাস্ত্র থেকে একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন শ্লোক তুলে প্রাচীন ভারতে নারীর মর্যাদার ছবিটি তুলে ধরা হয়—ফলত হয় তাঁরা শাস্ত্রসমূহে নারীর প্রতি অজস্র বৈষম্য ও অপমানমূলক বিধান এড়িয়ে যান, নয় তো সেই সব বিধিবিধানের সপক্ষে কোনো ‘মহৎ যুক্তি’ খুঁজে পান। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র সবেতেই নাকি নারীকে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে বানানো হয়েছে। স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ লিখছেন, মহিলাদের ‘সমতা’, ‘সম্মান’ ও ‘শ্রদ্ধা’-র যে-কথাগুলি পাশ্চাত্যে অহরহ শোনা যায়, ভগবান মনু সেগুলিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি মহিলাদের সর্বোত্তম সম্মান দিয়েছেন তাঁদেরকে ‘পুজো’ করার কথা বলে, ‘মা’-এর সম্মান দিয়ে (পৃষ্ঠা ৮৩)।
গৃহের ‘প্রকৃত মালিকানা’-ও ‘তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে’ (অথচ ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০-৩৬ সংখ্যক শ্লোকে নারীর ঘুম ভাঙা থেকে রাতে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ কর্তব্য তালিকা দেওয়া হয়েছে, যার সার কথা পতি থেকে শুরু করে পরিবারের সবাইকে খুশি করতে নারী প্রাণপাত করবে, তবেই নারী ইহলোকে যশ ও পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হবে)। এর পরেও নারীরা কেন অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করছেন তা স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থের বোধগম্য নয়। তাঁর সতর্কবার্তা: “কিছু মানুষ আমাদের ঘরোয়া শান্তি বিপন্ন করে অক্লান্ত ভাবে বলে থাকেন যে ভারতে নারীদের পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। … এই মতবাদের ফলে মেয়েরা দিন দিন জঙ্গি হয়ে উঠছে, যদিও ইংল্যান্ডের মেয়েদের মতো হয়ে ওঠেনি এখনও। আমরা যদি না এখনই এই প্রচার বন্ধ করতে পারি, এই বিদ্রোহ একদিন আমাদের সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি লণ্ডভণ্ড করে দেবে’ (পৃষ্ঠা ৭৮)। নারী-পুরুষ সমতার অপ্রাসঙ্গিকতা দাবি করে অন্য সনাতনবাদীরাও লিখছেন: “আমরা সবাই সম্মান প্রত্যাশা করি, কিন্তু তার জন্যে সমতার দাবিতে আকচা-আকচির প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর আমাদের ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন” (Indiaspirituality Blog (Amrut)), পৃষ্ঠা ১৫৪) দৃষ্টান্ত আরও বাড়িয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করাই যায়। মোদ্দা কথাটি হল—সনাতন ধর্মের প্রবক্তারা হিন্দু সমাজ-সংগঠনের একটি রক্ষণশীল ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ছবি তুলে ধরে তার সংরক্ষণে সোচ্চার হন। ভারতীয় ঐতিহ্যে বহু উচ্চমার্গের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সে-সবের পাশাপাশি হিন্দু সমাজ-সংগঠনে ঐতিহাসিকভাবে রয়ে গেছে শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণাশ্রম, লিঙ্গভেদ ও জাতিভেদ ব্যবস্থার অনপনেয় চিহ্ন। হিন্দুধর্মের বহু ধর্মীয় গুরু তথা স্বামীজির মধ্যে বোধহয় এই কারণেই এক বৈপরীত্যের সন্ধান মেলে—দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক চিন্তার দিক থেকে তাঁরা উদার ও প্রাজ্ঞ, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে কট্টর ও প্রতিক্রিয়াপন্থী।
আলোচনার শেষে দুটি কথা বলার। এক, ‘গৌরবময়’ ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যর অসম্মান বা অবমাননা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে গর্ব করার মতো অনেক বিষয় আছে, আবার আছে আজকের দৃষ্টিতে নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য বিষয়ও। সাক্ষ্যপ্রমাণ-নির্ভর ইতিহাসচর্চা ‘ভালো-মন্দ’ এই দুই দিকেই আলোকপাত করে থাকে। প্রামাণিক ইতিহাসের সেটাই আবশ্যকি শর্ত।
দুই, ওয়েন্ডি ডনিগার তাঁর সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে (Against Dharma, Yale University Press: 2018) যে-কথাটি বলেছেন, আমরা অবশ্যই মনে রাখব। ব্রাহ্মণশ্রেণি প্রাচীন ভারতে একশৈলিক (monolithic) শ্রেণি ছিল না। আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রভাব পড়েছে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণগুলিতে—নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের বাসনা সেখানে স্পষ্ট। কিন্তু অন্য ভাবনার ‘ব্রাহ্মণ চিন্তক’-ও সেদিন সমাজে ছিল যাঁরা ‘গোপনে’ রেখে গেছেন বিকল্প ও ‘অন্তর্ঘাতী ভাষ্য’—ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও যার অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষণী ও সন্ধানী দৃষ্টিতে ঐতিহ্য ও ইতিহাস পাঠ করলে তাই বিকল্প মত, যুক্তি, অর্থাৎ ‘তর্কপ্রিয় বহুমাত্রিক’ ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান মিলবে।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।- আরও পড়ুননির্বাচন ২০২৬! - bikarnaআরও পড়ুনজামায়াতের কার্যকরী নির্বাচনী কৌশলে দেশের বাছাইকৃত এলাকায় চমকের গল্প। - লতিফুর রহমান প্রামানিকআরও পড়ুনএপস্টাইন এর ফাইল - একটি কেলেঙ্কারি, নাকি একটি ব্যবস্থা: বৈশ্বিক পুঁজির Eros - Tuhinangshu Mukherjeeআরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডলআরও পড়ুনতিরিশ দিন অথবা এক কোটি ষোল লক্ষ ঘন্টা: শিক্ষা-ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর জটিল অঙ্ক - সীমান্ত গুহঠাকুরতাআরও পড়ুনদিন গোনার দিন ৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমধুবাতা ঋতায়তে - শারদা মণ্ডল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 অলোক মন্ডল | 223.176.***.*** | ০৪ অক্টোবর ২০২৩ ২২:০৬524279
অলোক মন্ডল | 223.176.***.*** | ০৪ অক্টোবর ২০২৩ ২২:০৬524279- অলোক মন্ডল সুন্দর বিশ্লেষণ
 guru | 103.175.***.*** | ০৫ অক্টোবর ২০২৩ ১৩:২৮524304
guru | 103.175.***.*** | ০৫ অক্টোবর ২০২৩ ১৩:২৮524304- খুবই মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ |
-
Kishore Ghosal | ০৫ অক্টোবর ২০২৩ ২৩:২৬524322
- খুবই সুন্দর বিশ্লেষণ। হয়তো "বিজ্ঞাপন" এর মত শোনাবে - "ধর্মাধর্ম" বইটিতেও এই নিয়েই বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি।
 সর্বানী ব্যানার্জী | 2401:4900:1c3f:a7d4:a83c:d2c:6681:***:*** | ০৬ অক্টোবর ২০২৩ ০৪:১১524326
সর্বানী ব্যানার্জী | 2401:4900:1c3f:a7d4:a83c:d2c:6681:***:*** | ০৬ অক্টোবর ২০২৩ ০৪:১১524326- চমৎকার বিশ্লেষণ.. তোমার লেখা মানেই অনেক কিছু অজানা তথ্য জানতে পারা।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc, kk, দ)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












