-
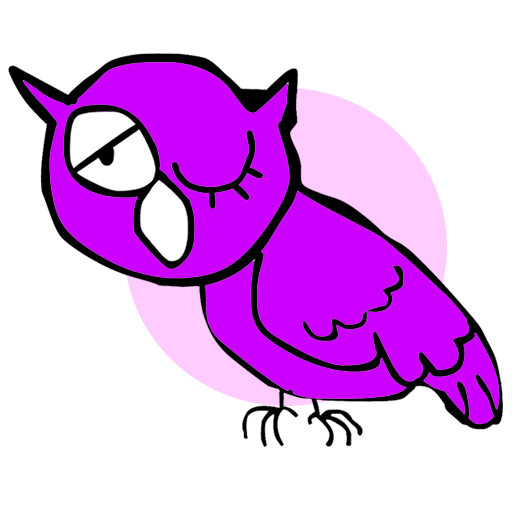 বুলবুলভাজা স্মৃতিচারণ
বুলবুলভাজা স্মৃতিচারণ
-
এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়।
বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচণ্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা
-
- নতুন আলোচনা
-
বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:
- পাতা : ২১
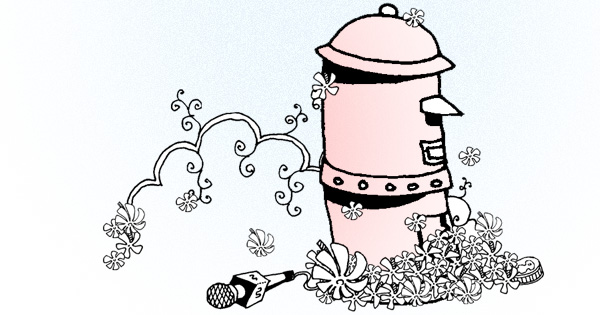
দু-প্যান্ডেলের মাঝখানটায় - সোমনাথ রায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ০২ অক্টোবর ২০২৫ | ৫৩৫ বার পঠিতঅনুরূপা এবং তার গার্লস কলেজ দলটা ওনাকে দেখে বড়ো ভরসা পেয়েছে, এসব রাস্তায় পুজোর দিন হলেও কেমন গা ছমছম করে কিনা, স্পেশালি কয়েকটা হোস্টেল কাটিং ছেলে পদ্মপুকুরের লাইন থেকেই যে ভাবে অ্যাটেম্পট নিচ্ছিলো। আপাতত বোধিস্বত্ত্ব এইখান দিয়ে হনহনিয়ে, রাদার বলা ভালো দৌড়েই যাচ্ছে, ম্যাডক্সে লোকজন গোল হয়ে বসবে, অলরেডি একঘন্টা লেট, সুদীপ্তা কার সঙ্গে গল্পো জুড়ে দিলো কে জানে, আর উলটো দিক থেকে তুমুল ঝগড়া করতে করতে সৌমিতা-রাণা হেঁটে আসছে; সৌমিতা হয় এই শেষ কথা বললাম বলে তুমুল চেঁচাচ্ছে (হোমগার্ড সাহেব বেশ আমোদ পাচ্ছেন এতে) অথবা জাস্ট কোনও কথাই বলছে না, রাণা-কে তো বলেই দিয়েছে, আমি আলাদা আর তুই আলাদা ঘুরছি, এর পর আর কথা বলারও কিছু নেই। ... ...

ঢাকের দিনে ঢুকুঢুকু - ঋতেন মিত্র
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ : নস্টালজিয়া | ০২ অক্টোবর ২০২৫ | ৩৯৮ বার পঠিতথার্ড ইয়ারে থেকে আমার কেমন করে একটা নতুন নাম হল। "সভাপতি'। তবে তখন থেকে মাল-পার্টিগুলোকে একটা স্ট্রাকচার দেওয়ার চেষ্টা করতাম। প্রথমে একটা উদ্বোধনী স্পিচ । তারপর এনাউন্সমেন্ট হত আধঘণ্টা অন্তর। "এবারে পানু পাঠ করে শোনাবেন' এই রকম আর কি। বাইরে সিকিউরিটি বসার পর আমার রুমে ভেন্যু শিফট হল, সিগগি ফেলার জন্য আলাদা ট্রাশের দরকার হত না, কারন গোটা রুমটাই ছিল মোটামুটি তাই। আর ছিল আমার একখান স্পেশাল লাল ব্যাগ। কাঁধে ঝোলানো। এই ব্যাগটা করে নোংরা জামা কাপড় নিয়ে শনিবার বাড়ি ফিরতাম আর বাড়ি থেকে কাচা জামা নিয়ে আসতাম। ঐ ব্যাগ নিয়েই বেরোতাম মাল কিনতে। ঐ ব্যাগটাও কেমন করে জানি লেজেও, একরকমের প্রতীক হয়ে গেল। ... ...
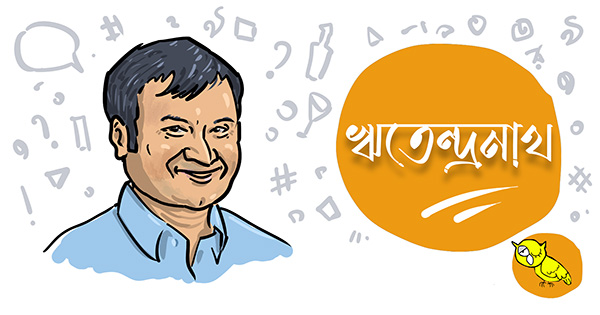
ঋতেন্দ্রনাথ - যদুবাবু
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ২৪ মার্চ ২০২৫ | ১৪২৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৭, লিখছেন (সমরেশ মুখার্জী, :|:, শেখরনাথ মুখোপাধ্যায় )'আমাদের দিনগুলিও অপূর্ণ, অপূর্ণ আমাদের রাত্রি, তবুও হাত ফস্কে জীবন চলে যায় যেন অকম্পিত ঘাসের মধ্যে একটি মেঠো ইঁদুর।' লিখেছিলেন এজরা পাউন্ড। জীবনের দিকে, এবং বারবার এই সন্ধেবেলায় নিজেদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে সত্যিই অদ্ভুত ঘটনাহীন জীবন যেন নিস্তরঙ্গ দুপুরের উঠোন। পুকুরের বুক চিরে ব্যাঙাচি খেলার মত একটা করে ঢিল ছুটে যায় মাঝেমাঝে - সত্যিই কি জলের স্তর চিরে যায়? চেরে না। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন যেন ঐরকম, কত কিছু হয়ে যায় দাগ পড়ে না। তবু সেইসব নিস্তরঙ্গ দিনগুলোর মধ্যে একদিন একটা বিপর্যয় ঘটে যায়। আমরা বোঝার আগেই একটা অন্য পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছুই। আর জেনে যাই - সময় দুইরকম হয়। বিপর্যয়ের আগে, আর বিপর্যয়ের পরে। 'যেমন অসত্য ছিল দীর্ঘ গতকাল, যেমন অসত্য হবে অনন্ত আগামী'। ঋতেনদার সাথে আমার আলাপ ২০০৩ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে। আমাদের বিস্ট্যাটের ক্লাস শুরু হয়েছে সেদিন, লাঞ্চব্রেকের আগেই অমর্ত্য দত্তর ক্লাসে গ্যালোয়ার টাওয়ার অফ ফিল্ড-টিল্ড শুনে তখন কান দিয়ে ধোঁয়া-টোঁয়া বেরোচ্ছে, এই অবস্থায় ক্যান্টিনের রাস্তায় আকর্ণবিস্তৃত নিষ্পাপ হাসি মেখে একজন ভালোমানুষ গোছের দাদা এগিয়ে এলেন। ঋতেনদা। ... ...

ঋতেন ও তার বন্ধুরা - সোমনাথ রায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৫ মার্চ ২০২৫ | ১৯৪৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (Anish, প্রতিভা, সমরেশ মুখার্জী)হয়তো সেই কারণেই, ঋতেন নিজের গল্পগুলো তার বন্ধুদের নাম দিয়ে বলত। ঋতেনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা, যাপন ও উপলব্ধির কথাগুলোকে আমরা বলতাম ঋতেনের বন্ধুদের কথা। ফেসবুক, অরকুটে, গুরুচন্ডা৯র ভাটিয়ালিতে ও বিভিন্ন টইতে এই বন্ধুদের বকলমে ঋতেন যে কতকিছু লিখে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। পারিবারিক দিক থেকে সে ছিল কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের পৌত্র এবং কবি রাম বসুর দৌহিত্র। পারিবারিক পরিমণ্ডলের সূত্রে যে সম্পদ তার কাছে ছিল, তার ছটাও আমরা ঋতেনের বন্ধুদের গল্প হয়ে পেয়েছি। ... ...
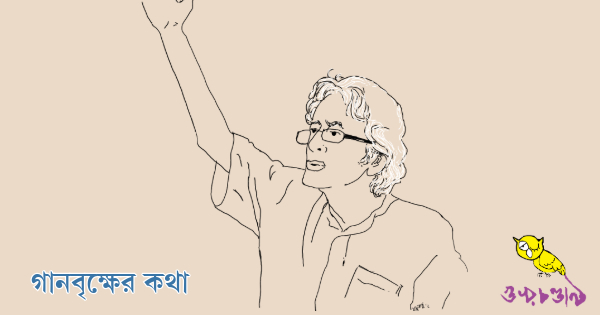
গান বৃক্ষের কথা - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ১৮২৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Eman Bhasha, Touhid Hossain)
কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ৩০ নভেম্বর ২০২৪ | ৮৭৪ বার পঠিতসিনেমার ওপরে লেখা থাকতো অনন্যা, অজন্তা। ওগুলো যে হলের নাম পরে বুঝেছি। আমি ভাবতাম লেখিকার নাম। ভাবতাম, এই বই তিনজন চারজন লিখেছে? কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারতাম না, লজ্জায়। একটা বিজ্ঞাপন ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। শট গান। পাখি মারার ছররা বন্দুক। ৬০ টাকা দাম। ডাকযোগে পাঠানো হয়। শোনা গেল, দু একজন ঠকেছে। অন্যজায়গার। শুধু পাইপ এসেছে। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ২৩ নভেম্বর ২০২৪ | ১২৪৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (দ, হীরেন সিংহরায়, দ)এক ভদ্রলোকের কথা মনে আছে। এলেন। বছর ত্রিশেক বয়স। দিন কুড়ি থাকলেন। সন্ধ্যা বেলায় বিচিত্র গল্প শোনালেন। তারপর একদিন একটা চাদর নিয়ে চলে গেলেন। আর একজনের কথা খুব মনে আছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কা চেহারা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষ। কামারশালা বসাতেন আমাদের বৈঠকখানার পাশে। রাতে থাকতেন বৈঠকখানায়। হাঁড়িকুঁড়ি ঝালাই করতেন। তামার হাঁড়ি পাতিল নিকেল করতেন। রিপিট মারতেন কড়াই বা বালতিতে। কাজ ছিল চমৎকার। বেশ কয়েকবছর এসেছিলেন। তাঁরা বেগুন দিয়ে একটা তরকারি করতেন। বেড়ালের পায়খানার মতো রঙ হতো। গোলমরিচের হাল্কা ঝাল থাকতো। আহা অমৃত। আমি তো সারা সন্ধ্যা কোনও মতে একটু পড়ে কামারশালেই বসে থাকতাম। ওই আগুনে রঙ, হাপরটানার কায়দা, নিপুণভাবে ঝাল করা, আমাকে মুগ্ধ করে দিত। ইচ্ছে হতো, হাপর টানি। দুয়েক বার চেষ্টা করেছি। সুবিধা হয় নি। গণদেবতা তখন পড়ে ফেলেছি। আমার তাঁকে অনিরুদ্ধ কামার মনে হতো। ... ...

কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৬ নভেম্বর ২০২৪ | ৭৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (হীরেন সিংহরায়)
কাদামাটির হাফলাইফ - ইট পাথরের জীবন - ইমানুল হক
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ০৯ নভেম্বর ২০২৪ | ১১৮৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (কৌতুহলী, Eman Bhasha, কৌতূহলী)গ্রামে আগে ছেলেদের প্রচুর কাজ ছিল। চাষে সাহায্য করা পড়াশোনা করা ছাড়াও ক্লাব করা ফুটবল খেলা, হাডুডু কবাডি নুনচিক / গাদি/ জাহাজ খেলা, শীতে ভলিবল খেলা, ডাংগুলি পেটানো, মার্বেল খেলা, ভাটা খেলা, নিদেন পক্ষে দাবা চাইনিজ চেকার লুডো বা বাগ বন্দি বা তাস খেলা। নাহলে আড্ডা দেওয়া। যাত্রা নাটকের মহলা দেওয়া। সবাই নাটক যাত্রা না করলেও মহলা দেখতে বা শুনতে ভিড় করতেন। নানা ধরনের খেলার দর্শক হতেন। আড্ডায় গিয়ে কথা শুনতেন। মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েরা বিকেলে পাড়া বেড়াতেন। এ ওর চুল বেঁধে দিতেন। কেউ নতুন কোনও সেলাই ফোঁড়াই কুটুম বাড়ি গিয়ে শিখে এলে শিখতে যেতেন। ... ...

হারিয়ে গেল সুখের ট্রামযাত্রা - শুকদেব চট্টোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ১৮২১ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৭, লিখছেন (অয়নেশ, রমিত চট্টোপাধ্যায়, r2h)রেল পরিষেবা চালু হওয়ার পর শিয়ালদহ স্টেশনে বাইরে থেকে আসছে প্রচুর মালপত্র। স্টেশনে আসা মালপত্র শহরের নানা প্রান্তে পৌঁছানর ব্যবস্থা করাটা হয়ে উঠল নগরকর্তাদের প্রধান সমস্যা। সমস্যার কথা জানানর পর ভারত সরকারের কাছ থেকে ট্রাম চালাবার পরামর্শ আসে। কোলকাতার Justice for the Peace পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করলেন। কমিটি, গ্রামের থেকে আসা পণ্য বিভিন্ন গুদামে পৌঁছে দেওয়ার উপযোগী করে একটি রুট ঠিক করল। পরিকল্পনা মঞ্জুর হল। দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে শেয়ালদা থেকে বৈঠকখানা রোড, বৌবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত লাইন পাতা হল। আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত লাইন পাতা হয়েছিল কারণ, ওইখানে ছিল তখনকার ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়ার টিকিটঘর। শিয়ালদহ এবং হাওড়ার মধ্যে পণ্য পরিবহণের সুবিধার কথা চিন্তা করেই ওই স্থান নির্বাচন করা হয়। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় চলল প্রথম ট্রাম। ... ...

হাসপাতালের ডায়েরি - পারমিতা চৌধুরি
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১০ জুন ২০২৪ | ১৫০৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (মন ছুঁয়ে গেল, Aditi Dasgupta, দ)এ বছর চৈত্রের শুরু থেকেই ঝলসে দেওয়া শুকনো গরম। সেই গরমে sskm এর এক একটা লাইনে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে নারী পুরুষ। মেয়েরা এখানে সংখ্যাগুরু। সংসারের যাবতীয় কাজ ভোর রাতে উঠে সামলে তারা চলে আসে। কখনো নিজের জন্য, কখনো সন্তানের জন্য। এমনকি এমন মেয়ের দেখা পেয়েছি যে sskm চেনে হাতের তালুর মত আর তার হাত ধরে প্রথমবারের জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছে তার স্বামী। মেয়েরা না কি রাস্তা পেরোতে পারে না ... ...

সারেতে থাই নববর্ষ - হীরেন সিংহরায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৮ এপ্রিল ২০২৪ | ১৮৬৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (kk, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, হীরেন সিংহরায়)থাইল্যান্ডে দোল নেই। কিন্তু নববর্ষের দিনে আছে জল ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা। এপ্রিল মাসে বেজায় গরম। লাওস কামবোদিয়া থাইল্যান্ডের পথে ঘাটে সেদিন জল আক্রমণের ধুম পড়ে যায়; মারো পিচকারি! সেটা ছবিতে মাত্র দেখেছি। আমাদের এই মন্দিরে তার একটা ছোটো এডিশন আছে – এক ভিক্ষু ঝ্যাঁটা দিয়ে সবার মাথায় জল ছড়িয়ে দেন। দুঃখের বিষয় যে থাইল্যান্ড বা লাওসের স্টাইলে আমরা তাঁকে জল কামান দিয়ে আক্রমণ করতে বা তাঁকে পাল্টা ঝাপটা মারতে পারি না! নববর্ষের পরবের অন্য রিচুয়ালগুলি মোটামুটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ন্যাপহিলের অনুষ্ঠানে - যেমন প্রার্থনার পরে ভিক্ষুদের খাদ্য দ্রব্য দান। সকলে আনেন কিছু না কিছু, সার দিয়ে বসে থাকেন দানের জন্য, ভিক্ষু সেটি গ্রহণ করলে পরেই স্থান ত্যাগ করতে পারেন। অল্প বয়েসি ছেলে মেয়েরা বয়স্ক নারী ও পুরুষের পা ধুইয়ে দেন, পিতা মাতার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক সেটি। পুণ্য অর্জনের আরেকটি পন্থা - বুদ্ধ মন্দির বা স্তূপ নির্মাণে শ্রমদান। মাঠের মধ্যে বালি দিয়ে তৈরি স্তূপ মন্দির আছে, দূরে এক কোনায় রাখা বালির পাহাড়; সেখান থেকে পাত্র ভরে কিছুটা বালি এই নির্মীয়মাণ মন্দিরে পৌঁছে দেওয়াটা একটা সিম্বলিক সহায়তা। নববর্ষের এই দিনে নতুন জামা পরা আবশ্যিক, নিজের বা পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় কম,দান বেশি এবং মদ্যপান বারণ! ... ...

ও চাঁদ - সেমিমা হাকিম
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৭ এপ্রিল ২০২৪ | ২১২০ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (kk, Aranya , Touhid Hossain)আমরা দেশের বাড়ি যেতুম ২৯ শের রোজায়। সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে পরদিন ঈদ নয়ত আর একদিন মানে তিরিশটি রোজা সম্পূর্ণ করে ঈদ পালন। তখন আর চাঁদ দেখার ঝামেলা নেই। হাদিস মোতাবেক তিরিশটি রোজা হয়ে গেলে অবশ্যই পরদিন ঈদ। এখন যেমন,"যাহ! সৌদিতে আগে ঈদ হয়ে গেল। আমাদের হল না কেন?” বলে বিভিন্ন বিতণ্ডার শুরু তখন সেসব কেউ ভাবতও না। চাঁদ দেখা গেলে ঈদ হবে সেই অঞ্চলে নয়ত রেডিওয় কান পেতে থাকতেন মুরুব্বিরা- নাখোদা মসজিদের ইমামসাহেব যা ঘোষণা করবেন মেনে নিতেন সবাই। ... ...

বর্ষশেষ, বর্ষশুরু - অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ১৩ এপ্রিল ২০২৪ | ১৭২৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১০, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Naresh Jana, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এক সন্ধ্যা থেকে আরেক সন্ধ্যা, এক পূর্ণ-চন্দ্র থেকে এক চন্দ্র-হীন রাত কিংবা আরেক পূর্ণ-চন্দ্র, শীত থেকে গ্রীষ্ম, বাড়ির সামনে গাছের ছায়া ঘুরতে থাকে, আজ যেখানে ছায়া পড়েছে আবার কত সকাল বাদে এই ছায়া সেখানে প্রায় অমনি করে এসে পড়বে, দিন, রাত, পক্ষ, মাস, ঋতু, বছর, কোথাও সারা বছর জীবন এক ভাবে ভিজে যায় কি পুড়ে যায়, কিংবা একই ফুল ফোটে, চিরবসন্তের কোকিল ডেকে যায়, কোথাও ঋতুতে ঋতুতে লহরের পর লহর তুলে প্রকৃতি বদলে যায়, দেয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার আসে – কোথাও কেবলই দিন গুনে, কোথাও শীতে পাতাখসা গাছেদের ডালে ডালে বসন্ত আসার মাঝে, কোথাও বসন্তের দিন ফুরালে আকাশ, বাতাস আগুন হয়ে ওঠার আগে, শরীর দিয়ে, চেতনা দিয়ে যতি খুঁজে নিই আমরা, বর্ষশেষ, বর্ষশুরু। ... ...

নারীত্বের উদ্যাপন - ডঃ মঞ্জু রায় - রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ০৮ মার্চ ২০২৪ | ২৬১৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৬, লিখছেন (Arindam Basu, kk, Arindam Basu)কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে মঞ্জু রায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগে গবেষণায় যোগ দিলেন প্রফেসর অমরনাথ ভাদুড়ির কাছে। তারপর গবেষণাই করেছেন সারাজীবন। গবেষণার বিষয় ছিল ক্যান্সারের ওষুধ আবিস্কার। ডঃ মঞ্জু রায় এবং তাঁর স্বামী ডঃ শুভঙ্কর রায় একসঙ্গে কাজ করে কর্কট রোগ বা ক্যান্সারের চিকিৎসায় মিথাইল গ্লাইওক্সাল নামক যৌগটির কার্যকারিতা প্রমাণ করেছিলেন এবং ক্যান্সারের ওষুধ হিসেবে এই যৌগটিকে সাধারণ মানুষের নাগালে আনতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কাজ করেছেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS, যেখানে সি ভি রমনও কাজ করেছেন) এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে; শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার এবং সম্মানও পেয়েছেন সারাজীবনে। ... ...
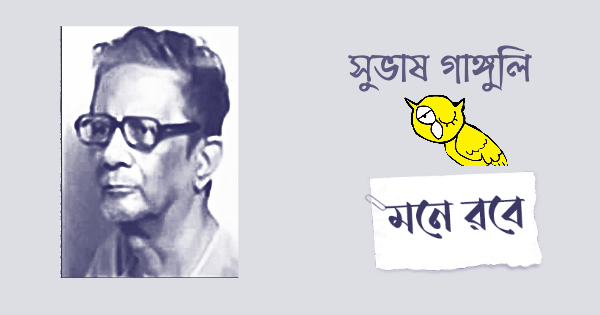
সুভাষদা... এবারের বইমেলায় দেখা হবে না! - কল্লোল
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ : স্মৃতিকথা | ৩০ নভেম্বর ২০২৩ | ১৭৫৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (??, Ranjan Roy, কল্লোল )সুভাষদা, সুভাষ গাঙ্গুলিকে নিয়ে লিখতে গেলে এখন এই বয়সে এসে ঝাপসা হয়ে যাওয়া স্মৃতি ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ভেসে চলে যায়। এই তো সেদিন এপিডিআরের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে সাক্ষাতকার নিতে গেছিলাম সুভাষদা-ভারতীদির ফ্ল্যাটে। সেদিনও সেই প্রথমদিনের মত উষ্ণ গলায় সাদর ডাক। সেদিনও সেই প্রথমদিনের মত খাদির পাঞ্জাবী আর বড় ফাদের পাজামা। সেই প্রথমদিনের মত কদমছাঁট চুল, নাঃ সেবার ছিলো একমাথা কালো এবার পাক ধরেছে তাতে। সেই একই রকম ছিপছিপে অবয়ব, কালো ফ্রেমের চশমা। ... ...
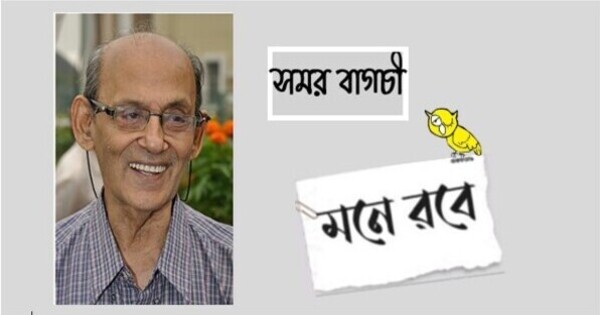
বিরানব্বইয়ের যুবক - প্রদীপ দত্ত
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ : স্মৃতিকথা | ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ২৪৬১ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (রবীন মজুমদার, শম্ভুনাথ সান্যাল, সুজয় আদক )৯২ বছরের কর্মময় জীবন শেষ হল। আমাদের মনের মধ্যে হাহাকার নেই, শূন্যতা কিছুটা আছে, এমন মানুষ কোথায় পাব আর? আমাদের কাছে তিনি ছিলেন বিস্ময়। এই বয়সে এত উৎসাহ, অসুস্থ শরীরেও এমন শারীরিক সক্ষমতা থাকে কি করে? শেষ বয়সেও তাঁর তারুণ্যময় জীবনযাত্রা, কাজকর্ম এবং চিন্তাভাবনা দীর্ঘদিন মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করব আমরা। ... ...
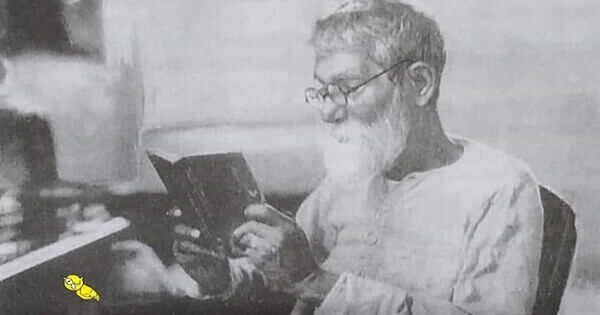
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভিটা ও বসতবাড়ি - শিখা সেনগুপ্ত
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ০২ আগস্ট ২০২৩ | ২০৭৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন ( পার্থ সারথী দত্ত, &/, হীরেন সিংহরায়)কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা বাঙালি’ কবিতায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়াছে বিয়া...”, আবার একই বছরে জন্ম হওয়াতে তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশস্তিপাঠে বলেন, “কালের যাত্রাপথে আমরা একই তরণীর যাত্রী...”। তাঁকে বাঙালি চেনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমী, ছাত্রদরদী, দানবীর, ব্যাবসায়ে উদ্যোগী পুরুষ হিসেবে। এ লেখায় তাঁর জীবনের এমন কিছু অংশের কথা বলবো, যার কিছু অন্যান্য বইয়ে পাওয়া গেলেও, বাকি আমি জেনেছি পারিবারিক গল্প হিসেবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম—অবিভক্ত বাংলার (ব্রিটিশ ভারত) খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাড়ুলি কাটিপাড়া গ্রামে এক প্রাচীন জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে। সাল ১৮৬১, তারিখ ২রা আগস্ট। বংশের পুর্বপুরুষ দেওয়ান মানিকলাল রায়চৌধুরী বাংলার নবাবের থেকে দক্ষিণদেশে অনেকগুলো তালুক পত্তনি পেয়ে কপোতাক্ষ-তীরে এই অঞ্চলে, গাছপালা কেটে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, জমিদারি স্থাপনা করেন। রায়ের আল বা আলি থেকে গ্রামের নাম হয় রাড়ুলি আর গাছপালা কেটে স্তুপ করে রাখা পাশের গ্রামের নাম কাটিপাড়া। মানিকলাল যথেষ্ট অর্থশালী ছিলেন। ভারী লোহার কড়িকাঠের বরগা, চুন-সুরকি দিয়ে তিনি অন্দরমহলে মহিলাদের জন্য একটি দ্বিতল বাড়ি তৈরি করেন। এই অন্দররমহলেরই একতলার একটি ঘরে, মানিকলালের বংশধর হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর স্ত্রী ভুবনমোহিনী দেবী জন্ম দেন প্রফুল্লকে। ... ...
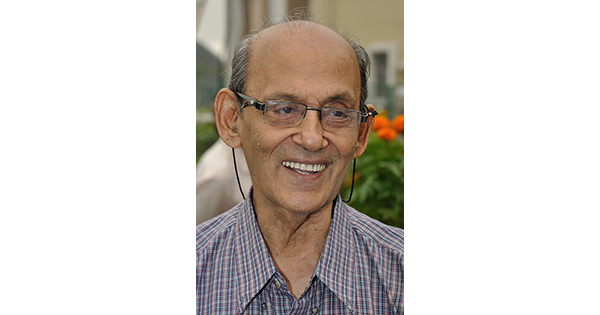
তোমার ছোঁয়ায় তোমার আলোয় - মঞ্জিস রায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ২৮ জুলাই ২০২৩ | ১৭৩৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (sarmistha lahiri)“১৯৮৪ সালে হ্যালির ধূমকেতু যখন এসেছিল, তখন বিড়লা মিউজিয়াম হ্যালির ধুমকেতু দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। তখন আমি সবে এই বিজ্ঞানের জগতে ঢুকেছি। সেই সময়ে আমার ওঁকে প্রথম দেখা। একজন মানুষ, যিনি দৌড়ে একবার ছাদে যাচ্ছেন একবার নিচে নামছেন। কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা দেখে তার সমাধান করতেন। এর পর অল ইণ্ডিয়া অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমার্স মিট, সারা ভারত জুড়ে অপেশাদার আকাশপ্রেমীদের সংগঠন, তার যে মিট, সেটা আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে করেছিলাম। সেই মিটটার জায়গা খোঁজার জন্য আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন কখনও নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, কখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। এরপর একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে সংগঠন করার পরে। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ওঁর সঙ্গে করি এবং শিখি যে বিজ্ঞান কিভাবে ডেমনস্ট্রেট করতে হয়। ... ...
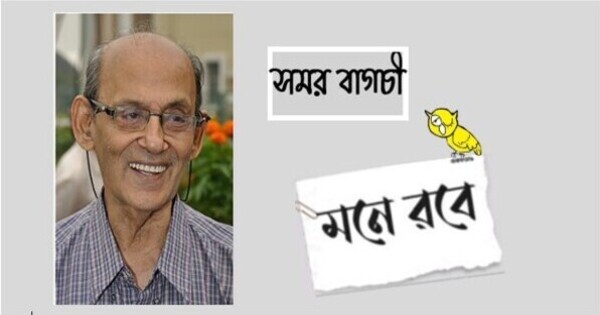
সমর বাগচী: আমার স্মৃতির বেলাভূমিতে - অশোক মুখোপাধ্যায়
বুলবুলভাজা | স্মৃতিচারণ | ২৩ জুলাই ২০২৩ | ২১৮৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮বিজ্ঞানের লোকপ্রিয়করণের পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে সমরদার ছিল এক তীব্র অন্তর্দহন। গাছপালা বনাঞ্চল সবুজের আচ্ছাদন পাহাড়ের গালিচা ক্রমবর্ধমান হারে উচ্ছেদ ও ধ্বংস দেখতে দেখতে তিনি মনে হয় যেন পাগল হয়ে উঠতেন। আমাদের বলতেন, মানুষ এত মূর্খ হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে বোঝান। জল জমি বায়ু চলে গেলে পশু পাখি নিঃশেষিত হয়ে গেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? বাজার দোকান মল আর কেনাকাটার ভিড় দেখতে দেখতে দেশে ক্রমবর্ধমান ভোগবাদের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে তাঁর ছিল অন্তহীন ক্ষোভ। বিভিন্ন সভায় গিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলতেন, আমাদের এত জামা জুতো ব্যাগ কেন লাগবে? রাস্তায় আর কত গাড়ি চালাতে পারবে? আর কত কারখানা করতে পারবে না দেশের সীমিত সম্পদকে ব্যবহার করে? সমস্ত সম্পদ যদি আমরাই শেষ করে দিয়ে যাই, ভবিষ্যতের শিশুদের জন্য আমরা কী রেখে যাব? আর তখনই যেন এক বেদনাতুর আক্ষেপ বেজে উঠত তাঁর কণ্ঠে – যারা দেশটা চালাচ্ছে, তারা কি কিছু বুঝতে পারছে না? ... ...
- পাতা : ২১
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
(লিখছেন... Sara Man, Supriyo Mondal, Sara Man)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... :|:, bikarna, bikarna)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দ, হীরেন সিংহরায়, Tuhinangshu Mukherjee)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- বুলবুলভাজা গুরুচন্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগ। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখা অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯ ও লেখকের অনুমতি ও উল্লেখ প্রয়োজনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।












