- বুলবুলভাজা পড়াবই মনে রবে

-
নিজের কবিতাকে কিছুতেই হতে দেননি তাঁর তরজমা করা অজস্র মহাকবিতার প্রতিধ্বনি
অভীক মজুমদার
পড়াবই | মনে রবে | ০৯ আগস্ট ২০২০ | ৩২৬১ বার পঠিত 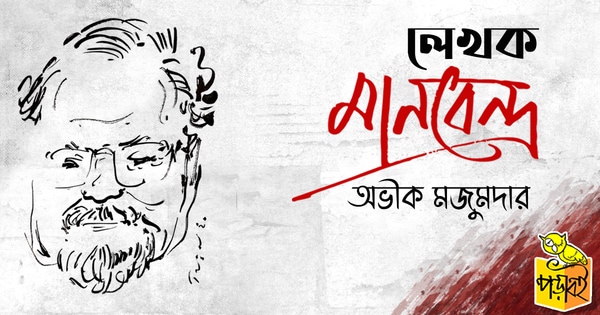
১. আমাদের ছাত্রবয়সে ‘কাব্যনাট্য’ আর ‘নাট্যকাব্য’ নিয়ে পাতার পর পাতা আহাম্মকি উত্তর লিখতে হত। প্রমাণ করতে হত রচনায় কোন্ শব্দে বেশি জোর! মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই দুর্নিবার নির্বুদ্ধিতায় ঢুকব না। তিনি কবি অনুবাদক নাকি অনুবাদক কবি?
তবে তরজমার সঙ্গে মৌলিক কাব্যচর্চার একটা সূক্ষ্ম বহু কৌণিকতা আছে। মানবেন্দ্রকে মনে রেখেই তরজমা শব্দটি ব্যবহার করলাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, অনুবাদ শব্দটিতে আছে ‘বাদ’ আর তরজমায় ‘জমা’। সুতরাং, তিনি ‘তরজমা’-কেই বেশি আদরের মনে করেন।
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যরচনার সঙ্গে এই জমাখরচের হিসাব রাখাটা বেশ জরুরি হয়ে পড়ে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চারটি কিন্তু অনূদিত কাব্যগ্রন্থ প্রায় ত্রিশটি। যদিও এর বাইরেও বহু কবিতা অনুবাদ গ্রন্থিত হয়নি। এই অসম বণ্টন কি কোনো ইশারা দেয়? নাকি তাঁর অদম্য এক পরিকল্পনাকেই প্রকাশ করে?
২. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টি ঠিক উলটো। অনূদিত কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। একই কথা প্রযোজ্য বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে শঙ্খ ঘোষ অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। বুদ্ধদেব বসু অকপটে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন কবিতা লেখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন তিনি অনুবাদে মন দেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও প্রায় একই ধরনের প্রণোদনায় বিশ্বাসী ছিলেন। একে আমরা একটি বিশেষ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।
দ্বিতীয় প্রবণতা লক্ষ করা যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে। সেখানে অনুবাদ এবং মৌলিক কাব্যরচনা চলে সমান্তরাল পথে। কেউ কারও বিকল্প নয়। একই প্রবণতা হয়তো দেখা যাবে অরূণ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং পুষ্কর দাশগুপ্তের ক্ষেত্রেও। একই কথা বলা চলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবারূণ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও।
কবিতা অনুবাদকের মধ্যে আবার কেউ কেউ মৌলিক কবিতার ধারকাছ মাড়ান না। যেমন চিন্ময় গুহ। পলাশ ভদ্রেরও কবিতা খুব চোখে পড়েনি।
মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথকে আলোচনার বাইরে রাখছি, যদিও এঁরা দ্বিতীয় দলেই পড়বেন।
বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে দুই বিরোধী নন্দনশিবিরের সদস্য হলেও অনুবাদের সঙ্গে মৌলিক কবিতার সম্পর্কের নিরিখে বেশ খানিকটা সামীপ্য আছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষত বোদলেয়র আর রিলকের মাধ্যমে আলোড়িত হন। সেই চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যেতে থাকে তাঁর ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ কাব্যপর্বে এবং পরবর্তীকালে। অন্যদিকে, বিষ্ণু দে প্রথম পর্বে বহুলাংশে গভীর ভাবে এলিয়ট এবং পরবর্তী কালে এলুয়ার, আরাগঁ এবং নেরুদার দ্বারা প্রভাবিত হন। কে জানে, প্রত্যক্ষ প্রভাবের চিহ্ন এবং কৃতজ্ঞতাবশতই হয়তো শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দেন, ‘র্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব’!
৩. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য, আমার অন্তত মনে হয়, একটু অন্যরকম। তরজমাকারীকে আমার নদী পারাপারের বড়ো মাঝি মনে হয়। অনবরত দুই ভাষানদী পারাপারের অভিজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে লেখকের ‘আত্ম’-কে লুপ্ত করারই অনুশীলন। মানববাবু সেকথা বুঝতেন। এই ‘মিডিয়াম’ হিসেবে কাজ করতে করতে কণ্ঠস্বর বদলে যাবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেটা মানববাবুর সম্ভবত অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সর্বদা চাইতেন ‘নিজস্ব’ কণ্ঠস্বর নিয়ে কবিতায় ফিরে আসতে। হয়তো সেই জন্যই এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতেন, প্রস্তুতি নিতেন। লক্ষ করুন, ‘অর্ধেক শিকারী’ (রচনা ১৩৬৩-১৩৭০। প্রকাশ ১৩৮২), ‘বাঁচাকাহিনী’ (রচনা ১৩৭১-১৩৮১। প্রকাশ ১৩৮৩), ‘সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি’ (রচনা ১৩৮৫-১৩৯৫। প্রকাশ ১৪০৬), ‘এই সময় শনির’ (রচনা ১৩৬৩-১৪০৭। প্রকাশ ২০০৩)—এরকম মানচিত্র প্রমাণ করে তিনি কত দূর নিভৃত অথচ সচেতন কিমিয়াবিদ্যার উপাসক ছিলেন। সারা বিশ্বের অনবদ্য এবং অতি-শক্তিশালী কবিদের কণ্ঠে তিনি যেসব মহাকবিতা উপহার দিয়েছেন পাঠককে তার ব্যাপ্তি এবং আয়তন বিস্ময়কর। তিনি সন্তর্পণে নিজের কবিতায় তাঁদের প্রতিধ্বনি করতে চাননি। একটু লক্ষ করলেই দ্যাখা যাবে, তাঁর পুনরাবৃত্ত কাব্যবিষয় নিজস্ব জীবনযাপন, আর চারপাশের বহুতরঙ্গিত জনদুনিয়া। তারই নানা মিহি-মোটা প্রসঙ্গকে শ্লেষ, রসিকতা আর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরতে চেয়েছেন তিনি। ভাষার নানান পরীক্ষানিরীক্ষা, সংরূপের বিভিন্ন প্রয়োগ সেখানে লক্ষণীয়। আরও মন দিয়ে দেখলে মনে হয়, অনুবাদের ক্ষেত্রে যেসব ভাষাবিন্যাসে তিনি প্রদীপ্ত তার সঙ্গে এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার বহু পার্থক্যও রয়েছে। তিনি ধারালো, কিন্তু ধারদেনা করে শান দেননি।
৪. সমস্যা হল, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরজমার পাঠক সীমিত হলেও সংখ্যাটি নিতান্ত অল্প নয়। অথচ, তাঁর নিজস্ব কাব্যগ্রন্থগুলির পাঠকের সংখ্যা একেবারেই হাতে-গোনা। ফলে, যে গুরুত্বে তাঁর পর্যালোচনা প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। লেখার মধ্যে এখান-ওখান থেকে দু-চারটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর পূর্বাপর প্রবণতাগুলিকে ধরা অসম্ভব। তিনি চলে গেছেন। তাঁর পাঠকবর্গ কি অন্তত দে’জ থেকে প্রকাশিত ‘মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাসংগ্রহ’ (২০০৪) বইটি আগাগোড়া পড়ে দেখতে চাইবেন? হয়তো সেখানেই লুকিয়ে আছে তর্পণের প্রকৃত পবিত্র পন্থা।
৫. ‘অর্জুন যেমন ভাবে পাখির একটি চোখই শুধু দেখেছিলো
সেইভাবে প্রোমোটার কলোনির এই খুদে বাড়িটার দিকে
তার তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।
হঠাৎ মিনতি যেন ঘুম ভেঙে জাগে।
সাত নং বেডের রুগিকে এইবারে ইঞ্জেকশন দিতে হবে—
ইনট্রা-ভিনাস।’
(ডাকপিয়ন)
মানবেন্দ্রবাবুর স্কেচ: হিরণ মিত্র
থাম্বনেল গ্রাফিক্স: স্মিতা দাশগুপ্ত
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 b | 14.139.***.*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৫96097
b | 14.139.***.*** | ০৯ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৫96097- আরেকটু বেশি হলে ভালো লাগতো।
 মৌলিক মজুমদার | 2409:4066:16:c9c8::190b:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০২:০৫96324
মৌলিক মজুমদার | 2409:4066:16:c9c8::190b:***:*** | ১৬ আগস্ট ২০২০ ০২:০৫96324পড়লাম। ভাল লাগল
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Srimallar, .)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, kk)
(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... :|:, aranya, dc)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Srimallar)
(লিখছেন... Bratin Das)
(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।












