- হরিদাস পাল আলোচনা শিক্ষা

-
ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার বলতে সত্যি কী বোঝায়?
অনির্বাণ কুণ্ডু
আলোচনা | শিক্ষা | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ১৪৫২ বার পঠিত | রেটিং ৫ (২ জন) 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলে একটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ভালো বাংলা কী হবে জানি না, জ্ঞানতন্ত্রের চাইতে জ্ঞানভাণ্ডার কথাটা বোধহয় কিঞ্চিৎ বেশি গ্রহণযোগ্য। এর সম্বন্ধে কেউ কেউ অত্যুৎসাহী, কেউ অতিমাত্রায় শঙ্কিত। দু-দলের পক্ষেই যুক্তির অভাব নেই। সে সব যুক্তির মধ্যে আমরা এখানে যাব না, কারণ তাতে বিজ্ঞানের চেয়ে রাজনীতি ও নানারকম আর্থসামাজিক কূটকচালির গুরুত্ব বেশি। তবে জ্ঞানতন্ত্র বলতে প্রাচীনকালের শিক্ষা বা জ্ঞানের চর্চার পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার কথা যে অবাস্তব—তা এর প্রবক্তারাও বোঝেন। সারা পৃথিবীতেই জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কিছু স্বীকৃত পদ্ধতি আছে, তার বাইরে গেলে আমাদেরই ক্ষতি। সুতরাং আশা করা যায় – গুরুকুল, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইত্যাদি ফিরিয়ে আনা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য প্রাচীন ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানের কী অগ্রগতি হয়েছিল—তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেটা সাধু উদ্দেশ্য। আধুনিক জ্ঞানের চর্চা ইউরোপীয় কাঠামো অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস ঔপনিবেশিক চশমা দিয়ে না দেখাই ভালো। তাহলে আশঙ্কা কেন?
জ্ঞান মানে অবশ্যই শুধু বিজ্ঞান নয়। দর্শন, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, সবই নলেজ বা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এখানে শুধু বিজ্ঞানের অংশটুকু নিয়েই কথা বলব, তার বেশি যোগ্যতা আমার নেই। বিজ্ঞান মানে, যে শাস্ত্র প্রকৃতিকে জানতে সাহায্য করে, আর প্রকৃতি বলতে জড় ও জীব – দু-পক্ষকেই বোঝায়। সাহিত্যচর্চা করতে গেলে যেমন ভাষা ও তার ব্যাকরণ জানতেই হয়, তেমনি বিজ্ঞানের চর্চা করতে গেলেও বিজ্ঞানের ভাষা জানতে হয়। বিজ্ঞানের এই ভাষার নাম অঙ্ক। কাজেই অঙ্ককেও আমরা আপাতত বিজ্ঞানের মধ্যেই ধরব।
অঙ্ককে বিজ্ঞানের ভাষা বললাম কেন? একটা ছোট্ট ফরমুলা দিয়ে যা বোঝানো যায়—অন্তত যাঁরা সে ভাষা পড়তে পারেন তাঁদের কাছে—সেটা লিখে বোঝাতে গেলে হয়তো এক পাতা লাগবে। শুধু তাই-ই নয়। অঙ্কের মধ্যে একটা কঠোর যুক্তির শৃঙ্খলা আছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এক সময়ে জীববিজ্ঞানের চর্চায় অঙ্ক অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আজকাল সে দিন পাল্টেছে, অঙ্কের একাধিক শাখা—যেমন পরিসংখ্যান—জীববিজ্ঞানের আলোচনাতেও দরকারি হয়ে উঠেছে।
বিজ্ঞান বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সেটা মূলত পশ্চিমী বিজ্ঞান, অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান। আধুনিক বিজ্ঞানের ভরকেন্দ্র ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং শিল্পবিপ্লবের সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপ, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিরাট সংখ্যক ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের আশ্রয় দেবার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও দ্বিতীয়—এবং বিজ্ঞানের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য—ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে গ্রিক সভ্যতা বিজ্ঞানের চর্চায় নিজেদের উজ্জ্বল অবদান রেখেছিল, কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগের অন্ধকারে সে ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়। মধ্যযুগে পারস্য থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ করে চলছিলেন। তাঁদের কাজ ইউরোপে পৌঁছে সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটায়, এখনো বহু বিজ্ঞানের পরিভাষায় আরবি নামের ছায়া রয়ে গেছে। যেমন অ্যালজেব্রা।
আরব-পারস্যের এই বিজ্ঞানীরা যে তাঁদের জ্ঞানের একটা বড় অংশ হিন্দ বা ভারত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সে কথা তাঁরাই বলে গেছেন। বহু সংস্কৃত পুঁথির আরবি অনুবাদ হয়েছিল। অনেক সংস্কৃত শব্দ আরবি হাত ঘুরে ইউরোপে পৌঁছেছিল। যেমন ত্রিকোণমিতির সাইন বা কোসাইনের উৎস সংস্কৃতে জ্যা বা কোটিজ্যা। তার মানে, জ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতীয় সভ্যতার অবদান নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ছিল না। ঠিক কতটা ছিল – তার প্রকৃত মূল্যায়ন জরুরি। ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা আমাদের মনে করতে শেখায়, যে ইউরোপই শ্রেষ্ঠ। সেটা যেমন সত্যি নয়, তেমনি নিজের দেশকে গৌরবান্বিত করার জন্যে, জ্ঞানের জগতে সব কিছুই ভারতীয় সভ্যতার দান—এটাও ভয়ঙ্কর মিথ্যে।
প্রাচীন (এমনকি মধ্যযুগেও) ভারতীয় জ্ঞানের ধারক ও বাহকেরা সকলেই হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন, অথবা প্রাক্-হিন্দু বৈদিক সভ্যতার লোক। সিন্ধু সভ্যতার জ্ঞানের চর্চা বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তবে ধাতুবিদ্যা তাঁরা জানতেন। একটু অবাক লাগে ভাবলে, যে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনকালে ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ কেউ অবদান রাখেননি। অথচ সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, এ সব দিকে তাঁদের কীর্তি অতুলনীয়।
ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের গুরুত্ব ঠিক কতটা, সেটা বুঝতে গেলে কয়েকটা জিনিসে আমাদের নজর দিতে হবে।- প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।
- ভারতীয় সভ্যতা বিজ্ঞানের যে সব ঘটনা বা নিয়ম আবিষ্কার করেছিল, তা বিজ্ঞানের যুক্তির শৃঙ্খলা মেনে হয়েছিল কিনা।
- অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে কিনা।
খুব অল্প কয়েকটি উদাহরণই দেব, তার বেশি জায়গা এই প্রবন্ধে নেই।
প্রাসঙ্গিকতা
প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা ভালো—সব সভ্যতাই জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু না কিছু দিয়ে গেছে। কেউ বেশি, কেউ কম, কিন্তু তাতে কারো অবদানের গুরুত্ব কমে না। সে যুগের অনেক জিনিসই এখন আর সে অর্থে প্রাসঙ্গিক নয়। চিকিৎসাপদ্ধতি হোক, বা আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন – প্রাচীন বা মধ্যযুগের পদ্ধতি এখন কেউ ব্যবহার করে না। এখানে প্রাসঙ্গিকতা মানে, সেই জ্ঞান বিবর্তিত হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত আসতে পেরেছে কিনা। যেমন মধ্যযুগীয় অ্যালকেমি থেকে এসেছে আধুনিক রসায়নশাস্ত্র।
জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ও চিকিৎসাশাস্ত্র – এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাই পারদর্শী ছিল। জ্যামিতির একটি বিশেষ সমস্যা, পাই (π) বা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের আসন্ন মান নির্ণয়ের কথা পরে আলোচনা করব। ভারতীয়েরা অঙ্ক লেখার ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথম ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে তা আবিষ্কৃত হয়, কে করেছিলেন তা অজানা। একেই চলতি কথায় শূন্যের আবিষ্কার বলা হয়। দশমিক পদ্ধতিতে যে কোনো সংখ্যা লেখা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে সাধারণ লোকেও বড় বড় সংখ্যার যোগ বা গুণ করতে পারত। নবম শতাব্দীর প্রথমে পারস্যের আল-খোয়ারিজমি ও আরবের আল-কিন্দি এই পদ্ধতিকে মুসলিম দুনিয়ায় চালু করেন, সেখান থেকে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে – ভারতীয়েরা শূন্যের ব্যবহার করতেন দশমিক পদ্ধতিতে, এক থেকে নয়ের আবর্তন কখন শেষ হবে সেটা বোঝাতে। শূন্য যে একটা সংখ্যা, কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করা যায়, বা কোনো সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করা যায় – এ কথা তখন তাঁরা আলোচনা করেননি। অনেক পরে, নবম-দশম শতাব্দীতে, শ্রীধর আচার্যের বইতে শূন্য দিয়ে যোগ বা গুণের কথা পাই। এই শ্রীধরই দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের সূত্র বের করেন। ইনি বাঙালী ছিলেন বলে একটা মত আছে।
জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সে যুগে পৃথিবীর কোথাওই জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের তফাৎ করা হত না, স্বয়ং কেপলারও রাজজ্যোতিষী ছিলেন। ৩৬৫ দিনে সৌর বছরের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ থেকে শুরু করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে আর্যভট, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, লল্ল – ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস বিশ্বের কোনো দেশের তুলনায়-ই উপেক্ষণীয় নয়। আর্যভট স্পষ্টভাবে বলেন, যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত বই ‘ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত’ আরবি এবং সেখান থেকে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদদেরও প্রভাবিত করেছিল। এখানে মনে রাখতে হবে, আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় থেকেই গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার অনেক জ্ঞান ভারতে আসে (একে ভারতীয়রা বলেছেন যাবনিক) এবং আর্যভট ও পরবর্তী জ্যোতির্বিদদের চিন্তাধারায় গ্রিক জ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। তাতে ভারতের কোনো অগৌরব নেই, বিজ্ঞান এইভাবেই এগোয়। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায়ই জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণভিত্তিক—গণিতভিত্তিক নয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা মূল সূত্রগুলি আবিষ্কারের চাইতে পর্যবেক্ষণের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন।
রসায়নশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদান মূলত আয়ুর্বেদ ও ধাতুবিদ্যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের “এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি” বইটিতে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। ঋগ্বেদে অয়স্ শব্দটি পাওয়া যায়, তার মানে যে কোনো ধাতু, না শুধুই লোহা – তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু এ কথা বলাই যায়, যে খ্রিস্টের জন্মের আগেও ভারতে তামা, লোহা, দস্তা, টিন, ও এদের নানারকম সঙ্কর ধাতুর ব্যবহার জানা ছিল। দিল্লির কুতব কমপ্লেক্সে অবস্থিত লৌহস্তম্ভটি চতুর্থ শতাব্দীর, এখনো তাতে মরচে ধরেনি—এটা বিস্ময়কর।
আয়ুর্বেদের কথা যখন উঠল, চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাও একটু বলা উচিত। অগ্নিবেশ, চরক, বা সুশ্রুতের লেখা সংহিতাগুলি প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যবিদ্যার জ্ঞানের মূল আকর। চিকিৎসাশাস্ত্র মূলত আয়ুর্বেদ নির্ভর। এই বইগুলি প্রামাণ্য (যদিও এদের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত এবং সম্ভবত অর্বাচীন অংশ আছে – যার সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্ক নেই, তাদের গুরুত্ব দেওয়ার দরকারও নেই), এখনো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এঁদের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, এবং এখানে কোনো উদ্ভট চিকিৎসা বা সার্জারির বিবরণ পাই না – যেমন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা, মানুষের দেহে হাতির মাথা জুড়ে দেওয়া, বা বিনা মাতৃগর্ভে সন্তান উৎপাদন।
গণিতচর্চার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে কেরালার পণ্ডিতদের কথা বিশেষ করে বলা উচিত। এঁদের মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হলেন সঙ্গমগ্রামের মাধব (আনুমানিক ১৩৪০ – ১৪২৫)। ইনি থাকতেন বর্তমান কেরালার মালাপ্পুরম জেলায়। মাধবের নিজের কোনো রচনা পাওয়া যায়নি, কিন্তু তাঁর অনেক অনুগামী নিজেদের লেখায় মাধবের বহু কাজ—প্রমাণসহ—উল্লেখ করেছেন। এই অনুগামীদের মধ্যে পরমেশ্বর, জ্যেষ্ঠদেব ও নীলকণ্ঠ সোমায়াজি অগ্রগণ্য। এঁদের লেখা থেকে জানতে পাই, মাধব ত্রিকোণমিতিতে সাইন, কোসাইন ও আর্কট্যাঞ্জেন্টের অসীম শ্রেণীর সূত্র নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেছিলেন (তবে জ্যেষ্ঠদেবের কিছু কাজও খুবই উল্লেখযোগ্য)। মাধবের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে ইউরোপে নিউটন, লাইবনিৎজ ও গ্রেগরি এগুলির পুনরাবিষ্কার করবেন। তাই এই শ্রেণীগুলিকে এখন মাধব-নিউটন, মাধব-গ্রেগরি, এইরকম নামেও ডাকা হয়। ক্যালকুলাসের গোড়াপত্তনের কাজও মাধবের রচনায় পাওয়া যায়। কেরালা গোষ্ঠীর কাজ ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে বাণিজ্যের যোগাযোগের সূত্রে ইউরোপ ভূখণ্ডে পৌঁছেছিল কিনা, তার মীমাংসা হয়নি, তবে ভারতের অন্যান্য অংশে এঁদের কাজের খুব একটা পরিচিতি ছিল না। অথচ আধুনিক গণিতের আলোচনায় এঁদের কাজই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।যুক্তির শৃঙ্খলা
অঙ্ক ও বিজ্ঞান কঠোর যুক্তিভিত্তিক শাস্ত্র। এই যুক্তিপ্রবাহ বা ন্যায় – অবরোহী বা আরোহী – দুরকমই হতে পারে। অবরোহী ন্যায়ে কয়েকটি মূল সত্যের ওপর ভিত্তি করে এগোনো হয় এবং মূল সত্যগুলি ঠিক থাকলে তার সমস্ত অনুসিদ্ধান্তই সত্যি হতে বাধ্য। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ইউক্লিডের জ্যামিতি। সেখানে পাঁচটি মূল সত্য বা অ্যাক্সিয়মের ওপর গোটা জ্যামিতি জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে; আজও স্কুলে ইউক্লিডের জ্যামিতি অবশ্যপাঠ্য। ইউক্লিড আধুনিক গণিতের যুক্তিপ্রবাহ নির্ধারণ করেছিলেন বলাটা অত্যুক্তি নয় (অনেক পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, গণিতবিদরা দেখান যে পঞ্চম সত্যটি বাদ দিয়েও আরেকরকম জ্যামিতি তৈরি করা যায়। সে অন্য গল্প)।
আরোহী ন্যায়ে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। পর্যবেক্ষণ যত বেশি হবে, সিদ্ধান্ত তত নিখুঁত হবে। আমরা কয়েক লক্ষ কাক দেখে যদি সিদ্ধান্ত করি – সব কাকের রং কালো, সেটা আরোহী ন্যায়। যদি সাদা কাক দেখতে পাই, তখন আমাদের সিদ্ধান্ত পালটাবে, বলতে হবে যে ৯৯.৯৯৯৯ শতাংশ কাক কালো। বিজ্ঞান বেশিরভাগ সময়ে আরোহী ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে, সেইজন্যেই বিজ্ঞানের সূত্রগুলির পরিমার্জনের দরকার পড়ে। এইখানেই পরীক্ষার গুরুত্ব; হাতেকলমে পরীক্ষা না করে, বা পরীক্ষালব্ধ তথ্য ব্যবহার না করে, বিজ্ঞানের চর্চা হয় না।
মোদ্দা কথা হল – কোনো জিনিসকে বিজ্ঞানের সত্যের মর্যাদা পেতে হলে মধ্যবর্তী যুক্তির ধাপগুলি অপরিহার্য। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অধিকাংশ সময়ে তাঁদের বইতে অন্তিম সিদ্ধান্তটি লিখেছেন, মধ্যবর্তী ধাপগুলো দেখাননি, অর্থাৎ তাঁরা কীভাবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন – সেটা সবসময়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এটা একটা বড় কারণ যে তাঁদের আবিষ্কার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি (এটা অ-ইউরোপীয় অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঘটেছে)। খাস ইউরোপেও এমন উদাহরণ আছে। গণিতবিদ পিয়ের দ ফার্মা তাঁর একটি বইয়ের মার্জিনে একটি সিদ্ধান্ত লিখে রেখেছিলেন, বলেছিলেন – প্রমাণটা এত বড়, যে মার্জিনে ধরবে না। এটি ফার্মার শেষ উপপাদ্য নামে খ্যাত। সেটি দীর্ঘদিন কেউ প্রমাণ করতে পারেননি, ১৯৯৪ সালে অ্যান্ড্রু ওয়াইলস উপপাদ্যটি প্রমাণ করেন, তাই প্রমাণের কৃতিত্ব ওয়াইলসের, ফার্মার নয়।
খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের কোনো এক সময়ে বৌধায়নের শুল্বসূত্র লেখা হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু গাণিতিক ফর্মুলা আছে, যা যথেষ্ট নিখুঁত। যেমন দুইয়ের বর্গমূল পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক। কিন্তু এটি যে অমূলদ রাশি, কয়েকটি ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করে এর মান পাওয়া যায় না – সেটা তখন কেউই জানতেন না। মুশকিল হল, কীভাবে সংখ্যাটি পাওয়া গেল – সেটা কোথাও বলা নেই, তার ফলে একই পদ্ধতিতে তিন বা পাঁচের বর্গমূল বের করা যাবে কিনা – তার কোনো ধারণাই আমরা পাই না। পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী বা গণিতবিদদের সম্বন্ধেও মোটের ওপর একই কথা প্রযোজ্য। তাঁদের বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই শ্লোকের আকারে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা। পরে যাঁরা টীকা লিখেছেন, তাঁরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন আর্যভটের বিখ্যাত বই আর্যভটীয় – লেখা অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে, তার ব্যাখ্যা করেছেন ভাস্কর ও আরো প্রায় নশো বছর পরে নীলকণ্ঠ সোমায়াজি।
আর্যভটের কথা যখন উঠল, পাইয়ের মান নির্ণয় নিয়ে দু-চার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাই (π), অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত। আজ আমরা জানি পাই একটি তূরীয় সংখ্যা, এর একেবারে সঠিক মান নির্ণয় অসম্ভব, আমরা শুধু আসন্ন মান বের করতে পারি, যেমন ৩.১৪১৫৯২৬৫৪…। চিন, মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, মেসোপটেমিয়া, গ্রিস – সর্বত্রই পাইয়ের মান নির্ণয়ের নানারকম চেষ্টা দেখা যায়, সবাই স্বাধীনভাবেই এগিয়েছিলেন, একজনের প্রভাব অন্যের ওপর পড়েছে বলে প্রমাণ নেই। পাইয়ের মান যে তিনের থেকে সামান্য বেশি – এটা সবাই বলেছেন, বৌধায়নও। কী করে নির্ণয় করতে হবে, সেই যুক্তির ধাপগুলি প্রথম দেখান আর্কিমিডিস। যেমন একটা বৃত্তের মধ্যে এবং ঠিক বাইরে দুটো বর্গক্ষেত্র এঁকে সহজেই দেখানো যায় পাইয়ের মান ২.৮-এর চেয়ে বেশি কিন্তু ৪-এর কম। বহুভুজের বাহুর সংখ্যা যত বাড়ানো যাবে, পাইয়ের মান তত ভালোভাবে বের করা যাবে। আর্কিমিডিস বলেছিলেন পাই ২২৩/৭১-এর চেয়ে বেশি কিন্তু ২২/৭-এর কম। পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক গণিতবিদ জু চংজি পাইয়ের মান সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। আর্যভট পাইয়ের মান বলেছিলেন ৬২৮৩২/২০০০০ = ৩.১৪১৬। হয়তো সকলেই আর্কিমিডিসের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু বিশদে কেউ কিছু বলেননি।
তার মানে, যুক্তির ধাপগুলো উহ্য থাকলে আমরা যদি সেগুলো পুনর্গঠন করতে পারি, বা আমাদের পূর্বসূরীরা করে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই আবিষ্কারকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু এই রন্ধ্রপথে অপবিজ্ঞান ঢুকে পড়তে পারে, সেটাই আশঙ্কার কারণ।বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান
যা বিজ্ঞানের যুক্তির শৃঙ্খলা মেনে চলে না, কিন্তু নিজেদের বিজ্ঞান বলে চালাতে চায় – তাই-ই অপবিজ্ঞান। যে সব দাবি আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মতে অবাস্তব, তাকে বিজ্ঞান বলা অশিক্ষার নামান্তর। গ্রহের শান্তির জন্যে যে পাথর ধারণ করা হয়, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই – একথা হয়তো জ্যোতিষীরাও আড়ালে স্বীকার করবেন। দূরের কোনো গ্রহ পৃথিবীতে কোনো মানুষের ওপর যেটুকু বল প্রয়োগ করে—নিউটনের সূত্র দিয়ে সহজেই সেটা বের করা যায়—তার চেয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় চলা ট্রাকও বেশি বল প্রয়োগ করে। পাথরের এমন কোনো ধর্ম নেই – যা গ্রহের সেই অতি সামান্য টানকে প্রতিহত করতে পারে। তেমনি নানারকম বিশ্বাস বা কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মোড়কে চালানোও অপবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত, যেমন গ্রহণের সময় খাবার না খাওয়া। কাব্য, পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থে নানারকম অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, যেমন গণেশের হস্তিমুণ্ড বা পুষ্পক রথ, ওগুলো কবিদের কল্পনা বলেই মেনে নেওয়া ভালো।
কিন্তু এগুলোই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। সাধারণ বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায় – ওপরে বলা জিনিসগুলো বিজ্ঞান হতে পারে না, মানুষের বিশ্বাসের ওপরেই তাদের বাঁচামরা। অনেক সময় অপবিজ্ঞানকে সূক্ষ্মভাবে বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে দেওয়া হয়। যেমন, পৃথিবী সব জিনিসকে নিজের দিকে টানে, তাই তারা পৃথিবীতে এসে পড়ে – কোনো প্রাচীন শাস্ত্রে এরকম কথা লেখা থাকলেই, নিউটনের অনেক আগে আমরা মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছি—এটা প্রমাণ হয় না। পৃথিবীতে আপেল এসে পড়ে, কারণ পৃথিবী আপেলকে টানে—এটা গুহামানবরাও বলতে পারত। ব্রহ্মাণ্ডে সব টানাটানিই যে একই সূত্রের ফল—সেটা নিউটনই প্রথম দেখান, আর বিজ্ঞানের যে কোনো সূত্রের জন্যে এই সার্বজনীনতাই মূল কথা।
শাস্ত্রে, ধর্মগ্রন্থে, বা সাহিত্যে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা থাকবে না—এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের কাজ – সেই সব কথাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া। চরক বা সুশ্রুতের চিকিৎসাবিদ্যা, আর্যভট বা মাধবের অঙ্ক, এখন তা ঠিক ভুল যাই প্রমাণিত হোক না কেন, কবিকল্পনা নয়। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে যা বর্ণিত আছে তা কবিকল্পনা হতে বাধা নেই, বরং অতিরঞ্জন কাব্যের অলঙ্কার হিসেবেই স্বীকৃত। ধর্মগ্রন্থের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো—সব ধর্মের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। যাঁরা মনে করেন, ধর্মগ্রন্থে যা আছে তাই-ই একমাত্র অভ্রান্ত সত্য আর যা সেখানে নেই তা ভ্রান্ত বা অধার্মিক কথা, তাঁরা বড় ধার্মিক হতে পারেন কিন্তু আধুনিক সভ্য মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারেন না।
জেমস আশার নামে এক ধর্মযাজক ওল্ড টেস্টামেন্টকে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে অঙ্ক কষে বের করেছিলেন যে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সামান্যতম বিজ্ঞানের ধারণা যাঁর আছে, তিনিই জানবেন এটা কত হাস্যকর। যাঁরা প্রাচীনকালে এই সব বই লিখেছিলেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানতেন, কালক্রমে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে (তার জন্যে বহিরাগত আক্রমণকারীদের দায়ী করা মুখরোচক), এই লুপ্ত জ্ঞানের তত্ত্বও অপবিজ্ঞানের উৎস।
ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা হবে—এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই আশঙ্কার পেছনে অনেক কারণ আছে, তা সকলেই জানেন। নানারকম কুসংস্কারকে দেশজ ঐতিহ্যের মোড়কে বিজ্ঞান বলে চালাবার চেষ্টা হবে, বা যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এমন বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্যে করদাতাদের টাকা খরচ হবে (যেমন গোবর বা গোমূত্রের তথাকথিত পবিত্রতার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার খোঁজ) – এ আশঙ্কা অমূলক নয়, এবং সমষ্টিগত চিন্তাধারার এই মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাও খুব কঠিন নয়। পরিষ্কারভাবে বলা যাক – প্রাচীন ভারতে বিমান বা দূরদর্শন ছিল না, পুষ্পক রথ বা সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টির উল্লেখ রূপক বা কবিকল্পনা। একই কথা প্রযোজ্য স্টেম সেল গবেষণা বা টেস্টটিউব বেবির ক্ষেত্রে। জন্মের কাহিনীতে সামাজিক কলঙ্কের ভয় লুকিয়ে থাকলে তা আড়াল করার জন্যে অনেক অলৌকিক জিনিসের অবতারণা করতে হয়, একমাত্র মূর্খরাই তা আক্ষরিক অর্থে ধরে নেয়।
তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেল। যে সমস্ত তত্ত্ব বা আবিষ্কারের পেছনে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরীক্ষার ব্যবহার হয়েছে, তা প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। যেমন উড়োজাহাজ, মহাকাশযান, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, বিগ ব্যাং তত্ত্ব, অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, পরমাণু বোমা, জিনপ্রযুক্তি, বা ক্যান্সারের চিকিৎসা। কী আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব ছিল? প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে যা যুক্তি দিয়ে অনুমান করা যায়, আর নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে (ট্রায়াল অ্যান্ড এরর) বা অঙ্ক কষে যা পাওয়া যায়। বারুদ, কাগজ, পাইয়ের মান, আহ্নিক গতি, অয়নচলন, আয়ুর্বেদ, সবই তার মধ্যে পড়ে।
যদি বলেন, আধুনিক সব আবিষ্কার যে সে যুগে ছিল না তার প্রমাণ কী? প্রাচীন জ্ঞান কি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না? মিশরীয়রা কীভাবে মমি বানিয়েছিল তা কি আমরা এখন জানি? এই কুযুক্তির দুটো উত্তর আছে। এক, স্টেম সেল বা উড়োজাহাজের জন্যে যে প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি লাগে সেটা প্রাচীন যুগে থাকা সম্ভব ছিল না, বিজ্ঞানেরও ধারাবাহিক বিবর্তন হয়। যা ছিল, তা কোনো চিহ্ন না রেখে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না—অন্তত কোনো বিজ্ঞানীর লেখায় তার বিশদ বর্ণনা থাকবে, শুধুমাত্র কাব্যে বা ধর্মগ্রন্থে নয়।
দ্বিতীয় যুক্তি, অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ দরকার, অনস্তিত্বের নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কৌতুকনকশাটি মনে করি, যেখানে প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ও বাতাসে অক্সিজেনের অস্তিত্ব জানা ছিল কি না, তার সম্বন্ধে একজন আক্ষেপ করছেন --- “তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যাল্ভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রদর্শন করিবে ইহাও কি সম্ভব! যে ম্লেচ্ছগণ শত শত আর্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উষ্ণীষ ও শিখাসমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে?” এখন কি পরিস্থিতি খুব কিছু পাল্টেছে?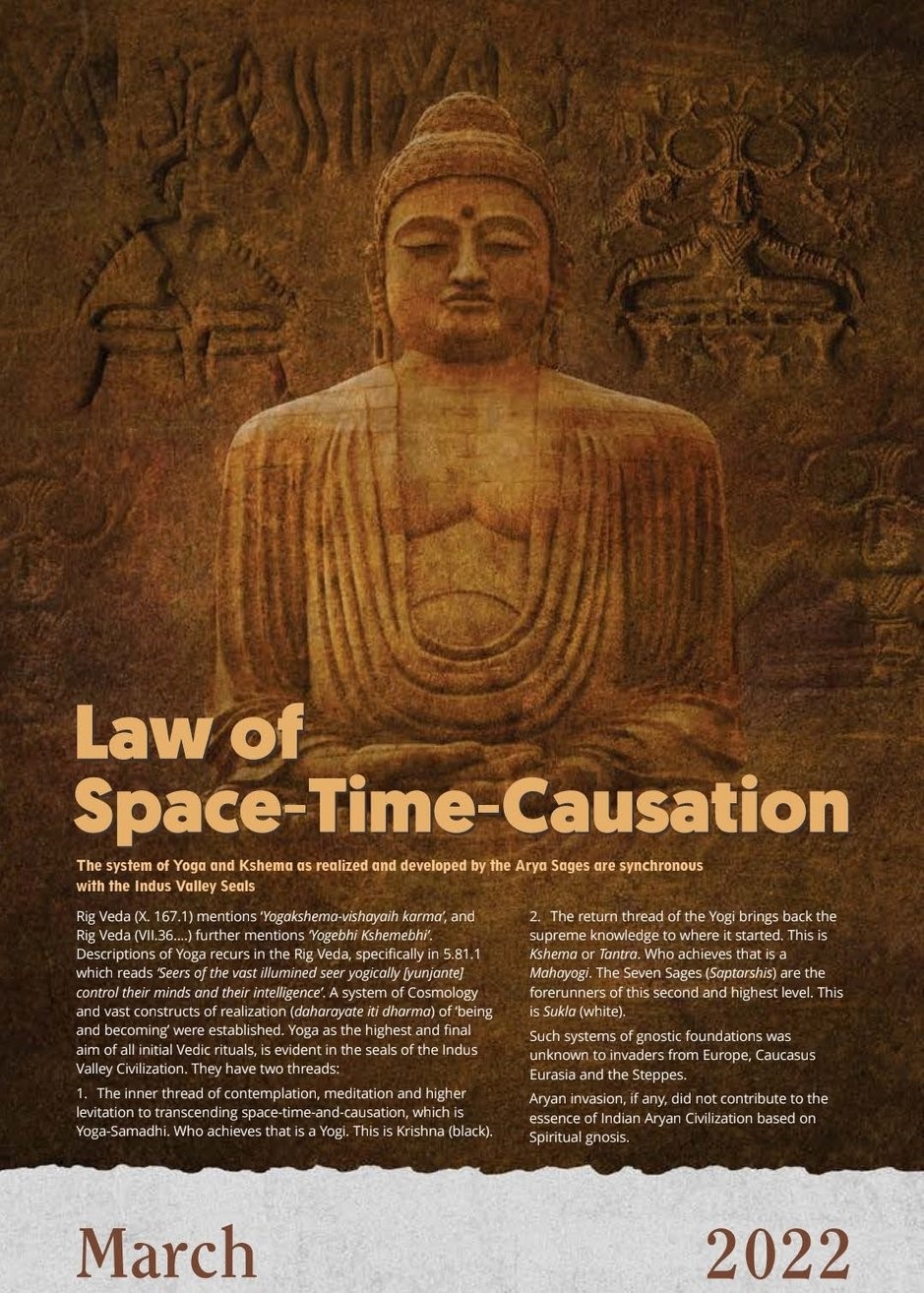
"আই আই টি খড়্গপুর থেকে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমস-এর ক্যালেন্ডারের একটি পাতা: সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সিলমোহর, যোগক্ষেম ও স্পেস-টাইম - এক দেহে হল লীন" --- গুরু-রোবট-১৭
লেখাটি পূর্বে বিজ্ঞানভাষ পত্রিকার নভেম্বর, ২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 মত | 165.225.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩:৪৫528622
মত | 165.225.***.*** | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩:৪৫528622- বেশ
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।














