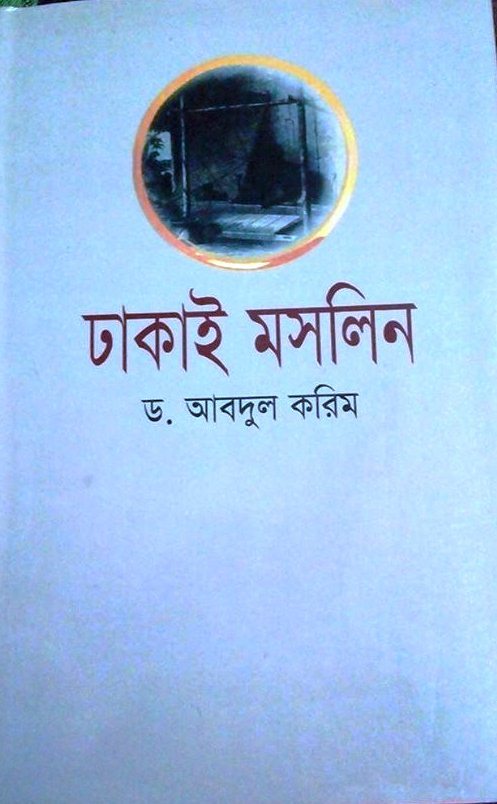- ভাটিয়ালি
- এ হল কথা চালাচালির পাতা। খোলামেলা আড্ডা দিন। ঝপাঝপ লিখুন। অন্যের পোস্টের টপাটপ উত্তর দিন। এই পাতার কোনো বিষয়বস্তু নেই। যে যা খুশি লেখেন, লিখেই চলেন। ইয়ার্কি মারেন, গম্ভীর কথা বলেন, তর্ক করেন, ফাটিয়ে হাসেন, কেঁদে ভাসান, এমনকি রেগে পাতা ছেড়ে চলেও যান।
যা খুশি লিখবেন। লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়। এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই। সাজানো বাগান নয়, ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি। এই হল আমাদের অনলাইন কমিউনিটি ঠেক। আপনিও জমে যান। বাংলা লেখা দেখবেন জলের মতো সোজা। আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
পাপাঙ্গুল | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১৪:১৯542566
- উপন্যাস নয় এটা পড়তে পারেন -
-
দ | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১৩:৫৩542565
- একি! মসলিন বানানোর টেকনিক তো বিলুপ্ত হয় নি। যেটা বিলুপ্ত হয়েছিল সেটা হল ফুটি কাপাস গাছ। তো সে গাছটাও বাংলাদেশে উদ্ধার করা গেছে বলে পড়েছিলাম। ফুটি কাপাসের তুলো থেকে সুতো বের করে মসলিন বোনা এতদিনে হয়ে যাবার কথা। খুঁজে দেখতে হবে।
-
Manali Moulik | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১৩:২৭542564
- রমাপদ চৌধুরির উপন্যাস 'লালবাঈ' এই পর্বটির ইতিহাসের একটি দারুণ উৎস। যদিও উপন্যাসের খাতিরে কল্পনা আছে তাও... ওখানে হাবসি সুলেমানের কাছে একটি মেয়ে মসলিন বিক্রি করতে আসছে ও জানাচ্ছে, মসলিন কেবল মেয়েরাই বুনতে পারে তাও ৩০ বছর বয়স অবধি। তারপর আর নাকি বিশেষ সুক্ষ্ম কাজ করা মসলিন তৈরী হয় না। এখন তো আর্টিফিসিয়াল মসলিন তৈরী হচ্ছে ও আন্তজার্তিক বাজারে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত কীভাবে মসলিন তৈরী করা হতো, সে পদ্ধতি আজও অজানা। আর ইংল্যান্ডে পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ভারত, পারস্য, চিনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিকে পার্লামেন্ট তিনবার আইন এনে নিষিদ্ধ করে দেয়। সেটা ব্রিটিশ শিল্পপতিদের চাপেই, নাহলে তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছিলো না। এটা গেলো বাণিজ্যিক কথা। সমাজ-সংস্কৃতির দিকে যে মসলিন একদা শ্রেষ্ঠ বসনভূষণ বলে গণ্য হতো, আভিজাত্যের প্রতীক ছিলো, ঊনিশ শতকের একটু মাঝামাঝি থেকে সেটা 'অশ্লীল ও বিলাসী পোশাক' বলে গণ্য হতে থাকে। এটা নাকি ' seductive ' ধরণের যা পরা উচিত নয়। এটা ভিক্টোরীয় সভ্য ধারণার ফসল।
-
 এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:৪১542563
এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:৪১542563 - আমি তো ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে ১৭৭০-ই ধরেছি। তার অব্যবহিত পরেই তো ১৭৭৬।এই মহিলারা কাজ হারাচ্ছেন কেন? কারণ ১৭৮২ সালে, ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাপাই ক্যালিকো আমদানি করা বন্ধ হয়। যে ভারতীয় মসলিন এতদিন সারা বিশ্বের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং যার চাহিদা ছিল আকাশছোঁয়া, ১৭৮৩-তে ম্যাঞ্চেস্টারে মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন শুরু হওয়ার পরে, ভারতবর্ষ থেকে মসলনির রফতানির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে এই সময় থেকে শুধু মসলিন নয়, ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সামগ্রিক ক্ষেত্রেই অবক্ষয় শুরু হয়। ১৭৮৭-তে ইংল্যান্ডে কেবল ঢাকাই মসলিন রফতানির পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। অথচ ১৭৯৯ সালে ঢাকা থেকে ইউরোপে সমস্ত বস্ত্র রফতানির পরিমাণ কমে ১২.৫ লক্ষ টাকা হয়। ১৮১৩-তে তার পরিমাণ আরও কমে মাত্র ৩.৫ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায় এবং ১৮১৭-তে মোট রফতানির পরিমাণ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে। ফলে অন্ততপক্ষে ২৫ লাখ মহিলা সুতো কাটুনি সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যান।ব্রিটিশরা চাড্ডিদের ধম্মোবাপ। সেই ধম্মোবাপদের নিন্দে শুনলে তাদের 'কৃতজ্ঞ মুৎসুদ্দিরা' কিছুতেই আর নিজেদের চেপেচুপে রাখতে পারে না।
-
Manali Moulik | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:৩৫542562
- @এলেবেলে তথ্যগুলি অনেকাংশে সঠিক। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় 1770 খ্রিষ্টাব্দে, বঙ্গাব্দ ১১৭৬। তাই এটা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে পরিচিত। যেমন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষটা বঙ্গাব্দের হিসাবে পরিচিত।
-
 এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:২৯542561
এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:২৯542561 - এসব আলবালচোদ্দচালের জন্য এই সাইটে আসার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। এলেবেলে আর ইমানুল নামদুটো দেখলেই এরা নাদবার জন্য রেডি হয়ে থাকে। হচ্ছে কথা ১৭৯০ পর্যন্ত, চলে আসছে রানি রাসমণি। হচ্ছে কথা বিধবা মহিলা জমিদারদের নিয়ে, সেখানে চলে আসছে নিজস্ব জমিদারির কথা।মহিলাদের কাজের কথা এসেছে না? তো রইল তার একটা হিসাব। ১৭৭৬ সালে অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ৮০ হাজার মহিলার কাটা সুতোয় ২৫ হাজার তাঁত চলত। উৎপন্ন হত ১৮ লাখ কাপড়।
 দীপ | 2402:3a80:1cd4:a752:578:5634:1232:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:১৮542560
দীপ | 2402:3a80:1cd4:a752:578:5634:1232:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:১৮542560- পেন্নাম ঠাকুরমশাই! এতোদিন কোথায় ছিলেন?বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ করছিলেন বুঝি?এখন তো শ্রাদ্ধের সুযোগ আরো বেড়ে গেছে!
 দীপ | 2402:3a80:1cd4:a752:578:5634:1232:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:১৫542559
দীপ | 2402:3a80:1cd4:a752:578:5634:1232:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১২:১৫542559- শতাংশের হিসেবে কতো মহিলা কাজ করতেন? ঈশ্বরী পাটনী মহিলা? ঈশ্বরীপ্রসাদ মহিলা? অন্নদাশঙ্কর, দুর্গাপ্রসাদ মহিলা?তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলায় মহিলা জমিদারের সংখ্যা কতো?রাণী রাসমণি তাঁর স্বামীর জমিদারি চালাতেন, তাঁর নিজস্ব জমিদারি ছিলোনা! এই জমিদারি তাঁর নিজস্ব কোনো কৃতিত্বে প্রাপ্ত নয়!
-
 এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১১:৪৯542558
এলেবেলে | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১১:৪৯542558 - r2h | 134.238.***.*** | ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ২৩:২৭এইটা পড়ে আরও মনে হল। মোগল আমলে পাবলিক ট্রানজাকশনের ভার মেয়েদের হাতে ছিল, ব্রিটিশ শাসনে দেখা গেল আগে নাকি অন্ধকারে ময় ছিল, কী আশ্চর্য।সোমনাথ আইন ই আকবরী থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে আকবরের সময় বাংলার মেয়েরা দরবারে খাজনা দিতে আসতেন, যদিও তদানীন্তন ইংল্যান্ডে মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার কারণে অনুবাদক জেরেট এই ঘটনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি। সেটা তাঁর সমস্যা, বাংলার বা বাংলার মহিলাদের নয়।কিন্তু হুতো কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে 'ব্রিটিশ শাসনে দেখা গেল আগে নাকি অন্ধকারে ময় ছিল'? কোম্পানির দেওয়ানি লাভ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামান্য আগে পর্যন্ত (১৭৯০) বাংলার যে তিনজন জমিদার কোম্পানিকে সর্বোচ্চ খাজনা দিতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহিলা ও বিধবা। রানি বিষ্ণুকুমারী দিতেন বছরে ৩৫ লাখ টাকা, রানি ভবানীর বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ ছিল ২৬ লাখ টাকা এবং দিনাজপুরের রানি বছরে ১৫ লাখ টাকা খাজনা দিতেন।বাংলার এই মহিলা জমিদাররা যে রীতিমতো দাপটের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতেন, তার উদাহরণ হলেন মহিষাদলের রানি জানকী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহিষাদলে লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক নথিতে রানি জানকীর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাত্র এক বছরে, তিনি লবণ সরবরাহের জন্য কমপক্ষে পাঁচটি ভিন্ন ঠিকাদারের সঙ্গে স্বাক্ষর করেন।শুধু তাই নয়, এই মহিলারা নানা ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণও করতেন। এ প্রসঙ্গে সবার আগে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর নাম মনে আসার কথা যিনি ছিলেন তুলনামূলকভাবে ছোট জমিদারি মন্থনার (বর্তমানে রংপুরে অবস্থিত) দাপুটে জমিদার এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ তথা রংপুরের প্রজা বিদ্রোহের নেত্রী।কাজে কাজেই বাংলার বিধবা নারীরা পুরুষদের 'দয়া'র পাত্রী ছিলেন না কিংবা তাঁদের 'হা অবলা নারী' হিসাবে অভিহিত করারও যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে পাশার দান উল্টে যায়, যদিও সেটা হয়েছিল ব্রিটিশদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ মদতের ফলে। তার আগে যে বিখ্যাত ঈশ্বরী পাটনির মুখোমুখি হই আমরা, তিনি ছিলেন একজন মহিলা।
 অরিন | 119.224.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১১:০৩542557
অরিন | 119.224.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১১:০৩542557- &/, "এই হিপোপটেমাস রান্নার বইটা কি অনেক পুরোনো ?"২০০৬ সালে প্রকাশিত, তবে ও বই ঠিক রান্নার বই নয় মনে হয়।
 &/ | 107.77.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১০:২৬542556
&/ | 107.77.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ১০:২৬542556- জলহস্তীর রোস্টের ব্যাপারটা সিনেমাতে .... এই হিপোপটেমাস রান্নার বইটা কি অনেক পুরোনো ?
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৮:৫৩542555
- @ডিসি বাঃ! চমৎকার।
 dc | 2a09:bac3:3f41:a8c::10d:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৮:১৪542554
dc | 2a09:bac3:3f41:a8c::10d:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৮:১৪542554- অমিতাভদার পোস্টটা আগে দেখতে পাইনি। আমরা সবাই ভালো আছি। মেয়ে কলেজে পড়ছে, সেই ফাঁকে আমি আর বৌ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৮:০২542553
- &/ ৬:৩৭
হ্যাঁআলোচনা হয়েছিল এইটুকু মনে পড়ে আর কিছু মনে পড়ে না। আবার এইরকম একটা কিছু মনে পড়ে যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে গরীব এবং বড়লোকের আলাদা আলাদা খাদ্যের গল্প/বিবরণও ছিল।
 রান্নার বই | 108.16.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:৪৯542552
রান্নার বই | 108.16.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:৪৯542552- রান্নার বইয়ের কথাই যখন হচ্ছে আমিই বা বাদ যাই কেন, মান্ধাতা যখন হাপ প্যান্টালুন পরতেন সে আমলে ঘাঁটাঘাঁটি করা, পাতা উল্টে পড়া গোটা দুই নাম দিয়েই যাই - Philosopher in the Kitchen আর How to cook a hippopotamus!
 kk | 2607:fb91:4c21:664d:e4c0:70a0:d163:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:০০542551
kk | 2607:fb91:4c21:664d:e4c0:70a0:d163:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৭:০০542551- মডার্নিস্ট কুইজিন, স্যরি।
 kk | 2607:fb91:4c21:664d:e4c0:70a0:d163:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৬:৫৫542550
kk | 2607:fb91:4c21:664d:e4c0:70a0:d163:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৬:৫৫542550- ওরেব্বাস, ঐ 'মলিকিউলার গ্যাস্ট্রোনমি' দুর্দান্ত বই! আমি 'মডার্ন কুইজিন সিরিজ' আর 'ফুড ল্যাব' পড়িনি। অবশ্যই পড়বো। সাজেশনের জন্য অরিনবাবুকে ধন্যবাদ। এই ধরণের বইয়ের কথায় মনে পড়লো আমরা বাইবেলের মত পড়তাম অগুস্ত এস্কোফিয়ের 'ল্য গীদ কুলিনেয়ার'। ইংরেজি অনুবাদ অবশ্য। মূল বইটা পড়ার মত ফ্রেঞ্চ বিদ্যা আমার নেই। টেক্স্টবুকের কথা বলতে গেলে আমার আরো দুটো প্রিয় বই এসে পড়বে -- ফ্রেঞ্চ কুলিনারি ইনস্টিট্যুটের 'দ্য ফান্ডামেন্টাল টেকনিকস অভ ক্লাসিক ব্রেড বেকিং' আর ইন্টারন্যাশনাল কুলিনারি ইনস্টিট্যুটের 'দ্য ফান্ডামেন্টাল টেকনিকস অভ ইতালিয়ান কুকিং'। তবে টেক্স্টবুক পড়তে সবার অত উৎসাহ থাকবে কিনা জানিনা।
 &/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৬:৩৭542549
&/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৬:৩৭542549- বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাড়ির রান্নাবান্না নিয়ে একবার কথা হচ্ছিল অন্যত্র, একলহমাদার মনে থাকতে পারে হয়ত। এই ধরণের কোনো বই আছে কি? মানে পুরাতন বাংলা সাহিত্যে রান্নাবান্না ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (মানে খাবারে আলু টম্যাটো কাঁচালংকা এইসব কেন নেই, কেন থাকা উচিত নয়, এইসব নিয়ে)
 অরিন | 132.18.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৫:২৬542548
অরিন | 132.18.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০৫:২৬542548- দ, "অরিনের টইটা বাংলা খাবার ও বইয়ের তাই ওখানে না দিয়ে এখানে আমার পছন্দের কটা বই লিখে যাই "অসংখ্য ধন্যবাদ, দ, বিশেষ করে পাক রাজেশ্বরের রেফারেন্সটি রাখার জন্য। আপনার লেখাটা এখনো পড়া হয়ে ওঠেনি, পরে সময় করে পড়তে হবে।দ, রমিত এবং kk masala ল্যাব এর কথা লিখেছেন, আমি কিছুটা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইংরিজি বইগুলো এই তালিকার আওতা থেকে বাইরে রাখতে চেয়েছি কারণ বাংলায় কি লেখা হয়েছে এই নিয়ে আগ্রহ।বাংলা রান্নার বেশ কিছু ভালো ইংরিজি বই আছে, যেমন জয়া চালিহা মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের "calcutta cookbook" অনবদ্য এই জন্যে যে প্রচুর গল্প আর রেসিপি, কলকাতার সাবেক রান্না নিয়ে, তারপর ইতিহাস নিয়ে। একইরকম ভাবে আসমা খানের monsoon ও সুন্দর লেখা গল্প আর রেসিপির ভারী সুন্দর সংমিশ্রণ, বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন খাবার। এগুলো নিয়ে পরে কোন সময় আলোচনা করা যেতে পারে নিশ্চয়ই।Masala Lab নিয়ে বলতে গেলে যে বইটির কথা সবচেয়ে প্রথমে মনে হয় সেটি Harold McGee র লেখা প্রায় হাজার পাতার On Food and Cooking সুপ্রাচীন বই, তবে এখনো চমৎকার পাঠযোগ্য, আরেকটি সিরিজ উৎসাহীরা পড়ে দেখতে পারেন Nathan Myrhvold এর ছয় খণ্ডে প্রকাশিত Modernist Cuisine। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখ্য বই, যাঁরা উৎসাহী পড়ে দেখতে পারেন হার্ভে টিস্ এর লেখা Molecular Gastronomy, এবং অবশ্যই কেনজি লোপেজ অল্ট এর Food Lab।পরে এ নিয়ে আরেকটু লেখার ইচ্ছে রইল।
 &/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:২৩542547
&/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:২৩542547- এতসব উদার পাশ্চাত্য পিয়ানো সুটার ইত্যাদি চর্চা করে টরে শেষে সম্বন্ধ করে মেয়েকে দোজবরে বিয়ে দিয়ে বেড়াল পার করে দেওয়া, সেই ব্যাপারও হত।
 &/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:২০542546
&/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:২০542546- তরুণীদের পিয়ানো বাজিয়ে গান করা, সন্ধেবেলা তাদের জন্য অনেক পাণিপ্রার্থী তরুণের ভীড় বৈঠকখানায়, ফুল চকোলেট ইত্যাদি গিফ্ট আনা, তরুণীদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে পার্টি থ্রো করা---এই ধরণের পাশ্চাত্য 'ভদ্রমহিলাসুলভ' আচরণ সাধারণ আম-বাঙালির ঘরে ছিল না বলেই মনে হয়, শহরবাসী অভিজাত কন্যারাই এইসবের দাবী করতে পারতেন।
 &/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:১১542545
&/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:১১542545- ব্রাহ্ম ( কিছু কিছু হিন্দু ও অন্যধর্মেরও) মহিলারা যে ভিক্টোরীয় 'ভদ্রমহিলাসুলভ' হবার ধারণা লাভ করেন ও সেইমত আচরণ করেন, সেটা শহরকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র একটি বৃত্তের মধ্যেই ছিল বলে মনে হয়।
 &/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:০৭542544
&/ | 151.14.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০২:০৭542544- না না, 'সহবৎ' বা 'ভদ্রমহিলাসুলভ' আচরণ পশ্চিমী শিক্ষার অনেক আগে থেকেই বঙ্গদেশে ছিল। সারদামণি বা রাসমণিরা এবং আরও বহু বহু নারী যাঁরা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু দিব্যি ভদ্রমহিলাসুলভ আচরণ করতেন।
-
Manali Moulik | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০১:২৭542543
- &/ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে এদেশে আসে ভিক্টোরীয় মানসিকতার সভ্যতার ধারা। যার দ্বারা প্রথমপর্বে নারীরা (অধিকাংশই অভিজাত) শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 'সহবৎ' বা 'ভদ্রমহিলাসুলভ' আচরণের ধারাটি লাভ করেন। পূর্বতন যুগে হয়তো অবস্থা ভালো ছিলো না, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার বলা যায় না। এইপর্বেও জমিদার বা উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারাই শাসন পরিচালনা বা অন্যান্য কারণে উঠে এসেছেন আলোচনায়....বৃহত্তর সাব-অল্টার্নের কন্ঠস্বর কখনই শোনা যায় না। স্পিভাকের যুক্তিই গ্রহণযোগ্য। জানি না এসব কথা বলা উচিত কিনা, তবে এই 'ভদ্রমহিলা' ধারণাটি খুব সুখকর হয়নি বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে। সম্প্রতি বর্ষীয়সী অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পীর বক্তব্যও এই ধারার। তবে সেই আমলে অন্য বিকল্পগুলির তুলনায় এটি অগ্রসর ছিলো বলা যায়।
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০১:১৪542542
- &/ | ২৩:১৪শুভ বিজয়া &/।
তোমার কাছাকাছিই মানে বৃহত্তর ন্যাশভিলে, নানান কিছু নিয়ে ঘেঁটে ছিলাম। এবার একটু দম পাওয়া গেছে আশা করি।
-
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০১:০৭542541
- dc | ২৩:০৭
ভালো আছি ডিসি। আর এখন তোমার দেখা পেয়ে দিল একদম গার্ডেন গার্ডেন। তোমরা সপরিবার সবাই সুস্থ আছ ত?
-
রমিত চট্টোপাধ্যায় | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০০:৩৯542540
- মাসালা ল্যাবের ভদ্রলোক তো নিয়মিত ইউটিউবে ভিডিও দেন। খুব ইনফোরমেটিভ আর সাথে বেশ কিছু মিথ কেও ভাঙেন। বেশ ভাল লাগে।এই সূত্রেই আরেক ইউটিউব চ্যানেল রেকো করে যাই, হাউ টু কুক দ্যাট। এক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রমহিলা খাবার দাবার সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুয়ো ভাইরাল ভিডিও বাস্ট করেন আর সমস্ত নিজে টেস্ট করে দেখান। এটাও বেশ ভাল।
 &/ | 107.77.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০০:২২542539
&/ | 107.77.***.*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০০:২২542539- পাবলিক ট্রানজ্যাকশনের ভার মহিলাদের হাতে ছিল বঙ্গদেশে মোগল আমলে --- এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে , প্রশ্ন ও আছে
 kk | 2607:fb91:4c21:664d:18bd:8b51:8b5f:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০০:০৬542538
kk | 2607:fb91:4c21:664d:18bd:8b51:8b5f:***:*** | ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ০০:০৬542538- দমুদি বলার পরে আমি 'মাসালা ল্যাব' পড়েছিলাম। খুবই ভালো লেগেছে। আরেকটা বই খুব ভালো লেগেছিলো, এই বিষয় নিয়ে যখন ইংরেজী বইয়ের কথা এলোই তখন বলি, অ্যান্থনি বোর্ডেনের লেখা 'দ্য কিচেন কনফিডেনশিয়াল'।
 r2h | 134.238.***.*** | ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ২৩:২৭542537
r2h | 134.238.***.*** | ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ২৩:২৭542537- &/ | ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ০৩:০৪
- ...ভদ্রঘরের মেয়েরা মঞ্চে নাচ গান ইত্যাদি করবে, সেটা তখনকার সমাজে একেবারেই পছন্দের ব্যাপার ছিল না। মাত্র শ দেড়েক বছর আগের কথা, তখনও 'সুবর্ণলতা'দের ন-দশ বছর বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আটকা পড়ে যেতে হচ্ছে নিয়মিত ভাবে। আট-দশটি করে সন্তান উত্পাদন করে অকালে পরলোকে যেতে হচ্ছে তাদের অনেককেই।
এইটা পড়ে ভাবছিলাম, মানালির মঙ্গলকাব্য আর মোগল পড়ে আবার মনে পড়লো।
এই ভদ্রঘর শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ আরকি। বর্ণহিন্দু, বেশি করে ব্রাহ্মণপরিবারের বাইরে বৈষম্য উল্লেখযোগ্য রকমের কম ছিল, এমনটা নানান জিনিসপত্র পড়ে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ঐ সাবল্টার্নের কন্ঠস্বর শোনা যায় কিনা ঐ প্রশ্নে এই ভদ্রঘর ব্যাপারটা সমগ্র বাংলার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েছে।
পূববাংলাতেও জমিদারি পরিচালনায় মহিলাদের বড় রকম ভূমিকা থাকতো বলে মনে হয়েছে নানান জিনিসে।
ব্রাহ্মরা একটু নতুন রকম করছিল, যদিও সেও জাতপাত কন্টকিত বর্ণহিন্দু ডমিনেটেড, কিন্তু বেলুড় দক্ষিনেশ্বরকেন্দ্রিক জিনিসপত্র তাতে আরেক ঘটি জল (এই রে, সেই যাঁর নাম করতে নেই তিনি এলেন বলে)।
তো তথাকথিত অগ্রনী সমাজ নিজেদের সহ সবাইকে পশ্চাতে টেনে নিয়ে গেছে, এমন মনে হয়।
- সোমনাথ | ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ২২:৪৯
- ...উদাহরণ দিচ্ছেন যে বাংলায় পাবলিক ট্রাঞ্জাকশনের ভার পরিবারের মহিলাদের উপর ছিল, তিনি তা জারি রাখেন।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
(লিখছেন... :/, lcm)
(লিখছেন... Ranjan Basu, Tania )
(লিখছেন... দীপ, দীপ, ধোরবা)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত