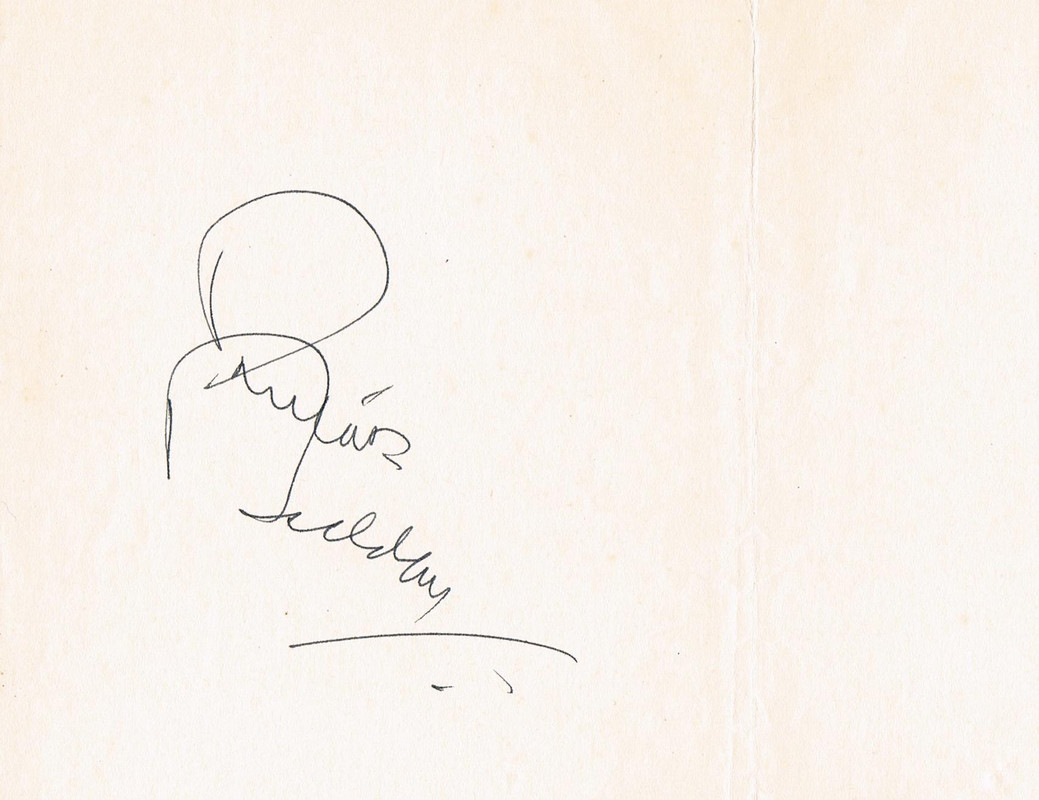- টইপত্তর স্মৃতিচারণ আত্মজৈবনিক

-
Deleted Scenes — বাতিল দৃশ্যাবলী
সে
স্মৃতিচারণ | আত্মজৈবনিক | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৪০৯৩ বার পঠিত - স্বাতী, অরণ্য, দেবাশীষ, পার্থ, মহুয়া, নার্গিস, সুদেষ্ণা এবং আরও বেশ কয়েকজনের ( যাদের নাম এখানে নিলাম না প্লীজ অভিমান করো না) অনুরোধে শুরু করছি এই নতুন থ্রেড। হয়তো খুব গুছোনো লেখা হয়ে উঠবে না, তবে স্মৃতি থেকে এই আবছা ছবিগুলো মুছে যাবার আগেই ঝেড়ে মুছে এখানে গুছিয়ে রেখে দেব।কমেন্ট সেকশন থেকেই শুরু হবে মূল লেখাটা।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 সে | 2001:1711:fa42:f421:21bc:bc8b:f27a:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০২:৪১735796
সে | 2001:1711:fa42:f421:21bc:bc8b:f27a:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০২:৪১735796- রিফিউজি
ছোটবেলা ভাবতাম বড় হয়ে গেলে অনেক স্বাধীনতা পাব, হাতে টাকা পয়সা থাকবে যেমন খুশি খরচ করব ক্যাডবেরি, তেঁতুলের আচার আর চানাচুর কিনে। যৌবনে ভাবতাম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়স হয়ে গেলে জীবনটা ম্যাদামারা হয়ে যাবে, তখন মরে গেলেও কোন আফশোস নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলবার পর জীবন অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে।
একটা ব্যাপার হয়ে গেল ইদানীং। এর জন্য অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি টেলিকমিউনিকেশন এবং ফেসবুককে আগাম ধন্যবাদ দিচ্ছি।
প্রায় বাইশ বছর পর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা হল। মেসেনজারে। লাস্ট যদ্দূর মনে পড়ছে দেখেছি তাকে ১৯৯৫ এর মার্চ কি এপ্রিলে। তাশখন্দে সেটাই আমার পড়াশোনা করবার এবং থাকবার শেষ বছর। সে অবশ্য তখন আর পড়াশোনা করত না। অ্যাসাইলাম খুঁজছিল। ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত করত, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত ইয়োরোপের কোন একটা দেশে যদি তার অ্যাসাইলাম মঞ্জুর হয়। আফগানিস্তানে তখন বসন্ত...,থুড়ি তালিবান এসে গেছে। ওকে আমি তখন প্রায় ন দশ বছর ধরে চিনি। ওর নাম জামিলা — জামিলা বাহাদুর। কাবুলের মেয়ে। জামিলা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল সম্ভবত ১৯৯২ নাগাদ, কিন্তু পড়াশোনার শেষে কাবুলে ফিরে যেতে চায় নি। ১৯৮৯ এ আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনারা ফেরত চলে এলেও মুজাহিদিনদের সমস্যা তখনো শেষ হয় নি। গৃহযুদ্ধই তো হচ্ছিল ওদেশে মনে হয়। সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় জেনে সোভিয়েত সেনাদের ফিরিয়ে আনা হয়, এবং যে সব আফগান ছাত্রছাত্রীরা তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকত, তাদের ইমিউনিটি ক্রমশ আর থাকে না। তাদের "যতদিন খুশি" সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকতে দিতে চায় না আর প্রশাসন। তারপরে তো ১৯৯১ এর ভাঙন এবং জোর করে করে আফগানদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। সবই নিজের চোখ দেখা, সেসব লম্বা লম্বা বোরিং গল্প। আমরা নানান দেশের ছাত্রছাত্রীরা সেসময় যে যার নিজের তালে ছিলাম। এমনিতে একই হস্টেলে থাকছি, একই টয়লেট বাথরুম শেয়ার করছি, একই রান্নাঘরে পাশাপাশি উনুনে আমরা মিলেমিশে রান্না করছি, কিন্তু প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্ল্যান ভিন্ন — কারন প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দেশের পাসপোর্ট, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কালচারাল পোলিটিক্যাল পটভূমিকার দেশের তরুণ নাগরিক সব। আসলে, এখন মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন ছিল। সবাই চেয়েছিলাম ভাল ভাবে মাথা উঁচু করে জীবনের পরবর্তী টাইম স্লটটা বাঁচতে। আফগানরা স্বেচ্ছায় তাই ফিরে যেতে চায় নি আফগানিস্তানে। আমরা, অন্যরা ওদের এই গোঁয়ার্তুমিটা তখন বুঝিনি, বুঝতে চাই নি। আমাদের মধ্যে অ্যাপাথি কাজ করত। অদ্ভুত ধরণের হিংস্র ছিলাম আমরা।হিংস্র তো ছিলামই, হিংসুটেও ছিলাম আমরা। রিফিউজিদের পরোক্ষে হিংসে করতাম, মনের গভীরে কোথায় যেন একটা এরকম যুক্তি কাজ করত, — দেখেছ, পড়াশোনায় অগা, বছর বছর ফেল করা স্টুডেন্টগুলো চমৎকার চ্যানেল বের করে ফেলেছে ইয়োরোপের ঝকঝকে দেশগুলোয় পাকাপাকি বসবাস করবার, অথচ আমরা যারা কিনা পোলিটিক্যালি স্টেবল দেশের নাগরিক, আমাদের জন্য কোন সহজ রাস্তা নেই, আমাদের হাড়ভাঙা খাটাখাটনি করে পড়াশুনো করতে হবে, ভাল রেজাল্ট চাই, একগাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা চাই, কেবল কম্পিটিশান আর কম্পিটিশান। অথচ দেখ, রিফিউজিদের কী মজা, — দেশে ঝামেলা লেগেছে সেই সুবাদে ওদের ভাগ্য খুলে গিয়েছে। কি সুন্দর দুমদাম হল্যান্ড, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কে চলে যাচ্ছে। এ অনেকটা মহাভারতের শেষের দিকটার মত। অনেক খেটে খুটে সারাটা জীবন সত্যি কথা বলেও যুধিষ্ঠির পায়ে হেঁটে স্বর্গে গেছেন, পথে অল্প নরক দর্শনও হয়ে গেছে, স্বর্গে গিয়ে দেখেন তিনিই লাস্ট। বাকি সব পাপী তাপী লোকজন আগেই সেখানে উপস্থিত, নিজেকে চীটেড মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের। আমাদেরও সেরকম লাগত, কত কষ্ট করে খেটে খুটে পড়াশুনো করে চেষ্টা চরিত্র করে বিদেশে পাড়ি দিই, আর অ্যাসাইলাম সীকাররা জাস্ট এমনি এমনি ফরেন কান্ট্রিজে চলে যায়।
আমাদের রিফিউজি বন্ধুরা রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস কিনত, নতুন দেশে গিয়ে বসবাস করবার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে। অনেক সময় আফগানিস্তান থেকে ওদের পরিবারের অন্য সদস্যরাও এসে উপস্থিত হত হস্টেলে, ওদের ঘরেই গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকত তারা। আপাতভাবে মনে হবে তারা বুঝি গোপনে অজ্ঞাতবাসে রয়েছে। আসলে এ সবই ছিল ওপেন সিক্রেট।
জামিলার দিদি জামাইবাবুকে দেখেছি হস্টেলে ক্ষণিকের জন্য। ওরা এমনিতে খুবই চুপচাপ, প্রায় অশরীরির মত থাকত — ঐ হঠাৎ হয়ত কারো সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল বাথরুম থেকে বেরোনোর সময়, কিন্তু কথা বলবার জন্য কোন কমন ভাষা নেই, তারা বলত দারি বা পুশতু, আমাদের সাধারন ভাষা ছিল রাশিয়ান।
এমনি করে করে স্বল্পমেয়াদি অতিথিরা কখন আসত, কখন চলে যেত, সেরকম টের পাওয়া যেত না।
আমার মেয়ে যেদিন জন্মায়, তার আগের দিন সন্ধেবেলায় আমার প্রসববেদনা একটু একটু করে শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার উল্লাসে সেভাবে গমগম করছে না তখন নতলা হস্টেলবাড়িটা, কারন তখন গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছে। প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই দেশেবিদেশে বেড়াতে গেছে, পড়ে আছে ছায়ার মত অশরীরী কজন মাত্র, কিছু রিফিউজি এবং একজন আসন্নপ্রসবা।
...ভাবলাম একবার দেখে আসি কে কে আছে প্রতিবেশীদের মধ্যে। আসলে আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে এরকম অবস্থায় লোকজন সঙ্গে নিতে লাগে, বিবাহ বা মৃত্যুতে যেমন লোক জড়ো করে জানিয়ে দেবার রীতি, তেমনি একজন মনুষ্যপ্রাণীর জন্ম হবে কিছু সময় পরে — একথা জানানো দরকার আশেপাশের মানুষজনকে।
আমরা তিনতলায় থাকতাম। আমার ঘর তিনশো পাঁচ নম্বর। কুড়িটা করে ঘর প্রত্যেক তলায়। করিডোরে বেরিয়ে দেখলাম, সব কেমন নিঝুম নিশ্চুপ। খুব দূরে কোথাও কোন এক ঘরে মিউজিক সিস্টেমে গান বাজছে, কিন্তু সে গানের সুর ও কথা বড্ড আবছা। আমার শিরদাঁড়ার নীচের দিকে ব্যাথা হচ্ছে, পেটেও কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ব্যাথা এসে এসে ফিরে যাচ্ছে। একটু হেঁটে দেখলাম তিনশো তের নম্বর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, দরজায় নক্ করলাম — কোন আওয়াজ নেই, পিন ড্রপ সায়লেন্স। লিফটের বোতাম টিপলাম, পাশাপাশি দুটো লিফট, দুটোই বন্ধ। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখি সেই তিনশো তের থেকে বেরিয়ে এসেছে জামিলা, আমাকে জিগ্যেস করল — সব ভাল তো?
দেখলাম সে সেজেগুজে রেডি হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। সূর্য জাস্ট ডুবেছে যদিও রাত প্রায় নটা বাজতে চল্ল। ওর সামাজিক কুশল বিনময়মূলক প্রশ্নের উত্তরে বললাম, সব ভাল, তুই কোথাও যাচ্ছিস এখন?
ও জানাল যে কারা যেন আসছে দেশ থেকে, তাদের রিসিভ করতে ও যাচ্ছে এয়ারপোর্টে। ওকে আর আটকালাম না। নিজেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম। আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে কাগজপত্র ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে চুলটুল আঁচড়ে রেডি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম অ্যাম্বুলেন্সের।
সেই সপ্তাহেই শনিবারে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছি হস্টেলে, একা নই — সঙ্গে আছে নতুন একজন মনুষ্যপ্রাণী। নতুন শিশুকে নিয়ে আমি একজন অনভিজ্ঞ মা অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি তখন প্রতিদিন।হাসপাতাল থেকে ফিরে নবজাতকের গায়ে মোড়া কাপড় খুলে ফেলে তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে নিলাম, তার দুহাতে তখনো কাপড়ের দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে টিকিট, তাতে কীসব সংখ্যা অক্ষর লেখা। সেসব সন্তর্পনে কেটে ফেলে দিলাম। তারপর মনে হল, বাচ্চাটাকে একটু চান করিয়ে পরিস্কার করে ফেলি। যেই ভাবা, সেই কাজ। নীল রঙের প্লাস্টিকের নতুন বাথটাব কেনাই ছিল, যেই সেটায় জল ভরে আনতে বেরিয়েছি অমনি সরাসরি জামিলার মুখোমুখি। চারদিনের বাচ্চাকে চান করাবার ডিসিশান নিয়েছি শুনে সে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল। জল ভরা বাথটাব ঘরে এনে বাচ্চাকে চান করাতে যাচ্ছি, জামিলা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে, সঙ্গে ওর মা। জামিলার মা নিজে এগিয়ে এসে অভিজ্ঞ হাতে বাচ্চা কোলে নিয়ে খুব অল্প জল দিয়ে চানের মত একটা কিছু করিয়ে দিলেন।
বুঝলাম, সেদিন যাকে রিসিভ করতে জামিলা এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল, তারই হাতে আমার মেয়ে প্রথম (মতান্তরে দ্বিতীয়, প্রথম চান টা জন্মের পরপরই হয় যেহেতু) চান করল। এগুলো খুবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তারপরে অনেক সময় বয়ে গিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে, আমরা ইন্জিনিয়ারিং পাশ করেছি, গবেষণার লাইনে ঢুকেছি কেউ কেউ, আবার কেউ কেউ ব্যবসা বানিজ্যের পথে এগিয়েছি। আমাদের হস্টেলের আফগান ছেলেমেয়েগুলো টায়েটুয়ে পাশ করে কেউ বিতাড়িত হয়েছে, কেউ বাক্স প্যাঁটরা বেঁধে সদর্পে বিদায় নিয়ে ইউরোপগামী ট্রেনে চড়েছে।
আমার দুটো ঘর পাশে থাকত ক্লাসমেট শাকিবা দরবেশি, তার রুমমেট ছিল রাইমা — আমাদের চেয়ে বছর তিনেকের সিনিয়র। রাইমা কিছুতেই পাশ করে নতুন ক্লাসে উঠতে চাইত না। দুটো বছর স্রেফ ফেল করে কাটিয়ে দিল, যাতে আরো বেশিদিন থেকে যাওয়া যায়। তারপর ওকে প্রায় জোর করেই পাশ করিয়ে দেওয়া হল ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। রাইমাকে এবার ফিরে যেতে হবে, কাবুলগামী ফ্লাইটের ওয়ান ওয়ে টিকিট ওকে বারবার সংগ্রহ করতে বলছে ডীনের অফিস থেকে। কিন্তু রাইমা সে পথ মাড়ায় না। চুপচাপ লুকিয়ে থাকে নিজের ঘরে বলতে গেলে গা ঢাকা দিয়ে। দিনের বেলা তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, সন্ধে হলে সে খুব যত্ন করে পোলাও রান্না করে, তারপর ওরা পরিপাটি করে গুছিয়ে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে খেতে বসে। নান, পোলাও, স্যালাদ, চা, এইসব অনেক সময় নিয়ে গল্প করতে করতে তারিয়ে তারিয়ে খায়। কোন তাড়া নেই জীবনে।
আমরা, যারা স্টেবল দেশের মানুষ, যাদের দেশে ফিরতে ভয় নেই— সেই আমরা ওদের এই হেলদোলহীন জীবনটা দেখি, ভাবি আর নানারকম মন্তব্য করি। ইশ্, সময়ের কী অপচয়। বয়স বেড়ে যাচ্ছে অথচ এরা চাকরি বাকরি করছে না। যেন সন্ধেবেলা পরিপাটি করে পোলাও খাবে, হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প আড্ডা করাটাই ওদের জীবনের উদ্দেশ্য।
সেই রাইমাকে একদিন সন্ধেয় রান্নাঘরে আর দেখতে পেলাম না। প্রথমে ওকে দেখতে না পাওয়াটা খেয়াল করিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে রান্নাঘরে গিয়ে মনে হল রাইমা কদিন ধরে পোলাও রাঁধছে না। কী হল? শাকিবাকে জিগ্যেস করতে জানা গেল যে সপ্তাহখানেক আগে দুপুরবেলা রাইমাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তারা তক্কে তক্কেই ছিল। কী কারনে বুঝি সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল সম্ভবত বাসন মাজতে। সেই সময় পুলিশ ওকে নিয়ে গেছে, পাঁচ মিনিটও সময় দেয় নি জামাটা বদলে নেবার জন্য।
রাইমার সঙ্গে কখনো সেরকম গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল না। তবে ও যেদিন ওর ডিপ্লোমা ডিফেন্ড করেছিল, সেদিন নিয়ম মত সবার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে ওর গায়ে জল ঢেলেছি। এরকমই প্রথা ছিল আমাদের —কেউ ডিফেন্ড করে ফিরে এলে তাকে ভিজিয়ে চুপচুপ করে দেওয়া। দূর থেকে সবাই লক্ষ্য রাখতাম খালি হাতে সে ফিরে আসছে, যাবার সময় হাতে থাকত ডিপ্লোমার কাগজপত্র, ফিরবার সময় খালি হাত মানেই সে উতরে গিয়েছে, সে আর ছাত্র নয়, তার স্টেটাস পাল্টে গেল, সে এখন এক সদ্য সদ্য পাশ করা ইন্জিনিয়ার, অতএব ঢালো জল।
রাইমা যে খুব একটা খুশি ছিল সেদিন, তা নয়। পাশ করে যাওয়ার দুটো দিক তার কাছে। প্রথমত তার এখন নিজস্ব একটা পেশা, একটা ডিগ্রি হল, দ্বিতীয়ত তাকে চলে যেতে হবে। চলে যাবার পথ অনেক। নিজের দেশে ফেরা যায়, যদিও সেখানে কোন চাকরি কোন জীবিকা নেই, সমস্ত ইন্ফ্রাস্ট্রাকচারই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে। অন্য দেশেও যাওয়া যায় — রিফিউজি স্টেটাস নিয়ে। কিন্তু সেসব দেশেও যাবার জন্য লম্বা লাইন, অনেক নিয়ম কানুন। সংসার সন্তান থাকলে তাতে প্রায়োরিটি বাড়ে, কিন্তু রাইমার কোন নিজস্ব সংসার তো নেই, বিয়ে করে নি, এমনকি একটা বয়ফ্রেন্ড পর্যন্ত নেই ওর।
সন্ধেবেলা রাইমার ঘরে যাই, তখনো পুরো সন্ধে হয় নি। আজ সেলিব্রেশনের সময়। কিন্তু ওর ঘরে তেমন কোন উৎসবের আয়োজন চোখে পড়ে না। নিয়মমত পোলাও বানানোর আয়োজন চলছে, এটাই ওদের নিয়মিত খাবার। শুধু আফগান নয়, উজবেকদের মধ্যেও পোলাও একটা নিয়মিত সাধারন টাইপের খাবার। আমরা ক্যান্টিনে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পোলাও কিনে খেতাম। তা রাইমা পোলাওয়ের জন্য গাজর ছাড়াচ্ছে, মাংস রয়েছে একপাশে, পেঁয়াজ রয়েছে। হঠাৎ কী হল, বলল, চল আজ ভোদকা খাব। আরো কজন মেয়ে ছিল সেখানে, সকলে হৈহৈ করে তাতে সায় দিল। আমরা কজন রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম মদের দোকানে। অনেকটা পথ। একটা মাঠ পেরিয়ে অলিগলি পেরিয়ে, কারো বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে শর্টকাট করে যেখানে নিকটতম মদের দোকান, সে জায়গাটার নাম কারা-কামিশ। আমাদের মনের মধ্যে খানিক সংশয়, দোকান খোলা পাব তো? কে মদ চাইবে? শত হলেও জায়গাটা মধ্য এশিয়া, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমান কাজ করে চলেছে এদেশে মেয়েরা, তবু অনেক সামাজিক বাধা আছে, যেগুলো চোখে দেখা যায় না, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় না, যে অসাম্য হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় রীতি। মদ ছেলেরা কিনবে, কি হয়ত বুড়িরা। কিন্তু চারপাঁচটা সদ্য তরুণী হাহাহিহি করতে করতে দোকানির কাছে মদ চাইবে, এটা কেমন যেন বেখাপ্পা বেমানান। অবিশ্যি, আমরা সেদিন যৌবনের তেজে আনন্দে বদ্ধপরিকর, দোকানে যদি না দেয়, যদি বলে ফুরিয়ে গিয়েছে, তবে অন্য প্ল্যান আছে। ঘুষ দেব দোকানিকে। তাতেও যদি না দেয় তবে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব হোটেল অলিম্পিয়া। হোটেলের নীচে রেস্টুরেন্টে চব্বিশ ঘন্টা ভোদকা পাওয়া যায়, সেখানে দেবেই, দাম বেশি নেবে, হয়ত ঘুষও নেবে। এত কিছু করতে পারছি আমরা, আর সামান্য একটু ঘুষ দিতে পারব না?
...অলিম্পিয়া অবধি যেতে হয় নি। প্রৌঢ় দোকানদার তো আসলে সরকারি কর্মচারি, দোকান তো সরকারের। সে বিনা বাক্যব্যয়ে তিন বোতল ভোদকা দিয়ে দিল, হাফ লিটার করে এক একটা বোতল। এর কমে একটা পার্টি হতে পারে না। বীরের মত তেজে আমিই নিঃসঙ্কোচে মদ চাইলাম দোকানির কাছে। দোকান থেকে বেরিয়ে আমাদের সে কী উল্লাস, কী হাসি।
সে হাসি ক্রমশ বাড়তে থাকে। কয়েক বোতল পেপসি জোগাড় হয়ে যায়। হস্টেলে ফিরে এসে আমরা চার পাঁচটা মেয়ে কারোর তোয়াক্কা না করে সেলিব্রেট করি রাইমার ইন্জিনিয়ার হওয়া। রাত ভোর হয়ে যায় খাওয়া পান গল্পে হাসিতে নাচে গানে।
সেই মেয়েটাকে কিনা পুলিশ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। পুলিশ নয়, পুলিশ নয়, মিলিৎসিয়া। পুলিশ ছিল না ওদেশে।যুদ্ধ যে শুধু তখন আফগানিস্তানেই চলছিল তা তো নয়। আরো অনেক দেশে যুদ্ধ চলছিল তখন নিবন্ত উনুনের মত ধিকধিক করা অল্প আঁচে। যেমন আলজিরিয়ার সঙ্গে মরক্কো, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলছে তো চলছেই, কখনো একটু জোরকদমে হয়, আবার ঝিমিয়ে যায়, ফের কখনো বাড়ে, এইরকম। ইরাকের সঙ্গে ইরাণেরও জোরসে যুদ্ধ হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে হয়েছে কিন্তু তা বলে ইরাকি ছাত্ররা (ও দেশ থেকে কোন ছাত্রী আসত না, অন্তত আমি তো জানি না, শুনিও নি) কক্ষনো অ্যাসাইলাম চায় নি। ওরা প্রত্যেকেই ছিল বেশ পয়সাওয়ালা, পয়সা ওড়াতেও জানত বটে। সেই সঙ্গে ছিল টাকার দেমাক। আমার সঙ্গেই তো দুজন ইরাকি পড়েছে, ফায়েজ এবং গাসান। পয়সা ওড়ানোয় ওরা এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায় দেখ। দামি দামি রেস্টুরেন্টে যেত ওরা নিয়মিত, রাশিয়ান মেয়েদের পেছনে পয়সা খরচ করত, দেদার মদ খেত, মোট কথা যেগুলো নিজেদের দেশে করা সহজ নয় সেসব। আবার কোন দিন দেখা যাবে ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরে মাথায় সাদা রুমালের ওপর তবলার বিড়ের মত কালো রঙের একটা বিড়ে লাগিয়ে, মানে অথেন্টিক আরব পোশাক পরে দল বেঁধে কোন একটা উৎসব অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য লাইফস্টাইলে আসলে আমরা সকলেই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম তখন, দেশ মধ্য এশিয়ায় হলে কী হবে, আমাদের তখন অনেক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাটাও একটা কারন ছিল হয়ত কারো কারো স্বদেশে ফিরে না যেতে চাইবার পেছনে। তবে যেটা বলছিলাম, ইরাণের কারোকে দেখিনি তাশকেন্তে, একবারই একটা ইরাণী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মস্কোয় (গ্রীষ্ম ১৯৮৯), পরে মনে হয়েছিল সে হয়ত কোনদিনও ফিরে যাবে না তেহরানে।
মরক্কো আলজিরিয়ার ছাত্রছাত্রীরা খুব ফ্রান্সে বেড়াতে যেত বটে কিন্তু তাদের মধ্যেও রিফিউজি হয়ে উঠবার কোন চাপ সে সময় দেখতে পাই নি।
আমাদের বিদেশীদের মধ্যে একটা খুব কমন টার্ম ছিল আফগানিস্তানকে তাচ্ছিল্য করে ষোলো নম্বর রিপাবলিক বলে উল্লেখ করবার, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব পনেরোটা রিপাবলিক ছিল এবং দেশময় ভরে গেছে আফগান নাগরিকে, তাই ওরকম নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে ক্রমশ আফগানিস্তানকে গ্রাস করে নেবে সোভিয়েতরা। কিন্তু আদতে তো তা ঘটল না। তাশকেন্ত এয়ারপোর্টে নিয়মিত এসে পৌঁছত বেশ কিছু করে কফিন। সেই কফিনের ভেতরে সোভিয়েত সেনাদের দেহ। আফগানিস্তান থেকে। অনেক দিন ধরে ধরে, অনেক বছর ধরে ধরে যখন একটা দেশে যুদ্ধ চলতে থাকে, তখন কেমন যেন একটা অভ্যাস হয়ে যায় যুদ্ধকে সঙ্গে করে জীবন অতিবাহিত করা। ওরই মধ্যে লোকে বিয়ে করে, সন্তান জন্মায়, কিছু থেমে থাকে না, কেউ অপেক্ষা করে না যে যুদ্ধটা শেষ হলে তবে বিয়ে করব, কি যুদ্ধ থামলে পরে তবে বাচ্চাকাচ্চা হবে। কেউ অপেক্ষা করে না। কেউ তো জানে না কত দিন, কত বছর লাগবে যুদ্ধ থামতে, ততদিন কে অপেক্ষা করবে? কেউ তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়। আর সেভাবে দেখতে গেলে ঐ ধিকিধিকি করে নিবন্ত উনুনের মত যুদ্ধের দেশ তো আমি নিজেও দেখে এসেছি, পাঁচ ছবার ঘোরা হয়ে গেছে কাবুল। সেরকম খুব বেশি অস্বাভাবিক রকমের ভয়ঙ্কর তো কিছু লাগে নি সেখানে, যেরকম দেখা যায় ওয়ার ফিল্মগুলোয়। একটা কি দুটো মৃত্যু দেখেছি, কিছু ধ্বংসাবশেষ, প্রচুর বন্দুকহাতে মানুষ — যাদের কেউ সেনা, কেউ সেনা নয়।(চলবে)
 Amit | 120.22.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:০৬735797
Amit | 120.22.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:০৬735797- চমৎকার
 Amit | 14.203.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:৪৪735798
Amit | 14.203.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:৪৪735798- একটা পলিটিক্যালি ইন্কারেক্ট কথা ভাবি মাঝে মাঝে। রাশিয়ান বা কমুনিস্ট ইনফ্লুয়েন্স ৫০-৬০ বছর ধরে থাকার কারণেই হয়তো এই মধ্য এশিয়ার দেশগুলো -উজবেকিস্তান / কাজাখস্তান / তাজিকিস্তান ইত্যাদি কট্টর ইসলামিক দের হাতে অতটা পড়েনি। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পরে গত ২০-৩০ বছরেই যতটা অবনতি হয়েছে , তাতে সেই ৫০-৬০ বছরের গ্যাপ না থাকলে যে কি হতো কেউ জানেনা। আজকে হয়তো অনেকগুলো মিনি আফগানিস্তান হয়ে যেত।
 সে | 2001:1711:fa42:f421:e8d7:1e6:3e9:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৪:০১735799
সে | 2001:1711:fa42:f421:e8d7:1e6:3e9:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৪:০১735799- একদম ঠিক অমিত। আমি দুবছর আগেও ঘুরে এসেছি। সে গল্প লিখব পরে।
 স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৭735800
স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৭735800- এই যে সমবেত আপ্যাথি এইটা খুব ইন্টেরেস্টিং লাগে আমার। সত্যজিত রায় বলেছিলেন যে '৪২ এর মন্বন্তর আমাদের উপর সেভাবে দাগ ফেলেনি। ওঁরা তখন নতুন চাকরি পেয়েছেন, নতুন নতুন পরিকল্পনায় বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত - তার মধ্যে মন্বন্তর জায়গা পায় নি। এইটা পড়ে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এ কী রকম সৃষ্টিশীল মানুষ রে ভাই। সেনসিটিভিটি,ফেলোফিলিং নাই। পরে বুঝেছি এমনটা হয় তো, হ্যাঁ ভাল ব্যাপার না নিশ্চয় কিন্তু হয়। কেন হয়? এক্সপোজার, নিজের সোশ্যাল লোকেশন নাকি অন্য কিছু? ধরে উঠতে পারিনি .. লেখাটা মন দিয়ে পড়ছি।
 kaktarua | 192.82.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৯:২৬735801
kaktarua | 192.82.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৯:২৬735801- বাহ্!
 মহুয়া | 174.74.***.*** | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:৫১735806
মহুয়া | 174.74.***.*** | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:৫১735806- অপেখ্যায় রইলাম...
-
 স্বাতী রায় | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:১৫735820
স্বাতী রায় | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:১৫735820 - অপেক্ষায় ...
 সে | 2001:1711:fa42:f421:f9fe:4ab1:581e:***:*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২০:০৯735821
সে | 2001:1711:fa42:f421:f9fe:4ab1:581e:***:*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২০:০৯735821- বড্ড কাজের চাপ। মরবার টাইম পাচ্ছি না। দিচ্ছি, দিচ্ছি...
-
Ranjan Roy | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৬:৫৯735827
- আমরা আছি , আমরা আছি। অপেক্ষায়, অপেক্ষায়।
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১২:৫০735829
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১২:৫০735829- উৎসব
যেদিন প্রথম গুছিয়ে রাশিয়ানে কথা বলতে শিখলাম, সেদিন মায়া আবিদোভনাকে বলেই ফেলেছিলাম সেই কথাটা যে কথাটা বলবার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি। শুধু বললেই তো হবে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে তাকে। সে যদি পুরোপুরি বুঝতে না পারে আমার কথা, তাহলে সব ভেস্তে যাবে, আমার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। ধৈর্য ধরে মনে মনে গুছিয়ে তৈরী করেছি প্রত্যেকটা বাক্য, বাছা বাছা শব্দরূপ ধাতুরূপ এবং যুক্তি দিয়ে।
ক্লাসে দুটো পিরিয়ডের মধ্যে একটু করে বিরতি থাকে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি এমনি এক বিরতিতে একা পেয়ে এগিয়ে গেছলাম মায়া আবিদোভনার দিকে। উনি প্রথমটায় ভেবেছিলেন যে পড়াশুনোর ওপর কোন প্রশ্ন আছে। কথা বলতে শুরু করে খেই হারিয়ে যায়, সমস্ত গুছিয়ে ভেবে রাখা বাক্যগুলো ভুলে যেতে থাকি। উনি ধৈর্য ধরে থাকেন, কোন তাড়া দেন না। আমার কথা শুনতে গিয়ে ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে বলি, মায়া আবিদোভনা যে বিষয় নিয়ে পড়ব বলে এসেছি এ দেশে, সে বিষয় আমি পড়তে চাই না, সে বিষয় আমি একেবারে ভালবাসি না, আপনি বুঝতে পারছেন? উনি বলেন, তাহলে কী পড়তে চাও তুমি? আমতা আমতা করে বলি আমার পছন্দের বিষয়ের নাম। আমি অভিনয় শিখতে চাই, অভিনেত্রী হতে চাই।
উনি চুপ হয়ে যান। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, কিন্তু এখন তুমি যে গ্রুপে ভাষা শিখছ, সে গ্রুপে যা যা পড়ানো হচ্ছে সেসবের সঙ্গে তো তোমার পছন্দের বিষয়ের অনেক তফাৎ, তুমি পড়তে এসেছ বায়োফিজিক্স, তোমার গ্রুপের অন্যরা পড়বে ডাক্তারি, এখন তুমি যা বলছ তাতে তো অন্য গ্রুপে গেলে ভাল হত। আমি যুক্তি সাজাতে থাকি, আচ্ছা যদি আমি কাল থেকেই অন্য গ্রুপে চলে যাই তাহলেও কি খুব অসুবিধে হবে? বিষয় পাল্টানো কি খুব শক্ত ব্যাপার? আপনি পারবেন না ডীন কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে?
মায়া আবিদোভনা চিন্তায় পড়ে যান, কিন্তু আশ্বস্ত করেন যে উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন আমার বিষয় বদল করতে। কদিন পরে খবর দেন, হয়ত আমাকে প্রস্তুত হতে হবে আলাদা পরীক্ষার জন্য। আমি আশার আলো দেখতে পাই। পরীক্ষা দিতে হলে অবশ্যই দেব, প্রমাণ করে দেব যোগ্যতা। তবে কারোকে বলিনা এই গোপন অভিসন্ধি। ক্লাসের একজনও জানতে পারে না, ইন্ডিয়ান কমিউনিটিরও কেউ জানে না এ ব্যাপারে। বলা যায় না, শুধু মুধু ঠাট্টা টিটকিরি করে মনটা ভারী করে দিতে পারে। মার্চের মাঝামাঝি খবর দিলেন শারিপভা, প্রস্তুত হও পরীক্ষার জন্য, যে কোন দিন ডাক পড়তে পারে। তোমার পরীক্ষা এখানে হবে না, যেতে হবে ইনস্টিটিউটে, ভয় পেও না আমরা তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।
দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে গেছে পরীক্ষার দিন ক্ষণ। আর কী সমাপতন, নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি দেখে ফেলেছি সেই ইনস্টিটিউটের দরজা। আর মাত্র কটা দিন রয়েছে হাতে। জায়গাটা দেখে মনটা যেমন ভাল হয়ে গেছে, তেমনি পরীক্ষার জন্য দুরুদুরু কাঁপছে হৃদপিণ্ড। গোপনে প্রস্তুতি নিই পরীক্ষার, পাছে কেউ দেখে ফেলে হাসাহাসি না করে। এইজন্যই ফাঁকা রাস্তা আমার এত প্রিয় হয়ে উঠছে। কেউ ডিস্টার্ব করবার নেই, পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার এটাই বেস্ট জায়গা।
এপ্রিলের মাঝামাঝি এক ঝলমলে দিনে আমায় বগলদাবা করে নিয়ে চললেন শারিপভা। সঙ্গে সহকারী ডীন লারিসা ভাসিলিয়েভনা সিমোনভা। হস্টেলের পেছনের দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেদিক দিয়েই পা চালিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। কীরকম পরীক্ষা হবে, কারা পরীক্ষা নেবে কিছুই জানি না। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম চিয়াত্রালনি ইন্সতিতুতের সদর দরজায়। ওঁরা আমায় নিয়ে গেলেন দোতলার একটা ঘরে। সে ঘরে ডেস্ক বেঞ্চি কিচ্ছু নেই। ফাঁকা ঘর, দুটো চেয়ার, মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা লম্বা মত কাঠের টুকরো। দুজন লোক ঢুকে পড়েছে ঘরে, ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কথা বলছেন নীচু গলায়। এঁরাই আমার পরীক্ষক। ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।
একজন আমাকে জিগ্যেস করলেন,— তুমি গান গাইতে পার? করোনা, একটা গান করো আমরা শুনি।
না, গলা শুকোয় নি, ভয় পাই নি, চট করে ভেবে নিতেও পারিনি। ঝলমলে বসন্তের দুপুরে ঘন বর্ষার রবীন্দ্র সংগীত ধরেছি মন্দ্রলয়ে, আআজিই ঝঅরোও ঝঅরোও মুউখঅরোও বাআদোওরোও দিইনেএ…
লোকদুটো কেমন অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছনোর আগেই একজন উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে। এমতাবস্থায় গান থামালে ডাহা ফেল করব। লোকটা দরজার দিকে হেঁটে চলে গেল, দরজাটা ভাল করে চেপে বন্ধ করে ফিরে এসে বসল আবার চেয়ারে। আমি তড়িৎগতিতে স্ট্র্যাটেজি পাল্টে ফেলেছি। অন্তরা শুরু করে দিয়েছি অন্য সুরে, দ্রুত লয়ে। অল্প পরেই গান শেষ। পুরো পরীক্ষাটা চলছে দুটো ভাষায়। ওরা রাশিয়ানে জিগ্যেস করছে, আমি বাংলায় নেচে কুঁদে লাফিয়ে ইম্প্রোভাইজ করে চলেছি। প্রায় মিনিট চল্লিশ ধরে চলেছিল সেই ভয়ানক কাণ্ড কারখানা। চারজন দর্শকেরই বলিহারি কন্ট্রোল মুখের পেশির ওপর। নিজের নাচন কোঁদন তো নিজে দেখিনি, কিন্তু ওঁরা না হেসে গম্ভীর মুখে অতক্ষণ বসে রইলেন কীকরে সে আজও রহস্য রয়ে গেছে। মাঝে একবার সেই কাঠের টুকরোটাকে কাল্পনিক ডিঙি বানিয়ে ঝড়ের রাতে নদী পেরোনোর অভিনয়ও করতে হয়েছে। পরীক্ষার শেষে কী যে হল বুঝতে পারলাম না, পরে জানিয়ে দেবে বলল। থিয়েটারের ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে আমার দুই শিক্ষিকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। আমার সঙ্গে ফিরতে চান না। কী আর করব, হাঁটা দিলাম একাই হস্টেলের দিকে। একটু পরে পেছন ফিরে অন্যমনস্কতার কারনটা বুঝলাম, দুজনেই একটা খাবারের দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। নিশ্চয় দুর্লভ কোন খাবার এসেছে দোকানে, লাইন দিয়ে কিনে না ফেললে পরে আবার কবে পাওয়া যাবে কেউ জানে না। হতে পারে তা দামি চকোলেট, কি সসেজ, কি আরও লোভনীয় কিছু। সবসময় লোকজন কেবল লাইনে দাঁড়াচ্ছে। দুটো অপশন তোমার হাতে, হয় লাইনে দাঁড়াও, নয় ঘুষ দাও। অনেক জিনিসের জন্যই লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। নয়ত ঘুষ দিয়ে নিতে হয়। দোকানপাট ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয় বলে অসাধু কর্মচারীরা পন্য লুকিয়ে ফেলে বেশি দামে গোপনে বেচে দেবার চেষ্টা করে।মে দিবসে পর পর দুদিন ছুটি থাকে, পয়লা এবং দোসরা। তার কদিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের জন্য ৯ই মে আবার ছুটির দিন। এই সব দিনগুলোয় উৎসবের আনন্দ উদযাপন করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই রীতি। সকাল নটার মধ্যে সেজে গুজে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে নিকটবর্তী কোনও একটা স্মৃতিসৌধ গোছের জায়গায়। আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে নিয়ে গেল বাসে করে “ভূমিকম্প স্কোয়ারে” (প্লোশাদ জিম্লাত্রেসেনিই); সেখানে ফুলে ফুলে ছয়লাপ অবস্থা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ করে ফিরে এলাম আবার হস্টেলে। পয়লা এবং নয়ুই মে দুদিন ই বাধ্যতামূলকভাবে টিভির সামনে বসে দেখতে হল মস্কোর প্যারেড, লাইভ টেলিকাস্ট। এরকম টেলিকাস্ট আগেও একবার দেখা হয়ে গেছে ছঁয়ুই নভেম্বরে। ছঁয়ুই এবং সাতুই নভেম্বর খুব জাঁক জমকের সঙ্গে দেশব্যাপী উদযাপিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় উৎসব। পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুসারে সে তারিখ আসলে ছিল পঁচিশে ও ছাব্বিশে অক্টোবর। মস্কোর রেড স্কোয়ারে (ক্রাসনাইয়া প্লোশাদ) বিশাল কুচকাওয়াজ অনেক অস্ত্র শস্ত্রের গর্বিত প্রদর্শন। চারিদিকে লাল পতাকা, সমস্ত লালে লাল। সেবারেও শীতের মধ্যে গোড়ালি ডোবা বরফের মধ্যে ভূমিকম্প স্কোয়ারে গিয়ে বিপ্লবের আটষট্টিতম জয়ন্তীতে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হুররা হুররা বলেছি, মায়া আবিদোভনা আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রিহার্সাল দিইয়ে তৈরী করে রেখেছিলেন আমাদের। ভূমিকম্প স্কোয়ারের ছোট কুচকাওয়াজে মন্ত্র পড়ার মত করে একজন মাইকের সামনে যেই বলছিল “মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের আটষট্টিতম জয়ন্তীর অভিনন্দন!” (দা জ্দ্রাস্ৎভুয়েৎ শেস্তজেসিয়াৎভাসমোই গদাভশিনি ভিলিকোই অক্তিয়াবর্সকোই সৎসিয়ালিস্তিচেসকোই রেভালিউৎসিই!) অমনি আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিলাম— হুররা! সে যতবার বলছিল ততবার করে হুররা। হস্টেলে ফিরে দেখলাম টিভিতেও কুচকাওয়াজে ওরকম হচ্ছে, গ্যালারিতে দর্শকেরা হুররা করছে, হুররা থেমে গেলে পিন ড্রপ সায়েলেন্স, এমন অরগ্যানাইজড দর্শক এর আগে কোনদিনও দেখিনি।
এতটা বীররস দিয়ে উৎসব উদযাপনের অভ্যাস দেশে থাকতে তৈরী হয় নি। সেখানে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের পদ্ধতি ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মাইক বাজিয়ে গান, ইত্যাদি। এখানে বারোয়ারী উৎসবগুলো অধিকাংশই বীররসাত্মক হলেও ভক্তিরসও যে তাতে থাকে তা বুঝতে পারি। সকালের দিকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বন্ধু প্রতিবেশীদের অভিনন্দন জানানোর পরে সকলেই ছুটিটুকু মন দিয়ে উপভোগ করে। সন্ধে হলেই সরকারি ভবনগুলোর গায়ে দেখা যাবে আলোকসজ্জা। অক্টোবর বিপ্লবের জয়ন্তীতে আলো দিয়ে সাজিয়ে লেখা থাকবে “বিপ্লব জিন্দাবাদ” (স্লাভা রেভালিউৎসিই), ঝলমল করবে চতুর্দিক। প্রতেকটা শহরে লেনিনের মূর্তিসহ একটা করে লেনিন স্কোয়ার (প্লোশাদ লেনিনা) থাকবেই। সেখানে মেলার মত পরিবেশ, লোকজন সেজেগুজে এসে ঘুরছে আনন্দ করছে। সব উৎসবেই এই একই রীতি। উৎসব বিশেষে শুধু স্লোগানগুলো বদলে যায়, মে দিবসে বলে “শান্তি, শ্রম, মে” (মির, ত্রুদ, মাই), নারীদিবসে “৮ই মার্চ জিন্দাবাদ” (স্লাভা ভাসমোয়ে মার্তা) কি “সোভিয়েত নারী জিন্দাবাদ” (স্লাভা সোভিয়েৎস্কিম জেনশিনাম), নতুন বছরের দিনেও ঝলমল করে প্লোশাদ লেনিনা। সন্ধের দিকে প্রায় সকলেই কম বেশি কয়েক পাত্র ভোদকা চড়িয়ে উৎসবে সামিল হয়। আমরা বিদেশিরাও যাই, যেতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।নতুন বছরের দিনটায় অবশ্য অন্যরকম মজা হয়েছিল। সেই মাছ ছুঁড়ে ফেলা এবং তা ফিরিয়ে দিয়ে আসার ঘটনার পরে গডউইনদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পয়লা জানুয়ারি আমরা কয়েকজন মিলে সিনেমা দেখতে গেছলাম। তাশকেন্তে বেশ অনেকগুলো সিনেমাহল, এবং রাশিয়ানে ডাব করা হিন্দি সিনেমা কোনও না কোনও হলে চলবেই। সেসব অধিকাংশই পুরোনো বই, রাজকাপুর ঘরানার। অল্প স্বল্প সমসাময়িক বইও চলে যেমন, মিঠুন চক্রবর্তীর ডিস্কো ডান্সার, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত অমর আকবর অ্যান্টনি, ইত্যাদি। ইন্ডিয়ানরা রাশিয়ানে ডাব করা হিন্দি বই দেখতেই পছন্দ করত। পয়লা জানুয়ারি প্লোশাদ লেনিনার ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না, লোকজন যারা রয়েছে সবই মারাত্মক রকমের মাতাল, রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমরা তিনচারজন মিলে গরম জায়গা খুঁজতে কাছেই একটা সিনেমাহলে ঢুকে পড়লাম। হলটার নাম ইস্ক্রা (বাংলা অর্থ স্ফুলিঙ্গ, এই হলে হিন্দিবই চলত না), কী বই চলছে নাম না দেখেই ঢুকে পড়েছি। সেই প্রথম একটা রাশিয়ান ছবি দেখেছিলাম যেটা বীররসাত্মক নয়, ওয়র মুভি নয়, আমার দেখা দশটা প্রিয় সিনেমার মধ্যে এইটা সারাজীবন থেকে যাবে। গুনে গুনে তিন মাস হয়েছে তখন ভাষা শেখা , সব সংলাপ বুঝতে পারি না, তবু হাঁ হয়ে আদ্যন্ত দেখেছিলাম বইটা এবং অবাক হয়েছিলাম এত কড়াকড়ির দেশে ঐ বই কীকরে দশ বছর আগে(১৯৭৬) ব্রেঝনেভের আমলে সেনসরের ছাড়পত্র পায়! নাঃ ভদ্রলোক সত্যিই রসিক ছিলেন। “নিয়তির পরিহাস, অথবা চট করে শুকিয়ে উঠুন” (ইরোনিয়া সুজবি, ইলি স্লোঃকিম্ পারম্) এই নাম সেই বইটার (এখন ইন্টারনেটে দেখলাম ইংরিজিতে অনুবাদ করছে: Irony of fate, or enjoy your bath উঁহু, “enjoy your bath” টা সঠিক অনুবাদ নয়)। আমার সঙ্গীরা প্রথমে খুব হাসতে থাকে মজার ঐ সিনেমা দেখতে দেখতে, তারপর রাত হতে থাকে, তাদের খিদে পেতে থাকে, হস্টেলে ফিরবার জন্য তাড়া দেয় ঘন ঘন, তিনঘন্টার ওপর চলে সিনেমা, আমি জেদ ধরে বসে থাকি শেষ না দেখে কিছুতেই বেরোতে রাজি হই না। ঐ একটাই রাশিয়ান সিনেমা দেখা হয়েছিল প্রথম বছর, যেটা সিলেবাসের বাইরে, যেটার বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়। খুব অল্প ভাষাজ্ঞান নিয়েও হাসতে হাসতে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তা ভাবায় এবং ভয় পাইয়ে দেয়। গল্পটা এইরকম, না জেনে কেউ যদি এক শহরে যেতে গিয়ে অন্য শহরে উপস্থিত হয়, তবে সে ফারাক বুঝতে পারবে না। গল্পের নায়ক মস্কোয় থাকে, মাতাল অবস্থায় ঘটনাচক্রে সে পৌঁছে যায় লেনিনগ্রাদ। দুটো শহরে একই নামের রাস্তা, একই রকম দেখতে বাড়ি, দরজার চাবি পর্যন্ত মিলে যায়, ঘরের আসবাব এক, জামাকাপড়, বাসনকোসন সমস্ত অবিকল এক। আমরা দর্শকেরা হেসে কুটিপাটি হচ্ছি, রাস্তা বাড়ী দরজা জানলা চাবি সব মিলে যাচ্ছে দেখে। হয়ত বিদেশি বলেই আমার চোখে পড়ছে বেশি করে যে বিপ্লব নববর্ষ সব অনুষ্ঠানই একরকম, সবসময়েই লোকে ভক্তিভরে ফুল দিয়ে আসে প্লোশাদ লেনিনায়, এমনকি বিয়ে করে নবদম্পতিও লেনিনের স্ট্যাচুর কাছে সবার আগে যায়, ভক্তি ভরে ফুল দেয়, ফটো তোলে, বাকি সব অনুষ্ঠান এর পরে।
ঐ নতুন বছরের সময় থেকেই একটু একটু করে বুঝতে পারতাম সোভিয়েতদের চেহারার প্রভেদ, চিনতে পারতাম কে এশীয় কে ইয়োরোপিয়ান, কে উজবেক কে রাশিয়ান।থিয়েটারের ইন্সটিটিউটে পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে এক উইকেন্ডে মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের হস্টেলে গিয়ে এলপি রেকর্ডে একটা উজবেক দলের গাওয়া কয়েকটা রাশিয়ান গান শুনেছিলাম। গ্রুপটার নাম ইয়াল্লা, গেয়েছেন ফারুখ জাকিরভ। সুর যেমন সুন্দর তেমনি প্রত্যেকটা কলির মানে বুঝতে পারাও রোমাঞ্চকর। অজানা গান বাজছে রেকর্ডে, উচ্ কুদুক (এটা তিনটে কুয়োর গান) কিংবা সেই বিখ্যাত গানটা— চাইখনা। সে গানের মর্ম পূবের দেশের লোক ছাড়া বুঝবার সাধ্যি আর কারও নেই।
মে দিবসের ছুটির পরপরই শেরগোল পড়ে গেল হস্টেলে। খুব করিৎকর্মা এক ডিরেক্টর এসেছেন হস্টেলে, সামনের সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল। সেই ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নাচ গান করানো হবে। আমাদের মধ্যে থেকে জনা তিরিশেককে তিনি বেছে নিলেন। আন্তর্জাতিক ফেস্টিভালের আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য স্টেজে নাচবে গাইবে আন্তর্জাতিক টিম। এই হচ্ছে আইডিয়া। লাতিন অ্যামেরিকার ছেলেমেয়েরা চমৎকার নাচতে পারে, আমি ইন্ডিয়ার কলঙ্ক কোনও দিনও নাচ শিখিনি। খুবই ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য হলের ডিরেক্টর মশাই। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, যে দেশের সিনেমায় প্রত্যেকটা নায়িকা এবং খলনায়িকা কথায় কথায় নেচে ওঠে, সত্যিই সেই দেশ থেকে এসেছি কিনা। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র উনি নন। গোটাকতক স্টেপ শিখিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে হাত ঘোরানো। একটা গ্রুপ ডান্সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরকম করলেই চলবে। প্রত্যেকদিন বিকেল হলেই শুরু হয়ে যেত আমাদের রিহার্সাল। চলেছিল ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হবার আগের দিন অবধি, তাশকেন্তের প্রাসাদের মত অডিটোরিয়াম দ্রুঝবি নারোদভ -এ।
রিহার্সাল যখন তুঙ্গে, প্রায় মেরে এনেছি নাচের সব কটা স্টেপ, এমনি এক বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে মায়া আবিদোভনা সেখানে উপস্থিত। স্টেজের ওপর থেকেই দেখছি তিনি নীচে দাঁড়িয়ে ইশারা করে চলেছেন। আমাদের প্র্যাকটিসটা শেষ হতে না হতেই মামা বলে একটা মেয়ের গানের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। মামা মালির মেয়ে, যেমন স্টেজ ফ্রি তেমন ব্যক্তিত্ব। মামা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চোখ বুজে দরদ দিয়ে গাইছে, আমি লাফিয়ে স্টেজ থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছি। মায়া আবিদোভনা খুব তাড়াহুড়ো করে বললেন, “খবর আছে, তুমি পাশ করে গেছ”। কীসের পাশ? মাথায় ঢোকে না কথাগুলো। উনি চোখ কপালে তুলে বলেন—মনে নেই সেদিন পরীক্ষা দিয়ে এলে অভিনয় শিখবে বলে!
স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়বার সময় পা যে মচকেছে তা অনুভব করতে পারিনি। শারিপভা বেরিয়ে গেলেন অডিটোরিয়ামের একেবারে সামনের একটা গেট দিয়ে স্টেজের দুপাশে যেগুলো থাকে। আমার মাথার মধ্যে কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না, কানে যেন তালা লেগে গিয়েছে, স্টেজের ওপর মামা হাত নেড়ে নেড়ে গানের ভাব বোঝাচ্ছে। প্রথম সারির ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়লাম। এ আনন্দ সংবাদ কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে না। সমস্ত আনন্দটা চেপে রাখতে হবে নিজের মনের ভেতরে। একেবারে ‘লেংচে মরি’ অবস্থায় আবার স্টেজে উঠলাম, স্টেপস ভুল হতে লাগল, ডিরেক্টর চেঁচামেচি করছেন, বাট হু কেয়ার্স! ওরে বাবা, এ খবর চেপে রাখা যায় না, পেট গুড় গুড় করে আনন্দে, হস্টেলে ফিরেই বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ফেলি গোটা কতক। মাথাটা একটু ঘুরে ঝিমঝিম করে, উঁহু এ জিনিস চেপে রেখা অসম্ভব, শাম্মি কাপুরের মত লাগছে নিজেকে, ইয়াহু! ডুডুম ডুডুম ডুম! ইয়াহু! চাহে কোয়ি মুঝে জংগলি কহে, কহনে কো জি কহতা রহে… ইয়াহু! ডুডুম ডুডুম ডুম! নিরীহ রুমমেট দুজন আমার আচরণে কিছু আঁচ করে থাকতে পারে। ঐ ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাবে এত আনন্দ নিয়ে। বেরিয়ে পড়েছি বাইরে, অন্যমনস্কভাবে বাস পাল্টাতে পাল্টাতে পৌঁছে গেছি দোম্ব্রাবাদ।
দোম্ব্রাবাদের বন্ধুবান্ধবেরা এ খবর সুখবর হিসেবে নিল না, বসে গেল আলোচনাচক্র যুক্তি তর্ক সহকারে। উত্তর দক্ষিণ দুরকম ভারতের লোকই রয়েছে সেখানে। তারা আমাকে বোঝাতে থাকে অভিনেত্রী হবার কুফল কী কী হতে পারে। প্রথমত স্টেজের নাটক কাকে বলে সেটাই এরা জানত না, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ভারতে এত প্রদেশ রয়েছে, তারা অনেকেই তাহলে স্টেজের অভিনয় কাকে বলে সেটা জানে না? “ডান্স ড্রামা” ভেবে নেয়। হিন্দি সিনেমার ভেতরে যেগুলো দেখায়, মনে করে সেগুলোই করতে চাচ্ছি। সিনেমার অভিনয় বোঝে। আরও বোঝে যে সিনেমায় যারা অ্যাকটিং করে সে সব মেয়েরা “ক্যারাকটারলেস”, তাদের দিয়ে সংসার হয় না, তারা জামাকাপড়ের মত পুরুষ সঙ্গী বদলায়, তাদের কেউ রেসপেক্ট করে না। আমি যদি অ্যাকটিং এর লাইনে যাই তবে আমাকে বিয়ে করবে কে? তারা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও কেন আমি এসব পথে যেতে চাইছি, কে আমাকে এরকম দুর্বুদ্ধি দিয়েছে, আমার বাড়ির লোকজন এ খবর পেলে শকড্ হবে, এবং ফাইনালি আবারও জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার “ক্যারাকটার” খারাপ হয়ে গেলে কেউ আমাকে বিয়ে করবে না।এত সব কথা এর আগে ভেবে দেখিনি মন দিয়ে। হয়ত দেশে ঘনিষ্ঠজনেদের মনের কথা এরকমই, কেবল ভদ্রতার মুখোশটুকু খুলে এত খোলাখুলিভাবে তারা তাদের মনের কথা বলে উঠতে পারে নি। দেশে থাকতেও মনের মত পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে পারি নি, পছন্দের পেশা বেছে নেবার পথে অনেক বাধা থাকে ভদ্রলোকের ঘরে জন্মালে। আত্মীয় স্বজন শিক্ষক হিতাকাঙ্খীরা ভুলিয়ে ভালিয়ে কেবলই বুঝিয়েছে এখন অভিনয়কে পেশা হিসেবে ভেব না, তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কত সুন্দর অঙ্ক কষতে পারো, ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জটিল জটিল তত্ত্ব কি চমৎকার বুঝে ফেলেছ, কত নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, সবাই কি ওরকম পারে? এত কিছু যখন পেরেছ তখন “ভালো ভালো” সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করে পরিবারের মুখোজ্জ্বল করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আরে বাবা নাটক করা তো পালিয়ে যাবে না। প্রথমে একটা ভদ্র গোছের শিক্ষাগত যোগ্যতা রইল, পাশে ফ্রি-টাইমে নাটক কর না, কেউ তাতে বাধা দেবে না। এর নাম ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ইচ্ছেটাকে চেপে মেরে দেওয়া। এসব আমি দেশে থাকতেই বুঝে ফেলেছিলাম, হয়ত ওদের বিচারে “বুদ্ধিমতী” বলেই। যে শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে ফেলতে পারে, সে এই ছেলেভুলোনো ফন্দিও ধরে ফেলে, কিন্তু সে কিছু করে উঠতে পারে না, নিজের ইচ্ছেমত পেশা বেছে নেব বললেই তো তা করা যায় না, অনুরোধ মগজধোলাই ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং সমস্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি ভেঙে পড়ো, যতক্ষণ না তুমি পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে হেরে যেতেই হবে, তুমি আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে তোমার পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, যতদিনে এদের কথা মেনে তোমার অপছন্দের পেশা বেছে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, ততদিনে তোমার নিজের পছন্দের পেশায় যাবার পথ আরও দুর্গম হয়ে গেছে। এত শত ভেবেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম এখানে নিজের পছন্দমত তালিম নিতে পারব বলে, মাথার ওপরের ছাদ, কি অন্নবস্ত্রের জন্য কারো মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে না। মাথার ওপরের নিরাপদ ছাদ এবং অন্ন বস্ত্রের বিনিময়ে বড্ড বেশি দাম চোকাতে হয় সংসারে, মনের স্বাধীনতা থাকে না, সমস্ত ইচ্ছেকে বেঁধে ফেলতে হয় যদি তা অন্নদাতার ইচ্ছের সঙ্গে না মিলে যায়। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, ঘর থেকে দুম করে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে গাছতলায় কি ফুটপাথে থাকাও তো নিরাপদ নয়। অনেক বেশি আঁটঘাট বেঁধে পথ বেছে নিতে হয়, পরামর্শ করবার মত কারওকে পাওয়া যায় না পাশে। এই ই তোমার ভবিতব্য। নাটকের মেয়ে বনে গেলে তোমায় বিয়ে করবে কে? কী ভাবে কাটাবে তুমি বাকি জীবনটুকু যদি বিয়েই না হল? ভদ্র পেশা বেছে নাও, ভালো ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট কর, ভালো ভালো পাত্রেরা লাফ দিয়ে ছুটে চলে আসবে তোমায় বিয়ে করতে। এমন সুযোগ কি সকলে পায়? কত গরীব দুঃখী আছে দুনিয়ায়, তারা খেতে পায় না দুবেলা পেট ভরে, পড়াশোনা করবার সুযোগ পায় না, কত মেয়ে কচি বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে খেটে মরে। তুমি তো এদের দলে নও, তুমি প্রিভিলেজড মেয়ে। তবু তোমার স্বাধীনতা নেই নিজের পছন্দের পেশা বেছে নেবার, দুটি স্তন একটি যোনি থাকার জন্য তুমি যখন তখন চাইলেই যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে না। তোমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। একথা দেশে থাকতে সফিসটিকেশনের মোড়কে ঢাকা অবস্থায় শুনেছি, এখানেও শুনে নিলাম চাঁচাছোলা ভাষায়। মূল বক্তব্যে প্রভেদ নেই। প্রভেদ আছে শুধু আমার ভৌগলিক অবস্থানে। আপাতত মাথার ওপরের ছাদ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এখানে। মনটা তেতো হয়ে গেলেও এটুকু জানি আমি জলে পড়ে যাব না। ক্যারাকটারটা একদম খারাপ হয়ে যাবে সেটা বোঝা গেছে। এরা বলল, যেসব মেয়েরা অ্যাকটিং করে তাদের কত রকমের সীন করতে হয় পুরুষদের সঙ্গে, এর পর থেকে কোনও ইন্ডিয়ান কি আর আমার সঙ্গে মিশতে চাইবে? কত ভালো ভালো সাবজেক্ট নিতে পারতাম, ডাক্তারি, জার্নালিজম, মেয়েরা তো এসব পড়ছে এখানে, এসব পড়েও অনেক টাকা রোজগার করা যায়, আফগানিস্তান থেকে জাপানি কাপড় কিনে স্মাগল করে এনে চোরবাজারে বেচে দেওয়াও অনেক সম্মানের কাজ নাটকের মেয়ে হবার চেয়ে, লোকে রেসপেক্ট করে, ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। একটু সন্দেহ ঢুকল মনে, এরা আমার বিয়ে নিয়ে এত চিন্তিত কেন? আমায় পোটেনশিয়াল পাত্রী ভেবে রেখেছে নাকি নিজেদের জন্য? খুবই সম্ভব, এই তো প্রেমে পড়ার বয়স।
ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে দ্রুঝবি নারোদভের অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। সারা দুনিয়ার সিনেমা জগতের সেলিব্রিটিদের দেখতে উপচে পড়েছে জনতা। তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না মিলিৎসিয়া, ফাঁক পেলেই হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে বেড়া ভেঙে। আমাকে শাড়ি পরা দেখে সেলিব্রিটি বলে ভুল করে ঘিরে ফেলে। যত তাদের বোঝাই যে আমি সাধারন একজন ছাত্রী, তারা মানবেই না। ভারতীয় মেইনস্ট্রিম সিনেমা এমন ঘোর লাগিয়েছে এদের চোখে, যে ঝলমলে সিল্কের শাড়িতে আমাকে দেখে তাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম অবস্থা। রীতিমত দরাদরি শুরু করে দেয়, অটোগ্রাফ না দিলে ছাড়বে না। সই করতে করতে ভিড় ঠেলে বেরোচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি বিশেষ সতর্কতা নিয়ে গার্ড করে টপ সেলিব্রিটিদের তোলা হচ্ছে গাড়িতে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলো, জনতা হুড়মুড়িয়ে ছুটে যেতে থাকে সেদিকে। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় প্রাসাদের চত্বর। আমরা যারা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম ছোট ছোট গ্রুপ করে ফিরতে থাকি হস্টেলের দিকে। কিছু ফটো তোলা হয় প্রাসাদের পটভূমিকায়। দুনিয়ার নানান দেশ থেকে এসেছে কত ডিরেক্টর ফিল্মস্টার তাদের সিনেমা নিয়ে। সেই সিনেমাগুলো কি এখন তাশকেন্তের সিনেমাহলগুলোয় দেখানো হবে? কোন ভাষায় দেখানো হবে বইগুলো? এখানে তো রাশিয়ান ডাবিং ছাড়া কোনও বিদেশি বই দেখানো হয় না। ইন্ডিয়া থেকে কারা কারা এসেছে ঐ সেলিব্রিটিদের মধ্যে? রেখা, শ্রীদেবী এরা যদি এসে থাকে? এদের কারওকে সামনা সামনি দেখতে পাওয়া যাবে না? কারা এসেছে? কোথায় নিয়ে গেল ওদের? সেই অ্যক্ট্রেসটার নাম যেন কী, আহা সেই যে অমর আকবর অ্যান্টনি তে ছিল যে মেয়েটা, সেই যে— অভি অভি ইসি জাগা মে এক লেড়কি দেখি হ্যায়, আহা দেখি হ্যায়, আহা দেখি হ্যায়… ইশ্ পেটে আসছে মুখে আসছে না নামটা। সে এলে দারুণ হবে।
পরের দিন রবিবার। দশটা এগারোটার আগে কেউ ব্রেকফাস্ট করে না। এমনি রবিবারে এগারোটার মধ্যেই গডউইন এসে পড়েছে আমার হস্টেলে। কী ব্যাপার, নাটকের মেয়ের সঙ্গে যোযাযোগ রাখার মত গর্হিত কাজ করতে ওর একটুও দ্বিধা হল না? সকলে মিলে যখন লেকচার দিচ্ছিল তখন তো সবই শুনছিল, নিজেও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছে, এত তাড়াতাড়ি পাল্টি খেল ছেলেটা! গডউইনের মুখে সলজ্জ হাসি। এরা তো শনিবারের রাতে ঘুমোয়ই না বলে জানি, সারারাত মদ খায় হৈ হুল্লোড় করে। সেই ছেলে এত সকাল সকাল এত দূর থেকে এখানে এসেছে কেন, মতলব টা কী ওর? এই প্রশ্নটাই ওকে সোজাসুজি করে বসি। কান এঁটো করে হেসে ফেলে সে। একেবারে ধরা পড়ে যাবার হাসি। মতলব একটা আছেই, সেটা হচ্ছে আমায় হোটেল উজবেকিস্তানে নিয়ে যাওয়া, সেখানে টপ ক্লাস সেলিব্রিটিরা এসেছে, কাপুররা তো আছেই, আরো অনেক সেলিব্রিটি রয়েছে, কোলকাতা থেকে এক বেংগলি ম্যান ও এসেছে, সে অ্যাক্টর না অন্য কিছু সেটা গডউইন জানে না, গতকাল হোটেলে গেছল মদ গিলতে, মিলিৎসিয়া গেটের কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। হাই সিকিউরিটি জোন এখন হোটেল উজবেকিস্তান। এখন আমি যদি ওর সঙ্গে যাই, তাহলে হয়ত ইন্ডিয়ান গার্লকে দেখে গার্ড বা মিলিৎসিয়ার মন নরম হতে পারে, অবশ্যই শাড়ি পরে যেতে হবে, শাড়ি না পরলে পাবলিক বুঝবে কেমন করে যে আমি জেনুইন ইন্ডিয়ান গার্ল কি না। ওরা যাবে ওখানে বিদেশিদের কাছ থেকে ব্ল্যাকে ডলার কিনতে, ওদেরকে হোটেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করল গডউইন মাথা নীচু করে। ওরা মানে? ও একা আসেনি! উঁহু, নীচে অপেক্ষা করছে আরও দুজন, ডলারের আশায় আশায় এই অবধি এসেছে। কিন্তু আমার এতে কী লাভ? আমার তো ব্ল্যাকে ডলার কেনার সঙ্গতি নেই, আমার নিজের কী উপকারটা হবে? প্রশ্নের উত্তর ওর ঠোঁটের গোড়াতেই রেডি ছিল — হোটেলের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে কত শত ফিল্ম স্টার, যাকে পছন্দ তার সঙ্গেই আলাপ করতে পারবে। এমন করে বলল গডউইন, এ যেন স্বয়ম্বর সভা, হোটেলে ঢুকে যাকে পছন্দ তার গলায় মালাটা পরিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। খদ্দরের একটা সাদা শাড়ি পরে চললাম ওদের সঙ্গে। হোটেলের কাছাকাছি আসতেই দেখি মিলিৎসিয়া এবং গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোকের মুখ দেখে কেমন চেনা চেনা লাগছিল, ওরা কানে কানে আমাকে সাবধান করে দেয়, লোকটা কেজিবির এজেন্ট। দরজার কাছটায় ঝাঁকে ঝাঁকে রূপসী মেয়ে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ভেতরে ঢুকবার পার্মিশান নেই। গলায় আইডেন্টিটি কার্ড ঝোলানো না থাকলে অ্যাডমিশন প্রোহিবিটেড।
গডউইনরা ফিসফিসিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ভেন্ট্রিলোকুইস্টদের মত করে আমার কানের পাশে বলে যায়, “কিসি তরফ মাৎ দেখনা, সিধা চলা যাও, ইয়ে সারে প্রসটিটিউটসকো ইগনোর করকে সিধা গেট কে সামনে চলো স্মার্টলি”। আমি ওদের নির্দেশ মেনে সোজা গেটের কাছে গিয়ে গার্ডকে উপেক্ষা করে গটগটিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই, গডউইনকে গেটে আটকে দিলে পেছন ফিরে গার্ডকে হাতের ইশারা করে ইংরিজিতে বলে দিই যে ও আমার সঙ্গে আছে। বাকি দুজনকে কিছুতেই ঢুকতে দেয় না গার্ড। এই প্রথম ঢুকলাম হোটেলটার ভেতরে। উচ্ছ্বাসে আত্মহারা গডউইন আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, “সাড়ি ইজ ইয়োর পাসপোর্ট অ্যান্ড ইউ আর মাই পাসপোর্ট”। অল্প সোজা গেলেই নাক বরাবর ডাইনিং হল। গডউইন সব চেনে। হলের ভেতর অতিথিরা লাঞ্চ করতে বসেছে, কিন্তু হলের দরজায় আবার আটকে দেয় গেটকীপার, ভেবেছে আমরা খেতে ঢুকছি বুঝি। আমাদের গলায় তো কার্ড ঝুলছে না। খোলা দরজার বাইরে থেকে উঁকি ঝুকি মেরে গডউইন একজনকে দেখতে পায়, গেটকীপারকে বলে, “ঐ তো ওঁকে খুঁজছি আমরা”। বেশি দূরে নয়, কয়েকটা টেবিল পরেই দেখতে পাই দুজন বসে খাচ্ছে। একজন যুবক, তার মুখোমুখি আর একজন আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসা, তার টাক দেখা যাচ্ছে। গডউইন আমাকে বলে, “ক্যান ইউ রেকগনাইজ দেম? দে আর বেংগলিজ”। ঐ যে টাক মাথা লোকটা বসে খাচ্ছে সম্ভবত তার সঙ্গে কথা বললেই কাজ হবে, তাকেই ও কাল দেখেছে। ওরকমভাবে ওদের দেখে হাতটাত নেড়ে কথা বলছি দেখে সেই যুবক খাওয়া ছেড়ে উঠে এল দরজার কাছে, আমাকে দেখে পরিস্কার বাংলায় বলল, “আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন”? গডউইন বাংলা বোঝে না, আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল আবার। যুবকটিকে আগে কখনও দেখিনি, সে সপ্রতিভভাবে বলল, “আমাকে কী করতে হবে, অটোগ্রাফ চাই নাকি”? বললাম, “না অটোগ্রাফ না, ঐ ওঁকে একবার ডেকে দেবেন”? ভদ্রলোকটি এর মধ্যে এদিকে ফিরে তাকিয়েছেন, হাত তুলে ডাকলেন ওঁর টেবিলে। দেখলাম খাওয়া প্রায় শেষই হয়ে গেছে ওঁদের। গডউইন ধরা গলায় বলল, “স্যার উই আর ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস হিয়ার, আই অ্যাম গডউইন অ্যান্ড শী ইজ…”। যুবক সেখানে দাঁড়ালো না, ঘরে যাচ্ছে বলে চলে গেল সেখান থেকে। গডউইন আবার ভেন্ট্রিলোকুইস্টদের মত করে ধমকালো আমাকে, “অটোগ্রাফ লে নে মে কেয়া হর্জ থা”! টাক মাথা ভদ্রলোক জানালেন, তিনি বাংলা সিনেমার ডিরেক্টর, ঐ যুবকটি ওঁর লেটেস্ট বইয়ের নবাগত নায়ক, বইটা দেশে প্রাইজ পেয়েছে, এখন ফেস্টিভালে ওটা নিয়ে এসেছেন ওঁরা দুজন। নিজের পরিচয়ও দিলেন, গডউইন বাংলা সিনেমার জগতে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারও নাম জানে না, কিন্তু আমি তো এঁর বানানো একটা বই বিদেশযাত্রার আগেই দেখে ফেলেছি। ইনি আর্ট ফিল্ম বানান। লেটেস্ট বইটার নাম “কুঠার”, জানালেন নির্দেশক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। খাবার টেবিলেই আলাপ এগোতে লাগল আমাদের। “বাঃ বাঃ কী পড়ো তোমরা? গডউইন ডাক্তারি পড়ছ? বাঃ, কোন ইয়ার? আর তুমি কী পড়তে এসেছ? বাঃ খুব ভাল। নাটক নিয়ে পড়বে এতো বেশ আনন্দের কথা”।
আমি উৎসাহ পাই। বলি, “জানেন আপনার সেই সিনেমাটা দেখেছি যেটায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন, ওঁকে আমি মনে মনে গুরু মানতাম, কিন্তু উনি তো মারা গেলেন, তবু আমি অভিনয় শিখব বলে জেদ করে এখানে এসেছি, …”। উনি মন দিয়ে আমার কথা শোনেন, তারপর গডউইনের সঙ্গেও কথা বলেন, গডউইন ডলারের প্রসঙ্গটা কীভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না, ইনি কতটা পয়সা ওয়ালা লোক, কত ডলার ভাঙাবেন, আদৌ ভাঙাবেন কি না কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না। আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গডউইন জানতে চায় আরও ইন্ডিয়ান আছেন কিনা যাদের সঙ্গে উনি আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে গডউইন। রিস্ট ওয়াচটা দেখে নিয়ে তারাচাঁদবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন, বলেন, “চলো লবিতে দেখা হয়ে যেতে পারে, জয়া শুড বি দেয়ার বাই নাও”। উনি লবির দিকে এগিয়ে যান আমরা পিছুপিছু ফলো করতে থাকি, গডউইন বলে, “ও মাই গড, জয়াপ্রদা ইজ মাই টপ ফেভারিট, রিমেমবার দ্যাট শরাবিওয়ালা সং? মুঝে নওলখা মাংওয়া দে রে ও সঁইয়া দিওয়ানে, হোয়াট অ্যা ফিল্ম ইয়ার! আই হ্যাভ সীন ইট থ্রি টাইমস”।
লবিতে খুব কম লোক, একজন কি দুজন। রিসেপশান ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িপরা এক ভদ্রমহিলা ডেস্ক ক্লার্কদের কিছু বলছিলেন। তারাচাঁদবাবু আমাদের নিয়ে বসলেন সোফায়। দূরে করিডোর দিয়ে পাঞ্জাবি কুর্তা পরা একজন রোগামতন লোক হেঁটে আসছে মনে হল। রিসেপশানে কথা শেষ করে শাড়িপরা ভদ্রমহিলাটি এদিকে ঘুরতেই তারাচাঁদবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, “জয়া! এই দেখ একজন বাঙালি মেয়ে এসেছে দেখা করতে”। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব? তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না, ইনি তো নওলখাওয়ালা জয়া নন, ইনি তো জয়া ভাদুড়ি! সেই রোগা লোকটিও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন একদম আমার সামনে। তারাচাঁদবাবু আমাদের পরিচয় দিচ্ছেন এঁদের সঙ্গে, আমি ঢোঁক গিলে সেই রোগা লম্বা লোকটিকে বলে ফেললাম, “এক্সকিউজ মী— ইয়োর অটোগ্রাফ প্লিজ…”। কিন্তু হাতের কাছে কাগজ কলম কিছু নেই, এক লাফে রিসেপশন থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিলাম, কলম ওঁর নিজের কাছেই ছিল। রিসেপশানের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে খশখশ করে সেই কাগজে সই করে দিলেন অমিতাভ বচ্চন।চলবে...
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০০735830
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০০735830- গান ও নদী—তোমরা গান গাইতে পারো?
লোকটা জিগ্যেস করেছে রাশিয়ানে, কিন্তু বাক্যটার বাংলা অনুবাদ করলে এরকমই দাঁড়ায়। বিকেলের আলো কমে আসছে, প্রশ্নটা করে লোকটা আমাদের কাছে এগিয়ে এল। আমরা দুজন। ফেরেসালাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে। লোকটার পরণে কোট প্যান্ট, মাথায় কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল, বয়স তার পঞ্চাশও হতে পারে আবার ষাটও হতে পারে। প্রশ্নটা করবার পর থেকে সে মিটমিটিয়ে হাসছে, দুচোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দুজনকেই যেন জরিপ করে নিচ্ছে। ফেরেসালাম আমার ফ্রকে টান দেয়, অস্পষ্ট করে ইংরিজিতে বলে, লেটস্ গো। আসলে ও বলতে চাইছে, চল্ পালাই এখান থেকে। তবু আমরা নড়তে পারি না। আমাদের পা যেন পাথরের মত ভারি হয়ে গেঁথে রয়েছে মাটিতে। লোকটা হাতের ইশারা করে আমাদের ডাকে, মুখেও বলে, এসো ভেতরে এসো। তার পেছন পেছন আমরা যেন হিপনোটাইজড হয়ে চলতে থাকি। লতানে গোলাপে মোড়া লোহার দরজাটা ঠেলে, আরও একটু এগিয়ে তিনচার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে কাঠের দরজা খুলে বাড়িটার ভেতরে নিয়ে যায় সে আমাদের। ফের সে আমাদের প্রশ্ন করে, — তোমরা কি গান গাইতে জানো?ঘরের মধ্যে একটা পিয়ানো। সিনেমায় সাধারণত যেসব প্রকান্ড হাপরের মত ডালা খোলা পিয়ানোর সামনে বসে নায়ক নায়িকারা গান করে তেমন পিয়ানো এটা নয়, এটায় ডালার অংশটা বাদ, পরে জেনেছিলাম এগুলোকে ভার্টিকাল পিয়ানো বলে। ঘরে আমাদের তিনজনকে বাদ দিলে আরও মানুষ রয়েছে। চারজন কিশোর কিশোরী সেই পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গানের খাতা হাতে নিয়ে। এদের গান শুনেই পথ চলতে চলতে আমরা থমকে দাঁড়িয়েছিলাম বাড়িটার বাইরে। জানলা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে গানের মাস্টার মশাই তাই দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য এরা গান গাইছে না। ঘরে আরও কিছু বাদ্য যন্ত্র রয়েছে যেগুলোর নাম আমি জানিনা। মাস্টারমশাই ঘরের সবার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজের নাম বললেন আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচ, তারপর ছাত্রছাত্রীদের বললেন গান ধরতে। একজন পিয়ানোর সামনে টুলটায় বসে বাজাতে লাগল, বাকিরা দাঁড়িয়ে। গান শুরু হয়ে গেছে — রো ও দিনা… ভি লি কা ই য়া মাইয়া রো ও দি না.. (বাংলা করলে দাঁড়ায়, জন্মভূউমি… ম হা আন আমার জন্মভূউমি…)।
খুবই দেশাত্মবোধক গান, মহতী জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা জানানো হয়েছে গানের কথায়, কিন্তু বাপরে কী কণ্ঠ এদের, যেন অপেরা হচ্ছে! আওয়াজে কেঁপে যেতে হয়, তেমনি গম্ভীর সুর। কায়দা করে ঝুঁকে পড়ে গুনতে চেষ্টা করছি কতগুলো অক্টেভ ঐ পিয়ানোর। সাড়ে সাতটা অক্টেভ, অর্থাৎ সাতের বেশি আটের চেয়ে কম। দু কলি গাওয়া হলে তিনি হাতের ইশারা করতেই গান থেমে গেল। আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচ আমাদের দিকে ফিরে বললেন— গাও না, তোমরাও গাও এবার।
এখন ফেরেসালাম আমতা আমতা করে মুখ খুলল, — না মানে, আমরা তো গান গাইতে জানি না।
— গান সবাই জানে।
মাস্টারমশাই আমাদের গানের পরীক্ষা না নিয়ে ছাড়বেনই না। একটা টিপয়ের ওপর রাখা রয়েছে টিপট, কাপ, প্লেটে কয়েক টুকরো প্লাম কেক। সেই দিকে নজর ঘুরিয়ে দিয়ে লোভ দেখাতে লাগলেন, গান গাইলে প্লাম কেক দেবেন বলে। নিজেই আআআ করে একটা স্বর গেয়ে বলেন, এইটে গাও, আআআ। ফেরেসালাম মুখ খোলে না। আমি গেয়ে উঠি আআআ। উঁহু আরো জোরে, আরো জোরে গাও! উনি পেটের নাভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ওখান থেকে উঠে আসবে আওয়াজ, গাও, আবার গাও, এইতো, হচ্ছে হচ্ছে, হবে না মানে? এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ চলল। প্রথম দিকে একটু হাঁফিয়ে যাচ্ছিলাম, ক্রমশ কায়দাটা মনে হল একটু একটু ধরতে পারছি তবে এ জিনিস একদিনে হবার নয়, অনেক চেষ্টা লাগবে, অনেক রেওয়াজ করলে পরে পেট থেকে যেন উঠে আসবে আওয়াজ। উনি বলে দিলেন, প্রত্যেক মঙ্গল আর শুক্রবারে চলে আসবে বুঝেছ, এই নাও কেক, এই গানের ইস্কুলের নাম নারোদনাইয়া ফিলার্মোনিয়া, মনে থাকবে তো?মাস্টারমশাইকে একবাক্যে কথা দিয়ে দিই, নিশ্চয় আসব নিয়মিত। ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার পরে লক্ষ্য করি ফেরেসালামের মুখ গম্ভীর। ও এমনিতেই কথা বলে খুব কম। আমরা একই ক্লাসে পড়ি, ইথিওপিয়ার মেয়ে ফেরেসালাম। আরও একজন ইথিওপিয়ান আছে আমাদের ক্লাসে, সে ছেলে। আশেনাফি। আশেনাফি যেমন ছটফটে, ফেরেসালাম তেমনি শান্ত, একেবারে বিপরীত চরিত্র। কী হলো তোর বলতো? ও কিছু বলে না, কিছুক্ষণ পরে আবার বলি, বলবি তো কেন এমন চুপ মেরে রয়েছিস। ও শান্ত স্বরে বলে, —দেখলি কত দেরি হয়ে গেল, এখন হস্টেলে ফিরে কত কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।
—জানিনা আবার! এখন আমাদের পড়াশুনোর চাপ নেই বললেই হয়, কেবলই তো ভাষা শেখা, সন্ধেবেলা রান্নাবান্না গল্পগুজব হৈহল্লা ছাড়া কীই এমন দরকারি কাজ থাকে যে দেরি হলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে!
ও আর কোন কথা বলে না। আমরা পা চালিয়ে ফিরতে থাকি।আসলে আমরা বিকেলের দিকটায় বেরিয়েছিলাম একটু কেনাকাটি করতে। ফেরেসালামের কিনবার দরকার ছিল চুলে দেবার তেল, ও মাথায় মাখে ভিটামিন এডি অয়েল, যে তেল কৌটোর তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্প্রীংএর মত কুঁচকোনো আফ্রিকান চুলের যত্নের জন্য চাই ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টি জোগানো তেল। সেই স্পেশাল তেলের সন্ধানে অনেক দোকান ঘুরেছি, মনোমত কিছুই পাওয়া যায় নি, পথের ধারে ছোট ছোট রাসবেরির ঝোপে সদ্য ফল ধরেছে, রং তখনও সাদা, সেসবই তুলে তুলে খেতে খেতে ফিরছিলাম এ গলি সে গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ গান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, আলাপ হল আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচের সঙ্গে। এই দেশে, এই তাশখন্দ শহরে তো দেখতে দেখতে ছমাসের ওপর কেটে গেছে। বুক ঠুকে যেখানে সেখানে একা বেরোতে পারি, এখন আমরা গড়গড় করে রাশিয়ান বলতে পারি, পড়তে পারি, লিখতেও পারি মোটামুটি ভালই। শীতকাল প্রায় শেষই হতে চলল। জীবনে প্রথম তুষারপাত দেখেছি গত অক্টোবরে। তুষার জমে জমে সাদা করে ফেলেছিল শহরটাকে। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ। সেই বরফ গলে যায়, আবার পড়ে জমে গলে, ফের পড়ে, বাতাস পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠাণ্ডায় কাঁপি, অনভ্যস্থ পায়ে হাঁটতে গিয়ে জমে যাওয়া কঠিন বরফের ওপর পা হড়কে আছাড় খাই, মানিয়ে নিতে থাকি শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়ায়। শীতের ছুটি ছিল দু সপ্তাহের। ফ্যাকাল্টির নিয়ম মাফিক আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল স্যানাটোরিয়ামে, শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপরে। জায়গাটার নাম চির্চিক। সেখানে দুটো সপ্তাহ কেটেছে খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে। রোজ রাতে একটা করে সিনেমা, তার মধ্যে অধিকাংশই হরর ফিল্ম। সেই রাতের শোতে আমার জীবনের প্রথম দেখা হরর ফিল্মের নাম —ভী। নিকোলাই গোগোলের লেখা গল্প থেকে, বেশ পুরোনো ফিল্ম, ১৯৬৭ সালে তৈরি। কিন্তু তা হলে কী হবে? সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে স্যানাটোরিয়াম অবধি হেঁটে আসবার পথটা বনের মধ্যে দিয়ে। সে পথে কোনও বাতি নেই। অল্প স্বল্প চাঁদের আলো পড়ছে বরফের ওপর। পাঁচ ছজনের ছোট ছোট দল বানিয়ে আমরা বেয়ে উঠছি পাহাড়ি রাস্তা। রাত হয়ত বারোটা কি একটা। সিনেমার সব ডায়ালগ বুঝতে না পারলেও ভয়ের দৃশ্যগুলোর জন্য তো আর ভাষা জানতে হয় না। সেই থমথমে আবছা অন্ধকার পথে যেই কোনও গাছের ডাল থেকে ছপাৎ করে বেশ খানিকটা তুষার পড়ল, আমরা কেঁপে উঠছি সবাই অস্ফুট আর্তনাদে। টাটকা দৃশ্যগুলো মনে করতে না চাইলেও বেশি বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে কেউ আবার বদমায়েসি করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তখন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলেও ঘর থেকে বেরিয়ে একা একা টয়লেট যেতে পারি না। আমার রুমমেটদেরও একই দশা। শোবার ঘরগুলো পরপর সারি দেওয়া লম্বা করিডোরে, সেখানে সারারাত জ্বলছে খুব অল্প পাওয়ারের লাইট, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যায় না ঐ আলোয়। করিডোরে একটু পরে পরেই লম্বা লম্বা কাচের জানলা, ছোট ছোট গোল টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে নানারকমের লিলি ফুল। সেই সব পেরিয়ে যেতে হবে টয়লেট। লিলি ফুল দেখলেই মনে পড়ে যায় হরর ফিল্মের সেই সীনটার কথা যেখানে গির্জাঘরের বেদীতে রাখা সুন্দরী মেয়েটার মৃতদেহের কাছে হুবহু এই রকমেরই সাদা সাদা লিলি। মেয়েটার মাথায় হলুদ-সাদা ফুলের মুকুট পরানো। হিরো যখন একা একা বেদীটার কাছে গিয়ে মেয়েটার মুখের দিকে ঝুঁকে কীসব বলছিল, মৃত মেয়েটার বন্ধ দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল, যা মুহূর্তের মধ্যে বনে গেছল রক্ত! ওরে বাবারে! আমি সারারাত জেগে কাটিয়ে দেব কিন্তু ঐ করিডোর পেরিয়ে টয়লেট যাওয়া অসম্ভব। ঘরের মধ্যে আমরা কেউ কাউকে বলতে পারিনা যে সবাই জেগে রয়েছি, সবারই হিসি পেয়েছে। ঐ দুটো সপ্তাহেই আমরা সবাই সবার বন্ধু হয়ে যাই, সেই স্যানাটোরিয়ামেই। সেখানেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করে ফেলেছি একটা সরু নদী। পরে জানতে পারি নদীটার নামও জায়গাটার নামে— চির্চিক। অত ঠাণ্ডাতেও নদীটার কাছে গিয়ে কান পাতলে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সবটা জমে যায় নি, বরফের তলা দিয়ে কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছিল, ঝরঝর করে লাফিয়ে পড়ছিল নদীবক্ষের নীচের দিকের পাথরগুলোর ওপর। চুপ করে দেখবার মত ধৈর্য বা সময় হাতে থাকত না। আমাদের দলটা তখন দাঁড়িয়ে থাকবার মত বিরক্তিকর কাজ করত না, হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতাম আরও আকর্ষণীয় কিছু। সেই দলে কি ফেরেসালাম একবারও থাকেনি? মনে পড়ে না ঠিক করে। আজ নাহয় বাবা তুই চুলের তেল পাস নি দোকানে, তা বলে অত মুষড়ে পড়বার কী আছে, অ্যাঁ?
মঙ্গল এবং শুক্র, বার দুটো বিলক্ষণ মনে আছে। কদিন পেরোতেই বিকেলবেলা ক্লাসের পর ফেরেসালামের ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছি। ঘরে ওর তখন দুজন রুমমেট এবং একটা অচেনা ছেলে। ফেরেসালাম এক ডেচকি স্প্যাগেটিসেদ্ধ নিয়ে ঢুকল মিনিটখানেকের মধ্যেই। টেবিলের ওপর নানারকম নাম না জানা মশলা। সেইসব মশলা মেশাতে শুরু করল গরম স্প্যাগেটিতে। আমাকে বলল, তুইও খাবি কিন্তু।
— খাব কী রে এখন, গানের ইস্কুলে যাবি না!
কোনও উত্তর দেয় না সে। রুমমেট দুজনের একজন পানামার মেয়ে, ড্যানেলিস রোমানো। অন্য মেয়েটা ইথিওপিয়ার, যে সেই অচেনা ছেলেটার সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে বসে আছে, আমাকে দেখে একটু হেসেছিল যখন ঘরে ঢুকেছিলাম। আমি আবার তাড়া দিই ফেরেসালামকে, পাঁচটার মধ্যে পৌঁছতে হবে তো, তোর রান্নাবান্না কতটা বাকি? শান্ত হয়ে সে উত্তর দেয়, আজ যেতে পারছি না, আজ আমার রান্না করার ডিউটি। অদ্ভুত তো! আমি রেগে যাই, বিরক্ত হই। তবু বলি, পরেরদিন অন্য কাউকে ডিউটি দিবি। ও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি ওর রুমমেট ও সেই ছেলেটি চুমু খেতে ব্যস্ত, ড্যানেলিস আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে।প্রথম শীত ১৯৮৫ ( আসলে, জীবনের উষ্ণতম দশটি শীতের প্রথমটি)। পেছনের সারিতে বাঁদিক থেকে – আমজাদ, জামিলা, গাসান, করিমা, আশেন্নাফি, ফেরেসালাম, আমি, (বাকিদের নাম মনে পড়ছে না)।সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে – আব্দুররজ্জাক, মানুয়েল, (নাম মনে নেই) ও কেনেত।রাস্তায় বেরিয়ে খেয়াল হয়, আরে, এ কদিন তো গানটা প্র্যাক্টিস করা হয় নি, গলাও একদম সাধা হয় নি, সেই আআআ করে একেবারে শরীরের ভেতর থেকে আওয়াজ বের করা। বেমালুম ভুলেই গেছলাম। যদি মাস্টারমশাই বুঝতে পেরে যান যে ফাঁকি দিয়েছি! কী আর করা যাবে, যা হবার হবে, দৌড়তে দৌড়তে যাই, রাস্তাটা ভালমত মনেও পড়ে না, কিন্তু জেদ চেপে গেছে লতানে গোলাপে মোড়া সেই লোহার গেট খুঁজে বের করবই। সেদিন আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচকে একটু দুর্বল কেমন যেন অসুস্থ মনে হয়, তবু আমাদের গানের ক্লাস, গলা সাধা সবই হয়। ঐ চারজন ছাত্রছাত্রী অদ্ভুত ভাল গায়, ওরা সবাই কনসেরভাতরিয়াতে ভর্তি হবে বলে তৈরী হচ্ছে। কনসেরভাতরিয়া হচ্ছে মিউজিকের ইউনিভার্সিটি। ক্লাসের শেষে চুপিচুপি ওঁকে জিগ্যেস করি, কত মাইনে দিতে হবে এখানে? উনি হো হো করে হেসে বলেন, — কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, যাও বাড়ি যাও এখন।
বাড়ি মানে হস্টেল অবশ্য তখনই ফিরি না। আরো অলি গলি হাঁটি। আমাকে তো আর ঘরে ফিরে রান্না করতে হয় না। যখন খুশি খাই, যা বানাতে পারি তাই ই খাই। ভাগ্যিস ঐ ইন্ডিয়ান দুজনের সঙ্গে খাই না, তাহলে পালা করে করে রান্নার ডিউটি পড়ত। গানের ইস্কুলের সরু গলিটা এঁকে বেঁকে গিয়ে পড়েছে একটা সরু রাস্তার ওপরে। এ পথে কোনও দিন আসিনি আগে। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার! সরু রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। একদম চওড়া নয়, সরু মত নদী। দেখলে মনে হবে নালা বুঝি। না, এ নালা নয়। একটু দূরেই রয়েছে একটা ছোট্ট সেতু, পায়ে হেঁটে পার হবার সেতু। নদীর দুপারেই গাছ। কী নাম এই নদীর? পথে লোকজন তেমন নেই, মানে প্রাপ্তবয়স্ক লোক নেই। কতগুলো বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটে ছুটে খেলছে একটু দূরে। ওদের জিজ্ঞেস করা যাবে না। এত সুন্দর একটা নদী ছিল এত কাছে, অথচ তা জানতামই না এতদিন? একটু হেঁটে এগিয়ে একজন বুড়িকে দেখতে পাই। বলি,— নমস্কার, মাফ করবেন, একটা কথা জানতে চাই, কী নাম এই নদীর?
বুড়ি সম্ভবত রাশিয়ান ভাল জানে না, তবু ভুরু কুঁচকে শুনে বুঝে ফেলে আমার প্রশ্ন। একগাল হেসে নদীটার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলে— চির্চিক।
জানতে পারিনি যে সেদিনই ছিল আমার শেষ গানের ক্লাস। নদী আবিষ্কারের সঙ্গে এও বুঝে ফেলেছিলাম যে পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই গোল। যে নদীকে তুমি দুমাস আগে দেখে এসেছ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যেতে, সে ই চুপিচুপি এসে উপস্থিত নির্জন রাস্তার ধারে। কেউ তোমাকে আগে থেকে বলে দেয় নি যে এই পথ ধরে সিধে হেঁটে গেলেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় আমার সঙ্গে আর কেউ রইল না সাক্ষী হয়ে। তা হোক গে, আকাশের আলো যখন একেবারে পড়ে যায় নি তখন পিছুটানই বা কীসের? আরেকটু হেঁটে দেখা যাক আরও কী কী আছে এই নদীর ধার ঘেঁষে। ডানহাতে নদীটাকে রেখে চলতে থাকি। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা। বাঁদিকে গাছপালার আড়ালে বাড়ি টাড়ি রয়েছে। আরেকটু এগোলে রাস্তা একটু সরু হয়ে যায়, সরু রাস্তা এসে পড়ে একটা বাগানের মত জায়গায়। বাগান মানেই এমন নয় যে পথ ওখানেই শেষ, বাগান পেরিয়ে গেলে ফের রাস্তা পাওয়া যাবে দেখা যাচ্ছে। নানানরঙের গোলাপের গাছ দিয়ে বাগানটা খুব সুন্দর করে সাজানো। ফুটে রয়েছে আরও অনেক ফুল যাদের নাম আমি জানিনা। আর রয়েছে কিছু গাছ, যাতে ফুল নেই। এমনি একটা গাছের পাতা দেখে চমকে উঠতে হয়, সে পাতা সবুজ নয়, হালকা নীলচে আভা। যদিও এপাশটা ছায়া ছায়া মত, তবুও সবুজকে নীল ভেবে ভুল করবার মত খারাপ চোখ তো আমার নয়। হাতে ধরে দেখি, সত্যিই নীল। একটু মোটা, ফোলাফোলা মত পাতা, পাথরকুচি পাতার মত অনেকটা। যাক, এটাও আবিষ্কার করা হয়ে গেল। সঙ্গে কেউ আসেনি ভালই হয়েছে। নিজের ইচ্ছে মত হাঁটব। বাগানটা আসলে একটা মস্ত বাড়ির সঙ্গে জোড়া। একটা দরজাও দেখা যাচ্ছে বাঁদিকে, দরজার পাশে পাথরের ফলক। এগিয়ে গিয়ে পড়তে চেষ্টা করি কী লেখা রয়েছে। পরপর দুটো ভাষায় লেখা, একপাশে উজবেক ভাষায়, অন্যপাশে রাশিয়ানে। ফলকটা পড়ে নিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না, ঠিক পড়ছি তো? এসব কী হচ্ছে এই বিকেল থেকে! আবার পড়ি। এটাই তো থিয়েটারের ইনস্টিটিউট! আমি তো এখানেই থিয়েটার শিখতে চাই, এটাই তো আমার আসল পরিকল্পনা। যে কথা আমার ক্লাস টিচার ছাড়া কেউ জানে না, সেইটের জন্য আমাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে এবার। আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই না, আমি অভিনয় শিখতে চাই। আমি অভিনেত্রী হব। বুকের ভেতরে ধুকপুক করে। মাথা তুলে বাড়িটার দিকে তাকাই এবার ভাল করে, এই গেটটা হচ্ছে পেছনের গেট, সামনের দিকেও গেট থাকবে, সেই গেটে যাবার জন্য নিশ্চয় অন্য দিকে রাস্তা আছে। না, আজ এইটুকুই থাক। নীল গাছগুলো পেরিয়ে বাগানের শেষে অন্য রাস্তাটা ধরে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি সেদিকে নদী দূরে সরে যাচ্ছে, এই রাস্তাও সোজা চলেছে বড়ো রাস্তায়, যে দিকে গেলে বিশাগাচের ট্রলিবাস ধরা যাবে।
পরের দিনও ফেরেসালাম যেতে চায়নি আমার সঙ্গে। সরাসরি বলে দিল, কী লাভ আছে ওখানে গিয়ে, সে তো ডাক্তারি পড়বে বলে এসেছে এদেশে, ঐ ভূতুড়ে পরিবেশ, ঐ পাগলাটে গানের মাস্টার, এসব তার সুবিধের ঠেকে নি। একা একাই চলে গেলাম। লতানে গোলাপে মোড়া লোহার গেট আজ বন্ধ। উঁকি ঝুকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলাম ভেতরে আলো জ্বলে কিনা, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি গানের আওয়াজ একটুও যদি শুনতে পাই। সব নিস্তব্ধ। কেউ কোত্থাও নেই যে জিগ্যেস করব। আবার কি আসব পরের দিন? মাস্টারমশাই কি অসুস্থ? হতেও পারে। বেশ বলেছিল ফেরেসালাম, ভূতুড়ে পরিবেশ। ভূতই তো। ভূতের রাজাও বলা যায়। ভূতের রাজার আশীর্বাদে এই গুপী গাইনটার হেঁড়ে গলার যদি কিছুটা উন্নতি হতো! কিন্তু বরাতে নেই।বিশাগাচের মোড়ে মস্ত একটা বাজার আছে। বেশ পুরোনো বাজারটা। সন্ধে হলে নিয়ম মত বাজার বন্ধ হয়ে যায়, যেমন আর সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতেই। বিশাগাচের মোড়ে তাই বাজার বন্ধ হবার ব্যস্ততা। কম করে জনা তিরিশেক লোক ব্যস্ততার সঙ্গে বাজার করে বেরিয়ে আসছে বাসস্টপের দিকে। সবার হাতেই কম বেশি মালপত্তর। তবে মূল বাজারটা বন্ধ হলেও বিক্রিবাট্টা এখনি পুরোপুরি বন্ধ হবার নয়। বাজারের সামনে ফুটপাথে ছোট ছোট পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেছে কিছু দোকানি। বাজার বন্ধ হবার পরেই এদের ব্যবসা শুরু হয়। কেউ বিক্রি করছে ফুল, এক বুড়ির টুকরিতে রয়েছে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা গরম সামসা। বাজারের গেটের পাশে ছুরি শান দেবার দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল এইমাত্র। পরপর এসে উপস্থিত হচ্ছে গাজরের স্যালাদ বিক্রেতা, কেউ বেচছে ঠোঙায় ভরে সদ্য রোস্ট করা গরম গরম সূর্যমুখীর বীজ। আমি ঝুঁকে পড়েছি বিশ পয়সার সামসা কিনতে। ভেড়ার মাংস আর চর্বি দেওয়া গোল প্যাটিসের মত দেখতে এই সামসা, বুড়ি দরদ দিয়ে মশলার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল সামসার ওপর। দুতিনটে ছেলেকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করছে। ফাঁকা ট্যাক্সি নেই তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে, কোন গাড়ি কাছ দিয়ে গেলেই হাত তুলছে থামানোর চেষ্টায়। ওদের ছটফটে ভাব দেখেই আরেকটু নজর করে দেখলাম এরা তো সব আমাদের হস্টেলের ছেলে। সব কটার নাম জানিনা তবে একজন আমার ক্লাসমেট, ইরাকের ছেলে গাসান, গাসান আবিদ কাতার। আমাকে দেখতে পেয়েও ওরা যেন চিনতে চায় না। থেমে যায় একটা গাড়ি, ওরা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে গাড়িটার মধ্যে। গাড়ি ছেড়ে দেয়, জায়গাটা ভরে থাকে সেন্টের গন্ধে। জানি ওরা কোথায় চলেছে এত তাড়াহুড়ো করে। একদম সঠিক ঠিকানাটা বলতে পারব না যদিও, ওরা গেল কোনও একটা দামি রেস্টুরেন্টে, সেখানে গিয়ে খানাপিনা করবে নাচবে, রেস্টুরেন্টের গায়কের হাতে এক মুঠো নোট গুঁজে দিয়ে পছন্দের গান গাওয়াবে, ইচ্ছুক মেয়েদের ডেকে আনবে নিজেদের টেবিলে, মাতাল হয়ে অনেক রাতে টলতে টলতে ফিরে আসবে হস্টেলে। গাসান অর্ধেক দিন ক্লাসে আসে না, ঘুম থেকেই উঠতে পারে না সকালে। আশেনাফির সঙ্গে একদিন কী একটা ব্যাপারে কথা কাটাকাটির পর হাতাহাতি মারামারি হচ্ছিল, তখন এসব কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল আশেনাফি। গাসানও কম যায় না, খোঁটা দিয়েছিল আশেনাফিকে গরীবের দেশ ইথিওপিয়া বলে, বলেছিল, তোরা তো খেতেই পাস না, তোদের দেশে না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মরছে লোক। পকেট থেকে কয়েকটা রুবলের নোট বের করে বলেছিল, ডোনেশান চাই? মারামারি থেমে যায় এরপর। আশেনাফি চেঁচিয়ে জবাব দিতে পারেনি আর, কেবল ফ্যাকাশে মুখটা হাসি হাসি করবার মত করে আস্তে আস্তে বলছিল, ওদের তো তেল বেচে এত টাকা, যেদিন সব তেল ফুরিয়ে যাবে সেদিন টেরটি পাবে। সমর্থন পাবার প্রত্যাশায় আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল সে। আমরা চুপ করেছিলাম। কতটা তেল, সে তেল বেচতে বেচতে কত দিনে ফুরোবে এবং ততদিন আমরা বেঁচে থাকব কি না এসব তো এখনই হিসেব করা যাচ্ছে না, তাই চুপ করে থাকা। তবু সে নিজেকে ওভাবেই সান্ত্বনা দেয়।মাঝের তিনজন হচ্ছে ফেরেসালাম, আশেন্নাফি ও আমি।
গাসানরা ট্যাক্সি করে চলে যাবার পরে আর ট্রলিবাস নিতে ইচ্ছে করে না। ডান হাতে পড়ে কমসামোলসকাইয়া ওজেরা — বড়ো একটা লেক। আর খুব বেশি হাঁটতে হবে না, দুটো স্টপ। আমাদের হস্টেল এই রাস্তার ন নম্বর বাড়ি। ইউক্রেনের বীর বাগদান হ্মেলনিৎসের নামে এই রাস্তার নাম। আচ্ছা মধ্য এশিয়ার এই মরুদ্যানে সুদূর ইয়োরোপের বীরপুরুষ কী করেছিল যে তার নামে এই রাস্তা? উজবেকদের মধ্যে বিখ্যাত লোকের এতই অভাব? এইটে জিগ্যেস করতে হবে তো কাল ক্লাস টিচার মায়া আবিদোভনা শারিপভাকে। উঁহু শারিপভাকে নয়, জিগ্যেস করব ইতিহাসের শিক্ষক ভ্লাদলেন উসমানোভিচ ইউসুপভকে। অল্প পথ বাকি। সামসাটুকু খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে শেষ করবার আগেই এসে পড়বে হস্টেলের দরজা।আমাদের হস্টেল থেকে বেরিয়েই রাস্তায়, যিনি ছবির প্রিন্ট আউট বানিয়েছিলেন, তিনি উল্টো প্রিন্ট আউট করে ফেলেছেন ভুল করে। কাজেই ডানদিক গুলো বাঁদিক হয়ে গেছে আর বাঁদিকগুলো ডানদিক।
চলবে…
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০৮735831
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০৮735831- ইলেকশান১৯৮৫র সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তাশখন্দে পৌঁছনোর পরে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। অক্টোবরের শুরুতেই পড়েছিল ইলেকশানের তারিখ— ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রত্যেক ইন্ডিয়ানের জন্য একটা করে ভোট। প্রার্থী প্রথম দিকে ছিল দুজন, কদিন পরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল তিনজনে। প্রত্যেকের ভোট জরুরি, একটা ভোটের এদিক ওদিক হলেও ইলেকশানের ফলাফল পাল্টে যেতে পারে। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তিন পক্ষ থেকে তুমুল ক্যাম্পেনিং চলছে। শহরের মধ্যিখানে আমাদের হস্টেলে মাত্র তিনজন ইন্ডিয়ান থাকলেও প্রার্থীরা এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা দলে দলে ক্রমাগত হানা দিতে লাগল আমার ঘরে। অনুরোধ করা, বিপক্ষের প্রার্থীদের নামে কুৎসা রটানো, সমস্তই চলতে লাগল পুরোদমে। সকলের বক্তব্যই শুনছি, সবাইকেই আশ্বাস দিচ্ছি ভোট দেবার। জীবনে এই প্রথম ভোট দেব। ইন্ডিয়ায় থাকতে ভোট দেবার বয়স ছিল না, ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি তখনও। তখনও ইণ্ডিয়ায় একুশ বছর বয়স না হলে ভোটার লিস্টে নাম উঠত না। ভোটাধিকারপ্রাপ্তদের তর্জনীতে কালো দাগ দেখে ভাবতাম কবে আমিও ওরকম দাগ নিয়ে গর্বের সঙ্গে ঘুরতে পারব, ও দাগের স্টেটাসই আলাদা।এখানে ভারতীয় পাসপোর্টের জোরেই আমার ভোটাধিকার তৈরী হয়ে গেছে। আমাদের হস্টেলের বাকি দুজন ইন্ডিয়ান ভোট দেবে বিহারের ক্যান্ডিডেট রঞ্জন কুমারকে। রঞ্জন কুমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র, সে থাকে শহরের এক প্রান্তে ভুজগারাদোক নামক একটা জায়গায় একুশ নম্বর হস্টেলে। ঐ অঞ্চলে একজন খুব সিনিয়র বাঙালি আছেন, তিনি দীপুদা নামেই পরিচিত। রঞ্জন কুমার দীপুদাকেও বিশেষভাবে চেনে। দীপুদার হস্টেলে সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার পার্টি আছে, সে আমায় নেমন্তন্ন করে গেল। বলল, চিন্তা নেই কেউ একজন এসে আমায় নিয়ে যাবে দীপুদার হস্টেলে। যে সে রবিবার নয়, সেদিন পঁচিশ ঘন্টায় এক দিন*। বাকি দুজন ক্যান্ডিডেটের একজন তামিলনাডুর ছেলে রবিশংকর, সে ও মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সে ও একুশ নম্বর হস্টেল, এবং তিন নম্বর ক্যান্ডিডেট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বলবন্ত সিং, দিল্লির ছেলে, হস্টেল নং চোদ্দ।
বলবন্তের ক্যারাকটার সার্টিফিকেট ভাল নয় সে খবর রঞ্জন কুমার আগেই জানিয়ে দিয়েছে। সে মদখোর এবং মাতলামির রেকর্ড খুবই বাজে, নিয়মিত ভাংচুর করে, পড়াশোনায়ও সুবিধের নয়, ইত্যাদি। বলবন্তের দল রঞ্জনের বিরুদ্ধে বলে গেছে যে রঞ্জন এক বছর ফেল করে রিপিট করেছে, সে কমিউনিস্ট পার্টির কোটায় পড়তে এসেছে, ইত্যাদি প্রভৃতি। রবিশংকরের চেলাচামুণ্ডা সংখ্যায় কম, ছেলেটাকে দেখে বাকি দুজনের তুলনায় ভদ্র বলে মনে হল, মনে মনে ঠিক করলাম রবিশংকরকেই ভোটটা দেব। তবে রঞ্জন যেরকম উৎসাহ নিয়ে আমাকে দীপুদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছে, পরে হয়ত রঞ্জনকেই ভোটটা দিয়ে দিতে পারি।সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার ছিল ডে-লাইট সেভিং এর দিন। ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দেবার ব্যাপার সেই প্রথম জানলাম। সকাল দশটা থেকেই সেজেগুজে রেডি হয়ে আছি কখন আমায় নিতে আসবে। রঞ্জন নিজেই এল। ট্যাক্সি করে নিয়ে চলল ষোলো নম্বর হস্টেলের দিকে। যাবার পথে সে অনেক কিছু জানাচ্ছে আমাকে, কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গে মিশব না, ভারতীয় মেয়েদের ভদ্রতা নম্রতা আব্রু সম্মান এসব কতটা জরুরী এ দেশে, দেশের মেয়েদের চালচলনই বলে দেয় দেশের ঐতিহ্য, আরও অনেক কিছু, যেমন, কী করে রেসপেক্ট পেতে হয়, ইত্যাদি। সব কথা আমার কানে পুরোপুরি ঢুকছেও না। আমি আনন্দে ডগোমগো যে আজ বাংলায় কথা বলতে পারব। দীপুদার বাড়ি যাচ্ছি, মানে ঠিক বাড়ি নয় যদিও, হস্টেল। তা হলেও একটা সিনিয়র দাদা বলে কথা। রঞ্জন কানের কাছে ভ্যাড় ভ্যাড় করছে করুক, উঃ বাবা আর কতক্ষণ বাকি ষোলোনম্বরে পৌঁছতে!দীপুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হস্টেলের গেটের মুখটায়— এক হাতে দইয়ের বোতল (হুবহু হরিণঘাটার দুধের বোতলের মত দেখতে), অন্য হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার বছর দুয়েকের মেয়ে ইন্দিরা। শুনলাম বৌদি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে অ্যাডমিটেড, সদ্যোজাত ছেলের জন্ডিস হয়েছে। উনি হাসপাতালে গিয়ে বৌদিকে দইটুকু দিয়েই ফিরে আসবেন জলদি, সংক্রামক রোগের হাসপাতালে এমনিতেও রোগীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করবার ব্যবস্থা নেই। তবে চিন্তা নেই, অতিথিরা অনেকেই এসে গেছে, সোজা চারতলায় গিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে গল্প গুজবে যোগ দিতে পারি।
এদেশে যত ইন্ডিয়ানের ঘরে মেয়ে জন্মায় সবার নাম এক ধারসে ইন্দিরা রাখে। মেডিক্যালে পড়ে বর বৌ শিবকুমার ও উর্মিলা, তাদের মেয়ের নামও ইন্দিরা। নামের কি এতটাই আকাল পড়েছে?
চারতলায় লিফট থেকে বেরোতে না বেরোতেই গমগম আওয়াজে মালুম হয় পার্টি শুরু হয়ে গেছে। এই টাইপের হস্টেলগুলো নতলা হলেও প্রত্যেক তলায় চারটে করে বড়ো ঘর এবং আটটা ছোটছোট ঘর। এছাড়া চারটে টয়লেট একটা স্টোররুম এবং তার বিপরীতে বড়োসড়ো একটা রান্নাঘর। প্রত্যেক তলায় দুটো কমন ব্যালকনির একটা রয়েছে সিঁড়ি তথা লিফটের দিকে, অন্যটা রান্নাঘর সংলগ্ন। রান্নাঘরের দিক থেকেই আড্ডার আওয়াজ আসছে, গোটা দশবারো ছাত্র সেখানে বিয়ারের বোতল হাতে ঘোরাঘুরি করছে, একজন মধ্যবয়সী ভারতীয় ভদ্রমহিলা কোমরে আঁচল বেঁধে দুধ জ্বাল দিতে ব্যস্ত। আমি সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত ভ্যানিলা কাস্টার্ড তৈরী হবে, তাই দুধ অল্প আঁচে ঘন করা হচ্ছে। ভদ্রমহিলা কলকাতার বাঙালি, নাম শিপ্রা, তিনি ভারত সরকারের কোন একটা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। গভর্নমেন্ট থেকেই ওঁকে মাস দুয়েকের জন্য কীসব কাজে এখানে পাঠিয়েছে, থাকছেন তাশখন্দের নামকরা হোটেল গাসতিনিৎসা তাশখন্দ -এ, নিজের কাজের ব্যাপারে উনি খুব একটা খুলে কিছু বলতে চান না। ওঁর থাকার মেয়াদ প্রায় শেষ, আগামিকালই বেড়াতে যাচ্ছেন রাশিয়ায় কৃষ্ণসাগরের তীরে সোচি-তে। সেখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে তাশখন্দে ফিরবার পরেই বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠবে। একেবারে কাকতালীয়ভাবে রাস্তায় দীপুদার সঙ্গে ভাগ্যিস ওঁর দেখা হয়ে গেছল, তাই ওঁকে নেমন্তন্ন করে আনা সম্ভব হয়েছে। সবাই বিয়ার খাচ্ছে দেখে আমিও একটা বোতল তুলে নিতে গিয়ে তুষারের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তুষার আমারই সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছে, যদিও এ শহরে ওর এবং আমার হস্টেল আলাদা। ও বলল— নিবি নাকি একটা? খাবি? খেতেই পারিস, তবে এতসব লোকজন রয়েছে তো, কে কী মনে করবে, বুঝতেই পারছিস, অন্য কোন সময়ে আলাদা করে খাস, আসলে এখানকার পাবলিক তো, হঠাৎ করে কে কী কমেন্ট করে দেবে…।
রান্নাঘরের মুখোমুখি স্টোররুমটায় ঢুকলাম। ওটাই দীপুদার বৈঠকখানা। নড়বড়ে শেলফে পুরোনো বাসন, টেবিলের নীচে বেশ কিছু ছোটছোট আরশোলা, টেবিলের ওপর রাখা আছে দুটো গোটা শুকনো মাছ। নোনা মাছ, চ্যাপ্টা মত, আঁশ টাস শুদ্ধই শুকোনো হয়েছে। এগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিয়ারের সঙ্গে খেতে হয় টাকনা হিসেবে। আপাতত দুটো মাছই অক্ষত, কেউ হাত লাগায় নি। সবাই খোলা ভেঙে ভেঙে চিনেবাদাম খাচ্ছে। রান্নাঘর এবং বৈঠকখানার মধ্যবর্তী করিডোরের দেয়াল ঘেঁষে একটা প্লাস্টিকের কমোড, শিশুদের ব্যবহারের জন্য। সম্ভবত ইন্দিরা ওটা ব্যবহার করে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই দীপুদা ফিরে এলেন। ইন্দিরা বাংলা বলে না, রাশিয়ান বলে, তাও উত্তমপুরুষে কিছু বলতে শেখেনি, সমস্তই প্রথম পুরুষে। সে কাঁদোকাঁদো স্বরে ঘোষণা করল, “ইন্দিরা পায়খানা করতে চায়”। বেগতিক দেখে আমি তাকে কমোডে বসিয়ে দিলাম। দীপুদার ঘরটার দিকে কেউ যাচ্ছে না, অন্য একটা ফাঁকা ঘরে গোটা দুয়েক টেবিল পাশাপাশি জুড়ে বড়ো ডাইনিং টেবিলের আকার দেওয়া হয়েছে, টেবিলক্লথের অভাবে সেটা ফুল ফুল ডিজাইনের বেডকভার দিয়ে ঢাকা। কাস্টার্ড কতটা কী হয়েছে জানা গেল না, কিন্তু প্রচণ্ড ঝাল দেওয়া ভেড়ার মাংসের ঝোল রান্না করেছিল কামরুজ্জমান। কামরু কে এই প্রথম দেখলাম, সে ডাক্তারির ছাত্র। কে একজন মাংসের ঝোল গড়ানো গরম ডেচকিটা তাড়াতাড়ি বেডকভারের ওপর এনে রাখল। চিনেমাটির প্লেটে প্লেটে ভাত পরিবেশন হয়ে যেতেই সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেচকির ওপর। শিপ্রাদি নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে নীচু স্বরে দীপুদাকে বললেন, আহা সত্যিইতো অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, দুটো বেজে গেছে, তার মানে অন্য দিন হলে তো তিনটেই হতো, তাইনা?
খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যাবার পর শিপ্রাদিকে আর আটকে রাখা গেল না, উনি চলে যাবেনই, অনেক বাঁধা ছাদার কাজ বাকি পড়ে আছে হোটেলে। ইন্ডিয়ান ছাত্ররা বিয়ার এবং ভরপেট মাংসভাত খেয়ে ইতিউতি বসে বসে ঝিমোচ্ছে, কয়েকজন কেটেও পড়েছে। অগত্যা দীপুদা শিপ্রাদিকে হোটেলে পৌঁছে দিতে ছুটলেন। ইন্দিরার দেখভাল করতে রইলাম আমি, সেও খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।
লোকসংখ্যা খানিকটা কমে গেলেও সন্ধেবেলা পার্টি আবার টগবগিয়ে উঠল। এখন আর শিপ্রাদি নেই, তাই ছেলেরা স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারছে, এখন আর খিস্তি টিস্তি দেবার আগে আগুপিছু দেখে ব্রেক কষবার প্রয়োজন হবে না। অস্থায়ী ডাইনিং রুম ছেড়ে সেই ঘুপচি স্টোররুমে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে শুরু হয়ে গেল গোপন আলোচনা। আসন্ন নির্বাচনে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রার্থী বলবন্ত সিং কে হারানোর জন্য পরামর্শ করা দরকার। ঘরের কোণে রাখা একটা নোংরা মত বালতির ভেতর থেকে বেরোলো দু বোতল সস্তার ভোদকা, এ সমস্ত ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনাসভায় অল্প একটু মদ টদ না থাকলে পরিস্থিতির গুরুত্ব হালকা হয়ে যায়। ছোট ছোট গ্লাসে নীট মদ। সেই মাছ দুটোকে আগেই খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে বাক্স প্যাটরার পেছনে চালান করে দেওয়া হয়েছে, মদের বোতল ও গ্লাস রাখবার জন্য টেবিলের ওপর যথেষ্ট জায়গা চাই।
যাদের ভোট রঞ্জন কুমারের দিকে টেনে আনা যেতে পারে তাদের একটা লিস্ট তৈরী হয়ে গেল মুখে মুখে। ওরা ধরেই রেখেছে যে আমার ভোটটা পাবে। তিনজন আউটকাস্ট টাইপের ভোটারের নাম সসঙ্কোচে উচ্চারিত হল, দরকার হলে তাদের কাছে গিয়েও দরবার করতে হবে, তিনজনই মহিলা। কী কী অপরাধে তাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা সরাসরি জিগ্যেস করাটা শোভন হয় না, চুপ করে থাকলে ধীরে ধীরে ওদের কথাবার্তা আলোচনা থেকে আপনি জানা যাবে। তিনজনের একজন হচ্ছে মীনাক্ষি, ওর একঘরে হবার কারণ আমার জানা, — ‘রান্ডি’ টাইপ। বাকি দুজনও কি একই গোত্রের? উঁহু, সম্ভবত না। তাদের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতেই সবচেয়ে বেশি ঘাবড়াচ্ছে রঞ্জন, একজনের নাম মিসেস খান, ডক্টরেট করছেন সাহিত্যের ওপর, তাঁর স্বামী পাকিস্তানি; অন্য জন মীরা, তিনি নিজে ডাক্তারি পাশ করে গবেষণারত। মীরার স্বামীও ডাক্তারিতে গবেষণা করছেন, বাংলাদেশি মুসলমান, নাম সামদানি। এই দুজনের কাছে যেতে রঞ্জনের সঙ্কোচ। ঠিক সঙ্কোচ নয়, ভয়। মিস্টার খান কি ইন্ডিয়ান ছোকরাদের ঘরে ঢুকতে দেবে? কাশ্মীরের মানচিত্র নিয়ে কদিন আগেই একুশ নম্বর হস্টেলে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান মারপিট হয়ে গেছে, প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছিল সেখানে। এমতাবস্থায় মাথা নীচু করে মিসেস খানের কাছে গিয়ে ভোট চাওয়া, যে মেয়ে অবিশ্বাসী ‘গদ্দার’, যে কিনা পাকিস্তানি ছেলেকে বিয়ে করবার মত জঘন্য কাজ করেছে, শেষে তার কাছে একটা ভোটের জন্য হাত পাততে হবে? দীপুদা রঞ্জনকে আরেকটু মদ ঢেলে দেন, সে এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে ঘোলা চোখে দীপুদার দিকে তাকায়, ক্রমশ সেই চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে। বেশ কিছক্ষণ সবাই চুপ। সিচুয়েশন খুব সিরিয়াস। দীপুদা ধীরে ধীরে বলেন, পোলিটিক্সে ইমোশানকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজ করতে হয় রঞ্জন, চেষ্টা কর, তুমি পারবে, পারতে তোমাকে হবেই, তুমি বাঘের বাচ্চা, তোমার চেয়ে বেটার এলিজিবল ক্যান্ডিডেট কে আছে আমাকে দেখাও, আমি মেনে নেব।রাত বাড়ছে। কিন্তু গোপন আলোচনাসভা ভাঙবার কোন লক্ষন তখনও দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে ইন্দিরাকে ঘুম থেকে তুলে কৌটোর বেবিফুড খাইয়ে দিলেন দীপুদা। ইতোমধ্যে আরেকজন কন্ট্রোভার্শিয়াল ভোটারের নাম উঠে এসেছে লিস্টিতে, সে মেয়ে নয়, সে নাসির। ডাক্তারির ছাত্র, সেকেন্ড ইয়ার। নাসিরের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব বারবার দেখা গেছে, যে কোন অনুষ্ঠানে তাকে ডাকা হলে সে নাকি নতুনদের কাছে নিজের পরিচয় দেয় এরকমভাবে— আই অ্যাম নাসির, ফ্রম কাশ্মীর। ওর এই ঔদ্ধত্ব মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। ব্যাটা এদেশে এসেছিস ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে, আর পরিচয় দিচ্ছিস নিজেকে কাশ্মীরি বলে?
আবার মেজাজ গরম হয়ে যায় সবার। ১৯৮৫ সাল। কী এমন সমস্যা হচ্ছে কাশ্মীরে? আমি বুঝতে পারি না, তাই বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছি। সকলেই কটমটিয়ে তাকায় আমার দিকে। আমি ঘাবড়াই না এবার, শান্ত ভাবে যুক্তি দিয়ে বলি,— দেখুন রঞ্জন ইজ ফ্রম বিহার, আই অ্যাম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কামরুজ্জমান ইজ অলসো ফ্রম বিহার —
আমায় বাক্য শেষ করতে দেয় না রঞ্জন, সে চেঁচিয়ে ওঠে— নো! উই অল আর ইন্ডিয়ানস, দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়ান অ্যান্ড ওনলি আইডেন্টিটি, ম্যায় বিহারি, তুম বাংগালি, ও মাদ্রাসি, অ্যায়সা নেহি চলেগা। নাসির যদি নিজেকে কাশ্মীরি বলে চালাতে চায়, তবে চলে যাক না সালা পাকিস্তান। সালা পাকিস্তানিরা আমাদের লেড়কিদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ বাংলাদেশির পয়সা দেখে ইন্ডিয়ান লেড়কি ভেগে যাচ্ছে, এরা সাচ্চা ইন্ডিয়ান? রঞ্জন নড়বড়ে টেবিলটার ওপর চাপড় মারায় গ্লাসগুলো কেঁপে ওঠে।
—আমাদের লেড়কি মানে! হোয়াট ডু ইয়ু মীন?
এরকম প্রশ্নের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, যেন একটা স্বতঃসিদ্ধের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করেছি। ওদের মধ্যে একজন শান্ত ভাবে বলে, তুমি নতুন এসেছ এখানে, কাল যদি একটা পাকিস্তানি কি বাংলাদেশি তোমাকে লোভ দেখায়, দারু পিলায়, তুমি কি তার সঙ্গে চলে যাবে? যাবে না তো? কারণ তুমি আচ্ছি লেড়কি, মনে প্রাণে একজন ইন্ডিয়ান। কিন্তু এরকম মেয়েও আছে যারা নিজের দেশকে রেসপেক্ট করে না। যে নিজের দেশকে রেসপেক্ট করে না, সে রেসপেক্ট পাবে কীকরে? বুঝেছ এবার?
দীপুদা সামলে নিতে চান পরিস্থিতি, বলেন — যাইহোক, রঞ্জনের মত ভাল ছেলে হয় না, তবে উঠে পড়ে লাগতে হবে। কামরুজ্জমান বলে দেয় যে নাসির যদি ফারদার ঝামেলা করে, যদি রঞ্জনকে ভোট না দেয়, তবে “ইৎনা মারুঙ্গা না সালেকো পাকড়কে”…। মোট কথা সভা ভেঙে যায়। রাত এগারোটা। সেই দুপুরের পর কেউই মদ ছাড়া কিছু খায় নি, আমি তো মদ খাবার যোগ্য গন্য হই নি। যে যার হস্টেলে চলে গেল টলতে টলতে। আমি কী করে ফিরব জানি না। দীপুদা বলল, এত রাতে তুমি একা একা যেও না, আজকের রাতটা আমার এখানে থেকে যাও, কাল ভোরে ট্রলিবাস পেয়ে যাবে মোড়ের মাথা থেকে, চিনে গেছ তো এখন।
আমি থেকে যেতে রাজি হয়ে যাই। তারপর আমরা অস্থায়ী ডাইনিং রুমটা পরিস্কার করে ফেলি। বাসন কোসন উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি দীপুদা সরাসরি চালান করে দেন স্টোর রুমের সেই টেবিলটার তলায়। বাচ্চাসহ বৌদিকে কাল পরশুর মধ্যেই ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। ঘরদোরের যা অগোছালো অবস্থা হয়েছে বৌদি হাসপাতালে থাকাকালীন সে অবর্ণনীয়। দীপুদাকে কাল সারাটা দিন ধরে ঘর গোছাতে হবে, সব নোংরা পরিস্কার করে না ফেললে ছোট ছোট দুটো শিশু নিয়ে বাস করা স্বাস্থ্যকর নয়। ঘরটায় ঢুকলাম, মস্ত একটা খাট, মেঝেয় কার্পেট পাতা, কার্পেটের ওপর হরেকরকম জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। দীপুদা বললেন, তুমি দেয়ালের দিকটায় শুয়ে পড়, আমি ধারের দিকে শুচ্ছি, মাঝখানে অয়েল ক্লথ পেতে ইন্দিরাকে শুইয়ে দিচ্ছি, কোন অসুবিধা নেই তো? অসুবিধা হবার প্রশ্নই নেই, ঘুমে প্রায় ঢলে পড়ছি, একটা লেপ টেনে নিয়ে শুতে না শুতেই এক ঘুমে রাত কাবার। ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে, প্রায় সাতটা বাজছে রিস্টওয়াচে, দীপুদার নাক ডাকছে শুনতে পেলাম। আর ডাকলাম না, বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। এক ঘন্টার মধ্যে হস্টেলে পৌঁছে দাঁত মেজে চুল আঁচড়ে খাতাবই সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে যেতে হবে। দীপুদার হস্টেলের নীচে গেটের কাছে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে রয়েছে বুড়ি চৌকিদার। সে আমার দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে, তাকে দায়সারা গুড মর্নিং বলেই আমি দৌড়তে লেগেছি ট্রলিবাস ধরতে।
ভুজগারাদোক থেকে আট নম্বর ট্রলিবাসে করে পাখতাকোর-এ নেমে ফের আরেকটা ট্রলিবাস নিয়ে তবে পৌঁছব আমার এলাকায়, এলাকাটার নাম বিশাগাচ। ভোরের আলো যত বাড়ছে, ট্রলিবাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে গুনগুন করছি সিনেমার গানের সুর। যাক বাবা একটা বাঙালি ফ্যামিলির দেখা মিলল অবশেষে। আর চিন্তা নেই, দীপুদাতো বলেই দিয়েছে যখন খুশি যেতে পারি ওখানে। বৌদি হাসপাতাল থেকে ফিরুক আগে তারপর যাব একদিন, বাচ্চা ছেলেটার কী নাম দিয়েছে জানাই হলো না কাল। ঘরদোর নোংরা হলেও দীপুদার মধ্যে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না। উনি অবশ্য আর বেশিদিন থাকবেন না এদেশে, ডিসার্টেশন প্রায় রেডি হয়ে গেছে, যে কোন দিন পিএইচডি থিসিস ডিফেন্ড করে ডক্টরেট হয়ে ফিরে যাবেন ইন্ডিয়াতে। তখন একটা ইন্ডিয়ান কমে যাবে এই শহর থেকে, ছাপ্পান্ন থেকে কমে পঞ্চান্ন হয়ে যাবে, নাকি চুয়ান্ন? যদি দীপুদার বৌকে ধরি হিসেবের মধ্যে তাহলে তো চুয়ান্ন হওয়াই উচিত। ওরা যখন গোনে, তখন কি ডিপেন্ডেন্টদেরো গোনে? না বোধহয়, বৌদিতো স্টুডেন্ট নয়, বৌদি হচ্ছে হাউজওয়াইফ, বৌদির ভোটাধিকার নেই। বৌদির নামটা জেনে নিয়েছি, সাগরিকা। ফোটোও দেখলাম ঘরে রাখা ছিল ফ্রেমে বাঁধানো, অপূর্ব সুন্দর মুখটা, অনেকটা প্রিয়ম হাজারিকার মুখটা যেমন, সেই “তেরো নদীর পারে” সিনেমার প্রিয়মের মত, বৌদি শ্যামবর্ণা। আমারতো বিকেলের দিকে কিছু করবার থাকে না, যদি দরকার পড়ে বিকেলের দিকে এসে বৌদিকে কাজকর্মে সাহায্য করে যাব আমি, ছুটির দিনগুলোয় তো যাবোই। ট্রলিবাস থেমেছে পাখতাকোরে। এবার চার অথবা ছ নম্বর ট্রলিবাসের স্টপের দিকটায় যেতে হবে, অল্প একটু হাঁটা। আমি আনন্দে উড়ে উড়ে চলছি আর গাইছি, — সে কোন রূপকথারই দেশ, ফাগুন যেথায় হয় না কভু শেষ, হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ ( কথা মনে পড়ছে না, শুধু সুরটুকু আছে) রেখে এলেম তারে, সাত সাগরের পারে, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে—ক্লাসে আমার পাশে যে ছেলেটা বসে তার নাম মহম্মদ আবদুর রজ্জাক। আফগান। পড়াশোনা খুব একটা ভাল এগোচ্ছে না ওর। ওকে আবদুর বলে ডাকলে ও শুধরে দেয়, আবদুর নয় আবদুল। আবার আবদুল বলে ডাকলে ক্লাসের অন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে। একজনকে তার নাম ধরে ডাকলে এত হাসবার কী আছে! পরে আমজাদ বুঝিয়ে দেয় যে রজ্জাক বলে ডাকতে হবে বা আবদুররজ্জাক বলে, শুধু আবদুল বলতে নেই, আবদুল মানে চাকর, গোলাম। যেমন কারো নাম গোলাম নবী হলে তাকে শুধু গোলাম বলা যাবে না, হয় নবী বলে ডাকতে হবে, নয় গোলাম নবী। এসমস্ত দেশে থাকতে শেখা হয় নি, এখানে এসে শেখা হয়ে যাচ্ছে।
সেই রজ্জাকের সঙ্গে একদিন সন্ধেবেলায় চলেছি দোমব্রাবাদ, এক নম্বর মেডিকেল ইন্সটিটিউটের স্টুডেন্টদের হস্টেলে। জায়গাটা চিনি না বললে ভুল হবে, একবার গেছি আগে, দুতিনবার বাস বদল করে করে যেতে হয়, সবটা সন্ধের অন্ধকারে ঠিকঠাক ঠাওর করতে পারব না। আসলে এই যাওয়াটা আগে থেকে প্ল্যান করে যাওয়া নয়, অথচ খুব জরুরি।
হয়েছে কি, দীপুদার হস্টেলের সেই পার্টির পর দুটো দিন মহানন্দে কাটল মনটা খুশি ছিল বলে। তারপর ভাবছি যে বৌদি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ফিরল কিনা, তাদের শরীর কেমন আছে একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। তারপর ভাবি যে বুধবারে গেলে যদি ভাবে খাবার লোভে এসেছে, তাই একটু রাশ টানি নিজের আবেগে, ঠিক করি যে বেস্পতিবার যাব, তাহলে নিশ্চয় আমাকে হ্যাংলা ভাববে না ওরা। সেদিন ছিল বেস্পতিবার। ক্লাসের পর যাব ভেবে রেখেছি ষোলো নম্বর হস্টেলের দিকে, কিন্তু যাওয়া হল না, দুই অতিথি এসে উপস্থিত। এরাও ভারতীয় ছাত্র, মেডিক্যালের। দোমব্রাবাদে থাকে। কেউ এলে খুব ভাল লাগে, আনন্দ হয়। এরা আজ ভোটের প্রচার করবে না, তা সহজেই অনুমেয়। এরা মস্ত বড়ো একটা টাটকা মাছ নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে — বাঙালি মেয়েকে ইমপ্রেস করবে বলে। সর্বনাশ করেছে! দেশে থাকতে মাছ রান্না করতে শিখিনি। শুধু মাছ কেন, কোন রান্নাই জানি না। কষ্টে সৃষ্টে নিয়মিত হাত পুড়িয়ে যাহোক তাহোক করে রান্না শিখে নিচ্ছি নিজে নিজেই। অতিথিদ্বয় ডিম্যান্ড করল তারা বাঙালির হাতের রান্না করা মাছ খাবে। ঐ মাছ কীকরে রাঁধে আমি জানি না, কোন মশলা দেয়, কীকরে সমস্ত আঁশ ছাড়াব, কীভাবে কুটব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপরে খেয়াল হল আমার কাছে তো কোনরকম মশলাই নেই। এসব জানাতেই ওরা প্রথমে অবিশ্বাস করলেও, পরে হতাশ এবং অসন্তুষ্ট হল। যেন ধরেই রেখেছে যে প্রত্যেকটা বাঙালি মাছ রান্না করাটা জানবেই। তারপর সামান্য কথা কাটাকাটি, মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলায় আরেক দফা মান অপমান হবার পরে ব্যাপারটা আর আয়ত্বের মধ্যে থাকে নি।
তারা মাছ ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করল এবং মেয়ে হয়েও রান্না না জেনে এতগুলো বছর কীকরে কাটিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি নিয়ে তাদের অবাক হবার শেষ নেই। অ্যাইসা রাগ হল যে, মাছটা নিয়ে চারতলার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি বাইরে। তারাও দাঁড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। একটু পরে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চওড়া ফুটপাথের ওপর মাছটা পড়ে আছে, দুয়েকজন লোক যারা হেঁটে যাচ্ছে একবার করে ঝুঁকে দেখে নিচ্ছে মাছটা। কেউ সাহস করে ওটা ধরছে না। একটু পরে একটা বড়ো ঠোঙা নিয়ে নীচে গিয়ে মাছটা ঠোঙায় ভরে ওপরে নিয়ে এলাম, তারপর ভাবলাম যাদের মাছ তাদেরকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসি, তখনই রজ্জাকের সঙ্গে বাসস্টপে দেখা হয়ে গেল। রজ্জাকও দোমব্রাবাদ যাচ্ছে। চারতলার ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলায় মাছটা সামান্য ক্ষত বিক্ষত হয়েছে কিন্তু ধুয়ে টুয়ে নিলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে নিশ্চয়ই। অতটা রেগে যাওয়া আমার উচিত হয় নি, মাথাটা গরম হয়ে গেছল ওদের কথাবার্তার ধরণ দেখে। হালকা করে একটু সরি বলে নেব, ব্যস। বেশি মাথা নোয়ানোর প্রয়োজন নেই।
মেডিকেলের এক নম্বর হস্টেলেই ঐ অতিথিযুগলের বাস। রজ্জাক চলে গেল দুনম্বর হস্টেলে কার সঙ্গে যেন দেখা করতে। এক নম্বরের বুড়ি চৌকিদার ভেতরে খবর পাঠাল যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তারা আছে কিনা জানতে। রিসেপশনের সোফায় বসে আছি এমন সময় একটা ছোটখাট অসম্ভব রোগা ফর্সা ছেলের আবির্ভাব। পরিস্কার ইংরিজিতে জানতে চাইল কার জন্য অপেক্ষা করছি ইত্যাদি, তারপর বলল, চলো আমার ঘরে এসে বসো। চৌকিদারকে বলে দিল যে আমি তার ঘরে আছি। ঘরটা একতলায় চৌকিদারের টেবিল থেকে তিন পা দূরত্বে। ছেলেটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে, আমার নাম নাসির, নাসির আহমেদ শাহ। আরিব্বাস! এই সেই বহু চর্চিত কাশ্মীরি রেবেল নাকি? নামটুকু শুনেই আমি খপ করে বলি, ফ্রম কাশ্মীর? ও অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝতে পারলে, আমায় দেখলেই বোঝা যায়, তাই না? যেমন তোমায় দেখেই আন্দাজ করছি, তুমি বাঙালি, ঠিক না?
সন্ধেবেলায় একজন ডাক্তারির ছাত্রর সাধারণত যা করা দরকার, নাসির সেটাই করছিল, পড়াশোনা। তবু আমাকে আপ্যায়ন করে চা খাওয়াল, কথা বলল। মাছ কোলে নিয়ে বসে নাসিরের কথা শুনছিলাম। সে শ্রীনগরের বাসিন্দা নয়, শ্রীনগর থেকে অনেক দূরে তার গ্রাম। তার গ্রামে এবং আশেপাশের আরো বেশ কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে একজনও ডাক্তার নেই। তাই সে ডাক্তারি পড়তে এসেছে। ফার্স্ট ইয়ারের পড়া শেষ করে যখন গ্রামে গেছল, তখন গোটা তিন চার গ্রাম থেকে অনেক রোগী এসেছিল তার কাছে চিকিৎসা করাতে। সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। বারণ করে দিয়েছে এভাবে আসতে। বলে দিয়েছে, আর পাঁচ বছর পরে এসো। ততদিনে আমি ডাক্তারি শিখে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসব গ্রামে। ঊনিনশো নব্বই সালের গ্রীষ্মে নাসিরের গ্রাম আর চিকিৎসক শূণ্য থাকবে না, সবাই পথ চেয়ে বসে থাকবে তার। আমি চা খেতে খেতে নাসিরের গ্রামের গল্প শুনি, অধিকাংশই অসম্ভব গরীব মানুষ। জমিতে চাষ হয় জাফরানের। জাফরান শুকোয়, বাছে, কখনও জাফরান খায় চায়ের মত। শীতকালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে জোব্বার মধ্যে একটা পাত্রে অল্প করে কয়লার আগুন নিয়ে বেড়ায় বুকের কাছে ধরে। এই সব শুনতে শুনতে জানতে চাইলাম সামনের রোববারে ভোটে দিতে যাচ্ছে কিনা। নাসির জানালো সে অবশ্যই যাবে, রবিবারে তো আর ক্লাস কামাই করতে হবে না। এর মধ্যে খবর আসে যে সে দুজন তখনো হস্টেলে ফেরেনি। কী আর করা, মাছটা আরেকজনের হাতে সঁপে দিই। কী মাছ, কেন মাছ, মাছের ইতিহাস একটুও বলি না। তার পর টুক করে কেটে পড়ি ঐ চত্বর থেকে।শনিবারে হাফছুটির পর সোজা চলে গেলাম ষোলোনম্বর হস্টেল। চারতলাটা নিঝুম নিঃস্তব্ধ, বেলা তখন আড়াইটে তিনটে মত। সেদিনের পার্টি অ্যাটমসফেয়ারের সঙ্গে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সব বেশ গুছোনো পরিচ্ছন্ন। রান্নাঘরটার উল্টোদিকে সেই সংকীর্ণ বৈঠকখানার দরজাটা আলগা করে ভেজানো, রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম কেউ নেই, এমনকি ইন্দিরার কমোডটা পর্যন্ত নেই। তবে কি ভুল তলায় চলে এলাম? ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই দেখি বৌদি এসে দাঁড়িয়ে আছেন। নিঃশব্দে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন টেরই পাই নি। ফটোতে যেমন দেখেছিলাম তেমনি রূপ, কেবল মুখটা বিষন্ন, হাসি নেই। তবে কি শরীর এখনো সারে নি ছেলের? আমি নিজের পরিচয় দিই, বৌদি শুনে বলেন, চিনতে পেরেছি। তারপর ঘরে ডেকে নেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, ইন্দিরা ঘুমোচ্ছে খাটে, বাচ্চা ছেলেটা ছোট বেবিকটের মধ্যে কাপড়ে মোড়া, মুখটুকু দেখাই যায় না। ঘরের চেহারা ফিরে গেছে, সব গুছোনো, একটা বেবি বেবি গন্ধ ভরে রয়েছে। কার্পেটের একধারে পরিস্কার কাঁথা নেংটি ইত্যাদি গুছিয়ে রাখছিলেন বৌদি, সম্ভবত তখনই বাইরে আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলেন।
—হ্যাঁ বৌদি বলুন কী বলবেন বলছিলেন? আমি হেল্প করব আপনাকে কোন কাজে?
অসম্ভব রেগে যান বৌদি, দুচোখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসে, বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে তাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন আমাকে নিয়ে। রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ খোলেন।
—আমি যখন হাসপাতালে আমার অসুস্থ বাচ্চাকে নিয়ে রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছি, আমার স্বামী কবার দেখা করতে এসেছেন জানো? তিন সপ্তাহে পাঁচবারও নয়। আবার ঢঙ করে এক বোতল দই নিয়ে গেছে লোক দেখিয়ে। সেই সময় তুমি এখানে থাকতে তাই না? দিনের পর দিন তুমি এখানে থেকেছ, আমি সব জানি। একতলার চৌকিদার থুত্থুড়ে বুড়ি হলে কী হবে, সে সব দেখেছে, আমাকে সব বলেছে, আমি ফিরে আসব জেনে তুমি ভোরবেলা চোরের মত পালিয়ে গেছলে। ছিঃ, তোমার লজ্জা করে না আমার স্বামীর সঙ্গে শুতে? দুদুটো সন্তান আছে তার, একজন বিবাহিত মানুষের সংসারে তুমি ঢুকলে কী বলে? নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে!
একটা কথা উত্তর দিতে পারিনি, এতটাই আশ্চর্য হয়ে গেছলাম বৌদির কথা শুনে। কোথা থেকে শুরু করব, কী বলব, মাথায় খেলছিল না। কীভাবে প্রতিবাদ করব?
—আপনি যা বলছেন ভাবছেন সমস্ত ভুল।
বৌদি আরও রেগে গেলেন।
— ভুল? প্রমাণ আছে আমার কাছে, প্রমাণ দেখাব?
উনি ব্যালকনিতে আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালেন একটা ডেচকি। ঢাকনা বন্ধ করা। ঢাকনা খুলতেই ভকভক করে পচা গন্ধ। সেই শিপ্রাদির বানানো ভ্যানিলা কাস্টার্ড এতদিনে পচে বীভৎস চেহারা নিয়েছে। সেদিন পার্টির শেষে সবাই ভুলে গেছলাম কাস্টার্ডের কথা। বৌদি চেঁচান, তুমি অস্বীকার করতে পারো যে এটা তুমি বানাও নি? বুঝলাম, এখানে যুক্তি তর্ক সব বৃথা। কত আশা নিয়ে এসেছিলাম, বৌদিকে নিয়ে কত কিছু করব ভেবে রেখেছিলাম, সমস্ত স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে শেষ। এই মহিলার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তিনি চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, চৌকিদারকে ডেকে আনবো? সে সব দেখেছে, সে সব জানে, দিনের পর দিন এখানে লীলাখেলা হয়েছে।
ঐ বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। যাবার আগে বললাম, বৌদি আপনি নিজের স্বামীকে চেনেন না? এই কথা বলেও অবশ্য কোন লাভ হল না, তিনি তখনও বলে যাচ্ছেন, চিনি না আবার? চিনি বলেই তো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি আমার, ইত্যাদি ইত্যাদি।
লিফটের জন্য দাঁড়ানো মানে ঐ মহিলার কথা আরও কিছুক্ষণ শুনতে বাধ্য হওয়া। তাই তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই একতলায়। দেখি বুড়ি চৌকিদার তখনও পিটপিট করে দেখছে আমাকে। মনে মনে বলি, দেখ, ভালো করে দেখ, ছিঃ, এত নোংরা মন যে দুজন মানুষের সম্পর্কে শুধু সেক্স ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিস না?
রাস্তায় বেরিয়ে হু হু করে কান্না পেয়ে যায় আমার। মানুষ এরকমও হয়? এ কোথায় এলাম আমি! এদেশে সামনের এতগুলো বছর বাঁচব কীকরে? মনে হয় তখুনি দেশে ফিরে যাই। ভয়ঙ্কর হোমসিকনেস আমাকে গ্রাস করতে থাকে।হস্টেলে ফিরে খবর পেলাম দেশ থেকে আমার জন্য চিঠি এসেছে। প্রথম চিঠি। প্রায় একমাস হল আমি দেশ ছেড়েছি, প্রথম চিঠি পাঠিয়েছিলাম সেই সময়েই, সে চিঠি পৌঁছেছে এবং অবশেষে এসেছে উত্তর। তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছলাম তো ক্লাস শেষ হবার পরে, চিঠি দেবার জন্য আমার খোঁজ করেছিল লাইব্রেরিয়ান, আমায় খুঁজে পায় নি। সোমবারে লাইব্রেরী খুললে সে চিঠি আমি হাতে পাব। ভারতবর্ষ থেকে চিঠি পৌঁছতে পনের দিন মত লাগে। আরেকটা জিনিস হয়ে গেছে যখন ছিলাম না, দেয়ালে ঝোলানো কাচের দরজা লাগানো শেলফটা পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেছে। যখন পড়ে গেছল, তখন ফেরার পথে হয়ত হাঁটছিলাম কি ট্রলিবাসে ছিলাম, এতবড় একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে টেরই পাই নি। ভূমিকম্প রোজই প্রায় হয় অল্প বিস্তর। আজ বেশ জোরে হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। আজকাল আর ভূমিকম্পে বাড়ি ধ্বসে গিয়ে চাপা পড়ে মরবার ভয় নেই। ঊনিশশো ছেষট্টির ভূমিকম্পে যখন গোটা তাশখন্দ প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল, তারপর থেকে সমস্ত বাড়িই এমন করে বানানো হয়েছে যাতে সহজে না ভাঙে। পুরোনো বাড়িগুলোকে বিশেষভাবে সারানো হয়েছে যাতে ঐরকম দুর্যোগেও যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। মোটামুটি সব বাড়িই ৯ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্পেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু ভূমিকম্পে যখন বাড়িগুলো দোলে বা থরথরিয়ে কাঁপে, তখন আলগা জিনিসপত্র টুপটাপ ধুমধাম পড়েই যেতে পারে, কি ইলেকট্রিকের লাইনে ধরে যেতে পারে আগুন। সেজন্য পইপই করে সাবধান করে দেয় বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি সুইচ অফ করতে না ভোলে যেন কেউ। আমার রুমমেট দুজন ইতিমধ্যেই কাচ টাচ সরিয়ে সব পরিস্কার করে ফেলেছে। ঘর গুছোতে গুছোতে প্রায় ভুলেই গেলাম প্রায় বিকেলের সেই অপমান। চিঠিতে দেশের খবর পাব ভেবেও মনে উত্তেজনা। তার ওপর কাল তো ইলেকশান। এখনো মনস্থির করতে পারছি না কাকে ভোট দেব। এরা এই ইলেকশান নিয়ে এত মেতেছে, এতটাই বাড়াবাড়ি করছে যেন জিততে পারলে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নয়, একেবারে ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট বনে যাবে। কী লাভ এসব করে? এদেশে ছাত্র ইউনিয়ন নেই, যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমসামোল। আমরা তো বিদেশি— ফরেনার। ফরেনাররা তো আর দেশের অভ্যন্তরীণ পোলিটিক্সে ঢুকতে পারবে না, তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে। যে জিতবে, মানে যে ছেলেটা প্রেসিডেন্ট হবে সে নিশ্চয় বাকি ইন্ডিয়ানদের ওপর খুব ফোপরদালালি করবে, মেয়েদের ওপর গার্জেনি ফলাবে। একটা মাসও কাটেনি তারই মধ্যে যা তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। আবার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছে সাগরিকা বৌদির দুর্ব্যবহার। উনি কি সন্দেহ বাতিক গ্রস্থ? ভাবতে পারল কী করে যে আমার খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নেই ওর ঘরে গিয়ে দিনের পর দিন কাটানো ছাড়া? কি জানি, দিনের পর দিন সারাক্ষণ একটা ঘরে মধ্যে থাকতে থাকতে বাচ্চা কাচ্চার কাঁথা কাচতে কাচতে বাইরের জগতের সঙ্গে সেরকম কোন যোগাযোগ না থাকায় ওরকম হয়ে গেছে। ওর তো কথা বলবার লোক বলতে স্বামী এবং বুড়ি চৌকিদার। ক্লাসে যায় না, ছোটখাট চাকরি করবারও কোন স্কোপ নেই বিদেশিদের, সারাটা দিন বন্দি হয়ে রয়েছে ষোলো নম্বর হস্টেলের চারতলার কোণের একটা ঘরে। বৌদির ওপর রেগে যেতে পারি না, কেমন একটা মায়া হয়। মনে মনে ওকে ক্ষমা করে দিই। দেশে থাকতে সত্যিই সমাজটাকে চিনিনি। বিদেশে এসে চিনছি।
নাঃ, কালকে ইলেকশানে যেতেই হবে। মীনাক্ষি বলে মেয়েটা নিশ্চয় আসবে কাল। সবকটা ইন্ডিয়ানকে একসাথে দেখবার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর হতেই পারে না। কাল আমি যাবোই। ভুজগারাদোকের পঁচাশি নম্বর হস্টেলের একটা হলঘরে নির্বাচন কেন্দ্র। সেজেগুজে যাব।
রোববার দুপুরে দুজন ছাত্র আলাপ করতে এল আমার ঘরে। প্রথমে দেখে ভেবেছি বুঝি ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারা পরিস্কার বাংলায় নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমার ভুল ভাঙালো। এরা বাংলাদেশি, একজন বলল, — আমার নাম দেবেশ, আমি হিন্দু, দেবেশ হালদার। অন্য জন্য বলে, —আমি নেসার খান। দেবেশ ভুজগারাদোকে থাকে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, চোখে চশমা, হিন্দু হলেও সে পানি খেতে চায়। নেসার খান খুব জোরে জোরে হাসে, বাজখাঁই গলা, লম্বা ফর্সা, ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটে। তার হস্টেল নাকি আমার এই হস্টেল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, ট্রলিবাসে মাত্র একটা স্টপ, হেঁটেও যাওয়া যায়। আমার কাছে বাংলা গল্পের বই টই কিছু আছে কিনা খোঁজ নেয় নেসার, আমি বই এনে দেখালে সে বেছে বেছে “শেষের কবিতা” টা ধার নিতে চায় যত শীঘ্র সম্ভব ফেরৎ দেবার অঙ্গীকার করে। দিয়ে দিই। এইটুকু কমিউনিটি, এ বই হারাবে না। বইটার মধ্যে আমার বাবার স্মৃতি রয়েছে, বাবা কিনেছিল বইটা তার কিশোর বয়সে। তবু দিলাম। নেসার বই নিয়ে চলে গেল, যাবার আগে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিল কাগজে, দেখি নামের বানান নেছার। ছ কেন? ওরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বলে, কেন ভুল কোথায়, ছ ই তো হবে। ওঃ আপনারা ক্যালকাটার বাঙালিরা এত কষ্ট করে করে বাংলা বলেন! দেবেশ আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। আমার রুমমেট দুজনকে দেখে বলে, এরা ভিয়েতনামি নাকি? না, এরা লাওসের মেয়ে, ভিয়েতনামের কোনও মেয়ে নেই এই হস্টেলে অনেকগুলো ছেলে আছে। দেবেশ ভিয়েতনামিদের রাশিয়ান উচ্চারণ নকল করে করে শোনায়, কয়েকটা জোক বলে, সেসমস্ত জোক ব্যাকডেটেড, আজকের দিনে একদম রুচিসম্মত নয়। তাতে চেহারা উচ্চারণ নিয়ে বিদ্রূপ আছে, যৌন গন্ধও আছে যেমনটা চলত আশির দশকে। আমি বলেছিলাম যে সব ভিয়েতনামিরা কিন্তু একই রকম দেখতে নয়, কয়েকজন বেশ লম্বা চওড়া গায়ের রঙেরও তারতম্য আছে। দেবেশ জানায় তা তো হবেই, যুদ্ধের সময় জন্মেছে যারা তাদের কারও কারও শরীরে বইছে অ্যামেরিকান রক্ত। আরেকটু থেকে সে চলে যায়, যাবার আগে হাসিমুখে বলে, ভগবান হাফেজ।
আমার মনে পড়ে ছোটবেলা বাবা শিখিয়েছিল, আমার নাম তোমার নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। আমার প্রথম শেখা ছড়াগুলোর একটা এইটাই। কিছু বুঝতাম না তখন যুদ্ধ বিষয়ে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গল্প শুনে ভাবতাম একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে সারাদিন সবাই খুব মারপিট করে, তাকেই বলে যুদ্ধ। ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হলে বাবা দেখিয়েছিল নারকেলের ফালির মত দেশটার ম্যাপ। একবার একজন জ্যাঠাগোছের ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিল বাড়িতে, তাকে ঐ “আমার নাম তোমার নাম”টা শুনিয়েছিলাম, সে আমায় শুধরে দিয়েছিল, —বলব নাকো বাপের নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।
তারপর খ্যা খ্যা করে খুব হেসেছিল। সেটা কি এই সব কারনেই? এখন তো বড় হয়েছি, কত কিছু শিখছি জানছি, কত দেশের মানুষজন চারপাশে। আজ জানলাম কিছু ভিয়েতনামির ধমনীতে বইছে অ্যামেরিকানের রক্ত। বাঃ। তার শরীরে আর এতটুকুও ভিয়েতনামের রক্ত অবশিষ্ট রইল না? তাদের মায়েদের রক্ত সব শুষে নিঙড়ে বের করে নেওয়া হয়ে গেছে? আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি। টের পাচ্ছি যে বড় হয়ে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি, মেয়ে থেকে মহিলা বনে যাওয়া সম্ভবত একেই বলে।ভোটের দিন বিকেলে একা একাই যাচ্ছিলাম নির্বাচন কেন্দ্রে, কিন্তু হস্টেলের বাকি দুজন ইন্ডিয়ান প্রায় জোর করেই তাদের সঙ্গে তুলে নিল আমায় ট্যাক্সিতে। ওরা সম্ভবত খবর পেয়ে গেছে যে আমি রঞ্জন কুমারের ভোটার। চাপা উত্তেজনায় কথা বেশি হয় না, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা খুব আলাপি হয়, ড্রাইভারের নানা প্রশ্ন ও কৌতুহল নিরসন করতে করতে আমরা পৌঁছই গন্তব্যে। ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় আমার সহযাত্রী অনিল অরোরা অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, স্কার্ট কিঁউ পহেনতি হো, সাড়ি নেহি হ্যায় ক্যা?
বিয়েবাড়ির মত সাজগোজ করে এসেছে সব, কেবল গয়নাগাটি বাদ। ভুরভুর করছে সেন্টের গন্ধ। বিকেল তিনটেয় ভোট শুরু হবার কথা। পঁচাশি নম্বর হস্টেলের একতলার হলঘরটায় প্রচুর চেয়ার পাতা। একদিকে ছোট একটা স্টেজের মত বানিয়েছে, নীচু স্টেজ। অধিকাংশ লোকজনই হস্টেলের বাইরে উঠোনে বাগানে ছোট ছোট জটলা করে রোদ পোয়াচ্ছে। আমি তো নতুন লোক, এরা সব কত বছর ধরে পরিচিত, বন্ধুত্ব শত্রুতা সমস্ত মিলিয়েই এরা নিজেদের মুখগুলো চেনে। কয়েকটা জটলার পাশ ঘেঁষে গিয়ে আবহাওয়াটা বুঝতে চেষ্টা করলাম, ভোট নিয়ে কথাই বলছে না কেউ, নভেম্বরে দিওয়ালি উৎসব হবে, সেই সব নিয়ে প্ল্যানিং চলছে। নভেম্বরে দিওয়ালি? তারমানে দুর্গাপুজো তো এসে গেল! মহালয়া হয়ে গেছে? নাকি দুর্গাপুজো চলছে এখন? এই প্রথম দুর্গাপুজো দেখা হল না, এরকম আরও কত বছর সামনে আছে কে জানে। দিওয়ালি মানে কালিপুজো, বাজিটাজি ফাটানো হয় কি এখানে? কোত্থেকেই বা পাবে এখানে বাজি। সাড়ে তিনটে বেজে গেল তা ও ভোট শুরু হয় না। প্রত্যেক প্রার্থীই নিজ নিজ দলের ভোটারদের জন্য আরও একটু অপেক্ষা করতে চায়। আরেকটু অপেক্ষা করবার পর বর্তমান প্রেসিডেন্ট সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে হলঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এক ফাঁকে রঞ্জন কুমার আমার কানে কানে বলে গেছে ভোটের পর যেন চলে না যাই, আজ সন্ধেবেলা পার্টি আছে। সবাই বসে পড়লে পরে বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দেওয়ালির পার্টির দিনটা ঘোষণা করে দিল, তারপরে তিন ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা করা, একজন নাম প্রপোজ করছে, আরেকজন সেটা সেকেন্ড করছে, এইভাবে তিন প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়ে গেল, যথাক্রমে রঞ্জন কুমার, রবিশংকর ভেঙ্কটরমন এবং বলবন্ত সিং। বলবন্ত সিং এত মদ খেয়ে এসেছে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, তাকে দুপাশ থেকে দুজন ধরে রেখেছে। সেরেছে! এ কোনও গোপন ভোট নয়, ওপেন সিস্টেম! নো ব্যালট পেপার, হাত তুলে ভোট দাও। আমার পাশে বসে আছে কামরুজ্জমান, সে ফিসফিস করে বলে দিল, রঞ্জনের নাম অ্যানাউন্স করলেই যেন হাত তুলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জনের নাম অ্যানাউন্স হয়ে গেছে, স্টেজে রঞ্জন দাঁড়িয়ে। অনেকেই হাত তুলল, আমি কোলের ওপর হাত জড়ো করে রেখেছি, কামরুজ্জমান দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করছে পাশে, —হাথ উঠাও, উঠাও!
যেন কিছু শুনতে পাইনি এমন মুখ করে অন্য দিকে চেয়ে আছি, সেদিকেও রঞ্জনের ভোটাররা হাত তুলে আমার দিকে তাকিয়ে। কোন দিকে তাকাবো? কয়েক মুহূর্তের জন্য সব দর্শক তাকিয়ে আছে এদিকেই, তাদের কারও হাত তোলা, কারও হাত নামানো, কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখছে। মনে হল যেন থিয়েটারের স্টেজের ওপর আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছি, চোখের সামনে এই সব দর্শকদের আর দেখতে পাচ্ছি না, নাটক শুরু হয়ে গেছে, আশেপাশে লোকজন চেয়ার দেওয়াল সমস্তটাই অন্ধকার, সেই অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে নিজের রোলটা শুধু অভিনয় করে যেতে হবে, বাদবাকি পরে দেখা যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ওরা হাত গুনতে শুরু করে দিল, এক দো তিন… তেইস, চৌবিস। আবার গোনা হল, …এক্কিস বাইস তেইস চৌবিস। রঞ্জনকুমার চব্বিশটি ভোট পেয়েছে, নাসির ও ভোট দিয়েছে তাকে। দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট রবিশংকর। আমি হাত তুললাম। সারা ঘরে সম্মিলিত আশ্চর্য হবার নিঃশ্বাস। একটু অপেক্ষা, আবার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অভিনয় করবার মত একটা মিনিট। মোট ভোট মাত্র চার। রবিশংকর নিজে এবং তার দুই সঙ্গী বাদ দিলে আমি একমাত্র যে তাকে ভোট দিয়েছি। তারপর তৃতীয় ক্যান্ডিডেট বলবন্ত সিং। বাকি হাতগুলো উঠল, আবার গণনা, এক দো তিন চার… বাইস তেইস চৌবিস পচ্চিস। আবার গোনা হল, পঁচিশ। মোট ভোটার সংখ্যা ছাপ্পান্ন, তিনজন অনুপস্থিত, ভোট দিয়েছে তিপ্পান্ন জন, রবিশংকর চার ভোট, রঞ্জন কুমার চব্বিশ ভোট, এবং বলবন্ত সিং পঁচিশ ভোট পেয়ে জয়ী। তাকে পাঁজাকোলা করে অভিষিক্ত করা হল। রঞ্জনের দল আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। চ্যাংদোলা করে বলবন্তকে হলের বাইরে নিয়ে যেতে না যেতেই চেয়ার ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি রবিশংকর আমার সামনে এসে হাসি মুখে ঝুঁকে বলছে, থ্যাংকিউ ভেরি মাচ, লেটস গো টু সেলিব্রেট। তাকে ইংরিজি বলতে শুনে একজন তারস্বরে চেঁচালো, — হিন্দি মে বোল সালে মাদার চোদ, রাষ্ট্রভাষা মে বোল! এরপর দুই দলে চিৎকার চেঁচামিচি, অনেক নতুন নতুন খিস্তি শেখা হল। আমাকে গার্ড করে সেখান থেকে বের করে নিয়ে, রবিশংকর ও আরো দুজন সোজা একুশ নম্বর হস্টেল।
এই হস্টেল যেমন রঞ্জনের তেমনি রবিশংকরেরও। দুজনেই হেরেছে, কিন্তু রবিশংকরের ঘরে তখন ক্রেটের পর ক্রেট ভোদকা ও পেপসি। পার্টি হবে। এর নাম পোলিটিক্স। রঞ্জন জিতে যেতে পারে জেনে বলবন্ত সিং এর উপদেষ্টা কমিটিও গোপন বৈঠক করে। সেখানে ঠিক হয় যে রবিশংকর তার ভোটারদের বুঝিয়ে বাঝিয়ে বলবন্তকে ভোট দিতে বলবে। এসব লাস্ট মোমেন্ট ডিসিশান, ভোটের আগের দিন এই সমস্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। রবিশংকর যে জিতবে না তা আগেই বোঝা গেছল, ও পেতে পারত শুধু সাউথ ইন্ডিয়ানদের ভোট, সেটা খুব বেশি নয়। কিন্তু বলবন্ত সেগুলো শিওর শট পেয়ে গেলে তার জয়ের পথ সহজ হয়। রবিশংকরের পক্ষে শেষ মুহূর্তে মনোনয়নপত্র ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাহলে রঞ্জনের দল সব জেনে যেতে পারত, শেষ মুহূর্তে মারপিট হয়ে গিয়ে ইলেকশানটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত। বরঞ্চ এটাই ভাল, বলবন্ত প্রেসিডেন্ট এবং রবিশংকর ভাইস প্রেসিডেন্ট। বলবন্ত অধিকাংশ সময়েই মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে মূল ক্ষমতা থাকবে রবিশংকরের হাতে।
রবিশংকরের ঘরে ভিড় হতে থাকে, সন্ধে হয়ে গেছে। ওরা আমাকেও অফার করে। স্ট্রং মদ ভোদকা, নীট। হাসি ঠাট্টা হৈ চৈ হচ্ছে, কিন্তু বলবন্তকে দেখা যায় না কেন? অনেকেই জানতে চায় বলবন্ত কোথায়? প্রশান্ত এসে খবর দেয়, বলবন্ত মত্ত অবস্থায় হস্টেলের সামনে থেকে একজন রাশিয়ান মেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে। ওকে এখন ডিস্টার্ব করাটা কোন কাজের কাজ নয়। বিকেলের দিকে বিদেশিদের হস্টেলের গেটের সামনে সেজেগুজে মুখে রং মেখে অনেক মেয়েকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রশান্তের কথা। আমি নর্থ ক্যালকাটার মেয়ে, সন্ধেবেলা খান্না সিনেমার উল্টো দিকে হরিসা’র বাজারের অন্ধকারে অমন রংমাখা মেয়ে ছোটবেলা অনেক দেখেছি।
একটু পরেই বোতল ভাঙার আওয়াজ। জয়ী ও পরাজিত দলের মধ্যে বোঝাপড়া, পেপসি ও ভোদকার বোতল যেই খালি হচ্ছে, অমনি সেগুলো ছুঁড়ে মারা হচ্ছে শত্রুপক্ষের দিকে। রঞ্জন কুমার একুশ নম্বরে ফেরেনি, সে রয়েছে অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে, এবং সেখান থেকেই মেঘনাদের মত বোতল টোতল ছুঁড়ছে। রবিশংকরের দুই রুমমেট রামলিঙ্গম ও রামনারায়ন আমাকে এগিয়ে দিতে চলল ট্রলিবাস স্ট্যান্ড অবধি, বলা যায় না রঞ্জন যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, বডিগার্ড থাকলে ঝুঁকিটা কম। হস্টেল এলাকায় তুমুল বোতল বৃষ্টি চলছে। আমি আবারো মনে করি নর্থ ক্যালকাটার কথা, পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি দেখে বড়ো হয়েছি, এরা বোতল ভেঙে আর নতুন কী দেখাবে। এক চুমুক ভোদকায় নেশা হয় না, কিন্তু মেজাজটা সব মিলিয়ে ফুরফুরে। দুই রামকে বডিগার্ড হিসেবে পেয়ে আমি মনে মনে বলছি, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্, ক্ষিপ্ত তেজে মারো বোম্, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্, লেফ্ট রাইট লেফ্ট রাইট, … মোট কথা ওরা যা আরম্ভ করেছে, তাতে আজ মিলিৎসিয়া** আসবেই।
টীকা:
* ডে-লাইট সেভিং: বছরের ঐ সময়ে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবারে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হতো। আবার মার্চের শেষ রবিবারে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে আনা হতো। শীতের মরশুমে রাতের অন্ধকার বেশিক্ষণ থাকে সেসব ভেবেই হিসেব টিশেব করে এই নিয়ম চালু হয়েছিল, কিন্তু ১৯৯১ এ দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পরে উজবেকিস্তান আর সময় পাল্টানোর ঝামেলায় যেত না।
** মিলিৎসিয়া: সোভিয়েত ইউনিয়নের পুলিশ।
চলবে…
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:১২735832
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:১২735832- বাজার ও বিস্ফোরণজয়া বচ্চন ও তারাচাঁদবাবু নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন দেখে আমি এগিয়ে গেছলাম আমতা আমতা করে অটোগ্রাফ চাইতে কিন্তু সুযোগ পেলাম না, উনি বললেন যে ওঁর বাচ্চারা ওপরে ঘরে একা রয়েছে, তড়িঘড়ি সেই করিডোরের দিকে মিলিয়ে গেলেন। কিছুটা সময় চারজনে সেই মাঝারি লাউঞ্জে প্রায় চুপচাপ বসেছিলাম। ভারতীয় সিনেমার এক নম্বর তারকা অহংকারহীনভাবে সাধারণ কথাবার্তা বলছিলেন তারাচাঁদবাবুর সঙ্গে। পাশে গডউইন ও আমি হাঁ করে সেসব দেখছিলাম। ডলার ফলার সব মাথা থেকে উড়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ওঁদের কীসব মিটিং প্রোগ্রাম এসব শুরু হবে, হাতে ভাঁজ করা অটোগ্রাফের কাগজটা নিয়ে চলে যাচ্ছি তারাচাঁদবাবু পেছন থেকে ডেকে আমায় পরদিন সকালে ওখানে ফের যেতে বললেন। বললেন নিয়ে যাবেন ফিল্মের বাজারে, সেখানে ফিল্ম বিক্রি হয়, আমার ভাষাজ্ঞান ওঁর কাজে লাগতে পারে ফিল্ম বেচবার জন্য। পরদিন সোমবার, ক্লাস কামাই করিনি কোনওদিন এর আগে, তা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলাম। ফিরবার পথে গডউইন ইয়ার্কি মারছিল, তারাচাঁদবাবুর পরের সিনেমার নায়িকা বানিয়ে ফেলতে পারেন আমাকে। আর্ট ফিল্মের জন্য তো আর নাচ টাচ জানতে হয় না, সুন্দরী হবারও বাধ্য বাধকতা নেই।
সে বড় ধীর স্থির সময় ছিল। এক দেশ থেকে অন্য দেশে চিঠি পৌঁছতে মেরেকেটে পনের দিন তো লাগতই, রেডিওর নিউজও কান পেতে শুনতাম আমরা, টেলিভিশনে বিদেশের চ্যানেল পাওয়া যেত না, খবরের কাগজ থকে বাসি খবর জেনে নিতে হতো যদি তা আদৌ ছাপা হয়ে থাকে। তবু চেরনোবিলের ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা জানতে পারিনি সেভাবে। বিদেশের ঘটনা নয়, তবু প্রায় সমস্ত ঘটনাই চেপে দেওয়া হল জনসাধারণের কাছে। যেটুকু না বললেই নয় সেই ধাঁচে জানানো হয়েছিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দুর্ঘটনার খবর, হতাহত কতজন, কী পরিমান তেজষ্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে গেল পরিবেশে, আরও কত বছর ধরে এর মূল্য দিয়ে যাবে পরিবেশ, কিছুই জানানো হল না দেশের জনগনকে। দিন কয়েক পরে সবাই ভুলে গেলাম সে খবর, চেরনোবিল তো কত দূরে সেই ইয়োরোপে উক্রাইনায়, মধ্য এশিয়ার মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি, মধ্য এশিয়ার মানুষেরা সিনেমার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিল বসন্তের ফিল্ম ফেস্টিভালে। আর তো কিছু পাল্টায় না জীবনে, সেই একই খবর ঘুরে ফিরে শুনতে হয় রেডিও টিভিতে, সেই একই ভাবে উৎসব ও ছুটির দিনের উদযাপন, একই লাইন দোকানে, সব যেন থেমে রয়েছে, পাল্টায় কেবল সিনেমাগুলো। সিনেমাগুলো নিয়ে যায় অন্য দুনিয়ায়, সফর করিয়ে আনে স্বপ্নের দেশে মাত্র আড়াই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে, এক রুবল চল্লিশ পয়সার বিনিময়ে। রাজ কাপুর কি কম অক্সিজেন জুগিয়েছেন এই মানুষগুলোর জীবনে? সেবারই ওঁর শেষ সফর ছিল এই ফেস্টিভালে। হয়ত কোনও ফিল্মের শুরুতে এক মিনিটের জন্য তিনি দেখা দিতে পারেন সিনেমা হলে, এই আশায় আশায় ভিড় করে অপেক্ষা করে উজবেকরা, বুড়ো বাচ্চা যুবক যুবতী সবাই হিন্দি সিনেমার ফ্যান। অ্যাডভান্স বুকিং করে টিকিট কাটা যায় না, তাই প্রতিটি শোয়ের আগে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়ায় তারা। লাইনে দাঁড়ানোতো নতুন কিছু নয়, প্রতিদিনই তো কিছু না কিছুর জন্যে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। ইন্ডিয়ান সিনেমা অধিকাংশই মিলনান্তক। গল্পের শেষে প্রেমেরই জয় হবে, সবাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের জগতে শান্তিতে বসবাস করতে চলে যাবে। দর্শক জানে এসব কথা। আবার সাচ্চা প্রেমের জন্য কেউ ত্যাগ স্বীকার করলে হাপুস নয়নে কেঁদে তারা রুমাল ভেজায়। কাঁদতে লজ্জা পায় না। আগে কতবার দেখেছি হল থেকে বেরিয়ে গিয়েও এরা বিজাতীয় ভাষায় গেয়ে ওঠে, দোস্ত দোস্ত না রহা…। সব শব্দের মানেও বোঝে না। গানের তো ডাবিং হয় না! তবু ওরা গায়।ফিল্ম বাজার কাকে বলে তা জানলাম সেদিন। “দোম কিনো” বলে একটা সিনেমা হল এবং তৎসংলগ্ন ফিল্ম সংক্রান্ত অফিসে আমিই ট্যাক্সি করে নিয়ে গেছি তারাচাঁদবাবুকে। শত হলেও ইনি আমাদের অতিথি, স্টুডেন্ট হতে পারি, কিন্তু এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যেন তিনি আমার দেশে বেড়াতে এসেছেন, উজবেকিস্তান তো আমার দেশ নয়, কেন এমন মনে হল তবু!
ফিল্মের বাজার চলছে দুটো কি তিনটে ঘরে, তার মধ্যে একটা ঘরে লোক বেশি। ছোট স্ক্রিনে এক একটা ফিল্মের ছোট ছোট অংশ দেখানো হচ্ছে, হিন্দি এবং বাংলা। যারা পছন্দ করবে বলে বসে আছে তারা এই দুটো ভাষার একটাও বোঝে না, সীন দেখে আগ্রহী হলে বলে —অনুবাদ করে দাও, কী গল্প এই সিনেমার? আমি যতটা পারি রাশিয়ানে বলে দিই। কুঠার তাদের পছন্দ হয় নি। কুঠারে নাচ গান নেই, ফাইট নেই, তারা মন্তব্য করে নিজেদের মধ্যে, সে মন্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে দিই নি আমি তারাচাঁদবাবুকে। আরও অনেকগুলো ফিল্ম রয়েছে সেগুলো বিক্রির ব্যাপারেও তারাচাঁদবাবুর ভূমিকা বা দায়িত্ব রয়েছে দেখলাম। ফিল্মগুলো রিজেক্টেড হতে দেখে তারাচাঁদবাবুরা ইংরিজিতে অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন, হয়ত আমার রাশিয়ান অনুবাদকে সাবস্ট্যান্ডার্ড ভেবে থাকতে পারেন, বিক্রি করাটা আসল উদ্দেশ্য, ওঁরা মরিয়া হয়ে উঠছিলেন। পাশের ঘরে কিছু অন্য ভাষার ফিল্ম টপাটপ বিক্রি হয়ে গেছল। যে ছবিগুলো ওঁদের পছন্দ হচ্ছিলো সমস্তই খুব কালারফুল, নাচে গানে সুন্দর লোকেশানে সমৃদ্ধ। কীভাবে যে সময় কেটে যাচ্ছিল তা বোঝা যায় নি। সেদিন লাঞ্চ হয় নি। আমি এমনিতেই তখন দেশে যাবার টিকিটের জন্যে পয়সা বাঁচিয়ে দিনে একবার খেতাম, সাত আট মাসে চোদ্দ কিলো ওজন কমে গেছল। তারাচাঁদবাবুর মন মেজাজ খুব একটা ভাল ছিল না, একটা ব্রেক নিয়ে দোম কিনোর পাঁচতলার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। উনি সিগারেট খাচ্ছিলেন, হাতের কব্জিতে অনেক পাথর টাথর বসানো রিস্ট ওয়াচ। এই রিস্টওয়াচ নবাগত নায়কের বাবা উপহার দিয়েছে ওঁকে, অনেক দাম সেই ঘড়ির, তিরিশ নাকি চল্লিশ হাজার টাকা। কি মনে হয়ে হয়েছিল, বলেছিলাম, এত দুর্ভিক্ষ সমাজ চেতনা গরীব দুঃখীদের নিয়ে সিনেমা বানান এদিকে চল্লিশ হাজারের রিস্ট ওয়াচ পরেন। উনি করুন চোখে তাকিয়ে রইলেন, না পরলে নায়ক দুঃখ পাবে, নইলে সস্তার ঘড়িই তো পরি বিশ্বাস করো। আমি ঘড়িটা দেখতে চাইলাম, উনি খুলে দিলেন। ঘড়িটা হাতে নিয়ে বললাম, এবার এটা নীচে ফেলে দিই? নীচে ঐ যে ফোয়ারাটা রয়েছে সেটার ওপর তাক করে ছুঁড়ছি। উনি কাতর হয়ে বললেন, তবে সময় দেখব কীকরে, আমার তো আর ঘড়ি নেই। আমিও যুক্তিবাদী, বললাম, ঐ দেখুন রাস্তার ওপারে গাছের সারি, তার পেছনে একটা দোকান আছে, ওখান থেকে সবচেয়ে সস্তার ঘড়ি কিনে দেব আপনাকে, খুব সস্তা, কিন্তু সময় দেখাবে, ফেলে দিই এটা এখন? তারাচাঁদবাবু চুপ করে গেছলেন, একটু পরে বললেন, ঘড়িটা দাও, ঐ দোকানে কী পাওয়া যায়, চলো দেখি।
ফিল্ম বাজার আরও চলেছিল, আমরা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা অবধি ছিলাম। রাস্তার ওপারের সেই দোকানটায় গেছলাম তারপর। সেখানে ঘড়ি দেখা হয় নি, তারাচাঁদবাবুর চোখ চলে গেছল টপ শেলফে রাখা মুভি ক্যামেরাগুলোর দিকে। দাম ছশো থেকে হাজার রুবলের রেঞ্জে। উনি হিসেব করছিলেন ডলারে কত পড়বে। বিক্রেতাকে অনুরোধ করে ক্যামেরাগুলোর পুস্তিকা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছিলেন তিনি। সমস্ত রাশিয়ানে লেখা হলেও স্পেসিফিকেশনগুলো সংখ্যাতেই লেখা থাকে। কিনতে চাইছিলেন একটা মুভি ক্যামেরা। হয়ত যথেষ্ট ডলার ছিল না সঙ্গে, বলেওছিলাম যদি ব্ল্যাকে ভাঙাতে চান ব্যবস্থা করে দিতে পারি, সরকারি রেটের বিশ গুণ বেশি পাবেন, কিন্তু দিল্লিতে পারবেন কি কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বের করতে? উনি বলেছিলেন সেসব হয়ে যাবে, এত সব স্টারেরা ফিরবে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই হবে, ওদের কেউ চেক করে না। শেষে ফিরিয়ে দিলেন বুকলেটগুলো হয়ত যথেষ্ট টাকা পয়সা ছিল না সঙ্গে, কিংবা মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। ওঁকে হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় ঐ হোটেলেরই কাছে একটা কাফেটেরিয়ায় কফি ও সসেজ খেয়েছিলাম আমরা। আমার সঙ্গে ছিল কিছু জিনিস কলকাতায় আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য, একটা রেলগাড়ির নিখুঁত মডেল ও এক টুকরো ড্রেস মেটিরিয়াল। উনি নিজেই বলেছিলেন প্রথম দিন, যদি চিঠি পৌঁছে দিতে হয় বাড়িতে কি ছোটখাট কিছু গিফট, সেইজন্যই এনেছিলাম সেগুলো। কাগজে লিখে এনেছিলাম বাড়ির ঠিকানা। আমরা তখন উত্তর কলকাতার হালসিবাগানে থাকতাম। হোটেলে ঢুকবার মুখে গডউইনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গডউইন কে ডেকে নিয়ে তিনজনে গেলাম ওপরে ওঁর রুমে। জিনিসগুলো দিয়ে একটু বসেছিলাম আমরা। উনি আর দুদিন পরেই ফিরে যাচ্ছেন। উনি আমার পাশে বসেছিলেন খুবই ঘেঁষে, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি কিন্তু মুখোমুখি বসে গডউইন লক্ষ্য করছিল। উনি হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে ক্যাজুয়াল কথা বলছিলেন, আমার অস্বস্তি লেগেছিল, কিন্তু ভেবেছিলাম হয়ত এ আমার মনের ভুল। গডউইন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ওকে স্যার, উই শুড লীভ নাও, আপকো তো রেস্ট লেনা হ্যায়। তারাচাঁদবাবু বিড়বিড়িয়ে কী বলছিলেন সব আমার কানে যায় নি। একটা কথা কানে ঢুকেছিল, এই ছেলেটাকি তোমার বয়ফ্রেন্ড? না তো, ও আমার বয়ফ্রেন্ড কেন হবে! উনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। বাইরে বেরিয়ে গডউইন বলেছিল, আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইয়োর সিচুয়েশন, মহোল দেখকে চলনা। আমার মনে তখনও সংশয় ছিল, সারাটা দিন যার সঙ্গে ঘুরলাম এত জায়গায়, কত গল্প করছিলেন নিজের জীবনের, বৌ প্রেম দুই পুত্র সাফল্য ব্যর্থতা সিনেমার জগতের কথা, এমনকি আমাকে সরাসরি অফারও দিয়েছেন ওঁর ফিল্মে অভিনয়ের, আমিই বরং প্রত্যাখান করেছি, বলেছি আগে তো বিষয়টা শিখব তারপরে তো কাজ করব। উনি বলছিলেন কলেজে ইন্সটিটিউটে কতটা শেখাবে শিখতে হয় হাতে কলমে, তারপর অন্যমনস্ক হয়ে নিজের কথা তুলেছিলেন, দেখ না আমিই তো এ জিনিস পড়ব বলে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিলাম, সেখানে পড়া হল না, লাভের মধ্যে কেবল বিয়েটা হল। প্রায় আমার বাপের বয়সী একটা লোক, ওঁর ছেলে তো আমার বয়সী, আরেক ছেলে অসুস্থ তা ও বলেছিলেন, তিনি কি সত্যিই আমার গা ঘেঁষে বসে কাঁধে হাত দিয়ে আবোলতাবোল বকে যেতে পারেন? আমার কান্না পেতে থাকে। বলি, গডউইন বড্ড টায়ার্ড লাগছে, তুই আমাকে একটু পৌঁছে দে না আমার হস্টেলে।
জুনের গোড়াতেই আমাদের সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। পাশের খবরও সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাচ্ছিলাম। এদেশে তিন রকমের নম্বর হয়। টায়েটুয়ে পাশ করলে তাকে বলে তিন, ভাল করলে চার, খুব ভাল করলে পাঁচ। এছাড়া ফেল করলে তাকে কোনও নম্বর দেওয়া হয় না, কিন্তু দুই বলতে ফেল বোঝায়। একটা জিনিস বুঝে গেছলাম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড টার্ড আর নেই। এ জিনিস হজম করতে প্রথম দিকে অসুবিধে হয়েছিল, অসুবিধে তো নরম করে বলছি, রীতিমতো কষ্ট হয়েছিল, অ্যাডিকশান কাটানোর মত কষ্ট। ছোটবেলায় দূরসম্পর্কের এক কাকা, সতুকাকা আসত আমাদের বাড়ি। সতুকাকার ছিল নেশা, অ্যাডিকশান, রেস খেলত সে নিয়মিত। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও তার নেশা কাটানো যায় নি, শনিবারে তাকে কিছুতেই কলকাতার বাইরে রাখা যেত না, টাকা না থাকলে শনিবারে সে ধার করতে বেরতো আত্মীয় বন্ধুদের কাছে। এদেশে এসে আমারও প্রথম দিকে নিজেকে রেসুড়েদের মতো লেগেছিল, পরীক্ষা মানে শনিবার এগিয়ে আসছে, মাথার ভেতর পাগলা ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে ছুটতে চায়, অথচ আগাগোড়া রেস কোর্সটাই লোপাট হয়ে গিয়েছে। সেই মাধ্যমিকের টাইম থেকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ঘোড়দৌড়ের রেসে। ডিভিশন, স্ট্যান্ড করা, লেটার, স্টার, কতগুলো লেটার, কত বেশি নম্বর, অমুকের চাইতে কত নম্বর কম বা বেশি, কীরকম কায়দা করে উত্তর সাজিয়ে লিখলে বেশি নম্বর দেবে পরীক্ষক, ক্রমাগত প্রিটেস্ট টেস্ট ফাইনালের তামাশা। কে কার কান ঘেঁষে আধ ইঞ্চি বেশি নম্বর পেয়ে বেরিয়ে গেল, কে পারল না, যে পারল না তাকে লোক দেখানো হায় হায়, ইশ, আহা উহু, ভেতরে ভেতরে অন্যের কম নম্বরে নিজের শাডেনফ্রয়েডে। এই রেস শেষ হয় না, ফের উচ্চমাধ্যমিক, আরও কড়া রেস, আরও উন্নত জকি চাই, দৌড়ের নেশা রক্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অজান্তে কার্বন মনোক্সাইডের মত, যতক্ষণে না মেরে ফেলছে কেউ টের টি পাবে না, সম্পূর্ণ সিম্পটমহীন নেশা। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রথম কয়েকটা পত্র দেবার পর আর পরীক্ষা দিতে ভাল লাগেনি, ছেড়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু জকির চাকরিতে যে ঢুকেছে সে কি অত সহজে পার পায়? বেটিং করছে শুভানুধ্যায়ীরা, তারা তো অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দৌড়ে জিতি বা না জিতি, মাঝ পথে থেমে যাই বা না যাই, স্বতঃসিদ্ধের মত জানতাম দৌড়নোই একমাত্র পথ, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে এসে সেটাই প্রথম ধাক্কা। মহানগর সিনেমার সেই সীনটা মনে পড়ত, মাধবী অফিস যাবার আগে দাওয়ায় খেতে বসেছেন, ননদের ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ি উঠোনের কলঘর থেকে উঁকি মেরে জিগ্যেস করে, বৌদি পালং শাক খেয়েছ? বৌদি বলে, পাশ করে গেছিস। ননদ বলে, শুধু পাশ! আমারও সেরকম অবস্থা, শুধু পাশ! সবার স্টেটাস “পাশ” করা কেন হবে? এত শ্রেণী বিভাজন তোমাদের সমাজে, কৃষক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী বুদ্ধিজীবি শ্রেণী, অথচ পড়াশোনা থেকেই শ্রেণীটুকু তুলে দিল। কীকরে প্রমাণ করব শ্রেষ্ঠত্ব, কীরকম গোদা সিস্টেম, দৌড়নোর চার্মটাই নেই, উইথড্রয়াল রিয়্যাকশানে কাতরাতে থাকি ভেতরে ভেতরে। ক্রমশ মেনে নিতে হয়, মেনে না নিয়ে উপায় নেই। দৌড়নোটা বাধ্যতামূলক না হওয়াটা যে অভিশাপ নয়, তা বুঝতেও সময় লাগে। প্রাচুর্যের ঘরে ফেলে ছড়িয়ে খাবার মত। তোমার যা খুশি পড়ো, মোটামুটি যোগ্যতা থাকলেই চলবে। সব জানা থাকলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আর শিখবে টা কী? যদি পরে মনে হয় এ বিষয়ে তুমি আগ্রহ পাচ্ছ না, কি বিষয়টা আয়ত্ব করা তোমার পক্ষে মুশকিল, তাহলে ছেড়ে দিলেই হবে। অন্য কিছু শিখো, অন্য প্রোফেশন বেছে নিও। সেই মত চাকরি করবে। চাকরির অভাব নেই দেশে। হ্যাঁ এইটাই কথা, চাকরির অভাব নেই দেশে। সেভাবে বড়ো চাকরি ছোট চাকরি বলে খুব একটা বিভেদ নেই, আবার আছেও। সে প্রসঙ্গ পরে হয়ত আসবে। একজন শিক্ষিকার স্বামী হয়ত কারখানার শ্রমিক, কিংবা একজন সেলসম্যানের বউ বাসের ড্রাইভার। চাকরি নিয়ে যে পরিমান কাস্ট সিস্টেম ইন্ডিয়ায় দেখে এসেছি তাতে এরকম পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হত। ক্যাশিয়ারের বউ কেন ট্রলিবাস চালাবে? ক্যাশিয়ার তো হোয়াইট কলার জব, মানে তথাকথিত ভদ্রলোকের চাকরি, তার বউ কিনা ট্রলিবাস চালাচ্ছে! কায়িক শ্রমের কাজ, ব্লু কলার জব। ক্যাশিয়ার কোনও অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করা বউ পেল না? এদের আয়ের অঙ্কে সেরকম কোনও তফাৎ ছিল না। ছোটবেলা ট্রামের ড্রাইভার হতে চেয়েছিলাম। হতে পারিনি। ট্রাম কোম্পানীতে মেয়েরা চাকরি করত না, ড্রাইভার কন্ডাক্টর চেকার ডিপোর কর্মচারী কেউ মেয়ে ছিল না, একজনও নয়। সোভিয়েত দেশে দলে দলে মেয়ে বিশাল বিশাল বাস চালাচ্ছে, ট্রাম, ট্রলিবাস সব চালাচ্ছে, দেখে আনন্দ হয়েছিল, সত্যিকারের আনন্দ। বিশ্বাস করেছিলাম এর নামই সমানাধিকার। নতুন জিনিস দেখলে যেমন ঘোর লাগে চোখে, তেমনি ঘোর। সময়ের সঙ্গে চোখ সয়ে আসে, খুঁটিয়ে দেখার চোখ তৈরী হয়, এত সমানাধিকারের মূলে কী তা একটু একটু জানা যায়। তবে শিক্ষা কখনই প্রিভিলেজ ছিল না। নইলে এতগুলো দেশ থেকে গাদা গাদা ছাত্র আনিয়ে বিনামূল্যে পড়ানো, খাইয়ে দাইয়ে রাখতে পারে? কেন করছিল এত সব ওরা? কী লাভ হচ্ছিল এতে? অনেক বছর পরে একটা বাঙালি মেয়ে এই নিয়ে স্মৃতিচারণা করবে বলে নয় নিশ্চয়। এমনও তো নয় যে এই শিক্ষার সুফল ওরা সরাসরি পাবে, বিদেশি ছাত্রগুলো ওদেশেই কাজ কর্ম করে ওদের ফিরিয়ে দেবে এই শিক্ষার খরচ। বিদেশিদের পক্ষে নাগরিকত্ব পাবার কোনও পথ খোলা ছিল না, সোভিয়েত দেশের নাগরিককে বিয়ে থা করলেও নাগরিকত্ব পাওয়া যেত না সহজে। তবে কেন এই বিশাল খয়রাতি? সবই কি বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্য? এসব শুনলে রেসের ঘোড়াও দৌড় ভুলে ফিক করে হেসে দেবে।
আমাদের হস্টেলে একজন চৌকিদার কাজ করতেন যিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেটেরান। পুরুষ নন, মহিলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উনি তরুণী। তা ১৯৮৫-৮৬ নাগাদ ওঁর বয়স কম বেশি নব্বই বছর। বন্দুক নিয়ে লড়াই করেন নি, কিন্তু টেলিফোন টেলিগ্রাফের লাইন টাইনে কীসব যেন করতেন, শত্রুপক্ষের খবরাখবর জানার ব্যাপারে। খুব বেশি লেখাপড়া শিখেছেন বলেও মনে হয় না। ১৯১৭য় রুশ সাম্রাজ্যের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর উনি রাশিয়াতেই ছিলেন সেই পূর্ব ইয়োরোপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সম্ভবত টেলিফোনের সেই কাজই করেছিলেন। কবে কখন কীভাবে কেন মধ্য এশিয়ার তাশকেন্তে এসেছিলেন তা জিগ্যেস করা হয় নি। দুরকমের পেনশন পেতেন, যুদ্ধের ভেডেরান হিসেবে এবং অবসরের বয়স হয়ে যাবার জন্য, তা সত্ত্বেও চৌকিদারের চাকরি করতেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আইনত নারীপুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি পেলেও রাতারাতি মেয়েরা পুরুষের মত কাজ সমানে সমানে কাজ করেনি, অন্তত সর্বস্তরে তো নয়। হ্যাঁ যুদ্ধের জন্য প্রচুর পুরুষের মৃত্যু হয় দেশে। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা সংখ্যায় অনেক কম গিয়েছিল যুদ্ধে। ঐ যুদ্ধের কারনেই দেশে পুরুষের সংখ্যা কমে যায়, তারা যে কাজগুলো করত সেসব কাজের দায়িত্ব মেয়েদের দেওয়া হয়। অনেক পুরুষই যুদ্ধে মারা যায়, নারী পুরুষের অনুপাত খুব বেড়ে যায়, তখন মেয়েরা সব কাজই করত, নইলে দেশ চলবে না, সব থেমে যাবে। সেই ভাবেই দ্রুত মেয়েদের গ্রহন করা হয়েছে “পুরুষালি” কাজে, তবুও পার্টির উচ্চপদে মেয়েদের প্রায় দেখাই যেত না। সেই পদগুলোয় ক্ষমতা পাওয়া যায় অনেক, পনেরোটা রিপাবলিকের একটাতেও কোনও মেয়ে সর্বোচ্য ক্ষমতাসীন হয় নি। বরং দশ সন্তানের জননী হলে সেই নারীকে হিরোর সম্মান ও সুযোগ দেবার নিয়ম ছিল। হ্যাঁ, নারীর নিজের শরীরের ওপর অধিকার ১৯১৮ সালেই স্থাপিত হয়েছিল, সন্তানের ওপর অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, বিবাহবহির্ভূত সহবাস, ইত্যাদি। স্তালিনের আমলে এসব আইনের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। এ সবই পুঁথিগত তথ্য, বাস্তবের গল্প আস্তে আস্তে আসবে এই লেখায়। রঙচঙে সোভিয়েত নারী পত্রিকায় সেসব গল্প ছাপার যোগ্য হিসেবে বিবেচ্য হয় নি। সেই সব সোভিয়েত নারীদের সঙ্গে সুখে দুঃখে কাটিয়েছি দশটা বসন্ত, তারা কেউ রাশিয়ান, কেউ উজবেক, কেউ তাতার, আবার কেউ জার্মান।
টাকা পয়সা যেটুকু জমাতে পেরেছিলাম তা দিয়ে টায়ে টুয়ে দেশের যাতায়াতের টিকিট কেটে ফেলা গেল স্টুডেন্টস কনসেশনের ৩০% ছাড়ের জন্য। রুটটাও সংক্ষিপ্ত। তাশকেন্ত-দিল্লি-তাশকেন্ত। এই রুটে ব্যবসা বানিজ্যের কোনওরকম সুযোগ নেই। অর্থাৎ ছুটির পর তাশকেন্তে ফিরে আমায় ফের পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে স্টাইপেন্ডের ওপর। কলকাতায় পৌঁছে বাড়িতে কিছু দুঃসংবাদ জানতে পারলাম, সে সব খবর চিঠিতে জানিয়ে আমার বিদেশবাস দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত করতে চায় নি নিকটাত্মীয়েরা। নিজেকেও খুবই স্বার্থপরের মত লেগেছিল কিছু করতে পারছি না বলে। অবশ্য করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। দুমাসের ছুটি ছিল, একমাসও থাকতে পারিনি কলকাতায়, তাশকেন্তের জন্য মন কাঁদত। সে ও এক ধরণের হোমসিকনেস। চৌরঙ্গীর আয়েরোফ্লোত (Аэрофлот) অফিসে গিয়ে সরকারদাকে দিয়ে টিকিটের তারিখ এক মাস এগিয়ে আনি। দেখা করতে গেছলাম তারাচাঁদবাবুর বাড়ি। উনি সেই রেলগাড়ি ড্রেস মেটিরিয়ালে মুড়ে নিজে হাতে পৌঁছে দিয়ে গেছলেন, একটা ধন্যবাদ দিতে হয়, এবং মনের মধ্যে খচখচ করছিল যে জিনিসটা সেটারও হেস্তনেস্ত হবার দরকার ছিল। আমার বন্ধু রানা তারাচাঁদবাবুর পাড়ার কাছেই থাকত। রানাকে নিয়ে একদিন সকালে পৌঁছে গেছলাম ওঁর বাড়ি। সে এক নাটকীয় সকাল। আগের রাতে ভগ্নীপতিকে দাহ করে শ্মশান থেকে সবে ফিরেছেন তিনি। বৈঠকখানায় বিষন্ন মুখে বসে আছেন, রাত জাগার চিহ্ন ওঁর সারা মুখে। ওঁকে ঘিরে ইতি উতি বেশ কয়েকজন লোক, কেউ অতিথি, কেউ মোসায়েবি করছে, প্রত্যেকেরই আসার উদ্দেশ্য ভিন্ন। রানা ও আমি দরজার কাছটায় দাঁড়িয়েছিলাম। একজন বলছিল যে একটা বাচ্চা জোগাড় করা হয়েছে। তারাচাঁদবাবু জানতে চাচ্ছিলেন বাচ্চাটার সাইজ কতটা, বাচ্চাটা ফর্সা না কালো। লোকটা মাথা নীচু করে দুহাত বাড়িয়ে সাইজ বোঝালে মনে হল নবজাতকের মত, অস্পষ্ট স্বরে সে বলল, তেমন ফর্সা নয় একটু পাউডার মাখালেই—। তুমুল রেগে গেলেন তিনি। ফর্সা বাচ্চা চাই, বললেন, বড়োদেরই পাউডার মাখাচ্ছি না তো বাচ্চাটাকে পাউডার মাখাব নাকি! বোঝা গেল নতুন বইয়ের শুটিং চলছে, কোনও ফর্সা বাচ্চার রোল আছে। আমরা এসব দেখছিলাম, তারপর তিনি আমাদের দেখে ডেকে বসতে বললেন। ঘর ভর্তি একগাদা অচেনা লোকের সামনে আমার প্রশংসা করতে শুরু করে দিলেন, মেজাজ অল্পক্ষণের জন্য একটু ভাল হল, তারপর আবার যেই কে সেই, একজন যুবক কী যেন বলতে গেছল জোর ধমক খেল। আর বসিনি সেখানে। মনের মধ্যে যে সংশয় এবং প্রশ্ন বয়ে বেড়াচ্ছিলাম তার উত্তর সেদিনের কথাবার্তার মধ্যেই পেয়ে গেছি। রানাকে সেজন্যই সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। উনি বার বার করে যেতে বলছিলেন অন্য দিন। ওরেব্বাবা, আর কখনও ওমুখো হই!
ছুটিতে বাড়ি ফিরবার খবর শব্দের বেগে ছড়িয়ে গেছল বন্ধুদের মধ্যে। তপন, কল্লোল, পুরুষোত্তম, রানা, সবার প্রথম প্রশ্ন— ভোদকা এনেছিস? আনিস নি! সে কী হতাশা ওদের। তার পরে একের পর এক প্রশ্ন, ব্রেইন ওয়াশ হয় কিনা, রাশিয়ান মেয়েদের দেখতে কতটা সেক্সি, শুনেছি ওরা নাকি খুব ফাস্ট (জানতে চাইছিল চাইলেই শুয়ে পড়া যায় কিনা), টিকিটের দাম কে দিল, চেরনোবিলের দুর্ঘটনার* জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা, এত রোগা হলি কীভাবে, মদ খাস, ওখানে খুব মাংস আর রুটি খাস না রে? অনেক প্রশ্নেরই উত্তর জানতাম না, যেমন ব্রেইনওয়াশেরটা। সিনেমায় দেখা হীরক রাজার দেশের সেই মগজ ধোলাইয়ের মেশিন সত্যি হয় কিনা জানতাম না। কমিউনিস্টরা কী পদ্ধতিতে মগজ ধোলাই করে? উত্তর দিতে না পেরে লজ্জা করে। চেরনোবিলের ব্যাপারটাও দেখলাম ওরা অনেক বেশি জানে। ন দশ মাসের বিদেশবাসের মধ্যে রুটি মাংস খেয়েছি কবে মনেই পড়ল না, পোলাও খেয়েছি কয়েকদিন, ওদের বলতে ইচ্ছেই করল না। আরও প্রশ্ন ছিল ওদের মনে, আমি “ফাস্ট” বনে গেছি কিনা। হয়ত ঐ বয়সে এসব প্রশ্ন করাই স্বাভাবিক। দশটা মাস অন্য দেশে কাটিয়ে এসে কেমন যেন মনে হচ্ছিল দেশটা পাল্টে গেছে, বন্ধুগুলো বদলে গেছে, বা হয়ত আমি নিজেই বদলে যাচ্ছি দ্রুত। কিছু পুরোনো অভ্যাস ভুলে গেছলাম, নিজের শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করা। গত দশটা মাসে রাস্তায় বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে কোনও লোক গায়ে হাত দেয় নি ভিড় থাকুক বা না থাকুক, “আওয়াজ” খাওয়া হয় নি কত দিন হয়ে গেছে, সোজা হয়ে হাঁটার অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে, কলকাতায় ফিরে এসে টের পেলাম সেসব ছুটিতে।
দিল্লি থেকে যখন ফ্লাইটে উঠছি তখন রাত অনেক। সাড়ে তিনশো যাত্রীর মধ্যে শুধু একজন নামবে তাশকেন্তে, উজবেকিস্তানের ঘড়িতে তখন বাজবে দেড়টা।
আগেভাগে নামতে হবে বলেই দরজার সামনে বসেছি। আয়েরোফ্লোতের বিমানে কোনও সীট নম্বরের ব্যাপার নেই, যার যেখানে পছন্দ বসবে। কে কোথায় বসে এ নিয়ে মনোমালিন্য বিবাদও হয় না। আমার পাশে দুটো সীট খালি। গেট বন্ধ হবার ঠিক আগে হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন একজন। দেখেই কেমন একটু চেনা চেনা লাগল, মাঝ বয়সী বাঙালী ভদ্রলোকটি তো আমার চেনা। কলকাতায় দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার, উনি একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের অনারারি কনসাল। ভদ্রলোকও আমাকে দেখে চিনতে পেরে গেলেন, প্রোফেসর অনিল ধর। আমার পাশেই বসে পড়লেন প্রোফেসর ধর।
— কী ব্যাপার, তুমি চলেছ কোথায়, মস্কো?
— না, অতদূর যাব না, সওয়া তিন ঘন্টার পথ, সামনের স্টপেজেই নেমে যাব।
গোটা দিল্লিতে একজনও চেনা লোকের দেখা মেলেনি, ডিপার্চার গেটের সামনে যত জন অপেক্ষা করছিল, ঘুরে ঘুরে সকলের মুখ দেখেছি যদি চেনা কেউ বেরিয়ে পড়ে, পাশের যাত্রীর সঙ্গে আলাপ আড্ডা দিতে দিতে যেতে না পারলে সাড়ে তিন ঘন্টা করব টা কী? অথচ এরকম অভাবনীয় ভাবে যে চেনা পরিচিত সহযাত্রী পেয়ে যাব কে জানত! প্রোফেসর ধর যে আসলে অধ্যাপনা করেন না সে সব কলকাতায় থাকতেই জেনেছিলাম। প্রথম জীবনে কিছুকাল অধ্যাপনা করলেও, পরে উনি প্রোফেশন পাল্টে ব্যবসায়ী বনে গেছেন। তখন সবে আমার প্রথম বিদেশ যাত্রার দিন ক্ষণ ঠিক হয়েছে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম আনন্দে, ওঁর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল কোনও একটা অনুষ্ঠানে, তখনই উনি ওঁর কার্ড দিয়েছিলেন। ক্যামাক স্ট্রীটে ওঁর অফিসেও একবার গেছলাম এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, কফি খাইয়েছিলেন আমাদের। কারও অফিসে গিয়ে কফি খেতে পাওয়া ছিল এক দারুণ সম্মানের ব্যাপার। সে এমন এতটা বয়স, যখন লোকে আমাদের মাঝে মাঝে আপনি বলে সম্বোধন করে ফেলছে। ইনিও প্রথমে আপনি আপনি করলেও অল্প পরেই তুমিতে চলে এসেছিলেন। সেই ভদ্রলোক কি না আজ আমার সহযাত্রী! উনি চলেছেন প্রাগে। মস্কোতে ফ্লাইট বদলাতে হবে। প্রাগ থেকে যাবেন লন্ডন, সেখানেও ব্যবসার নানারকম কাজ মিটিং ইত্যাদি আছে। অনেক গল্প করতে লাগলেন। দিল্লিতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন শুধু এই কারণে যে ব্যবসার কাজে বারবার দিল্লিতে যাতায়াত করতে হয়, বিদেশ যাত্রা করবার জন্যও দিল্লি খুব দরকারি। এয়ার হোস্টেসদের ডেকে ডেকে বেশ কয়েকবার মদ চেয়ে চেয়ে খেয়ে একটু পরেই ওঁর চোখের দৃষ্টি চকচকে হয়ে উঠল। টয়লেট থেকে যখন ঘুরে এলেন, গায়ে ভুরভুর করছিল ওডিকোলনের গন্ধ। গা ঘেঁষে বসছিলেন। অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে চলছিলেন। এই ধরণের ব্যবহার আমি কিছুদিন আগেই আর একজন স্বদেশবাসীর কাছে পেয়েছি। বলতে গেলে সেই একই ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ডিনার এলো, অত্যন্ত সাধারণ খাবার, মশলাহীন চিকেন, কালো রুটি, চীজ মাখন কফি। আয়েরেফ্লোতের মশলাহীন খাবার ভারতীয় জিভে রুচবার মত নয়। আমার কিন্তু বেশ লাগছিল খেতে। কেমন যেন মনে হচ্ছিল নিজের চেনা শহর, চেনা রাস্তা, চেনা ঘর, বাতাসের চেনা গন্ধ এগিয়ে আসছে। আর তো মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি। উঠে গিয়ে অন্য সীটে বসব? এয়ার হোস্টেসকে ডেকে বলব যে পাশের যাত্রী অস্বস্তিকর ব্যবহার করছে? মায়া হল লোকটার জন্য। একটু সরে বসলাম। বিদেশে যাবার পথে, কি বিদেশের মাটিতে নেমেই এরা বদমায়েসি করবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। বেচারা লোকটা, এই একটু আগে নিজের দুই ছেলের গল্প করছিল, নিজের বাচ্চাদুটোকে খুবই ভালবাসে, ছেলেরা সেন্ট লরেন্সে পড়ছে, ছোট ছেলে কেমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে রং চড়িয়ে চড়িয়ে ইস্কুলের গল্প করে সেসবও শুনেছি, আবার নেশা হবার ভাণ করে আমার গায়ে ঢলেও পড়ছিলেন প্রোফেসর ধর। এত টাকা পয়সা রোজগার করেছে, অথচ মেয়েদের গায়ে হাত দেবার সুযোগ খুঁজছে, এয়ার হোস্টেসকেও ছাড়ে নি সেসব ও চোখ এড়ায় নি আমার। এর পরে কলকাতায় কখনও দেখা হলে ওকে কি আর সম্মান করতে পারব? আমি সজাগ হয়ে দূরত্ব বজায় রেখে বসে থাকি। একটু পরেই এরোপ্লেন নীচে নামতে শুরু করে। অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে ছবির মত ল্যান্ডিং, আমি উঠে পড়ি। তাশকেন্ত এসে গেছে।
*চের্নোবিলের দুর্ঘটনা। বহুচর্চিত বিষয়। সংক্ষেপে ১৯৮৬র শীতের শেষের দিকে নিউক্লীয়ার পাওয়ার প্লান্টের ছাদ উড়ে যায়। সহজ করে বললে বিস্ফোরণের ফলে ছাদটা উড়ে যায়। তারপরে মাধ্যাকর্ষণের জেরে আগের জায়গায় ফিরে এলেও তেরছা হয়ে বসে। ফলে সেই ফাঁক দিয়ে রেডিয়েশন ছড়াতে থাকে। তাও ভালো যে নিউক্লীয়ার পাওয়ার প্লান্টের ভেতরের চাপ, সব সময় অ্যাটমস্ফীয়ারিক চাপের চেয়ে বেশ কম রাখা হয়, নাহলে রেডিয়েশন অনেক বেশি মাত্রায় ছড়াতো।
কিন্তু কেন এমন বিস্ফোরণ হয়েছিলো? কিছু জায়গা ঠিকমতো ঠান্ডা রাখা যায় নি বলে। কেননা নিয়মিত যে পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের দরকার ছিলো সেটা করা হয় নি। এর ফলে প্রচুর প্রাণহানি এবং শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও পরিবেশের অশেষ ক্ষতি হয়। খবরটা প্রথমে চেপে দেবার চেষ্টা হয়। এদিকে পশ্চিম ইউরোপ অবধি সেই সময়টা দিনের বেলাতেই সন্ধের মতো অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, যেন আকাশ কালো করে মেঘ করেছে, সূর্য দেখাই যাচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপেই প্রথম ধরা পড়ে যে মূল কারণ তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সোভিয়েত দেশ স্বীকার করে চের্নোবিলের দুর্ঘটনা। তারও পরে খবর পায় দেশের ভেতরের মানুষ। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত অনেক রেখে ঢেকে কমিয়ে প্রকাশ করা হয়। আসল ডিটেল ১৯৯৩-৯৪ নাগাদ জানতে পারে জনগন। অনেক দেরীতে।
চলবে…
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:১৮735833
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:১৮735833- সব বদলে বদলে যায়গভীর রাতে ইন্টারন্যাশানাল টার্মিনালে একজন, হ্যাঁ মাত্র একজন যাত্রী নেমেছে। টার্মিনালের লম্বা লম্বা করিডোরগুলোর আলো নেভানো। অনেকটা পর পর ক্ষীণ আলো যেটুকু জ্বলছে তাতেই পথটুকুর আবছা আন্দাজ পাচ্ছি, একটাই পথ তাই ভুল হচ্ছে না। দীর্ঘ পথের শেষে ইমিগ্রেশনের কাউন্টার। কেউ নেই। দরজা বন্ধ। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, এবার সেই করিডোরগুলোর আলো পর পর জ্বলে উঠল। ইমিগ্রেশন অফিসার এল। লাগেজ এল। দুজন কাস্টমস অফিসার আমার সুটকেস খুলে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজল বেআইনি জিনিস কিছু আছে কি না। বুঝলাম কেন লোকে এই রুটে যাতায়াত করে না। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাইরেটা ফাঁকা। গভীর রাত। দূরে একটা দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। বড্ড ঘুম পায়। আমার হস্টেল দশ মিনিটেরও কম দূরত্বে। সেখানে পৌঁছে দেখি মেইন গেট বন্ধ। দরজার কাচে দুম দুম করে ধাক্কা মারি, ঘুম চোখে আমায় দেখে সেই বুড়ি চৌকিদার অবাক, —এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি, আরও এক মাস ছুটি আছে তো! আমি সুটকেস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে চারতলা অবধি উঠব কী করে তাই ভাবছি, সে আবার বলে, তোর ঘর তো আর নেই, তোর ঘরে এখন অন্য লোকে থাকছে।
সর্বনাশ করেছে, আমি ঘুমোব কোথায়? বাড়ি যাবার সময়ে যে ঘর খালি করে গেছলাম সে কথা এতদিন মনেই ছিল না, এরা সেই ঘর ইয়ুথ হস্টেলের মত করে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। আমার দুই রুমমেট যারা গরমের ছুটিতে লাওস যেতে পারেনি, বা যারা আফ্রিকা কি লাতিন অ্যামেরিকার মত দূর দেশ থেকে এসেছে তারাও টিকিট কিনতে পারেনি, তারাই রয়ে গেছে হস্টেলে। কেউ কেউ অন্য শহরে বেড়াতে গেছে। সে রাতটা সিঁড়ির ধাপে বসেই কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে পাদফাকের অফিস খুলল। সেক্রেটারি লোলা মিষ্টি হেসে বলল কোনও চিন্তা নেই, তুমি চিয়াত্রালনি ইন্সতিতুতে চলে যাও, এই নাও কাগজ, ওখানেই তোমায় হস্টেলে ঘর দিয়ে দেবে আজ।জিনিসপত্র চৌকিদারের কাছে রেখে টুক করে দোমব্রাবাদের মেডিকেল হস্টেলে চলে যাই, যদি কেউ থাকে। সবাই গরমের ছুটিতে হয়ত দেশে যায় নি। ডাক্তারিতে সবাই সব বিষয়ে পাশ করতে পারে না, পাশ না করলে বাড়ি যাবার পার্মিশান পাওয়া যায় না। যা ভেবেছি, গোটা চার পাঁচ ভারতীয় ছাত্র হস্টেলের গেটের সামনে গুলতানি করছিল, আমায় দেখতে পেয়ে তাদের ভূত দেখার মত মুখ হয়ে গেছে। দেড় দুদিন যাবদ আমার একই পোশাক এবং চুলটুল না আঁচড়ানো চেহারা, ঘুমও হয় নি, দিল্লির গরম, ফ্লাইটে বদমাশের পাশে তিন ঘন্টা, তারপরে গভীর রাতে কাস্টমসের সঙ্গে মোকাবিলা, ঘর বেহাত হয়ে সিঁড়িতে রাত কাটিয়ে অবশেষে নতুন হস্টেলে ঘর পাবার কাগজ হাতে পেয়েছি, কিন্তু সমস্ত জিনিস নিয়ে অচেনা হস্টেলে একা যাবার শক্তি নেই। দুজন তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল। পঙ্কজ এবং অজয় কুমার ঘোষ। আধ ঘন্টার মধ্যে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চিয়াত্রালনি ইন্সতিতুতের সামনে। ইন্সটিটিউটের অফিসে আমার অ্যাডমিশনের কাগজ জমা দিলাম। সেক্রেটারি ভদ্রলোক কীসব রেজিস্টার খুলে দেখলেন, এদিক ওদিক খুচখাচ কাগজ গোছালেন, তার পরে আমাকে জিগ্যেস করলেন আমি উজবেক ভাষা জানি কি না। জানি না। উনি বললেন তাহলে তো এবছর হবে না। তার মানে! আমরা তিনজনেই সমস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছি। জানা গেল, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, প্রত্যেক বছর রাশিয়ান ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয় না, এক বছর অন্তর করে রাশিয়ানে পড়ায়। এবছর উজবেক ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হবে। তাহলে কী উপায়? আমরা ফিরে চলি পাদফাকে। লোলা আমাকে দেখে অবাক হয়, আমাদের আরেকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডীন লারিসা গ্রেগরিয়েভনা তখন সেখানে উপস্থিত। হড়বড়িয়ে সব বোঝাতে গিয়ে প্রথমে গুলিয়ে গেলেও উনি বুঝতে পারেন, ফোন করেন চিয়াত্রালনি ইন্সতিতুতে। আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিছু বুঝতে পারছি না কী করব। ঐ ছেলে দুটো কথা বলছে লোলার সঙ্গে। মিনিট দশেক আলোচনার পর ঠিক হয়, দুটো পথ খোলা আছে আমার। এক, রাশিয়ার কোনও শহরে গিয়ে নাটকে ভর্তি হওয়া, হয়ত তারা আবার পরীক্ষা নিতে পারে, ফলাফল কী হবে তার নিশ্চয়তা নেই, দুই, তাশকেন্তেই আমার পছন্দের অন্য কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করা। এই দু নম্বর অপশন শুনে পঙ্কজ ও অজয় কুমার ঘোষ লাফিয়ে ওঠে, ডাক্তারি পড় ডাক্তারি পড় ডাক্তারি পড়, করে কান ঝালাপালা করে দেয়। আমি শুধু ভাবছি, তাহলে আমার আর এ জন্মে থিয়েটার করা হবে না। কেমন করে করব? এত বাধা। নিজের মাতৃভাষাই এই বিষয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হওয়া উচিত, মানুষের মন নিয়ে কাজ, তবু চেষ্টা করেছিলাম অন্য একটা ভাষা শিখে সেই ভাষায় অভিনয় করবার, তাতেও বিধি বাম। আর কত লড়ব? মন ভেঙে যাচ্ছে। একটা মাস ছুটিতে ছিলাম কোলকাতায়, আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভেবেছি। কয়েকটা আর্ট ফিল্ম দেখলাম, আগের মত সেরকম রোমাঞ্চ অনুভব করিনি, আগে খুব ভাল লাগত। এবার কেমন যেন আলগা আলগা লেগেছে, গল্পের বিষয়বস্তু আগে যেমন নির্ভুল মনে হত, এবার দেশে গিয়ে তেমন লাগে নি, অনেক ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। কেন এমন হচ্ছে? “ভাল মেয়ে” হিসেবে যে চরিত্রগুলো দেখানো হচ্ছে সেগুলো বড্ড ওল্ড ফ্যাশনড ঠেকছে আমার চোখে। আমার বন্ধুরা তাই দেখেই বাহ বাহ করল, আমরা কফি হাউসে বসে আড্ডা মারলাম, ওরা চেরনোবিল জানতে চেয়েছিল আমি বলতে পারিনি, আমি তারাচাঁদবাবুর গল্পটাও ওদের বলতে চাইনি। ছকে বাঁধা কিছু গল্প আছে যেগুলো চলছে, যেগুলো আমার বন্ধুরা তপন, কল্লোল, পুরুষোত্তম, রানা অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, আমিও করতাম ছ সাত আট দশমাস আগে পর্যন্ত। এখন কেমন যেন টান কমে যাচ্ছে, রানাদের বললে ওরা হাসবে, বলবে খুব ফরেন রিটার্নড হয়ে গেছিস এই ক মাসে। কিন্তু তা নয় রে। সমাজতান্ত্রিক দেশে “কুঠার” বিক্রি করা যায় না। মায়ের কাছে মাসির গল্প বলার মত কেস হয়ে যায়।
লারিসা গ্রেগরিয়েভনা আমার কাঁধে হাত রাখেন, কী নিয়ে পড়তে চাও তুমি? এই নাও বুকলেট এর মধ্যে সব কটা বিষয়ের নাম আছে, দেখ কোনটা পড়তে ইচ্ছে করে। আমার কেমন যেন হাসি পায়। এই তো সেদিন ভ্লাদলেন উসমানোভিচ বলছিলেন যে যেদিন কমিউনিজম আসবে সেদিন যার যে প্রোফেশন খুশি সে সেটাই নিতে পারবে, কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। মিখাইল সের্গেইভিচ নাকি সেদিকেই আরও এক পা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশটাকে, হুঁ হুঁ বাওয়া এরই নাম পেরেস্ত্রৈকা, গ্লাসনস্ত। তাহলে কি কমিউনিজম এসেই গেল? বুকলেটটায় চৌষট্টি পৃষ্ঠা, আমি ফরররর্ করে পাতাগুলো উল্টে চোখ বন্ধ করে আন্দাজে একটা পাতায় এক জায়গায় আঙুল রেখে বলি —এইটা!
লোলা বলে, শূন্য ছয় শূন্য আট। আমি চোখ খুলি। ছেলে দুটো ঝুঁকে পড়ে দেখে নেয় শূন্য ছয় শূন্য আট এই কোড নম্বরের অর্থটা কী, পাশে কী লেখা আছে। তারপর পঙ্কজ বলে ফেলে, আরে ইয়ে তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যায়!
আধ ঘন্টা পরে একটা অঙ্ক পরীক্ষা হয় আমার, মুখে মুখে। তাতে উৎরে যাই। লাঞ্চের পর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে যাই আমরা। বিকেলের মধ্যে তল্পিতল্পা নিয়ে ভুজগারাদোক। তিরিশ নম্বর হস্টেলের বি ব্লক, তিন তলা। এই হস্টেলে খুব কম মেয়ে, কোনও ইন্ডিয়ান মেয়ে নেই এই ইন্সটিটিউটে, তবে আরও একজন ইন্ডিয়ান মেয়ে স্টুডেন্ট আছে এ তল্লাটে, সে জার্নালিজমের ছাত্রী গীতা। তার অবশ্য ফিফথ ইয়ার, মানে ফাইনাল ইয়ার। আরও মেয়ে আছে, ফিফথ ইয়ারের ছাত্র লাক্শার সিং এর বৌ পাম্মি মানে পরমিন্দর। সে পড়ে না, তার কোলে এগারো মাসের শিশুকন্যা। আর আর …উঁহু আর নেই। লাক্শার সিং দোতলায় থাকে, তার ঘরে নিয়ে যায় আমায় ঐ দুজন। ওরা সকাল থেকেই সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুরছে, প্রচুর হেল্প করেছে, ওরা না থাকলে এত কিছু একদিনে পারতামই না। সব শুনে লাক্শার সিং হাসি মুখে বলেন, কোনও চিন্তা নেই এটা মেয়েদের সাবজেক্ট, বেশি শক্ত ড্রইং থাকবে না, হাল্কা সাবজেক্ট। পঙ্কজ ও অজয় কুমার ঘোষ দুজনেই তাও চিন্তা প্রকাশ করে। লক্শর অভয় দেন, আরে না না, সহজ ড্রইং থাকবে, মেক্যানিকালের মত কি সিভিল বা আর্কিটেকচারের মত নয়। আমি বোকার মত বলে ফেলি, মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ড্রইং কি খুব শক্ত। লক্শর সিং স্মিত হেসে বলেন, মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ মর্দওয়ালা সাবজেক্ট, নট সুটেবল ফর গার্লস।
দিনান্তে নিজের একটা ঘর, একটা বিছানা পেয়ে মনে হয় আমার বাড়িতে এ খবর শুনলে কত খুশি হবে। ইঞ্জিনিয়ার হব। ইঞ্জিনিয়াররা সবাই চাকরি পায়, গরীব ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে অক্সিমোরোন। ঐ ছেলে দুটোও খুশি আল্টিমেটলি আমার শুভ বুদ্ধি হয়েছে বলে। দেশে যাবার আগে গডউইনরা তো সব চেঁচিয়েছিল, সুন্দরী নই যে মেইনস্ট্রিম সিনেমায় নায়িকার রোলে চান্স পাব, নাটক ওরা বুঝত না, আমারও আর শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। এই যা হয়েছে ভাল হয়েছে। নতুন ঘরে প্রথম রাতে ঘুম আসতে চায় না, জানলায় পর্দা লাগানো হয় নি, রাস্তার আলোয় ঘরের ভেতরটা ভরে গেছে। হলদে কাঠের মেঝে, হলদে কাঠের টেবিল, সাদা দেওয়াল, প্রকান্ড ঘরটা কেমন মরুভূমির মত। লক্শর সিং গরমের ছুটিতে দেশে যায় নি কেন? ফেল করেছে নাকি মর্দওয়ালা সাবজেক্টে? আচ্ছা এই ভুজগারাদোকেই আর একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে ছিল না! সেই যে রান্ডি টাইপ, আহা কী নাম যেন তার, ধুত্তেরি মনে পড়ছে না, নাকি সে অন্য কোথাও থাকে? কী পড়ে মেয়েটা? দীপুদাও তো এই পাড়াতেই। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়াররা কী করে? কম্পিউটার বানায়? কম্পিউটার দেখতে কীরকম হয় কে জানে। কম্পিউটার দিয়ে খুব বড়ো বড়ো অঙ্ক নাকি হুশ করে সেকেন্ডের মধ্যে কষে ফেলা যায়। নেক্সটবার যখন কোলকাতায় যাব বন্ধুদের সামনে খুব রেলা নেব। এক বোতল ভোদকা নিয়ে যেতেই হবে ওদের জন্য, নইলে প্রেস্টিজ থাকে না।
আলো জ্বালিয়ে সিলিং সমান উঁচু কাবার্ডগুলোর দরজা খুলে ফেলতেই নতুন রঙের গন্ধ নাকে এসে লাগল। এ ঘরে তিনটে কাবার্ড। তার মানে তিন জনের জন্য এই ঘর। নেহাৎ গরমের ছুটি চলছে তাই বাকি দুজন এখনও আসে নি। কাবার্ডের মধ্যে রেখেছি আমার কাপড় চোপড়, অন্য জিনিস পত্র। এই হস্টেলটা একেবারে আনকোরা নতুন, মূলতঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএর ছাত্রদের জন্য তৈরী। দোতলাটা বিবাহিত ছাত্রদের দিয়েছে বৌ বাচ্চা নিয়ে থাকার জন্য, তিনতলাটা মেয়েদের। এই ফ্লোরের অধিকাংশ ঘরই ফাঁকা। আমি গভীর রাতে সুটকেস খুলে জিনিস গোছাতে লেগে যাই। হলদে কাঠের টেবিলটা আজ সন্ধেবেলায় নিজে নিজেই বানিয়েছি। নতুন টেবিল, কাঠের টুকরোগুলো হস্টেল থেকেই দিয়েছিল, একটা কাগজে ছক আঁকা ছিল, সেই ছক দেখে দেখেই বানালাম। টেবিলটা সরিয়ে জানলার সামনে নিয়ে যাব ভাবলাম। একটু ঠেলা দিতেই সেটা হুড়মুড় করে খুলে মেঝেয় পড়ে গেল। সর্বনাশ, এখন কী হবে? ভাগ্যিস আশে পাশের ঘরে কেউ নেই, যে পরিমান আওয়াজ হয়েছে তা বলবার নয়। আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ি। কথা বলবার কেউ নেই। কথা বলতে এত ভালবাসতাম আমি, সেই আমার ভাগ্যেই জুটেছে এরকম একটা জীবন। এ ভালো না মন্দ, তা বুঝতে হয়ত সময় লাগবে।
পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু। ইস্কুল ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট সর্বত্র, গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে। অগস্টের শেষে আমার রুমমেট হল একজন উজবেক মেয়ে, সে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী, নাম জেবো। জেবো পড়ছে ফলিত গণিত, রাশিয়ানে যাকে বলে প্রিক্লাদনাইয়া মাতেমাতিকা। জেবো ভাঙা ভাঙা রাশিয়ান বলতে পারে, আমি ভারতীয় জেনে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, তার ধারণা হিন্দি সিনেমার মত আমিও ঝলমলে সাজগোজ করে যখন তখন নেচে নেচে গান গাইব। সে তার আরও দু তিনজন বান্ধবীকে জুটিয়ে এনে আমায় অনুরোধ করতে থাকে নাচতে। অনুনয় বিনয় থেকে ক্রমশ তা হুকুমের লেভেলে পৌঁছে যায়, কিন্তু নাচ তো আমি জানি না, বকা ঝকা এমনকি মারধোর করলেও নাচ আমার দ্বারা হবে না। ওদের ধারণা হিন্দিস্তানের সব মেয়েরাই নাচতে পারে, নাচের ট্যালেন্ট নিয়েই সব ভারতীয় মেয়ে জন্মাচ্ছে। খুবই আশাহত হয় ওরা। আমাদের বন্ধুত্ব জমে না, তা সত্ত্বেও কদিন দু তরফেই খুব চেষ্টা করা হয়। জেবো সপ্তাহখানেক আমার ঘরে ছিল। বিশাল বিশাল চার্ট পেপার, খাতা পত্তর নিয়ে সে তার ফাইনাল ইয়ারের পড়াশোনার পরিবেশ তৈরী করছিল। খুচখাচ গল্প করত। তার একজন বয়ফ্রেন্ডও ছিল যে এলে জেবো বেড়াতে যেত বাইরে। এই জেবোর কাছেই কথায় কথায় জেনেছিলাম উজবেক মেয়েদের বিয়ের পর একরকম পরীক্ষা দিতে হয়, সতীত্বের পরীক্ষা বা বলা যেতে পারে কৌমার্যের পরীক্ষা। খুব গর্ব ভরে সে বলেছিল, মেয়েদের জীবনে এটা খুব গর্বের ঘটনা, এই পরীক্ষায় পাশ করে তারা শ্বশুরবাড়ীর কাছে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করে। আমি উল্টে ওকে বলি, এতো খুব প্রাইভেট ব্যাপার, শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বরবৌয়ের ঘর থেকে রক্তমাখা রুমাল নিয়ে হৈচৈ করছে, সবাই ঝুঁকে ঝুঁকে সেই রক্তের দাগ দেখে নতুন বৌয়ের সতীত্ব যাচাই করছে, এতে তো অস্বস্তি হবার কথা, ছেলেরা কি নিজেদের সতীত্বের পরীক্ষা দেয়? জেবো রেগে যায়, অসন্তুষ্ট হয়, বলে, ছেলেরা কি পেটে সন্তান ধরে, তাদের পরীক্ষা দেবার কোনও দরকার নেই তো! এর দুয়েক দিনের মধ্যেই সে ঘর বদলে অন্য কোথায় যেন চলে যায়, সম্ভবত অন্য কোনও হস্টেলে। তিরিশের বি তে তাকে আর দেখিনি। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই আমার রুমমেট হয় মঙ্গোলিয়ার মেয়ে, তুমে। ওর পুরো নাম তুমেন্দেনবেরে সাইদারাহিন, স্বভাবে জেবোর একেবারে অপোজিট। তুমের কাছ থেকে মঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন করেছিলাম, অনেক বছর পরে একটা ফ্যান ফিকশন লিখি (“প্রোফেসর শঙ্কু ও মোংরু”), সেখানে ঐ জ্ঞান অল্প বিস্তর কাজে লেগে গেছল।
তুমে বড্ড চুপচাপ মেয়ে, সে বলেছিল সতীত্ব টতিত্বের ফান্ডা মঙ্গোলিয়ায় নেই, মাত্র দু মিলিয়ন জনসংখ্যা যে দেশের সেখানে বিয়ের রাতের রক্তমাখা রুমাল নিয়ে উল্লাস উৎসব অ্যাফোর্ড করা যায় না। হয়ত আরও কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ফার্স্ট ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংএর ছাত্রীকে এর বেশি সে বলেনি। সে তখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর থার্ড ইয়ার। পাঁচ মাস পরে জেনেছিলাম তার বাবা মঙ্গোলিয়ান এম্ব্যাসীর অ্যাম্বাসাডার, অথচ তুমের লাইফস্টাইল ছিল অবিশ্বাস্য রকমের সাদামাটা— একটা দামি সাবান পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেখিনি, তার ছিল মাত্র দুসেট কাপড়জামা, একটাই ফুরিয়ে যাওয়া লিপস্টিক যেটা সে দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তলানিটুকু বের করে করে ঠোঁটে ঘষে নিত। আর ছিল তার মাসলম্যান বয়ফ্রেন্ড আম্রা।
তিনশো পনের নম্বর ঘরে তুমের সঙ্গে বেশিদিন আমার থাকা হয়ে ওঠেনি, ঊনিশশো সাতাশির বসন্তকালে প্রায় জোর করেই ঘর পাল্টে দেওয়া হল আমার নতুন হওয়া বয়ফ্রেণ্ডের আদেশে। প্রেমে পড়বার ঐইতো বয়স। হস্টেলের পেছনের দিকে তিনশো পাঁচ নম্বর ঘরে দুই উজবেক রুমমেটের সঙ্গে থাকতে শুরু করলাম। তিনশো পনের ছিল হস্টেলের সামনের দিকটায়, জানলার সামনেই নীচে প্রায় চারপাঁচ মিটার চওড়া করে ফুলের বাগান গাছ পালা দিয়ে ঘেরা। সেটার পর সরু রাস্তা পিচে মোড়া। রাস্তার ওপারে প্রকান্ড মাঠ, মাঠের ওপারে বুনো আপেলগাছে ভরা জঙ্গল, তারও ওপারে দেখা যায় বারো এবং চোদ্দ নম্বর হস্টেল। তার পরে শুধু আকাশ। হস্টেলের সামনের রাস্তাটা দিয়ে সবসময় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, সেই রাস্তাতেই মাঝে মাঝে দেখতাম একটা মেয়ে অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যায়। মেয়েটার গায়ের রং ময়লা, মনে হয় ভারতীয় হলেও হতে পারে। একদিন সে চোখ তুলে ওপরে তাকাল, আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ মেয়েটাই মীনাক্ষি, যার সম্বন্ধে অল্প অল্প গল্প শুনেছি গত এক বছর ধরে। ব্যস, সেই থেকে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।
মীনাক্ষির সঙ্গে আলাপ হবার সময়টা সেই সময় যখন সবাই এইডস (রাশিয়ানে “স্পিদ্”) রোগটার নাম জেনে ফেলছে, দুনিয়া কাঁপিয়ে এইচআইভি-এইডস এর প্রতিরোধে ক্যাম্পেইন চলছে। প্রতিটি ফরেনার (বা যে সব সোভিয়েত নাগরিক বিদেশ সফর করে এসেছে) কে এলিজা টেস্ট করানো হচ্ছে বাধ্যতামূলক ভাবে। তখনও অবধি কোনও এইচআইভি পজিটিভ বিদেশি ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় নি। তখন এইভাবে প্রচার চলছে — স্পিদ্ হয় তিন ক্যাটেগোরির মানুষদের, যথা, হোমো সেক্সুয়ালদের, এইচআইভি পজিটিভ গর্ভবতী মায়ের থেকে তার গর্ভস্থ সন্তানের এবং যারা ক্ষণে ক্ষণে সেক্স পার্টনার পাল্টায় অর্থাৎ বেশ্যাদের। হোমো সেক্সুয়ালিটি এবং বেশ্যাবৃত্তি সারা দেশে এমনিতেই নিষিদ্ধ। বাকি থাকে একটি মাত্র অপশন, আক্রান্ত মায়ের থেকে গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে সংক্রমন। এই তিনটি মর্মে নিয়ম করে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এইচআইভি-এইডস এর অ্যাওয়ারনেস্ জাগিয়ে তোলা হচ্ছিলো এবং প্রথমেই মিলিৎসিয়ার দায়িত্ব থাকে জন হিতার্থে কাজ করবার।
সে অদ্ভুত দৃশ্য। নিজের চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। স্পিদ কন্ট্রোলকে সামনে রেখে
সন্ধের মুখটার যে সব হস্টেলে বিদেশীরা থাকে তার পেছন দিকে নিঃশব্দে চুপচাপ আলো নিভিয়ে লুকিয়ে থাকত মিলিৎসিয়ার ভ্যান। অল্পবয়সী সোভিয়েত (হ্যাঁ তাদের অধিকাংশই রুশি) মেয়েরা কোনো বিদেশি ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেই তাকে খপ্ করে ধরে জোর জবরদস্তি করে ভ্যানে তোলা হচ্ছিল। সাত আটটা (বা কম বেশি ) মেয়েকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো স্পিদ্-এর “টেস্ট” করাতে। আদতে কোনও ডাক্তারি পরীক্ষাও হত না, মেয়েগুলো কিছুক্ষণ পরেই ছাড়া পেয়ে যেত, তবে মিলিৎসিয়ারা এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না। হয়ত তাদের পাসপোরৎ আটক করে রেখে দিলো (আজ দেব কাল দেব করে ঘোরাবে), নয়ত মার ধোর বলাৎকারের বিনিময়ে পাসপোরৎ ফেরৎ পেত মেয়েগুলো। মিলিৎসিয়া বলে কথা! এদের বিরুদ্ধে তো আর ধর্ষণের রিপোর্ট লেখানো চলে না। “ভালো” মেয়েদের তুলে নিয়ে গেলে তাদের খুবই বিপদে পড়তে হতো। ঐ পাসপোরৎ ছাড়া ওদেশে কোনও নাগরিকেরই গতি নেই, সব জায়গাতেই ওটা দেখাতে হয় আইডেন্টিটি প্রুফ হিসেবে, যদিও ওই পাসপোরৎ দিয়ে বিদেশে যাওয়া যায় না।
মীনাক্ষির পরিচিত এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে একবার গল্প হচ্ছিল। তার সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমরা সমস্বরে বললাম, ফেরৎ পেলি তোর পাসপোরৎ?
– আর বলিস না। লোকটা তো আমায় রোজ ঘোরাচ্ছে আজ দেব কাল দেব করে। যখন টাইম দেয়, থানায় যাই, গিয়ে দেখি নেই – কোথায় বেরিয়ে গেছে। অন্য দিন গেলে দেখা হলে বলে কী সব প্রোটোকল লেখা বাকি আছে। এমনি করতে করতে প্রায় দু মাস কেটে গেছে। পাসপোরৎ সব জায়গায় দরকার, ওটা না দেখালে স্টাইপেন্ডের টাকাও তোলা যায় না।
– তারপর?
– তারপর আবার কী? এমনি করে দু মাস ঘোরানোর পর একদিন থানার মুখটায় দেখা হলো, সে তখন গাড়ি নিয়ে কোথায় একটা বেরোচ্ছে, গাড়ীতে স্টার্ট দিচ্ছিল। আমাকে ডেকে গাড়ীতে তুলে নিলো। পথে যেতে যেতে কাজের কথা হলো। লোকটা বলল, দ্যাখো তোমার কেসটা দুমাস ধরে পড়ে আছে, এখন এটা কোর্টে উঠবে, শিগ্গিরই তোমার কাছে চিঠি যাবে কোর্টে উপস্থিত হবার জন্য। আমার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। একবার এইসব মামলায় জড়িয়ে পড়লে আমার জীবনে কালো ছাপ পড়ে যাবে, কোনও দিনও ভাল চাকরি পাব না। লোকটা আমার মনে ভাব বুঝে নিয়ে বলল, অবশ্য তুমি যদি বুদ্ধিমতি হও তবে এর ফয়সালা এখনই হয়ে যেতে পারে।
– হল ফয়সালা?
– হল তো। আমি বললাম কী করতে হবে? সে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসলো। আমি কিছু বললাম না। সে গাড়ি ঘুরিয়ে নির্জন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে, তার যা কাজ করবার করে নিল।
– আর পাসপোরৎ? দিল?
– কেন দেবেনা? পকেটে করে নিয়েই ঘুরত সবসময়। কাজের শেষে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলো। এই দ্যাখ্!
দেখলাম পারপোরৎ, নিদাগ। কোনো ভুলভাল স্ট্যাম্প মেরে দেয় নি ভেতরে। টানা বেশ কয়েক বছর এইভাবে মিলিৎসিয়ার অত্যাচার চলেছিলো। ভাগ্যিস দেশ ভেঙ্গে গিয়েছিলো, তখন মিলিৎসিয়া আরো ইন্টারেস্টিং কাজ খুঁজে পায়। প্রথম দিকে আমরা জানতামই না যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমেও সংক্রমন ছড়ায়। সে সময় আমরা সমকামীদের ঘৃণা করতাম, জানতাম বেশ্যাবৃত্তি ও সমকামিতা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
*** *** *** *** ***
দেশে থাকতে কিছু রবীন্দ্রসংগীত শিখেছি, গেয়েছি। হস্টেলে গিয়ে বাঙ্গালী না থাকায় স্নানের সময় ছাড়া গান গাইতাম না। মীনাক্ষির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পরে ওর সামনে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছি, কিন্তু বাণীপ্রধান হওয়ায় ও মানে বুঝতে পারেনি, সেভাবে উপভোগ করতে পারেনি। তখন রোজই মীনাক্ষির হস্টেলে বেড়াতে যেতাম, বা ও আসত আমার হস্টেলে। ওর একজন রুমমেট ছিলো, রুশ মেয়ে, সে আদ্দেকদিন হস্টেলের ঘরে ফিরতো না। সন্ধে হলেই নানান বন্ধুবান্ধব আড্ডা ইত্যাদি নিয়ে আড্ডা মারা ছিলো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। মীনাক্ষির প্রচুর বন্ধুবান্ধব, তারা সব নানান দেশের। মাঝে একটি ছেলে বড্ড উৎপাত শুরু করল। নাম বসির, বাড়ী করাচি। সে জানে তাকে আমরা পছন্দ করিনা, তবু সন্ধেবেলা হুট্ করে মীনাক্ষির ঘরে চলে আসবে, দরজায় টোকা দেবে। নানাভাবে তাকে বোঝানো হয়েছে ,তবু সে আসবেই। আমি ইচ্ছে করে তার নাম ভুলভাল বলতাম, বসির বলতে গিয়ে রশিদ বলতাম, আরও নানাভাবে তাকে নিয়ে রগড় করা হতো তবু সে নাছোড়বান্দা। সেদিন আমরা ঠিক করেই রেখেছি, বসির এলেই বলব “আমরা তো এখন বেরোচ্ছি” ইত্যাদি। অথচ এত প্ল্যান করার পরে বসির আর আসেই না। না এলেই ভালো, কিন্তু ওকে জব্দ করার প্ল্যান বানিয়েও সেটার প্রয়োগ হচ্ছে না, তাই আমরা একটু টেনশনে ছিলাম। রাত সাড়ে দশটার সময়ে ভাবলাম অনেক আড্ডা হয়েছে, এবার রান্না চড়ানো যাক। সেদিন মীনাক্ষির হস্টেলেই এসব হচ্ছিল যদ্দূর মনে পড়ছে। রান্না করতে গিয়ে দেখা গেলো কিছুই প্রায় নেই ফ্রীজে। তখন আমরা দুজনে মিলে আমার হস্টেলে চলে এলাম। এগারটা নাগাদ রান্না চাপিয়েছি, রান্না বলতে মাংস আর ভাত, ঘরের দরজা হাট করে খোলা কারন বারবার রান্নঘরে যেতে হচ্ছে, হঠাৎ দরজার সামনে দেখি মূর্তিমান হাজির। মীনাক্ষিকে তার ঘরে না পেয়ে এখানে উপস্থিত। পূর্বনির্ধারিত প্ল্যান অনুযায়ী “আমরা তো এখন বেরোচ্ছি…” বলা যাবে না, তাতে রান্না পুড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমরা তখন সহ্যের শেষ সীমায়। “কেয়া খানা বন্ রহা হ্যায়? গোশ্ত? ” বলে বসির রান্নঘর থেকে একবার ঘুরেও এলো। সে রান্নাঘরে গেলে মীনাক্ষি করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “যোষি কুছ তো কর্। ম্যায় বহৎ পরিশান হুঁ”। “কুছ” বলতে যে কী করব আমার মাথায় এল না, এদিকে বসির চেয়ার টেনে বসে খোশগল্প করতে চাইছে। আমাদেরও হাসিহাসি মুখ করে সেই গল্পে তাল ঠুকতে হচ্ছে; এরকম সময়ে আমি চেয়ার থেকে উঠে বুকশেল্ফের দিকে গেলাম। ভাব দেখাতে চাই, যেন অনেক পড়া করতে হবে। যদিও সেই আইডিয়াটা খুব একটা ধোপে টিঁকবে বলে মনে হলো না। আর বসিরও “ও সারে কিতাব ফিতাব ছোড়িয়ে! আইয়ে গপ্শপ্ করতে হেঁ… ” বলে ডাক দিলো আমাকে। তৎক্ষণাৎ আমার মাথায় আইডিয়া খেলে গেল। দেশ থেকে আনা অখণ্ড গীতবিতানটা হাতে নিয়ে আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম “রশিদ, গানা সুনোগে?”
বসির তো আনন্দে আটখানা, মীনাক্ষিও চোখ গোল্লাগোল্লা করে আমাকে দেখছে। আমি গীতবিতানের প্রথম পাতা থেকে গান গাইতে শুরু করলাম “কান্না হাসির দোল্দোলানো পৌষফাগুনের পালা…” , রসিদ চুপ করে শুনে যাচ্ছে। গানের মধ্যে কথা বলতে নেই, অসভ্যতা। গান শেষ হলে ওয়াঃ ওয়াঃ করল, করে আবার যেই কথা বলতে যাবে, অমনি দুনম্বর গানটা ধরেছি, “সুরের গুরুউউউ…” বসির কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলো সেটা খোলাই রয়ে গেল, আমি গাইছি “দা আ ও , দা আ ও, দা আ ও গো সুরের দীইইক্খা” মীনাক্ষি কাজ করে চলেছে, স্যালাদ কাটছে, একবার রান্নাঘরে গিয়ে মাংসের ঝোলের সিচুয়েশনটা দেখে এলো। আমি গান গেয়েই চলেছি ” মন্দাকিনীর ধারা, ঊষার শুকোওতারা, আ আ আ মন্দাকিনীর ধারা আ” বসির চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। দরজার কাছে গিয়ে করিডোরে উঁকি মেরে দেখে নিল মীনাক্ষি কোথায়, এদিকে মীনাক্ষি ঘরে এসে প্লেট গুছোচ্ছে তখন বসির আবার চেয়ারে বসতে যাবে, এই মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে হস্টেল কাঁপিয়ে , “কোলা হলের বেগে,এ এ” গেয়ে উঠতেই দেখি বসির দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গানটা শেষ অবধি গাওয়া হয় নি। খাওয়া দাওয়ার পরেও গভীর রাত অবধি আমাদের হাসতে হাসতে কেশে ফেলে যাতা অবস্থা হয়েছিলো। এর পরে বসির আর আসতই না, এমনকি পথে ঘাটে দেখা হলেও এড়িয়ে যেত। মীনাক্ষি সুযোগ পেলেই, “আরে রশিদ, কাঁহা খো গয়া থা তুম্, কভি আয়া তো করো! যোষি রবিন্দর সংগীত সুনায়েগি…” বললেই, বসির নিমেষে কোথায় যে উধাও হয়ে যেত কে জানে।চলবে…
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:২৩735834
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:২৩735834- নিষিদ্ধ বস্তুমীনাক্ষির সঙ্গে আলাপের পর জিগ্যেস করেছিলাম তোকে পর পর দুবার ইলেকশানের দিনগুলোয় দেখিনি কেন বল তো? ও জানিয়েছিল যে ১৯৮৫ র ইলেকশনের দিন ও ছিল হাসপাতালে, ১৯৮৬ তেও তাই। এত হাসপাতালে যাস কেন? আসলে অক্টোবরের শেষ কি নভেম্বের গোড়ায় প্রতি বছর যখন ইলেকশনের ডেট পড়ে সেটা সীজন চেঞ্জের টাইম। কেন জানি না, ঐ সময়ে ওর হাঁপানি খুব বেড়ে যায়, প্রত্যেকবার। এ দেশে তো আর নিজের বাড়ি বা আপনজন বলতে কেউ নেই, অসুখ করলে হাসপাতালে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। মীনাক্ষিকে মাঝে মাঝেই হাসপাতালে যেতে হয়। ও প্রথম যখন এদেশে এসেছিল, তখন ডাক্তারির স্টুডেন্ট ছিল মস্কোয়। কিন্তু মস্কোর ঠান্ডায় প্রতিদিন ভোরে মেডিকেল ইন্সটিটিউটে ক্লাস করতে যেতে ওর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, মেডিকেলে ক্লাস কামাই করার মাশুল খুব বেশি দিতে হয়। হাসপাতালেই ছিল ও। খবর পেয়ে ওর বাবা চলে এলেন মস্কো, তিনি আবার মীরাট ইউনিভার্সিটির রুশ ভাষা বিভাগের হেড। বাবা এসে মেয়ের এই অবস্থা দেখে বুঝলেন ওকে বাঁচাতে হলে মস্কোর চেয়ে কম ঠান্ডা জায়গায় একটু কম সিরিয়াস বিষয় নিয়ে পড়তে দিলে হয়। চেষ্টা চরিত্র করে মীনাষিকে পাঠানো হল তাশকেন্তে রাশিয়ান ফিলোলজি পড়বার জন্য। সেই থেকে ও তাশকেন্তে রয়েছে, মাঝে এক বছর অসুস্থতার কারনে পরীক্ষাও দিতে পারে নি। তবু মীনাক্ষি দেশে ফিরে যেতে চায় না। এখানে কত জনে কত কুৎসা রটায় ওর নামে, তবু ও এখানেই থাকতে চায়। বড্ড অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা। সব কিছুই তো অদ্ভুত লাগে এদেশে। আসলে তখন ছিল একটা ট্রানজিশন ফেজ, আসতে আসতে আমরা সবাই পালটাচ্ছিলাম, মীনাক্ষিও।
রিসেন্ট ইলেকশানের গল্পটা ওকে বলতে না পেরে আমার শান্তি নেই। তাই বলেই ফেললাম। ১৯৮৬র ইলেকশনের দিন সত্যিসত্যিই হাতাহাতি মারামারি হয়েছিল।
আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে যে শহরে দশ পনেরোর বেশি ইন্ডিয়ান ছাত্র আছে সেসবখানে দলবাজি তো মাস্ট বটেই, কিন্তু সে শুধু মুখের কথায় বা প্যাঁদাপেঁদি বা চোরাগোপ্তা হানাহানির স্টেজেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তেড়েফুঁড়ে আইনী স্বীকৃতি দাবী করে। ব্যাপারটা খুব অর্গ্যানাইজ্ড্ভাবে হয়। প্রথমে ছাত্ররা একটা “ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট্স্’ অর্গ্যানাইজেশন” বানায় তারপরে গোটা দুতিন বা চারেক দলকে তার মধ্যে লড়িয়ে দেয়। যত বেশি দল, তত মজা। শীতের আগেই ইলেকশানের দিন ঠিক হয়ে যায় এবং কোন দল জিতবে এই নিয়ে গরম গরম মারামারি হতে থাকে। এগুলো রেগুলার প্র্যাক্টিস্। এম্ব্যাসীর কাছে সব খবরই পৌঁছয়, কিন্তু খুব্যাক্টা খুনোখুনির স্টেজে ঝামেলা ম্যাচিওর করে না। তারপরেই শীত পড়ে যায়, পড়াশুনোর চাপ অল্প বিস্তর বাড়ে, ঠান্ডা, ঝড়, বরফের টাইমে ছাত্ররা অল্প কেলিয়ে পড়ে- তাই শীতের আগেই ইলেকশানের ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া হয়। অদ্ভুত সেই বিকেল। চাপা উত্তেজনা। স্ট্যাক করা আছে মালের বোতল ক্যান্ডিডেটদের ঘরে। রেজাল্ট বেরোনোর পরে যেন মালের অভাবে হাপিত্যেশ করতে না হয়।
৮৫ নং হোস্টেলের একতলার হলঘরে তিলধারণের স্পেস নেই। টান টান উত্তেজনা। টোটাল ৫৬ জন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ইন্ক্লুডিং মী। জয়েন্টলি দুজন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। এবার হাত তুলে ভোট হবার পরে দেখা গেল রেজাল্ট টাই হয়েছে।
দুই বিজয়ী দল চুপচাপ নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গেল। তারপরে ভোৎকা ফুল চার্জ করে সেই রাতেই বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। ঐতিহাসিক সেই প্যাঁদাপেঁদিকে পাবলিক পরবর্তীকালে “এইট্টিসিক্সের লড়াই” বলে কোট করত। কতোগুলো ফাঁকা মদের বোতল ভাঙ্গা হয়েছিলো তার হিসেব কেউ কষেনি। পুলিশ এসেছিলো কিন্তু বীরপুঙ্গবেরা গা ঢাকা দেওবার ব্যাপারে ছিলো এক একটি ওস্তাদ। কিন্তু প্রবল ভাঙচুর ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান খতিয়ে দেখতে ইউনিভার্সিটি ও পলিটেকনিকের হত্তাকর্তারা ভারতীয় এম্ব্যাসীকে তলব করে। সে এক গমগমে ব্যাপার।
ফের ইলেকশান। উঁহু, কোনো হোস্টেলের হলঘরে নয়। শহরের তাগড়া থিয়েটারে গদিমোড়া অডিটোরিয়ামে।
স্টেজের ওপরে মখমলের চেয়ারে বসে রয়েছেন ফার্স্ট সেক্রেটারী ও সেকেন্ড সেক্রেটারী মহাশয় যুগল। মস্কো থেকে আগের রাতের ফ্লাইটেই এসেছেন। দুজনেরই নীল সুট পরণে। নীচে দর্শকের আসনে আমরা সবাই, ভোটার ও ক্যান্ডিডেটসকল। সবাই খুব সেজেগুজে এসেছে। শনিবার নয়, তবুও আমাদের প্রত্যেককে ক্লাস থেকে বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়েছে। এবারেও বিয়েবাড়ী অ্যাটমস্ফেয়ার। দামী শাড়ীর খশ্খশ্, বাহারী সুট পরা যুবকের দল, যে যত পেরেছে পারফিউম আফটার্শেভ ঢেলেছে। বল্বন্ৎ তা সত্ত্বেও প্রায় আউট, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। বল্বন্ৎ ভার্সেস রঞ্জনকুমার। টাই হবার চান্স রাখেনি ইন্ডিয়ানরা। ছাপ্পান্নর বদলে ভোটারের সংখ্যা সেদিন সাতান্ন।
কীকরে তা সম্ভব? একজন লুকোনো ভোটার ছিলেন, একজন রিসার্চার। নিজে ভারতীয় কিন্তু বিয়ে করেছে পাকিস্তানীকে, তাই তাকে আগে কেও ডাকত না উৎসবে অনুষ্ঠানে। সেদিন তাকে প্রায় গার্ড অফ্ অনার দিয়ে আনা হয়েছিলো। ফার্স্ট সেক্রেটারীর সামনে নিজের নেভি ব্লু পাসপোর্ট দেখিয়ে সেই রিসার্চার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ভোট দিয়েছিলেন।
রেজাল্ট নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নি। রঞ্জনকুমার যে হেরেছিলো তাতেই আমাদের আনন্দ।
সুষ্ঠুভাবে ইলেকশান সম্পন্ন করে মস্কোয় ফিরে যাবার আগে প্রথম ও দ্বিতীয় সচিব নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ছাত্রদের যে পারে জ্ঞান দেয়। তবে একটি লাইন আমার মনে আছে, হুবহু মনে নেই তবে এইরকম- দ্যাখো মদ খেতে বারণ তো করতে পারি কিন্তু তোমরা শুনবে না, তাই বলছি বুঝে শুনে খেও, এদের মতো তাগড়া স্বাস্থ্য তো আমাদের নয়, তাই লিমিট বুঝে খেলেই আর ঝামেলা হয় না।
এটা সম্ভবতঃ ফার্স্ট সেক্রেটারীই বলেছিলেন। করতালিতে ফেটে পড়েছিলো অডিটোরিয়াম। সেবার থেকেই চালু হয়ে গেল গোপন ব্যালট পেপার।
মীনাক্ষির কথা আবার ঘুরে ফিরে আসবে, এখন অনেক পরের অন্য একটা ঘটনা বলি।
সেটা সামার ভেকেশানে দেশে যাবার টাইম। জুলাই ফুলাই হবে। খুব সম্ভবতঃ তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটাই দেশ। নাকি জাস্ট ভেঙ্গে গেছে? মনে করতে পারছি না। যাই হোক, সন্ধে সাড়ে আটটা নটার আগে অন্ধকার হয় না তখন। খুব ভাল ওয়েদার। আমাদের ফ্লাইট সেই রাতে, এয়ার ইন্ডিয়ার। আমরা বলতে চারজন। আমি ও আরো তিনটে ছেলে। একজন কাশ্মীরি (আফতাব), আরেকজন দিল্লীর (হরিশ), বাকিজন পোর্ট ব্লেয়ারের (অভি)। কাশ্মীরি ছেলেটা দিল্লীতেই থাকে। পোর্ট ব্লেয়ারের ছেলেটা আবার বাঙালী কিন্তু বাংলা জানে না। সকলে দিল্লীর ফ্লাইটই ধরব। তা সন্ধেটা কাটাচ্ছি মস্কোর পার্ক কুলতুরীর মধ্যে একটা রেস্টুরেন্টে। আমাদের বসবার জায়গা রেস্টুরেন্টের বাইরে খোলা আকাশের নীচে। আফতাব ও আমি নিয়েছি ফ্রেশ স্ট্রেবেরী আইস্ক্রীম উইথ আখরোটের টুকরো। সঙ্গে রয়েছে লেমন জেলি ও পেপ্সি। হরিশ ও অভি আইস্ক্রীম খায় না – খুব ম্যাচো স্বভাবের, তাই বিকেল থেকেই চলছে বিভিন্ন মদ, সঙ্গে টুকটাক স্ন্যাক্স্। হরিশ অভির থেকে সিনিয়র ও যথেষ্ট ঝানু প্রকৃতির। অভির মেন্টরিং করছে হরিশ। মেয়েদের সঙ্গে কিকরে আলাপ করতে হয়, কোন মেয়ে কেমন করে পটাতে হয় সব হরিশের নখদর্পণে, নানারকম টিপ্স্ দিচ্ছে সে ব্যাপারে। এই ট্রিপেই নয়, ওরা বরাবরই একসঙ্গে ঘোরে, নানান মেয়ে ঘটিত অ্যাড্ভেঞ্চারে যায়। অভি বলতে গেলে হরিশের শিষ্য এ ব্যাপারে।
আমি ও আফতাব বাইরে বলে লেকের জল দেখছি, বাচ্চারা দৌড়চ্ছে, চেঁচামেচি, বারের ভেতর থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ। ওরা দুটোয় একবার করে গেলাস ভরে মদ নিয়ে আসছে, আমাদের সঙ্গে একটু বসছে, ফের ঢুকে যাচ্ছে রেস্টুরেন্টের ভেতরে। দুজনেরই হাল্কা নেশা হয়েছে। বেশি হাসছে। এবার দুজনে ভেতরে গেল। আফতাব ও আমি জল্পনা করছি, এখানেই ডিনার সেরে ফেলব কিনা। ফ্লাইট সেই রাত্রে। ফ্লাইটে উঠেই ঘুমোবো, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে খেতে দেয় – বড্ড বিরক্ত লাগে। কী অর্ডার দেওয়া যায় ঠিক করে ফেললাম, তবুও হরিশ ও অভির কথা ভেবে অপেক্ষা করছি, ওয়েট্রেসকে ডাকিনি।
দুম করে হরিশ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে – হাতে তুড়ি দিয়ে বলল, – চল্ ইয়ার, অভি নিকাল্তে হেঁ ইধার্সে।
– আরে, ডিনার তো কর্ লে! (আফতাব বলল)
– নেহি ইয়ার, অভি নিকাল্তে হেঁ ফটাফট্।
– ঔর অভি?
– আয়েগা বাদমেঁ। চল্ চল্ এক কাম ইয়াদ আয়া।
হরিশের ভীষণ তাড়া। ঝটিতি পার্ক থেকে বেরিয়ে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। সোজা শেরেমিয়েতভো২ এয়ারপোর্ট। পাক্কা চল্লিশ মিনিটের জার্নি।
হরিশের কোন “কাম ইয়াদ” এসেছিল, সেটা জানা হল না। আগে আগে পৌঁছনর জন্যে ভাল পছন্দের সীট পেলাম, আরও বেশ কয়েকটা চেনামুখের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তুমুল হুল্লোড় করতে করতে দিল্লীর ফ্লাইটে চেপে প্রায় না ঘুমিয়ে গল্প আড্ডা খাওয়া দাওয়া হাসি ঠাট্টা করতে করতে সময় কাটিয়ে দিলাম। কি অদ্ভুত মানুষ আমরা, একবারও অভি ফ্লাইটে কোথায় বসেছিল, ও ফ্লাইট সময়মতো ধরতে পেরেছিল কিনা সে ব্যাপারে ভাবি নি। জাস্ট ভুলে গেছলাম ওর কথা।
ছুটি কাটিয়ে ফের ওদেশে ফিরলাম। পুরোদমে নতুন সেমেস্টার, নতুন নতুন সাবজেক্ট, নতুন টাইমটেবল, আনন্দময় হোস্টেল লাইফ।
অভি কিন্তু ফেরেনি। সবাই ঠিক সময়ে বা একটু দেরী করে ফিরেছে, কিন্তু একমাস কেটে গেল, দুমাস। অনুপস্থিতির জন্যে ওর নাম কাটা গেছে শুনলাম ইন্স্টিটিউটের খাতা থেকে।
– ভেরি স্যাড্ ইয়ার!
– শায়দ শাদি করকে সেট্ল্ হো গিয়া উধার্।
– লওন্ডিবাজি খতম্।
– আজীব সা বান্দা হ্যায়!
নানান রকমের কমেন্ট করে ছাত্ররা।
ধীরে ধীরে অভিকে আমরা ভুলে গেলাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার নাকি লক্ষ্য করা গেছল যেটা কয়েকবছর পরে (চার বছর পরে) শুনেছিলাম। ইন্ডিয়ান এম্ব্যাসীর একতলার সেই বিরাট টেবিলটাতে ভারতীয় ডাকের অঁভলপে অভির নামে চিঠি আসত পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। ভায়া ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ, সাউথ ব্লক, নিউ ডেলি। অনেকের বাড়ী থেকেই সস্তার পোস্টেজে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে চিঠি আসত। তারাই দেখতে পেত অভির চিঠি পড়ে আছে।
-মালটা গেল কোথায়?
-বাড়ীর লোকে ভাবছে ও এখনো পড়ছে, এদিকে ও হয়ত অন্য কোনো শহরে গিয়ে হেভি মাগিবাজি করছে।
ঠিক এইরকমই রিয়্যাক্শন্ ছিলো অনেকের। কিন্তু ঐ অবধিই। তারপরে আমরা ভুলে যেতাম।
হরিশ খুব ঘন ঘন মস্কো যেত তখন। ওখানে ওর রাশিয়ান গার্লফ্রেন্ড ছিলো, মেয়ে ছিল। অন্যান্য ধান্দাও ছিল – কেমন করে সেট্ল্ করবে, বিজনেস করবে, এসমস্ত।
দেশে ফিরে আসার এক সপ্তাহ আগে হাড় হিম করা একটা খবর শুনেছিলাম। একটা বাংলাদেশি ছেলে এসে আমাকে বলে গেছল। হরিশ নাকি মদের ঝোঁকে কন্ফেস করেছে। সেই ক বছর আগে পার্ক কুলতুরীর রেস্টুরেন্টে ওর সামনে অভি খুন হয়ে যায়। একটার পর একটা মদ কিনছিল ওরা। ঘুরছিল হাসছিল, মেয়ে পটাবার চেষ্টা করছিলো। এমনি একটা মেয়েকে গিয়ে পটাবার চান্স নিয়েছে, দূর থেকে লক্ষ্য রাখছিল মাফিয়া। সেই মেয়ে মাফিয়ার গার্লফ্রেন্ড। দুজন হেফ্টি লোক এল, অভিকে জাস্ট ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে দেয়ালে মাথা থেঁতলে দিল, তারপরে কোনো রিস্ক না নিয়ে রিভলভার বের করে কাছ থেকে মাথায় গুলি।
ভেতরের গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া এতে এক সেকেন্ডের জন্যেও থামেনি। হরিশ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে তড়িঘড়ি এয়ারপোর্ট চলে যায়। আমরা বাইরেই বসে আইসক্রীম খচ্ছিলাম – দশ মিটারেরও কম দূরত্বে একটা খুন হয়ে গেল, কিছু বুঝতেই পারলাম না।
দেশ তখনও জোড়া। একত্র। এমন সময়ে ওদেশে মা কে নিয়ে এসেছিলাম বেড়াতে। যা হয় আরকি, দেশ থেকে আত্মীয় স্বজন এলে স্থানীয় দেশের নেটিবদের বাড়িতে ডেকে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায়, গল্প করে।
ফ্লোরা নামের এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে তেমনি এক সন্ধ্যায় ভুরিভোজের নিমন্ত্রন ছিলো। ফ্লোরা আমাদের ইন্সটিটিউটের বিদেশিদের ফ্যাকাল্টিতে একাধারে ক্লার্ক এবং ক্যাশিয়ার। প্রথমে অল্প চা মিষ্টি নোনতা, তারপরে ডিনার, সবশেষে খোশগল্প। সেইসময়ে ফ্যামিলি ফোটোর অ্যালবাম দেখাচ্ছিলো ফ্লোরা। এক এক করে সব ফোটো দেখাচ্ছে ও চিনিয়ে দিচ্ছে কে কোনজন। বিরাট ফ্যামিলি একান্নবর্তী পরিবার। সেই পরিবারের সকলেই হাসি মুখে আমাদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন। এরা খুবই অতিথি বৎসল জাত। তাশকেন্তের পুরোনো শহরে সামারকান্দ দার্ভাজা বলে একটা জায়গায় ফ্লোরাদের বাড়ি। সে বাড়ির বাইরে পাঁচিল তোলা, বাইরের দিকে কোনও জানলা নেই। ফ্লোরার দিদি ও জামাইবাবুর ফোটো দেখলাম। তারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ও ছিলেন তাই চাক্ষুষ মানুষগুলোকেও দেখলাম।
অ্যালবামে আরও একজনের ফোটো আছে, সেই দিদির সঙ্গেই যেন মনে হলো। ফ্লোরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সেই ফোটোর সঙ্গে – দিদি জামাইবাবু। খটকা লাগছে- দিদি তো একজনই কিন্তু জামাইবাবুর ছবিগুলো মনে হচ্ছে দুজন আলাদা মানুষের। একদম আলাদা মুখ। আমার মনের ভাব আঁচ করে নিয়ে সে বলেছিলো – পরে কখনও বলব।
এরপরে ফ্লোরাকে আমার পাল্টা নিমন্ত্রণ করবার পালা। সেই নিমন্ত্রণরক্ষার্থে এসে সে তখন ঐ ফোটোর কনফিউশান দূর করে দেয়।
বেশ কিছু বছর আগে দিদির বিয়ে হয়েছিল সেই জামাইবাবুর সঙ্গে, যাঁকে শুধু ফোটোয় দেখলাম। এর কিছুদিন পরে এরা দল বেঁধে ভ্লাদিভস্তকে বেড়াতে যায়। দিদি জামাইবাবু ফ্লোরা নিজে আরও দুজন ভাই মা এক কাকা অনেকে মিলে। খুবই আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটছিল। অদ্ভুত সুন্দর সেই দ্বীপ। খুবই ঝলমলে আনন্দের পরিবেশে গান বাজনা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে এনজয় করছিল ওরা সকলে। এক সন্ধ্যায় ওরা সবাই রেস্টুরেন্টে খেতে গেছে। এক সময় জামাইবাবু টয়লেটে গেল। ওরা সব খাচ্ছে তখন ডেসার্ট। মোটামুটি হাল্কা নেশাও হয়েছে। চমৎকার বাজনা বাজছে। ডেসার্ট শেষ হয়ে গেল, বাজনা একটার পর একটা হয়ে যাচ্ছে, বিল চোকানোর সময় এসে গেছে- বিল জামাইবাবুই ভরবে – সে আর টয়লেট থেকে ফেরে না। লোকজ্ন অপেক্ষা করছে তো করছেই। শেষে টয়লেটে গিয়ে খোঁজা হল। টয়লেটে খুঁজে তাকে পাওয়া গেল না, রেস্টুরেন্টের বাইরে, আশেপাশে কোত্থাও না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। ক্রমশ অন্ধকার নেমে এল, জাহাজের আলোগুলো জেগে উঠছে একে একে অন্ধকার সমুদ্রের দিক থেকে। মিলিৎসিয়াকে খবর দেওয়া হল। খোঁজ খোঁজ রাস্তায় হাসপাতালে সর্বত্র। তারপরে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে আর কোনোদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। নিরুদ্দেশ। তবে এই নিরুদ্দেশের ঘটনাকে জাস্টিফাই করবার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যে গল্পটা ওরা মেনে নিয়েছিল সেটা হচ্ছে – কোনও কারনে মাফিয়ার হাতে মৃত্যু হয়েছে জামাইবাবুর। মাফিয়ারা নাকি এমন করে। খুন করে ফেলে দেয় সমুদ্রে। এমন নাকি আরও হয়েছে সেই জমানায়।
অভিও ওরকম নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ভ্যানিশ। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া না গেলে তো আর মৃত বলে অত সহজে ঘোষণা করে দেওয়া যায় না। খুন বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায় কোনও রাষ্ট্র নিতে চায় না। বিদেশি হলে তো আরওই না। মানুষগুলো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
ওদেশে পড়তে যাবার আগে বা পরে সব দেশের সব ছাত্রদের তো উদ্দেশ্য অভিন্ন থাকে না। কেউ সোভিয়েত দেশটাকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে আরও পশ্চিমে পাড়ি দিতে চায়, কেউ পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে সুখে বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করবার কথাও ভাবে, কেউ ওদেশেই থেকে যেতে চায় বিয়ে থা করে- এই আশায় আশায় যে শীঘ্রই ওখানকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, তৈরী হবে ব্যক্তিগত মালিকানার কনসেপ্ট।
ব্যবসা বানিজ্য করে ওখানেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়ি ইত্যাদি করা যাবে। পেরেস্ত্রৈকার কিছু না কিছু সুফল তো হওয়া উচিৎ। অন্ততঃ এইটুকু, যেখানে “নিজের” বলে কিছু থাকবে।
এই চাওয়াগুলো কি অস্বাভাবিক? ঐ দেশটার প্রত্যেকটা মানুষও কি এগুলো চায় নি যে নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে তাদেরও কিছু থাকবে, যেখানে ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেবে না রাষ্ট্র, যেখানে সমস্ত কিছুই লুকিয়ে লুকিয়ে জমাতে হবে না। সেই জমানোটা তো শুধু টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি জমি গয়না নয়, হয়ত কোনও গোপন বিশ্বাস, ভালোবাসা, আস্থা, যা হয়ত হতেও পারে ঈশ্বরের প্রতি। ঊনিশশো সতেরো থেকে সেই সফল বিপ্লবের পর থেকে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ তো নেই, সত্তর বছর কেটে গিয়েছে, তিনটে কি চারটে জেনারেশন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বেড়ে উঠেছে, বেঁচে বর্তে রয়েছে এমন পরিবেশে যেখানে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ হয় না। নিষিদ্ধ বলিনি কিন্তু, তবে হয় না। কোনও ধর্মীয় উৎসব বা ছুটি নেই।
মীনাক্ষির ঘরে অনেক গোপন জিনিস আমি দেখে ফেলেছিলাম নানান সময়ে। ইচ্ছে করে বা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নয়, এমনিতেই চোখ চলে যেত। হয়ত মুখে কিছুই বলিনি, কিন্তু আমার চোখ চলে যাওয়াটাকে অনুসরণ করে প্রত্যেকবার ও কেমন যেন ধরা পড়ে যাবার মত অস্বস্তিতে ভুগত। প্রত্যেকবারই ও নিজে থেকেই যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইত, কেমন করে সেই সব নিষিদ্ধ আইটেম ওর ঘরে এল এসব জাস্টিফাই করতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। অথচ আমি কিন্তু কোনও দিনই কোনও জাস্টিফিকেশন চাই নি। আমার চোখে বা বিশ্বাসে ঐ সব আইটেম নিষিদ্ধ মনে হতো না। কিন্তু তা বোঝালেও কি বুঝবে মীনাক্ষি! ওর মনে প্রাণে তখনও অনেক অনেক সংস্কার, যেগুলোকে ও না পারছে রাখতে না পারছে ফেলতে। ফেলতে গেলে বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যেতে পারে, রাখতে গেলে কাঁটার মত সর্ব শরীরে বিঁধবে, কোথায় যাবে ও তখন? যদি একটি বারের মতও এটুকু বিশ্বাস করত যে আমি মুখে যা বলছি, মনে মনেও সেটাই মীন করছি, তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ত বিষিয়ে উঠত না। নিষিদ্ধ জিনিস কি একটা? একবার দেখতে পেয়েছিলাম ছেঁড়া মত একটা প্লাস্টিকের মোড়ক, সেটা হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি, ও এমন করে তাকাল আমার দিকে যে মোড়কটা ফেলবার আগেই দেখে ফেলতে পারলাম যে ওটার গায়ে কয়েকটা অক্ষর লেখা আছে, প্রিজারভেটিভ – বাংলায় কন্ডোম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল জাস্টিফিকেশনের গল্প। যতই স্মার্ট নিজেদের মনে করি না কেন, পেট থেকে পড়বার পরে যে সমাজে বেড়ে উঠেছি সেখানে অবিবাহিত মেয়ের ঘরের কোণে কন্ডোমের মোড়ক পাওয়া আশির দশকের শেষ ভাগে প্রচলিত অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খায় না। সে তো নিষিদ্ধ আইটেমই বটে। আরেকবার দেখতে পেয়েছিলাম একটা বই। বইটার সবুজ রঙের মলাট। সেই প্রথম আমি কোরান শরীফ স্বচক্ষে দেখলাম।চলবে…
 সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৬:৫১735836
সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৬:৫১735836- পার্ট-টু
দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে জানতাম যে গল্পটা ওখানেই শেষ। জানতাম, যারা শুনতে চাইবে তাদেরকে গল্পটা আমি আমার মত করে বলব। এ গল্প যেন সিনেমা দেখে এসে সেটা অন্য কারওকে শোনানোর মতন। প্রত্যেকবার একটু একটু করে বদলে যায়, সবটাই স্মৃতি থেকে কিনা। এতজন মানুষের কাছে এত এত গল্প করেছি ঐ দেশটার, বা আরও সোজাসুজি বললে আমার জীবনের একটা চুড়ান্ত অভিজ্ঞতাময় সময়ের, যে অনেকেই ভেবে বসে, যে হয়ত বাড়িয়ে বলছি বা মিথ্যে বলছি। জনে জনে তো প্রমাণ দেখানো সম্ভব নয়, ফোটো ও সই মিলিয়ে নেবার মত হাতে গরম দলিল দস্তাবেজও নেই, তাই ঠিক করলাম আবার যাব সেইখানে। ফিরে আসার চব্বিশ বছর পরে ফের গেছলাম সেই ঠাঁইয়ে। ঐযে সেসব কী বলে না। সার্কল অফ লাইফ, বা ঐ ধরণের কিছু। হ্যাঁ, সেই বৃত্তকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পাড়ি জমালাম উজবেকিস্তান। ঊনিশশো পঁচাশি থেকে পঁচানব্বই দশটি বছরের ফ্রেমে আমার দেখা উজবেকিস্তান, যার অধিকাংশই তাশখন্দ শহর এবং যার পরতে পরতে মিশে আছে স্মৃতি; যে স্মৃতির বিভিন্ন অংশগুলোকে তুমি চাইলে টেনে বাড়িয়ে নিতে পারো, ইচ্ছে করলে কিছু অংশ লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারো অপ্রয়োজনীয় মনে করে। অথচ গল্পটা দুম করে আমূল পাল্টে গেল। হঠাৎই। দীর্ঘ বিরতির পর ফের শুরু হয়ে গেল সিনেমা। চব্বিশ বছর পরে আবার গিয়েছিলাম উজবেকিস্তানে। প্রথমবারে গিয়েছি ওদেশে ছাত্র হিসেবে, এবারে নেহাৎই পর্যটক, তবে কি দুটো গল্পের আঙ্গিক আলাদা? পর্যটক তো লিখবে ভ্রমণবৃত্তান্ত, ছাত্র কী বলেছিল? সে বলেছিল জীবনের পথে অভিজ্ঞতার তীব্রতায় নাস্তানাবুদ একটা মস্ত বড়ো ভ্রমণকাহিনি।
গেলবারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবার কিচ্ছুটি মিলছে না। আমার সঙ্গে আছে একজন, যাকে আমি বহুবার বলেছি সেই দেশটার গল্প। এখন চাক্ষুষ মিলিয়ে নেবার পালা। আয়েরোফ্লোতের বিমান গভীর রাতে ল্যান্ড করল তাশখন্দে। এবারে ইমিগ্রেশন অফিসার মুচকি হেসে দুমদাম ছাপ মেরে দেয় পাসপোর্টে, ভিসা টিসার ঝামেলা চুকে গেছে। কাস্টমসের চোখ রাঙানি নেই, ঝলমল করছে এয়ারপোর্ট আলোর রোশনাইয়ে। বুঝলাম শহর বদলে গেছে একশো আশি ডিগ্রি না হলেও ছুঁই ছুঁই। তবে এটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল, যে শহরটাকে নিজের হাতের মুঠোর মত চিনতাম, সে যতই বদলাক আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না।
এবারে আমাদের থাকবার মেয়াদ দু সপ্তাহের কিছু বেশি। পর্যটক হিসেবে সঙ্গে একটা ক্যামেরা থাকা জরুরি, অথবা স্মার্টফোন। পাছে কিছু মিস করে ফেলি, তাই হুড়মুড়িয়ে স্মার্টফোনে ঘনঘন ফোটো তুলে রাখাই দস্তুর। সে নাহয় তুললাম শয়ে শয়ে ফোটো, জমিয়ে রাখলাম তা ফোনের মেমরি কার্ডে, কিন্তু সেই পুরোন দশটা বছরের স্মৃতিতে যে অসংখ্য ছবি, সেগুলোর প্রিন্ট আউট নেওয়া যায় না, অথচ তা গুণে গুণে দশ গোল দেবে এই হাজার হাজার মেগাপিক্সেলের ফোটোগুলোকে।
শহর অবশ্যই বদলেছে। ট্রামের লাইন নেই, ট্রামের সঙ্গে ট্রলিবাসও উধাও। এমনকি বাসের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি সাইজেও ছোট্ট হয়ে গেছে বাসগুলো। অনুপাতে রাস্তাগুলো চওড়া হয়েছে; এদিকে ছটা ওদিকে ছটা করে বারো লেনের ট্র্যাফিক চলছে হুহু করে বড়ো বড়ো রাস্তায়। রাস্তা পার হতে গিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছি বারে বারে। সঙ্গত কারণেই ট্রাম ট্রলিবাস বাতিল হয়েছে বুঝতে পারি; এগুলোর সারাই-মেরামৎ, নতুন করে কিনে আনার হুজ্জৎ থেকে নিষ্কৃতি পেতেই এই ব্যবস্থা। এখন তো আর সেই সোভিয়েত আমল নয়, সেই একান্নবর্তী পরিবার আর নেই, সবাই আলাদা আলাদা, তাই এই ব্যবস্থা। সেকালে ট্রাম আমদানি হতো চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। বাস আসত হাঙ্গেরি থেকে। সেখানে শতাধিক বছরের প্রাচীন ইকারুস নামের সেই বাস তৈরীর কারখানাটাই উঠে গেছে এই নতুন মিলেনিয়ামের গোড়ায়। তবে সারাটা শহর জুড়ে এবং দেশ জুড়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না, চলছে শেভ্রোলে কোম্পানীর মোটরগাড়ি। গাড়িগুলোর মডেল যদিও বা আলাদা হতে পারে, প্রত্যেকটা গাড়ির রং সাদা। রাস্তা জুড়ে
স্রোতের মত বয়ে চলেছে অসংখ্য সাদা সাদা শেভ্রোলে - এ এক অপার্থিব দৃশ্য। শুনলাম গাড়ি স্থানীয় কারখানাতেই তৈরি হচ্ছে। দাম মোটামুটি সস্তাই এবং গুণগত মান যথেষ্ট ভাল। তবে মেত্রো আছে আগের মতই স্বমহিমায়। স্টেশনগুলোয় ঢুকতে গেলে মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষায় পাশ করা চাই। নতুন লাইন হয়েছে, নতুন নতুন স্টেশন হয়েছে। পুরোন স্টেশনগুলো আছে, আর আছে পুরোন সেই ট্রেনগুলো। অবশ্য গোটাকতক নতুন ট্রেনও দেখলাম বৈকি।
আমি জাতিস্মরের মত খুঁজে চলেছি পূর্বজন্মের জায়গাগুলো। আমার নবছরের জীবনের সাক্ষী যে হোস্টেল, তাতে ঢুকতেই বাধা পেলাম। চারিদিকে লোহার গরাদ দেয়া পাঁচিল, হোস্টেলের সদর দরজা আগে যেখানে ছিল, সেখানে দেয়াল তুলে দিয়েছে এরা। খিড়কির দরজার কাছে তৈরি হয়েছে নতুন সদর দরজা। তবু উঁকি দিতে মন চায়। ঐ অট্টালিকার ভেতরে পড়ে রইল আমার জীবনের নটা বছর, আমি উঁকি দিয়ে একটিবার তাকে দেখতে চেয়েছিলাম, অনুমতি মেলেনি। হোস্টেলটাকে বাইরে থেকে প্রদক্ষিণ করতে করতে খুঁজতে থাকি চেনা ঘরগুলোর জানলা। জানি চেনামুখেরা সেখানে থাকতে পারেই না, কিন্তু স্মৃতিগুলো টুপটাপ ঝরে পড়তে থাকে, চোখের আর দোষ কী!
কিছু অদ্ভূত সমস্যা আমার আছে। দুনিয়ার দারুণ দারুণ সব জায়গায় বেড়াতে গিয়ে যেসব অবশ্য দ্রষ্টব্যের তালিকা টুরিস্ট গাইডে পাওয়া যায়, সেগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়েছি। না, না, ভিড় টিড়ের দোহাই দিয়ে, কি পর্যটকদের ফোটো তোলার হিড়িক দেখে নয় কিন্তু – ওগুলো কাছ থেকে দেখে তেমন কোনও বিশেষ রোমাঞ্চ অনুভব করি না। ফের মনে হয় বইয়ের পাতা উল্টে ছবি দেখে নিলেই চলবে। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। সেই দশটা বছরকে সঙ্কুচিত করে দুসপ্তাহের মধ্যে অতি দ্রুততায় আমি পার হয়ে যেতে চাইলাম সেই শহর, নদী, মরু, গ্রাম, অজস্র স্মৃতিসৌধ, বাগিচা, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি, ইন্সটিটিউট, বাজার, থিয়েটার, আরও যা যা সম্ভব - প্রত্যেকটা জায়গা। কোথাও বেড়াতে গিয়ে কারোকে হাসপাতালে বেড়াতে যাবার কথা কি কেউ শুনেছে? আমি কিন্তু খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলাম সেই হাসপাতালে যেখানে আমার সন্তানের জন্ম হয়েছিল। কী বলে একে বাংলায়? নস্টালজিয়া?
পূর্বপরিকল্পিত ছক ধরে ধরে পরপর বেড়াতে থাকি খিভা, বুখারা, সমরকন্দ। সত্যি কথা বলতে কি, মোবাইল ফোন খুঁজে খুঁজে ফোটো বের করে তারিখ মিলিয়ে না নিলে সত্যিই মনে করতে পারব না সেসব জায়গাগুলোর দৃশ্য। কিন্তু কোনও ফোটো ছাড়াই চোখের সামনের ভেসে ওঠে খিভার সেই দূর্গের মধ্যে যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম, সেই বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যবহার। তারা আমাদের ভাষা বোঝে না, আমরাও তাদের ভাষা জানি না। কেবল বাড়ির কর্তা কিছুটা রাশিয়ান জানতেন, সেটুকুই ছিল ভাষা ভিত্তিক যোগসূত্র। বাকিটা মানবভাষা, যার কোনও বর্ণমালা নেই, ব্যাকরণ নেই, সাহিত্য নেই, অথচ সে অবলীলাক্রমে অফুরান প্রকাশ করতে পারে তার অনুভূতি অভিব্যক্তি। তাদের আদর যত্ন আপ্যায়নে ত্রুটির তো প্রশ্নই নেই, বরং ভরা ছিল অতিথিপরায়নতা, ডলারের হিসেবে সে ঋণ চোকানো অসম্ভব। ফিরে যাবার দিনটিতে গোটা পরিবারের সব সদস্য এসে দাঁড়িয়েছেন ট্যাক্সির পাশে। দুনিয়ার কোন তারা লাগানো হোটেলে পাওয়া যাবে এই ভালোবাসা? এই দেশটার মানুষগুলোর ভালোবাসার টানই মনে হয় আমায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছল চব্বিশ বছর পরে উজবেকিস্তানে। হায়রে আর আমি কি না মূর্খের মত গাড়ির মডেল, রাস্তার প্রস্থ, নতুন হোটেল, দোকান, এইসব জড়বস্তুর মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম দেশটার হৃদস্পন্দন।
বুখারায় যে ট্যাক্সিটি দৈনিক কড়ারে ভাড়া নিই, সেই ট্যাক্সিওয়ালা যুবকটি সারাক্ষণ বকবক করে চলে, তার গল্প আর ফুরোতেই চায় না। অনর্গল কথা বলার ভেতরেই সে দিয়ে চলে বর্তমান সমাজ ও অর্থনীতির বিবরণ, সম্পূর্ণ অজান্তেই। হাইওয়ের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টের দোতলায় বসে আমরা চুপচাপ দেখে চলেছি বিশাল বিশাল ট্রাক বোঝাই করে চলেছে তুলো, উজবেকিস্তানের বৃহত্তম ফসল। কোথায় যায় এই তুলো? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না যুবকটি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, ফের বলে -বাবা মায়ের কাছে শুনেছি আগের জমানায় সব মানুষই খেয়ে পরে বাঁচত, এখন অবস্থা বড্ড খারাপ, অনেক কলকারখানা উঠে গেছে।
সমরকন্দের ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে চুপচাপ প্রকৃতির ভেবেছিলাম। আসল কারণ সে ইংরিজিও জানে না, রাশিয়ানেও সমস্যা। তবু সে কত জায়গায় আমাদের নিয়ে যায়, সেসব জায়গায় আমি আগে কখনও যাই নি। একদিন বিকেলে একটি কাফেতে গিয়ে বসেছি, যে মেয়েটি পরিবেশন করছিল, সে চেহারা দেখেই চিনেছে যে আমরা ভারতীয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মিউজিক বদলে দেয়, একের পর এক বাজতে থাকে হিন্দি ফিল্মের গান। আর সেইসঙ্গে তার লাজুক হাসি। পাড়ার কাছে আরেকটি কেক পেস্ট্রির দোকানেও সেই একই অবস্থা। পাশে এসে সঙ্গে নিয়ে ফোটো তোলার ধুম।
তাশখন্দে একটি রেস্টুরেন্ট - গালুবাইয়া কুপালা, এখনো আছে। তবে এখন নিয়ম করেছে ড্রেসকোড ছাড়া প্রবেশাধিকার নেই। আমরা তো সেসব জানি না, ঢুকতে গেছি পরণে ধুলিধূসরিত জিন্স। বলে- ড্রেসকোড চাই। তো আমরা বললাম - ঠিক আছে, ঢুকব না।
তারা কী ভেবে, দৌড়ে এসেছে পেছন পেছন, বলছে - এসো এসো, তোমাদের ড্রেসকোড লাগবে না।
আমরা হেসে বাঁচিনা। এমন দেশ আর কোথাও পাওয়া যাবে আজকের দুনিয়ায়?
যাকে আমি উজবেকিস্তানের গল্প শুনিয়েছি বারে বারে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে প্রথমে তাশখন্দ শহরটার চেহারার পরিবর্তন দেখে একটু হকচকিয়ে গেছলাম। সেই পুরোন সময়ের সঙ্গে বাড়ি ঘর রাস্তা পুরোপুরি মেলাতে পারিনি বলে। তবে বাকিটুকু মিলে গেছে। রাস্তা ঘর গাড়ি এসব তো বাইরের খোলস। সেটুকু ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে যেটা থাকে সেটা দেশের মানুষ, তাদের মন, স্বভাব, আন্তরিকতা, তাদের ভালোটুকু, তাদের মন্দটুকু। সেটুকু বদলায়নি। তাই চব্বিশ বছর পরেও, লম্বা ইন্টারভ্যালের পরেও গল্পের পার্ট-টু টা দুঃখের নয়, আনন্দের - পুরোন স্মৃতিটুকুর মতই।
আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, পিকচার অভি বাকি হ্যায়। প্রচুর গল্প আছে।
চলবে ...
 Amit | 121.2.***.*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৯:১৩735839
Amit | 121.2.***.*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৯:১৩735839- বাহ্। শেষটা আগে পড়ে ফেললাম। বাকিটা আবার ফিরে পড়ছি। মিখাইল সের্গেইভিচ মানে কি গর্বাচেভ ?
 সে | 2001:1711:fa42:f421:5de5:f9b4:9f5:***:*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:২৬735840
সে | 2001:1711:fa42:f421:5de5:f9b4:9f5:***:*** | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:২৬735840- হ্যাঁ।
-
 যোষিতা | ০১ মার্চ ২০২৪ ১৯:০৭742421
যোষিতা | ০১ মার্চ ২০২৪ ১৯:০৭742421 - এটা আবার কন্টিনিউ করব
 দীমু | 182.69.***.*** | ০৮ মার্চ ২০২৪ ১০:১৮742497
দীমু | 182.69.***.*** | ০৮ মার্চ ২০২৪ ১০:১৮742497- বসে আছি
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Faruk Munshi, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পম্পা ঘোষ)
(লিখছেন... দ, প্যালারাম, .)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... অরিন, হীরেন সিংহরায়, অরিন)
(লিখছেন... Somnath mukhopadhyay, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, albert banerjee)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... dc, albert banerjee)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত