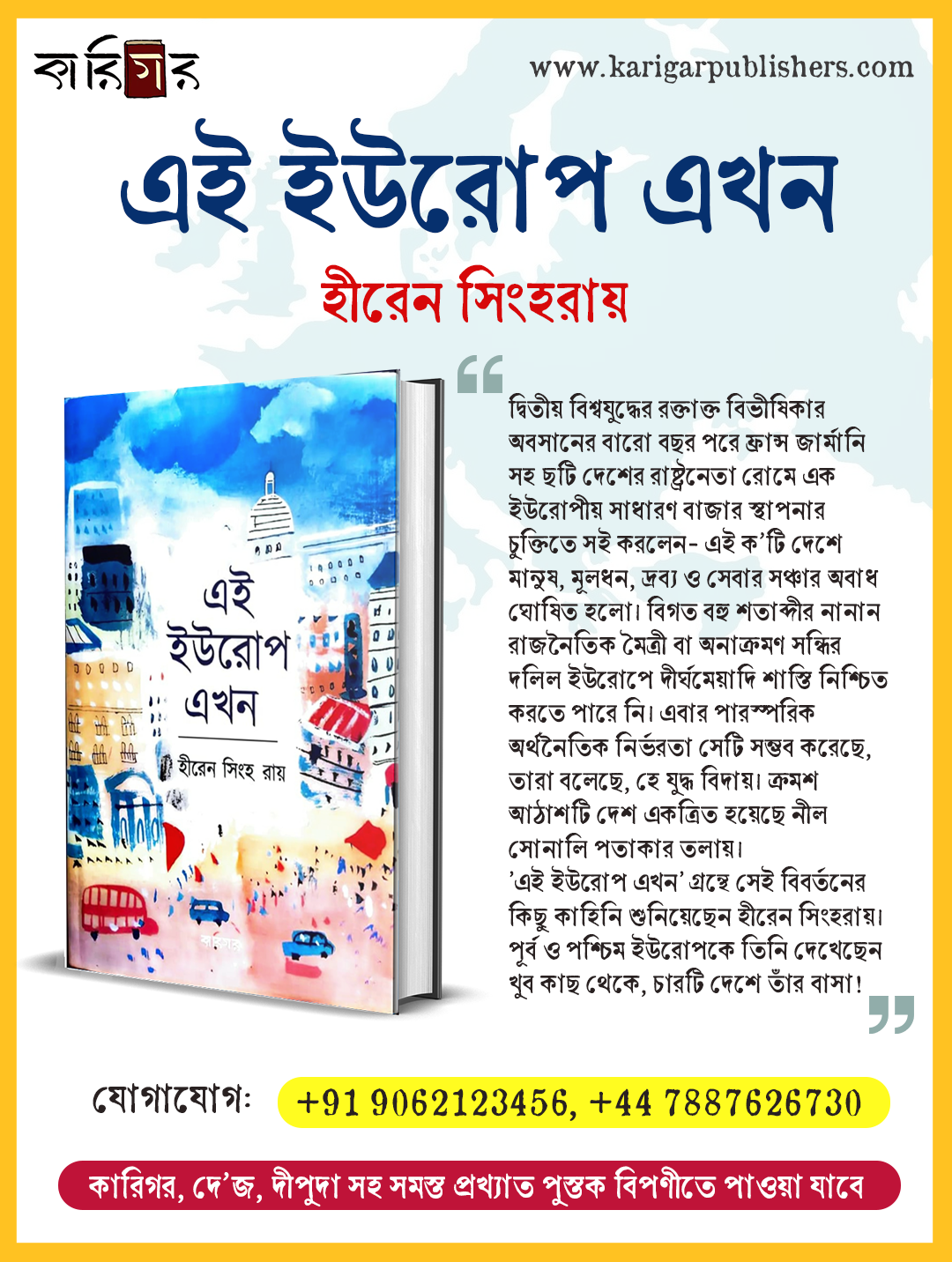- খেরোর খাতা

-
বিদ্যাসাগরপুজো ও বাংলাভাষা
Somnath Roy লেখকের গ্রাহক হোন
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ২১৪৯ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন) - বিদ্যাসাগরপুজোর হিড়িকে আমরা যেন ভুলে না যাই তাঁর প্রায় একশ বছর আগে রামপ্রসাদ সেন বাংলাভাষায় যে পদগুলি রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে আজকের লিখিত বাংলার ফারাক সামান্যই। এবং তাঁর বহু পদ বরিশালের মাঝিমাল্লার কাছ থেকে উদ্ধার করে ঈশ্বরগুপ্ত কবিকাহিনিতে ছাপিয়েছিলেন। তবে রামপ্রসাদী বাংলা যাকে বলে যবনীমিশেলযুক্ত, যে বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদূরিত করার ইচ্ছে অনেকে আজ প্রকাশ করছেন।
আরও ইন্টারেস্টিং দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে চৈতন্যসাহিত্য থেকে কিছু বাংলা গদ্যের নমুনা দিয়েছেন, যেগুলি প্রায় পাঁচশ বছর আগে রচিত। পাঠক পড়লে দেখবেন, সেই অর্বাচীন বাংলায় কত প্রাঞ্জল গদ্যরচনা হত।
বাংলাভাষার আগের অর্জনগুলি ভুলে/ না জেনে জপেনদার মতন শুধু বিদ্যাসাগরচর্চা করলে আমরা একটা বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে উঠতে পারব না। সেইটা হল, রামপ্রসাদে্র সময় অবধি গড়ে ওঠা বাংলাভাষা কী কারণে পরবর্তীযুগে বিস্মৃত হল? কেন এরকম এক দুরূহ 'সাধুভাষা'র প্রবর্তন হল, যাকে উদ্ধার করতে একজন রবীন্দ্রনাথের দরকার পড়ল?
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
Somnath Roy | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ২২:২৫97749
 প্রাঞ্জল গদ্যরচনা | 2600:1002:b012:df40:fd3f:bcbc:6c82:***:*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৩:৫৫97752
প্রাঞ্জল গদ্যরচনা | 2600:1002:b012:df40:fd3f:bcbc:6c82:***:*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৩:৫৫97752এ নিয়ে একটু বিস্তারিত হয় না ?
-
Somnath Roy | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:১০97759
ধরুন, রূপ গোস্বামীর কারিকা থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি- “পূৰ্ব্বরাগের মূল দুই । হঠাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ শ্রবণ। আগে তার সেবা। তার ইংগিতে তৎপর হইয়া কাৰ্য্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে ।”
প্রাঞ্জল এবং ছন্দোময়। অথচ আমরা শুনে এসেছি বিদ্যাসাগরের আগে বাঙালি গদ্য লিখত না। রামমোহন প্রমুখের গদ্য খুব সুবিধের নয়, এও সত্যি।তাহলে কটি প্রশ্ন থাকে-এক, এই গদ্য ব্যতিক্রম কী না? দীনেশ সেন প্রমুখ কিছু বাংলাগদ্যের উদাহরণ পেয়েছেন। তা সংখ্যায় প্রচুর নয় একথা সত্যি। কিন্তু, তার ভাষারীতি যদি দেখি, পদ্যের ভাষার থেকে অদীক্ষিত কানে খুব পৃথক ঠেকবে না। যেমন উপরের উদাহরণের সঙ্গে নরোত্তম দাসের পদ তুলনা করি- ‘প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিবা /তার পর রাধাকৃষ্ণ সেবা যে করিবা।' দেখব শব্দচয়ন ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার প্রায় একরকম।তাহলে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়, গদ্য এত কম লেখা হত কেন? একটা জিনিস বোঝার ছাপাখানার আগের যুগে বইপত্তর সীমিত সংখ্যায় থাকত। আর আইন আদালতের কাজ আজকের মতনই শাসকের ভাষায় হত। তাহলে সাহিত্য দরকার হত কীসে? তত্ত্ব, তথ্য ও রূপরস আদানপ্রদানে। আমরা খেয়াল করব, রামপ্রসাদের পদ বরিশালের মাঝিদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ব্যাপক মানুষের কাছে ভাবনা প্রায় অবিকৃত আকারে পৌঁছবে যদি তা তার স্মৃতিতে থাকে, তাই সম্ভবতঃ পদরচনার দিকে বেশি সচেষ্ট হয়েছিলেন কবিরা। তাঁরা গদ্য লিখেছেন কিন্তু গণসাহিত্য গদ্যে হয় না। তাই প্রাথমিক সাহিত্যফর্ম ছিল অন্তমিলযুক্ত, নির্দিষ্ট কাঠামোর পদ। তত্ত্ব কথা হয় সুরে ফেলা হত নয় কাহিনিতে বর্ণ্না করা হত, যাতে মুখে মুখে ফেরা মানুষের গান হয়ে যায়।তৃতীয় প্রশ্ন, সেই গণসাহিত্যের ধারা বর্জিত হল কেন? সেইটার উত্তর খোঁজা দরকার।
 T | 146.196.***.*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:০৪97764
T | 146.196.***.*** | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:০৪97764এই গদ্য ব্যতিক্রম। সেদিনই ভাটে এই দীনেশবাবুর উল্লিখিত পদটার কথা বলছিলাম। এরকম কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে ভুলে ভরা সংস্কৃত সমেত। পদ্য তো বোঝা যায় দিব্যি। ছাপাখানা নেই, এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ভাষারীতি তখন তাদের স্থানিক বৈশিষ্ট্য সমেত জ্বলজ্বলিং, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তো নেই। গদ্যে লিখিত গণসাহিত্যের ধারা কি ছিল আদৌ ?
-
Somnath Roy | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৪:৩৭97765
না আমার ধারণা গদ্য সেই কারণেই বেশি লেখা হত না। লেখকরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতেন- নিজের সম্প্রদায় বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কাছে নিজের বক্তব্য পৌঁছনোর দায়টাই মূল ছিল। সেই কারণেই গদ্য বেশি লেখা না হওয়ার কথা। এই আচরণ মালা, সন্দর্ভ (দেহকড়চ) ইত্যাদি খুব সীমিত অডিয়েন্সের জন্যই লেখা মনে হয়।
-
 Ishan | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:১৪97773
Ishan | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:১৪97773 যতি চিহ্ন জানলে গদ্য না জানবার কী আছে? তবে পুরোনো বাংলায়ও গদ্য লেখাকে কোনো কুশলতার পরিচায়ক মনে করা হতনা। ও তো সবাই পারে, টাইপ। এতে করে নি:সন্দেহে আমরা অনেক মণিমুক্তো হারিয়েছি।
Swarnendu Sil আমাকে আর্যভট্ট পড়তে দিয়েছিল। টীকা ছাড়া এক লাইনও বুঝতে পারিনি। আন্দাজ করতে পারি ফান্ডাটা ছিল, রচনাকার ছন্দে বেঁধে সূত্রগুলো লিখে রাখবেন, কিন্তু আসল বিদ্যাটা গুরুক কাছ থেকেই শিখতে হবে। সে গুরুও ভোগে, বিদ্যাও ভোগে, এখন শুধু গরুদের দাপাদাপি।
সে বই অবশ্য সংস্কৃতে। কিন্তু বাংলায়ও চিন্তার ধরণ আলাদা ছিল ভাবার কোনো কারণ নেই।
-
 Ishan | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:৪৫97774
Ishan | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০৯:৪৫97774 আরেকটা কথা হল রামপ্রসাদী বাংলা অসম্ভব সুন্দর। সাধারণভাবে কোনো লেখার গুণাগুন বিচার করা হয়, সেই সময়ের নিরিখে। পরবর্তীতে সেরকম আর কেউ লেখেননা। এমনকি রবীন্দ্রনাথের বহু অসাধারণ গান বা কবিতা, ধরুন, সোনার তরী, আজ হুবহু ওই ভাষায় লেখা হলে কেউ ছাপতেননা। দোষ রবীন্দ্রনাথেরও নয়, আজকের সম্পাদকেরও নয়, সময় এবং লিখনভঙ্গী পাল্টে গেছে।
কিন্তু রামপ্রসাদ, আমার জানা সমস্ত বাঙালি কবি এবং লেখকের মধ্যে, রামপ্রসাদ হলেন দুইটি ব্যতিক্রমের একজন। কোন অপরাধে, দীর্ঘমেয়াদে, সংসার গারদে থাকিব -- এ বস্তু আজ লিখতে পারলেও লোকে গর্ববোধ করত। থাকিব শব্দটা বাদ দিলে, এমনকি রকব্যান্ডেরও সুপারহিট গান হতে পারত আজও।
যেটা ধাঁধা, (এলেবেলেবাবু বলবেন, মোটেই ধাঁধা নয়), সেটা হল বিদ্যাসাগর এই পুরো ধারাটা জেনেও বাংলাকে সংস্কৃত কণ্টকিত করে তোলার কাজে কেন ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ওই গুরুগম্ভীর ভাষা, কেন খামোখা কেবল তৎসমে পরিপূর্ণ? সংস্কৃত তো আকাশ থেকে পড়েনি। বরং বৃটিশ শাসনের অব্যবহিত আগেই বাংলার সংস্কৃত শিক্ষা গৌরবের চরমে ছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নবদ্বীপ এবং বারাণসী সমগোত্রীয় ছিল, যে গরিমা ইংরেজ আমলের কল্যাণে শুধু উবে যায় নয়, ধীরে ধীরে বিস্মৃতও হয়। সে ফার্সি শিক্ষারও প্রবল চল ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বা ফার্সি সুপন্ডিতরা কেউ বাংলাকে ঘেঁটে দেবার তালে ছিলেননা। সংস্কৃত এবং ফার্সি শব্দ বাংলায় হরবখৎ ঢুকেছে, ঢোকারই কথা, কিন্তু বাংলাকে সংস্কৃত করে ফেলার চেষ্টা তখন ছিলনা। সেটা শুরু হল সংস্কৃত এবং ফার্সি যখন উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে তখন।
এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বজনবিদিত। ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে প্রতিভাবান পুরুষটি কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টোদিকে হেঁটেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ের লোতির অনুবাদ পড়লে পুরোনো রামপ্রসাদী বাংলার ছাঁচ দেখা যায়। এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই লেখাটিও আজও সাম্প্রতিক বলে অবিকল ছেপে দেওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হলেন সেই দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, কাল যার উপরে ছাপ ফেলেনি।
এই দুই ব্যতিক্রম যে আমাদের ভাষায় আছেন, সেটাই প্রমাণ করে মোটামুটি একশ বছর খানেক উল্টো স্রোতে হাঁটার চেষ্টা করে আমরা ফেরত আসি আবার আমড়াতলার মোড়ে। সাধু বাংলা তৈরি এবং তার বিসর্জন, এই দুটোই হল বস্তুত মাটি খোঁড়া এবং বোজানোর পণ্ডশ্রম।
এইটা কেন হয়েছিল সত্যি বুঝিনা। ধর্মীয় কারণে নয়। কারণ বিহারীলাল কিংবা রবীন্দ্রনাথ, কেউই ফার্সিবিরোধী কিছু ছিলেননা। ঔপনিবেশিক ভদ্রলোক সংস্কৃতি প্রচলনের জন্য ছোটোলোকের ভাষা থেকে নিজেকে পৃথক করার জন্য নয়। তেমন হলে ইংরিজিই তো ছিল এলিটপনা দেখানোর জন্য। দেখানো হতও। আর ভদ্রলোক নামক বর্গটির উৎপত্তি, এখন যেভাবে ভূমিসত্বভোগীদের সঙ্গে জুড়ে দেখানো হয়, ব্যাপারটা ঠিক তাও নয়। কলকাত্তাইয়া ভদ্রলোকরা নব্য জমিদারীর ফসল, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভদ্রলোক বর্গ তো কেবল ঔপনিবেশিক না। টুলো পন্ডিতদের আমল থেকেই সুসংস্কৃত পণ্ডিত ব্যাপারটা চালু ছিল। তাঁরা কখনও সংস্কৃত পান্ডিত্যকে বাংলার ঘাড়ে চাপাননি।
মনে হয়, সংস্কৃত যখন তার জায়গা হারাতে শুরু করল, যা নেই, তার অভাববোধই সংস্কৃত পন্ডিতদেরকে বাংলার ঘাড়ে সংস্কৃতকে চাপিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। ওভাবেই সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন হবে, এইরকম গোষ্ঠীগত অবচেতন কাজ করেছিল হয়তো। যেভাবে খ্রিশ্চানরা দেখে রেজারেকশনকে। অথবা ফ্রয়েডিয় ডিসপ্লেসমেন্টও হয়তো বলা যায়। কে জানে।
-
Somnath Roy | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:২৬97777
'সাধু'ভাষা নির্মাণে ফার্সি বাদ দেওয়ার সচেতন প্রয়াস আলাদা করে লক্ষ্য করা যায়। সেটা কি একটা বড় কারণ ছিল? পুরোনো শাসকের ভাষা/ ভাষিক প্রভাব বর্জন করে নতুন জমানার গেঁড়ে বসা নিশ্চিত করতে।
বিষয়টা হচ্ছে, এই আমলের সাহিত্যকীর্তি থেকে মুসলমানরা পুরো বাদ। চৈতন্যসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের যুগেও মুসলমানের প্রভাব, অংশগ্রহণ দেখা যায়। আবার উনবিংশ শতাব্দীর ভাষানির্মাণ যখন চলছে, সেই সময় বাংলার মুসলমান সমাজ ব্রিটিশদের সঙ্গে এক দীর্ঘমেয়াদি লড়াই চালাচ্ছে। বাংলা থেকে সবচেয়ে বেশি জেহাদি উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করতে যেত বলে হান্টার জানাচ্ছেন। অথচ, এই পুরো ইতিহাসটা কলকাতার উত্থানের সঙ্গে জলবিভাজিত হয়ে আছে। কেবল তিতুর নারকেলবেড়িয়া জঙ্গ (লক্ষ্যণীয়, যুদ্ধ নয় জঙ্গ) ছাড়া মুসলিম সমাজের কোনও বিদ্রোহের প্রভাব বাংলার মূলধারার ইতিহাসে দেখা যায় না। সেই বিচ্ছিন্নতাই ভাষার সংস্কারের একটা উপাদান হয়েছে কি?
-
Somnath Roy | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:৪৬97778
রামপ্রসাদ হয়ত শতাব্দীতে একজন তৈরি হন, কিন্তু রামপ্রসাদের ধারা পৃথক কিছু নয়। বৈষ্ণব পদাবলী এমন কি বাউলফকিরদের অনেকের পদ পড়লে মনে হয় হুবহু আজকের ভাষায় লেখা। এঁরা সকলে একটি ধারার ফসল। এঁদের মধ্যে অনেকে একাধিক ভাষায় পদ রচ্না করতে পারতেন- কোন অডিয়েন্সের জন্য কেন লিখছেন সে হিসেবে নিজের ভাষা পাল্টাতেন।
একটা জিনিস ভেবে দেখার, কবিওয়ালাদের বাংলা কিন্তু সেই সহজতা থেকে বিচ্যুত হয় নি। বাংলার পদকর্তাদের একটা ধারা ছিল, যা আধুনিক বাংলার সামনে নষ্ট হল বলে মনে হয়। গদ্য বাংলা কখনওই সেই গণসাহিত্যের রূপ পায় নি।নরোত্তম দাসকে নিয়ে আগে গুরুতে লিখেছিলাম। আবার লিঙ্কটা দিলাম, ওনার বিভিন্ন লেখা, গান ইত্যাদি দেখলে এর একটা আভাস পাওয়া যায়। পারলে পড়ো- https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=14104
 সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:৫১97779
সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:৫১97779গদ্য লেখায় সংস্কৃত ভাষার যোগের পেছনে যে সংস্কৃত পন্ডিতদের উদ্যোগ ছিল এরকম একটা যুক্তি বঙ্কিমের "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধতে আছে। এই লেখাটি কিন্তু সংস্কৃতবহুল গদ্যরও ক্রিটিক (বিদ্যাসাগরী ভাষা) আবার অন্যদিকে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষারও ক্রিটিক (যেহেতু টেকচাঁদি ধরণ দিয়ে বা সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার ধরণ দিয়ে গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ের প্রকাশ কুলোয় না।)
তো এই প্রবন্ধটির প্রথমদিকে আছে -
"কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা;অপরটির নাম অপর ভাষা"।
সাধুভাষা কেন প্রচলিত হল সেটার কারণঃ
"গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতেই পারেই না। .... সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব।"
এই "সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের" প্রভাব কতখানি ছিল, কেন ছিল সেসব বিচারের বিষয়।
 সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:৫৮97781
সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১০:৫৮97781লেখাটায় এও ছিল যে -
পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত - এখনও হইতেছে।
যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অবুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকারী।
পদ্যের কাজ আর গদ্যের কাজ এই দুটিতে ভাগ ছিল, সভ্যতার উন্নতি, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় যে যুক্তি-তর্ক-বিচার ইত্যাদি, সেই কাজে গদ্যই দরকারী, এরকম একটা মত ছিল বলে মনে হয়।
 এলেবেলে | 202.142.***.*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:১৫97783
এলেবেলে | 202.142.***.*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:১৫97783ঈশান যেহেতু আমার প্রসঙ্গে এনেছেন, তাই সোমনাথ-ঈশান-সিএস তিন গুণী ব্যক্তিকেই বলব, এ বিষয়ে আমার লেখার তৃতীয় অধ্যায়ে চোখ রাখতে। কান টানব, মাথা আপসে আপ হাজির হবে।
ডিসক্লেমার - ইহা কোনও 'টিজার' নহে।
-
 সম্বিৎ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:৩৬97785
সম্বিৎ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১১:৩৬97785 রামপ্রসাদের বাংলা নিয়ে কোন কথা হবে না -
জানি জুঁই-মালতী হায়,
কত গন্ধ যে ছড়ায়
তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়।
ওরে, তোর মত যে নেইকো তাদের মায়ে-পোয়ে আলাপন।এই আটপৌরে কথা কাব্যসঙ্গীতের চক্করে অনেক ফর্মাল হয়ে গেছিল। অথচ বহুদিন অব্দি আধা-শহুরে কবিগান, আখড়াই, হাপ-আখড়াইতে এই ধরণের মানুষের মুখের কথা বসত। শহুরে সংস্কৃতিতে শ্লীল হবার আকাঙ্খায় বোধহয় গানের কথা পাল্টাতে আরম্ভ করল। নিধু থেকেই এই বদল দেখা যাবে। তখন কোথায় বিদ্যেসাগর?
রামমোহনের বাংলা কেমন ছিল? দেবেন ঠাকুরের? ব্রাহ্ম বাংলা ওই উপনিষদ-ঘেঁষা তৎসম-বহুল ভাষা চালু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তো সেই শুনেও বড় হয়েছেন। হিঁদু বঙ্কিম আর বিদ্যাসাগরের তৎসমবহুল বাংলা কি ব্রাহ্ম বাংলাকে কাউন্টার করতে?
-
 lcm | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:০২97786
lcm | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:০২97786 Linguistic Purism .... https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_purism
 সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৩৩97788
সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৩৩97788ঈশান লিখেছে -
"বঙ্কিমচন্দ্রের ওই গুরুগম্ভীর ভাষা, কেন খামোখা কেবল তৎসমে পরিপূর্ণ?"
কিন্তু ঐ প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল ,
বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে , যতটুকু বলিবার আছে , সবটুকু বলিবে - তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।
এ থেকে মনে হয়না যে ভাষার ব্যাপারে ওনার ছুৎমার্গ ছিল । বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা আর প্রবন্ধের ভাষা তো অনেকটাই আলাদা, উপন্যাসেও ভাষা বদলেছে, প্রথম দিকের উপন্যাসের তুলনায়, পরে। সংস্কৃত কাব্যর প্রভাব ছিল হয়ত, যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করছেন।
 সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৫০97790
সিএস | 2405:201:8803:bf6f:f861:92bb:4ff4:***:*** | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১২:৫০97790প্রথম নোটটিতে সোমনাথবাবুর লিখেছিলেন -
কেন এরকম এক দুরূহ 'সাধুভাষা'র প্রবর্তন হল, যাকে উদ্ধার করতে একজন রবীন্দ্রনাথের দরকার পড়ল?
পড়ে মনে হয় সাধুভাষা থেকে মুক্তির কথা রবিবাবুই ভেবেছিলেন শুধু। ওরকম ছিল না মনে হয়, ভাষা নিয়ে দ্বন্দ তো বঙ্কিমের লেখাতেই পাওয়া যাচ্ছে।
এই তর্কটা মনে হয় অনেকদিন ধরেই ছিল, রবিবাবু সেটা এক্স্টেন্ড করেছিলেন।
-
Somnath Roy | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ১৬:৪৯97813
শুধু এক্সটেন্ড বললে ভুল হবে, ক্লিঞ্চ করিয়েছিলেন। লিখিত বাংলাভাষাকে মানুষের ভাষা করে তোলা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলেই সম্ভব হয়েছিল মনে করি। আরও কেউ কেউ ভাবলেও, ব্লো টা রবীন্দ্রনাথই দিতে পেরেছিলেন।
 দীপ | 2402:3a80:196c:3865:778:5634:1232:***:*** | ২৮ মার্চ ২০২৫ ১১:৩৫541956
দীপ | 2402:3a80:196c:3865:778:5634:1232:***:*** | ২৮ মার্চ ২০২৫ ১১:৩৫541956- "সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার অভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন– আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্, এবং নিজের বাক্চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন, কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎচরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিস্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্ক-জাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি– এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"ভাদ্র, ১৩০২, চারিত্রপূজা
 দীপ | 2402:3a80:196b:f7c4:678:5634:1232:***:*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ০১:২২541988
দীপ | 2402:3a80:196b:f7c4:678:5634:1232:***:*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ০১:২২541988- ২০২২ সালের গঙ্গাসাগর মেলা চলছে। মনসাদ্বীপ আশ্রমের তরফে গঙ্গাসাগর ক্যাম্পাসে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের মনসাদ্বীপ আশ্রমের গেস্ট হাউসে আছেন বড় পুলিশ আধিকারিকরা। প্রথম দিন এসে শুনলাম একজন এস পি সাহেব এসেছেন তিনি মেলা চলাকালীন আমার সঙ্গে কোন একদিন দেখা করতে চান ও একসঙ্গে প্রসাদ পেতে চান। আমি যেহেতু দুপুরে ও রাতে মেলা প্রাঙ্গণেই প্রসাদ পাই তাই ঠিক হল সকালের প্রাতরাশ একসঙ্গে খাওয়া যাবে।
পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়া হল। আধিকারিক রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার বাসিন্দা। কথা হল আশ্রম নিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে। খাওয়া শেষ হতে আমি ওনাকে এগিয়ে দিতে এলাম। মন্দিরের সামনে আসতেই উনি আমার হাত দুটো নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে সজল চোখে বললেন, "জানেন তো মহারাজ, আমরা রাজস্থানীরা আপনাদের দুজন বাঙ্গালী মহাপুরুষের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। একজন হলেন রাজা রামমোহন রায় অন্যজন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। এনারা ছিলেন বলে আজ আমাদের মেয়েরা সতী হবার হাত থেকে বেঁচেছে আর সুদূর ঝুনঝুনু গ্রামে মেয়েরা স্কুলে পড়ছে। আপনার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য স্বামী বিবেকানন্দ নয়।আসল উদ্দেশ্য সেই মহানদের আমার নিজের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।"
ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। ভুলেই গিয়েছিলাম ঘটনাটা। আজ যখন চারিদিকে নারী দিবস পালনের ঢেউ চলছে তখন হঠাৎই এই ঘটনা মনে পড়ল। কই আজকের দিনে ভুলেও তো কোন নারীকে এঁদের কথা বলতে শুনলাম না?
আমার বিনম্র প্রণাম এই দুই মহামানবকে।
স্তবপ্রিয়ানন্দ
 দীপ | 2402:3a80:196b:f7c4:678:5634:1232:***:*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ০১:২৩541989
দীপ | 2402:3a80:196b:f7c4:678:5634:1232:***:*** | ৩০ মার্চ ২০২৫ ০১:২৩541989- নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরো পাপ। পূর্বপ্রজন্মের মিথ্যা নিন্দা জঘন্যতম পাপ।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন , asim nondon, Guruchandali)
(লিখছেন... দেবোপম, কৃশানু ভট্টাচার্য্য , kk)
(লিখছেন... Typo, Typo)
(লিখছেন... দ, aranya, b)
(লিখছেন... a)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... ., হাঅভাপ্রা, হাঅভাপ্রা)
(লিখছেন... aranya)
(লিখছেন... Mrকুমুদি, ., Asim Bhattacharyya)
(লিখছেন... Nirmalya Nag, Ranjan Roy, Kuntala)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।